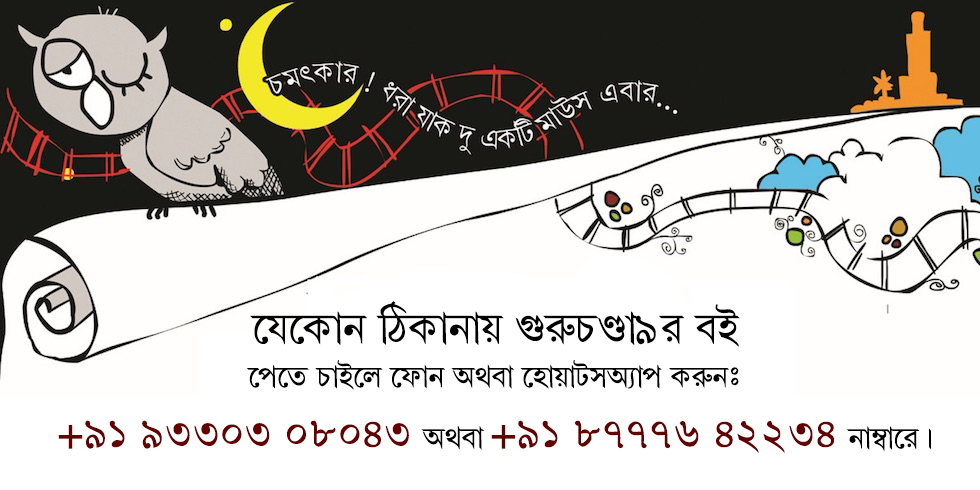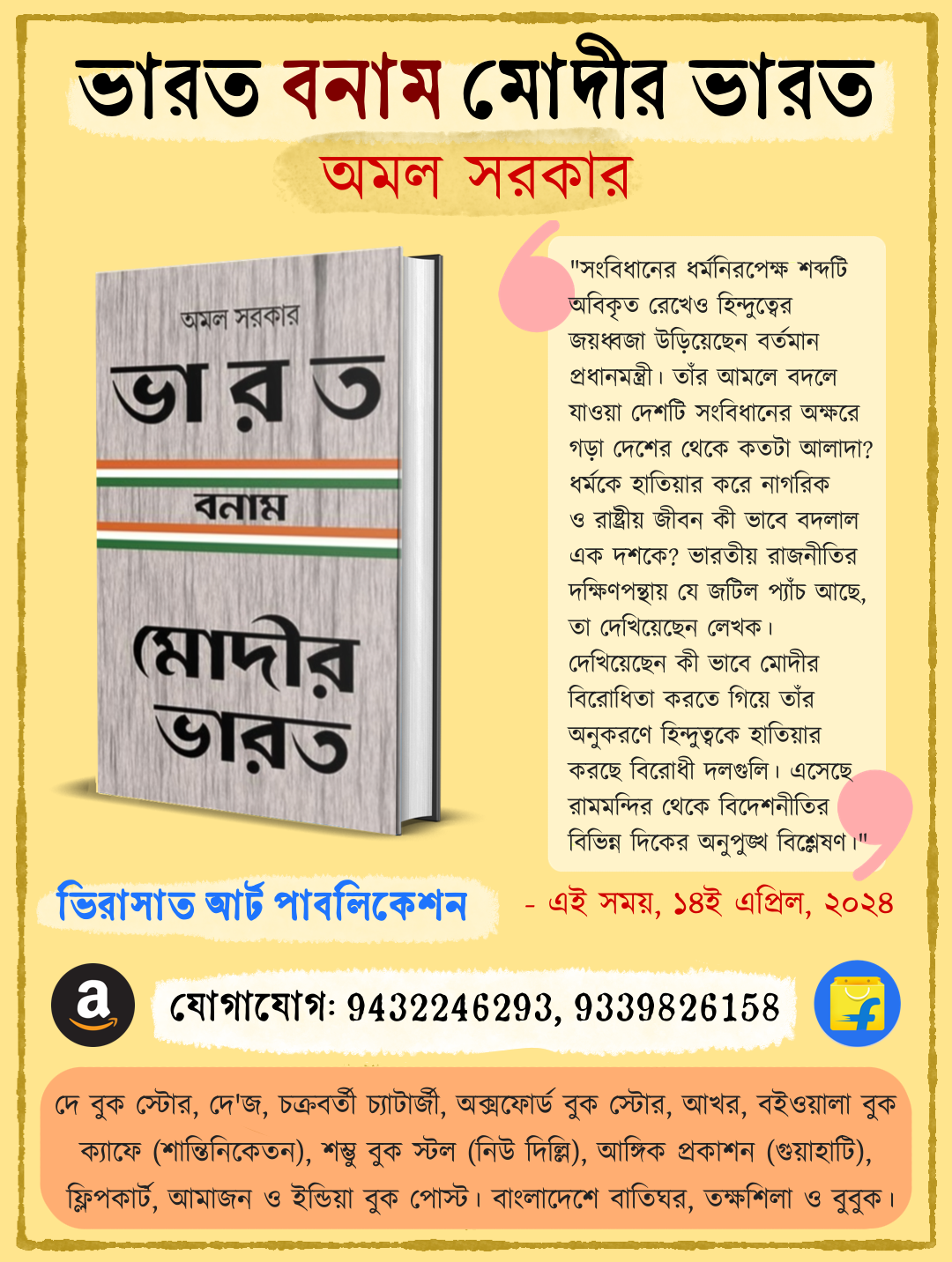- হরিদাস পাল ব্লগ

-
অনন্ত লেকের জলে চাঁদ পড়ে আছে
Sakyajit Bhattacharya লেখকের গ্রাহক হোন
ব্লগ | ২৩ জুন ২০১৬ | ৯৭১৮♦ বার পঠিত - তারপর একদিন আমরা জেগে উঠি দীর্ঘ নিদ্রার পর। রূপকথার মতো, নারীর মতো, প্রেমের মতো সেইসব প্রথম ভোরের আলোয় সত্যের মুখ দেখা যায়। সেই অনাস্বাদিত ভোরবেলায় আমি ফিরে আসি গন্তব্য ছেড়ে, লাস্ট ট্রেন মিস করে নিজের শিকড়ের কাছে। সে আমার নিজস্ব মাকন্দো। আমার দক্ষিণ কলকাতা। প্রথম প্রেমের মত যাকে লুকিয়ে রাখতে হয় টেস্টপেপারের পাতার ভাঁজে। সেই প্রেম তাত্বিকতার খবর রাখে না। তা ছিল নিতান্তই সমর্পণ। তাতে সরলতা ছিল।
আমরা যারা গদার বর্ণিত মার্ক্স ও কোকাকোলার সন্তান, তাদের নব্বই দশকের প্রেমে তুমুলভাবে ফিরে ফিরে এসেছে দক্ষিণ কলকাতা। এমনকি উত্তরের ছেলেমেয়েরাও প্রেম করতে চলে আসত এখানে। এই সেই গড়িয়াহাটার মোড়, যেখানে ভিড়ে ভিড়াক্কার রাস্তায় প্রেমিকার হাতবদল হয়ে যায় অনায়াসে। এই সেই গলফগ্রিন কবরখানা, যেখানে অ্যাংলো তরুণীর কবরের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া যেত। এবং এখানেই সেই ঢাকুরিয়া, যার অনন্ত লেকের জলে চাঁদ পড়ে ছিল। আছে।
আমি বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়তাম, এবং অবধারিতভাবে আমাদের বন্ধুদের প্রথম প্রেম ঘুরেফিরে ধাক্কা খেয়েছে রিচি রোড, লাভলক সরণী আর ম্যাডক্স স্কোয়ারের আধো অন্ধকার গলিঘুঁজিগুলোতে। শীত পড়ার আগে আগে, যখন একটা আবছা ধোঁয়াটে চাদর জড়িয়ে থাকে সন্ধের শহরের গায়ে, সেই সময়ে এইসব জায়গাগুলো মায়াময় হয়ে ওঠে। একটা নরম মনকেমন আলগা লেগে থাকে ফুটপাতের পাশে কৃষ্ণচূড়ার শরীরে, ম্যাডক্সের ঘাসের শিশিরে, উঁচু উঁচু পুরনো ফ্ল্যাটবাড়ির কালচে বিবর্ণ দেওয়ালে। হাজরা রোড থেকে তিনখানা পরপর গলি দিয়ে ম্যাডক্স স্কোয়ারে ঢোকা যায়। তার একটার গায়ে আটকে থাকা অনেক পুরনো পুরনো বাড়ি আছে। সেখান দিয়ে হেঁটে গেলে সন্ধেবেলা নাচের ধপধপ আওয়াজ পাওয়া যেত। পাওয়া যেত ঘ্যাসঘ্যাসে রেডিওর বেগম আখতারকে। কত কত সন্ধেবেলা আমি এবং সেই মেয়েটি দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়েছি সেইসব বাড়িদের সামনে ! চুপচাপ শুনে গেছি ‘তুঝসে মিল কর হামে, রোনা থা, বহোত রোনা থা’। বেগম কাঁদতেন। গ্র্যান্ডফাদার ক্লকে ঢং ঢং করে ছ’টা বাজত। কেউ একজন দোতলা থেকে গলা তুলে বলত, “মালতি, চায়ের জল চাপানো হল?” অন্ধকার ম্যাডক্স স্কোয়ারের বেদিগুলো তখন সন্ধ্যের পাগল, পথহারানো ভিখিরি আর মনকেমন ক্লান্ত বেশ্যাদের মাথা রাখার জায়গা। এই পৃথিবীর কোনো ঈশ্বর যে জীবনকে কখনো কুড়িয়ে নেবে না।
আরো ছিল বিড়লা মন্দিরের পাশের গলি। গোটা গলিটা অস্বাভাবিক রম্য এবং নির্জন। প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে যাবার পর দুম করে ধাক্কা খেয়ে শেষ হচ্ছে এক প্রাসাদোপম নিস্তব্দ বাড়ির গেটে। রাস্তার দুধারে প্রহরীর মত পাহারা দিচ্ছে কৃষ্ণচুড়া এবং রাধাচুড়া, ঝড়ের সময় আমাদের শরীরে যারা ঝরণার মত ফুলের কুঁড়ি বিছিয়ে দিত। হিম হিম নীরব সেই গলির একটা ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকত এক অন্ধ অ্যালসেশিয়ান। তাকে নিয়ে তার বৃদ্ধা মানুষ বন্ধুটি প্রতিদিন বিকেলবেলা গলিপথে হাঁটতেন। অন্ধ কুকুর মাঝে মাঝে চলতে চলতে ল্যাম্পপোস্টের গায়ে ধাক্কা খেত। ককিয়ে উঠত আলতো। কিন্তু বৃদ্ধা কিছুতেই তাকে চেনে বাঁধতেন না। ছেড়ে দিতেন নিজের মত করে। গন্ধ শুঁকে শুঁকে নড়বড়ে পায়ে আবার সে টলতে টলতে ফিরে আসত বন্ধুর কাছে। হাঁটুতে মাথা ঘষত। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া হত। রাস্তার ধারে একটা বেঞ্চে বসে থাকত দুজনে । সম্ভবত এই পৃথিবীতে দুজনেই নিঃসংগ ছিল। অনুমান করতাম, কারণ আমার প্রেমিকা একবার সেই কুকুরটির মাথায় হাত বোলাচ্ছিল, আর কুকুরটি বারেবারে গন্ধ শুঁকে অনুমান করবার চেষ্টা করছিল কে এই নতুন মানুষ! বারেবারে মাথা ঝাঁকিয়ে, নাক ওপরে তুলে, প্রাণপণে হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিচ্ছিল, জিভ দিয়ে চেটে দিচ্ছিল গা। সম্ভবত বৃদ্ধাটিকে বাদ দিলে তার ভাগ্যে অন্য মানুষের আদর জুটত না। আমি অ্যালসেশিয়ানটির অন্ধ চোখে তখন জল দেখেছিলাম। দক্ষিণ কলকাতার প্রেমের কথা উঠলে আমার আজও অবধারিত মনে পড়ে যায় এক অন্ধ অ্যালসেশিয়ানের চোখের কোণায় এক ফোঁটা জলকে।
আমরা তখন সদ্য স্কুল পেরচ্ছি, কলেজে ঢুকব ঢুকব করছি। দুহাজার সাল ততদিনে দুই তিন বছরের পুরনো হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যবিত্ত টানাটানির ছাত্রজীবনে প্রেম মানে তখন টিউশনির টাকা বাঁচিয়ে বালিগঞ্জ ধাবায় এক প্লেট মাটন কষা আর দুখানা রুটি ভাগাভাগি করে খাওয়া। বইমেলাতে সারাদিন দুজনে ঘুরে ঘুরে দুখানা লিটল ম্যাগ কিনে শুকনো মুখে বাইরে বেরনো। প্রেম মানে তখন হাজরা থেকে হেঁটে হেঁটে আনোয়ার শা রোড আসা। বাসভাড়া দিয়ে একটা এগরোল কিনে দুজনে ভাগ করে খাওয়া। যখন রোলটা শেষ হয়ে আসত, দুজনেই শক্ত করে কাগজটা চেপে ধরে রাখতাম। পালা করে অল্প অল্প কামড় দিতাম। যাতে অপরজন শেষ টুকরোটুকু খেতে পারে। প্রেম মানে তখন পাড়ার এসটিডি বুথে ২ টাকা দিয়ে পাঁচমিনিট ফোন করে তিনমিনিট দুজনেই চুপ করে থাকা। কি বলব কেউ জানত না। আজকের জেন ওয়াই সম্ভবত ভাবতেও পারবে না মোবাইল ফোনবিহীন সেই যুগে চিঠি লিখে প্রোপোজ করার অনুভূতি কেমন ছিল। ডায়রির পাতা ছিঁড়ে যত্ন করে গোটা গোটা অক্ষরে লিখে তাকে দুভাঁজ করে রেখে দেওয়া বইয়ের ফাঁকে। দুরুদুরু বুকে নীল স্কার্ট আর দুই বিনুনীর গম্ভীর চশমাওয়ালা মুখের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো। কাঁপা হাতে তুলে দেওয়া চিঠি। বেশিরভাগ সময়েই উত্তর আসত ‘পরে জানাব’। সেই ‘পরে’টা সাধারণত আর আসত না। আস্তে আস্তে সকলেই ভুলে যেত। একলা রোগা ছেলেটি শুধু মাঝে মাঝে একটু অন্যমন্সক হয়ে পড়ত যখন মেয়েটির স্কুলের সামনে দিয়ে যেত। হয়ত পা-টা ধীর হয়ে যেত অজান্তেই। তারপর সমবেত স্কুলবালিকাদের খিলখিল হাসির শব্দে চমকে গিয়ে কান ফান লাল করে দ্রুত পায়ে প্রায় দৌড়ে পার হয়ে যেত সেই চত্বর। তারপর যা হয়, জীবন নিজের ছন্দে গড়িয়ে যেত। সেই ছেলেটা বড় হত। বিদেশ চলে যেত পড়াশোনা করতে। তার আর মনেও থাকত না সেই চিঠি বা মেয়েটির মুখ। কিন্তু দেশে ফিরে আসার পর এক শীতের বিকেলে সে আবার অজান্তেই বেলতলার সেই স্কুলের সামনে চলে যেত। পা যেন তাকে চালিয়ে নিয়ে আসত। আর তারপর স্কুলের উল্টোদিকের তিনকোণার বেদীর রেলিং-এ সে অনেক অনেকটা সময় বসে থাকত। চুপচাপ। কোনো কারণ ছাড়াই।
দক্ষিণ কলকাতার এই আলো-আঁধারি রহস্যের ম্যাজিক মোমেন্টগুলোই আমাদের একটা প্রজন্মকে প্রেম চিনিয়ে দিয়েছিল। ম্যাডক্স স্কোয়ারের দুর্গাপুজোর কথা বলছি না। সেটা বছরের একটা বিশেষ সময়ে ঘটত, আর সত্যি বলতে কি আমার বেশ কৃত্রিম এবং ওভারহাইপড লাগত ব্যাপারটা। তার বাইরে সারা বছর ধরে কুয়াশার চাদর গায়ে অথবা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে, রোদে পুড়ে কিংবা যাদবপুরের বাবুর্চির রোলের দোকানের সামনে লম্বা লাইনে যে প্রেম, সেই প্রেমের কোনো তুলনা আমি পৃথিবীর অন্য কোনো শহরে পাইনি। প্যারিসে স্যিয়েন নদীর ধারে দেখেছি প্রেমিকা বই পড়ে শোনাচ্ছে আর প্রেমিক তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। ডাবলিনে টেম্পল বারের রাস্তায় দুই প্রেমিকা পরস্পরকে নরম আদর করছে দেখেছি। কিন্তু স্বার্থপর এবং অন্ধ গোঁয়ারের মত তারপরেও নিজের শহর নিয়ে লড়ে গেছি, দুখানা মাত্র কারণে। ডাবলিন হোক বা প্যারিস, ওদের কোনও দক্ষিণ কলকাতা ছিল না। আর ওদের ভাষাটা বাংলা নয়। সদ্য ক্লাস ইলেভেনের একটা রোগা, নরম দাড়ি ওঠা ছেলেকে যোধপুর পার্কের আর্চিস গ্যালারির সামনে দাঁড়িয়ে এক নরম আকাশী রং-এর ওড়না দেওয়া সালোয়ার কামিজ একবার বলেছিল, “তুমি করে ডাকবি না। বুড়োদের মত শোনায়। তুই করে ডাকিস প্লিজ”। ছেলেটার তখন মনে হয়েছিল পরের সাতদিন ধরে মেয়েটার নরম আংগুল ছুঁয়ে থেকে আলতো করে শুধু ‘তুই, তুই আর তুই’ বলে যায়। মেয়েটা চলে যেতে যেতে পেছন ফিরে তাকিয়ে গালের পাশ থেকে একটা চুলের গোছা আলতো হাতে সরিয়ে বলেছিল, “তুই সিগারেট খেলে সেই গন্ধটা আমার খুব ভাল লাগে জানিস!” সেলিমপুর ঢাকুরিয়ার সাতাত্তর রকম আলোর ছটা ছিটকে এসে তখন ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাদের চোখ।
সেই প্রেম কালের নিয়মেই টেকেনি। কিন্তু তাতে কি ! দক্ষিণ কলকাতার গল্পগুলো, মায়া রহস্য আর ম্যাজিকগুলো তো তাতে মিথ্যে হয়ে যায় নি !
(চলবে। আরো কিছুটা)
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত। - আরও পড়ুনপ্রকৃত উত্তরাধুনিক? - পাপাঙ্গুলআরও পড়ুননমুনা - Sukdeb Chatterjeeআরও পড়ুনশিক্ষা না ভিক্ষা? - Anirban Mআরও পড়ুনহাঁটতে হাঁটতে - দআরও পড়ুনবৈঠকি আড্ডায় ১৭ - হীরেন সিংহরায়
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 সে | 198.155.168.109 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৭:৪৫55024
সে | 198.155.168.109 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৭:৪৫55024- ট্রামের সেকেনক্লাস ১০ পয়সা থেকে বেড়ে ১৫ পয়সা। ঐ সময় থেকেই এক/দুই/তিন পয়সার কয়েন কমে যেতে যেতে বিলুপ্ত হতে শুরু করেছিল। হলদে রঙের ভারি হলদে পদ্মফলওয়ালা কুড়ি পয়সার কয়েন ১৯৭৬ নাগাদ আর সারকুলেশনে ছিল না, বদলে এসে গেছল হালকা অ্যালুমিনিয়ামের কয়েন। সেইম উইথ ভারি দশ পয়সার কয়েন। সেগুলোকেও রিপ্লেস করে ফেলেছিল হালকা দশ পয়সা।
 Atoz | 161.141.85.8 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৭:৪৬55025
Atoz | 161.141.85.8 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৭:৪৬55025- ধরে নিচ্ছি আপনারা মাত্র দুইটিই সন্তান। যদি তা না হয়ে থাকে, তাহলে অন্য সন্তানদের পড়াশোনার খরচও ইনক্লুড করতে হবে। আরো নানারকম বাড়তি খরচও রয়েছে।
 সে | 198.155.168.109 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৭:৪৯55026
সে | 198.155.168.109 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৭:৪৯55026- ৭৭/৭৮/৭৯ সালে গভঃ এইডেড ইস্কুল মাস্টারদের মাসিক স্যালারি ছিল তিনশো থেকে চারশোর ভেতরে। বছর বছর দশ টাকা ইনক্রিমেন্ট হতো। মাঝে মাঝে ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স বা মাগ্যিভাতা মিলত, বা মিলতই না, এরিয়ার পে খাতে জমা থাকত, অনেকমাস পর পর একসঙ্গে পেমেন্ট দিত। টেন পার্সেন্ট অফ বেসিক পে।
 সে | 198.155.168.109 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৭:৫০55027
সে | 198.155.168.109 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৭:৫০55027- প্রাইমারী ইস্কুলের মাস্টারদের মাইনে ছিল আরো কম।
 Atoz | 161.141.85.8 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৭:৫৩55028
Atoz | 161.141.85.8 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৭:৫৩55028- সরকারী কর্মচারীদের একেবারে প্রাথমিক লেভেলেও মনে হয় ঐরকমই রেঞ্জে ছিল মাইনে। কেন্দ্রীয় সরকারীতে হয়তো বেশির দিকে, রাজ্য সরকারীতে কমের দিকে। অর্থাৎ গড়ে ঐ মাঝামাঝি পড়ছে সাড়ে তিনশো টিনশোর কাছে।
 সে | 198.155.168.109 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৭:৫৬55029
সে | 198.155.168.109 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৭:৫৬55029- পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে মাইনে চল্লিশ থেকে ষাট পঁয়ষট্টি, সিনিয়রিটি থাকলে, বিটি পাশ করা থাকলে আরেকটু বেশি, মেরেকেটে বড়জোর একশ টাকা। ১৯৭৭র নাগাদ বামফ্রন্ট শাসন শুরু হয়ে, স্যালারি রিভিশন শুরু হয়। মাইনে একধাপে কিছুটা বাড়ে। সত্তের দশকের শুরুতেই অবশ্য কিছুটা বেড়েছিল, কিংবা তারো আগে যুক্তফ্রন্ট আমলে। বামফ্রন্ট আসবার পরে প্রথম দফায় মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় দফায় ১৯৮১সাল নাগাদ উচ্চমাধ্যমিকও সম্পূর্ণ অবৈতনিক হয়।
 সে | 198.155.168.109 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৭:৫৮55030
সে | 198.155.168.109 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৭:৫৮55030- মাধ্যমিক স্তরে স্কুল টিচারদের মধ্যে মোটামুটি তিনটি ভাগ ছিল শিক্ষকদের বেতনক্রমের। বিএ পাশ, বিএ বিটি, এমেবিটি। বিটি পাশ না করলে ইনক্রিমেন্ট হতো না ঠিকমতো।
 Atoz | 161.141.85.8 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৭:৫৯55031
Atoz | 161.141.85.8 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৭:৫৯55031- অর্থাৎ এই ৩০০ কি ৪০০ আয়ের মানুষদের পক্ষে কারুরই জাস্ট সন্তানদের প্রাইভেট পড়ানোর জন্য ১০০ খরচ করে ফেলা সম্ভব ছিল না। বাড়ীভাড়া দেবর ব্যাপার থাকতে পারে, সারা মাসের বাজারের খরচ, নানারকম বিল পেমেন্ট করার ব্যাপার থাকতে পারে। কাপড়চোপড় কেনার আবশ্যক থাকতে পরে। অসময়ের জন্য কিঞ্চিৎ সঞ্চয়ের ব্যাপার থাকতে পারে।
তবে প্রাইভেট টুইশন ইন থিং হয়ে পড়ে সম্ভবত আরো অনেক পরে, আশির দশকের শেষদিকে। তার আগে এগুলোর চল ছিল বেশ ধনাঢ্য ঘরেই সম্ভবতঃ।
 সে | 198.155.168.109 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৮:০১55032
সে | 198.155.168.109 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৮:০১55032- খুব কম সংখ্যক ইস্কুল টিচারই এমে পাশ ছিলেন। তাই বেতনের স্কেল আলাদা ছিল। অ্যাভারেজ দেখতে গেলে মেজরিটি বিএবিটি, তাই বেতন স্কেলও অ্যাভারেজ।
 Atoz | 161.141.85.8 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৮:০৪55033
Atoz | 161.141.85.8 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৮:০৪55033- অনেকসময় আগেই স্কুলে চাকরি পেয়ে নিয়ে পরে বিটি পাশ করে নিতেন অনেক শিক্ষক/শিক্ষিকা।
 সে | 198.155.168.109 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৮:১৩55034
সে | 198.155.168.109 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৮:১৩55034- প্রাইভেট টিউশন যদিও লিগ্যাল ছিলো না ফুলটাইম শিক্ষকদের জন্য, তবু তাঁরা সংসার চালানোর জন্য টিউশান করতেন অনেকেই। প্রচুর শিক্ষক স্বামীস্ত্রী দুজনেই শিক্ষকতা করতেন, শহর ও মফস্বলের দিকে। সেক্ষেত্রে ডবল ইনকাম এবং টিউশানি থাকলে আরো বেশি। সত্তরের দশকের শেষের দিক থেকে প্রাইভেট টিউশানি শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। বিশেষ করে উঁচু ক্লাসে পড়াতেন যাঁরা, তাঁদের জন্য পরিশ্রমসাধ্য হলেও, বেশ লাভজনক ছিল। অনেক শিক্ষকের চাকরীর বেতনের থেকে টিউশানির বেতনজনিত আয়ের পাল্লা বেশি ভারি থাকত। তবে তাঁরা সংখ্যায় খব বেশি নন। একবার নামডাক হতে শুরু করলে, কোচিং ক্লাস খুলে ফেলতেন, রমরমিয়ে চলত সেই ব্যবসা। আয়করের আওতা থেকেও মুক্ত। তবে, খুব পরিশ্রম করতে হতো। সকালের ব্যাচ, তারপর চান করে দুমুঠো মুখে গুঁজে ইস্কুলে ছোটা, ইস্কুল ছুটির পরে দু তিনটে ব্যাচ, শনি রবি ও ছুটির দিনে এক্স্ট্রা ব্যাচ, নোটস তৈরী করা। ছাত্ররা ঠিক সময় মত পেমেন্ট করছে কিনা সেদিকে নজর রাখা, খামের মধ্যে নোটের সংখ্যা কম দিলো কিনা সেসমস্ত গুণে রাখা।
 সে | 198.155.168.109 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৮:১৪55035
সে | 198.155.168.109 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৮:১৪55035- বিটি পড়বার জন্য পেইড লীভ মিলত ত।
 Atoz | 161.141.85.8 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৮:২৩55036
Atoz | 161.141.85.8 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৮:২৩55036- হুঁ, সমান্তরাল একটা ব্যবসার মতন হয়ে গিয়েছিল স্কুল শিক্ষকদের প্রাইভেট টুইশনি।
তারপরে তো মনে হয় নতুন আইন এনে বন্ধ করতে হয় বাড়াবাড়িটা। সেটা খুব সম্ভবতঃ ২০০১ কি ২০০২ সাল, বা তার পরের বছর। সেই সময়েই বহু স্কুল-শিক্ষক উপর উপর প্রাইভেট পড়ানো ছেড়ে দিতে বাধ্য হন, কিন্তু আসলে আড়ালে সবই চলতে থাকে। জাস্ট মিডলম্যান হিসেবে টিউটোরিয়াল হোমগুলোর তত্ত্বাবধায়ক এসে পড়েন। তিনি স্কুলশিক্ষক নন, তাই তার কোনো আইনগত বাধা নেই।
 সে | 198.155.168.109 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৮:২৭55037
সে | 198.155.168.109 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৮:২৭55037- টিউশানির জগতে ফ্লারিশ করবার জন্য শিক্ষকতার বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ইংরিজি এই চারটে বিষয়ের চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশি। মাধ্যমিক পর্যায়ে। তারপরেই প্রাধান্য পেত লাইফ সায়েন্স। বাদবাকি, ভূগোল, বাংলা, ইতিহাসের শিক্ষকদের ডিম্যান্ড ছিল কেবল বিশেষ কিছু ছাত্রমহলে, যেসব ছাত্র প্রচুর নম্বর পেতে চায়, স্টার পেতে চায়, এমনকি স্ট্যান্ড করবার প্রতিযোগিতায় আছে তাদের মহলে কোনো বিষয়ই অবহেলার নয়। তাছাড়া ঐচ্ছিক বিষয় তো থাকতই। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আবার বিজ্ঞানের শাখায় বিশেষ চাহিদা জয়েন্ট পরীক্ষার্থীদের তৈরী করতে পটু শিক্ষকদের। বাকি রইল আর্টস ও কমার্স শাখা। সেসব লাইনেও আলাদা আলাদা কোচিং এর ব্যবস্থা। তবে কলেজের অধ্যাপকরাও এই ব্যবসায়ে অংশ নিতেন। তা সত্ত্বেও ইস্কুল হোক কি কলেজের শিক্ষক, নামডাক যাঁদের বেশি, তাঁদের কোচিংগুলোতেই ভর্তি হবার ঝোঁক দেখা যেত সিরিয়াস পড়ুয়াদের।
 Atoz | 161.141.85.8 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৯:২৩55038
Atoz | 161.141.85.8 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৯:২৩55038- শুধু আয়করমুক্তই না, এই সমান্তরাল ব্যবসা ছিল পুরোপুরি হিসাব টিসাবের আওতা থেকে মুক্ত। কোনোরকম অডিট ইত্যাদির কোনো সিস্টেমের আওতায় এরা পড়তেন না। কারুর কাছে কোনোরকম আয়ের হিসাব দাখিল করতে হতো না এনাদের। অর্থাৎ সম্পূর্ণ হিসাব-বহির্ভূত অর্থোপার্জন। অথচ এগুলো একজন দু'জনকে পড়ানোর মতন নন-কমার্শিয়াল টাইপ ছোটো ব্যাপার ছিল না, এক একজন ব্যাচে ব্যাচে পড়াতেন। এক এক ব্যাচে পাঁচ ছজন থেকে শুরু করে পনেরো-বিশজন থাকতে পারতো। এক টিউটর প্রায়শই তিন কি চারটি ব্যাচ পড়াতেন গড়পড়তা। নামকরারা আরো অনেক বেশি।
পুরো ব্যাপারটা একধরণের শিল্প-কারখানা টাইপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শুল্ক ও আয়করমুক্ত, হিসাব বহির্ভূত অর্থোপার্জনের কারখানা।
 Atoz | 161.141.85.8 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৯:৩০55039
Atoz | 161.141.85.8 (*) | ২৬ জুন ২০১৬ ০৯:৩০55039- আর একটা ব্যাপার, এই মাধ্যমিক/ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক হয়ে যাবার সময়ের সঙ্গে এই প্রাইভেট টুইশনির সমান্তরাল ব্যবসা রে রে করে ওঠার সময়ের একটা কো-রিলেশন দেখা যাচ্ছে।
 কল্লোল | 125.185.157.239 (*) | ২৭ জুন ২০১৬ ০১:৫৩55040
কল্লোল | 125.185.157.239 (*) | ২৭ জুন ২০১৬ ০১:৫৩55040- দুই ভাইকে পড়িয়ে ১০০টাকাই পেতাম। হ্যাঁ, ওনারা উচ্চবিত্তই ছিলেন। দুই ছেলেই সাউথ পয়েন্টে পড়তো। ভদ্রলোক সম্ভবতঃ সেলসে ছিলেন। ভবানীপুরে ওনাদের পৈত্রিক দোতলা বাড়ি, তার একতলায় ভাড়া। যদুবাজার থেকে গাঁজা পর্কের দিকে যেতে বাঁদিকের ফুটে বেশ কিছু সরু সরু রাস্তা আশুতোষ মুখার্জি রোড আর হরিশ মুখার্জি রোডকে জুড়তো, তার একটা, সম্ভবতঃ চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রিট। প্রতিদিন পড়াতে যে্তে হতো, বিকালে। সাড়ে চারটে/পাঁচটা নাগাদ। রোজ চায়ের সাথে দারুন সন্দেশ জুটতো।
তখন অবশ্য, অতো কোচিং সেন্টার চালু হয়নি। ফলে আমাদের মতো প্রচুর বেকার কোন স্কুলের সাথে যুক্ত না থেকেও প্রচুর টিউশনি পেতো। সেটাই তখন দস্তুর ছিলো। বন্ধুবান্ধব/আত্মীয় ইঃর সুপারিশে এসব পাওয়া যেতো।
 Atoz | 161.141.85.8 (*) | ২৭ জুন ২০১৬ ০১:৫৯55041
Atoz | 161.141.85.8 (*) | ২৭ জুন ২০১৬ ০১:৫৯55041- ধন্যবাদ কল্লোল। আমারও তাই ধারণা ছিল। উচ্চবিত্ত পরিবার।
 Atoz | 161.141.84.108 (*) | ২৭ জুন ২০১৬ ০৪:৩৯55043
Atoz | 161.141.84.108 (*) | ২৭ জুন ২০১৬ ০৪:৩৯55043- ও ব্বাবা, শুধু বড়লোকই না, রীতিমতন এলিট।
ঃ-)
ডিঃ ইয়ার্কি করলাম, কিন্তু গড়পড়তা অন্য বাঙালিদের তুলনায় আপনারা যে অনেকটাই সচ্ছল ছিলেন সেটা আর আলাদা করে বলে দিতে হয় না।
সাতষট্টি আটষট্টি সালে মাসে ১০০ টাকা দিয়ে প্রাইভেট টিউটর রাখা কেবল ধনীদের সম্ভব ছিল।
তখনকার ১০০ টাকা আজকালের প্রায় আট কি ন'হাজার টাকার মতন।
 Ranjan Roy | 192.69.150.53 (*) | ২৭ জুন ২০১৬ ০৪:৫২55042
Ranjan Roy | 192.69.150.53 (*) | ২৭ জুন ২০১৬ ০৪:৫২55042- এতোজ,
যেহেতু আড্ডা হচ্ছে তাই কিচু ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কথা প্রসঙ্গক্রমে এসে যাচ্ছে।
বাবা ছিলেন ভিলাই স্টিল প্ল্যান্টে ইঞ্জিনিয়র। আমরা তিন ভাই কোলকাতায় জয়েন্ট ফ্যামিলির বাড়িতে। বাবার মাসিক বাজেটে কোন বীমা প্রিমিয়াম বা রেকারিং ডিপোজিট ইত্যাদি ছিল না। প্ল্যান্টের ভাল কোয়ার্টারে ভাড়া ও বিজলি সামান্য দরে কাটা হত।
স্টেটসম্যান ও দেশ ছাড়া অন্য কোন বই কেনার খরচ নেই। ইংরেজি বই প্ল্যান্টের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি থেকে, বাংলা বই পাঠাগারের থেকে আনত।
সিনেমার বাজেট বা হোটেলে খাওয়ার বাজেট ছিল না। জামা কাপড় কটন, স্পার্টান। আমাদেরও কড়া বাজেটে রাখত। নাকতলা স্কুলের ফীস নামমাত্র।
বাবার প্রায়োরিটি ছিল খাওয়া/খাওয়ানো-- বিশেষ করে মাছ/মাংস/ডিম/ফল ও বাচ্চাদের পড়াশুনো।
তাই যে কোন টেক্স্ট বা রেফারেন্স বই কিনে দিতে সদাই তৈরি।
ও হ্যাঁ, জয়েন্ট ফ্যামিলিতে বাবার মাসিক কনট্রিবিউশন সবচেয়ে বেশি থাকত।
কোন সেভিংস করতে বিশ্বাস করত না।তাই রিটায়ার করে ভুগেছিল।
আমরা তিন ভাই।
আমি সেই দিনে আর্টসে হায় ম্যাথস নেওয়ায় বাধ্য হয়ে ঘরে টিউটর রাখতে হয়েছিল। কারণ স্কুল আমার জন্যে আলাদা পিরিয়ড অ্যাডজাস্ট করতে রিফিউজ করেছিল।
বাবার মাস চলত ডেফিসিট বাজেটে। ঘরে দামি খাট/পালং এর বদলে সাদামাটা চৌকি ছিল।
 Ranjan Roy | 192.69.166.24 (*) | ২৭ জুন ২০১৬ ০৬:৫৫55044
Ranjan Roy | 192.69.166.24 (*) | ২৭ জুন ২০১৬ ০৬:৫৫55044- ধ্যাৎ!
বছরে একবার মাত্র একটা প্যান্ট আর শার্ট কেনা, হাওয়াই চটি পরে ঘোরা, ট্যাক্সি না চড়া, চৌকিতে শোয়া, ঘরে কোন বিশেষ ফার্নিচার ফ্রিজ ইত্যাদি না থাকা, টিভি বা গাড়ি না থাকা, সিনেমা দেখতে হলে পুরনো খবরের কাগজ বেচে দেওয়া ও ৪১, ৪৫ এবং ৬৫ পয়সার সামনের সিটে বসে দেখা, গার্লফ্রেন্ডদের খাওয়াতে না পারা ( বাদামভাজার পয়সা নির্লজ্জের মত ওদের থেকেই চেয়ে নেওয়া)-- এসব দেখচেন না?ঃ))))।
ও হ্যাঁ, সেইসব দিনে পুরী দার্জিলিং কোথাও না যাওয়া?? এমনকি নবদ্বীপ বা মুর্শিদাবাদও নয়।ঃ(((
আর বীমা না করা? ব্যাংক ব্যালান্স না থাকা?
 Atoz | 161.141.85.8 (*) | ২৭ জুন ২০১৬ ০৭:১১55045
Atoz | 161.141.85.8 (*) | ২৭ জুন ২০১৬ ০৭:১১55045- আমজনতার সিংহভাগ এর দশভাগের একভাগও পেত না সেই আমলে। টালির বাড়িতে থাকতো, বৃষ্টি হলে জল পড়তো, ইলেক্ট্রিসিটি ছিল না, লন্ঠন দিয়ে কাজ চলতো। খাওয়াদাওয়া বলতে কচুঘেচু শাকপাতাই বেশীরভাগ দিন, হয়তো মাঝে মাঝে চুনোমাছ।
গার্লফ্রেন্ড!!! রামো রামো রামকহ! পাড়ার মরাল জ্যেঠামশাইরা লম্বা ছাতার বাড়ি দিয়ে বখাটেপনা ঘুচিয়ে দিত। ঃ-) (এমনকি নব্বইঅয়ের দশকেও আমাদের বেম্ম মফস্বলে পেরেম পীরিত ছিল লুজারস গেম। ছেলেপিলে বখাটে হয়ে গেলে তবে ওসব করে এই সামাজিক নিদান ছিল ঃ-) )
আর বীমা, ব্যাংক ব্যালেন্স???? এইগুলোর নাম ক'জনে শুনেছিল সেই আমলে?
 Ranjan Roy | 192.69.166.24 (*) | ২৭ জুন ২০১৬ ০৭:৪৫55046
Ranjan Roy | 192.69.166.24 (*) | ২৭ জুন ২০১৬ ০৭:৪৫55046- হার মানলাম।ঃ)))
আয়না দেখালেন বটে!
 Atoz | 161.141.85.8 (*) | ২৭ জুন ২০১৬ ০৮:১৯55047
Atoz | 161.141.85.8 (*) | ২৭ জুন ২০১৬ ০৮:১৯55047- আয়নার কি আছে, এ তো স্রেফ অঙ্ক। জাস্ট পাটিগণিত।
ঃ-)
 Abhyu | 34.158.253.128 (*) | ২৯ জুন ২০১৬ ০৩:২৯55048
Abhyu | 34.158.253.128 (*) | ২৯ জুন ২০১৬ ০৩:২৯55048- বড়লোক হওয়াটা তো কোনো অপরাধ নয়, সে নিয়ে হীনমন্যতা থাকারও কোনো দরকার নেই, সে তখনকার দিনেই হোক বা আজকের দিনে :)
 Abhyu | 34.158.253.128 (*) | ২৯ জুন ২০১৬ ০৩:৩৮55049
Abhyu | 34.158.253.128 (*) | ২৯ জুন ২০১৬ ০৩:৩৮55049- সেই এক জমিদারের ছেলে কবে একবার লিখে গেছেন - আমি তোমাদেরই লোক - সেই থেকে সবাই ঐ লাইনটা মেনে চলতে চায়! :)
ডিঃ মসকরা
 h | 212.142.105.221 (*) | ২৯ জুন ২০১৬ ০৩:৪১55050
h | 212.142.105.221 (*) | ২৯ জুন ২০১৬ ০৩:৪১55050- কমরেড এর সোনার কলম হোক, মানে যদি অলরেডি না হয়ে থাকে। কিন্তু বন্ধুত্ত্ব পূর্ণ প্রতিবাদ রেজিস্টার করে গেলাম, এটা করবিন এর লিডারশিপ চ্যালেঞ্জ না;-)
'একলা রোগা ছেলেটি শুধু মাঝে মাঝে....' এই যে বাংলা সাহিত্যে রোগা না হলে লোকের অসহায়তা বোঝানো যায় না, এর তো একটা বিহিত দরকার কমরেড। এই জন্যেই আমার আত্মজীবনী অলিখিত এবং প্রায় অনেকটা সে কারণেই অপ্রকাশিত থেকে গেল। তাছাড়া এটা রেকর্ড করা জরুরী, ছোটো ছোটো মেয়েরা মোটা ছেলেদের ব্যাপারে হেবি হারামি হয়, তারা যাদের ওমা কি সুইট বলে বা যাদের দিকে তাকায়, তাদের জন্য মোটে কান্না কাটি অভিমান চোখ ফোলানো, ঠোঁট কাঁপানো , গেল গেল বেহুলা ভাব কিংব আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে সন্ধের দিকে টুনটুনি মূলক গিলিগিলি সমূহ সব তুলে রাখে হয় রোগাদের জন্যো, নইলে ছাত্র পরিষদের বাইকওয়ালা মস্তান দের জন্য। তখন বিমান দা জোট ও করেনি, আমারো বাইক ছিল না, প্লাস যারা সরু হয় এবং কবিতা নিয়ে মেয়েদের হোস্টেলের সামনে দিয়ে বার বার যাতায়াত করে তাদের বাজার অন্যায় রকম ভালো হওয়ায় আমার এ বলিবর্দ্দসম কাঁধে হায় মাথা রেখেছে শুধুই শান্তিনিকেঅনি দুষ্ট ঘুঘুর বিষ্ঠা। তাই প্রতিবাদের পথ আমি ছাড়িনি, শোভোন ও দেখিয়ে দিয়েছে, বাইক চড়ে ধর্মতলার মোড় কিংবা মিন্টুপার্ক কিংবা সিয়ালদা যেতে গার্সিয়া বর্নাল এর মতো সরু বা হেঁপো না হলেও চলে।
 d | 144.159.168.72 (*) | ২৯ জুন ২০১৬ ০৩:৪৮55051
d | 144.159.168.72 (*) | ২৯ জুন ২০১৬ ০৩:৪৮55051- কিন্তু বীরভুমের মধ্যবয়স্কাদিগের সেইইইই সব ইসেমূলক চাহনীর গল্প কি কমরেড বিস্মৃত হইয়াছেন?
এইঅজন্যই বলি ঢপের একটা খাতা মেনটেইন কর, নাহলে ঢপের কনসিসটেন্সি থাকে না।
 h | 212.142.105.221 (*) | ২৯ জুন ২০১৬ ০৪:০৯55052
h | 212.142.105.221 (*) | ২৯ জুন ২০১৬ ০৪:০৯55052- ঃ-) এটা সত্যি ই আমার মনে নেই ঃ-))) এই পাতা টাকে ঢপের খাতা বলাটা কি শিষ্টতা হবে? আমি তো গত দশ বছরে যা ভেবেছি বা ভাবার ভান করেছি, সব ই এইখানেই অলরেডি আছে আর যা ভাবা উচিত ছিল সেগুলো বাকিদের লেখা পড়লেই পাওয়া যাবে ;-) তাই লোড নিচ্ছি না, কনসিস্টেন্সি ইজ দেয়ার, বিট স্ক্যাটার্ড , জাস্ট লাইক ট্রুথ;-)
 san | 11.39.40.67 (*) | ২৯ জুন ২০১৬ ০৪:৩৪55053
san | 11.39.40.67 (*) | ২৯ জুন ২০১৬ ০৪:৩৪55053- চমৎকার লাগল। উত্তর পূর্ব কলকাতায় বড়ো হয়েও কিরকম রিলেট করতে পারছি। হয়তো ম্যাজিকটা কিছুটা ওই সময়েরও।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... দ, kk, অরিন)
(লিখছেন... প্রতিভা, kk, অরিন)
(লিখছেন... Naresh Jana, সন্তোষ সেন , দ)
(লিখছেন... Somnath Pal, রমিত চট্টোপাধ্যায়, পোল খুলে গেল)
(লিখছেন... Prabhas Sen, Argha Bagchi, সিক্যুয়েল চাই)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... Aranya )
(লিখছেন... অসিতবরণ বিশ্বাস )
(লিখছেন... অসিতবরণ বিশ্বাস , Eman Bhasha, Q)
(লিখছেন... অরিন , JAYANTA GUHABISWAS, প্রাক্তন)
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... অরিন, অরিন, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, ছোট মুখে , সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল, দীপ, দীপ)
(লিখছেন... kk, দীপ, dc)
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : [email protected] ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত