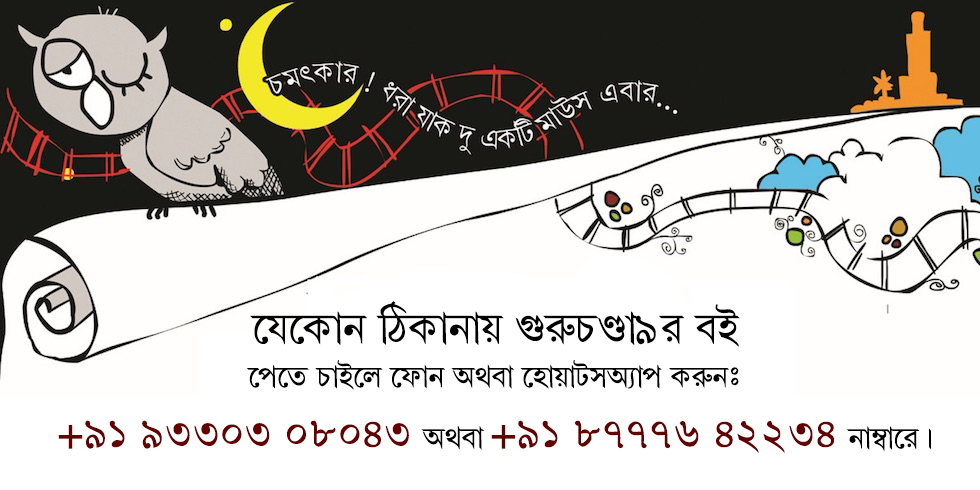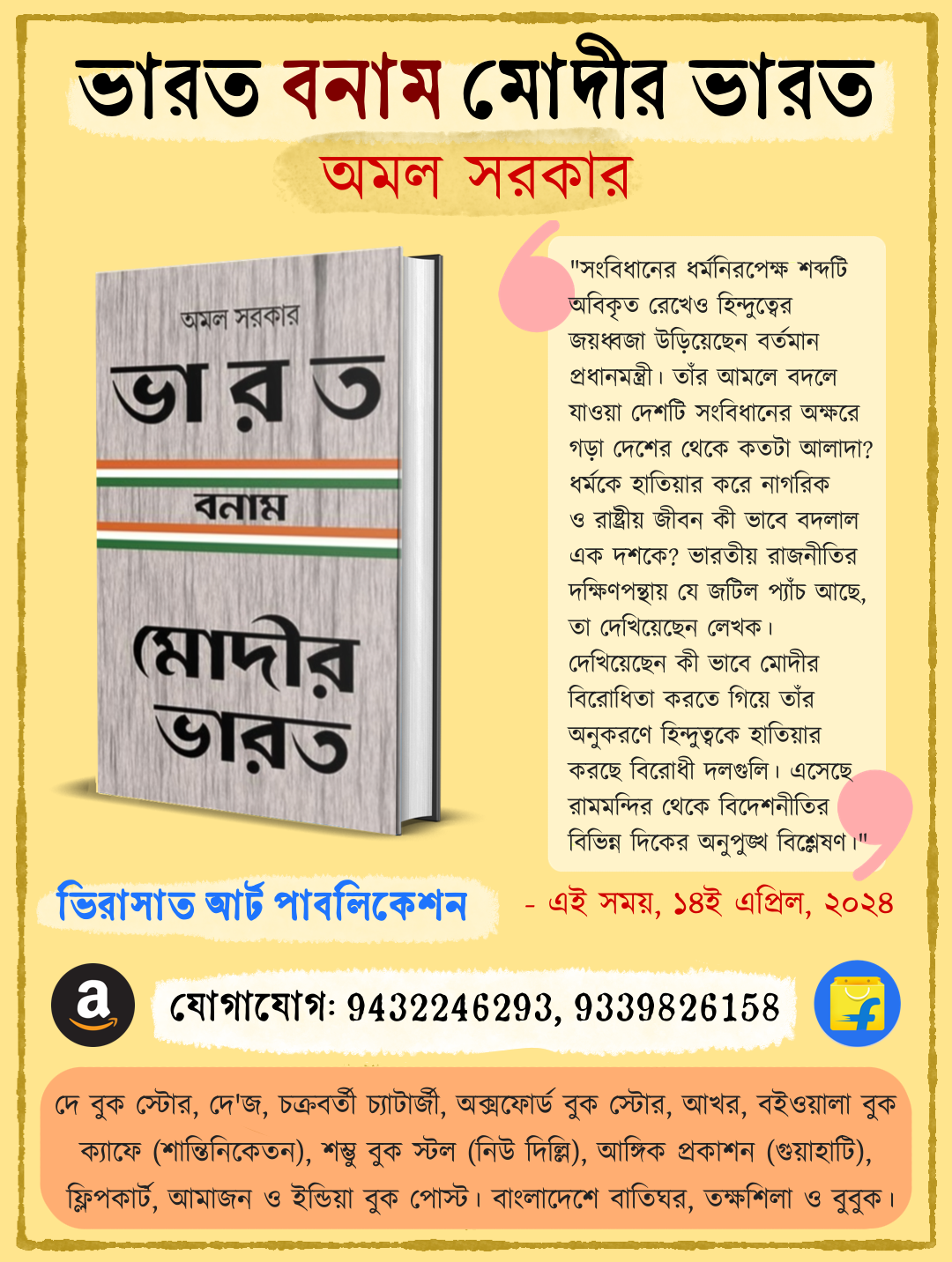- টইপত্তর অন্যান্য

-
"KOLOROBER BISHOY O পদ্ধতি" নিয়ে আলোচনার জন্য আমার বক্তব্য
Chandan Debnath
অন্যান্য | ০৮ নভেম্বর ২০১৪ | ১৩৬৭♦ বার পঠিত
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 Chandan Debnath | 113.17.84.83 | ০৮ নভেম্বর ২০১৪ ০৯:৫৩653105
Chandan Debnath | 113.17.84.83 | ০৮ নভেম্বর ২০১৪ ০৯:৫৩653105- “কলরবের বিষয় ও পদ্ধতি” নিয়ে আলোচনার জন্য আমার ভাবনা
আগামী ৯ নভেম্বর-এর আলোচনার বিষয়বস্তু এখনও আমার কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। ঠিক মতো না বুঝেই কিছু লিখে পাঠাচ্ছি – শরীর ভালো না থাকাতে সরাসরি আলোচনায় হাজির থাকতে পারবো না বলে। মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক কিছু মনে হবে না আমার কথাগুলো। তবে আমি চালু প্রথার একটু বাইরে গিয়ে নিজের ৩০ বছরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই কথাগুলো লিখবো। সেখানে আমার কিছু অভিজ্ঞতার উল্লেখ থাকবে। পয়েন্ট আকারে যতোটা সংক্ষিপ্ত ভাবে সম্ভব আমার বক্তব্য হাজির করছি।
১) আমার প্রথম প্রশ্ন হল, আমাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য কী হবে? আমার অভিমত হল, পুঁজিবাদের অবসান ঘটানো। এমন একটা সমাজ নির্মাণ করা, যেখানে কোনও শ্রেণী বিভাজন থাকবে না। অর্থাৎ একটা শ্রেণীহীন সমাজ। শুধু তাই নয়, অন্যও কোনও রকম সামাজিক বৈষম্যই সেখানে থাকবে না। কারণ পুঁজিবাদ তো শুধু শ্রেণী বিভাজন ভিত্তিক একটা সমাজ নয়, এখানে আরও অনেক রকম সামাজিক বৈষম্য রয়েছে। যেমন লিঙ্গ বৈষম্য সহ আরও অনেক রকম বৈষম্য। পুঁজিবাদের অধীনেই সেই ধরনের বৈষম্যগুলোর অবসান সম্ভব কি না, বা শ্রেণীহীণ সমাজ গঠন করা গেলেই ঐ বৈষম্যগুলো আপনা থেকেই বিলুপ্ত হবে কি না, সেটা অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়।
২) কিন্তু পুঁজিবাদের বিলোপ ঘটাতে গেলে পুঁজিবাদকে তো আগে ভালো করে বুঝতে হবে। আমার মনে হয় কেউই আমরা জোর গলায় বলতে পারবো না, “আমি পুঁজিবাদ খুব ভালো করেই বুঝি”। খুব স্বাভাবিক যে, পুঁজিবাদ সম্পর্কে আমার জ্ঞান অন্য অনেকের মতোই চোখের সামনে যা দেখছি, শুনছি, পত্র-পত্রিকা মিডিয়া ইন্টারনেট থেকে যা জানতে পারছি, তাই থেকে। তবে এগুলোই শুধু পুঁজিবাদ সম্পর্কে আমার জ্ঞানের উৎস নয়। আমার জ্ঞানের অন্যতম উৎস হল কার্ল মার্কসের লেখাপত্র, বিশেষ করে তাঁর “ক্যাপিটাল” গ্রন্থ। এখনও অবধি আমার মনে হয়, পুঁজিবাদ সম্পর্কে এটাই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আরও অনেক রকম বই থাকতে পারে। কিন্তু সেসব পড়ার সুযোগ আমার খুব একটা হয়নি, আমার আর্থিক সমস্যার কারণে। কিছু বই অবশ্য পড়েছি, কিন্তু মার্কসের “ক্যাপিটাল” গ্রন্থটাই এখনও পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। পুঁজিবাদ সম্পর্কে এখানে যে বিশ্লেষণ আছে, সেটা আজকের পুঁজিবাদ সম্পর্কেও প্রযোজ্য বলে আমি মনে করি। মার্কস যে সময়ে ঐ গ্রন্থ রচনা করেন, তার পরে অবশ্য বহু বছর কেটে গেছে। পুঁজিবাদের বেশ কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন (structural change) হয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদের বুনিয়াদি জায়গায় (fundamental basis) কোনও পরিবর্তন হয়নি। সেটা একই আছে। (বুনিয়াদি জায়গা বলতে আমি ঠিক কী বলছি, সেটা এখানে লিখছি না। ওটা আলোচনার সময়েই বলবো।) বুনিয়াদি জায়গাতেই যদি পরিবর্তন হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হবে, একটা গুণগত পরিবর্তন (qualitative change) পরিবর্তন ঘটে গেছে। যদি সেটাই হয়ে থাকে, তাহলে এটাকে আর পুঁজিবাদ না বলে অন্য কিছু বলতে হয়। পুঁজিবাদ না হলে তাহলে কী? যাই হোক, কেউ অবশ্য এই ব্যাপারে আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করতেই পারেন। তাঁরা কোনও ভালো বই সাজেস্ট করলে আমার পড়তে কোনও আপত্তি নেই – যদি আমার আর্থিক সামর্থ্যে কুলায়। এই ব্যাপারে আমার কোনও অযৌক্তিক বায়াস নেই।
আমার মোদ্দা কথা হল, পুঁজিবাদ বলতে আমরা কী বুঝি, সেটা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হোক।
৩) সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ বলতে আমরা কী বুঝি, সেটা নিয়েও খোলামেলা আলোচনার দরকার আছে। এই ব্যাপারেও আমার জ্ঞানের মূল উৎস হল মার্কস- এঙ্গেলস-এর লেখাপত্র। তবে সম্ভব হলে অন্য লেখকদের বইও পরি। যেমন কয়েক মাস আগে রিচার্ড উলফ-এর লেখা “DEMOCRACY AT WORK: A CURE OF CAPITALISM” বইটা পরলাম। কিন্তু কনভিন্সড হতে পারলাম না। আমার আর্থিক সামর্থ্য খুব কম হলেও ৯২৩ টাকা দিয়ে বইটা কিনেছিলাম। কিশলয় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিল, “তুমি এতো দাম দিয়ে বইটা কিনে ফেললে?” কিন্তু কী করবো? প্রচুর পড়াশুনার দরকার আছে তো। তাই আমার মনে হয়, এই পড়াশুনার ব্যাপারে একটা কালেকটিভ এফোর্ট থাকা দরকার আছে। এখানে টাকা পয়সার সমস্যা সবাইকে শেয়ার করা ছাড়াও পড়াশুনার ক্ষেত্রেও একটা জব ডিসট্রিবিউশন-এর দরকার আছে বলে মনে করি। আমার ভীষণ মনে হয়, আমাদের একটা খোলামেলা স্টাডি সার্কেল তৈরি করা দরকার, যেখানে নিয়মিত আলোচনা হবে।
৪) এবার আসি সংগঠনের কথায়। আমি যতোটুকু বুঝি, পুঁজিবাদের মূল বিপক্ষ শক্তি হল শ্রমিকশ্রেণী। কারণ শ্রমিকদের “উদ্বৃত্ত শ্রম” শোষণ করে যে “উদ্বৃত্ত মূল্য” আদায় হয়, সেটাই পুঁজিপতিদের মুনাফার উৎস। কিন্তু শুধু ট্রেড ইউনিয়ন দিয়ে কাজ হবে না। কাজ হবে না বলতে এটাই বলতে চাইছি যে, পুঁজিবাদের বিলোপ ঘটানোর লক্ষ্যে যে সর্বহারা বিপ্লব করতে হবে, ট্রেড ইউনিয়ন সেই বিপ্লবের জন্য উপযুক্ত সংগঠন নয়। যদিও ট্রেড ইউনিয়নেরও একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে। কিন্তু এই লড়াই আত্মরক্ষামূলক (defensive)। ট্রেড ইউনিয়ন হল পুঁজিবাদের ভেতরেই “মানুষের মতো” বেঁচে থাকার জন্য মালিকের সাথে (এবং অনেক ক্ষেত্রে সরকারের সাথেও) দরকষাকষির একটা হাতিয়ারের বেশি কিছু নয়। দরকার শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠন। সেই সংগঠন কিন্তু নেই। এটা আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারবো না। এমনকী ট্রেড ইউনিয়নগুলোও চলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের কথায় নয়, বরং কোনও না কোনও পার্লামেন্টারি পার্টির ইচ্ছা মতো। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আমাদের কাজ কি শুধুই এটা হবে যে, তাদের চলমান ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সপক্ষে কাজ করা? নাকি আমাদের আরও কিছু কাজ আছে? আমার তো মনে হয় আমাদের উচিত, দেশ তথা বিশ্ব রাজনীতির আঙ্গিনায় শ্রমিকশ্রেণীর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র একটা আন্দোলনের ধারা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করা। লক্ষ্য হতে হবে, রাজনীতির আঙ্গিনায় শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্য (hegemony) প্রতিষ্ঠা করা। পার্টির আধিপত্য নয়, শ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। (শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলন বলতে আমি কী বুঝি এবং পার্টির আধিপত্য নয়, শ্রেণীর আধিপত্য বলতে আমি কী বুঝি, সেটা আলোচনার সময়েই বলবো।)
[প্রসঙ্গত বলে রাখি, “শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্য” না বলে “সর্বহারা শ্রেণীর আধিপত্য” বলাই মনে হয় উপযুক্ত হবে। “শ্রমিকশ্রেণী” বললে, এরকম একটা ভুল ধারণা হতে পারে যে, নিয়োগপ্রাপ্ত “মজুরি খাটা শ্রমিক”দের (employed wage workers) কথাই শুধু বলা হচ্ছে। আমি কিন্তু শুধু তাঁদের কথাই বলছি না। যাঁরা একটা কাজ পাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অর্থাৎ যাঁদেরও বেঁচে থাকতে হলে কোনও না কোনও মালিকের গোলামি (wage slavery) করতেই হবে, তাঁদের কথাও বলছি। বলছি তাঁদের কথাও, যাঁরা ছাঁটাই হয়ে গেছেন কিংবা এক সময়ে শ্রমিক ছিলেন কিন্তু এখন “অবসর প্রাপ্ত” (retired)। “সর্বহারা” বলতে আমি সমাজের সেই অংশটাকেই বুঝি, যারা দুই অর্থে “মুক্ত”: ১) উৎপাদনের উপকরণগুলো থেকে যাদের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে (dissociated from the means of production), অর্থাৎ তারা কোনও ভাবেই সামাজিক উৎপাদনের উপকরণগুলোর মালিক নন। সেই অর্থে “মুক্ত”। ২) দাস প্রথার (slave system) মতো বিশেষ কোনও মালিকের কাছে মানুষটি বাঁধা নন। তাঁর এই স্বাধীনতা আছে যে, তিনি চাইলে মালিক বদল করতে পারেন। অর্থাৎ এই অর্থেও “মুক্ত”। কিন্তু এটাও দাসত্ব। মজুরি দাসত্ব (wage slavery)।]
৫) কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের একটা ভূমিকা থাকা দরকার আছে বলে মনে করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হল, কমিউনিস্টদের এখন যা অবস্থা (আমি পার্লামেন্টারি কমিউনিস্টদের কথা বলছি না, বলছি তাঁদের কথা, যাঁরা নিজেদের প্রকৃত কমিউনিস্ট বলে দাবি করেন), তাতে এই কাজ তাদের তাঁদের দিয়ে আদৌ কতোটা হবে, তাই নিয়ে আমার যথেষ্ট সংশয় আছে। আর যদি তাঁরা “শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠন” –এর নামে কিছু একটা গড়ে তুলতেও পারেন, সেটা পার্লামেন্টারি পথেই চলবে বলে আমার মনে হয়। সত্যি বলতে কী, তথাকথিত এই “বিপ্লবী শিবির” বা “তৃতীয় শিবির” ক্রমাগত বিপ্লবী লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হচ্ছে বলেই আমার মনে হচ্ছে। (আলোচনায় সরাসরি হাজির থেকেই এই সম্পর্কে আমার যুক্তিগুলো আমি তুলে ধরতে চাই। এখানে সেই যুক্তি হাজির করছি না।)
এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, “তৃতীয় শিবির”-এর ওপরে যদি আমার কোনও রকম আস্থাই না থেকে, তাহলে কাদের আমি প্রকৃত কমিউনিস্ট বলছি, যাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেন? ভুল বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্য বলে রাখতে চাই, “তৃতীয় শিবির” নিয়ে আমার যথেষ্ট সংশয় থাকলেও, ঐ শিবিরের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত মানুষজনকে আমি মোটেই “খরচের খাতায়” ফেলতে চাইছি না। কারণ আমি খুব ভালো করেই জানি যে, ওখানে অনেক সিরিয়াস কমরেড আছেন, যাঁদের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে মহৎ। কিন্তু এটাও আবার সত্যি যে, ১৯৭২-এ CPI (ML) আন্দোলন ভেঙ্গে যাওয়ার পরে বিগত চল্লিশোর্ধ্ব বছরে পুরনো ভুলের নির্মোহ পর্যালোচনা করে নতুন করে বিপ্লবী ঐক্য প্রতিষ্ঠা হওয়া তো দূরের কথা, গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অনৈক্য, পারস্পরিক রেষারেষি, প্রতিযোগিতা, এমমকী একে অন্যকে ল্যাং মারার দিকেই অবস্থা ক্রমাগত এগিয়েছে। এবং অদূর ভবিষ্যতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার (অবশ্যই সুনির্দিষ্ট বিপ্লবী নীতির ভিত্তিতে) কোনও সম্ভাবনা আছে বলেও মনে হয় না। বস্তুত, সমস্ত দেশেই মনে হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলোর মোটামুটি এরকমই অবস্থা।
[প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমি যে গোষ্ঠীর সাথে দীর্ঘ দিন যুক্ত ছিলাম, সেই গোষ্ঠী একই পার্টিতে সবার ঐক্যবদ্ধ হওয়ার লক্ষ্যে বেশ কয়েক বছর আগে একটা প্রস্তাব পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেছিল। তখন আমি ঐ গোষ্ঠীতেই ছিলাম। প্রস্তাবটা ছিল এরকমঃ ন্যূনতম জায়গায় ঐক্যের ভিত্তিতেই সবাই একটা পার্টিতে আসুক। কাউকেই নিজেদের আলাদা গোষ্ঠী অস্তিত্ব বিলোপ করতে হবে না। একই পার্টির ভেতরে প্রকাশ্যেই (গোপনে নয়) গোষ্ঠীগুলো থাক, কিন্তু কাজ চলুক ন্যূনতম জায়গায় ঐক্যের ভিত্তিতেই। আর একই পার্টির ভেতরে আলাপ আলোচনা চলুক ভিন্ন মতগুলোকে ধরে। আমার তখন মনে হয়েছিল এই প্রস্তাবে ভালো সারা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু হতাশ হয়েছি। কোনও সারাই পাওয়া যায়নি!]
গোষ্ঠীগুলোর কেন এই অবস্থা, তার গভীর বিশ্লেষণ হওয়ার দরকার আছে বলে মনে করি। এটাও আমাদের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। আমাদেরকেই এই বিশ্লেষণ করতে হবে, এবং প্রকাশ্যে সেই বিশ্লেষণ হাজির করতে হবে “তৃতীয় শিবির” সহ কোনও গোষ্ঠীভুক্ত নন, অথচ বিপ্লবী লক্ষ্যে কাজ করেতে এখনও আগ্রহী, তাঁদের সবার কাছ সেটা নিয়ে যেতে হবে। সেই লক্ষ্যে আমাদের একটা পলেমিকাল ম্যাগাজিন চালু করা দরকার বলে মনে করি। পলেমিকাল ম্যাগাজিন বলতে আমি ঠিক কেমন ম্যাগাজিনের কথা বলছি, সেটা আলোচনায় হাজির থেকেই বলবো। সত্যি বলতে কী, কয়েক বছর আগে এরকম একটা ম্যাগাজিন আমরা কয়েকজন মিলে শুরু করেছিলাম (বাংলায়)। প্রথম দিকে বেশ ভালোই চলছিল ম্যাগাজিনটা। ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে দুটো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে দুটো সেমিনারও করা হয়েছিল। ভালোই হয়েছিল সেমিনার দুটো। কিন্তু লেখকের অভাবে ম্যাগাজিন বেশি দিন আর চালানো গেল না। বন্ধই হয়ে গেল। ম্যাগাজিনের নাম ছিল “আলোড়ন”। পরে শুধু অনলাইন আকারে ম্যাগাজিনটা আবার নতুন করে চালু করা যায় কিনা, এই নিয়ে কিশলয়ের সাথে কথা বলি। কিশলয় বেশ ইন্টারেস্ট দেখায়। তারপর আমি, কিশলয় ও সুতনয়ার উদ্যোগে অনলাইন ম্যাগাজিন চালু হয়। কিন্তু সেটাও চালাতে পারলাম না মূলত লেখক ও অনুবাদকের অভাবে।
আপাতত আর বেশি কিছু লিখছি না। যদিও আরও অনেক কথা এবং নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলা প্রয়োজন ছিল বলে মনে করি। কিন্তু সময়ের অভাবে এবং নিজের শারীরিক অসুস্থতার কারণে সেটা সম্ভব হল না। আর আমার আশা তো এটাই যে, ৯ তারিখের আলোচনায় আমি হাজির থাকতে না পারলেও আলোচনাটা চলবে। তখন অনেক কথা বলবো এবং অন্যদের কথাও খুব ভালো করে শুনে বোঝার চেষ্টা করবো। আমার এখন জোর নিজেদের ভেতরে একেবারে খোলামেলা আলোচনার ওপরে। এবং আলোচনা অনেক দিন ধরে চালাতে হবে। (এটাকেই আমি স্টাডি সার্কেল বলছি। গোষ্ঠী সংগঠনগুলোর ভেতরে যেমন প্রথাগত স্টাডি সার্কেল চলে, সেরকম স্টাডি সার্কেল-এর কথা বলছি না।) ধারাবাহিক বেশ লম্বা সময় ধরে আলোচনা চালানোর ভেতর দিয়েই আমাদের সংগঠন নির্মাণের দিকে এগোতে হবে। এক্ষুনি কোনও রকমে “নতুন আর একটা সংগঠন” বানানোর তাগিদ আমাদের পরিহার করে চলতে হবে। ►
বিপ্লবী অভিনন্দন সহ
চন্দন দেবনাথ
_______________________________________________________________________
 তাপস | 126.202.194.234 | ০৮ নভেম্বর ২০১৪ ১৩:৩৭653106
তাপস | 126.202.194.234 | ০৮ নভেম্বর ২০১৪ ১৩:৩৭653106- আমার দু পয়সা
-----------------------------------------------
নন্দীর সঙ্গে আমার যেটুকু কথা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে লিখছি । নন্দী ও আমি সব বিষয়ে একমত না-ও হতে পারি । তবে একটা দুটো জায়গা ছিল, সহমতের । আমি আমার জায়গাটুকুই লিখি -
আরেকটা সংগঠন বা পার্টি বানানোর লক্ষ্যে ৯ তারিখের বৈঠক হচ্ছে না । আমি নিজে আরেকটা সংগঠন বা পার্টি বানাতে একটুও আগ্রহী নই । দুটো জিনিস একটু বুঝে নেওয়ার দরকার থেকে আলোচনা করার দরকার বোধ হয়েছিল । আলোচনা ও বৈঠকের উত্সাহ ও আগ্রহ নন্দীরই - আমি ন্যূনতম ধুনোও দিই নি । কিন্তু প্রয়োজন নিয়ে সন্দেহ প্রকাশও করিনি বা করছি না । তো যা বলছিলাম, দুটো জিনিস বুঝে নেওয়ার দরকার থেকে আলোচনা শুরু করার দরকার । দুটো খুব বেসিক জিনিস ।
১। হোয়াট ইজ (নট) টু বি ডান ।
২। হোয়াট ইজ (ইয়েট) টু বি ডান ।
ওই 'নট টু বি ডান' - এর মধ্যে পার্টি/গণসংগঠন না- করার ভাবনাই ছিল । অন্তত আমার বোধ অনুসারে । এই না-করার পর তাহলে আর কী করণীয় - সেইটা নিয়ে কথাবার্তা চলতে পারে । এবং দীর্ঘ সময় ধরেই চলবে হয়ত, যদি না ধৈর্যের অবসান ঘটে । বিপ্লবের ব্যাপারে একটুখুনি বলার, ও নিয়ে ভাবছি না । পুঁজিবাদের অবসান নিয়ে দুটো শব্দ - ইম্পসিবল প্রজেক্ট ।
 pinaki | 90.254.154.99 | ০৮ নভেম্বর ২০১৪ ১৮:৩১653107
pinaki | 90.254.154.99 | ০৮ নভেম্বর ২০১৪ ১৮:৩১653107- ইয়ে সব ক্যা হো রহা হ্যয়? ইয়ে নন্দী কউন হ্যয়?
 তাপস | 126.202.192.8 | ০৮ নভেম্বর ২০১৪ ২১:০১653108
তাপস | 126.202.192.8 | ০৮ নভেম্বর ২০১৪ ২১:০১653108- অভিজিত নন্দী । ও ফেবুতে একটা পেজ খুলেছিল । মেল চালু করেছিল তার আগে । পিনাকী মেলচেনে ছিল না?
 অভিজিৎ নন্দী | 127.194.230.173 | ০৮ নভেম্বর ২০১৪ ২৩:২৫653109
অভিজিৎ নন্দী | 127.194.230.173 | ০৮ নভেম্বর ২০১৪ ২৩:২৫653109- (প্রাথমিক আলোচনাটা এখান থেকে শুরু হয়েছিল)
বিকল্প রাজনৈতিক চেতনা – বিকল্প রাজনৈতিক কর্মসূচী? সে তৃতীয় ধারার,না চতূর্থ,নাকি পঞ্চম ধারার তা বলতে পারব না! বারবার যেটা ঘটতে দেখেছি তা হল,কোন একটা আঘাত বা হিংস্রতা নেমে আসে,তার প্রতিবাদ করা হয় – কখনও মিনমিনে গলায়,আবার কখনও বা শত-সহস্র মানুষের কলরবে। কিন্তু এই যে,ক্রমাগত: ঘটনার পেছনে ছোটা,এর কোনও অন্যথা হতে পারে না? অন্যদিকে,দেখেছি পার্টি রাজনীতি,যার নিজস্ব ধারা থাকে,কিন্তু সে অন্য ধারাকে জায়গা দিতে পারে না,না পেরে কখনও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে,কখনও বা অন্য মতের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে হিংস্রতাই হয়ে পড়ে তার সম্বল।
কিন্তু যাদবপুরের ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা ‘হোককলরব’ আজকের সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক সংস্কৃতির নিস্তব্ধতায় কিছুটা হলেও ভাষা দিয়েছে,হয়ে উঠেছে আজকের দিনের গ্রহণযোগ্য স্লোগান,তাকেও তো অস্বীকার করতে পারি না। প্রত্যেকবারের মত একেও যদি আর কিছুদিনের মধ্যে ‘স্বাভাবিক’ মৃত্যুবরণ করতে দিই,তা কি আমাদের সামাজিক,রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক দায়িত্বহীনতা হয়ে যাবে না?
জানি,কোনও রাজনৈতিক পথপ্রদর্শন করা এই মূহুর্তে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলে ফেলা – ‘এটাই আমাদের দর্শন’। সে তৈরী হোক চলার পথ ধরে, অনেকের হাত ধরে। তা হোক গতিশীল।
শুধুমাত্র সামনের দিকে এগুনো মানে পেছনে কিছু লোককে রাখা। মানতে পারি না আধুনিকতার সব কিছুই সুন্দর। আবার উন্নয়নের হিংস্রতাও চোখ এড়িয়ে যায় না। তাই প্রগতিশীলতা,আধুনিকতা বা উন্নয়ন এসব কথাগুলোও দ্বন্দ্ববিহীনভাবে উচ্চারণ করতে পারি না নিজেদের ভাবনা বা চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে।
তাই কথা বলতে চাই,বুঝতে চাই – কি করতে পারি? তাই,কথা বলতে চাই তাঁদের সাথে,যাঁরা পার্টি রাজনীতির একমুখী দর্শন বা মতামতের প্রাধান্যে নিজেদের নিজস্ব বৈচিত্রকে খুইয়ে ফেলেননি,যাঁরা চান এই রাজনৈতিক সাংস্কৃতির নৈ:শব্দের এবং হিংস্রতার অবসান,যাঁরা চান হোক-কলরব।
পার্টি গড়তে চাইছি না। কোনও পার্টির বিরোধিতা-মূলক রাজনীতিও নয়। বুঝতে চাইছি,এমন কোন রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা সম্ভব কিনা, যে রাজনীতিকে সাধারণ মানুষ ভয় পাবে না এবং ঘৃণা করবে না। সংসদীয় রাজনীতির বাইরেও যে সব রাজনীতির রেশ ওঠে মাঝে মাঝে,কোন কোন মুহূর্তে তাতে মানুষের ঢল নামে স্বতস্ফুর্তভাবে,বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে,আমাদের রাজনীতির ধরণকে একই রকম রেখে, আমরা কি বারংবার অপেক্ষা করে যাব,কবে আবার বিশেষ পরিস্থিতির উদয়ে সাধারণ মানুষের জমায়েত বাড়বে? নাকি ভাববো,আমাদের রাজনীতির ধরণটাকেই পালটানোর কথা,রাজনীতির ভাষা ও স্লোগানগুলো পালটানোর কথা,যাতে সাধারণ মানুষের কাছে তা সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য হয়। অবশ্যই এ ক্ষেত্রে populist politics এর সমস্যাগুলোও মাথায় রাখতে হবে।
প্রশ্নগুলো সহজ,কিন্তু উত্তর জানা আছে কি?
_________________________
ভিন্ন ভিন্ন মত শুনছি ও সমৃদ্ধ হচ্ছি। প্রত্যেকেই তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির যায়গা থেকে বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরূত্ব দিয়েই ভেবেছেন এবং লিখেছেন।
দেখছি,দল তৈরীর সমস্যাগুলো আমাদের ভাবাচ্ছে,কারণ আমরা বারংবার দেখেছি দল থেকে দলতন্ত্র তৈরী হয়,দল মানুষের উপরে উঠে যায় প্রায়শই। দেখেছি দলের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজের গণতান্ত্রিকরণ পদ্ধতির অকাল মৃত্যু।
আবার, রাজা তখনই রাজা,যখন প্রজা তাকে ও তার ব্যবস্থাপনাকে দ্বিধাহীন মান্যতা দেয়। মানুষের ভাবনা ও দর্শনের ভিত্তির উপরেই গড়ে ওঠে রাজার সাম্রাজ্য। তাই,উন্নত সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম হতে গেলে,রাজার ব্যবস্থাপনার প্রতিবাদ করলেই পুরো কাজটা শেষ হয়ে যায় না। বাকি থেকে যায় মানুষের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ভাবনা ও দর্শনগুলোর পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্গঠন। আর সেটাও,বৃহত্তর অর্থে রাজনীতির বাইরের পরিসর তো নয়ই,বরং মনে হয় একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।
_________________________
____________________________
তাই,রাজার শাসন ও ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর যেমন প্রয়োজন পড়ে (সে রাজা যেই হোক না কেন,তার রাজনীতি অন্য রাজার রাজনীতির সাথে নিজেকে যতই আলাদা করুক না কেন),অন্যদিকে নিরন্তর বিশ্লেষন ও ভাঙ্গা-গড়ার প্রয়োজন আছে প্রজার নিজের রাজনৈতিক,সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দর্শন ও কার্যকলাপের।
বৃহত্তর অর্থে যারা রাজনৈতিক,তাদের কেউ প্রথমটিতে জোর দেন,আবার কেউবা বেশি ব্যস্ত থাকেন দ্বিতীয়টি নিয়ে। আবার,কেউ কেউ স্বতস্ফুর্ততার উপরেই বেশি নির্ভর করে থাকেন। অপেক্ষা করে থাকেন কখন সমাজে এই সব বিষয় নিয়ে কার্যকলাপের ঢল নামবে। শুধু খেয়াল করেন না যে,এই ‘স্বতস্ফুর্ত’ আন্দোলনের পেছনেও ছিল অনেকের টুকরো টুকরো ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক পরিকল্পনা ও রূপায়ণ।
প্রশ্ন হল,এই স্বতস্ফুর্ততার মায়া কাটিয়ে এবং শুধুমাত্র বিরোধিতার অভ্যেস কাটিয়ে,আমরা কি পুরো কাজটাতে অংশগ্রহণ করতে পারি নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে?
_____________________________
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Shamik Roychowdhury, upal mukhopadhyay, যোষিতা)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, Subhas, b)
(লিখছেন... যোষিতা, Muhammad Sadequzzaman Sharif, যোষিতা)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... অরিন, অরিন, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, ছোট মুখে , সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... কই কই, উঃ বড্ড লেগেছে , কই কই)
(লিখছেন... kk, দীপ, dc)
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : [email protected] ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত