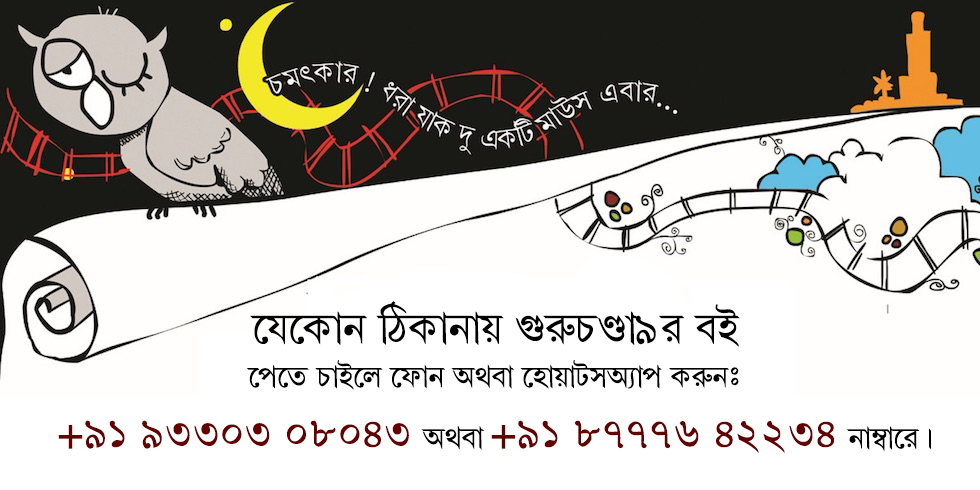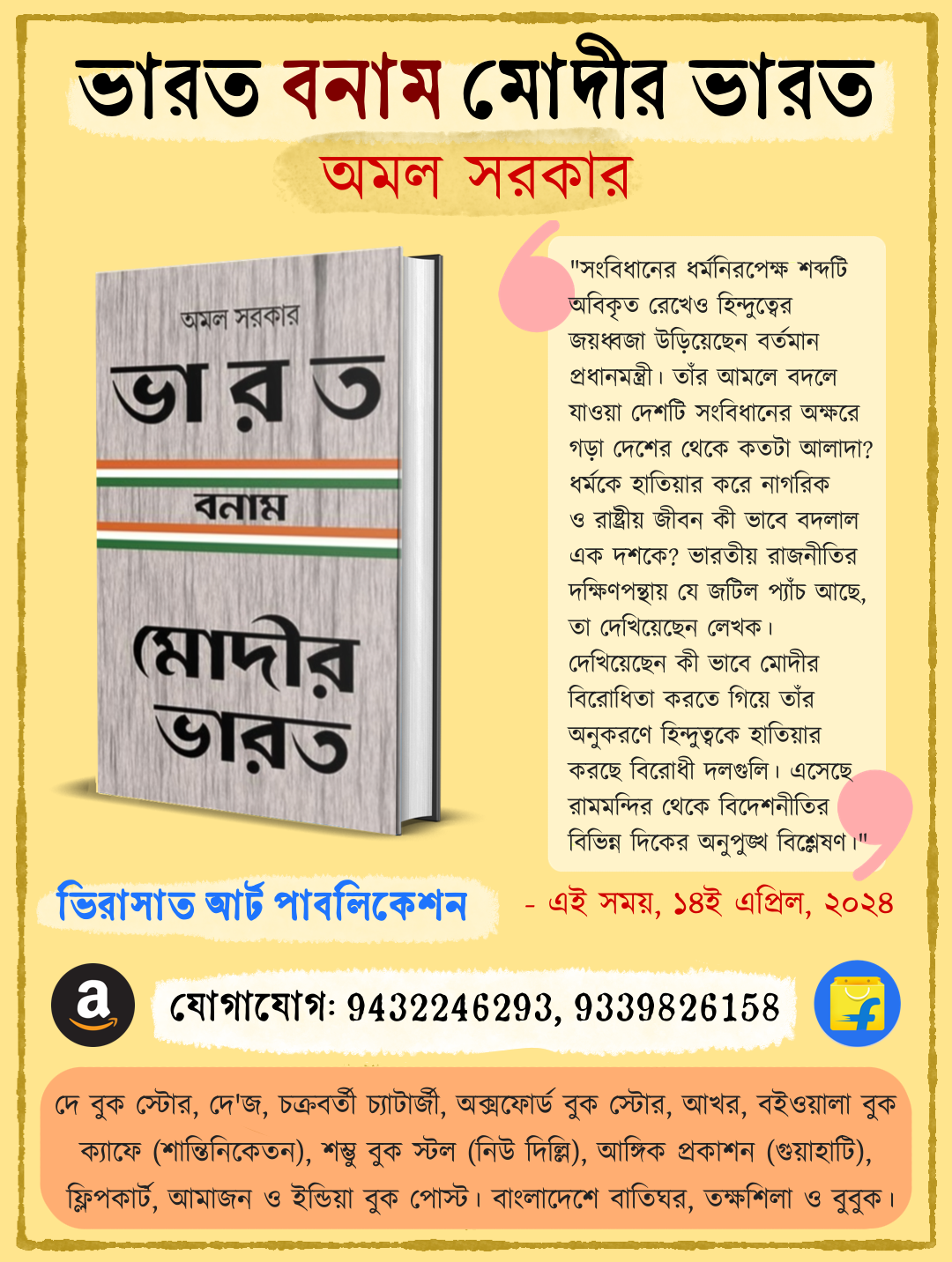- বুলবুলভাজা আলোচনা বিবিধ

-
চিহ্নিতকরণ অথবা চিত্রগুপ্ত প্রকল্পঃ অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে
সৌরভ ভট্টাচার্য লেখকের গ্রাহক হোন
আলোচনা | বিবিধ | ২৩ আগস্ট ২০০৯ | ৬৭২♦ বার পঠিত - ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্রের কূটকচালি পেরিয়ে যদি সহজ চোখে গত শতাব্দীর দিকে তাকানো যায়, তাহলে উন্নত এবং অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যে একটা বড় ফারাক দেখা যাবে। প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়াই বলুন আর আমেরিকা-ইংল্যান্ডই বলুন, অর্থনীতির পরিসরে রাষ্ট্রের ভূমিকার প্রভূত পার্থক্য সঙ্কেÄও প্রায় সব উন্নত দেশেই সামাজিক বা ভৌগোলিক পরিসরে রাষ্ট্রের উপস্থিতি সর্বব্যাপী এবং সুদৃঢ়। সোজা কথায়, উন্নত দেশের সরকারের হাত অনেক লম্বা - পরিষেবার বরাভয় আর প্রশাসনের খড়্গহস্ত দুটোই।আমেরিকা-রাশিয়াতে গভর্নমেন্টের খাতায় সক্কলের নাম আছে। আমাদের দেশেও কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি একটি প্রকল্প নিয়েছেন প্রত্যেক নাগরিককে (এবং বাসরত অনাগরিককে) আলাদা করে চেনবার, প্রত্যেককে একটি জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়ার। সরকারি কম্পিউটারে ধরা থাকবে প্রত্যেকের নাম, ধাম, বৃত্তি, মায় আঙুলের ছাপ পর্যন্ত। প্রকল্পের আনুমানিক খরচ চল্লিশ হাজার কোটি। গত মাসে এই প্রকল্পের কর্ণধার নিযুক্ত হলেন ইনফোসিসের প্রাক্তন সিইও নন্দন নিলেকানি। সার্থক নির্বাচন, নি:সন্দেহ। এই নিয়োগের সাথে সাথে বিষয়টি সংবাদের শিরোনামে এসেছে, এবং স্বাভাবিকভাবেই, প্রতিবাদের ঝড় না উঠুক, বিতর্কের হাওয়া বইতে শুরু করেছে।
প্রশ্নটি স্বাভাবিক - কী এমন রাজকার্য সাধিত হবে যার জন্য রাজকোষ এতখানি খালি করে দেওয়া? যদিবা উদ্দেশ্য মহৎ হয়, পুরো বিষয়্টা কিঞ্চিৎ তুঘলকী শোনাচ্ছে না? সরকার বাহাদুরের উত্তর: জাতীয় নিরাপত্তার জন্য এই চিহ্নিতকরণ অত্যাবশ্যক। বস্তাপচা অজুহাত। অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সরকারের চিত্রগুপ্তের খাতা খোলা কি এতটাই জরুরী? সমষ্টির নিরাপত্তার দায় কি রাষ্ট্রকে দেয়, ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণের অধিকার? আমাদের মত দেশে আর এক ভয়ের কথা - সরকারের পক্ষে কি এই তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা আদৌ সম্ভব? প্রশ্নগুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তবু, এই প্রকল্পের মূল্যায়নে অন্য একটি বাস্তব, ব্যবহারিক বিষয় সমান গুরুত্ব রাখে। এই যোজনা যদি সঠিকভাবে রূপায়িত হয়, তাহলে দেশের অর্থনৈতিক মানচিত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আসতে পারে। অথচ বাদী বা বিবাদী কোন পক্ষকেই সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করতে শোনা যাচ্ছে না। নন্দ্ন নিলেকানির এক সাক্ষাৎকারে "ফিনানশিয়াল ইনক্লুশান"-এর মৃদু ইঙ্গিত ছাড়া সরকারপক্ষ এবিষয়ে যা বলেছেন তার সব্টাই নিরাপত্তা নিয়ে। অবশ্যই, জাতীয় নিরাপত্তার পাঁচন তেতো হলেও জনতা গিলতে বাধ্য। কিন্তু প্রকল্প নিয়ে এত ঘাঁটাঘাঁটির পরেও সরকার পরিচয়পত্র-ব্যবস্থার শক্তি বা সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত নন একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই প্রবন্ধের একটাই উদ্দেশ্য, বিতর্কে একটি অর্থনৈতিক মাত্রা যোগ করা।
"উন্মুক্ত অর্থনীতি" বা ফ্রি মার্কেট বলতে যদি বোঝায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ, নি:শর্ত মুক্তি, সেই নিরিখে কিন্তু আমাদের দেশের অর্থনীতির দুই-তৃতীয়াংশ চূড়ান্তভাবে মুক্ত। যেহেতু সরকারি নথিতে এই বিরাট অংশের কোন অস্তিত্ব নেই, সরকারি বিধিনিষেধও এর উপর খাটে না। এই নথি-বহির্ভূত (ইনফরমাল) অর্থনীতির পরিসরে কারা আছেন? প্রায় সমস্ত কৃষিজীবি (ক্ষেতমজুর এবং জোতদার সমেত), সমস্ত দিনমজুর, প্রায় সমস্ত ছোট দোকানদার, ক্ষুদ্রশিল্পে নিযুক্ত প্রায় সকলেই, ছোট ছোট কারখানার মালিক এবং শ্রমিক, বাড়ির পরিচারক/পরিচারিকা, অধিকাংশ প্রমোটার, টিউশনি করা যুবকযুবতী - অর্থাৎ কিনা কর্মরত মানুষের সিংহভাগ (ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের হিসেবে ১৯৯০ সালে সংখ্যাটা ছিল ৯০%)। এই বিশাল কর্মকান্ডে সরকারের কোনো বিধিনিষেধ চলে না, কোন ন্যূ¤নতম মজুরি নেই, শ্রমিক বা ছোট ব্যবসায়ী কোন সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই, অতএব যেটা চলে সেটা মাৎস্যন্যায়। উপরন্তু, সরকার এই ইনফরমাল অর্থনীতি থেকে এক পয়সা বিক্রয়শুল্ক পান না, এবং আয়্করের ভাঁড়েও মা ভবানী বিরাজমানা। অবশ্যই নথিবহির্ভূত উপার্জন করেন সরকারি কর্মচারীরা, কিন্তু সে পয়্সা জনকল্যাণে খরচ হয় না, জনগণও সে পয়সার হিসেব দাবি করতে পারেন না।
সরকারি খাতায় সকলের নাম উঠলে এই "মুক্তাঞ্চল" সরকারের আইনের আওতায় আসবে। মাৎস্যন্যায়ের পরিবর্তে রামরাজ্য কায়েম না হলেও শোষণের মাত্রা খানিকটা কমবে, মানুষ একটা ন্যূনতম সুরক্ষা পাবে একথা নি:সন্দেহ। সরকারি পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছাতে সুবিধা হবে - দই-মারা-নেপোদের দৌরাত্ম্য কমবে। আরো লাভ, এই বিশাল কর্মকান্ডের অর্ধেকও যদি স্থায়ীভাবে করের আওতায় আসে, তাহলে রাজকোষের যা স্ফীতি হবে সে তুলনায় প্রকল্পের চল্লিশ হাজার কোটি নিতান্ত খোলামকুচি। অতএব, চিত্রগুপ্তের খাতা বানানোকে নেহাত তুঘলকী খেয়াল বলাটা সমীচীন হবে না। কিন্তু এই যোজনার সম্পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে শুধু প্রত্যক্ষ ফলের কথাই ভাবলে চলবে না, এর পরোক্ষ প্রভাবও সুদূরপ্রসারী।
একবার ভাবুন ফর্মাল এবং ইনফর্মাল পরিসরের সম্পর্কের কথা। ধরুন, একজন পানবিড়ির দোকানদার পেপসি কিংবা এভারেডি মজুত করতে চান। তাঁকে কেউ ধারে মাল দেবে না, অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে অগ্রিম দিয়ে কিনতে হয়। ফলে রিলায়েন্স বা স্পেন্সারের সুপারমার্কেটের থেকে পণ্যমূল্য অনুপাতে তাঁর ব্যবসায় পুঁজি বেশি প্রয়োজন হয়। এর কারণ কিন্তু শুধু ছোটবড়র পার্থক্য নয়। পেপসি বা এভারেডির কাছে "গোত্রহীন" দোকানদারের সঙ্গে চুক্তিতে ঝুঁকি বেশি, তাই তারা দরও হাঁকে বেশি। সরকারের খাতায় নাম থাকলে এই ঝুঁকি কম, নথিভুক্ত ব্যবসয়ীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। ছোট হলেও নথিভুক্ত দোকানদারের পক্ষে ব্যবসা তাই অপেক্ষাকৃত লাভজনক। তার কারণ, সরকারি নজরদারি এক নিশ্চয়তা, একধরণের আস্থার জন্ম দেয়। এর অভাবে ইনফর্মাল পরিসরে ঝুঁকির পরিমাণ অনেক বেশি। যদি দুজন ব্যবসায়ী ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত না হন, তাহলে লেনদেন অনেক সময় হওয়াই মুশকিল। এর ফলে ইনফর্মাল পরিসরে ছোট ব্যবসায়ী ছোটই থেকে যান। সরকারি পরিচয়পত্র এই ঝুঁকির পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে - তাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর প্রভূত মঙ্গল।
এবার তাকানো যাক একজন প্রান্তিক কৃষকের দিকে। জমি কিনতে, বীজ কিনতে, সার কিনতে, অথবা অন্য কোন ব্যবসা শুরু করতে তাঁরও পুঁজির প্রয়োজন হয়। কিন্তু জামানত (কোল্যাটেরাল) দেওয়ার সঙ্গতি না থাকলে ব্যাঙ্ক তাঁকে ফিরিয়ে দেবে।(এঁর দিকে তাকিয়েই গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র্র ঋণ বা মাইক্রোফিনান্স আন্দোলন - কিন্তু তার সাফল্যও সীমিত)। এই অবস্থায় তাঁর অমোঘ নিয়তি মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে ধার নেওয়া। শোষণ এবং অত্যাচারের পরবর্তী কাহিনী সুবিদিত - কিন্তু জাতীয় পরিচয়্পত্র এই গফুর মিঞা কিংবা রামা কৈবর্ত্তকে এই নিয়তি থেকে খানিকটা রক্ষা করতে পারে ব্যাঙ্কের বন্ধ দরজা খুলে দিয়ে।
ব্যাঙ্ক কেন জামানত চায়? কারণ প্রতিটি ঋণ ব্যাঙ্কের কাছে একটি ঝুঁকি (আবার সেই!) - অনাদায়ে ব্যাঙ্ককে সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। (প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, নব্বই দশকের মাঝামাঝি সরকারি ব্যাঙ্কগুলির মোট ঋণের এক-চতুর্থাংশ অনাদায়ী ছিল - স্বভাবত:ই আজ ব্যাঙ্করা এই ব্যপারে বেশ কড়া)। ব্যাঙ্কের প্রয়োজন ঋণ ফেরত পাওয়ার একটা নিশ্চয়তা - এবং সরকারি পরিচয়পত্র ঠিক সেই আস্থারই জন্ম দেয়। কারণ শোধ না দিলে চিত্রগুপ্তের খাতায় গ্রহীতার নামে লাল দাগ পড়ে যাবে - যদি সেই ব্যক্তিকে ভবিষ্যতে কোথাও কোন ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হতে হয়, তাহলে অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। দ্বিপাক্ষিক লেনদেনে সরকারের পরোক্ষ উপস্থিতির ফলে জামানতের প্রয়োজন দূর হয়। বিদেশে এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আমেরিকাতে সর্রকার প্রত্যেককে চিহ্নিত করেন একটি সোশাল সিকিউরিটি নম্বর (সামাজিক সুরক্ষা সংখ্যা) দিয়ে - সরকারি বেসরকারি যেকোন ছোট অঙ্কের ঋণ নিতে গেলে নিজের পরিচয় এবং ঐ নম্বরটিই যথেষ্ট। অতএব, আজ যে কৃষক সঙ্গতির অভাবে মহাজনের কাছে ভিটেমাটি বাঁধা দিচ্ছেন, অথবা যিনি ছোটখাটো ব্যবসার স্বপ্ন নিয়ে গ্রাম থেকে শহরে এসে অন্ধকারে মিশে যাচ্ছেন, পরিচয়পত্র তাঁদের আলোর সন্ধান দিতে পারে।
এই প্রকল্প সফল হলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ছোট লেনদেনের ইনফরমাল অর্থনীতির অনেকখানি সরকারি আওতায় আসবে। বাংলার ছোট ব্যবসায়ী অনেক নিশ্চিন্তে লেনদেন করবেন মহারাষ্ট্রের ব্যবসায়ীর সাথে। প্রব্রজন অর্থাৎ মাইগ্রেশান বাড়বে। আজকে ইনফরমাল পরিসরে পুঁজির চরিত্র অনেক বেশি স্থানীয়, স্থাবর। এই পরিসর শুকিয়ে এলে শুধু মানুষই নন, পুঁজিও সচল হবে। সেই অর্থে বিশ্বায়নের একটি অন্তর্দেশীয় রূপ দেখতে পাব আমরা। তাতে কিন্তু মহারাষ্ট্রে বৃষ্টি না হলে বাংলার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আজকের নিস্তরঙ্গ জীবনে কাল হয়তো খানিকটা অনিশ্চয়তার ঢেউ লাগবে।
পরিশেষে আবার ফিরে আসি গোড়ার কথায়। আমাদের অভ্যাস, যেকোন বিষয়কে চেপেচুপে, কেটেছেঁটে ডানপন্থা বনাম বামপন্থার অক্ষে সাজিয়ে নেওয়ার। এক্ষেত্রে কিন্তু এধরণের একমাত্রিক বিচার মূল বিষয় থেকে আমাদের সরিয়ে নিয়ে যাবে। প্রশ্নটি জনজীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকার। চিহ্নিতকরণ বা চিত্রগুপ্ত - প্রকল্পটিকে যে নামেই ডাকুন, এর মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবধান কমানো। পশ্চিমের প্রতিটি দেশেই রাষ্ট্রের হাত অনেক বেশি প্রসারিত। কমিউনিস্ট অথবা পুঁজিবাদী সব ব্যবস্থাতেই প্রতিটি লেনদেনকে সুরক্ষিত করে সরকারি সীলমোহর। রাষ্ট্রের থেকে "স্বাধীন" অর্থনৈতিক জীবন একান্তভাবে অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য। আমাদের পশ্চিম থেকে ধার নেওয়া গণতন্ত্রের ধারণার সঙ্গে, উন্নতির ধারণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে সর্বগামী রাষ্ট্রের ধারণা। এর কোন গ্রহণযোগ্য বিকল্প আমরা গড়ে তুলতে বা ভাবতে পারিনি। আমরা সরকারকেই চিনি আমাদের যাব্তীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের একমাত্র পরিচালক হিসেবে। সকলের নাম নথিভুক্ত হলে অবশ্যই ব্যক্তির উপর সরকারি নজরদারি বাড়বে, কিন্তু অর্থনীতির সুষ্ঠু পরিচালনক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি মানেই ব্যক্তির ক্ষমতা হ্রাস নয় - নাগরিকদের মধ্যে ক্ষমতার পুনর্বণ্টনমাত্র। সরকার তার ক্ষমতাকে জনকল্যাণের কাজে ব্যবহার করবে, না শোষণযন্ত্রকে শক্তিশালী করবে - সে বিষয়ে ব্যক্তিগত বিশ্বাস থেকে আমরা অনুমান অবশ্যই করতে পারি, কিন্তু কার অনুমান কতদূর সত্য ভবিষ্যতই সেকথা বলবে।
আগস্ট ২৪, ২০০৯
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। - আরও পড়ুনভ্রমণের বিষ - প্রতিভা সরকারআরও পড়ুনপরী ও সুপারহিরো - সুষুপ্ত পাঠকআরও পড়ুনশান্তি বিলাস - Sukdeb Chatterjeeআরও পড়ুনভোট : একটু কথা - Eman Bhashaআরও পড়ুনএক্সিট পোল - রমিত চট্টোপাধ্যায়আরও পড়ুনরাবণের প্রার্থনা - তাতিনআরও পড়ুনআইটির ভাইটি - কণিষ্ক
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... অরিন)
(লিখছেন... Somnath Pal, রমিত চট্টোপাধ্যায়, পোল খুলে গেল)
(লিখছেন... Prabhas Sen, Argha Bagchi, সিক্যুয়েল চাই)
(লিখছেন... )
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... রঞ্জন , রঞ্জন , r2h)
(লিখছেন... মোহাম্মদ কাজী মামুন, দ)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... haridas, এরাও তাই বলছে, Prativa Sarker)
(লিখছেন... Kishore Ghosal, সমরেশ মুখার্জী, kk)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... অরিন, অরিন, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, ছোট মুখে , সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... :|:, পাপাঙ্গুল, পাপাঙ্গুল)
(লিখছেন... kk, দীপ, dc)
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : [email protected] ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত