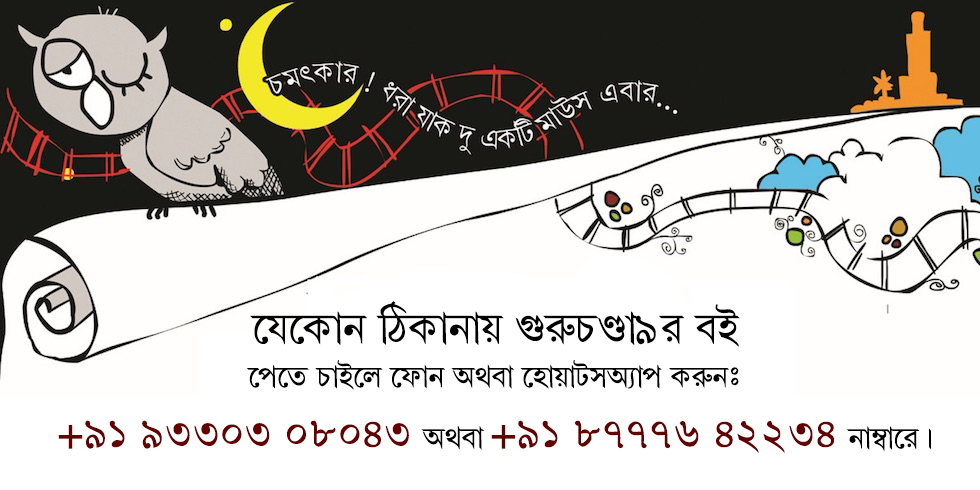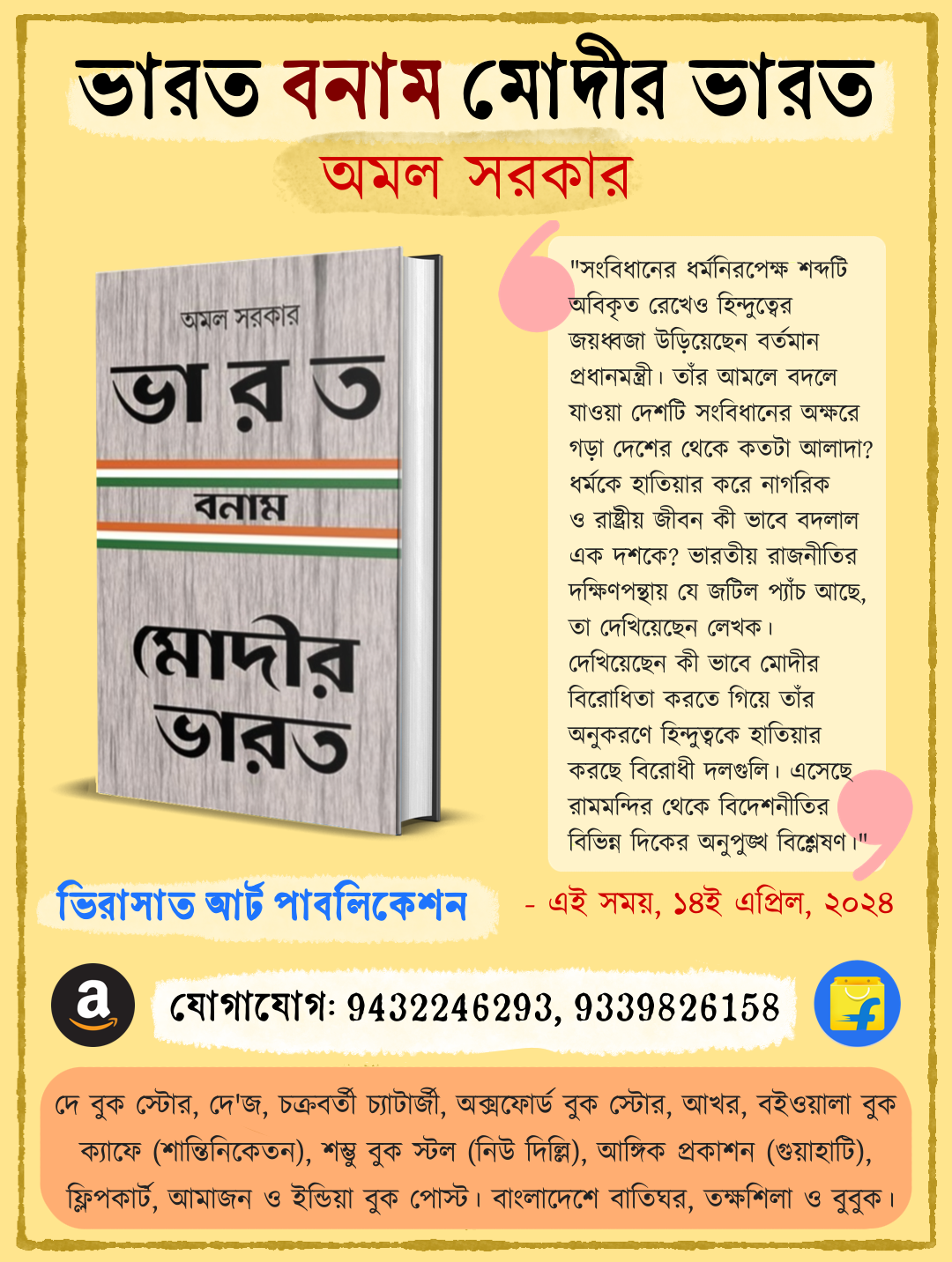- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 bip | 81.244.130.85 | ২৯ নভেম্বর ২০১৫ ১১:৫৯686954
bip | 81.244.130.85 | ২৯ নভেম্বর ২০১৫ ১১:৫৯686954- প্রাচীন ভারতের গণিত- মিথ বনাম বাস্তব
************************************************
হিন্দুদের অতীত আদৌ গৌরবের কি না-তাই নিয়ে কয়েকদিন আগে একটা পোষ্ট দিয়েছিলাম। চাড্ডিদের এমন পোষ্ট ভালো লাগার কথা না-কারন তারা একদমই পড়াশোনা করে না-আর এই অতীতের ইতিহাসটাও গোলমেলে। তবে আমার পোষ্টটাও ছিল বেশ দুর্বল। অনেক কিছুই পরিস্কার করে না লেখার জন্য, অনেকেই সঠিক মেসেজটাই ধরতে পারে নি।
প্রথম কথা হচ্ছে-প্রাচীন হিন্দু ভারত, বিশ্বমানব সভ্যতাকে এমন কিছু কি দিয়েছে, যা সভ্যতার গতিপথ পাল্টেছে? বা মানব সভ্যতায় ব্যাপক অবদান রেখেছে ?
আমি সেইসব প্রাচীন ভারতের আবিস্কার খুঁজছিলাম-যাদের ইম্প্যক্ট ফ্যাক্টর খুব বেশী গোটা বিশ্বে। সব খুঁজে পেতে মোটে দুটো জিনিস পেলাম- যেটা বলা যেতে পারে, প্রাচীন ভারতের অবদানে হাই ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর । কিন্ত এইসবের পরেও সামগ্রিক বিচারে দেখা যাবে ইজিপ্ট, চীন, সুমেরিয়ান বা গ্রীস সভ্যতার অবদান সভ্যতার ইতিহাসে সামগ্রিক ভাবে অনেকটাই বেশী। এর একটা বড় কারন এই যে বৈদিক ধর্ম বস্তুবিমুখ ছিল। সেখানে চীনের দর্শন বস্তু বা সমাজমুখী। ফলে গানপাউডার, কম্পাস, পেপার, প্রিন্টিং, মেটালার্জিক্যাল ফার্নেস এর মতন প্রায় সব গুরুত্বপূর্ন প্রযুক্তির জন্মস্থান প্রাচীন চীনে।
সভ্যতার ইতিহাসে ভারতের সব থেকে বড় অবদান দশমিক পদ্ধতি। গোটে বিশ্বে যে দশমিক নাম্বার পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়-তা হিন্দু-আরবিক নিউমেরাল বলে পরিচিত। যদিও এটা ভারতের আবিস্কার এবং পরে পার্সি-আরবিক বণিকের মাধ্যমে, তা ইউরোপের আসে।
গণিতে ভারতের বাকী অবদানগুলির স্ক্রুটিনি দরকার।
যেমন শুন্যের আবিস্কার। প্রচলিত ধারনা এটি ভারতের আবিস্কার। যা সম্পূর্ন ভুল। মিশরে খৃপূঃ ১৭০০ সাল থেকেই শুন্যের ব্যবহার চালুছিল। মেসোপটেমিয়া, রোমান, গ্রীস সব সভ্যতাতেই শুন্যের ব্যবহার ছিল।
ভারতের অবদান এই যে শুন্যকে কাজে লাগিয়ে দশমিক পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং তার ব্যপক ব্যবহার। যদিও দশমিক পদ্ধতি ইজিপ্টেও জানা ছিল-কিন্ত ব্যবহার ছিল না।
অনেকেই মনে করেন নেগেটিভ নাম্বার এবং বীজগণিতের ব্যবহার ও ভারতে প্রথম হয়। এই দাবীটি সর্বসম্মত নয়।
দুশো খৃষ্ঠাব্দেই চীনে ঋনাত্মক নাম্বার এবং বীজগণিতের প্রাথমিক প্রয়োগ দেখা যায়। ভারতে আর্য্যভট্ট এবং মূলত ভাস্করাচার্য্যের কাজেই ঋণাত্মক নাম্বার এবং বীজগণিতের প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্ত তা চীনের কয়েক শতক পরে ।
দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে ভারতীয় গণিতবিদেরা মূলত "নিউমেরিক্যাল" নির্ভর ছিলেন। বীজগণিতে সিম্বলের ব্যবহার বা জ্যামিতিতে চিত্রের ব্যবহার এবং গ্রীস ইন্ডাক্টিভ বা ডিডাক্টিভ লজিক-এই তিনটে গুরুত্বপূর্ন জিনিসের ব্যবহার তারা জানতেন না। ফলে তাদের কাজ সেই অর্থে পরবর্তীকালে আর কোথাও প্রভাব ফেলে নি।
আরেকটা মিথ, ভাস্কারা-২ নিউটন বা লেইবিঞ্জের অনেক আগেই ক্যালকুলাস আবিস্কার করে ছিলেন। এর ভিত্তি হিসাবে তারা দেখান ভাস্করের কাজে (১) গ্রহগুলির ম্যাক্সিম্যাম অবস্থানে যে ডিফারেন্সিয়াল শুন্য হওয়ার ধারনা (২) ভ্রাম্যমান পথের ম্যাক্সিমাম অবস্থানে রেট অব চেঞ্জ শুন্য হওয়ার ধারনা -তার ট্রিটিজে পাওয়া যায়।
সমস্যা হল, ক্যালকুলাসের ভাষা হয় জ্যামিতিক ( যা নিউটনের প্রিন্সিপিয়াতে আমরা দেখি) না হলে এলজেব্রিক। এর কোনটাই ভাস্করের জানা ছিল না-যেহেতু ভারতে এদুটি জনপ্রিয়তা লাভ করে নি। ফলে ক্যালকুলাস নিয়ে তার প্রাথমিক সিদ্ধান্তগুলি নিউটন বা লেইবিঞ্জের মতন গণিতের কোন শাখার জন্ম দিতে পারে নি।
ভারতে গণিত প্রতিভা অবশ্যই ছিল-আর্য্যভট্ট, হলায়ুধ, ভাস্কর -এরা সম্পূর্ন স্বাধীন ভাবেই গণিতের উচ্চ গবেষনা করেছেন। কিন্ত তিনটি কারনে প্রাচীন ভারতের গণিত গবেষনা- গণিতের বা মানব সভ্যতার ইতিহাসকে প্রভাবিত করে নি
(১) ভারতের গণিত গবেষনা ছিল অন্যদেশের গণিতজ্ঞদের থেকে বিচ্ছিন্ন । আরবেরা যেমন গ্রীস, ভারত, চীন সব দেশের জ্ঞান সিঞ্চন করে, গণিত গবেষনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন-ভারতের গণিতজ্ঞরা ছিলেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা। ফলে প্রাচীন ভারতে জ্যামিতির প্রসার হয় নি যাতে গ্রীকেরা পারদর্শী ছিল। ফলে ভাস্করাচার্য্যের পক্ষে ক্যালকুলাসের প্রাথমিক সিদ্ধান্তগুলি আবিস্কার করা সত্ত্বেও নতুন গণিতিক শাখার জন্ম দেওয়া সম্ভব হয় নি
(২) দ্বিতীয় সমস্যাটা হচ্ছে- গণিত চর্চায় ভারতীয়রা ডিডাক্টিভ বা ইনডাক্টিভ লজিকের ব্যবহার করত না। শুধু ইনটিউটিভলি সিদ্ধান্তগুলি লিখে রাখত। এর ফলে ভারতে গণিত চর্চা একটা ধাপের পরে আর এগোতে পারে নি। কিছু ভুল সিদ্ধান্তও পাওয়া যাবে । যেমন হলায়ুধ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন ০/০ এর মান শুন্য হওয়া উচিত।
(৩) তৃতীয় সমস্যাটা ঐতিহাসিক। ভারতের গণিত চর্চা ছিল বিশুদ্ধ-ফলিত কারনে না। ইউরোপে বা আরবে জ্যোতিবিজ্ঞান চর্চার মূল কারন আরো ভালো নৌ নেভিগেশন সিস্টেমের জন্ম দেওয়া। ইজিপ্টে জ্যামিতির জন্ম- জমির ট্যাক্সেশন থেকে। চীনে গণিতের চর্চা হয়েছে মূলত আরো ভাল যুদ্ধ স্ট্রাটেজির উদ্ভাবনের জন্য। আরবে গণিতের পেছনে মূল ড্রাইভার ছিল-উন্নত যুদ্ধাস্ত্র, নেভিগেশন সিস্টেম। ইউরোপেও তাই। ভারতে গণিত চর্চার একটা কারন যজ্ঞের কারনে বেদী, ইত্যাদির জ্যামিতিক মাপ নেওয়া। যা মোটেও কোন ড্রাইভিং বস্তুবাদি কারন ছিল না। ফলে ভারতের গণিত আরব বা ইউরোপের সাথে বেশী দিন পাল্লা দিতে পারে নি। কারন সব কিছুরই রাজকীয় অনুগ্রহ দরকার হত। যুদ্ধ বা রাজকার্য্যে ( ট্যাক্সেশন ) না লাগলে, সেই বিদ্যার চর্চা বেশী টানা সম্ভব ছিল না ।
ভারতের দ্বিতীয় অবদান অবশ্যই দর্শন শাস্ত্রে। উপনিষদের দর্শন পার্শীদের হাতে অনুদিত হয়ে ইউরোপে আসে। সফোমেয়ারের হাত ধরে ইম্যানুয়েল কান্টের হাতে প্রথম ভারতীয় এবং ইউরোপিয়ান দর্শনের সিন্থেসিস হয়। যদিও পরবর্তী কালে নিৎসে বা আধুনিক ইউরোপিয়ান দর্শন মোটেও কান্টিয়ান না। কিন্ত তা সত্ত্বেও , ইম্যানুয়েল কান্ট এখনো ক্ল্যাসিকাল ওয়েস্টার্ন দর্শনের সব থেকে বড় স্তম্ভ। এবং তার দর্শনের অনেকটাই উপনিষদ প্রভাবিত।
তবে প্রাচীন ভারতের বস্তুবাদি অবদান প্রায় শুন্য। সেই দিক দিয়ে চীনকেই বস্তবাদি সভ্যতার ভিত্তিভূমি বলা যায়।
- 0 | ২৯ নভেম্বর ২০১৫ ২১:৫৩686965
- মুক্তমনাতে আগেই পড়েছি। হাসান ভাইয়ার কমেন্টও পড়েছি। বেশ ইনফর্মেটিভ লেখা।
 cm | 127.247.97.70 | ২৯ নভেম্বর ২০১৫ ২২:২১686976
cm | 127.247.97.70 | ২৯ নভেম্বর ২০১৫ ২২:২১686976- বিপ জানেননা এমন বিষয় যদিও প্রায় নেই, তবু যদি কোন কারণে মিস করে থাকেন, https://en.wikipedia.org/wiki/Pell%27s_equation
https://en.wikipedia.org/wiki/Chakravala_method
লেখাটি অন্যান্য বেশির ভাগ লেখার মতই রাবিশ হয়েছে।
 বিপ | 81.244.130.85 | ৩০ নভেম্বর ২০১৫ ০২:২৪686987
বিপ | 81.244.130.85 | ৩০ নভেম্বর ২০১৫ ০২:২৪686987- আপনি না পড়েই বগল বাজাচ্ছেন মিঃ সি এম।
প্রাচীন ভারত পাটিগণিতে সেরা ছিল-পরের দিকে বীজগণিতেও উৎকর্ষ লাভ করে । ভাস্করা, মাধবাচার্য্য, হলায়ুধ-এরা একাধিক আইডেন্টি এবং
ইকোশন সমাধানে সম্পূর্ন মৌলিক অবদান রেখেছিলেন।
প্রশ্ন সেখানে না। প্রশ্ন হচ্ছে ভারতে গণিত চর্চার মৃত্যু হল কেন-আর কেনই বা আমাদের মধ্যে থেকে নিউটন বা লেইবিঞ্জের জন্ম হল না?
কারনটা হচ্ছে ভারতে গণিতজ্ঞরা , ইন্ডাক্টিভ/ডিডাক্টিভ লজিকের ব্যাবহার, জ্যামিতি এবং সিম্বলের ব্যবহারের ওপর জোর দেন নি।
সিদ্ধান্তগুলি সব একেকটা দীর্ঘ শ্লোক যা সিম্বলের ব্যবহারে হয়ত এক লাইনে লেখা যায়। ফলে "ম্যাথেমেটিক্স এজ মেথড" ভারতে গড়ে ওঠে নি।
পাটিগণিত দিয়ে পিরামিড নাম্বার সমাধান করতে গেলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই একজন গণিতজ্ঞকে অসাধারন মেধাবী হতে হবে-এবং সেক্ষেত্রে
ম্যাথেমাটিক্স এজ ডিসিপ্লিনএর গ্রোথ সম্ভব না।
আমার লেখাটা বুঝে মন্তব্য করলে বুঝতে সক্ষম হয়, কমেন্টগুলো বুঝে হচ্ছে।
 ranjan roy | 24.99.16.254 | ৩০ নভেম্বর ২০১৫ ০৬:০৯687009
ranjan roy | 24.99.16.254 | ৩০ নভেম্বর ২০১৫ ০৬:০৯687009- দুটো কথা জানতে চাই।
এক, ভারতে ন্যায় দর্শন, বৈশেষিক দর্শন ও সাংখ্যদর্শন কি সেই সময়ের অবস্থানে যথেষ্ট বস্তুবাদী নয়? ন্যায়এর কুমোরের চাকা, লাঠি ও দড়ির উদাহরণ কি প্রাচীনতম হস্তশিল্পের সঙ্গে দর্শনের যোগাযোগ দেখায় না?
এবং দর্শনের ভারতের পঞ্চপদী ন্যায়ের সিলোজিসম কি অ্যারিস্টটলের ডিডাক্টিভ ও ইন্ডাক্টিভের ত্রিপদী সিলোজিসমের সমন্বয় নয়?
দুই, দুটো নিরীশ্বরবাদী দর্শনে-- আস্তিক পূর্বমীমাংসা ও নাস্তিক বৌদ্ধ-- সৃষ্টিতত্ত্বের ও কার্যকারণ বাদের যে বর্ণনা পাই তা কি সেই সময়ের প্রেক্ষিতে ইউরোপের থেকে এগিয়ে নয়? বৌদ্ধ ডায়লেক্টিক্স কি মানবসভ্যতার চিন্তন পরম্পরায় ভারতের সর্বোচ্চ অবদান নয়?
 robu | 11.39.38.77 | ৩০ নভেম্বর ২০১৫ ০৯:৪৫687016
robu | 11.39.38.77 | ৩০ নভেম্বর ২০১৫ ০৯:৪৫687016- "আমার লেখাটা বুঝে মন্তব্য করলে বুঝতে সক্ষম হয়, কমেন্টগুলো বুঝে হচ্ছে। " - একটু বুঝিয়ে বলবেন?
 সে | 198.155.168.109 | ৩০ নভেম্বর ২০১৫ ১২:৫৮687017
সে | 198.155.168.109 | ৩০ নভেম্বর ২০১৫ ১২:৫৮687017- শুনুন, এই লিংকে একটা কথাও লেখার কথা নয় আমার, কারণ লেখাটা/গুলো আমি পড়িনি। কেবল হঠাৎ একটা বাজে বানান চোখে পড়েছে তাই জানাতে এলাম ওটা হবে - লাইব্নিৎস্। না জানলে রোমান হরফে লিখুন "Leibniz" - কেমন?
 PM | 59.14.104.119 | ৩০ নভেম্বর ২০১৫ ১৩:০৫687018
PM | 59.14.104.119 | ৩০ নভেম্বর ২০১৫ ১৩:০৫687018- ভারত আর চীন মিলিতভাবে সেই সময় পৃথিবীর ৭০% ব্যাবসা কনট্রোল করতো। কোনো রকম বস্তুবাদী চিন্তা ভাবনা ছাড়াই?
এটা তর্কের জন্যে বা বিপবাবুকে একা করা প্রশ্ন নয়। এই প্রশ্নটা এমনি-ই আমার মাথায় ঘোরে।
প্রচীন ভারত মানেই ভাববাদ এটা কি একটা মিথ? পৃথিবী জোড়া অর্থনৈতিক প্রভাব কি শুধু ভাববাদী দর্শন দিয়ে সম্ভব?
 shibir | 113.16.71.69 | ৩০ নভেম্বর ২০১৫ ১৩:২২686955
shibir | 113.16.71.69 | ৩০ নভেম্বর ২০১৫ ১৩:২২686955- ভাববাদী কেন হবে ? বস্তুবাদী দর্শন ছিলতো । চার্বাক (চরমপন্থী), বৌদ্ধ আর জৈন (নরমপন্থী) ।
আমিতো এতদিন লিবনিত্জ জানতাম ।
 Bratin | 11.39.36.24 | ৩০ নভেম্বর ২০১৫ ১৩:৪০686956
Bratin | 11.39.36.24 | ৩০ নভেম্বর ২০১৫ ১৩:৪০686956- আরে সে দি কাটাও না। সবাই এবারে তোমাকে দিদিমনি বলবে ঃ((
 potke | 190.215.41.209 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ০০:০০686957
potke | 190.215.41.209 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ০০:০০686957- ইয়ে, বিপ আপনি কি সিএম কে কিছু বল্লেন, অন্ক নিয়ে?
- dd | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ০৯:৫৯686958
- PMকে লিখছি।
এই প্রায় ৪০০ AD পর্যন্ত্য ভারতে রম রম করে বেবসা চলেছে। তখন বেসিক্যালি বৌদ্ধ যুগ। বলা হয় ষোড়োশ মহাজনপদ - কিন্তু আরো বেশী শহর গড়ে উঠেছে উত্তর ও পশ্চিম ভারত জুড়ে। বুদ্ধ ও জৈন - এই দুই ধর্মেই ব্যবসাকে হেয় করা হয় নি কখনো। বরং সংঘগুলি খুব একটিভ ভাবে ব্যবসায় সাহায্য করতো ঋন দান করে । সেই সময়ে রোম স্রামাজ্যও গম গম করছে আর ঝেড়ে তারা ভারত থেকে আমদানী করতো।
সেই রোম স্রামাজ্যও গেলো আর ভারত জুড়ে বসলো ব্রাহ্মণ্য বাদ। যতো রকমের বিধি নিষেধ করা যায় - সব চল্লো। সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হলো।বেশীর ভাগ নগরই পরিত্যক্ত হলো। কারীগড়ী গিল্ডগুলো উচ্ছন্নে গেলো।একেবারে শনির দশা।
 b | 135.20.82.164 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ১০:২০686959
b | 135.20.82.164 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ১০:২০686959- স্রামাজ্য ভারি পছন্দ হল। স্লা স্রামাজ্যবাদী।
 sm | 233.223.153.6 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ১১:০৯686960
sm | 233.223.153.6 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ১১:০৯686960- কিন্তু সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ করলো কেন? আফটার অল সেটা ছিল সোনার ডিম পাড়া হাঁস।
 avi | 113.24.86.5 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ১১:২০686961
avi | 113.24.86.5 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ১১:২০686961- আচ্ছা, গুপ্তযুগ তো ওই ৪০০ এডির আগের গপ্পো, আর গুপ্তযুগেই তো শুনেছি রোমানদের সাথে সর্বোচ্চ যোগাযোগ এবং ভারতের স্বর্ণযুগ। তা, গুপ্তদের সময় তো ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গুছিয়ে বসেছে, বৌদ্ধদের পালে হাওয়া কম।
আবার ৪০০ এডির পরেও তো বৌদ্ধ প্রাধান্য ফিরে এসেছে, হর্ষের উত্তর ভারতে বা পালদের বাংলা মগধে। বস্তুত শঙ্কর আর ইসলামের ধাক্কায় বৌদ্ধ প্রভাব চূর্ণ হল তো আরো পরে। তাহলে?
আর চোলদের সামুদ্রিক বিস্তার, শ্যাম কম্বোজে উপনিবেশ সবই তো ৭০০-৮০০ এডিতে। ওরা আবার ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিল যদ্দূর মনে হয়। তাহলে তো ব্যাপারটা অত লিনিয়ার লাগছে না?
সমুদ্র বহিত্রের ওপর বিধিনিষেধ সাগরে আরব জলদস্যুতা বাড়ার পরের নয় তো?
 PM | 116.76.148.96 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ১৪:৩২686962
PM | 116.76.148.96 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ১৪:৩২686962- আচ্ছা ডিডিদা, বুঝলাম। এখনো বৌদ্ধ ধর্ম যারা ফলো করে ( জাপান/থাইল্যান্ড অমি নিজে দেখেছি) তারা আমাদের থেকে বেশী ভালো আছে। ধর্ম অনেক দৈনন্দিন জীবন কেন্দ্রীক। থাইরা তো বেশ ধার্মিক। আমি ওদের সাথে একধিকবার ওদের মনেস্ট্রিতে গেছি। কি শান্তির জায়গা। মনে হয় ওরা একটা মধ্যপন্থা খুজে নিয়েছে। আমাদের মতো ব্রাহ্মন্য বাদ আর মায়াবাদের মাঝে দোল খাচ্ছে না।
 Ekak | 113.6.157.186 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ১৪:৩৪686963
Ekak | 113.6.157.186 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ১৪:৩৪686963- দোল না খেলেই হলো । থেরবাদী বনে যান ও এটাচমেন্টলেস হয়ে ঝপাঝপ কল্লা নাবিয়ে দিন । বার্মায় লাগলো বলে :)
 Oitihashik | 165.136.184.7 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ২১:৩৮686964
Oitihashik | 165.136.184.7 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ২১:৩৮686964- হারামজাদা আলাউদ্দিন খিলজি যদি নালন্দা পুড়িয়ে না নষ্ট করত তবে অনেক কিছুই পাওয়া যেত ।। কিন্তু সেই শুকর-খেখো টা কিছুই বাকি রাখেনি ।। অল্পস্বল্প যা পরে আছে - যেমন অংশু বধিনি - সেগুলো কি পড়েছেন ?
 Oitihashik | 165.136.184.7 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ২১:৪৯686966
Oitihashik | 165.136.184.7 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ২১:৪৯686966- এই লিংক টা একটু পরে দেখবেন - http://www.ijerd.com/paper/vol2-issue1/G02014649.pdf
 oitihashik | 165.136.184.7 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ২১:৫৩686967
oitihashik | 165.136.184.7 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ২১:৫৩686967- আর হ্যা, নাগপুর থেকে পাবলিশ করেছে bolei RSS Er maal - এইসব ধারণা করে বসে থাকলে আমি nachar
 abcd | 69.145.208.14 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ২২:১৩686968
abcd | 69.145.208.14 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ২২:১৩686968- @বিপ, উপরে লেখা তিনটে কারনের মধ্যে ১নাম্বার-এর প্রসঙ্গে আমার একটা প্রশ্ন ছিল। নতুন গণিতিক শাখার জন্ম দেওয়া কীভাবে সম্ভব বলে মনে গণিত ঐতিহাসিকরা মনে করেন?
আর একটা প্রশ্নঃ যে সময়ের কথা হচ্ছে সত্যিই কী ড্রাইভিং বস্তুবাদি কারন ছাড়া কোনও আবিস্কার সম্ভব ছিল তখন? আজকের দিনেও কী যে কোনও আবিস্কারের জন্য ড্রাইভিং বস্তুবাদি কারন অপরিহার্য নয়? বিপ-এর কথার ( ড্রাইভিং বস্তুবাদি কারন ছাড়া কোনও আবিস্কার) সাপোর্টে কোনও তথ্য প্রমান দিলে ভাল হয়।
 TB | 118.171.130.186 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ২২:৩২686969
TB | 118.171.130.186 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ২২:৩২686969- আচ্ছা, প্রোগ্রামিং করা বস্তুবাদি কাজ না ভাববাদি?
না কি মনের আনন্দে প্রোগ্রামিং করলে (যেমতি কলেজ ছাত্র অনেকে করে) উহা ভাববাদি, কিন্তু কোম্পানির জন্য করলে তাহা বস্তুবাদি?
 ranjan roy | 24.99.107.22 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ২৩:২৭686970
ranjan roy | 24.99.107.22 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ২৩:২৭686970- Oitihasik কে দুটো প্রশ্নঃ
১) 265 KAKASYA= about 965 Celsius এটা কী করে জানা গেল?
২) নালন্দা ধ্বংসকারী আলাউদ্দিন খিলজীকে কনডেম করতে হারামজাদা বা শুয়োরখেকো উপাধি দেওয়া কি একান্তই আবশ্যক? তাহলে আরেক বিধ্বংসক শশাংক বা অজাতশত্রুকে কি বলা হবে?
 ranjan roy | 24.99.107.22 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ২৩:২৯686971
ranjan roy | 24.99.107.22 | ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ ২৩:২৯686971- আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের "হিন্দু কেমিস্ট্রি" বলে বইটি সম্বন্ধে বিপ কী বলেন?
 potke | 126.202.69.238 | ০২ ডিসেম্বর ২০১৫ ০০:৩৬686972
potke | 126.202.69.238 | ০২ ডিসেম্বর ২০১৫ ০০:৩৬686972- এন আ টি র লোকজন এসব জার্নালে পাব্লিশ করছে আজকাল?
 কল্লোল | 111.63.207.255 | ০২ ডিসেম্বর ২০১৫ ০৭:৩৬686973
কল্লোল | 111.63.207.255 | ০২ ডিসেম্বর ২০১৫ ০৭:৩৬686973- ভারতীয় উপমহাদেশে গণিত তো বটেই বিজ্ঞানের কোন শাখাই বিকশিত হয় নি।
এর পিছনে একটা দার্শনিক কারন আছে বলে আমার মনে হয়। এটা নিতান্তই আমার মত।
এই উপমহাদেশের অধিবাসীরা অল্প আয়াসেই বেঁচে থাকার উপাদান পেয়ে যেতো। তার উপর একটা ভাসা ভাসা অদৃষ্টবদী দর্শন এখানকার সাধারনের গভীরে ক্রিয়া করতো।
উদাহরণ দেওয়া যাক। একজন কামার জানে লোহা কতটা লাল হলে তাতে কতটা জোর দিয়ে আঘাত করলে সে কতটা তার আকার পাল্টাবে। এটা অভিজ্ঞতা। কিন্তু সে কখনো প্রশ্ন করেনি - কেন এমন হয়। কারন সে উত্তর পেতো - জেনে কি হবে? তুমি তো এতোসব না জেনে ভালো-ই আছো পরিবার-পুত্র-কলত্র নিয়ে। আর যে দুঃখ-কষ্ট আছে তার থেকে মুক্তি পাবার জন্য বরং মোক্ষের কথা ভাবো। তাতেই মুক্তি।
এমন দর্শন অন্য কোথাও ছিলো না তা নয়। চিন, গ্রীস, মিশরেও ছিলো। কিন্তু সাধারনের মধ্যে এতো গভীরভাবে গাঁথা ছিলো না।
আর অবশ্যই গুরুমুখী শিক্ষা আর বর্ণবিভাগ জ্ঞানকে মুক্ত হতে বাধা দিয়েছে। সেটাও একটা বড় কারন। শূদ্রের জ্ঞানকে জ্ঞ বলে ধরাই হতো না। কুমোর, কামার, ধোপা, নাপিত, জমিতে কাজ করা মানুষ, এদের জ্ঞান ভান্ডার অবহেলিত হয়ে রইলো।
মহাভারতের গল্প হিসাবে চলে আসা নানান গাথা যা মূল মহাভারতের মধ্যে নেই তার একটি।
ব্যাস ফিরছেন হস্তিনাপুর থেকে। মন বিষন্ন। নিজেকে শুধাচ্ছেন - আমি কি চিরকালই পরের কাজ করে যাবো। অন্যের শ্লোক বিন্যস্ত করবো, অন্যের স্ত্রীদের গর্ভে সন্তান উৎপন্ন করবো, নিজের জন্য কি কিছুই করতে পারবো না! উনি এক ক্ষেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে ক্ষেতের কাজ দেখছিলেন। ক্ষেতে কাজ করা মানুষেরা তাকে জিগালে
- ও ঠাউর কি দ্যাখো অ্যাতো?
- এই তোমাদের কাজ দেখি। বলতে পারো বন্ধ্যা জমি উর্বর হয় কিসে?
- এ আর বেশী কথা কি! জমিতে আবর্জনা জমাও। তারপর একটা বর্ষা যেতে দাও। ব্যস।
ব্যাস ভাবলেন - তাইতো, আবর্জনা জমতে দিতে হয় আর তার সাথে জ্ঞনের ধারা - তবে না সৃষ্টি। শুধুই জ্ঞান সৃষ্টির উৎস নয়।
অন্ত্যজের কৃষি জ্ঞান বয়ে গেলো অন্য খাতে। মহাভারত পেলো চরাচর। কিন্তু কৃষি বিজ্ঞান অবহেলিত রয়ে গেলো।
- dd | ০২ ডিসেম্বর ২০১৫ ০৮:২৬686974
- @ Avi। হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। কিন্তু বিশদে উত্তর দিতে গেলে একটা প্রবন্ধই ফাঁদতে হয়। আর অল্পো কথায় সারাও যাবে না।
একচুয়ালি,কিছুদিন হলো আমি এইটা নিয়ে একটা লিখবো বলে মনে মনে সাঁট করছি। মানে এই কামিং অফ ডার্ক এজ ইন ইন্ডিয়া আর ব্রাহ্মণ্যবাদের জন্য পুরো সমাজটাই ভোগে গেলো - এটা নিয়ে।
একটি সবুর করুন
- dd | ০২ ডিসেম্বর ২০১৫ ০৮:৩৩686975
- এটা তো খ্যাল করলেন ,কল্লোল যে টুক করে রেসিয়াল প্রোফাইলং করে দিলো? কিন্তু এই প্রোফাইলিং কিন্তু দোষের নয় - মাইন্ড ইট।
কল্লোল যা বল্লো, তা হুবহু বলেন অনেক নামজাদা লোকেই। এই অদৃষ্টবাদের ভুত হিন্দু সমাজকে (হিন্দু = ভারতীয়) গিলে ফেলেছিলো । হিস্ট্রী ,স্পেশালি মিলিটারী হিস্ট্রীতে এই ধরনের কথা বহুবার,বহুবার উল্লেখিত হয়।
- dd | ০২ ডিসেম্বর ২০১৫ ০৮:৪৮686977
- রেফারেন্সটা খুঁজে পাচ্ছি না।
তৈমুরের সেনারা যখন মামুদ শাহের রাজ্য তছনছ করে দিচ্ছে তখন তার সাধ হয়েছিলো মোঙ্গোল সাম্রাজ্যকে দিল্লী পর্যন্ত্য টেনে আনবেন। তার প্রধান মন্ত্রী তাকে বল্লেন ভুলেও ইটি করবেন না। এই দেশে যে আসে সেই বুঝভম্বুল হয়ে যায়। তার চে যাস্ট লুটপাট করে আবার দেশে ফিরে যাই। তৈমুর সেই কথা শুনে ফিরেও গেলেন।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল, স্বাতী রায়, নিরমাল্লো)
(লিখছেন... প্রতিভা, kk, অরিন)
(লিখছেন... Naresh Jana, সন্তোষ সেন , দ)
(লিখছেন... Somnath Pal, রমিত চট্টোপাধ্যায়, পোল খুলে গেল)
(লিখছেন... Prabhas Sen, Argha Bagchi, সিক্যুয়েল চাই)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... অসিতবরণ বিশ্বাস , Eman Bhasha)
(লিখছেন... সিএস, প্রাক্তন, অরিন )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল)
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... অরিন, অরিন, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, ছোট মুখে , সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল, দীপ, দীপ)
(লিখছেন... kk, দীপ, dc)
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : [email protected] ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত