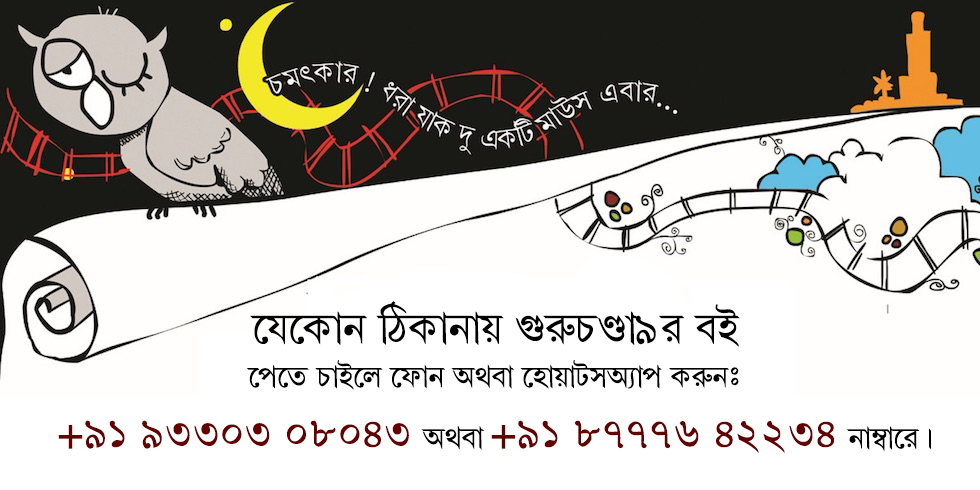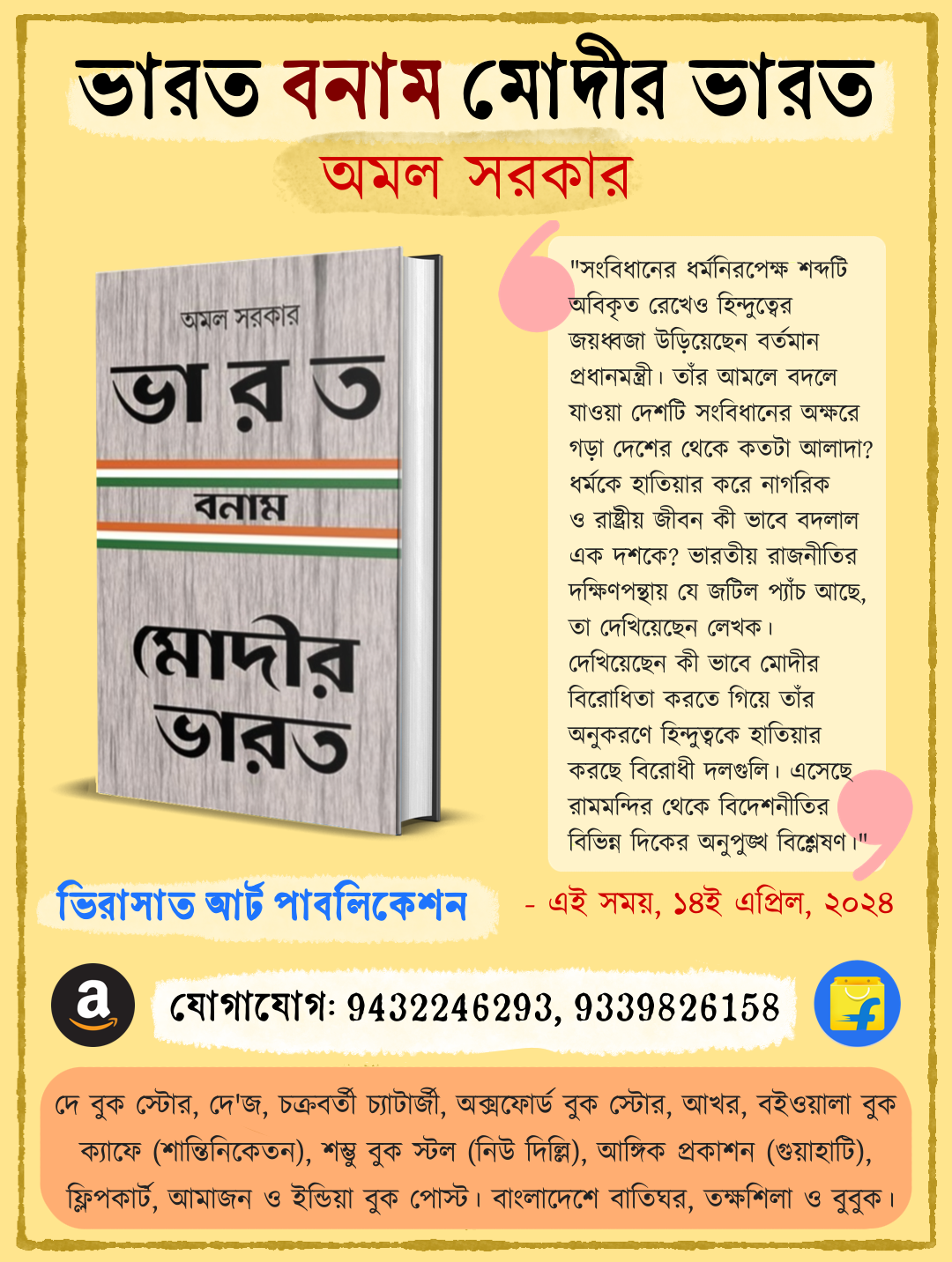- বুলবুলভাজা আলোচনা বিবিধ

-
শিক্ষা বিষয়ক
সলিল বিশ্বাস লেখকের গ্রাহক হোন
আলোচনা | বিবিধ | ২৮ জুন ২০১১ | ৬৬৪♦ বার পঠিত - গুরুচন্ডালিতে প্রকাশিত খসড়াটির সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে খসড়া বিষয়ক নিজেদের মতামত জানানোর অনুরোধ জানানো হয়েছিল। সেরকম বেশ কয়েকটি লেখা আমাদের কাছে এসেছে। এই লেখাটি তাদের মধ্যে একটি।
দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতা করা, ভাবনাচিন্তা করা, প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার সঙ্গে জড়িত থাকা, ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে এই উপলব্ধি হয়েছে যে বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থা বলে যা প্রচলিত, তার সঙ্গে "শিক্ষা' র সম্পর্ক খুবই কম। স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির এই সিস্টেমটাকে বরং বিদ্যালয়-ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। এই ব্যবস্থাটিতে শিক্ষা বস্তুটি অনুপস্থিত থাকে। কিন্তু এই ব্যবস্থা থেকে কিছুই শেখা হয় না তা বলে দেওয়া যায় না। যদিও কেউ কেউ তাই বলেন। এমনিতে ক্লাসরুমে বসে শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রদের যেটুকু ভাবের বিনিময় ঘটে, তাতে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েই যে জ্ঞানার্জন করেন, তা হয় ঘটনাচক্রে। তাই বলা যেতে পারে এই ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও ছাত্ররা একেবারে কিছু শেখে না তা নয়। তবে সে শিক্ষার পেছনে এই প্রচলিত ব্যবস্থার অবদান কম। "শিক্ষা' যেটুকু হয় সেটা হয় ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে কিছুটা বাইরে থেকে।
মনে হয় না এই ব্যবস্থাকে বজায় রেখে এর কোন উন্নতি করা সম্ভব। কিন্তু যেহেতু আপাতত তেমন পরিবর্তন ঘটছে না, এবং যেহেতু সারা কর্মজীবনে এবং অবসরজীবনেরও অনেকটা এই ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত থেকেছি। কিছু তাৎক্ষণিক সাফসুতরো এর মেরামতের কথা বলছি এখানে। খুব একটা লাভ হবে না তা মেনে নিয়েই।
এখানে যে সব ব্যাপারে সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে তার প্রত্যেক স্তরের জন্য বিস্তারিত প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে।
সিলেবাসে কিছু পরিবর্তন করে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। প্রচলিত ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা সিলেবাসের থেকে বিশেষ কিছু শিখে উঠতে পারে না। তারা যেটা শেখে, এবং আমরা শেখাই সেটা হল কিছু trick, পরীক্ষায় কীভাবে নম্বর তুলতে হয়, তার "ফন্দি'।
এই মুহূর্তে, যেখানে পড়াশোনা সবচেয়ে বেশী হবার কথা ছিল, সেই স্নাতক শ্রেণীর কলেজগুলিতে পড়াশোনা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। কলেজগুলি বন্ধ করে শুধু যদি একটা নাম লেখাবার জায়গা থাকে তবেও এখনকার এই শিক্ষাব্যবস্থা চলতেই থাকবে। ছাত্রছাত্রীরা নাম লেখাবে, দু বছরে একটা পরীক্ষা দেবে, পরীক্ষায় পাশ করবে বা ফেল করবে, তিনটে পরীক্ষা দিয়ে একটা পাশ করে বেরোলে ইউনিভার্সিটির আরও দুটো পরীক্ষা দেবে এবং পাশ করে বেরোবে। এই পুরো ব্যবস্থাটা চলতেই থাকবে।
ছাত্ররা এখন আর পড়তে যায় না ক্লাসে। মাস্টারমশাইরাও অনেকে আর পড়ান না । কোন মাস্টারমশাই পড়ান না একথা যেমন ঠিক নয়, তেমন কোন ছাত্রই পড়তে যায় না সেকথাও ঠিক নয়। মাস্টারমশাইদের ক্লাসে পড়াবার জন্য কিছু ছাত্রছাত্রী দরকার। সেটা তাঁরা পান না। না পাবার একটি কারণ হল - ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস করতে ভাল লাগে না। তারা ক্লাসে বসে এই পড়াশোনার মধ্যে মূল্যবান কিছু পায় না। অথচ ছাত্র শিক্ষক উভয়ের পারস্পরিক আদানপ্রদানের ওপরেই কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে শিক্ষা।
ক) প্রথম ধাপ: ভর্তি
ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের অনীহার কারণ খুঁজতে গেলে চালু ব্যবস্থার শুরুতে যাওয়া দরকার। এই ব্যবস্থার শুরুতেই স্কুল ছেড়ে একজন ছাত্র বা ছাত্রী "ভর্তি' হতে আসছে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় একটি মেধাতালিকা (এখানে বলে রাখা ভাল, এই মেধা বস্তুটির সম্পর্কে আমার প্রচুর প্রশ্ন আছে।) অনুসারে ছাত্রদের ভর্তি হবার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটি কলেজেই মেধা তালিকা হয়, সেই মেধা তালিকা অনুসারে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী ভর্তিও হন। কিন্তু অচিরেই একটা সময় সেই মেধাতালিকা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। তখন ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হতে থাকে কখনো কারো রেকমেন্ডেশনে, কারো ছেলেমেয়ে হিসেবে, ইউনিয়নের লোক হিসেবে, রাজনৈতিক দলের লোক হিসেবে এবং এরকম আরও অনেক উপায়ে।
এই রেকমেন্ডেশন যে কোন কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে কী ধরনের চাপ সেটা কলেজ প্রশাসনে যুক্ত না থাকলে বোঝা সম্ভব না। রেকমেন্ডেশন আসে রাজ্যপালের দপ্তর থেকে, মন্ত্রীদের কাছ থেকে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, শিক্ষা দপ্তরগুলো থেকেও রেকমেন্ডেশন আসে। যে সব সরকারী দপ্তরের থেকে রেকমেন্ডেশন আসে, সেগুলোর কাছে কলেজগুলো কোন না কোনভাবে দায়বদ্ধ বা ঋণী। ফলে ঐ অনুরোধ রক্ষা না করলে পরে দরকারের সময় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের হাতে হেনস্থা হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। আর ছাত্রসংসদ বা রাজনৈতিক দলের অনুরোধ উপেক্ষা করা আরও বিপজ্জনক, কারন রাজনৈতিক দলের রেকমেন্ডেশন উপেক্ষা করলে অধ্যক্ষকে বা প্রশাসককে অনেকসময় সরাসরি শারীরিক মানসিক নিগ্রহের শিকার হতে হয়। সমস্ত রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেই এই একই কথা প্রযোজ্য। কলেজে ভর্তির রাজনীতির ক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক দলের মধ্যেই বিন্দুমাত্র তফাত দেখা যায় না। রাজনৈতিক দলগুলির মদতপুষ্ট ছাত্রদল, এবং দুষ্কৃতিচক্র ও দুর্নীতিচক্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়েও ছাত্র ভর্তি করায়, যার পেছনে মেধা, কোন দলের প্রতি আনুগত্য বা আদর্শ খুঁজতে যাওয়া বৃথা।
এই জাতীয় দুর্নীতির পিছনে তাৎক্ষণিক কারণ হয় রাজনৈতিক ফায়দা, তোলাবাজী, ক্ষমতা দেখানো, ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে নির্দোষ এবং অনভিজ্ঞ তরুণ মনকে বিষময় করা। এর অনেক উদাহরণ দিতে পারবেন যে কোনো কলেজের যে কোনো শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী। এই সবের নিশ্চয় বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক কারণ আছে, কিন্তু কলেজে হাতে কলমে কাজ করার সময়ে সে সব কথা মনে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ কোনো কলেজের প্রশাসনকে প্রশ্ন করলে উত্তর পাবেন: আমাদের কলেজে এ-সমস্ত হয় না।
ইউনিভার্সিটির নিয়ম অনুসারে প্রতিটি কলেজে প্রতিটি বিষয়ে আসনসংখ্যা সীমিত। তার বেশী ভর্তি করা কলেজগুলির পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু রেকমেন্ডেশনের অত্যাচারে অধিকাংশ সময়েই কলেজগুলি নির্দিষ্ট আসনের চেয়ে অনেক বেশী ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে। যেহেতু বেশী সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হলে কলেজগুলির কিছুটা আয় বাড়ে, তাই কলেজ কর্তৃপক্ষের এই উদ্বৃত্ত ছাত্রদের ভর্তি করার কাজ বে-আইনি কিনা তা নিয়ে কোন মাথাব্যাথা নেই। যে সব ছাত্ররা নানা ধরনের রেকমেন্ডেশনে ভর্তি হয়, তাদের ক্লাস করার কোন দায় থাকে না। কারন যাঁরা তাদের রেকমেন্ড করেন তাঁরা বিনিময়ে শুধু এই ছাত্রদের আনুগত্য বা অর্থই চান। শুধু ভর্তির সময়েই নয়, এই অর্থ বা আনুগত্যের বিনিময়ে এটাও দেখা হয়, যাতে ছাত্রটি ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলেও ন্যূনতম উপস্থিতির নিয়মের তোয়াক্কা না করেই পাশ করে যেতে পারে। যে নিয়মের ফলে ন্যূনতম উপস্থিতি না থাকলে পরীক্ষায় বসতে পারারই কথা নয়। অপরপক্ষে যে ছাত্রটি অর্থের বিনিময়ে ভর্তি হয়, বা কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য দেখায়, তার কোন দায় থাকে না ক্লাসে উপস্থিত থাকার। কলেজে ভর্তি হবার মত ক্লাসে উপস্থিত না থেকেও উপস্থিতির ন্যূনতম হার বজায় রাখার উপায় একই। যে সব রাজনৈতিক দল, বা দপ্তর বা তার আধিকারিকরা এই মেধা তালিকা বহির্ভূত ছাত্রদের পাঠান তাঁরা চান যে সেই ছাত্র বা ছাত্রীটি তাঁদের দল বা দপ্তরটির প্রতিনিধিত্ব করুক। এই কারণে সে যদি কলেজের নিয়মাবলী মেনে চলতে না চায় তবে ছাত্রটির পেছনে তাকে যাঁরা রেকমেন্ড করেছেন তাঁদের পূর্ণ সমর্থন থাকে। ফলে ছাত্রদের ক্লাস না করার ব্যবস্থাটা ভর্তির সময়েই পাকা হয়ে যায়। আসনসংখ্যার তুলনায় বেশী ছাত্র ভর্তি করার অর্থই হল, এটা ধরে নেওয়া যে কিছু ছাত্র ক্লাসে আসবে না। সবাই ক্লাস করলে কিছুতেই আসনসংখ্যার অতিরিক্ত ছাত্র নিয়ে ক্লাস করা সম্ভব নয়।
এই অব্যবস্থা জারী রাখার মধ্যে কিছু শিক্ষকও জড়িত থাকেন। তবে তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। হয়ত শতকরা মাত্র দুই শতাংশ শিক্ষক এতে জড়িত থাকেন। কলেজের অফিসগুলির কেউ কেউ এই দুর্নীতির সঙ্গে প্রবলভাবে জড়িত। পুরো ব্যবস্থার মধ্যে থেকে এই দুর্নীতি দূর না করে শুধু সিলেবাস পরিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন একেবারেই অসম্ভব। তাছাড়া সিলেবাস পরিবর্তনের মধ্যেও দলতন্ত্র কাজ করে, বই বিক্রির ধান্ধাবাজীও কাজ করে।
ভর্তি বা অ্যাডমিশনের ব্যাপারে কিছুটা স্বচ্ছতা আনা সম্ভব এই ব্যবস্থাটিকে 'ওয়েব বেসড' করে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিভিন্ন কলেজের নানারকম সীমাবদ্ধতা আছে। কোন কলেজে সমস্যাটা আর্থিক, কোথাও বা প্রযুক্তিগত, কোথাও বা সম্পূর্ন অন্য কিছু। কিন্তু ভর্তির ব্যাপারে দুর্নীতি রোধ করতে পুরো ব্যবস্থার মধ্যে স্বচ্ছতা আনাই একমাত্র উপায়। এবং তথ্য-প্রযুক্তির সাহায্যে এ কাজ অনেকটাই করা সম্ভব এটা পরীক্ষিত সত্য।
যে সব কলেজে আসনসংখ্যার তুলনায় ছাত্র কম, সেখানেও ছাত্ররা ক্লাস করতে আসে না। কারন ছাত্রদের ধারনা পরীক্ষায় পাশ করার সঙ্গে ক্লাস করার কোন সম্পর্ক নেই। ক্লাসে শিক্ষকরা বলেন পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিষয়টি পড়তে। কিন্তু ছাত্ররা কেবল বিষয়টি পড়ে বিষয়টির উপর কোন প্রশ্নের উত্তর লিখতে সক্ষম হয় না। তারা আশা করে, নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তরটি শিক্ষকরা তাদের লিখিয়ে দেবেন, তারা পরীক্ষায় শুধু সেটা লিখে ভালভাবে পাশ করবে। তারা বিষয়টি পড়ে নয়, শুধু উত্তরটা পড়ে পাশ করতেই অভ্যস্ত। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এই ধারণা ভুলও নয়। ঠিক যে "উত্তর' লিখলেই পাশ করবে, এ কথা তো ব্যবস্থাই বলে। কে কী শিখল সেটার প্রকৃত মূল্যায়ণ করার কোন ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মের মধ্যে নেই।
একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশনের এত বেশী করেন যে তাঁদের আর ক্লাস নেবার উৎসাহ থাকে না। এ কথা সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ এমন বহু বিষয় এবং বিভাগ আছে যেখানে একজন শিক্ষকও প্রাইভেট টিউশনের সঙ্গে যুক্ত নন। সেখানেও ছাত্রদের ক্লাসে উপস্থিত থাকার আগ্রহের কোন পার্থক্য অন্য কলেজের তুলনায় বিন্দুমাত্র বেশী নয়। কিন্তু টিউশন তো চলতেই থাকে। একটি কলেজের কথা জানি, যেখানে দুটোর পরে কোন ক্লাস হয় না। সবাই টিউশনি পড়তে চলে যায়। এর সঙ্গে শিক্ষক অনেকে থাকেন, আবার শিক্ষক নন এমনও অনেকে থাকেন। একটা সমান্তরাল বিদ্যালয় চলতে থাকে। ব্যক্তি শিক্ষকের চাইতে বিভিন্ন সেন্টার সেখানে অধিকতর পেশীবহুল।
ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার বাড়াতে গেলে প্রথমেই ভর্তির ক্ষেত্রে অরাজকতা বন্ধ করতে হবে। কারো কোন অনুরোধ ছাড়াই নির্দিষ্ট মেধা তালিকা অনুসারে সঠিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হলেই সমস্যা কিছুটা দূর হবে। দুর্নীতি বাদ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান নিয়মগুলির যথাযথ প্রয়োগের ফলে বাড়তে পারে ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার।
খ) পার্সেন্টেজ
বর্তমানে ক্লাসে ন্যূনতম উপস্থিতির হারের যে নিয়ম রয়েছে, সেটাকেই যদি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা যায় তবেও বাড়বে ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার। এই নিয়মটি যথার্থ অবশ্যই বিচার-সাপেক্ষ। কিন্তু এখানে আমরা কেবল প্রচলিত অবস্থার কথাই বলব। নিয়মে বাঁধা পড়ে ক্লাসে এলে হয়ত ছাত্রছাত্রীদের বিষয়ের ওপর আগ্রহ বা মনোযোগ বাড়বে না বিন্দুমাত্র, কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় ঞ্ছপার্সেন্টেজেরঞ্চ নিয়ম তুলে দিলে ক্লাসেই আসবে না কেউ। তাই সেদিকে নজর দেবার আগে প্রথমে তৈরী করা দরকার নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হবার অভ্যাস। জোর করে কাউকে ক্লাসে এনে লাভ হয় না। বদ্ধ ঘরে বসে থাকতে হলে একটা মানসিক বাধা তো এসেই পড়ে। এখন ছাত্রছাত্রীরা, বিষেশত: যারা মেধা তালিকার বাইরে বিভিন্ন বিকল্প উপায়ে ভর্তি হয়েছে তারা জানে যে তাদের বিরুদ্ধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কিছু পদক্ষেপ নেওয়া অসম্ভব, কারণ তাদের পেছনে রয়েছে তাদের সেই রাজনৈতিক দল বা প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাভোগী গোষ্ঠী যাদের অবজ্ঞা করার ক্ষমতা বা সাহস কলেজ কর্তৃপক্ষের নেই।
কলেজ বা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার্থীদের আটকে দিতে পারে। কখনো কখনো দেয়ও। কিন্তু এই আটকে দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন হলে, বিশ্ববিদ্যালয় সব দায় চাপায় কলেজের উপর। বেচারা কলেজের তখন কিছু করার থাকে না।
উপস্থিতির হার বাড়লে শিক্ষকরাও উৎসাহিত হবেন আরও আন্তরিক ভাবে ক্লাস নেবার ক্ষেত্রে। বর্তমানে অগণিত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে তাঁরা প্রতিদিন ক্লাস নিতে গিয়ে প্রতিদিন নতুন নতুন মুখ দেখেন। সঠিক সংখ্যায় ছাত্রদের নিয়মিত উপস্থিতি শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার সহায়ক হবে। যার ফলে কেবলমাত্র পরীক্ষার প্রস্তুতির বাইরেও ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে হয়ত কিছুটা পারস্পরিক আদানপ্রদানের সম্পর্ক ফিরে আসবে, যা প্রকৃত "শিক্ষা'র সহায়ক।
গ) প্রশাসন
কলেজ প্রশাসনের আর এক প্রধান সমস্যা হচ্ছে উপযুক্ত অধ্যক্ষ পাওয়ার সমস্যা। দেখা যায় যে পদ খালি থাকলেও এবং সে পদে অধিষ্ঠিত হবার যোগ্যতা থাকলেও কোন ভাল শিক্ষকই সেই পদে যোগ দিতে চান না। যাঁরা অধ্যক্ষের পদে যোগ দিতে ইচ্ছুক, অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় যে তাঁর পেছনে তাঁর বা তাঁকে প্রভাবিত করছে এমন কোন গোষ্ঠীর স্বার্থ বর্তমান। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ক্ষমতার লোভ বা আর্থিক সুবিধার লোভও কাজ করে। এই উপলব্ধি থাকা সত্বেও যাঁরা কেবলমাত্র এই অচলায়তনে কিছুমাত্র "পরিবর্তন' আনার স্বপ্ন নিয়ে অধ্যক্ষের আসনে বসেন, তাঁদের ভুল ভাঙতে বেশী সময় লাগে না। এমন উদাহরণও খুঁজলে বহু পাওয়া যাবে। কলেজের উন্নয়ন করা বা প্রশাসনিক কঠোরতা দেখানো অধ্যক্ষের পক্ষে এই প্রচলিত ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। অনেকে দাবি করেন, এটা সম্ভব। কিন্তু দেখা যায়, তাঁরা নিয়ন্ত্রণ রাখেন ছাত্রসংসদ বা দলকে তুষ্ট করে। সব রকম ভাবে। কারণ একজন ছাত্র বা একজন শিক্ষাকর্মী বা শিক্ষক, ঘেরাও করে বা কর্মবিরতির মত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে একজন অধ্যক্ষকে হেনস্থা করতে পারেন। কিন্তু কোন অধ্যক্ষ কোন অবাধ্য ছাত্র বা কর্মচারী বা শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিতে পারেন না। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার আইনগত কোন অসুবিধা না থাকলেও বাস্তব পরিস্থিতি সেই আইন প্রয়োগের অনুকূল নয়। একজন অধ্যক্ষ, যিনি কলেজটা চালাবেন, তাঁর তো কিছু ক্ষমতা থাকা দরকার। বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থায় ক্ষমতাটা উল্টো দিকে অবস্থান করে।
প্রশাসনের ক্ষমতা বলতে কেবল শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেবার ক্ষমতা বোঝানো হচ্ছে না। শাস্তি প্রশাসনের প্রধান চালিকাশক্তি হতে পারে না। Principal কথাটার মানে হচ্ছে The first among the equals. অর্থাত তিনি শিক্ষাদীক্ষা, অভিজ্ঞতা, বয়স ইত্যাদিতে অগ্রগণ্য। একজন প্রিন্সিপ্যাল কেবলমাত্র শাস্তি দেবার কাজে অগ্রগণ্য এটা হতে পারে না। অগ্রগণ্য হবার অর্থ, তিনি হবেন একজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং মানুষ হিসেবে অগ্রগণ্য । ভাল শিক্ষক অধ্যক্ষ হতে আসবেন তখনই, যখন তিনি বুঝবেন প্রশাসনকে তিনি নিয়মমাফিক চালাতে পারবেন।
ঘ) শিক্ষকের অভাব
শুধু অধ্যক্ষ নন, কলেজে কলেজে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষকেরও আকাল। কিন্তু শুধু শিক্ষক কম বলেই কলেজে ক্লাস ঠিকমত হয় না একথা বললে ভুল হবে। সময়, ক্লাসরুমের সংখ্যা, শিক্ষকের সংখ্যা, সিলেবাস ইত্যাদি বুঝে নিয়ে রুটিন বানাতে বসলে দেখা যাবে একটা বিষয় ঠিক রাখতে গেলে অন্যটা অবিশ্বাস্য রকম বেমানান হয়ে যাচ্ছে সংখ্যার দিক থেকে। হয়ত শিক্ষক আছেন অনেক কিন্তু ক্লাসরুম নেই যথেষ্টসংখ্যক। কিংবা ক্লাসরুম খালি আছে প্রচুর কিন্তু শিক্ষক যে কজন আছেন তাঁরা যথেষ্ট ক্লাস নিয়ে পড়াতে গেলে বিশ্রাম না নিয়ে সারাদিন প্রতিটি ক্লাস করে যেতে হবে। এরকম নানা অসুবিধা।
ঙ) কী পড়বে ছাত্ররা
ছাত্রদের মধ্যে রয়েছে সঠিক বিষয় বেছে নেবার অসুবিধা। যে বিষয়ে চাকরির সুযোগ বেশি, সবসময় সেই বিষয়েই ছাত্রছাত্রীদের ভিড় বেশি। যারা সেই বিষয় নির্বাচন করছে তারা অনেকসময়েই সেটা ভাললাগা থেকে বেছে নিচ্ছে না। ফলে সে বিষয়ে তার ভাল করার আশা কম। অথচ শিক্ষাব্যবস্থা এমনই, যে পরীক্ষায় নম্বর পাবার কিছু ফিকির রপ্ত করলেই প্রায় যে কেউই সসম্মানে সফল হতে পারে। সমস্যা হচ্ছে এরকম ছাত্র যখন তার সাফল্যের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে পরবর্তী প্রজন্মের শিক্ষক হয়। এবং শিক্ষক হিসেবে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। শুরুতেই ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাউন্সেলিং করা দরকার, যাতে তারা তাদের ক্ষমতা অনুসারে বিষয় বেছে নিতে পারে, এবং সেই বিষয়ে তার বর্তমান প্রথাগত শিক্ষা ও সাফল্যলাভ হয়। নয়ত উপরোক্ত সমস্যা থেকেই যাবে যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সমাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।
চ) পরীক্ষা
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও একটি বিষয়ে চূড়ান্ত অব্যবস্থা চলে সেটা হল পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র তৈরি ও পরীক্ষার পরে খাতা দেখা। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে "আর্টস' বিষয়গুলির ক্ষেত্রে,খাতা দেখার কোন নির্দিষ্ট মান নেই। এক এক শিক্ষক একেকরকম ভাবে খাতা দেখেন। ফলে নম্বর পাবার ক্ষেত্রে ছাত্রদের মধ্যে নিদারুন বৈষম্য দেখা যায়। নিজের কলেজের শিক্ষকের খাতা দেখা আর বহিরাগত শিক্ষকের খাতা দেখার মধ্যেও বিস্তর তফাত। অনেকসময়েই নিজের কলেজের শিক্ষক নিজের কলেজের ছাত্রদের নম্বর কম দিতে দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন। এর কারণ ছাত্রদের নম্বর কম দেওয়ার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের "শাস্তি' পাওয়ার উদাহরণও অনেক আছে। খাতা দেখার একটা নির্দিষ্ট মান ঠিক না করতে পারলে উপরিলিখিত সমস্যাগুলি অবশ্যম্ভাবী। এ ছাড়াও খাতা দেখার ক্ষেত্রে আরও একটা সমস্যা বর্তমান। কম সময়ের মধ্যে অনেক সময়েই অনেক খাতা একজন শিক্ষককেই দেখতে হয়। খাতা দেখার মান এর ফলে প্রচণ্ড প্রভাবিত হয়। যদি এমন নিয়ম করা যায় যে প্রত্যেক শিক্ষককেই খাতা দেখতে হবে, তাহলে শিক্ষকপ্রতি খাতার সংখ্যা কিছুটা কমে এবং একজন শিক্ষকও খাতা দেখার জন্য সময়ে বেশী দিতে পারেন। যাঁরা পরীক্ষার খাতা দেখবেন তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব। উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের খাতা দেখার ক্ষেত্রে নম্বরের বৈষম্য কমে এটা ঘটনা। এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এমন কিছু কঠিন কাজও নয়। বহুবার নানাভাবে এই প্রশিক্ষণের প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে রাখা হলেও আজ অবধি এ বিষয়ে কিছু হয় নি। এ কাজে প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছার। ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়নের জন্য উপরোক্ত দুটি পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরী।
ছ) শিক্ষক নিয়োগ
শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই শোনা যায় যে নেট-স্লেট বা অন্যান্য নিয়োগের পরীক্ষার মান অত্যন্ত কঠিন এবং এই পরীক্ষাগুলিতে সাফল্যের হার অত্যন্ত কম। ফলে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। যাঁরা শিক্ষক হবেন তাঁদের কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হবে এটাই তো স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে কোন ছাড় থাকা উচিত না। এখানে নিয়োগের পরীক্ষায় সাফল্য ছাড়া অন্য কোন যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়।
এক সময়ে ইউজিসির নিয়ম মত প্রতি চল্লিশ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক থাকা প্রয়োজন বলে স্বীকৃত হয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষকের সংখ্যা এই অনুপাতের অনেক কম। নতুন শিক্ষক নিয়োগ না হয়ে এতদিন প্রয়োজন হলে আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থাও পাল্টে বরং চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের দিকে পুরো ব্যবস্থাটা চলে যাচ্ছে। একজন নিয়মিত শিক্ষকের সঙ্গে একজন আংশিক সময়ের শিক্ষক বা একজন চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকের বেতনের বৈষম্য অনেক। যে সমস্ত শিক্ষক চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করেন, বা যাঁরা আংশিক সময়ের জন্য নিযুক্ত, তাঁদের অনেক ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বশংবদ হয়ে থাকতে হয় কাজ হারাবার ভয়ে। ফলে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই ঠিকমত কাজ করতে পারেন না, অথবা, নানা ভাবে চাকরি রক্ষার জন্য আন্দোলন বা দরবার করায় ব্যস্ত থাকেন। যা শিক্ষার পরিবেশের পরিপন্থী। সব কলেজে এমন হয় না ঠিকই, কিন্তু এমন কলেজেরও অভাব নেই।
শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনেকসময়েই বলা হয় যে সঠিক মানের প্রার্থীর অভাব। অথচ বহু যোগ্য লোক রয়েছেন। বহু প্রার্থী রয়েছেন নেট স্লেট পাশ করা। অভাবটা হয়ত সঠিক মানের চাকুরীপ্রার্থীর নয়, অভাব সদিচ্ছার।
যে কটি বিষয় নিয়ে এখানে বলা হল তার সঙ্গে আনেক কিছু সংযোজিত হতে পারে। প্রতিটি বিষয় নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা হওয়া দরকার। নিশ্চয় অনেক বিষয় বাদ গেল। এমন একটি জটিল ব্যাপারে চটজলদি সমাধানসূত্র বলে দেওয়া উচিত নয়। এই কথাগুলি বৃহত্তর আলোচনার সূত্রপাত ঘটাক, এটাই কাম্য।
শ্রুতিলিখন: কৌশিক মিত্র
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। - আরও পড়ুনভ্রমণের বিষ - প্রতিভা সরকারআরও পড়ুনএক্সিট পোল - রমিত চট্টোপাধ্যায়আরও পড়ুনরাবণের প্রার্থনা - তাতিনআরও পড়ুনআইটির ভাইটি - কণিষ্ক
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল, Prativa Sarker, kk)
(লিখছেন... অরিন, kk)
(লিখছেন... Somnath Pal, রমিত চট্টোপাধ্যায়, পোল খুলে গেল)
(লিখছেন... Prabhas Sen, Argha Bagchi, সিক্যুয়েল চাই)
(লিখছেন... )
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... রঞ্জন , রঞ্জন , r2h)
(লিখছেন... মোহাম্মদ কাজী মামুন, দ)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... এরাও তাই বলছে, Prativa Sarker, বিপ্লব রহমান)
(লিখছেন... Kishore Ghosal, সমরেশ মুখার্জী, kk)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... অরিন, অরিন, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, ছোট মুখে , সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... :|:, পাপাঙ্গুল, পাপাঙ্গুল)
(লিখছেন... kk, দীপ, dc)
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : [email protected] ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত