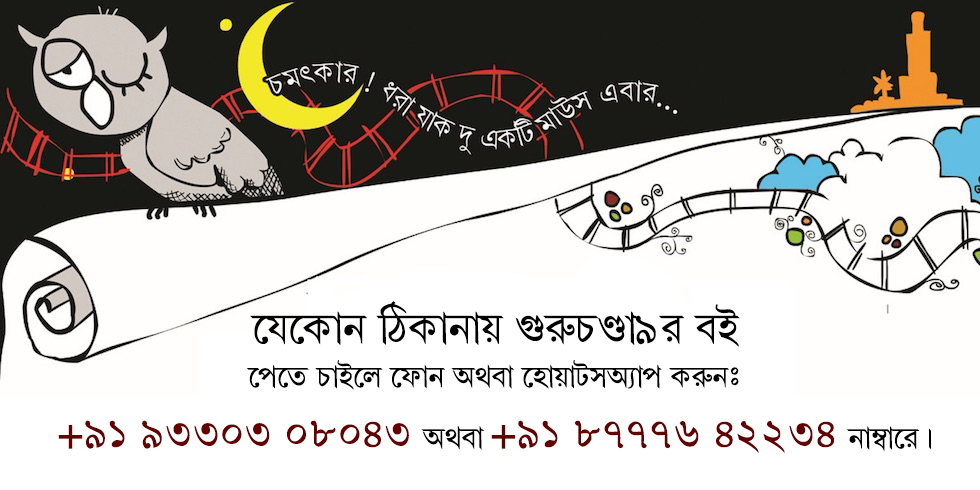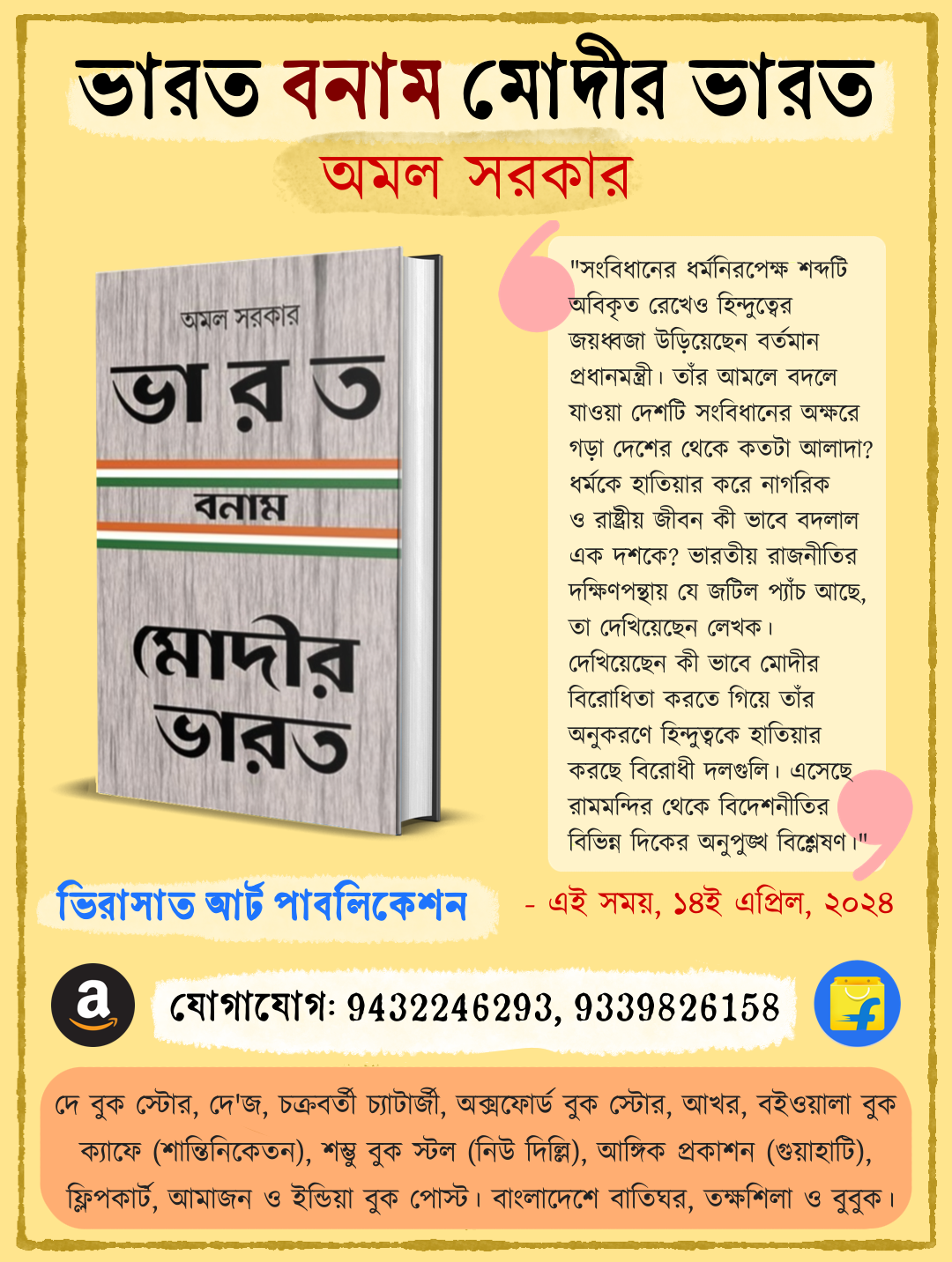- হরিদাস পাল প্রবন্ধ

-
মারাঠা ডিচ
Sukdeb Chatterjee লেখকের গ্রাহক হোন
প্রবন্ধ | ২৭ জুন ২০২৪ | ৬৮ বার পঠিত - মারাঠা ডিচ
শুকদেব চট্টোপাধ্যায়
অষ্টাদশ শতাব্দীর চারের দশক। দিল্লীর বাদশাহকে সন্তুষ্ট করে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ধীরে ধীরে ডানা মেলতে শুরু করেছে। কোলকাতা তাদের বড়ই পছন্দের শহর। কোলকাতাকে কেন্দ্র করেই তারা তখন আগামী দিনের স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু একটা উৎপাত তাদের শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। শুধু তারাই নয়, কোলকাতার বিত্তশালী নেটিভরাও যার পর নাই চিন্তিত। যদিও সেই উৎপাতের আঁচ তখনও কোলকাতার কোন মানুষের গায়ে লাগেনি, কিন্তু লাগতে কতক্ষণ!
বাংলার মানুষের তখন বড়ই দুঃসময়। আতঙ্কে আর ভয়ে দিন কাটে, বিশেষ করে গঙ্গার পশ্চিম পারের গ্রাম বাংলার মানুষদের। সব সময়ই একটা কি হয় কি হয় ভাব, এই বোধহয় তারা হানা দিল। দেখলে তো কথাই নেই, নাম শুনলেও লোকে আঁতকে ওঠে। এই হানাদারেরা কাছেপিঠের কেউ নয়, আসত সুদূর নাগপুর থেকে। এক সময়ে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল লুঠতরাজপ্রিয় মারাঠি বর্গিরা। বর্গিরা ছিল মারাঠি ধনগর জাতীয় অশ্বারোহী সেনা। অত্যাচারের নিরিখে শোলের গব্বর সিং এদের কাছে শিশু। পৌনে দুশ বছর আগের ভয় আজও ছেলে ভুলান ছড়া হয়ে মায়েদের মুখে মুখে ঘোরে।
খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে
ধান ফুরোলো পান ফুরোলো খাজনার উপায় কি?
আর কটা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি।
১৮৪১ থেকে টানা নয় দশ বছর এই বর্গি নামে কুখ্যাত মারাঠি তস্করেরা ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে নির্বিচারে লুঠতরাজ এবং হত্যা লীলা চালিয়ে গেছে। কবি গঙ্গারাম দত্তের ‘মহারাষ্ট্র পুরাণ’এ এই ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে।
রঘু(রাজা) আজ্ঞা দিলা(দিলেন) ভাস্করে।
তৎপর করিয়া চৌথাই আনি দিবা মোরে।।
রাজার আদেশ পাইয়া ভাস্কর চলিল ধাইয়া
সন্য সঙ্গে করিয়া সাজন।
ডঙ্কা নাগারা কত নীসান চলে সত সত
সন্য মধ্যে বাজিছে বাজন।
মহাশ্বেতা দেবীর ‘আঁধার মানিক’ উপন্যাসে বর্গিদের অত্যাচারের ফলে রাঢ় এবং গঙ্গার পশ্চিম অঞ্চলের মানুষেরা কিভাবে সর্বহারা হয়ে কাতারে কাতারে অন্যত্র পালাতে বাধ্য হয়েছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। অনেক অত্যাচারী হানাদারদের মত নিষ্ঠুরতার বিচারে বর্গিদের জন্যও সমকালীন ভারতের ইতিহাসে কিছুটা জায়গা সংরক্ষিত আছে, তবে বর্গিদের এই হানাদারির পিছনেও একটা ইতিহাস আছে। ছোট্ট করে জেনে নেওয়া যাক কি সেই পটভূমি যা তাদের প্রভাবিত, প্ররোচিত এবং প্রলোভিত করেছিল এই অঞ্চলপানে ধেয়ে আসতে।
সরফরাজ খানকে পরাজিত এবং হত্যা করে ১৭৪০ সালে আলিবর্দি খান বাংলার নবাব হন। সরফরাজের শ্যালক রুস্তম জং সেই সময় ছিলেন ওড়িশার ‘নায়েব নাজিম’ বা উপশাসক। রুস্তম তাঁকে মানতে অস্বীকার করলে বালাসোরের কাছে ফলওয়াইয়ের যুদ্ধে তাকে পরাস্ত করে আলিবর্দি নিজের ভাইপোকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। রুস্তম হেরে গেলেও হারিয়ে যায়নি। সাহায্যের আবেদন নিয়ে পৌঁছয় নাগপুরের মারাঠা শাসক রঘুজি ভোঁসলের দরবারে। মারাঠা সৈনের সাহায্যে রুস্তম ওড়িশা পুনর্দখল করে, যদিও অল্প সময়ের মধ্যেই আলিবর্দি ওড়িশায় এসে আবার রুস্তমকে পরাজিত করেন। সেই সময় অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়া রঘুজির কাছে রুস্তম ছিল উপলক্ষ মাত্র, আসল উদ্দেশ্য ছিল এই শস্য শ্যামলা অঞ্চলের সম্পদ লুঠ করা। এই অঞ্চল থেকে তাদের কাছে কোন চৌথ যেত না, সেটিও ছিল ক্ষোভের অন্যতম কারণ। ১৭৪২ সালে প্রচুর সৈন্যসামন্ত সাথে নিয়ে সেনাপতি ভাস্কর পন্ডিত বাংলা অভিমুখে রওনা দেয়। নবাব যখন বিদ্রোহ দমন করে কটক থেকে ফিরছেন তখন তিনি খবর পান যে মারাঠা বাহিনী পাচেটের মধ্যে দিয়ে বাংলায় প্রবেশ করছে। আলিবর্দি মারাঠাদের প্রতিহত করতে তৎক্ষণাৎ বর্ধমানের দিকে ধাবিত হলেন। নবাব পৌছবার আগেই মারাঠারা দ্রুত অন্য পথে বর্ধমান পৌঁছে লুঠ তরাজ করে চারিদিকে আগুন লাগিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ে।
এইভাবেই অত্যাচার ও লুন্ঠন চলতে থাকে বছরের পর বছর। আলিবর্দি সবরকম ভাবে চেষ্টা করেও এদের সাথে এঁটে উঠতে পারেননি, কারণ এরা সম্মুখ সমরে কমই আসত। গেরিলা কায়দায় হিট অ্যান্ড রান পদ্ধতিতে ওরা হামলা করত। দ্রুতগামী ঘোড়সওয়ারেরা ঝড়ের মত হঠাৎ আসত, লক্ষ পূর্ণ করে নিমেষে উধাও হয়ে যেত। এছাড়া আলিবর্দির মুস্তাফা, মীর হাবিবের মত কিছু অন্দরের শত্রু ছিল যারা মারাঠাদের কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছিল। কিছুতেই কিছু করতে না পেরে নবাব ছলের আশ্রয় নেন। আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে ভাস্কর পন্ডিতকে নিজের এলাকায় আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের সদলবলে হত্যা করেন। উৎপাতে সাময়িক ছেদ পড়লেও অচিরেই তা আবার শুরু হয়। নয় দশ বছরে বর্গিরা ছবার হানা দিয়েছিল। শেষমেশ ১৭৫১ সালে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা চৌথের প্রতিশ্রুতি এবং ওড়িশার অধিকার রঘুজিকে ছেড়ে দিয়ে বৃদ্ধ আলিবর্দি এই দীর্ঘমেয়াদি সন্ত্রাসে ইতি টানার চেষ্টা করেন। তুলনায় কম হলেও এর পরেও কয়েকবার বর্গির হাঙ্গামা হয়েছে। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রমশ ক্ষমতাশালী হতে থাকে। নিজেদের ক্ষমতা এবং স্থানীয় জমিদারদের সাহায্যে ধীরে ধীরে তারা বর্গিদের উৎপাতে দাঁড়ি টানতে সক্ষম হয়।
গঙ্গারাম দত্ত বর্গিদের ভয়াবহ অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন —
‘মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।/
সোনা রুপা লুঠে নেয়, আর সব ছাড়া।।
কারু হাত কাটে, কারু নাক কান।
একি চোটে কারু বধয়ে পরাণ।/
ভাল ভাল স্ত্রীলোক যত ধরিয়া লইয়া যায়।/
অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলায়।।/
এক জনে ছাড়ে তবে আর জনা ধরে।
তারা ত্রাহি শব্দ করে।।’’ (মহারাষ্ট্র পুরাণ)
ঝাড়গ্রামের কুলটিকরি থেকে পশ্চিম মেদিনিপুরের কেশিয়াড়ি যাওয়ার পথে পড়বে কিয়ারচাঁদ। এই এলাকায় নানা আকৃতির প্রচুর পাথর মাটিতে পোঁতা আছে। এখানকার জনশ্রুতি বলে বর্গিদের ভয়ে রাতে ওইসব পাথরের গায়ে মশাল বেঁধে দেওয়া হত যাতে দূর থেকে মনে হয় সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে। বর্গিদের অত্যাচার নিয়ে এমন অসংখ্য লোকগাথা আছে। লুঠেরারা মূলত ঘোড়সওয়ার হওয়ার জন্য নদীপথ পরিহার করার চেষ্টা করত। তাই গঙ্গার পূর্ব পারে তারা হানা দেয়নি বললেই চলে।
ফিরে আসি অষ্টাদশ শতকের চল্লিশের দশকের গোড়ার কোলকাতার কথায়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তখন সবে শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ করেছে। পলাশীর যুদ্ধে প্রদর্শিত বিক্রম তখন ভবিষ্যতের গর্ভে। শক্তি এবং প্রতিপত্তি যেখানে সীমিত সেখানে বিপদের সামান্যতম সম্ভাবনাতেও কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়াটাই স্বাভাবিক। লালদিঘিতে একটা কেল্লা করা হয়েছে বটে, তবে মাটির গাঁথনির নড়বড়ে সে কেল্লায় কারো তেমন ভরসা নেই। কোম্পানির মাতব্বরেরা চারজন সাহেবের একটা কমিটি তৈরি করলেন শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার হাল হকিকত জানার জন্য। কমিটির লোকজন শহরময় বিস্তর ঘোরাঘুরি করে এসে জানাল যে হাল মোটেই ভাল নয়। যা সৈন্য আছে তা দিয়ে বর্গির হাত থেকে শহরকে রক্ষা করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। এতএব আবার আলোচনা শুরু হল। বিত্তবান নেটিভরা যারপরনাই চিন্তিত, হামলা হলে সম্পদের লোভে প্রথম কোপ তাদের ওপরেই পড়বে। হানাদারেরা হাঁড়ির সব খবর রাখে, মুর্শিদাবাদে তো জগৎ শেঠের প্রচুর ধন সম্পত্তি লুঠে নিয়ে গেছে। প্রতিরক্ষা খাতে গঙ্গার ধারে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হল। বাগবাজার ঘাটে ‘টাইগ্রেস’ নামে একটা জাহাজ দাঁড় করান হল। পেরিন্স পয়েন্টে এসে দাঁড়াল আর একটা জাহাজ। গুটিকয়েক কামান ছড়িয়ে ছিটিয়ে সাত জায়গায় বসান হল। কিন্তু হলে হবে কি, সবই তো শহরের পশ্চিম দিকে। হুগলী নদি থাকায় পশ্চিম দিক থেকে বিপদের সম্ভাবনা অনেক কম। কিন্তু পূর্ব দিকে তো কিছুই নেই, একেবারে অবারিত দ্বার।
ওদিকে সাহেবদের তরফে নিত্য নতুন নতুন পরিকল্পনা হচ্ছে, বাতিল হচ্ছে, আবার হচ্ছে। সমস্যার কথা জানিয়ে শহরে প্রতিরক্ষা বাড়ানোর আবেদন বিলেতে গেল। সব দিক রেখে উত্তর এল। দিল্লীর বাদশা, বাংলার নবাব আর স্থানীয় মানুষের বিরাগভাজন না হয়ে প্রতিরক্ষার স্বার্থে যা করণীয় তা করা যেতে পারে। তবে খরচ যেন খুব বেশি না হয়। কিন্তু কি করণীয় সাহেবরা সেটাই স্থির করে উঠতে পারছে না। কিন্তু ব্যাপারটা আর তো ফেলে রাখা যায় না। কোলকাতার নেটিভরা আর অন্যের ভরসায় না থেকে আত্মরক্ষার্থে কি করনীয় তা ঠিক করার জন্য সভা ডাকল। সভায় ঠিক হল সারা শহর ঘিরে কাটা হবে ৪২ গজ চওড়া খাদ। উত্তরে বাগবাজার (পেরিন্স পয়েন্ট) থেকে শুরু করে পূর্ব দিক ঘুরে দক্ষিণে গোবিন্দপুর পর্যন্ত সাত মাইল লম্বা হবে এই খাদ। বাগবাজার থেকে একেবারে সোজা পূর্বদিক বরাবর খাদ কাটা হয়নি। হালসিবাগানের কাছে একটু উত্তর দিকে বাঁকান হয়েছিল, কারণ সেখানে ছিল গোবিন্দ মিত্র আর উমিচাঁদের বাগান বাড়ি। ওই জায়গায় আজ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বাড়ি। সিদ্ধান্ত সাহেবদের জানান হল। সাহেবরা আবার নবাবকে জানাল অনুমতির জন্য। অনুমতি পাওয়া গেল। কাজ শুরুর আগে কোম্পানি জানিয়ে দিল যে খরচাপাতি যা হবে তা নেটিভদেরই বইতে হবে। কোম্পানি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা আগাম নেওয়া হল। জামিনদার রইল শেঠেদের বাড়ির বৈষ্ণবচরণ, রামকৃষ্ণ, রাসবিহারী আর উমিচাঁদ। ১৭৪২ সালে কোদাল, বেলচা, নিয়ে কাজে লাগল শয়ে শয়ে মানুষ। Charles Stewart তাঁর History of Bengal (1813) এ লিখেছেন, “It (the ditch) also ran along the present Circular Road. It is said 600 coolies and 300 Europeans were engaged in this work, the earth excavated being used to form a road on the inward or town side.”
ছয় মাস অবিরাম কাজ চলার পর খবর পাওয়া গেল যে নবাব সমস্যার কিছু একটা সুরাহা করেছেন। ফলে খননকার্য ওখানেই শেষ। ইতিমধ্যে তিন মাইল খাদ কাটা হয়ে গেছে। বর্তমান এন্টালি অঞ্চল পর্যন্ত খাদ কাটা হয়েছিল, যদিও এ নিয়ে ভিন্নমত আছে। বাংলায় বর্গির হানা এরপরও অনেকবারই হয়েছে কিন্তু কোলকাতা অভিমুখে তারা কখনও আসেনি। গঙ্গা রক্ষা করেছে কোলকাতার মানুষদের। ভাগ্য ভাল যে তারা আসেনি। যদি আসত তাহলে এই খাদ যে কোন বাধাই হত না, তা বোঝা গিয়েছিল নবাব সিরাজউদৌলার কোলকাতা আক্রমণের সময়। কোন কাজে লাগল না অথচ ওই খাদের কারণে তখনকার কোলকাতার লোকেদের নাম হয়ে গেল ‘ডিচার’। বহু বছর ওই অবস্থায় পড়ে রইল অর্ধসমাপ্ত খাদ। ১৭৯৯ সালে লর্ড ওয়েলেসলির নির্দেশে ওই খাদ বুজিয়ে তৈরি হল কোলকাতার অন্যতম বৃহৎ রাস্তা, সার্কুলার রোড। পাল লেন আর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের মাঝামাঝি খাদের একটা টুকরো অনেকদিন পর্যন্ত অক্ষত ছিল, আজ সেটাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে বাগবাজারে আজও রয়ে গেছে একফালি রাস্তা, মারাঠা ডিচ লেন।
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত। - আরও পড়ুনপক্ষীর দল - Sukdeb Chatterjeeআরও পড়ুনদিলদার নগর ৪ - Aditi Dasguptaআরও পড়ুনপরমাত্মার লীলা! - Debasis Sarkarআরও পড়ুনধ্যান ও স্নায়ুবিজ্ঞান - অরিনআরও পড়ুনপ্রতিভা বনাম ভাগ্য - সুকান্ত ঘোষআরও পড়ুনবৈঠকি আড্ডায় ১৯ - হীরেন সিংহরায়
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... aranya, ভয়াবহ কান্ড করল এরা, বিচিপি লাও দেশ বাঁচাও)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... r2h, :-), বিপ্লব রহমান)
(লিখছেন... Argha Bagchi, অনুপ, aranya)
(লিখছেন... কৌতূহল, kk, kk)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... সোমনাথ, :-), বিপ্লব রহমান)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... রমিত চট্টোপাধ্যায়, দ, Suvasri Roy)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... রঞ্জন , kk, হীরেন সিংহরায়)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... আবার আলাদা করে কপালভাতি কেন?, syandi)
(লিখছেন... প্রাণায়াম, Ranjan Roy, nb)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Ranjan Roy)
(লিখছেন... অরিন , অরিন , &/)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : [email protected] ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত