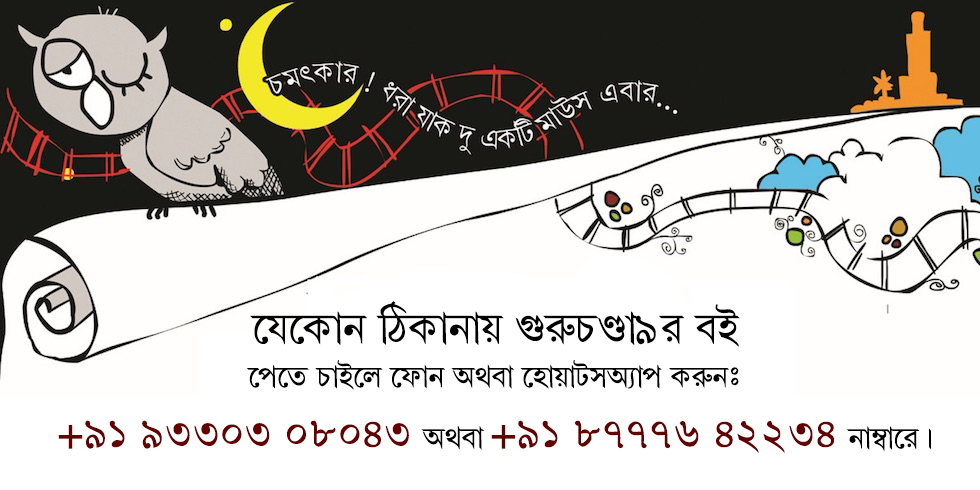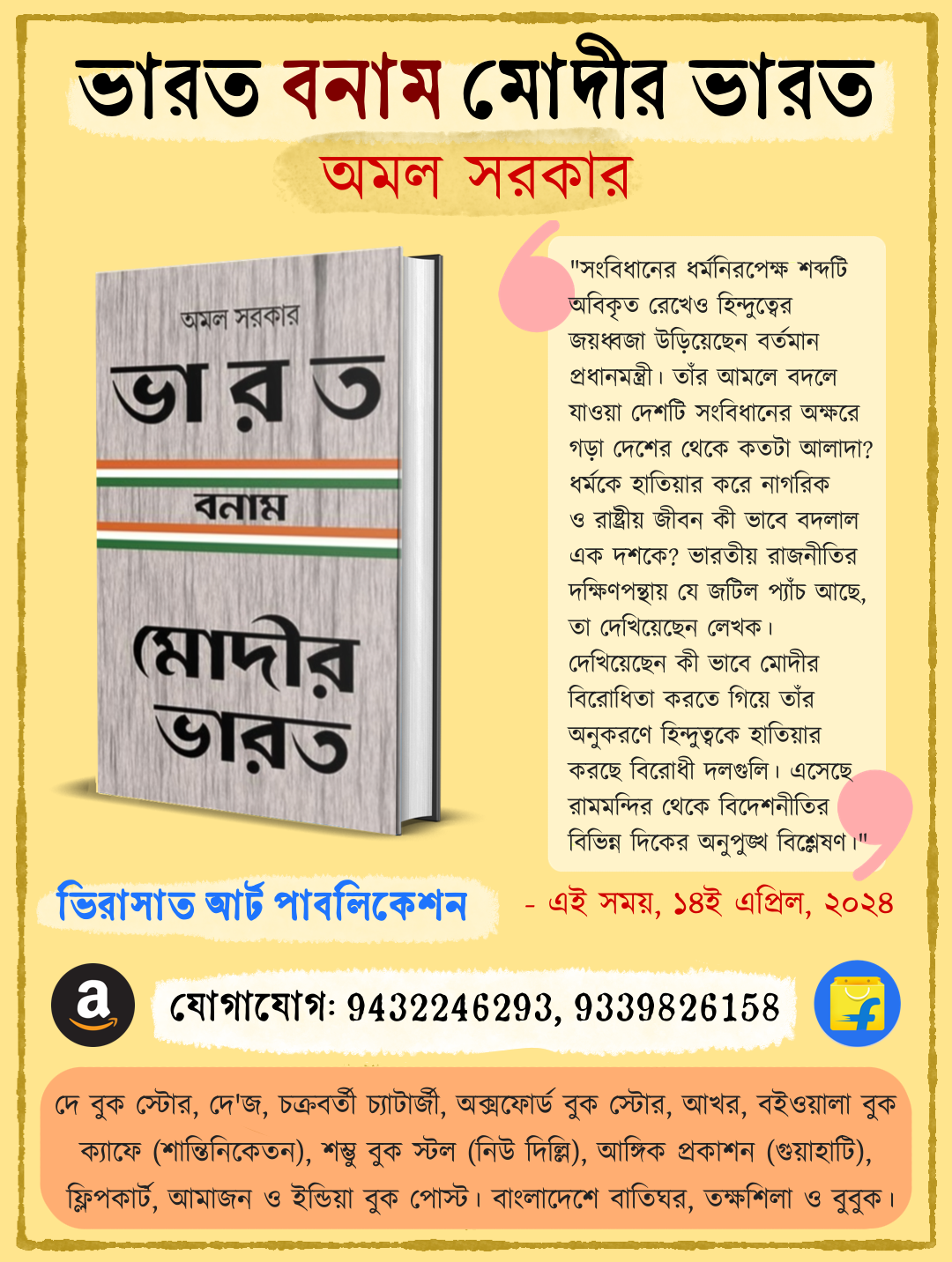- হরিদাস পাল ব্লগ

-
ধর্ম, মৌলবাদ ও আমাদের ভবিষ্যৎ : কিছু যুক্তিবাদী চর্চা
Debasis Bhattacharya লেখকের গ্রাহক হোন
ব্লগ | ২৫ ডিসেম্বর ২০২২ | ৫০৮৩৯ বার পঠিত | রেটিং ৪.৫ (২ জন) - ইসলাম সম্পর্কে আলাদা করে দু-চার কথা
মৌলবাদ নিয়ে এই ধরনের একটা লেখায় যদি কেউ ঘোষণা করেন যে, এইবার ইসলাম নিয়ে আলাদা করে কিছু বলা হবে, তখন পাঠকের সে নিয়ে একটা প্রত্যাশা তৈরি হতে পারে। কাজেই, এখানে গোড়াতেই সে ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে বলে রাখা দরকার, না হলে পাঠক হয়ত বিভ্রান্ত ও ক্ষুব্ধ হবেন। সম্ভাব্য প্রত্যাশাটি এই রকম যে, মৌলবাদের স্বরূপ নিয়ে যখন চর্চা হচ্ছে, এবং তার মধ্যেই আলাদা করে ইসলাম নিয়ে চর্চার ঘোষণা হচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই দেশে দেশে ইসলামীয় মৌলবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ নিয়ে ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যাবে এখানে, বিভিন্ন স্থান-কালে তার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ বিশেষ বৈচিত্র্যের উল্লেখ পাওয়া যাবে, এবং অন্যান্য ধর্মের মৌলবাদের সঙ্গে তার মিল ও অমিল এবং তার কার্যকারণ ইত্যাদি বিষয়ক অনুসন্ধান ও তার ফলাফলও পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, এখানে তা করতে পারলে ভালই হত, কিন্তু তার উপায় নেই। সেটা করতে গেলে আগে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধর্মের মৌলবাদের কার্যকলাপ নিয়ে একটা সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত আলোচনা সেরে রাখতে হত, তবেই তার প্রেক্ষিতে ইসলামীয় মৌলবাদের বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে পারত। দুঃখের বিষয়, সে পরিসর এখানে ছিল না, এখানে তো এতক্ষণ মৌলবাদ নিয়ে শুধু কতকগুলো অতি সাধারণ কথাই বলেছি। বলে রাখা দরকার, এখানে আমি সরাসরি সেইসব নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করব না, যদিও যা আসলে বলব তার মধ্যে এ বিষয়ে আমার মতামত ও চিন্তাভাবনারও কিছু ইঙ্গিত হয়ত মিলবে। এখানে আমি মূলত কথা বলব ইসলাম ধর্ম ও সংশ্লিষ্ট মৌলবাদ প্রসঙ্গে আমাদের সমাজের মূলস্রোত ধ্যানধারণা নিয়ে, এবং তার ঠিক-বেঠিক নিয়েও। এ নিয়ে কথা বলব কারণ, আমার ধারণা, ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে যাঁরা ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়তে চান, তাঁদের এ বিষয়টি এড়িয়ে যাবার কোনও উপায় নেই।
ওপরে বলেছি, যাঁরা ধার্মিক নন বরঞ্চ ‘ধর্ম’ জিনিসটার সমালোচক, তাঁদের মধ্যে ইসলাম নিয়ে দু রকমের ভাবনা বেশ পরিচিত। অনেকে মনে করেন, এই ‘মৌলবাদ’ সংক্রান্ত সমস্যাটা আসলে শুধুই ইসলামের সমস্যা, আর কারুরই নয় --- ধর্মের নামে ফতোয়াবাজি আর মারদাঙ্গা মূলত মুসলমানেরাই করছে। অন্যদের যদি আদৌ কিছু সমস্যা থেকেও থাকে, তো সেটা শুধু ইসলামি জঙ্গিপনার প্রতিক্রিয়া মাত্র। আবার, এ অবস্থানটি অন্য অনেকের দুশ্চিন্তারও কারণ। ইসলামি জঙ্গিপনার বিপদ স্বীকার করেও তাঁরা মনে করেন যে, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নির্দোষ ও নিরীহ আম মুসলমানের ঢালাও খলনায়কীকরণ হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে ছড়ানো হচ্ছে ঘৃণা বিদ্বেষ ও হিংস্রতা। প্রথম ভাবনাটি ভুল, কেন তার কিছু ব্যাখ্যা নিচে আছে।
আর ওই দ্বিতীয় প্রকারের যে দুশ্চিন্তা, আমি এবং আমার মত অনেকেই যার শরিক, তার এক প্রতিনিধি-স্থানীয় দৃষ্টান্ত আমার হাতে এসেছে কয়েকদিন আগে, আমার এক তরুণ বন্ধুর সাথে ফেসবুকীয় কথোপকথনে। তিনি কে, সেটা এখানে প্রাসঙ্গিক না, কিন্তু তিনি আমাকে যে সব প্রশ্ন করেছেন তা বোধহয় অতিশয় প্রাসঙ্গিক। এখানে সেগুলো হুবহু উদ্ধৃত করলে হয়ত আমাদের আলোচ্য প্রশ্নগুলোকে সুনির্দিষ্ট আকার দিতে সুবিধে হবে। অবশ্য, এখানে উদ্ধৃত প্রত্যেকটি প্রশ্নগুলোর সুনির্দিষ্ট ও নিষ্পত্তিমূলক উত্তর দেওয়া এ লেখার উদ্দেশ্য ততটা নয়, যতটা হল মূল প্রশ্নগুলোকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে সমস্যাটাকে আরেকটু স্পষ্ট করে তোলা। নিচে রইল সেই তরুণ বন্ধুর দুশ্চিন্তা-জারিত প্রশ্নগুলো।
“দাদা,
একটা বিষয় একটু বিস্তারিত জানতে চাই আপনার কাছে। আপনি যদি সময় করে একটু ডিটেইলসে উত্তর দেন, খুব উপকৃত হই। অনেকদিনই এটা আপনাকে জিজ্ঞেস করব করব ভেবেছি, কিন্তু করা হয়নি, কারণ বিষয়টা একটু সেন্সেটিভ, আর প্রশ্নটা একটু বিস্তারে করতে হবে।
ছোটবেলা থেকেই (ক্লাস ওয়ান থেকে) আমি দেখে এসছি, আমার পরিমণ্ডলে শুধুমাত্র ধর্মে মুসলিম হওয়ার জন্য মানুষকে সন্দেহের চোখে, বিদ্বেষের চোখে দেখা হয়। ক্রিকেটে পাকিস্তান জিতলে "কীরে, খুব আনন্দ বল!" বলে টন্ট কাটা হয়, কেবল নাম দেখে বাড়িভাড়া দিতে অস্বীকার করা হয়, এমনকি মুসলিম ছাত্র ক্লাসে ভাল রেজাল্ট করলেও "আশ্রম থেকে শেষে মুসলিম ফার্স্ট হবে" এরকম কথা খোদ টিচারের মুখেই শুনেছি। আমি ঘটনাক্রমে মুসলিম পরিবারে জন্মাইনি, কিন্তু একদম ছোটবেলা থেকেই আমার মুসলিম বন্ধু বা প্রতিবেশীদের এভাবে সামাজিক হেট ক্যাম্পেনিং এর মুখে পড়াটা ভীষণ দুঃখজনক লাগে। এই খারাপ লাগাটা ক্লাস ওয়ান থেকেই শুরু হয়েছিল, তো তখন তো আমি ধর্ম ভাল না খারাপ, যুক্তিবাদ ভাল না খারাপ, এতকিছু তো বুঝতাম না।
এখন মুসলিমবিদ্বেষকে যারা জাস্টিফাই করে, তাদের থেকে যে যুক্তিগুলো উঠে আসে, সেগুলো -
১) আর কোন ধর্মে আইসিস, তালিবান, বোকোহারামের মত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আছে?
২) "ওরা" (মুসলিমরা) সংখ্যায় বাড়লেই ইসলামিক রাষ্ট্র চায়, সংখ্যায় কমলেই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চায়।
৩) সব ধর্মে সংস্কার হয়েছে, কিন্তু "ওরা" এখনও মধ্যযুগেই পড়ে আছে।
৪) সব ধর্মেই বহুবিবাহ বন্ধ হয়েছে, কিন্তু "ওদের ধর্মে" বহুবিবাহ আজও জায়েজ, ওদের ধর্মে নারীর অবস্থা সবচাইতে খারাপ।
৫) "ওরা" নিজেদের বাঙালি মনে করে না, মননে চিন্তনে আরব, ওদের কাছে ধর্মই সব।
৬) ধর্মের নামে মানুষ হত্যা "ওদের ধর্মের মত কোন ধর্মই করেনি।"
৭) "ওদের" বাড়াবাড়ির জন্যই বিজেপির মত দলের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ, হিন্দু মৌলবাদ ইসলামিক মৌলবাদের প্রতিক্রিয়ার ফসল।
ইত্যাদি ইত্যাদি। আপাতত এই কটাই মনে পড়ছে।
এখন আমার প্রশ্ন
১) মুসলিমবিদ্বেষীদের এই দাবিগুলো কি তথ্যগতভাবে সত্যি?
২) সত্যিই কি ইসলাম আর পাঁচটা ধর্মের থেকে ব্যতিক্রমী ভায়োলেন্ট? এখন তো যুক্তি, তথ্য, পরিসংখ্যানের বিভিন্ন মেথডলজি দিয়ে অনেক বিষয় কম্পারেটিভ স্টাডি করা যায়। "ইসলাম অন্য পাঁচটা ধর্মের থেকে ভায়োলেন্ট" - এই বিষয়টা কি যুক্তি, তথ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায়? মানে আমার প্রশ্ন, দাবিটার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু?
৩) ধরে নিলাম, ইসলাম সবচাইতে ভায়োলেন্ট ধর্ম। কিন্তু তাতে করেই কি মুসলিমবিদ্বেষ জায়েজ হয়ে যায়?
৪) একজন নাস্তিক হিসাবে মুসলিম সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার হরণ করা হলে তার প্রতিবাদ করা কি অন্যায়?
৫) হিন্দু মৌলবাদ কি সত্যিই ইসলামিক মৌলবাদের প্রতিক্রিয়ার ফসল? ইসলামিক মৌলবাদ না থাকলে সত্যিই কি হিন্দু মৌলবাদ বলে কিছু থাকত না?
৬) আইসিস বা তালিবানের মত মুসলিম লিগ বা বর্তমানে মিমকে কি মৌলবাদী বলা যায়? নাকি "সাম্প্রদায়িক, কিন্তু মৌলবাদী নয়"-এমনটা বলা উচিত?
আমার প্রশ্ন করার মূল কারণটা কিন্তু কোনভাবেই ইসলামকে ডিফেন্ড করা বা তার ভয়াবহতাকে লঘু করা নয়। আমিও ধর্মহীন সমাজের স্বপ্ন দেখি, সব ধর্মের মত ইসলামের অবসানও আশা করি।
কিন্তু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত স্তরে ইসলামের সমালোচনাটা যেভাবে হয়, তার টোনটা ঠিক যুক্তিবাদের নয়, টোনটা বিদ্বেষের। এখন রিলিজিয়াস ক্রিটিসিজমকে ঢাল করে বুঝে বা না বুঝে অনেক প্রগতিশীল মানুষও বিদ্বেষের টোন ব্যবহার করছেন। এটা খুব আশঙ্কার।”
এখন, এই প্রশ্নগুলোর প্রত্যেকটাকে আলাদা করে উত্তর দেবার চেষ্টা না করে বরং এ প্রসঙ্গে কতকগুলো সাধারণ কথা ভেবেচিন্তে দেখি। তাতে করে সমাধান না আসুক, অন্তত সমস্যাটার চেহারাটা আরেকটু স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে পারে কিনা, দেখা যাক। হতে পারে, ভাবতে গিয়ে হয়ত ওপরের দু-একটা প্রশ্ন শেষতক বাদই পড়ে গেল, বা উল্টোভাবে, যে প্রশ্ন এখানে নেই তেমন কিছু এসে কথার মধ্যে ঢুকে পড়ল।
প্রথমেই বলা দরকার, অনেকে আধুনিক মৌলবাদী উত্থানকে মুসলমান জঙ্গি উত্থানের সঙ্গে এক করে দেখেন, যা মোটেই সঠিক নয়। বর্তমান পৃথিবীর প্রধান ধর্মীয় ধারাগুলোর সবকটির মধ্যেই মৌলবাদী উত্থান ঘটেছে, বিভিন্ন মাত্রা, ভঙ্গী ও ধরনে। আমেরিকায় খ্রিস্টান মৌলবাদীদের কথা আমরা জানি, জানি ইসরায়েলের ইহুদী মৌলবাদীদের কথা, জানি ভারতের হিন্দু মৌলবাদীদের কথা, এবং জানি এই ভারতেই আশির দশকে তেড়েফুঁড়ে ওঠা শিখ মৌলবাদীদের কথাও --- যাদের হাতে ভারতের এক প্রধানমন্ত্রী নিহত হয়েছিলেন। ‘অহিংসার ধর্ম’ বলে কথিত বৌদ্ধধর্মও এ প্রবণতার বাইরে নয় মোটেই। থাইল্যান্ড, বর্মা ও শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ধর্মের তরফেও জঙ্গি প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। আজ অনেকেরই হয়ত আর মনে নেই, দুহাজার এক সালের কুখ্যাত ‘নাইন ইলেভেন’-এর ঘটনার আগে পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ধর্মীয় নাশকতার ঘটনা বলে ধরা হত উনিশশো পঁচানব্বই সালের দুটি ঘটনাকে। তার একটি ঘটেছিল আমেরিকার ওকলাহোমা সিটি-র ‘ট্রেড সেন্টার’-এ, যাতে বিস্ফোরক-ভর্তি ট্রাক দিয়ে ওই ভবনটিতে ধাক্কা মেরে প্রায় দেড়শো লোকের প্রাণনাশ করা হয়েছিল, এবং সেটা ঘটিয়েছিল কতিপয় খ্রিস্টান মৌলবাদী। অন্যটি ঘটেছিল জাপানে, যেখানে পাতাল রেলের সুড়ঙ্গে বিষাক্ত সারিন গ্যাসের কৌটো ফাটিয়ে দেওয়া হয়, তাতে বিষাক্ত গ্যাসে সরাসরি যত না মারা যায় তার চেয়ে অনেক বেশি লোক মারা যায় এবং গুরুতরভাবে জখম হয় সুড়ঙ্গের ভেতরে আতঙ্কগ্রস্তদের দৌড়োদৌড়িতে পদপিষ্ট হয়ে --- এবং সেটা ঘটিয়েছিল কট্টরপন্থী বৌদ্ধদের একটি ক্ষুদ্র উপগোষ্ঠী। আমরা বৌদ্ধধর্মটা অন্তত অহিংস বলে জানতাম, তাই না? তার দু বছর আগে উনিশশো তিরানব্বই সালে ভারতে সংঘটিত কুখ্যাত ‘বম্বে বিস্ফোরণ’ অবশ্যই একটি বৃহৎ নাশকতা, এবং সেটা ঘটিয়েছিল মুসলমান জঙ্গিরাই। কিন্তু, মুসলমান মৌলবাদীদের বক্তব্য অনুযায়ী, সেটা ছিল তার এক বছর আগে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিক্রিয়া। বলা বাহুল্য, এই বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনাটিকেও আবার মুসলমানদের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া বলেই দেখানো হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেটা কোনও সাম্প্রতিক ‘অত্যাচার’-এর প্রতিক্রিয়া ছিল না। হিন্দু মৌলবাদীদের নিজেদের দাবি অনুযায়ীই, এটা নাকি মোগল সম্রাট বাবরের তরফে ঘটে যাওয়া পাঁচশ বছরের পুরোনো এক অন্যায়ের প্রতিকার মাত্র! এবং, এই বাবরি মসজিদের ধ্বংসও আবার এ দেশে ধর্মীয় নাশকতার প্রথম ঘটনা নয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও নয়। এ দেশে আজ পর্যন্ত ধর্মীয় নাশকতার সবচেয়ে বড় ঘটনা বলে যদি কোনও বিশেষ ঘটনাকে ধরতেই হয়, তো সেটা সম্ভবত উনিশশো চুরাশি সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে হত্যা করার ঘটনা। সেটা মুসলমানেরা ঘটায়নি, ঘটিয়েছিল শিখ মৌলবাদীরা।
ধর্মের সমালোচনা যে আধুনিক পৃথিবীর অন্যতম প্রধান কাজ, তাতে সন্দেহ নেই। সমালোচনা মানে সব ধর্মেরই সমালোচনা, ইসলামেরও। কিন্তু, ইসলাম ধর্মের সমালোচনায় একটি ভুল আমরা প্রায়শই করে থাকি। আমরা বলি, ইসলাম ধর্ম (এবং সেইহেতু ওই ধর্মাবলম্বীরাও) তো হিংস্র হবারই কথা, কারণ, ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্রে হিংসার উপাদান খুব বেশি আছে। হয়ত সত্যিই আছে, কিন্তু যুক্তিটা তা সত্ত্বেও ভুল, এবং দুটো দিক থেকেই ভুল। কারণ, প্রথমত, সব ধর্মশাস্ত্রেই হিংসার উপাদান কমবেশি আছে। এবং দ্বিতীয়ত, যে ধর্মের শাস্ত্রে হিংসার উপাদান কিছু কম আছে সে ধর্মগোষ্ঠীর মানুষের আচরণে হিংসা কম থাকবেই --- এ প্রত্যাশার ভিত্তিটাও বোধহয় খুব পোক্ত নয়।
হিংস্রতার বর্ণনা ও তার নৈতিক সমর্থন হিন্দু শাস্ত্রগুলোতে কোরানের চেয়ে কিছু কম নেই। কম নেই বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টেও, যদিও, হয়ত বা সত্যিই কিছু কম আছে নিউ টেস্টামেন্টে। আবার, শাস্ত্রগ্রন্থে হিংস্রতার বর্ণনা কম থাকলেই যে ধার্মিকেরা কিছু কম হিংস্র হবেন, এমন নিশ্চয়তাও পাওয়া কঠিন। যুদ্ধলিপ্সা, হত্যা এবং হিংস্রতায় যিনি প্রবাদপ্রতিম, সেই চেঙ্গিস খান কিন্তু মোটেই মুসলমান ছিলেন না, 'খান' পদবী দেখে যা-ই মনে হোক। খ্রিস্টানরা ষোড়শ-সপ্তদশ শতক জুড়ে আমেরিকাতে স্থানীয় অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যেভাবে হত্যালীলা চালিয়েছে নিউ টেস্টামেন্টের যাবতীয় ক্ষমার বাণী সত্ত্বেও, তা ইতিহাসে বিরল। মধ্যযুগের শেষে এবং আধুনিক যুগের গোড়ায় 'ক্ষমাশীল' খ্রিস্টানদের ডাইনি পোড়ানোর হিড়িক দেখে আতঙ্কে শিউরে ওঠেন না, এমন কেউই কি আছেন এ যুগে? 'ইসলামিক স্টেট' তার ঘোষিত 'বিধর্মীদের' হত্যা করে হত্যার উদ্দেশ্যেই, বা প্রতিশোধের উদ্দেশ্যে, এবং সেটা সারা জগতের লোককে ডেকে দেখানোর জন্যেও বটে। দেখ হে, আমরা কত ভয়ঙ্কর, কত বড় বীর, এই রকম একটা ভাব। কিন্তু মধ্যযুগের খ্রিস্টানরা ডাইনি মারত ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা দিয়ে, এবং যন্ত্রণা দেওয়াটাই সেখানে মূল উদ্দেশ্য, যাতে অকথ্য অত্যাচার করে তার মুখ থেকে অন্য আরেক ‘ডাইনি’-র নাম বার করে আনা যায়। এই কাজটির জন্য তারা বিচিত্র ও বীভৎস সব কলা-কৌশল ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছিল। কাজেই, বিশেষ একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর ধর্মান্ধতা ও ধর্মীয় হিংস্রতার সঙ্গে তার শাস্ত্রীয় অনুমোদনের একটা সহজ সরল সম্পর্ক ধরে নেওয়াটা বোধহয় সব সময় খুব নিরাপদ নয়।
মুসলমানদের হিংস্রতার মতই আরেকটি বাজে গল্প আছে মুসলমানদের জনসংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ে। মুসলমানদের হুহু করে বংশবৃদ্ধি হচ্ছে, এবং দ্রুত তারা হিন্দুদেরকে ছাপিয়ে গিয়ে গোটা দেশটাকে দখল করে ফেলবে, এই মিথ্যে আতঙ্কটা হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রচারের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু, বহু মানুষই যা সরলমনে বিশ্বাস করেন। এখানে বলে নেওয়া দরকার, মুসলিম জনসংখ্যা যে বাড়ছে এবং তার হার যে হিন্দুদের চেয়ে এখন পর্যন্ত কিছু বেশিই বটে, এটা কিন্তু মিথ্যে নয়। মিথ্যে হল এই প্রচারটা যে, এইভাবে বাড়তে বাড়তে হিন্দুদের চেয়ে তাদের সংখ্যা নাকি বেশি হয়ে যাবে, এবং তারাই দেশটাকে গ্রাস করে ফেলবে। আসলে ঘটনা হল, সব ধর্মের জনসংখ্যাই বাড়ছে, এবং সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার সব দেশেই সংখ্যাগুরুদের চেয়ে সামান্য একটু বেশি হয়, যদি সেখানে সংখ্যালঘু নিধন না চলে, এবং বিশেষত যদি সে সংখ্যালঘুরা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া হয়। জনসংখ্যাবৃদ্ধির আসল যোগটা ধর্মের সঙ্গে নয়, অর্থনীতির সঙ্গে। হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যেও গরিবদের জনসংখ্যাবৃদ্ধি যদি আলাদা করে হিসেব করা হয় তো দেখা যাবে যে তা সচ্ছল হিন্দুদের চেয়ে অনেক বেশি। সম্পন্নরা ভাল রোজগার করতে চায়, ভালভাবে থাকতে চায়, এবং সন্তানের জীবনযাপনও যাতে সে রকমই হয়, সে ব্যবস্থা করতে চায়। তারা জানে যে সেটা করতে গেলে সন্তানকে উচ্চমানের শিক্ষাদীক্ষা দেওয়া দরকার, তার পেছনে ভাল করে যত্ন ও খরচাপাতি করা দরকার, এবং সেটা করার ক্ষমতাও তাদের আছে। ছেলেপুলে বেশি হলে তা সম্ভব নয়, এবং তাতে করে বাচ্চার মায়ের স্বাস্থ্যের বারোটা বাজবে, মা ঘরের বাইরে গিয়ে পেশাগত কাজকর্ম করে অর্থ উপার্জনও করতে পারবে না। ফলে, তারা বেশি সন্তান একদমই চায় না। উল্টোদিকে, গরিবরা এত কথা জানেও না আর তাদের সে ক্ষমতাও নেই। ফলে তারা যত বেশি সম্ভব সন্তান চায়, সেটা মায়ের স্বাস্থ্যহানি ও মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে হলেও। গরিবরা জানে তাদের সন্তান দুধেভাতে থাকবে না, এবং শেষপর্যন্ত কোনও শ্রমসাধ্য কাজেই যোগ দেবে যাতে শিক্ষা বা 'স্কিল' সেভাবে লাগে না। ফলে, সন্তানের সংখ্যা বেশি হলে দুরবস্থা আর অযত্নের মধ্যেও হয়ত রোগভোগ মৃত্যু এড়িয়ে কেউ কেউ টিঁকে যাবে, আর পরিশ্রম করে পরিবারের আয় বাড়াতে পারবে, যৎসামান্য হলেও। অথচ এদেরই যখন অর্থনৈতিক উন্নতি হবে, তখন এরা মেয়েদেরকে পড়াশোনা শেখাতে চাইবে, ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সন্তানকে কেরানি-আমলা-ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-উকিল এইসব বানাতে চাইবে, ফলে স্বল্পসংখ্যক সন্তান চাইবে, এবং মায়ের জীবন ও স্বাস্থ্যকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করবে। একটু ভাল করে খোঁজখবর করলেই জানা যাবে, অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঘটছে কিন্তু আসলে ঠিক তাইই, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রেই। এবং, মুসলমানরা পিছিয়ে আছে বলেই তাদের অগ্রগতিও দ্রুততর। তাদের জন্মহারের বৃদ্ধি কমছে কিছু বেশি দ্রুতলয়ে। এভাবে চললে আর দেড় দুই দশক পরেই হয়ত হিন্দু-মুসলমানের জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার সমান হয়ে যাবে, এবং মুসলমানদের ভারত দখলের কুৎসিত অশিক্ষিত গল্পতেও তখন আর কেউই পাত্তা দেবে না। ইতিহাসের স্বাভাবিক গতি এই দিকেই।
এখানে 'অগ্রগতি' বলতে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমিয়ে আনার কথা বুঝিয়েছি। মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই কমিয়ে আনাটা হিন্দুদের চেয়ে বেশি হারে ঘটছে (বৃদ্ধির হার কমে যাওয়া মানে জনসংখ্যা কমে যাওয়া নয় কিন্তু, এ হার কমতে কমতে শূন্যের নিচে নামলে তবেই জনসংখ্যা কমতে শুরু করবে)। এই কমে আসাটা উন্নয়নের পরোক্ষ সূচক। এভাবে চলতে থাকলে কিছুদিন বাদে যে হিন্দু-মুসলমানের জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার সমান হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। পিছিয়ে আছে বলেই অগ্রগতি বেশি তাড়াতাড়ি হচ্ছে --- এ কথাটা হয়ত অনেককে বিস্মিত করতে পারে, কিন্তু কথাটা বলার কারণ আছে। নিশ্চয়ই জানেন, ভারত চিন ব্রাজিলের মত একটু এগিয়ে থাকা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ইউরোপ আমেরিকার উন্নত দেশগুলোর থেকে বেশি। এর কারণ হচ্ছে, একবার উন্নত হয়ে গেলে একই গতিতে আরও আরও উন্নত হতে থাকাটা ক্রমশই আরও বেশি বেশি করে কঠিন হয়ে ওঠে, তাই উন্নয়নের প্রথম দিকে বৃদ্ধির যে গতি থাকে পরের দিকে আর তত গতি থাকে না। মুসলমানদের জনসংখ্যার ক্ষেত্রেও তাইই ঘটছে, এবং আরও ঘটবে (ও দুটোকে খুব নিখুঁতভাবে মেলানোর দরকার নেই, যদিও)।
আমরা যারা এই বিষয়গুলোকে এইভাবে ভাবার চেষ্টা করি, তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আসে প্রায়শই, ফেসবুকে সে গর্জন রোজই শোনা যায়। এখন, এটা তো সত্যি কথাই যে, পশ্চিমবাংলার যুক্তিবাদীদের লেখালিখিতে, এবং যথারীতি আমার নিজের লেখাতেও, হিন্দু মৌলবাদের সমালোচনাই বেশি আসে, মুসলমান মৌলবাদের কথা বাস্তবিকই আসে অনেক কম। ঠিক এই অভিযোগটি সেক্যুলারদের প্রতি হিন্দু মৌলবাদীরা করে থাকেন নিয়মিতই (বস্তুত, প্রত্যেক ধর্মের মৌলবাদীরাই তাদের নিজস্ব গোষ্ঠী বা সমাজের সেক্যুলারদের প্রতি এই একই অভিযোগ করে থাকে)। কিন্তু একটু ভাবলে বুঝবেন, এটাই প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক। এবং, অন্যরকম কিছু হলেই বরং অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত হত, এমন কি অন্যায়ও হত। কেন, তার একাধিক কারণ আছে। প্রথমত, এ দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ যে মৌলবাদী হুমকিটির মুখোমুখি, সেটা তো হিন্দু মৌলবাদই, অন্য কোনও মৌলবাদ নয়। শিক্ষা-প্রশাসন-বিচারব্যবস্থার ধর্মীয়করণ, সংবিধানকে পাল্টে দেবার পরিকল্পনা, ভিন-ধর্মীদের ওপর দমন-পীড়ন, ধর্মের জিগির তুলে তার আড়ালে সরকারি সম্পত্তি পাচার --- এ সব তো মুসলমানরা করছে না, হিন্দুত্ববাদীরাই করছে। অতএব, তাদের মুখোশ খোলাটাই এখানে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। মুসলমান জঙ্গিরা নাশকতা ঘটালে তার মোকাবিলার জন্য পুলিশ-মিলিটারি আছে, কিন্তু নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসা মৌলবাদীদের রোখবার দায়িত্ব তো আর পুলিশ-মিলিটারি নেবে না, সেটা সাধারণ ভারতীয় নাগরিকের কাজ। আমি যে দেশে এবং যে ধর্মীয় সমাজের মধ্যে বাস করি, সেখানে যারা অন্ধত্ব ও হিংস্রতা ছড়াচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রকে বিনাশ করছে, তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোটাই তো আমার পক্ষে স্বাভাবিক, তাই না? বাংলাদেশি মুক্তমনারা যদি মুসলমান ধর্ম ছেড়ে হিন্দুদেরকে গালি দিতে থাকতেন, বা বার্ট্র্যান্ড রাসেল যদি 'হোয়াই আই অ্যাম নট আ ক্রিশ্চান' না লিখে 'হোয়াই আই অ্যাম নট আ হিন্দু' লিখে বসতেন, তাহলে যেমন উদ্ভট অসঙ্গত কাজ হত, এখানে আমরা হিন্দু ধর্ম ছেড়ে মুসলমান নিয়ে পড়লেও ঠিকই একই ব্যাপার হবে (যদিও বাংলাদেশি মুক্তমনারা ঠিক যা বলেন এবং যেভাবে বলেন, তার অনেক কিছুর সঙ্গেই আমার দ্বিমত আছে, তবে সেটা এখানে প্রাসঙ্গিক না)। দ্বিতীয়ত, আমরা পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ মুক্তমনা যুক্তিবাদী নাস্তিকেরা হিন্দু সমাজে জন্মেছি বলেই সে সমাজ ও তার ধর্ম শাস্ত্র রীতিনীতি আচার বিচার এইসব অনেক বেশি জানি, ফলে সে ব্যাপারে আমাদের সমালোচনা অনেক বেশি নিরেট, নির্ভুল এবং অর্থবহ হয়, যা ভিনধর্মী সমাজে যারা জন্মেছে তারা পারবেনা। ঠিক একই কারণে, মুসলমান সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে মুসলমান সমাজে জন্মানো যুক্তিবাদীদের সমালোচনা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ও ফলপ্রসূ হয়। যদিও, এর মানে মোটেই এই নয় যে এক ধর্মে জন্মানো লোক অন্য ধর্মের সমালোচনা করতেই পারবেনা --- যে কোনও মানুষের যে কোনও ধর্মের সমালোচনা করার অধিকার আছে, এবং করা উচিত। তবে কিনা, নিজের সমাজের অন্ধত্ব অযুক্তি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথমে সোচ্চার হওয়াটা যে কোনও মানুষেরই ‘স্বাভাবিক’ অধিকার, কর্তব্যও বটে।
আচ্ছা, তা সে যা-ই হোক, মোদ্দা কথাটা তাহলে কী দাঁড়াল --- মুসলমানেরা ধর্মান্ধতায় অন্যদের চেয়ে এগিয়ে, না পিছিয়ে? এসব ঠিকঠাক বলতে গেলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে পৃথিবীজোড়া সমীক্ষার নির্ভরযোগ্য ফলাফল চাই, না হলে সবটাই চায়ের দোকানের আড্ডা হয়ে যাবে। আপাতত আছে কি সে সব, আমাদের হাতে? সুখের বিষয়, সে সব আছে। এই কিছুদিন মাত্র আগেও সেভাবে ছিল না, কিন্তু এই একুশ শতকে বেশ ভালভাবেই আছে। বেশ কয়েকটি বিখ্যাত সংস্থা এখন মানুষের জীবনের নানা দিক নিয়ে প্রামাণ্য সমীক্ষা করে থাকে, তার মধ্যে ধর্মবিশ্বাসও পড়ে। এইসব সমীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে বড় বড় বিশেষজ্ঞরা নানা গভীর গবেষণাও করে থাকেন, এবং তাতে তেমন চমকপ্রদ কোনও ফলাফল পাওয়া গেলে সারা পৃথিবীর গণমাধ্যমে সে নিয়ে আলোড়ন উঠে যায়। এই রকমই একটি সংস্থা হল ‘উইন গ্যালাপ’। তারা সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে এক বিখ্যাত সমীক্ষা চালিয়েছিল ২০১২ সালে, তাতে বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের প্রাবল্য, ধর্মবিশ্বাস ছেড়ে বেরিয়ে আসা মানুষের সংখ্যা, এইসবের হিসেব ছিল। তাতে কি দেখা গেল? নিচে দেখে নিন ২০১২ সালের পৃথিবীজোড়া সমীক্ষার ফলাফল, সুন্দর করে সারণিতে সাজানো। এখানে পরিষ্কারভাবেই দেখা যাচ্ছে, নিজেকে বিশ্বাসী বলে দাবি করেন অথচ ধার্মিক বলে দাবি করেন না --- এমন মানুষের অনুপাত মুসলমানদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি। কারা কবে সমীক্ষাটি করেছে, এবং তা কোন নথিতে প্রকাশিত, সব তথ্যই পাবেন এখানে। এবার একটি ইসলামীয় দেশকে নিয়ে ভাবা যাক, যেখানে প্রায় সর্বাত্মক মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং ইসলামীয় রাষ্ট্র আছে। ধরুন, ইরান। এই দেশটা সম্পর্কে আপনি কী জানেন? জানি, এ প্রশ্নের উত্তরে প্রায় সকলেই একই কথা বলবেন। ছিয়ানব্বই দশমিক পাঁচ শতাংশ (সরকারি সেন্সাসের তথ্য অনুযায়ী) মুসলমান অধ্যুষিত একটি ধর্মান্ধ দেশ, যার মধ্যে আবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা শিয়া মুসলমানদের। কট্টর মৌলবাদীরা সেখানে দেশ চালায়, প্রশ্ন করলেই কোতল হতে হয়, মুক্তচিন্তা কল্পনাতীত। সম্প্রতি সেখানে হুলুস্থুলু ঘটে গিয়েছে, সে সব খবরাখবর আপনারা দেখেছেন। একটি মেয়েকে ইসলাম-সম্মত পোশাক না পরার অপরাধে সেখানে হত্যা করা হয়েছে, তাই নিয়ে প্রবল আন্দোলন হলে রাষ্ট্রের তরফে নেমে এসেছে দমন-পীড়ন, এবং সদ্য-সমাপ্ত ফুটবল বিশ্বকাপে সারা পৃথিবীর সামনে তার প্রতিবাদ করায় সে দেশের জাতীয় দলের এক খেলোয়াড়কে দেওয়া হয়েছে মৃত্যুদণ্ড। এখানে মৌলবাদের দাপটের ছবিটা একদমই স্পষ্ট, আবার গণমানুষের আপত্তিটাও খুব আবছা নয়।
এবার একটি ইসলামীয় দেশকে নিয়ে ভাবা যাক, যেখানে প্রায় সর্বাত্মক মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং ইসলামীয় রাষ্ট্র আছে। ধরুন, ইরান। এই দেশটা সম্পর্কে আপনি কী জানেন? জানি, এ প্রশ্নের উত্তরে প্রায় সকলেই একই কথা বলবেন। ছিয়ানব্বই দশমিক পাঁচ শতাংশ (সরকারি সেন্সাসের তথ্য অনুযায়ী) মুসলমান অধ্যুষিত একটি ধর্মান্ধ দেশ, যার মধ্যে আবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা শিয়া মুসলমানদের। কট্টর মৌলবাদীরা সেখানে দেশ চালায়, প্রশ্ন করলেই কোতল হতে হয়, মুক্তচিন্তা কল্পনাতীত। সম্প্রতি সেখানে হুলুস্থুলু ঘটে গিয়েছে, সে সব খবরাখবর আপনারা দেখেছেন। একটি মেয়েকে ইসলাম-সম্মত পোশাক না পরার অপরাধে সেখানে হত্যা করা হয়েছে, তাই নিয়ে প্রবল আন্দোলন হলে রাষ্ট্রের তরফে নেমে এসেছে দমন-পীড়ন, এবং সদ্য-সমাপ্ত ফুটবল বিশ্বকাপে সারা পৃথিবীর সামনে তার প্রতিবাদ করায় সে দেশের জাতীয় দলের এক খেলোয়াড়কে দেওয়া হয়েছে মৃত্যুদণ্ড। এখানে মৌলবাদের দাপটের ছবিটা একদমই স্পষ্ট, আবার গণমানুষের আপত্তিটাও খুব আবছা নয়।
আসলে, এখানে ধর্মীয় রাষ্ট্রের দোর্দণ্ডপ্রতাপের তলাতেই লুকিয়ে আছে অন্য এক বাস্তবতা। নেদারল্যান্ডের একটি গবেষণা সংস্থা (GAMAAN), ইরানই যাদের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু, তারা ২০২০ সালে ইরানে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে। সে সমীক্ষার ফলাফল যদি বিশ্বাস করতে হয়, তো সেখানে সাঁইত্রিশ শতাংশ মত লোক নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করেন (শিয়া-সুন্নি মিলিয়ে), যাঁরা কোনও ধর্মীয় পরিচয় দিতে রাজি নন তাঁরা বাইশ শতাংশ, যাঁরা পরিষ্কারভাবে নিজেকে নাস্তিক-অজ্ঞাবাদী-মানবতাবাদী এইসব বলে পরিচয় দেন তাঁরা সব মিলিয়ে প্রায় সতেরো শতাংশ, যাঁরা নিজেকে শুধুই 'স্পিরিচুয়াল' বলেন তাঁরা প্রায় সাত শতাংশ, এবং বাকিরা আরও নানা বিচিত্র ধর্মের মানুষ। নিচের ছবি দুটোয় সমীক্ষার ফলাফল এক নজরে পাওয়া যাবে। হ্যাঁ বন্ধু, একুশ শতকে পৃথিবী বদলাচ্ছে, এবং হয়ত বিশ শতকের চেয়েও দ্রুত গতিতে! এবং, ইসলামীয় দেশগুলো কোনওভাবেই এ প্রবণতার বাইরে নয়। নিচে সে সমীক্ষার ফলাফল দেখুন, চিত্রাকারে। ধর্ম, ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক, মৃত্যু-পরবর্তী জীবন, অবতার ইত্যাদি ধ্যানধারণা বিষয়ে ইরান-বাসীদের বিশ্বাস (বা অবিশ্বাস) ঠিক কী রকম, সে চিত্রও উঠে এসেছে সমীক্ষা থেকে। নিচে দেখুন।
ধর্ম, ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক, মৃত্যু-পরবর্তী জীবন, অবতার ইত্যাদি ধ্যানধারণা বিষয়ে ইরান-বাসীদের বিশ্বাস (বা অবিশ্বাস) ঠিক কী রকম, সে চিত্রও উঠে এসেছে সমীক্ষা থেকে। নিচে দেখুন। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুসলমানদের ধর্মপ্রীতি নিয়ে আমাদের অধিকাংশের মধ্যে যেসব জনপ্রিয় ধ্যানধারণা আছে, তার সমর্থন এইসব সমীক্ষার ফলাফল থেকে মিলছে না মোটেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে ইঙ্গিত এখান থেকে আমরা পাচ্ছি, সেটা সামগ্রিক বৈশ্বিক প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, নাকি একটা সম্পূর্ণ আলাদা উল্টোপাল্টা কিছু। সেটা বুঝতে গেলে বর্তমান শতকের বিগত কয়েকটি দশকে গোটা পৃথিবীর ধর্মবিশ্বাসের গতিপ্রকৃতি এক নজরে দেখে নেওয়া দরকার। এমনিতে সেটা একটু মুশকিল, কারণ, তার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থার করা অনেকগুলো সমীক্ষা-কর্ম খুঁটিয়ে দেখে সেগুলোর প্রাসঙ্গিক ফলাফলটুকু বেছে নিয়ে তুলনা করতে হবে। সেইজন্যে, আমি যতটা পেরেছি সেগুলোকে সাজিয়ে একটা মাত্র সারণিতে নিয়ে এসেছি, তাতে পাঠিকের কিছু সুবিধে হবার কথা। সেটা নিচে দিলাম, দেখুন। সারণির কোন সংখ্যাটি কোন সংস্থার করা কবেকার সমীক্ষায় পাওয়া গেছে, সেটা ওখানেই দেওয়া আছে। প্রথম সংখ্যাটি অবশ্য কোনও সংস্থার তরফে দেওয়া নয়। এটি দিয়েছিলেন সমাজতত্ত্ববিদ ফিলিপ জুকারম্যান, তখন পর্যন্ত প্রাপ্য সমস্ত টুকরো টুকরো সমীক্ষার ফলাফল এক জায়গায় করে।
তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মুসলমানদের ধর্মপ্রীতি নিয়ে আমাদের অধিকাংশের মধ্যে যেসব জনপ্রিয় ধ্যানধারণা আছে, তার সমর্থন এইসব সমীক্ষার ফলাফল থেকে মিলছে না মোটেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে ইঙ্গিত এখান থেকে আমরা পাচ্ছি, সেটা সামগ্রিক বৈশ্বিক প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, নাকি একটা সম্পূর্ণ আলাদা উল্টোপাল্টা কিছু। সেটা বুঝতে গেলে বর্তমান শতকের বিগত কয়েকটি দশকে গোটা পৃথিবীর ধর্মবিশ্বাসের গতিপ্রকৃতি এক নজরে দেখে নেওয়া দরকার। এমনিতে সেটা একটু মুশকিল, কারণ, তার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থার করা অনেকগুলো সমীক্ষা-কর্ম খুঁটিয়ে দেখে সেগুলোর প্রাসঙ্গিক ফলাফলটুকু বেছে নিয়ে তুলনা করতে হবে। সেইজন্যে, আমি যতটা পেরেছি সেগুলোকে সাজিয়ে একটা মাত্র সারণিতে নিয়ে এসেছি, তাতে পাঠিকের কিছু সুবিধে হবার কথা। সেটা নিচে দিলাম, দেখুন। সারণির কোন সংখ্যাটি কোন সংস্থার করা কবেকার সমীক্ষায় পাওয়া গেছে, সেটা ওখানেই দেওয়া আছে। প্রথম সংখ্যাটি অবশ্য কোনও সংস্থার তরফে দেওয়া নয়। এটি দিয়েছিলেন সমাজতত্ত্ববিদ ফিলিপ জুকারম্যান, তখন পর্যন্ত প্রাপ্য সমস্ত টুকরো টুকরো সমীক্ষার ফলাফল এক জায়গায় করে। এবার নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে, মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের গতিপ্রকৃতি অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে খুব বেশি আলাদা নয়। আসলে, এই একুশ শতকে দাঁড়িয়ে, সব ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যেই ধর্মবিশ্বাস ছেড়ে বেরিয়ে আসার যে প্রবণতা রয়েছে, মুসলমানরা কোনও মতেই সে প্রবণতার বাইরে নয় (অবশ্যই, এ হিসেব সামগ্রিক ও বৈশ্বিক, এবং অঞ্চল ও অন্যান্য পরিস্থিতি-ভেদে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য আছে)।
এবার নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে, মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের গতিপ্রকৃতি অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে খুব বেশি আলাদা নয়। আসলে, এই একুশ শতকে দাঁড়িয়ে, সব ধর্মগোষ্ঠীর মধ্যেই ধর্মবিশ্বাস ছেড়ে বেরিয়ে আসার যে প্রবণতা রয়েছে, মুসলমানরা কোনও মতেই সে প্রবণতার বাইরে নয় (অবশ্যই, এ হিসেব সামগ্রিক ও বৈশ্বিক, এবং অঞ্চল ও অন্যান্য পরিস্থিতি-ভেদে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য আছে)।
কেন এই জগৎজোড়া প্রবণতা? আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি বলবে, সবই যুগের হাওয়া। মানে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং গণতন্ত্র-মানবতাবাদ-যুক্তিবাদ এইসবের প্রভাবই এর কারণ। কথাটা সত্যি, কিন্তু সমাজবিদেরা এর চেয়েও বড় কারণ আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা আজ সুপ্রচুর তথ্য-যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন, মানব সমাজের উন্নতির সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক বিপ্রতীপ। দেশের মাথাপিছু আয় বাড়লে, সমাজকল্যাণে সরকার বেশি বেশি খরচা করলে, অর্থনৈতিক অসাম্য কমলে এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের হাল ভাল হলে ধর্মের রমরমা কমতে থাকে (এখানে আর বিস্তারে যাব না, যদিও আগে এ নিয়ে আলোচনা করেছি এবং পরেও করব)। সমাজ-বিকাশের এই সাধারণ নিয়ম মুসলমান সমাজের ওপরে প্রযোজ্য হবে না, এমনটা ভেবে নেওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। ইরানে যা ঘটছে, সেটা সমাজ-বিকাশের এই সাধারণ নিয়মের চাপেই। নেটে একটু খোঁজাখুঁজি করলেই দেখতে পাবেন, ইরানের মাথাপিছু উৎপাদন ভারতের প্রায় আটগুণ, বাজেটের শতাংশ হিসেবে স্বাস্থ্যখাতে সরকারি খরচ প্রায় সাতগুণ এবং শিক্ষাখাতে তা দেড়গুণেরও বেশি, এবং নারী ও পুরুষ উভয়েরই আয়ু আমাদের থেকে ভাল (গণতন্ত্র আর মানবাধিকারের দশা শোচনীয়, যদিও)। কাজেই, ইরানে মৌলবাদী রাজনীতি ও প্রশাসনের ওপর কেন গণ-অসন্তোষের চাপ আছে এবং পাকিস্তান আর আফগানিস্তানে কেন তা ততটা নেই --- এইটা বুঝতে পারা খুব কঠিন না।
বলা প্রয়োজন, সমাজ-বিকাশজাত এই চাপের খেলা সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান উন্নত পশ্চিমী দেশগুলোতেও, বিশেষত এই একুশ শতকে। এই সেদিন পর্যন্ত আমেরিকা আর আয়ার্ল্যান্ডে ধর্মবিশ্বাসের প্রাবল্য ছিল অন্যান্য উন্নত দেশের চেয়ে অনেক বেশি। ধার্মিক সমাজবিদেরা তাই দেখিয়ে বলতেন, অর্থনৈতিক উন্নতি হলেই ধর্মের রমরমা কমবে, এটা হচ্ছে গিয়ে প্রগতিবাদীদের বানানো একটা মিথ্যে কথা। কিন্তু সময় যতই গড়াচ্ছে ততই বিষয়টা জলের মত স্বচ্ছ হয়ে আসছে, এবং আপত্তি তোলবার পরিসর হয়ে আসছে অতিশয় সঙ্কুচিত। মার্কিন সমাজে ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তনটা দেখতে পাবেন এক নজরেই, নিচের লেখচিত্রে। লক্ষ করে দেখুন, ১৯৫০ সাল থেকে ২০২০ পর্যন্ত আমেরিকাতে যখন খ্রিস্টানরা এসে ঠেকেছে ৮৫ শতাংশ থেকে ৬৯-এ, এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা যখন মোটের ওপর একই আছে, তখন ধর্মহীনদের শতকরা অনুপাত গিয়ে ঠেকেছে শূন্য থেকে একুশে (অন্য কিছু সমীক্ষায় এটি প্রায় তিরিশ বলে দেখানো হয়েছে, যদিও)। আর, এই শতকের প্রথম দশকে আয়ার্ল্যান্ড-বাসীর ধর্মবিশ্বাসে যা ঘটেছে, সেটা দেখে নিন নিচের সারণিতে। আয়ার্ল্যান্ড হল গোঁড়া ক্যাথোলিক অধ্যুষিত একটি দেশ। একটা উন্নত পশ্চিমী দেশের পক্ষে অবিশ্বাস্যভাবে, এই সেদিন পর্যন্তও এই দেশটিতে গর্ভপাত নিষিদ্ধ ছিল, এবং গর্ভপাতের দরকার পড়লে আইরিশ নারীদেরকে পার্শ্ববর্তী ব্রিটেনে গিয়ে হাজির হতে হত। তারপর উন্নত আধুনিক অর্থনীতির সঙ্গে রক্ষণশীল ধর্ম-সংস্কৃতির দীর্ঘ সংঘর্ষের ফলাফল তখনই সারা বিশ্বের নজরে এল, যখন দু হাজার আঠেরো সালে গর্ভপাত আইনসিদ্ধ হয়ে গেল (আয়ার্ল্যান্ড নিয়ে আমার আলাদা একটি লেখা ‘গুরুচণ্ডালি’-তে পাবেন)।
আর, এই শতকের প্রথম দশকে আয়ার্ল্যান্ড-বাসীর ধর্মবিশ্বাসে যা ঘটেছে, সেটা দেখে নিন নিচের সারণিতে। আয়ার্ল্যান্ড হল গোঁড়া ক্যাথোলিক অধ্যুষিত একটি দেশ। একটা উন্নত পশ্চিমী দেশের পক্ষে অবিশ্বাস্যভাবে, এই সেদিন পর্যন্তও এই দেশটিতে গর্ভপাত নিষিদ্ধ ছিল, এবং গর্ভপাতের দরকার পড়লে আইরিশ নারীদেরকে পার্শ্ববর্তী ব্রিটেনে গিয়ে হাজির হতে হত। তারপর উন্নত আধুনিক অর্থনীতির সঙ্গে রক্ষণশীল ধর্ম-সংস্কৃতির দীর্ঘ সংঘর্ষের ফলাফল তখনই সারা বিশ্বের নজরে এল, যখন দু হাজার আঠেরো সালে গর্ভপাত আইনসিদ্ধ হয়ে গেল (আয়ার্ল্যান্ড নিয়ে আমার আলাদা একটি লেখা ‘গুরুচণ্ডালি’-তে পাবেন)। বলা বাহুল্য, মোটের ওপর এই একই ঘটনা ঘটবার কথা মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতেও, এবং ঘটছেও তাইই। বেশ কয়েকটি ধর্ম-শাসিত রক্ষণশীল দেশে কমছে কঠোর ধর্মীয় বাধানিষেধ, বাড়ছে ধর্মহীনতা, এবং সাধারণ্যে কমছে ধর্মের প্রতি আনুগত্য, যদিও অনেক ক্ষেত্রেই তা এখনও স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান নয়। বিষয়টাকে যদি খুঁটিয়ে নজর করা হয়, তাহলে এমন অনেক কিছুই হয়ত জানা যাবে, যে ব্যাপারে আমরা আগে সচেতন ছিলাম না। যেমন, ইরান-ইরাক-আফগানিস্তান যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষ থেকে ধর্মীয় রাষ্ট্র হয়ে গেল, এবং যেভাবে তুর্কি দেশটিতে ক্রমেই শক্ত হচ্ছে মৌলবাদের মুঠি আর টলমল করছে ধর্মনিরপেক্ষতার আসন, সে নিয়ে আমরা প্রায়শই দুশ্চিন্তিত হই। ঠিকই করি। কিন্তু, আমরা কখনই খেয়াল করে দেখিনা যে, এই ধরাধামে একান্নটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের মধ্যে একুশটিতে কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ সরকারই চলছে (সে ধর্মনিরপেক্ষতার দশা প্রায়শই আমাদের চেয়ে খুব একটা ভাল নয় যদিও, তবে সেটা তো অন্য চর্চা)। এবং, ধর্মনিরপেক্ষীকরণের প্রক্রিয়া এখনও চালু, সে তালিকায় এই সেদিনও যুক্ত হয়েছে সুদান।
বলা বাহুল্য, মোটের ওপর এই একই ঘটনা ঘটবার কথা মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতেও, এবং ঘটছেও তাইই। বেশ কয়েকটি ধর্ম-শাসিত রক্ষণশীল দেশে কমছে কঠোর ধর্মীয় বাধানিষেধ, বাড়ছে ধর্মহীনতা, এবং সাধারণ্যে কমছে ধর্মের প্রতি আনুগত্য, যদিও অনেক ক্ষেত্রেই তা এখনও স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান নয়। বিষয়টাকে যদি খুঁটিয়ে নজর করা হয়, তাহলে এমন অনেক কিছুই হয়ত জানা যাবে, যে ব্যাপারে আমরা আগে সচেতন ছিলাম না। যেমন, ইরান-ইরাক-আফগানিস্তান যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষ থেকে ধর্মীয় রাষ্ট্র হয়ে গেল, এবং যেভাবে তুর্কি দেশটিতে ক্রমেই শক্ত হচ্ছে মৌলবাদের মুঠি আর টলমল করছে ধর্মনিরপেক্ষতার আসন, সে নিয়ে আমরা প্রায়শই দুশ্চিন্তিত হই। ঠিকই করি। কিন্তু, আমরা কখনই খেয়াল করে দেখিনা যে, এই ধরাধামে একান্নটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের মধ্যে একুশটিতে কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ সরকারই চলছে (সে ধর্মনিরপেক্ষতার দশা প্রায়শই আমাদের চেয়ে খুব একটা ভাল নয় যদিও, তবে সেটা তো অন্য চর্চা)। এবং, ধর্মনিরপেক্ষীকরণের প্রক্রিয়া এখনও চালু, সে তালিকায় এই সেদিনও যুক্ত হয়েছে সুদান।
তবুও প্রশ্ন আসতেই পারে, এবং আসবেও, জানা কথা। ওপরে উদ্ধৃত আমার তরুণ বন্ধুর ভাষায়, সে প্রশ্নটা এ রকম --- “আর কোন ধর্মে আইসিস, তালিবান, বোকোহারামের মত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আছে?”। সত্যিই তো, প্রশ্ন হতেই পারে। ওপরে ব্যাখ্যা করেছি (এবং পূর্ববর্তী পর্বগুলোতেও), মৌলবাদী উত্থান সব ধর্মেই হয়েছে, শুধু ইসলামে নয়। এবং, জঙ্গি ক্রিয়াকলাপও কম বেশি হয়েছে সব ধর্মের তরফেই। সেই সত্যে ভর করে আমি হয়ত তর্ক করতে পারতাম, অন্যান্য ধর্মের মৌলবাদের সঙ্গে ইসলামের তফাতটা তাহলে গুণগত নয়, নিছকই পরিমাণগত। এরা কম, ওরা কিছু বেশি, এটুকুই মাত্র। কিন্তু, এ তর্ক শেষতক দাঁড়াবে না। পাথরের নুড়ির সঙ্গে পাথরের টিলার গুণগত পার্থক্যকে স্রেফ পরিমাণের দোহাই দিয়ে নস্যাৎ করাটা বোধহয় খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ইসলামীয় জঙ্গিপনার নিবিড়তা, ঘনত্ব, প্রচণ্ডতা এবং আন্তর্জাতিকতা, এ সবকে নিছক কম-বেশির ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। যদি বলি, মধ্যপ্রাচ্যে একাধিক আধুনিক রাষ্ট্র থেকে খামচে নিয়ে একটা গোটা এবং আনকোরা নতুন ধর্মীয় রাষ্ট্র বানিয়ে তোলা, অনেকগুলো দেশে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার উল্টে দিয়ে মৌলবাদী রাজত্ব কায়েম করা, প্রায় সবকটি মহাদেশে বড়সড় নাশকতা চালানোর মত সংগঠন তৈরি করতে পারা --- এত সব শুধুই জঙ্গিপনার কম-বেশির ব্যাপার, তার মধ্যে আলাদা করে বলার মত গুরুত্বপূর্ণ গুণগত বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই --- তাহলে অবশ্যই বোকামি হবে, বাস্তবকে অস্বীকার করার বোকামি। কাজেই, জঙ্গিপনার এই ভয়ঙ্কর নিবিড়তা আর ব্যাপকতাকে ইসলামীয় মৌলবাদের একটি স্বতন্ত্র গুণগত বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে, সেটা মেনে নিলেও আসল সমস্যাটা রয়েই যায়। সব মুসলমানই তো আর মৌলবাদী জঙ্গি নন, তার এক অতি ক্ষুদ্র অংশই কেবল মৌলবাদী জঙ্গি। কাজেই, এই জঙ্গিপনাকে ইসলামীয় মৌলবাদের একটি স্বতন্ত্র গুণগত বৈশিষ্ট্য বলে মেনে নিলেও প্রশ্ন থাকে, ‘ইসলাম’ নামক ধর্মটির কোনও মৌল উপাদান থেকেই কি এই বৈশিষ্ট্যটি উৎসারিত হচ্ছে, নাকি, মুসলমান অধ্যুষিত সমাজ তথা রাষ্ট্রগুলোর কোনও বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিই এ বৈশিষ্ট্যের নির্মাতা?
কেউ কেউ এ প্রশ্নের উত্তর খুব দ্রুত দিয়ে ফেলতে ভালবাসেন। তাঁরা বলেন, এ বৈশিষ্ট্য অবশ্যই ‘ইসলাম’ নামক ধর্মটিরই মৌল উপাদান থেকে নিঃসৃত, কারণ, ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্রে হিংসার অনুমোদন আছে। এ যুক্তিটি যে ভুল, সে আলোচনা ওপরে করেছি। কিন্তু কথা হচ্ছে, এ প্রশ্নের উত্তর তবে কীভাবে খোঁজা যায়? আজকের দিনে বিজ্ঞানে, বিশেষত সমাজবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে, এ ধরনের প্রশ্নের সমাধানের জন্য যা করা হয় তাকে বলে ‘কন্ট্রোল্ড্ এক্সপেরিমেন্ট’। সমাজের ওপর তো আর পরীক্ষা চলবে না, অতএব সেখানে দরকার ‘কন্ট্রোল্ড্ অবজার্ভেশন’ বা সুনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ। অর্থাৎ, পুরোপুরি একই রকম করে তৈরি (বা সংগ্রহ) করে রাখা দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে একটিতে একটি সুনির্দিষ্ট নির্ধারক উপাদান যোগ করে (বা একটি সুনির্দিষ্ট নির্ধারক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে), এবং অপরটিতে তা না করে, শুধুমাত্র প্রথম ক্ষেত্রটিতে কোনও এক নির্দিষ্ট প্রত্যাশিত ফলাফল এলো কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা, যাতে ওই নির্দিষ্ট উপাদানটির (বা প্রক্রিয়াটির) সঙ্গে ওই ফলাফলটির কার্যকারণ সম্পর্ক সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। কোনও ওষুধের কার্যকারিতা প্রমাণের জন্য যেমন একই ধরনের দু দল রুগির মধ্যে একদলকে সে ওষুধ দিয়ে এবং অন্যদলকে তা না দিয়ে পরীক্ষা করা হয় যে দ্বিতীয় দলের তুলনায় প্রথম দলের কিছু বেশি উপকার হল কিনা, এও তেমনি। মনে করুন প্রশ্ন উঠল যে, মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামের যে মৌলবাদী উত্থান দেখা গেল, ইরাকের খনিজ তেল এবং আফগানিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থানগত সামরিক গুরুত্ব না থাকলেও কি তা ঘটতে পারত, শুধুমাত্র ইসলামীয় শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কৃতির একান্ত নিজস্ব আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের কারণেই? এ প্রশ্নের বিজ্ঞানসম্মত ও বস্তুনিষ্ঠ উত্তর বেরিয়ে আসতে পারে একমাত্র সেই ধরনের পদ্ধতিতেই, অর্থাৎ, ‘কন্ট্রোল্ড্ অবজার্ভেশন’ বা সুনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। যেখানে ইসলামের প্রবল প্রভাব আছে অথচ কোনও বড়সড় অর্থনৈতিক বা সামরিক লাভালাভের পরিস্থিতি নেই, সে রকম সমস্ত জায়গাতেও কি মৌলবাদী জঙ্গিপনার উদ্ভব ঘটেছে? আবার, যেখানে ওই ধরনের পরিস্থিতি আছে অথচ ইসলাম নেই, সে রকম কোনও জায়গাতেই কি জঙ্গি আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেনি? এই ধরনের অনুসন্ধান হয়ত আমাদেরকে এ ধরনের প্রশ্নের বস্তুনিষ্ঠ উত্তরের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ প্রসঙ্গে এ রকম গবেষণার কথা আমাদের জানা নেই।
এই যে মুসলমান মৌলবাদের অস্তিত্বের কারণ হিসেবে ইসলামের আভ্যন্তরীণ কারণকে পুরোপুরিই দায়ী করা, ওপরের দুই অনুচ্ছেদে যার কথা বললাম, এর ঠিক উল্টো প্রবণতাটা হচ্ছে এর পেছনে ‘মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ’ (বা আরও সাধারণভাবে ‘পশ্চিমী চক্রান্ত’) বা ওই জাতীয় ইসলাম-বহির্ভূত কোনও কিছুকে পুরোপুরি দায়ী করা (এবং সেইহেতু ইসলামীয় সমাজ ও সংস্কৃতির আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যগুলোকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলে সাব্যস্ত করা)। মুসলিম মৌলবাদের উত্থানের পেছনে পাশ্চাত্য শক্তি, বিশেষত আমেরিকার ভুমিকা অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথেই আলোচনা করা উচিত। কিন্তু, বিশ শতকের পৃথিবীর ইতিহাসের সমস্ত ঘটনাই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গুলিহেলনে ঘটছে, চোখ বুজে এইটা বলে দিলে আপাতদৃষ্টিতে হয়ত তাকে নিন্দা করা হয়, কিন্তু আসলে শেষ বিচারে তার ক্ষমতাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেখা হয়। আমেরিকা (বা সাধারণভাবে ‘পশ্চিম’) মুসলমান দেশগুলোর আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল, শুধু এটুকু বললে প্রায় কিছুই বলা হয় না --- আসল প্রশ্ন হচ্ছে তারা তা পারল কী করে --- পৃথিবীর সব জায়গাতেই যে তারা যা চেয়েছে তাইই পেরেছে এমন তো আর নয়। মুসলমান সমাজ ও দেশগুলোর সুনির্দিষ্ট বিন্যাস ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, বিকাশের সুনির্দিষ্ট অবস্থা, তাদের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংশ্লিষ্ট সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তাদের তরফে নানা মতাদর্শ ও গোষ্ঠী-পরিচিতি নির্মাণের খেলা, এবং কখন ঠিক কোন তাড়নায় তারা কোন বৃহৎ শক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব বা শত্রুতার সম্পর্কে আবদ্ধ হচ্ছে, আর কোন বৃহৎ শক্তিই বা তাদেরকে সামলানো বা ব্যবহার করার জন্য ঠিক কী চাল চালছে --- এই সবের ভাল বিশ্লেষণ ছাড়া বিষয়টা ঠিকভাবে বোঝাই যাবে না। তাছাড়া, এই দেশগুলোতে 'সেক্যুলার' শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও প্রায়শই শাসকরা স্বৈরাচারি এবং দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে কেন, এবং, কেনই বা মৌলবাদীরা বারবার তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জনগণের পাশে থাকার ভাণ করতে পারে, এটাও এ প্রসঙ্গে গভীরভাবে বোঝার বিষয়।
বলা বাহুল্য, এ সব প্রশ্নে যথার্থ ও যথেষ্ট বিশ্লেষণ এবং নিষ্পত্তিমূলক উত্তর এখনও আসেনি সমাজবিজ্ঞানীদের তরফ থেকে। যতদিন তা না আসে, ততদিন আমরা কী করতে পারি? ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারি, বিষয়টি সম্পর্কে ইতিমধ্যে যা জানা গেছে সে সব জানার চেষ্টা করতে পারি, যুক্তিসম্মত ও বস্তুনিষ্ঠ চিন্তার অভ্যাস করতে পারি …………… আর কিছু পারি কি?
হ্যাঁ, পারি বোধহয়। মন থেকে অকারণ সন্দেহ ঘৃণা হিংসা বিদ্বেষ এইসব চিহ্নিত করে তা বর্জন করার অনুশীলনটা চালিয়ে যেতে পারি।
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত। - আরও পড়ুনপ্রসঙ্গ কোভিড ও ভ্যাকসিন : মাননীয় ষড়যন্ত্র-তাত্ত্বিক, আপনাকে বলছি স্যার - Debasis Bhattacharyaআরও পড়ুনইউরোপের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিপ্লব কি ঔপনিবেশিক শোষণ ছাড়া কিছুতেই হতে পারত না? - Debasis Bhattacharyaআরও পড়ুনসাত খুন মাফ। - Sobuj Chatterjeeআরও পড়ুনহস্টেল - Sukdeb Chatterjeeআরও পড়ুননতুন ঠিকানা - abhisek boseআরও পড়ুনখুশি - Suvasri Royআরও পড়ুনকাটাকুটি - সমরেশ মুখার্জীআরও পড়ুনবৈঠকি আড্ডায় ১৭ - হীরেন সিংহরায়আরও পড়ুনটুনটুন মুনটুন - সমরেশ মুখার্জীআরও পড়ুনশিক্ষা না ভিক্ষা? - Anirban M
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 guru | 103.211.20.30 | ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ ১৬:১৫514934
guru | 103.211.20.30 | ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ ১৬:১৫514934- সবাইকে notun বছরের শুভেচ্ছা |
-
Debasis Bhattacharya | ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ ২১:২২514935
- রাধার কানাই,
এখন আপনার বলা কথাগুলোর জবাব দেবার চেষ্টা করছি, কদ্দুর পারি দেখা যাক। যেহেতু আমার প্যারাফ্রেজিং-এ আপনি সহমত হয়েছেন, অতএব উত্তর দেবার সময় প্রশ্নগুলো বরং আমার বয়ানেই থাকুক।
প্রশ্ন - (১) ১৯৮০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে হঠাৎ করে একসাথে অনেকগুলো 'প্যান ইসলামিস্ট গ্রুপ' উঠে এল কেন (আপনি এ রকম আঠেরোটি সংগঠনের তালিকা দিয়েছেন)? মৌলবাদকে শুধু 'আধুনিকতার প্রতিক্রিয়া' বললে এ ঘটনার ব্যাখ্যা মিলছে না। মৌলবাদের উত্থান তো এক দেড়শো বছর ধরেই ঘটছে, তাহলে ওই অত্যল্প সময়সীমার মধ্যে এতবড় ঘটনা ঘটে যাওয়ার ব্যাখ্যা কি ইসলাম-বহির্ভুত কারণের (যেমন পশ্চিমী শক্তির মদত) দিকেই নির্দেশ করে না?উত্তর - আপনার পর্যবেক্ষণটি সঠিক, কিন্তু তাতে করে এখানে আমার মূল প্রতিপাদ্যটি বোধহয় আক্রান্ত হচ্ছে না। আমি বলেছি মৌলবাদ হচ্ছে আধুনিকতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, এবং ওই সময়কালটি তার মধ্যেই পড়ে। আপনি শুধু ইসলামীয় জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো উঠে আসার কথাই বলেছেন, তবে, মৌলবাদী উত্থানের অন্যান্য আরও সব গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোও কিন্তু ঠিক এই সময়সীমার মধ্যেই প্রস্ফুটিত হয়েছে (এবং, শুধু ইসলামের ক্ষেত্রে নয় মোটেই)। ইরানে মৌলবাদী বিপ্লব ও ক্ষমতা দখল, ১৯৭৯। আফগানিস্তানে 'মুজাহিদ'-দের তরফে সোভিয়েত-ঘেঁষা এবং আধুনিকতাবাদী নাজিবুল্লা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং তালিবানদের উত্থান, আটের দশকের শেষ এবং নয়ের দশকের গোড়া। ভারতে শিখ মৌলবাদের উত্থান ও পতন, আশির দশকের মাঝামাঝি। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে হিন্দুত্ববাদের নবোত্থান, নয়ের দশকের গোড়া। ব্যাপারটা কেন ঠিক ওই দুই দশকেই সবচেয়ে বেশি হল, এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গেলে ওই ধরনের প্রতিটা ঘটনাকে আতস কাঁচের তলায় ফেলে দেখতে হবে, একেকটা ঘটনার নিজস্ব 'মাইক্রো-ফিচার্স' বা অণু-বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে বার করে তার মধ্যে কোথায় মিল তা দেখতে হবে, এবং শেষে সেগুলো মিলেজুলে কীভাবে একটা 'ম্যাক্রো-প্যাটার্ন' বা মোদ্দা নকশা তৈরি করছে সেটা বুঝতে হবে। কিন্তু এখানে যে তা করা যাবেনা সেটা আমার লেখায় বলেছি। তবুও, সে রকম কিছু আলোচনা guru ওপরে করেছেন, এবং আপনি তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন (আমারও খারাপ লাগেনি), কাজেই আর বেশি কিছু বলছি না। শুধু একটাই কথা বলি, যে কোনও সামাজিক-ঐতিহাসিক ঘটনারই প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা 'স্ট্যাটিস্টিক্যাল নেচার' বা পারিসংখ্যায়নিক চরিত্র থাকে, এখানেও আছে। প্রথমে ছোট ছোট আলোড়নের মধ্যে দিয়ে শুরু হওয়া, তারপর বাড়তে বাড়তে ক্রমশ স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়ে একটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলে যাওয়া, এবং শেষে আবার তার জোর কমতে কমতে ক্রমশ মিলিয়ে যাওয়া। মৌলবাদের উত্থানও এ মোদ্দা নকশার বাইরে নয়। আপনি যেটা বলছেন সেটা ওর সর্বোচ্চ বিকাশের স্তর, এবং আমার ধারণা, একুশ শতকের এই তৃতীয় দশকে সে প্রক্রিয়া তার সর্বোচ্চ বিন্দু পেরিয়ে নিচে নামতে শুরু করেছে, এবং আমরা এখন যা দেখতে পাচ্ছি সেটা তার শেষের শুরু। তবে, অন্য আর একটা ব্যাপারও এর সঙ্গে জুড়ে থাকতে পারে। বিশ শতকের প্রথমার্ধ বহু সংখ্যক আধুনিকতাবাদী জঙ্গি আন্দোলনের সাক্ষী। উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, জাতিসত্তাবাদী আন্দোলন, কম্যুনিস্ট আন্দোলন। এক সময়ে ক্ষমতাবানের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ক্ষোভকে খুব সফলভাবেই ধারণ করতে পেরেছিল এই আন্দোলনগুলো। কিন্তু, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসতে থাকে। ফলত এটা অসম্ভব নয় যে, মানুষের প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ক্ষোভ কোথাও কোথাও সেক্যুলার প্ল্যাটফর্ম না পেয়ে মৌলবাদের ছাতার তলায় চলে আসছে। ব্যাপারটা মোটেই ভাল নয়, কিন্তু এটা একটা বাস্তব সম্ভাবনা। ওইসব আন্দোলনের ধ্বংসাবশেষ থেকে উপাদান আত্মসাৎ করে মৌলবাদ লাভবান হচ্ছে কিনা, সেটা একটা ভাল গবেষণার বিষয় হতে পারে।
প্রশ্ন - (২) উন্নত পশ্চিমী শক্তিগুলোর কাছে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও ধর্মের মৌলবাদে (খ্রিস্টান হিন্দু বৌদ্ধ ইত্যাদি) মদত দেবার সুযোগ আছে কি আদৌ? যদি না থাকে, তাহলে তা কি আবারও ইসলামীয় মৌলবাদী জঙ্গিপনার পেছনে একমাত্র ইসলাম-বহির্ভুত কারণই ('মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গুলিহেলন' ইত্যাদি) নির্দেশ করছে না?উত্তর - মদত দেবার সুযোগ নেই --- এ কথার অর্থ কী? যাদের ক্ষমতা আছে, অর্থ আছে, যোগাযোগ আছে, তাদের সুযোগ তো সব সময়েই আছে! খ্রিস্টান মৌলবাদকে আলাদা করে মদত দেবার আছেটাই বা কী, ওরা তো এমনিতেই পশ্চিমী দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক শক্তির (বিশেষত আমেরিকার) এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ (সেক্যুলার রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে লড়াইয়ে ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে, যদিও)! রাষ্ট্রের কাছ থেকে নানা ছাড় ও অনুদান আদায় করা, প্রগতিবিরোধী নানা সংরক্ষণশীল বিধান ক্রিয়াশীল করানোর জন্য রাষ্ট্রকে চাপ দেওয়া, ধর্মীয় শিক্ষার পরিসর ক্রমেই চওড়া করার চেষ্টা করা, আধুনিক অর্থনীতির মধ্যে থেকে নানা বাঁকা ও গলিপথে অর্থ নিষ্কাশন করে চার্চের অর্থভাণ্ডার বাড়ানো, সেক্যুলার ও বাম রাজনীতিকে নানাভাবে সীমাবদ্ধ করে দেবার চেষ্টা করা, জাতীয়তাবাদী আবগকে সব সময়েই ধর্মের রঙে রাঙিয়ে রাখার চেষ্টা করা, আন্তর্জাতিক প্রতিস্পর্ধাকে সামরিকভাবে আক্রমণ করার জন্য জনমত সংগঠিত করা এবং রাষ্ট্রকে চাপ দেওয়া --- এসব তো তারা ক্ষমতাবৃত্তের ভেতরে থেকে এবং তার অংশ হিসেবেই করতে পারে। আলাদা করে 'সুযোগ'-এর দরকার কী? তবু তা সত্ত্বেও, ব্যাকফায়ার তো করেই, যেমনটি guru বলেছেন।
প্রশ্ন - (৩) যেখানে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সঙ্কট আছে, সেখানে তো ইসলাম না থাকলেও জঙ্গি আন্দোলনের উৎপত্তি হতে পারে (যেমন শ্রীলঙ্কায় LTTE), তাহলে ইসলামে মৌলবাদী জঙ্গিপনার উদ্ভবের কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট দেশ তথা সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সঙ্কটের অনুসন্ধান না করে ইসলামের নিজস্ব গুণগত বৈশিষ্ট্য খুঁজে বেড়ানো কতটা সঠিক কাজ?উত্তর - কোনও ঘটনার 'কারণ' বলতে ঠিক কী বোঝেন? আমি যা বুঝি তা হচ্ছে মোটামুটি তিন রকমের জিনিস। 'ইন্টার্নাল স্ট্রাকচার' বা আভ্যন্তরীণ কাঠামো বা পরিস্থিতি, 'এক্সটার্নাল কন্ডিশন' বা বহিঃস্থ পরিস্থিতি, এবং 'ট্রিগারিং ফ্যাক্টর' বা অব্যবহিত পূর্ববর্তী উদ্দীপক ঘটনা। ধরুন, একটা বোমা ফেটে গেল। কেন? কারণ ওতে এখুনি আগুন দেওয়া হয়েছে ('ট্রিগারিং ফ্যাক্টর'), কারণ ওর ভেতরে খুব আঁট করে বারুদ ঠাসা আছে ('ইন্টার্নাল স্ট্রাকচার' --- ভেতরে খোয়া ক্ষীর থাকলে ফাটত না), এবং কারণ, ওর চারধারে ঠিকঠাক তাপমাতেয়া আর অক্সিজেনের সরবরাহ আছে ('এক্সটার্নাল কন্ডিশন' --- বোমাটা তরল নাট্রোজেনের ভেতরে থাকলে ফাটত না)। এই সব রকমের 'কারণ' মিলেজুলে বোমাটাকে ফাটিয়ে তোলে। এখানেও ঠিক সেইভাবে ভাবুন।ইসলামীয় ধর্ম ও সমাজের আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যগুলোকে একমাত্র নির্ধারক ধরা উচিত নয়, সে তো ওপরে বলেইছি। কিন্তু, তার কোনও ভূমিকাই নেই বা থাকতে পারেনা, এতবড় সার্টিফিকেট-টা কীসের ভিত্তিতে দেব?
প্রশ্ন - (৪) মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ একান্নটি রাষ্ট্রের মধ্যে একুশটি নয়, পঁচিশটি 'সেক্যুলার' বা ধর্মনিরপেক্ষ। ইসলামের নিজস্ব গুণগত বৈশিষ্ট্য তার বিপরীত হলে এইটা ঘটতে পারল কীভাবে?উত্তর - আমার তো মনে পড়ছে, একুশটাই দেখলাম। যাকগে, পঁচিশটা হলেই আমি খুশি হই, তবে একুশ না পঁচিশ তাতে মূল প্রশ্নে কিছু যাবে আসবে না। আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন, "ইসলামের নিজস্ব গুণগত বৈশিষ্ট্য তার বিপরীত হলে পঁচিশটি মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারল কীভাবে?" --- আমি তাহলে ঠিক একই যুক্তিতে পালটা প্রশ্ন করতে পারি --- "ইসলামের নিজস্ব গুণগত বৈশিষ্ট্য তার বিপরীত না হলে, এই একুশ শতকেও, বাকি ছাব্বিশটি মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ না হতে পারল কীভাবে?"এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, বর্তমান পৃথিবীতে পুরোপুরি ধর্ম-চালিত রাষ্ট্র আছে মাত্র ছটি, এবং তার মধ্যে পাঁচটিই মুসলমান --- সৌদি আরব, আফগানিস্তান, মাউরিটানিয়া, ইয়েমেন এবং ইরান। একটি মাত্র খ্রিস্টান --- শহর-রাষ্ট্র ভ্যাটিক্যান, যাকে প্রতি মুহূর্তে আধুনিক রাষ্ট্র ইতালির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়।
আপনি আরও দুটো প্রশ্ন জুড়তে চেয়েছেন।
প্রশ্ন - (৫) আঠারোটা মত প্যান ইসলামিস্ট গ্রুপ ঐ নির্দিষ্ট সময়ে গজিয়ে ওঠার জন্য ইসলাম বহির্ভূত কারণ হিসাবে পশ্চিমের পুঁজিপতিদের ফিনান্স করা ছাড়া অন্য কারণও থাকতে পারে, কিন্তু মুসলিম সমাজের বা মুসলিম মেজরিটি রাষ্ট্রের ধর্মীয় কারণে নিজস্ব কারণও থাকতে পারে, এমনটা ভেবে নেওয়ার অ্যালিবাই কী?
উত্তর - ওপরের (১) এবং (৩) নম্বর প্রশ্নের উত্তর একত্র করলে কোনও একটা ব্যাখ্যা দাঁড়াচ্ছে কি?
প্রশ্ন - (৬) "আপনি বলছেন, পশ্চিমা পুঁজিবাদীরা এটা পারল কী করে,সব জায়গাতেই তারা যা চেয়েছে, তা পারেনি।" এক্ষেত্রে, তারা "চেয়েছে কিন্তু পারেনি" এরকম একটা দুটো দৃষ্টান্ত দিলে ভাল হয়।উত্তর - এ ধরাধামের কোনও মহাশক্তিমানই কি সব ব্যাপারে যা খুশি তাই করতে পারে? 'রিয়্যালিটি' এক মস্ত শক্তিশালী এবং জটিল জিনিস ভাই! কোনও শক্তিমানই কি তার পুরো তল পায়, হাজার জ্ঞানীগুণীর সাহায্য নিয়েও? তাইই যদি পাবে, তো আমেরিকা তবে ছোট্ট ভিয়েতনাম থেকে মুখ পুড়িয়ে ফিরে এলো কেন? খোদ সোভিয়েত রাষ্ট্র বিনাশ হয়ে যাবার পরেও আমেরিকার বুকের কাছে বসে ছোট্ট কিউবা কীভাবে অটুট থাকে? আফগানিস্তানে মুজাহিদদের মদত দিয়ে সোভিয়েত-পন্থী সরকারকে হঠিয়ে মৌলবাদীদের প্রতিষ্ঠা করার দেড় দশক পরেও সে পাপ কীভাবে খোদ আমেরিকার সুরক্ষিত শক্তিকেন্দ্রে নাইন ইলেভেনের আতঙ্ক হয়ে ঝরে পড়ে? মহাশক্তিমানেরা রিয়্যালিটির অংশমাত্র, তার প্রতিস্পর্ধী নয়।
-
Debasis Bhattacharya | ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ ২১:২৪514936
- guru,আপনার কথাগুলোয় পরে আসছি।
 guru | 103.211.20.30 | ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ ২৩:০৮514937
guru | 103.211.20.30 | ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ ২৩:০৮514937- @দেবাশিষ বাবু আপনার রাধার কানাই এর প্রশ্নের উত্তরগুলি পড়ে ভালো লাগছে | বিশেষ করে শেষ যে উত্তরটি দিলেন সত্যি ভীষণ আশা জাগানোর কথা | তাহলে সত্যি ইতিহাসের কাছে পার্মানেন্ট সর্বশক্তিমান বলে কেউ নেই | মানুষের আশার জায়গা তাহলে আছে |আমি নিজে 1980-2020 সালের এই timeline এর মধ্যে রাধার কানাই যে মুসলীম জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর উল্লেখ করছেন সেগুলোকে একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ অঞ্চলের ভূ রাজনীতির ফসলের বাইরে আর কিছু ভাবতে পারিনা | আম্রিকার বর্তমানে শত্রু রাশিয়া ও চীন | আফগানিস্তান থেকেও সেনা সরিয়েছে আম্রিকা | সিরিয়া নিয়ে রাশিয়া তুর্কি ইরান মিলে একটি শান্তি প্রস্তাব আনছে | সেটিতে ভবিষয়তে শান্তি ফিরতেই পারে |সত্যি কথা বলতেকি মুসলিম জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি এখন পর্যন্ত ইতিহাসে এমন কিছু সুদূরবর্তী পরিবর্তন আন্তে পারেনি | গত কয়েক বছরে সেইভাবে তাদের দেখতেও পাওয়া যাচ্ছেনা | ভারতে শেষ বড়ো জঙ্গী ঘটনা ২০০৮ সালে এবং সেটি কে করেছিলো নিয়েও অনেক বিতর্ক আছে | এখন পর্যন্ত পশ্চিম এশিয়ার ও উত্তর আফ্রিকার কিছু অংশ বা আফগানিস্তান পাকিস্তান বর্ডার এর অংশ গুলিতে কিছু সন্ত্রাসবাদী সংঘটন আছে কিন্তু যেহেতু আম্রিকা মূল শত্রু মনে করে চীন ও রাশিয়াকে সেই কারণেই এইসব এলাকা নিয়ে আম্রিকা খুব বেশী মাথা ঘামাচ্ছেনা | সেকারণেই আমি এইসব এলাকাতে যেসব সন্ত্রাসবাদী সংঘটন আছে তারা লোকাল ভূ রাজনীতি এর উপরে নির্ভরশীল থাকবে এবং খুব বড়োমাপের কিছু ঘটনা ঘটাতে পারবেনা |পরিশেষে বলি যে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম প্রধান দেশগুলি যেমন মিশর আলজেরিয়া লিবিয়া এখানে যদি নিয়মিত ভাবে অবাধে মুক্ত নির্বাচন হয় ও নির্বাচনে যদি মুসলিম ব্রাদারহুড জাতীয় শক্তি গুলিকে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতে ও জিতে ক্ষমতায় আস্তে দেওয়া হয় তাহলে জঙ্গিবাদের আর প্রয়োজন হবেনা | পাকিস্তান ও লেবাননে আমরা এটাই দেখেছি যে রাষ্ট্র আস্তে আস্তে সশস্ত্র জঙ্গি গোষ্ঠীগুলিকে নির্বাচনের মধ্যে নিয়ে এসে জঙ্গিপনা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে | নেপালের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে মাওবাদী নেতা প্রচন্ড প্রায় ১০-১৫ বছর ধরে সশস্ত্র সংগ্রামের পরে অবশেষে নির্বাচনে আসার সিদ্ধান্ত নেন ও এখন তিনি নেপালের প্রধানমন্ত্রী |এই বিষয়ে আপনার মতামতের অপেক্ষাতে রইলাম |
-
Debasis Bhattacharya | ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ ২৩:৫৮514939
- রাধার কানাই,আপনার আরও একটি প্রশ্ন ছিল, সেটা এই রকম ---"ULFA, অগপ, তিপ্র্যালান্ড, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (যারা আলাদা গোর্খাল্যান্ড দাবি করে ইত্যাদি) এদের জন্মেরও বিভিন্ন কারণ আছে, এখন এই গোষ্ঠীগুলোর ধর্মকে আমরা কাঠগড়ায় তুলছি না, অথচ আমার মেনশন করা গোষ্ঠীগুলোর অনেকগুলোই কোন রাজনৈতিক কারণে উদ্ভুত হয়, সেটা জানার পরও তাদের ধর্মকে কাঠগড়ায় তুলছি কেন?"এর উত্তর guru ওপরে একভাবে দিয়েছেন, এবং খানিকটা বিস্তারিতভাবেই দিয়েছেন। আমার কাছে এর একটা অতিশয় সংক্ষিপ্ত এবং সাদাসিধে উত্তর আছে। সেটা guru-র উত্তরের পরিপূরক হয় কিনা, দেখা যাক।উত্তরটা হচ্ছে, উপরোক্ত গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক কারণে এবং তীব্র রাজনৈতিক দাবি নিয়ে হাজির হলেও তাদের ধর্মকে আমরা কাঠগড়ায় তুলি না, কিন্তু ইসলামীয় জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রে তা করি, কারণ, দ্বিতীয়োক্তেরা যা করে তা ধর্মের নামেই করে, এবং অন্যেরা তা করেনা।যারা নিজেরা চায় যে তাদেরকে একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবেই শনাক্ত করা হোক, এবং তাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা আচরণ ও অভিপ্রায়কে ধর্মীয় প্রেক্ষিতেই দেখা হোক, তাদের ক্ষেত্রে আমাদের অপশনটা কোথায়?
 &/ | 151.141.85.8 | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ০১:০৫514940
&/ | 151.141.85.8 | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ০১:০৫514940- এত বছরে গুরুচন্ডালিতে যত লেখা পড়েছি, সেসবের মধ্যে এই লেখাটি অন্যতম সেরা। আর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও বটে। এটি যদি কোনোদিন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তাহলে বড় বড় মন্তব্যগুলো সমেত প্রকাশ হওয়া উচিত। কারণ সেসব মন্তব্য থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস উঠে আসছে।
লেখক ও মন্তব্যকারী সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা।
-
Debasis Bhattacharya | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ০২:০০514941
- guru,কোনও বিশেষ দিন-ভিত্তিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের প্রশ্নে আমি একটু যেন অস্বচ্ছন্দ, সঙ্কুচিত, প্রত্যাহৃত থাকি। তবু, আপনাকে ধন্যবাদ, আপনিও আমার শুভেচ্ছা নেবেন।আপনি ওপরে যা বলেছেন, তার মধ্যে অনেক কিছুই খুব চিত্তাকর্ষক। এর সব কিছুই যে আমি খুব ভাল জানি, এমনটাও না। তবু, যৎসামান্য যা জানি, এবং তার ভিত্তিতে যেমন যা মনে হয়, একটু বলি। এর মধ্যে কিছু ইঙ্গিত নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে যা বলেছি তাতে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। বাকি আর কী কী আছে, দেখি।(১) খ্রিস্টীয় মৌলবাদীদের জঙ্গিপনার কথা আপনি বেশ গুরুত্ব দিয়েই উল্লেখ করেছেন, আমি তাতে সায় দিয়ে একটা কথা যোগ করব। খ্রিস্টীয় জঙ্গিরাও ইসলামীয় জঙ্গিদের মতই নাশকতাপ্রবণ, কিন্তু দুটোর মধ্যে তফাত আছে। ইসলামীয় নাশকতাগুলো যেমন বেশিরভাগই বড়সড় সাংগঠনিক প্রক্রিয়া ও যৌথ পরিকল্পনার ফসল, খ্রিস্টীয় জঙ্গিদের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। এদের সঙ্গে নানা ওই ধরনের সংগঠনের যোগাযোগ থাকে এবং তার মধ্যে দিয়ে জঙ্গির অভিপ্রায়টি সংহত হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাশকতার ঘটায় এক বা অতি অল্প কয়েক জন ব্যক্তি, গোটা পরিকল্পনা রূপায়ণ খরচ ইত্যাদি সবই তার বা তাদের। অর্থাৎ, খ্রিস্টীয় জঙ্গিপনা মূলত 'লোন উল্ফ্ ফেনোমেনন', কিন্তু ইসলামীয় জঙ্গিপনা তা নয়।(২) আপনার কথা থেকে যতটুকু বুঝলাম, আপনি ইসলামীয় জঙ্গিপনাকে উন্নত পশ্চিমী বিশ্বের তরফে একটা এক বিশুদ্ধ ইকো-জিও-পোলিটিক্যাল নির্মাণ বলে মনে করেন। আমি একে মোটেই উড়িয়ে দিতে চাই না, কিন্তু শুধু দুটো কথা বলতে চাই। এক, ইসলামীয় সমাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস ছাড়া এ নির্মাণকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। এবং দুই, মৌলবাদী উত্থান যেহেতু সব কটি প্রধান ধর্মেই হয়েছে, অতএব পশ্চিমী প্রকল্প ব্যতিরেকেই সব ধর্মের সাধারণ সাম্প্রতিক বিকাশ হিসেবে 'মৌলবাদ' ব্যাপারটার এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও প্রক্রিয়া আছে।আপনার আরও প্রশ্ন আছে, মনে আছে। তার কথায় পরে আসছি।
-
Debasis Bhattacharya | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ১৪:২৯514947
- guru,এবারে আপনার অন্য প্রশ্নগুলো।(১) ভারতে মস্ত মস্ত পণ্ডিতেরা বলেছেন, ভারতে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ব্যাপারটা নাকি ইউরোপের মত হওয়া উচিত নয়। এখানে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা রাখার দরকার নেই, বরং রাষ্ট্র সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করে চলবে এটাই নাকি হওয়া উচিত। শুধু রাধাকৃষ্ণণের মত ধর্ম-গদগদ বা আশিস নন্দীর মত আধুনিকতা-বিরোধী নয়, এমন কি অমর্ত্য সেনের মত সত্যিকারের আধুনিক ও সেক্যুলারকেও এই প্রশ্নে নরম এবং ধোঁয়াটে হতে দেখেছি। পরিষ্কার করে বলা দরকার, এই ব্যাপারটা আমাকে খুব বিরক্ত করে। প্রথমত, যুক্তির দিক 'সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করা' কথাটার কোনও মানেই হয়না, বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাস আর রীতিনীতিগুলো এতটাই আলাদা। আমি সকলের নিজস্ব মতামত ও বিশ্বাস পোষণ প্রচারের অধিকারটাকে শ্রদ্ধা করতে পারি, প্রশাসনের তরফে যেন বিশ্বাসের ভিত্তিতে ভেদাভেদ না করা হয় তার পক্ষেও সওয়াল করতে পারি, কিন্তু ঠিক-ভুল বিচার না করে সকলের সব কটা বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করতে যাব কোন দুঃখে, এ কি মামাবাড়ির আবদার নয়? এবারে, এই ননসেন্স-টিকে 'সর্ব ধর্ম সম ভাব' নামক একটি উদারগন্ধী ধামা দিয়ে চাপা দিলে ঠিক সেটাই হবার কথা, যা আজ হচ্ছে। এর প্রথম ধাপ হচ্ছে রাজনীতি আর প্রশাসনে ধর্মের অনুপ্রবেশ ('ধর্মনিরপেক্ষতা'-র ভারতীয় সংস্করণে প্রশাসনের সঙ্গে ধর্মের সংশ্রব নিষিদ্ধ নয় তো)। আর দ্বিতীয় ধাপটা হচ্ছে, ধর্মের প্রতি এই প্রশ্রয়ের সিংহভাগ ঝোলটুকু সংখ্যাগুরু ধর্মের কোলে টেনে আনা (আহা, রাজাসনে বসে ধর্মকর্ম বেশি তো করিনা, কিন্তু যা সামান্য একটু করি সেটা তো আমাদের ধর্মই হবে, কারণ আমরাই সংখ্যাগুরু, সব জায়গায় তো আমরাই আছি)। এই দ্বিতীয় ধাপটা যখন কাঁচা ছিল তখন থানায় কালীপুজো, বাবার থানে গিয়ে বাবার পায়ের বুড়ো আঙুল মাথায় ঠেকানো, নারকোল ফাটিয়ে সাবমেরিন উদ্বোধন --- এইসব অবধি চলতে পারত। এখন সেটি বেশ পোক্ত হয়ে ওঠায় খোদ পার্লামেন্টের ছাদে মুখ খেঁচানো অশোকস্তম্ভ বসিয়ে গেরুয়া বসন পরে বেশ খোসমেজাজে যাগযজ্ঞ করা যাচ্ছে।আমার মতে, পশ্চিমী ধর্মনিরপেক্ষতাকে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা ছাড়া এই কুৎসিত ব্যাধি থেকে আমাদের মুক্তি নেই।(২) হ্যাঁ, আমি তো বলেইছি যে মৌলবাদ হল আধুনিকতার উপজাত বস্তু (এবং সেইহেতু ধর্মের চিরকালীন আদিম অন্ধত্ব হিংস্রতা ও অযুক্তি থেকে তার পার্থক্য আছে)। এখন, আধুনিক শিক্ষা যেহেতু আধুনিকতার এক অপরিহার্য উপাদান, অতএব এখানে শিক্ষাও একটা ফ্যাক্টর তো বটেই। আমি গত পর্বে বলেছি, মৌলবাদীরা আধুনিক পৃথিবী সম্পর্কে জানেও, এবং তাকে সচেতনভাবে প্রত্যাখান করতে চান। আধুনিক শিক্ষা কিছুমাত্র না থাকলে তো সেটা পারা যেত না। তবে, উপজাতকে 'ফল' বলাটা কতদূর সঙ্গত, এখানে মূল প্রশ্নটা বোধহয় এটাই।অ্যালার্জি-প্রতিক্রিয়াকে পেনিসিলিন-এর 'ফল' বলে দাবি করা যতদূর সঙ্গত, অন্তত ততদূর সঙ্গত তো বটেই!
-
Debasis Bhattacharya | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ১৫:১৮514949
- guru,এবার আপনার শেষ প্রশ্নদুটো।(১) হ্যাঁ। একুশ শতক যত গড়াচ্ছে, ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের বাজার ততই নিচুর দিকে যাচ্ছে, সম্পূর্ণ একমত (ওপরে বলেওছি)। এবং, আমার মতে, এ প্রক্রিয়া অপ্রত্যাবর্তনীয় (irreversible), অর্থাৎ যা যাচ্ছে তা চিরকালের জন্যই যাচ্ছে। মৌলবাদ কিছুকালের জন্য ধর্মকে চাগিয়ে তুলতে পেরেছিল বা পারছে, কিন্তু তার খেসারত হিসেবে ভাবীকালের জমিতে ধর্মের কবরটি বেশ চওড়া এবং গভীর করেই খুঁড়ছে। ইতিমধ্যে, একদিকে ভূ-রাজনৈতিক-সামরিক দাবার বোড়ে হিসেবে তাদের বাজারমূল্য কমছে, এবং অন্যদিকে পশ্চিমী শক্তিগুলোও আগুন নিয়ে খেলা করার বিপদ বুঝতে পারছে। ফলত, টিঁকে থাকার বাস্তব ভিত্তিগুলোও ক্রমেই নড়বড়ে হয়ে পড়ছে, এবং আরও পড়তে থাকবে দিনকে দিন।(২) এবং হ্যাঁ, বন্দুকের বিরুদ্ধে পাল্টা বন্দুকবাজিটা সঠিক পথ নয়, দীর্ঘ ও কষ্টকর সংলাপের মধ্য দিয়ে মূলস্রোতে তাদেরকে টেনে আনাটাই প্রকৃত সমাধানের রাস্তা। এতেও একশো ভাগের ওপরে দুশো ভাগ একমত। আর যেটা রাস্তা সেটা হচ্ছে গরিব মানুষের আয়বৃদ্ধি, সুলভ কর্মসংস্থান, বিনামূল্যে ভাল মানের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, দক্ষ নিরপেক্ষ দুর্নীতিমুক্ত আইন ও প্রশাসন (পরের পর্বে এ নিয়ে হয়ত আরও কিছু বলার সুযোগ আসবে)। কিন্তু, কে করবে এসব?আমাদের সব বুদ্ধিশুদ্ধি আর সদিচ্ছা ঠিক এইখানে এসেই আটকে যায় যে!
 রাধার কানাই | 42.110.162.14 | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ১৫:২০514950
রাধার কানাই | 42.110.162.14 | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ১৫:২০514950- @গুরু আপনি কিছুটা আগের মন্তব্যে একটা প্রশ্ন করেছেন, " মোসাদেক,জিন্মা,সাদ্দাম হোসেন ,এরদোয়ান আর ইমরান খান- এদেরকে আমি ইসলামিস্ট মনে করি কিনা।মোসাদেক সম্পর্কে বিস্তৃত জানি না,অন্ততঃ এখানে মন্তব্য করার মত তো নয়ই। কিন্তু বাকি চারজন ইসলামিস্ট নয়,কিন্তু প্রশ্নাতীতভাবেই স্বৈরাচারী। আর ইরাক ইরান যুদ্ধের সময় তো সাদ্দাম হোসেন এর সঙ্গে আমেরিকার যোগসাজশও ছিল, অস্ত্র দেওয়া নেওয়াও ছিল।পরে ঘুরে যায় পরিস্থিতি। তাই এরা ইসলামিস্ট নয় এটা যেমন ঠিক , একইসাথে অনেকে এদের যেমন বিপ্লবী বা প্রতিবাদী মনে করে সেটাও নয় ,প্রশ্নাতী তভাবেই স্বৈরাচারী।আমার ধারণা এটাই।
-
Debasis Bhattacharya | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ১৫:২১514951
- &/, এসব কখনও বই হয়ে বেরোবে কিনা, সেটা আমারও জানা নেই। তবে, আপনার মন্তব্যে ভরসা পেলাম। ধন্যবাদ!
 guru | 103.175.169.143 | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ১৯:২৫514955
guru | 103.175.169.143 | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ১৯:২৫514955- @দেবাশীষ বাবু অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার আমার প্রশ্নগুলির অনেক ধৈর্য্য ধরে উত্তর দেবার জন্য | আমি গুরুতে কখনো এতো অর্থবহ ও গভীর আলোচনা দেখিনি | নিজেকে অনেকটা ঋদ্ধ লাগছে |১ | আপনার শেষের পয়েন্টটাই সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমার | দেখুন এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশেই এখনো সেইভাবে মানবতামূলক উন্নয়ন হয়নি এই দেশগুলি শুধুমাত্র পোস্ট কলোনিয়াল ভূ রাজনৈতিক ব্যবস্থা মাত্র , দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের ডিপো | বহু ক্ষেত্রেই এই অরাজক ও স্বৈরাচারী সরকারগুলো উন্নত পশ্চিমী দেশগুলোর সমর্থন ও আশীর্বাদের উপর পুষ্ট | আপনি যে মুসলীম প্রধান দেশগুলোয় নিজস্ব সেক্যুলার সরকারের কথা বলছেন তাদের অনেকেই কিন্তু আম্রিকি পুতুলমাত্র এবং অত্যাচার দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের ডিপো| যেমন ধরুন মিশর আলজেরিয়া মরোক্কো ইরাক সুদান জর্ডন UAE কুয়েত বাহরাইন প্রভৃতি | আম্রিকার একজন বিশিষ্ট পন্ডিত ড্যানিয়েল পাইপস এর সঙ্গে আমি নিজে কথা বলে জেনেছি উনি বলেছেন যে আম্রিকার ভয় যে ওই দেশগুলোতে অবাধ নির্বাচন হলে মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো অনেক ইসলামী জাতীয়তাবাদী সংঘটন ক্ষমতা দখল করে নেবে যারা হয়তো আম্রিকার কথা শুনবেনা | এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হচ্ছে যে 2011 সালে উত্তর আফ্রিকাতে জেসমিন বিপ্লবের পরে মিশরের হোসনি মুবারকের স্বৈরাচারী সরকার পড়ে গিয়ে গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত মুসলীম ব্রাদারহুডের মোহাম্মদ মুরসি সরকারকে আম্রিকা মিলিটারি ক্যু ঘটিয়ে ফেলে দেয় | আমি মনে করি পশ্চিমি সেক্যুলারিজম এর এটাই সবচেয়ে বড়ো কনট্রাডিকশন যেটি বিশেষ ভাবে মুসলীম বিশ্বে রাজনৈতিক অসন্তোষ তৈরী করছে ও মৌলবাদের পথ প্রশস্ত করছে |২ | আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি পশ্চিমি দুনিয়ার লিনিয়ার মডার্নিটি কেই একমাত্র আধুনিকতার পথ বলে মনে করেন | কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে এই পথ অনেকটাই আম্রিকি একমেরু বিশ্বের উপর নির্ভরশীল যেইখানে বিশ্ব অর্থনীতি একটি কোর পেরিফেরি সম্পর্কে আবদ্ধ যেইখানে আম্রিকা হচ্ছে কোর এবং সমস্ত বিশ্বের বাদবাকি দেশগুলি হচ্ছে পেরিফেরি অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের সম্পদ ওই কোর আম্রিকার কাছে আসবে | কিন্তু এর ফলে যে আর্থিক অসাম্য ও আর্থিক অন্যায় সূচিত হচ্ছে তার ফলে বিশ্বের বহু তৃতীয় বিশ্বের দেশেই এই পশ্চিমি দুনিয়ার লিনিয়ার মডার্নিটি এর উপরে বিদ্ধেষ তৈরী হচ্ছে | সমস্যা হলো পশ্চিমি বৈজ্ঞানিক আধুনিক শিক্ষার কাছে এই ঘটনার ব্যাখ্যা হয়তো আছে কিন্তু কোনো প্রতিকার নেই | এর ফলেই অনেক বেশী জঙ্গিবাদের সমস্যা তৈরী হচ্ছে |৩ | দেখুন বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হলেও বিজ্ঞানের একটি বড়ো সীমাবদ্ধতা হলো যে এশিয়া ও আফ্রিকার নিপীড়ত মানুষকে শান্তনা ও শান্তি দেবার কোনো ক্ষমতা নেই অন্তত আমি তো দেখিনা | বর্তমানে এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষের সামনে যে প্রবল আর্থিক অসাম্য তৈরী হয়েছে তার ফলে তাদের জীবনে আশার জায়গা নেই বললেই চলে এখন এই কারণেই তাদের ধর্মের কাছে আস্তে হয় নিজের জীবনে একটু আশা ও শান্তনা শোনবার জন্য | মৌলবাদীরা এই জায়গাটা চাইলে ব্যবহার করতে পারে | এবং মুসলিম দুনিয়াতে সেটাই হচ্ছে |৪ | "ইসলামীয় নাশকতাগুলো যেমন বেশিরভাগই বড়সড় সাংগঠনিক প্রক্রিয়া ও যৌথ পরিকল্পনার ফসল, খ্রিস্টীয় জঙ্গিদের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। এদের সঙ্গে নানা ওই ধরনের সংগঠনের যোগাযোগ থাকে এবং তার মধ্যে দিয়ে জঙ্গির অভিপ্রায়টি সংহত হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাশকতার ঘটায় এক বা অতি অল্প কয়েক জন ব্যক্তি, গোটা পরিকল্পনা রূপায়ণ খরচ ইত্যাদি সবই তার বা তাদের। অর্থাৎ, খ্রিস্টীয় জঙ্গিপনা মূলত 'লোন উল্ফ্ ফেনোমেনন', কিন্তু ইসলামীয় জঙ্গিপনা তা নয়।"তাই যদি হয় তাহলে 9/11, সংসদ হামলা মুম্বাই এটাক মাত্র একবার কেন হলো ? খোদ আমেরিকাতেই এই বছর ৬০০ এর বেশী আপনার ভাষায় "লোন উল্ফ্ ফেনোমেনন" হোয়েছে যাকে আম্রিকার ওরা রান্ডম শুটিং বলে থাকে | ইসলামীয় জঙ্গিপনা এতো ভালো সংঘটন থাকলেও মাত্র একবারের বেশি এটাক করতে পারলোনা ওদিকে খ্রিস্টীয় জঙ্গিরা তো ইচ্ছেমতো হামলা করছে যখন পারে এবং নিজের দেশেই নিজের নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে , কেন ?এর দুটো ব্যাখা হতে পারে | এক মুসলিম জঙ্গিরা আদৌ সেইভাবে দক্ষ ও সংঘটিত নয় আপনি যেইরকম বলছেন অথবা ওই 9/11 জাতীয় সন্ত্রাসের ঘটনাগুলি আমরা যা জানি সেইরকম হয়তো নয় | আমি আম্রিকার পল ক্রেইগ রবার্টস নামে এক অর্থনীতিবিদের কথা জানি যিনি আসলে ওসামা বিন লাদেন 9/11 করেছিল এই ব্যাপারটাকেই সত্যি মনে করেননা কেননা উনি মনে করেন 9/11 এর অনেক আগেই পাকিস্তানে কিডনি অসুখে ওসামা বিন লাদেন মৃত্যু হয়েছিল | আম্রিকার বুশ সরকারের ও মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের হাত আছে 9/11 এর পিছনে এটাই উনি মনে করেন |এখন আপনার মতামতের অপেক্ষাতে রইলাম |
 guru | 103.175.169.143 | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ২০:১৬514956
guru | 103.175.169.143 | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ২০:১৬514956- ৫ | "আমার মতে, পশ্চিমী ধর্মনিরপেক্ষতাকে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা ছাড়া এই কুৎসিত ব্যাধি থেকে আমাদের মুক্তি নেই। "আমি মনে করি তত্ত্বগতভাবে আপনার কথাটি সঠিক কিন্তু বাস্তবে পশ্চিমি অর্থনীতির মডেল সঠিকভাবে অনুসরণ না হলে কিন্তু পশ্চিমী ধর্মনিরপেক্ষতাকে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা অনুন্নত দেশের মানুষের পক্ষে অসম্ভব | এখন বর্তমান একমেরু বিশ্বের অর্থনীতির মডেল হলো কোর পেরিফেরি মডেল যেটির ব্যাপারে আমি আগের পোস্টেই লিখেছি | এই মডেলে পশ্চিমি দেশগুলি কোর ও এশিয়া আফ্রিকার বাদবাকি দেশগুলো পেরিফেরি | পেরিফেরির দেশগুলোতে আর্থিক অসাম্য এতো বেশি যার জন্য এই দেশগুলোর মানুষেরা এতটাই আর্থিক ও সামাজিক ভাবে লো কনফিডেন্স ও লো সেলফ এস্টিমে ভোগে যে তাদের পক্ষে কিছুতেই পশ্চিমী ধর্মনিরপেক্ষতাকে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়না | পশ্চিমী দেশগুলি কি এশিয়ার ও আফ্রিকার দেশগুলোকে কোর বানিয়ে নিজেরা পেরিফেরি হতে চাইবে যেইখানে এশিয়া ও আফ্রিকার গরিব দেশগুলির মানুষএর পক্ষে পশ্চিমি ধর্মনিরপেক্ষতাকে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা সম্ভব ? আমার তো মনে হয়না |
আমার এই প্রসঙ্গে 2020 সালের জানুয়ারী তে কলকাতা লিট্ ফেস্টে অমিতাভ ঘোষের একটি মন্তব্য মনে পড়ছে | উনি বলেছিলেন যে পশ্চিমি দুনিয়ার ধর্মনিরপেক্ষতার মূল রহস্য হলো যে গত কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপীয়ানদের আমেরিকা তে ঔপনিবেশিকরণের সাফল্য | এই হিস্টরিকাল ফেনোমেনন থেকেই ওরা এতো কনফিডেন্স পেয়েছে যার ফলে পরবর্তী কালে ওরা ধর্মনিরপেক্ষতাকে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করার সাহস পেয়েছে |
আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি যে আম্রিকা অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা এই তিনটি ভূখণ্ডকে যদি এশিয়ার মানুষ recolonize করতে পারে তাহলেই একমাত্র তারা ধর্মনিরপেক্ষতাকে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করার সাহস পাবে নচেৎ নয় |
আপনি কি মনে করেন ?
৬ | বর্তমানে আমি মনে করি ইসলামীয় জঙ্গিবাদের তুলনাতে islamopheobia আরো বেশি প্রাসঙ্গিক একটি ধর্মীয় মৌলবাদ | এই ফেনোমেনন টি কি ভারতের ধর্মের অভ্যন্তরীণ গঠন এর জন্য সৃষ্টি হয়েছে নাকি একটি আন্টি মডার্নিটি রিঅ্যাকশন ? আপনি কি মনে করেন ?
 দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 2401:4900:3142:aff3:0:47:405e:6301 | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ২১:১৫514957
দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 2401:4900:3142:aff3:0:47:405e:6301 | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ২১:১৫514957- guru,সর্বনাশ, আপনার এইসব নিয়ে ড্যানিয়েল পাইপ্স-এর সঙ্গে কথাবার্তা চলে নাকি? তাঁর যৎসামান্য দু-একটি লেখা নেট থেকে নিয়ে পড়ার সুযোগ হয়েছে আমার। আপনি তো পণ্ডিত লোক মশায়, আর আমি এক অত্যুৎসাহী অ্যাকটিভিস্ট মাত্র! আপনাকে এত সব বোঝাতে যাওয়া আমার ঠিক হয়েছে কিনা, সে নিয়ে এখন কিঞ্চিৎ লজ্জা ও আতঙ্কে আছি!
 guru | 103.175.169.143 | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ২১:৫৮514958
guru | 103.175.169.143 | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ২১:৫৮514958- ড্যানিয়েল পাইপ্স এর সঙ্গে প্রায় গত ১০ ১২ বছর ধরেই কথাবার্তা চালাচ্ছি | তবে আমি বিভিন্ন মতের মানুষের সঙ্গেই কথা চালাতে আগ্রহী | ওনার নিজস্ব একটি মত আছে এবং আমি ওনার বিরুদ্ধ মতের লোকের সঙ্গেও কথা বলেছি | পল ক্রেইগ রবার্টস যেইমন আম্রিকি পশ্চিম এশিয়াতে পলিসি নিয়ে ওর মতের বিরোধী কিন্তু আমি তার লেখাও পড়েছি |islamophoebia নিয়ে যেমন আমি আজ থেকে প্রায় ১ দশক আগেই দুজন আম্রিকি লেখক কেন ক্লিপেনস্টেইন ও পল Gottinger এর লেখাও পড়েছি ও তাদের সঙ্গে আলোচনাও করেছি |আমি রাধার কানাই কে যেইসব লেখকের নাম বলেছি যেমন পেপে এস্কোবার বা তারিক আলীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়নি | রবার্ট ফিস্কের সঙ্গে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে কথা বলার আর সুযোগ হবেনা ! ওদের শুধু লেখা পড়বার সৌভাগ্য হয়েছে |অমিতাভ ঘোষের মতটিও আমার মডার্নিটি নিয়ে একটি এক প্রশ্নের উত্তরেই ওই উল্লেখিত সম্মেলন টিতে দেওয়া |
 guru | 103.175.169.143 | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ২২:০৬514959
guru | 103.175.169.143 | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ২২:০৬514959- দেবাশীষ বাবু আপনার লেখাটি পড়ে ও আলোচনা করেও অনেকটাই ঋদ্ধ হয়েছি | চালিয়ে যান আপনি | বহুদিন এইরকম আলোচনা করার সুযোগ হয়না | শুধু একটি অনুরোধ করছি বিনীত ভাবে আপনি লেখা চালিয়ে যান |
 দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 2401:4900:3142:aff3:0:47:405e:6301 | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ২২:২৬514960
দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 2401:4900:3142:aff3:0:47:405e:6301 | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ২২:২৬514960- guru,একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি --- আপনি কি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স-এর সক্রিয় গবেষক? এই ধরনের লোকজন বাংলা ভাষায় আলোচনা সাধারণত করতে চান না। আপনি যদি তা চান, সেটা দারুণ ব্যাপার! এইসব বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে আরও কিছু ছাইপাঁশ লিখব, এ বাসনা আছে। সেক্ষেত্রে, আবারও আপনার সঙ্গে ইন্টেব়্যাকশনের অপেক্ষায় থাকব।
 guru | 103.175.169.143 | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ২৩:১২514961
guru | 103.175.169.143 | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ২৩:১২514961- @দেবাশিস্ বাবু আমি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস ও বিশ্বের ইতিহাসের ব্যাপারে আগ্রহী | বাংলা আমার মাতৃভাষা | আমার মাতৃভাষাতে এই নিয়ে মানুষকে জানাতে পারলে আমি সবচেয়ে খুশী হবো | আপনি লিখতে থাকুন আমার আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে খুবই ভালো লাগছে ও নিজেকে খুবই সমৃদ্ধ লাগছে |
 দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 2401:4900:3142:aff3:0:47:405e:6301 | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ২৩:৪০514962
দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 2401:4900:3142:aff3:0:47:405e:6301 | ০১ জানুয়ারি ২০২৩ ২৩:৪০514962- guru,অনেক ধন্যবাদ! আপনি আরও যা যা প্রশ্ন করেছেন সে ব্যাপারে আমার ধ্যানধারণা আমি সাগ্রহেই বলব। একটু সময় নিচ্ছি। বলবার সময়ে হয়ত অনেক ক্ষেত্রে আমার অ্যাকটিভিস্ট-সুলভ অ্যাটাচমেন্ট ফুটে বেরোতে পারে, অনুগ্রহ করে অপরাধ নেবেন না।আসলে কী জানেন তো, এই যে আমরা অযুক্তি ধর্মান্ধতা কুসংস্কার এইসবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করি, তাতে মাঝে মাঝেই মনে হয়, সমাজবিজ্ঞানীরা এইসব বিষয়ে কী বলেন সেইটা জানতে পারলে হয়ত কাজের অনেক সুবিধে হবে! সেই আশাতে গ্যাঁটের কড়ি খরচা করে বেশ কিছু বইপত্র সংগ্রহ করেছি। আপনি যে সব বই ও লেখকের নাম করলেন সেগুলো আমার কাছে নেই, তবে অন্য বেশ কিছু আছে। যেমন জুর্গেন্সমায়ার-এর 'টেরর ইন দ্য মাইন্ড অফ গড', বা হেক্টর আভালোস-এর 'ফাইটিং ওয়ার্ডস', এবং এই রকম আরও বেশ কিছু। আর সংগ্রহ করেছি অসংখ্য গবেষণাপত্র, থ্যাঙ্কস টু আলেকজান্দ্রা এলবাকিয়ান দিদি।এখন, এইসব পড়লেই তো হল না। পড়ে ঠিকঠাক বুঝছি কিনা বা সেখান থেকে যেসব উপলব্ধিতে পৌঁছচ্ছি সেগুলো বোকার মত হয়ে যাচ্ছে কিনা, সে সব নিয়ে একটা উদ্বেগ সব সময়েই মনের মধ্যে কাজ করে চলে।তাই, আপনাদের মত মানুষের মুখোমুখি পড়লে একটা ভ্যালিডেশন-এর সুযোগ ঘটে যায়!
 রাধার কানাই | 42.110.162.1 | ০২ জানুয়ারি ২০২৩ ১০:৫১514973
রাধার কানাই | 42.110.162.1 | ০২ জানুয়ারি ২০২৩ ১০:৫১514973- @গুরু আপনার এবং দেবাশিস্ দার আলোচনায় অবেক সমৃদ্ধ হয়েছি,অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা আপনাদের দুজনকেই। এখন বিভিন্ন মৌলবাদ, মৌলবাদের সংজ্ঞা, এর উদ্ভব ইত্যাদি নিয়ে দেবাশিস্ দা এই প্রবন্ধে তথ্যসমৃদ্ধভাবে আলোকপাত করেছেন, এমনকি উল্টোদিকে ইসলামোফোবিকদের অনেক অযুক্তিকেও ছেঁচে দিয়েছেন।আমি আপনাকে আরও একটা বাড়তি প্রশ্ন করছি।ইসলামোফোবিয়ার উদ্ভব,এর ডায়নামিক্স এবং এর পিছনের কুযুক্তিগুলোকে খণ্ডন করে যদি কোন ভাল বই ব গবেষণাপত্র থাকে,সেটাও / সেগুলোও সাজেস্ট করবেন প্লিজ? আগাম ধন্যবাদ আপনাকে
 guru | 146.196.47.98 | ০২ জানুয়ারি ২০২৩ ১২:০৭514974
guru | 146.196.47.98 | ০২ জানুয়ারি ২০২৩ ১২:০৭514974- @রাধার কানাই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে |ইসলামোফোবিয়া এখন সারা পৃথিবীতেই বিশেষ করে ভারতে একটি স্ট্রাকচারাল ইসু | ভারতে এই ইসলামোফোবিয়া নিয়ে জানার ও রিসার্চের অনেক স্কোপ আছে | পশ্চিমের দেশগুলির ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন ক্রুসেড ওয়ার অন টেরর এইধরণের ভূ রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব আছে যেইগুলির প্রভাব ভবিষ্যতেও থাকবে |আম্রিকায় ইসলামোফোবিয়া নিয়ে একটি বই হলো : "Islamophobia in America: The Anatomy of Intolerance" Khaled Beidoun |তবে ভারতে ইসলামোফোবিয়া নিয়ে অনেক ইন্টারনাল স্ট্রাকচারাল ইস্যু আছে | এখন ভারতীয় ও হিন্দু হওয়ার প্রধান ও প্রথম শর্ত হলো ইসলাম ও পাকিস্তানের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্ধেষ | এই ব্যাপারটিকে শুধুমাত্র কোনো রাজনৈতিক দলের ভোটে জেতার রাজনীতি নিয়ে দেখা ঠিক হবে বলে মনে হয়না | এই নিয়ে সেইরকম বই দেখছিনা তবে গাজালা ওয়াহাব একটি বই লিখেছেন "বর্ন এ মুসলিম " সেটি পড়ে দেখতে পারেন |একটি রিসার্চ পেপার আছে নিচে লিংক দিয়ে দিলাম যদিও এটি পুরোটাই আম্রিকাতে ইন্ডিয়ান আম্রিকান লবি কম্যুনিটি নিয়ে এবং তাদের মধ্যে ইসলামোফোবিয়া নিয়ে লেখা |
 guru | 146.196.47.98 | ০২ জানুয়ারি ২০২৩ ১২:১২514975
guru | 146.196.47.98 | ০২ জানুয়ারি ২০২৩ ১২:১২514975- @রাধার কানাই আরেকটি লিংক পেয়েছি পড়ে দেখতে পারেন |
 radhar kanai | 115.187.40.137 | ০২ জানুয়ারি ২০২৩ ১৪:৩০514979
radhar kanai | 115.187.40.137 | ০২ জানুয়ারি ২০২৩ ১৪:৩০514979- @গুরুঅনেক ধন্যবাদ আপনাকে
-
Debasis Bhattacharya | ০৩ জানুয়ারি ২০২৩ ০২:০৬514984
- guru,আপনার পরবর্তী প্রশ্নগুলোর জবাব দেবার চেষ্টা করছি, একসাথে নয়, দুটো একটা করে, একটু সময় নিয়ে নিয়ে।(১) আপনি যেভাবে মুসলমান-প্রধান দেশগুলোতে যত সেক্যুলার সরকার আছে বা ছিল তাদের সকলকেই দুর্নীতিগ্রস্ত অত্যাচারী এবং আমেরিকার হাতের পুতুল বলে দিচ্ছেন, এবং তাদের বিরুদ্ধে মৌলবাদী উত্থানকে সাম্রাজ্যবাদ-পোষিত স্বৈরাচারের প্রতিস্পর্ধী সংগ্রাম সাব্যস্ত করছেন, তার মধ্যে অন্তত দুটো ভুল আছে --- আমার মতে। প্রথমত, এর মধ্যে একটা অতিসরলীকরণ আছে, সব সময়ে ব্যাপারটা মোটেই ও রকম নয় (পুরোপুরি মিথ্যেও নয়, যদিও)। দ্বিতীয়ত, এর মধ্য দিয়ে মৌলবাদী জঙ্গিপনা সমীকৃত হয়ে যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরাচার-বিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামের সাথে, যে বিপদ সম্পর্কে আমি বরাবরই অতিমাত্রায় সতর্ক ছিলাম এবং আছি। মিশরে আমেরিকা মুসলিম ব্রাদারহুড-কে ক্যু ঘটিয়ে ফেলে দিয়েছে, হতেই পারে --- আমেরিকার তো সে গুণে ঘাট নেই। কিন্তু, ওটাকেই যদি একমাত্র সত্য বলে ধরেন, তাহলে আফগানিস্তানে সোভিয়েত-পন্থী নাজিবুল্লা সরকারকে হঠিয়ে তালিবানকে ক্ষমতায় আনার ঘটনাকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন, কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন পাকিস্তান এবং সৌদি আরবের সঙ্গে তার দীর্ঘকালীন সখ্যতার, এবং কীভাবেই বা ব্যাখ্যা করবেন ইরাকে সেক্যুলার সরকারকে হঠিয়ে এবং প্রবল ধ্বংসলীলা চালিয়ে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রাস্তাটি চওড়া করে বানিয়ে দেওয়ার? ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা, এমনিতে ইসলামীয় মৌলবাদকে মোটের ওপর ক্ষতিকর মনে করলেও, আমেরিকা কখনওই ইসলামীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে কোনও সুসঙ্গত, সুষম এবং নীতিগত অবস্থান নেয়নি। বস্তুত, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের স্থানিক ও তাৎক্ষণিক কৌশলগত কারণে আমেরিকা (এবং আরেকটু কম মাত্রায় ইউরোপও) যত না তার বিরোধিতা করেছে তার চেয়ে বেশি করে সাহায্যই করেছে।এখন, আপনার ধারণাটা জানতে চাই।(২) হ্যাঁ, আমি একজন অনুতাপহীন আধুনিকতাবাদী, এবং পশ্চিমী বা পশ্চিম-প্রভাবিত আধুনিকতা ছাড়া আর অন্য কোনও রকম 'আধুনিকতা' আমি অন্য কোথাও দেখতে পাইনা। তবে, যা আমি দেখতে পাইনা তা যদি আপনি আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমি অনুতাপহীন থেকে অনুতাপদগ্ধে পরিণত হতে রাজি আছি। ফলত, আমি আন্তরিকভাবে বিষয়টা আপনার থেকে বুঝতে চাইছি। অনুগ্রহ করে আমাকে এই কয়েকটি জিনিস একটু বুঝিয়ে বলুন --- (ক) আধুনিকতার সঙ্গে 'লিনিয়ার' বিশেষণটি জুড়ে আপনি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন? গণিতে উচ্চশিক্ষিত নই, তাও শুনেছি, এটি একটি গাণিতিক পরিভাষা, এবং গণিতের মধ্যেও তার নাকি আবার নানা অর্থ হতে পারে। স্কুলের জ্যামিতিতে ইউক্লীডীয় সরলরেখা 'লিনিয়ার'। স্কুলের বীজগণিতে 'লিনিয়ার' হল একঘাতবিশিষ্ট সমীকরণ। আবার, ডিফারেন্সিয়াল ইক্যুয়েশন-এ 'লিনিয়ার' মানে আরেক রকম ব্যাপার। সেই মোতাবেক, পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নেও কতকগুলো প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থা 'লিনিয়ার' আখ্যা পেতে পারে, যদি তাকে ওই ধরনের গাণিতিক সূত্র দিয়ে 'মডেল' করা যায়। এখন প্রশ্ন, আধুনিকতাকে আপনি 'লিনিয়ার' আখ্যা দিতে চান কেন? কোনও সমাজবিজ্ঞানী কি আধুনিকতাকে ওই ধরনের গাণিতিক সূত্র দিয়ে মডেল করতে পেরেছেন? একটু বুঝিয়ে বলবেন প্লিজ। আমি দেখেছি, আধুনিকতা-বিরোধীরা আধুনিকতাকে 'লিনিয়ার' এবং নিজেদেরকে 'নন-লিনিয়ার' আখ্যা দিয়ে এক অত্যাশ্চর্য সুখলাভ করেন। তবে, সে সুখ ঠিক কী এবং কেন, সে রহস্য আজও ভেদ করতে পারিনি। অনুগ্রহ করে উদ্ধার করবেন।(খ) আধুনিকতার মধ্যে, বা বিশেষত তার প্রচার-প্রসার-প্রভাবের প্রক্রিয়ার মধ্যে, নানা অসাম্য ও অন্যায় আছে, সে তো আর অস্বীকার করার জায়গা নেই। আর, যেখানে ও দুটো থাকবে, সেখানে অসন্তোষও অনিবার্য। কিন্তু, তার জন্য মৌলবাদী উত্থান হতে হবে কেন, অতীত কোনও এক স্বর্ণযুগে ফিরে চলার আহ্বান আসবে কেন? প্রাগাধুনিক যুগে কি অন্যায় ও অসাম্য এর চেয়ে কম ছিল?আপাতত এই দুটো জায়গায় পরিষ্কার হয়ে নিতে চাই।
 &/ | 151.141.85.8 | ০৩ জানুয়ারি ২০২৩ ০২:৩০514985
&/ | 151.141.85.8 | ০৩ জানুয়ারি ২০২৩ ০২:৩০514985- এইবারে খুব ভালো জায়্গায় এসে গেছে। অতি চমৎকার প্রশ্নোত্তর হচ্ছে। যত খোলাখুলি এসব হবে, ততই বহু ভুল ধারণা লোপ পাবে। স্বচ্ছতর হয়ে আসবে আমাদের দৃষ্টি। (মানে আশা করা যায় আরকি। নইলে সেই 'নজরুলের কবিতা টুকে টুকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পেয়ে গেলেন, তারপরে নজরুলকে ধুতুরা খাইয়ে পাগল করে দিলেন'---এইরকম টাইপের সব জিনিস ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে শেয়ার্ড হয় আর শেয়ার্ড হয়, আর কিছু লোকে বিশ্বাসও করে সেই কথামালার গল্পের মতন )
আপনাদের বিরাট ধন্যবাদ।
 দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 2401:4900:3146:fc1c:0:47:4107:c301 | ০৩ জানুয়ারি ২০২৩ ০৮:২৭514987
দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 2401:4900:3146:fc1c:0:47:4107:c301 | ০৩ জানুয়ারি ২০২৩ ০৮:২৭514987


-
Debasis Bhattacharya | ০৩ জানুয়ারি ২০২৩ ১১:৪৪514989
- guru,একটু সময় পেলেই আপনার প্রশ্নগুলোকে অ্যাড্রেস করে রাখতে চাইছি। সেই ধারায় :(৩) আপনি এই ঘটনায় কষ্ট পেয়েছেন যে, বিজ্ঞান এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষকে সান্ত্বনা ও শান্তি দিতে পারেনি। কিন্তু, আমি যতদূর বুঝি, মানুষকে সান্ত্বনা ও শান্তি দেওয়া বিজ্ঞানের কাজ নয়, বিজ্ঞানের কাজ বাস্তবতার স্বরূপ উপলব্ধিতে মানুষকে সাহায্য করা। সেটা ঠিকঠাক করা গেলে মানুষ নানা বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারে, জীবনকে আরও সহজ ও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। এবং, জীবন যথেষ্ট সহজ ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠলে আপনিই শান্তি আসে, তখন আর সান্ত্বনার দরকার পড়েনা। এখন আপনি এ কথা বলতেই পারেন যে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি মানুষকে খাটিয়ে বেশি বেশি সম্পদ তৈরি করার পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে ধনীর সংখ্যা ও ক্ষমতা বেড়েছে, অসাম্য ও শোষণ বেড়েছে, সাধারণ মানুষের ওপরে ক্ষমতাবানের নজরদারির ক্ষমতা বেড়েছে, ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র আবিষ্কার হয়ে হত্যালীলা বেড়েছে, বেপরোয়াভাবে সুখভোগের উপকরণ বানাতে গিয়ে পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে। সবই ঠিক। কিন্তু আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলুন, আধুনিকতা থেকে মুখ ঘুরিয়ে থেকে কি এশিয়া আর আফ্রিকা এ থেকে পরিত্রাণ পাবে? এশিয়া আর আফ্রিকার মানুষের কি মৌলকণার অভ্যন্তর, মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ বা জীবনের রহস্য এইসব জানবার আকাঙ্ক্ষা বা যোগ্যতা থাকতে পারেনা, তার প্রাপ্য শুধু অজ্ঞ ও অক্ষমের 'সান্ত্বনা ও শান্তি'? এশিয়া আর আফ্রিকার মানুষের কি পাকা বাড়ি পাকা রাস্তা গাড়িঘোড়া ফোন কম্পিউটর ওষুধপত্তর এইসব লাগবে না? এশিয়া আর আফ্রিকা যদি ইউরোপীয় আধিপত্যের সঙ্গে লড়াই করতে চায়, তবে কি পশ্চিমী বিজ্ঞানটা একটুখানি শিখে নিয়ে দরকারি অস্ত্রশস্ত্রগুলো নিজে বানিয়ে নেবার চেষ্টা করবে, নাকি বন্দুক বোমা আর ক্রুজ মিসাইলের হাত থেকে বাঁচার জন্য উপজাতীয় শামানকে ডেকে আনবে, যাতে তিনি পৌরাণিক দেবতাদেরকে যুদ্ধে নামাতে পারেন?এই বিষয়ে আপনার চিন্তা-ভাবনা জানার অপেক্ষায় রইলাম।
 guru | 115.187.51.147 | ০৩ জানুয়ারি ২০২৩ ১৬:৩৮514994
guru | 115.187.51.147 | ০৩ জানুয়ারি ২০২৩ ১৬:৩৮514994- @দেবাশীষ বাবু অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক সুন্দর ভাবে আমার প্রশ্নের উত্তরগুলি দেবার জন্য |১ | পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকাতে মুসলিম প্রধান দেশগুলিতে আমি মনে করি আমি মুক্ত ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের বিকাশ হলেই এই যেসব সমস্যাগুলি আপনি বলছেন অনেকভাবেই চলে যাবে যদিও হয়তো বেশ কয়েক দশক সময় লাগবে | তবে এটাও সঠিক যে কখনো কখনো এইভাবে এমন কোনো সরকার আস্তে পারে যাদের সঙ্গে হয়তো আপনার মতের একেবারেই মিল হবেনা যেমন মিশর ও আলজেরিয়াতে মুক্ত ও অবাধ নির্বাচন হলে ওখানে মুসলীম ব্রাদারহুডের ক্ষমতাতে আসার খুবই ভালো সম্ভাবনা | তবে এইসব ক্ষেত্রে আমার মনে হয় পশ্চিমী দুনিয়ার এইসব সরকারকে মেনে নেওয়াই উচিত যেহেতু ইস্রায়েল ও ভারতেও নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাতে আসা অ-সেক্যুলার সরকারকে তারা মেনে নিয়েছে | মেনে নেওয়ার সুফলও আছে | যেমন ধরুন টিউনিসিয়াতে আরব বসন্তের পরে an নাহিদা সরকার ক্ষমতাতে আসে যেটি আসলে সেই দেশের মুসলিম ব্রাদারহুডেরই একটি ফ্রন্ট | কিন্তু যেহেতু অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে তারা এসেছে সেই কারণে তাদের মেনে নেওয়া হয়েছিল এবং সেই কারণেই এই দেশটিতে আরব বসন্তের পরে অনেক পজিটিভ পরিবর্তন এসেছে | আসলে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত যে কোনো সরকারকেই মেনে নিলে এই রাডিক্যালিজম অনেকটাই কমে যাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে | তার সঙ্গে এটাও মেনে নিতে হবে যে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা সরকারগুলি অনেক সময়েই নিজের রাষ্ট্রীয় স্বার্থেই কাজ করবে যেই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সবসময়ে হয়তো আম্রিকার সঙ্গে এক হবেনা | এখন ঘটনা হচ্ছে পশ্চিমী দুনিয়ার তথাকথিত প্রগতিশীল মানুষেরা সবসময়ে এটা মেনে নিতে পারেননা যে গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত কোনো সরকার তাদের মতের বিরুদ্ধে কাজ করবে এবং এই কারণেই মুসলীম দুনিয়াতে তাদের বিরুদ্ধে একটি ফিলিং অফ injustice কাজ করে | এখন পশ্চিমি আধুনিকতার মানুষেরা যদি একটু উদার হয়ে মুসলিম দুনিয়াতে এই মুক্ত অবাধ নির্বাচনের পক্ষে বলেন তা সে যে মতভাবের দলই ক্ষমতাতে আসুক না কেন তাহলে অনেক সুফল হবে ভবিষয়তে |২ | লিনিয়ার আধুনিকতা মানে আমি বোঝাতে চাইছি যে পশ্চিমী আধুনিকতার মানুষেরা অনেকেই সারা পৃথিবীর মানুষকে একই রকম মনে করেন এবং মনে করেন যে সারা পৃথিবীতে আধুনিকতা তাদের দেশের মতো একই ভাবে আসবে | অর্থাৎ তাদের কাছে আধুনিকতার একটি মডেল হচ্ছে যে প্রথমে আসবে প্যাগানিজম তার পরে মনোথিইজম তার পরে সেক্যুলারিজম এবং সর্বশেষে নিহিলিজম বা শুন্যতা অর্থাৎ যেইখানে কোনো ধর্মেরই অস্তিত্ত থাকবেনা | এটাকে লিনিয়ার বলার কারণ হলো যে পশ্চিমীরা মনে করেন যে যেহেতু তাদের দেশে এইভাবেই আধুনিকতা এসেছিলো সারা পৃথিবীতেও সেই একিভাভেই আসবে |এখন ঘটনা হচ্ছে যে এশিয়া ও আফ্রিকাতে আর্থ সামাজিক ইতিহাস এইরকম ভাবে বিবর্তিত হয়নি কাজেই এইধরণের অতিসরলীকৃত আধুনিকতার প্রত্যাশাকেই আমি লিনিয়ার মডার্নিটি বোঝাতে চাই | আসলে যেসব সমাজ পশ্চিমের মতো একই পথে চলেইনি সেখানে পশ্চিমের ধাঁচের আধুনিকতা impose করতে গেলে তো রিঅ্যাকশন আসবেই যেটা আমরা দেখেছি |আসলে এশিয়া ও আফ্রিকার যেইসব সমাজে পশ্চিমের মতো শিল্পায়ন হয়নি এবং কলোনিজশন হয়েছে তাদের পক্ষে পশ্চিমের মতো আধুনিক হয়ে যাওয়া রাতারাতি প্রায় অসম্ভব | যতক্ষণ না সেইসব সমাজ শিল্পায়ন করে পশ্চিমকে colonize করতে পারবে ততক্ষন তারা পশ্চিমের মতো আধুনিক হতে পারবেনা |৩ | দেখুন আধুনিকতা অনেক ভাবেই আস্তে পারে | মূল কথা হচ্ছে আমার কাছে একটা দেশে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সুরক্ষিত থাকছে কিনা সেই আধুনিকতার প্রয়োগের ফলে সেটা দেখা | এখন রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বর্তমান বিশ্বে খুব কম দেশ আছে যারা একমেরু বিশ্বের অধীস্বরের থেকে আলাদা ভাবে চলার সাহস দেখাতে পারে | আমি আগেই বলেছি যে পাশ্চাত্য বিশ্বের কাছে আধুনিকতার যদি মানে হয়ে থাকে এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষের সঙ্গে কলোনিজশনের আমলের কোর পেরিফেরী সম্পর্ক বজায় রাখা তাহলে সেই আধুনিকতা এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষের দীর্ঘ মেয়াদি রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী |আফ্রিকাতে একটি প্রবাদ খুব চালু "মিশনারীরা আসার আগে কালোদের কাছে ছিল জমি ও সাদাদের কাছে ছিলো বাইবেল , মিশনারীরা আসার পরে সাদাদের হাতে রইলো জমি ও কালোদের হাতে রইলো বাইবেল "| আশা করি আপনি এইরকমের পশ্চিমি আধুনিকতার সমর্থন করবেননা |আমার কাছে ইসলামিক বিপ্লব পরবর্তী ইরান একটি আধুনিকতার মডেল যেইখানে ইসলামিক বিল্পবের পরে অনেক বেশি নারী শিক্ষা ও নারী ভোটাধিকার এসেছে | স্বাধীনতা পরবর্তী চীন ও ভারত এই দুটিও বেশ প্রাসঙ্গিক মডেল দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের জন্য | কিউবা ভিয়েতনাম বা ভেনেজুয়েলা এইগুলিও ছোট ছোট দেশের পক্ষে বেশ প্রাসঙ্গিক মডেল |ভারত চীন রাশিয়া ইরান তুর্কিয়ে এই দেশগুলি যেহেতু তাদের একটি কলোনিয়ালিজম-পূর্ব ইতিহাস আছে তাহলে তাদের নিজস্ব শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় স্বার্থ থাকতেই হবে এবং আমি মনে করিনা পাশ্চাত্যের মডার্নিটি মডেলটি সেই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে |নারী শিক্ষা প্রসার সমস্ত নাগরিকের জন্য ভোটাধিকার বিনা মূল্যে চিকিৎসা ও শিক্ষা খাদ্য নিরাপত্তা ও ওষুধ স্বনির্ভরতা এইগুলি সমস্ত এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলির রাষ্ট্রীয় স্বার্থ | কিন্তু পশ্চিমের পাশ্চাত্য মডার্নিটি ফসল IMF বা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক তাদের এই দিকে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতে দেয়না |এই দেখুন না এই তো ২০২২ সালের পাকিস্তানে গত ১০০ বছরের মধ্যে সবথেকে ভয়ঙ্কর বন্যাতে যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা বর্তমান যুদ্ধে উক্রেইনের ক্ষয়ক্ষতি থেকে অনেক বেশী | কিন্তু পশ্চিমি দুনিয়া পাকিস্তানের থেকে ইউক্রেইন্ কে অনেক বেশি সাহায্য করেছে শুধুমাত্র তাদের ভূ রাজনৈতিক স্বার্থে | IMF বা ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক কোনোরকম সাহায্য তো করেইনি উল্টে করের বোঝা ৪-৫ গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে | এইধরণের ব্যবহার পশ্চিমী আধুনিকতা কে মোটেই জনপ্রিয় করে তুলবেনা এটা বলাই বাহুল্য |আচ্ছা যেহেতু আপনি অনুতাপহীন পশ্চিমী আধুনিকতাবাদী, আপনি কি এইধরণের পশ্চিমী নিও-কলোনিয়ালিজম কেও পশ্চিমী আধুনিকতার অংশ মনে করেন ? আমি একজন চীনের নোবেলজয়ীর ব্যাপারে শুনেছি যিনি দুঃখ করে ছিলেন যে চীনকে পশ্চিমীরা সেইভাবে colonize করতে পারেনি তাই চিনে কোবিদ এসেছিলো | আমি কোনো ভাবেই এইধরণের দর্শনকে মানবতাবাদী ভাবতে পারিনা |পশ্চিমী ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ ও আচরণ পশ্চিমী আধুনিকতার একটি বড়ো কনট্রাডিকশন যেইখানে পশ্চিমী বিশ্বের বক্তব্য হলো "আমাকে অনুসরণ করোনা , আমি যা বলি শোনো "|৪ | আফ্রিকা ও এশিয়ার গরিব দেশগুলির গরিব মানুষের স্বার্থের জন্য তত্ত্বগত ভাবে পশ্চিমী আধুনিকতা হয়তো একটি ভালো মডেল কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে যতক্ষণ কলোনিয়াল আমলের কোর পেরিফেরি সম্পর্ক বজায় থাকবে পশ্চিমি উন্নত বিশ্ব ও এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে ততদিন এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে প্রকৃত পশ্চিমী আধুনিকতা আপনি ইমপ্লিমেন্ট করতেই পারবেননা |এই দেখুননা কেন গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য আম্রিকা ও ইউরোপ সবচেয়ে বড়ো দায়ী কিন্তু তারা সব দায় ঠেলে চাপিয়ে দিচ্ছে চীন ও ভারতের মতো গরীব দেশের জন্য | গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে এবছরের পাকিস্তানের বন্যাতে গত ১০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিন্তু পশ্চিমি বিশ্ব এব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলেছে |আপনী কি বলেন ??
 দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 2401:4900:7075:5c43:de76:8868:5758:e746 | ০৩ জানুয়ারি ২০২৩ ২০:০৩514996
দেবাশিস্ ভট্টাচার্য | 2401:4900:7075:5c43:de76:8868:5758:e746 | ০৩ জানুয়ারি ২০২৩ ২০:০৩514996- guru,আপনার পুরোনো প্রশ্নের ব্যাকলগ আগে ক্লিয়ার করে নিই, তারপরে আপনার নতুন কথাগুলোর উত্তর দেব। ইতিমধ্যে যদি আমার কথার প্রেক্ষিতে আপনার কিছু প্রতিক্রিয়া দেওয়ার থাকে, তো পর পর দিয়ে যেতে পারেন। আমি সাধ্যমত তার জবাব দেব, যথাক্রমেই।
-
Debasis Bhattacharya | ০৪ জানুয়ারি ২০২৩ ০০:০৭514998
- guru,
(৪) আপনার চার নম্বর প্রশ্নটি 'লোন উল্ফ ফেনোমেনন' সংক্রান্ত (ওপরের মন্তব্যের চার নম্বর নয়, আগের চার নম্বর)। আপনি প্রশ্ন করেছেন, খোদ আমেরিকায় খ্রিস্টীয় সন্ত্রাসবাদী 'লোন উল্ফ'-রা যখন শুধু এই বছরেই ছশোটি গণহত্যার ঘটনা ঘটিয়েছে, তখন মুসলমান জঙ্গিরা গত কয়েক বছরে নাইন ইলেভেন, সংসদ হামলা, মুম্বই হামলা জাতীয় মাত্র গুটিকয়েক হামলা চালাতে পারল কেন? এর উত্তরটা এমনিতে সোজা। 'লোন উল্ফ' হামলাগুলো হয় চার্চ বা স্কুল জাতীয় জায়গায় যেখানে একসাথে অনেকগুলো অপ্রস্তুত এবং অসহায় 'সফ্ট টার্গেট' পাওয়া যায় এবং প্রায় বিনা বাধায় অল্প সময়ে প্রচুর প্রাণনাশ করা যায়, ফলত সেটা একা একাই সম্ভব। কিন্তু মুসলমান জঙ্গিদের ঘটনাগুলো হচ্ছে স্পর্ধিত রাষ্ট্রবিরোধী হামলা, তা অনেক বেশি কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং সেইহেতু তাতে সংগঠনিক শক্তি ও পরিকল্পনা অনেক বেশি লাগে। উত্তরটি দেবার সঙ্গে সঙ্গে এও বলি, আপনার তথ্যটি একটু ক্রস চেক করবেন, ওই ধরনের ঘটনার ('লোন উল্ফ ফেনোমেনন') সংখ্যা কিন্তু ওর (৬০০) চেয়ে অনেক কম হওয়া উচিত।কিন্তু, 'ওরা কেন এত কম পারল' জাতীয় সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন বা তার উত্তরের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা ব্যাপার এখানে আছে। যেভাবে এবং যে প্রেক্ষিতে আপনি প্রশ্নটা করলেন, তাতে সন্দেহ হচ্ছে, ওপরে 'লোন উল্ফ ফেনোমেনন' ব্যাপারটার উল্লেখ আমি কেন করলাম সেটা ঠিকঠাক বোঝাতে পারিনি। আপনি সম্ভবত ভাবছেন, আমি প্রসঙ্গটি তুলেছি এইটা বোঝানোর জন্য যে, মুসলমান জঙ্গিদের কাজকর্ম খ্রিস্টান জঙ্গিদের তুলনায় অনেক বেশি সংগঠিত ও পরিকল্পিত। কোনও কোনও বিশেষ অর্থে হয়ত সত্যিই তাই, কিন্তু সম্ভাব্য সমস্ত অর্থে মোটেই তা নয়, এবং আমি এখানে সে ইঙ্গিত করতেও চাইনি। আসলে, আমি বলতে চেয়েছিলাম একটু অন্য কথা। বলছিলাম, মুসলমান মৌলবাদীদের কাছে তাদের 'টার্গেট' খুবই স্পষ্ট। সেক্যুলার ও বিধর্মী ব্যক্তি, তাদের প্রতিষ্ঠান, তাদের রাষ্ট্র, নিজ-ধর্মের মধ্যেকার সমালোচকের দল, এইসব। কিন্তু, খ্রিস্টান মৌলবাদীদের 'টার্গেট' অনেকটাই 'ডিফিউজ্ড্' বা ঝাপসা। রাষ্ট্রবিরোধী হিংসায় তারা যে তত উৎসাহী নয়, তার একটা কারণ অবশ্যই এই যে, আধুনিক রাষ্ট্রের সঙ্গে শেষ অবধি পেরে ওঠা যাবে না এই বোধটা তাদের টনটনে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কারণটা হয়ত এই যে, পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোতে (বিশেষত আমেরিকায়) কট্টর দক্ষিণপন্থী লবির প্রভাব যেহেতু এখনও যথেষ্ট বেশি, তাই আধুনিক রাষ্ট্রের সঙ্গে খ্রিস্টীয় মৌলবাদীদের একাত্মতা এখনও অনেকটাই আছে (কথাটা ওপরেও বলেছি)। মুসলমানদের যদি তারা নিকেশ করতে চায়, তো মুসলমান-প্রধান দেশকে আক্রমণ করার জন্য তারা আধুনিক রাষ্ট্রের ভেতরেই লবিয়িং করতে পারে, কাজেই রাষ্ট্রবিরোধী জঙ্গিপনার তাগিদ তাদের কিছু কম হওয়াই স্বাভাবিক। এবার, তাইই যদি হয়, তাহলে, যে ব্যক্তি-মৌলবাদীরা সরাসরি নিজের হাতে শত্রু নিকেশের কর্তব্য পালন করতে চায়, তাদের সাংগঠনিক ব্যাক-আপ খুব বেশি থাকার কথা না, এবং 'লোন উল্ফ' ভুমিকা প্রায় অনিবার্য।না, 'লোন উল্ফ' কথাটি আমার বানানো নয়। কুখ্যাত খ্রিস্টীয় জঙ্গি আলেকজান্ডার জেমস কার্টিস নিজেকে বা নিজের মত লোকেদের বর্ণনা দিতে কথাটা বানিয়েছিল। প্রথমে মার্কিন ইন্টেলিজেন্স এবং পরবর্তীকালে সমাজবিজ্ঞানীমহল ওখান থেকেই শব্দটিকে 'অ্যাডপ্ট' করে নেয়।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... সীমান্ত গুহঠাকুরতা , মন ছুঁয়ে গেল, Aditi Dasgupta)
(লিখছেন... মিঠু মণ্ডল )
(লিখছেন... Q, হেহে, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, Amit, Rouhin Banerjee)
(লিখছেন... দ, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, Kishore Ghosal)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, অরিন, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, Kishore Ghosal, সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... kk, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, সমরেশ মুখার্জী)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... যোষিতা, musil, যোষিতা)
(লিখছেন... অরিন, অরিন, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, ছোট মুখে , সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল, দীপ, দীপ)
(লিখছেন... kk, দীপ, dc)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : [email protected] ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত