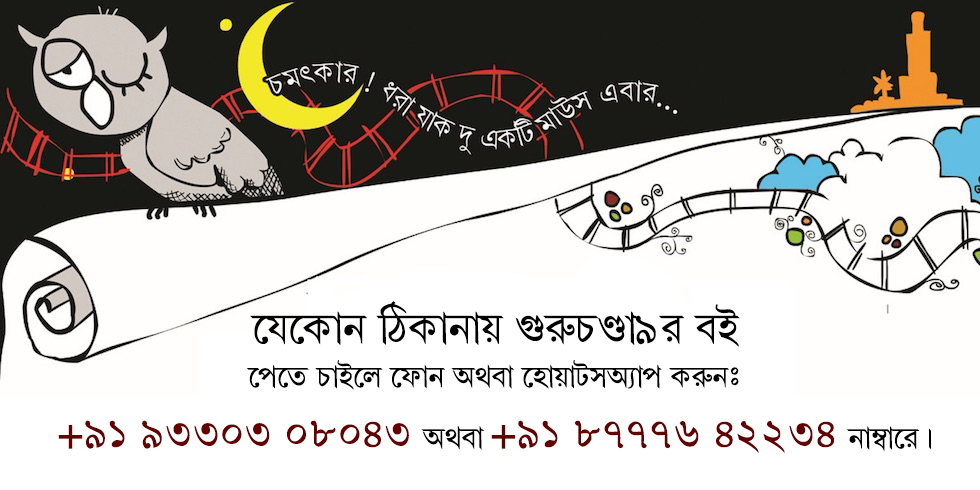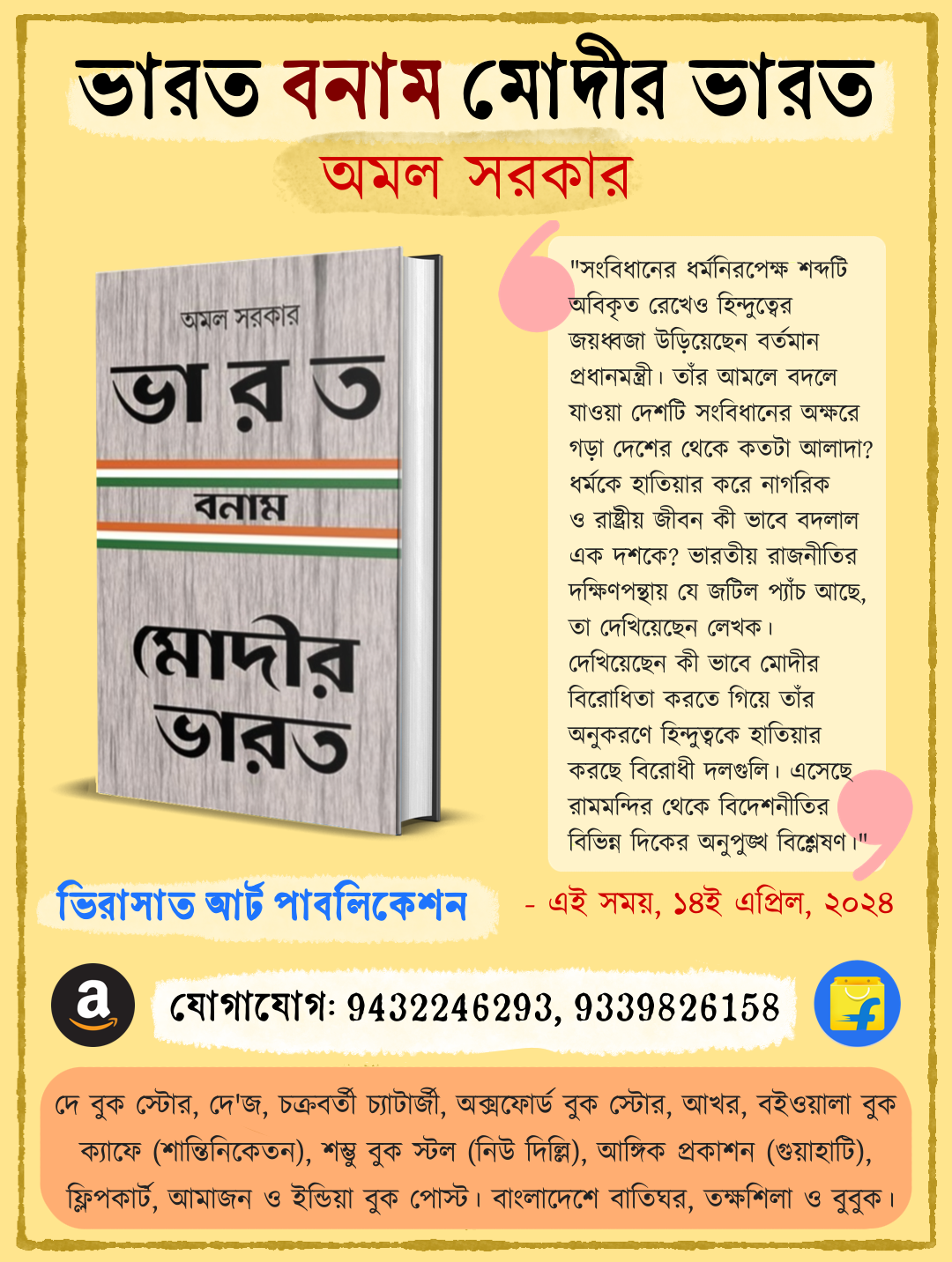- ভাটিয়ালি
- এ হল কথা চালাচালির পাতা। খোলামেলা আড্ডা দিন। ঝপাঝপ লিখুন। অন্যের পোস্টের টপাটপ উত্তর দিন। এই পাতার কোনো বিষয়বস্তু নেই। যে যা খুশি লেখেন, লিখেই চলেন। ইয়ার্কি মারেন, গম্ভীর কথা বলেন, তর্ক করেন, ফাটিয়ে হাসেন, কেঁদে ভাসান, এমনকি রেগে পাতা ছেড়ে চলেও যান।
যা খুশি লিখবেন। লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়। এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই। সাজানো বাগান নয়, ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি। এই হল আমাদের অনলাইন কমিউনিটি ঠেক। আপনিও জমে যান। বাংলা লেখা দেখবেন জলের মতো সোজা। আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি। - গুরুভার আমার গুরু গুরুতে নতুন? বন্ধুদের জানান
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 এলেবেলে | 202.142.96.8 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২৩:০১454223
এলেবেলে | 202.142.96.8 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২৩:০১454223আমিও ঢুকতে চাই না, তবে ওই হাত সুড়সুড় কচ্চে! ইন ফ্যাক্ট প্রথম পর্বে শিক্ষাসংস্কার শেষ করার পরে দ্বিতীয় পর্বে সমাজসংস্কারে হাত দেওয়ার আগে হপ্তাখানেক কিছু নতুন-পুরনো লেখা ঝালিয়ে নেওয়ার দরকার হচ্ছিল। ফাঁকে সামান্য বোরডম কাটাতে এখানকার 'সেন্টার স্টেজ'-এ চলে এসেছিলাম। সম্ভবত পরশু থেকে গা ঢাকা দেব। আপনারাও শান্তি পাবেন।
আজ্ঞে না, অ্যাডাম দেশজ শিক্ষাপদ্ধতিকেই সামান্য অদলবদল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাকে খারাপ তো বলেনইনি, উল্টে তার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন তাঁর তৃতীয় প্রতিবেদনে। সেই ব্যবস্থাকে টোমাসন চালু করে দেন। চরম সফল হওয়ার পরে ডালহৌসি তাকে বাংলায় চালু করতে বলেছিলেন। মানা হয়নি। অনেক পরে ১৮৭২ নাগাদ বাংলায় তা চালু করেন ক্যাম্পবেল। উচ্চশিক্ষায় কোপ পড়ছে বলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি তাঁকে তাড়িয়ে ছাড়ে। অথচ মহসীনের টাকায় চলা কলেজে তাদের পড়তে আপত্তি হয়নি! হান্টার কমিশনের রিপোর্ট দেখবেন, মুসলমানদের কী হাল হয়েছিল তা স্পষ্ট লেখা আছে। তারও আগে হান্টারের ইন্ডিয়ান মুসলমানস-এও সেই চিত্র ধরা আছে।
আর কেন মেকলে আসলেন, এসেই কমিটির মাথার বসলেন, কেন পাশ্চাত্য শিক্ষা চালু হল, কেন মাতৃভাষাকে অবহেলা করা হল - তার দীর্ঘ ইতিহাস আছে। শিক্ষিত বাঙালির ব্রিটিশপ্রীতি ও মুসলমান ভীতি তাতে স্পষ্ট। একই সময়ে বোম্বেতে কিন্তু মাতৃভাষাকে অবহেলা করা হয়নি। সোমপ্রকাশ ও সমকালীন বাংলা ও ইংরেজি সংবাদপত্রের একাধিক সম্পাদকীয় ও প্রতিবেদনে এই পাশ্চাত্য শিক্ষা চাকরির জগতে অতি দ্রুত কী অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছিল তার চিত্র আছে। ফলে আমাদের আম ও ছালা - দুই-ই গিয়েছিল। এত ইংরেজি চালু করেও ১৯৭১ সালে সংস্কৃত কলেজে আন্ডারগ্রাজুয়েট ছাত্র ২৬ জন, বহরমপুরে ৬ আর কৃষ্ণনগরে সম্ভবত ১৪ কিংবা ১৫! কী লাভ হল সব মিলিয়ে?
 b | 14.139.196.11 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২২:৫৯454222
b | 14.139.196.11 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২২:৫৯454222- ক দিন আগে চাঁদের বাঁ দিকে, একই সরলরেখায় বেস্পতি আর শনিকে দেখা যাচ্ছিলো। এখ্ন ডানদিকে দেখা যাচ্ছে।
 lcm | 99.0.80.158 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২২:৫৪454221
lcm | 99.0.80.158 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২২:৫৪454221- স্কুল শিক্ষার রিফর্ম তো দরকার ছিলই, রিপোর্টেই আছে বেশির ভাগ স্কুলেই একজন শিক্ষক ছিলেন, একজনই সব সাবজেক্ট পড়াতেন, বা, সিলেবাস যা ছিল সেটা তো বদলাতেই হত। সুতরাং একটা বদল হতই।
দুটো জায়্গায় ডিবেট ছিল, এক - ওরিয়েন্টাল ভার্সেস এঞ্জেলিস্ট, মানে, পদ্ধতি/কন্টেন্ট/মিডিয়াম সব মিলিয়ে - প্রাচ্য(দেশীয়) বনাম পাশ্চাত্য(ইংরেজি)। আর দু নম্বর, হল স্প্রেড - বটম আপ, না, টপ ডাউন। অর্থাৎ, নলেজ স্প্রেড - সমাজের নীচের তলার মানুষ বা আমজনতা লেখাপড়া শিখলে, কিছু বদল হলে সেতা বাবল হতে হতে আলটিমেটলি জমিদার বা ট্রেডার্স - সবাই তাতে অভ্যস্ত হবেন - এটা হল বটম আপ অ্যাপ্রোচ। বা, সমাজের অল্প সংখ্যক কিছু মানুষ শিক্ষিত হলে, নলেজ আস্তে আস্তে ট্রিকল ডাউন করে সমাজের সব স্তরে ছড়িয়ে পড়বে। এটা ছিল, অন্য আইডিয়া।
তো, আগে যে কম্বিনেশন ছিল - পদ্ধতি ছিল ওরিয়েন্টাল, আর, স্প্রেড মোটামুটি বটম, অর্থাৎ সবাই মোটামুটি একটা ইউনিফর্ম স্কুল এডুকেশন পেতে পারত, আর উচ্চ্শিক্ষার ব্যাপারটা অত ওয়েল ডিফাইনড ছিল না, মোটামুটি অভিজ্ঞতা, কতদিন ধরে প্র্যাকটিস করছেন এসব দিয়েই দিয়েই বিচার হত।
ইংরেজরা যে কম্বিনেশন নিলেন সেটি হল - এঞ্জেলিস্ট এবং টপ-্ডাউন অ্যাপ্রোচ। তো এই দুটো পার্ট কানেক্টেড। এঞ্জেলিস্ট পদ্ধতি নেওয়া হল, ইংলিশ মিডিয়াম - সেটি খরচসাপেক্ষ, সবাই অ্যাফোর্ড করতে পারবে না, কিছু মানুষ করবে, আইডিয়া ছিল যে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়বে, একসময় বাকিরা সবাই পাবে। টপ-্ডাউন (ট্রিকল ডাউন) অ্যাপ্রোচ।
একটি বিশেষ গোষ্ঠিকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে এডুকেশন দেবার এই পদ্ধতিটি অব্শ্যই শাসকের স্বার্থ রক্ষার জন্য তৈরি। বকলেম সেই সিস্টেম আজও চলছে।
এখন কথা হচ্ছে আইডিয়াল তা হলে কি ছিল - - অফ কোর্স, ওরিয়েন্টাল এবং বটম-আপ। আধুনিক বিজ্ঞান/দর্শন শিক্ষা এসব জার্মানি বা ফ্রান্স বা ইতালিতে সে যুগে কম কিছু হয় নি (বা রাশিয়া, পরের শতকে চায়্না) - কিন্তু তার জন্য শিক্ষাব্যব্স্থা ইংলিশ সিস্টেমে নিয়ে যেতে হয় নি।
 বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত | 49.37.4.59 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২২:১৫454220
বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত | 49.37.4.59 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২২:১৫454220- আমি চাই ইতিহাসে তুমি এনগেজ করো, তাইলে আমরা শিখতে পারবো। কারন তুমি আন্তাচে কথা কবা না। থ্যাংক ইউ। বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত
 সিএস | 2405:201:8803:bf86:e96f:9114:d708:492e | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২২:০৭454219
সিএস | 2405:201:8803:bf86:e96f:9114:d708:492e | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২২:০৭454219- ঈশান সকালে লিখেছে দেখলাম যে গ্রামবাংলায় এমন একটা শিক্ষাব্যব্স্থা ছিল যা দিয়ে অল্প লিখতে পারা, অংক করতে পারা এরকম শিক্ষা দেওয়া হত। কিন্তু আমি রিপোর্টের যতখানি পড়েছি সে পড়ে তো মনে হল অ্যাডাম সাহেবও ঐ পদ্ধতি বা উদ্দেশ্য নিয়ে খুশী ছিলেন না, ওতে ছেলেপুলেদের উন্নতি হয় না, সেই জন্যই শিক্ষা ব্যবস্থাটা ঢেলে সাজাবার প্রকল্প, ওনার ক্ষেত্রে যেটা প্রাথমিক স্তর থেকে, স্কুল তৈরী করে, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ব্যবস্থা করে। এমন মনে করার মনে হয়না কারণ আছে যে ইংরেজ ধারণায় স্কুল বলতে যা বোঝাতো (যা বাংলায় প্রচলিত ছিল তার থেকে আলাদা) অ্যাডাম সাহেবের ধারণা তার থেকে আলাদা কিছু ছিল। মেকলে সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল যে প্রাথমিকে জোর না দিয়ে মডেল স্কুল তৈরী করে ওপর থেকে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। অতএব এমন মনে করার কারণ নেই বলে মনে হয় যে অ্যাডাম সাহেবের মত কোম্পানী মেনে নিলে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার চরিত্র একেবারেই বদলাত না, বদলাতে যে হবে সেটা আমার ধারণা অ্যাডাম ও মেকলে দুজনেই মনে করতেন কিন্তু বদলাবার পদ্ধতিতে তফাৎ ছিল বেশী ভাবে।
এবার কোম্পানী কেন মেকলের মতই মেনে নিল সে ব্যাপারেও তো কোম্পানীর যুক্তি ছিল যা লিখিত ভাবেই আছে। সেই যুক্তির বাইরে কতখানি কোম্পানীর স্বার্থ, কতখানি অন্য উদ্দেশ্য, কতখানি দেশীয় সাবজেক্টদের দাস বানাবার চেষ্টা সেসব কোম্পানীর দলিল-্কাগজ না দেখলে মনে হয়না বোঝা যাবে।
(এই তর্কের মধ্যে ঢুকব না ভেবেছিলাম কিন্তু হাত সরসর করছিল বলে লিখে ফেলতে হল।)
 সিএস | 2405:201:8803:bf86:15cb:fe06:6677:5517 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২১:৩৩454218
সিএস | 2405:201:8803:bf86:15cb:fe06:6677:5517 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২১:৩৩454218- সিদ্ধান্তে আসিনি পুরোটা যদিও এই লাইনে বেশ কিছু পোস্ট হয়েছে যেগুলো পড়েই হয়ত এখানে অনেকেরই মনে হয়েছে যে আপনার লেখা এই নিয়েই ! আবার কেউ মনে করতে পারে, হ্যাঁ ঠিকই তো বড় মানুষরা কেউই বিশেষ সুবিধের নয়। মনে করি সেই জন্যই তক্ক তৈরী হচ্ছে এখানে, তক্কটা তখন ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে যেতে পারে।
আবার, সিদ্ধান্তে আসিনি বলেই ঐ প্যারার শেষ বাক্যটি লেখা হয়েছে।
 বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত | 49.37.4.59 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২১:২৬454217
বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত | 49.37.4.59 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২১:২৬454217- এলে, কে কোথায় থাকে দিয়ে কেউ রাগ করে না আর করলে পাত্তা দেবেন না। বা এটা নিয়ে মাথা ঘামায়েও লাভ নাই। আর টেক্সট বই এর উপরে যাদের চর্চা নেই, তাদের অপিনিয়ন নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই, কিন্তু বাজারে বই প্রবন্ধ লিখলে, সব রকম লোক রিয়াক্ট করবে, আপনি কত উত্তর দেবেন। আপনি ওভার দ্য টপ ক্যারাকটারাইজেশন টাইপের কমেন্ট গুলো, একটু রেস্ট্রেন্ড হয়ে করলে আলোচনা টা হয়, নতুন ফুল ফ্লেজেড পোবোন্ধ ইজ ইয়োর ফোর্টে, কনভারসেশন বা লিখিত কনভারসেশন মে নট বি ইয়োর থিং।এনাজ্জি খরচ না করে লিখে ফুল ফ্লেজেড প্রবন্ধ লিখে যানঃ-))) কুল। আমার আপনার লেখা ভালো লাগে।
সৈকত (দ্বিতীয়), বইটা পড়ে নিয়ে একটা রিভিউ লেখো। আমার পার্সোনালি মনে হয়, পার্থ চট্টোপাধ্যায় সবচেয়ে ক্রিয়েটিভ, সাব অলটার্ন ওয়ালা দের মধ্যে, মানে আমার মনে হওয়ায় কিছু এসে যায় না, কিন্তু তাও।
তাই ওনার বিশাল ফ্যান হওয়া সত্তএও আমি যে প্রবন্ধটি পড়েছিলাম যেটাতে জনপ্রতিনিধিত্ত্ব নিয়ে দু চার কথা ছিল, সেটি আমার একেবারেই ইম্প্রেসিভ লাগে নি।
প্রত্যেক টা ঘরানার ইতিহাস চর্চা র নানা সীমাবদ্ধতা আছে। তবে তার উৎস সন্ধান করলে সেটা কে তোমার অতটা অস্বাভাবিক মনে হবে না। কখন কোন ধরণের ইতিহাস চর্চা কে কি ধরনের চর্চার স্টেলমেট কে অ্যাড্রেস করতে হচ্ছে, সেটা দেখলেই তুমি নতুনত্ত্ব ও সীমাবদ্ধতা দুটো-ই ম্যাপ করা সম্ভব।
সাধারণ ভাবে সারা পৃথিবীতে পোস্ট কলোনিয়াল চর্চার বিপদ হলো, অনেক ক্ষেত্রেই সেই চর্চা টা সাংস্কৃতিক ইনসুলারিটি র একটা ডিফেন্স হয়ে যায়, সেটা সম্পর্কে সাবধানতা রেখে, কলোনী র নলেজ সিস্টেম এর নানা ধাষ্টামো কে ডিসম্যান্টল না করার কিছু নাই। আফ্রিকার কলোনীর ইতিহাসে যেরোকোম ভাবে রেস এলিমেন্ট ( হোয়াইট ম্যান'্স বার্ডেন) ইত্যাদি, যে ভাবে লোকে ক্রিটিক করেছে, আমাদের দেশে সেটা সব সময়ে হয় নি, তার হিসেব অনেক বাকি আছে, তার নানা কারণ আছে এবার সেটা সব মিলিয়ে ইমানিসিপেটরি হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে। আলটপকা কন্টেক্স্ট এর বাইরে টেক্সট পড়ে লাভ নেই। এগ্রিড।
প্রত্যেকটা ধারার ইতিহাস চর্চা কিছু না কিছু দিয়েছে। হবসবম যহন ব্যান্ডিট্স লিখছেন, তখন ষাঠের দশকের মাহাত্মেই হোক যে কোনো কারণেই হোক, শুধু যে ল-লেস দের থিয়োরাইজেশন করছেন তা না, ইউরোপে র মধ্যে সোর্স রাখছেন না, লাতিন আমেরিকা কে নিয়ে আসছেন। বা জ্যাজ সংগীত নিয়ে যখন লিখছেন,্তখন সারা জীবন মার্ক্সবাদী হবার জন্য যারা ওঁকে গাল দিয়েছেন, তাঁরাও ভদ্রলোকের ক্ষমতায় চমকাচ্ছেন। মার্ক্সবাদী ক্রিস্টোফার হিল যখন লেখেন, পৃথিবী তে অনেক পরিবর্তন ই আসবে, যেটা কিছু পাকা চুলো লোকের টেবিলের চারধারে বসে নেগোশিয়েট করা প্ল্যান করা বস্তু নাই হতে পারে, তখন সেটা শুধু বিপ্লবে 'বিশ্বাস' না, কিছু সময়ের কিছু সামাজিক সমস্যা র রিকনসাইল করার সম্ভাবনা খুব কম এরকম ঐতিহাসিক মুহুর্ত সম্পর্কে অনুধাবন করার অভিজ্ঞতা থেকে ভাবেন। লিটেরারি ক্রিটিসিজম থেকে যখন ইতিহাস পদ্ধতি ধার করে মহাফেজখানার বাইরে ইতিহাসের খোঁজ করে, তখন সোর্স এর সমস্যা প্রকট হয়। আবার একাধিক ভাষার , একাধিক অঞ্চলের সোর্স দেখলে, মহাফেজখ্কানার মধ্যেই ভ্যারিয়েশন খুঁজলে খানিকটা রিগর বাড়ে।
তার পরে হলো বহু খুঁজে পাওয়া ডকুমেন্টেশন এর গুল ধরতে পারা। 'পাওয়ার অফ ফলসহুড' ইত্যাদি। ইকো রা শুধু লিংগুইস্টিক্স করতে গিয়ে মধ্যযুগের ইউরোপ সম্পর্কে যে কাজ করছেন, তাতে শুধুই তথ্য নতুন আসছে না, মধ্যযুগ কে অন্ধকার যুগ বলা হয়েছে, সেটাকে আর তত অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হচ্ছে না। আমাদের দেশে সআধীনতার পরের ইতিহাস চর্চা যেমন সাংঘাতিক ভালো কিছু কাজ করছে, গবেষণার জগতে নতুন সোর্স, নতুন দৃষ্টি ভংগে আনছে, কিন্তু তার দুর্বলতা হল, স্টেট এন্টারপ্রাইজ এর সঙ্গে একটা একাত্মীকরণ সে আভ্যএড করতে পারছে না, মানে খুব সিম্পলি, বাংলাদেশ, বর্মা, নেপাল, দক্ষিন ভারত, স্রীলংকা, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এগুলোর আলাদা আলাদা ইতিহাস হয় ঠিক ই, কিন্তু সময় গুলো র একটা তুলনামূলক ইতিহাস দরকার, এবং মহাফেজখানা গুলোর একদম ফ্রি অ্যাকসেস হবা উচিত। অ্যাক্রস সাউথ এশিয়া, সাউথ এশিয়া টার্ম টা যদিও আমার বিশেষ পসন্দ না, ইট স্ম্যাক্স অফ আমেরিকান স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ। ইত্যাদি।
হ্যা এলে র এক্সপ্রেসনে একটা ওভার দ্য টপ পার্সোনাল ক্যারাকটরাইজেশন মাঝে মাঝে এসে যায়, সেটা হয়তো মিনিংফুল কনভরসেশনে যেতে না পারার ফ্রাসট্রেশন থেকে। যাক গে সেটা ইগনোর করে মোটামুটি ইতিহাস চর্চা হৌক। মানে পোসালে ঃ-)))
বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত
 এলেবেলে | 202.142.71.43 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২১:০৩454216
এলেবেলে | 202.142.71.43 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ২১:০৩454216//কার মনে কী ছিল, কে বদমাইশ, কার মনে প্যাঁচ, কে স্টুজ বা দালাল//
ভাটিয়ালিতে করা একটা হালকা মন্তব্য যে লেখাতে থাকবেই, সেই সিদ্ধান্তে দ্রুত চলে আসা কেন?
 সিএস | 2405:201:8803:bf86:b195:b6:db63:6f7d | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৯:১৫454215
সিএস | 2405:201:8803:bf86:b195:b6:db63:6f7d | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৯:১৫454215- -- দারাশুকো প্রথম খন্ডের আধখানার বেশী পড়তে পারিনি, উপন্যাস খুঁজে পাইনি যদি না ইতিহাসে যা ঘটেছিল তার কাল্পনিক বিবরণকে উপন্যাস বলি।
-- ইতিহাস একটা কনটেস্টেড স্পেস, তথ্য দিয়ে নিজের বক্তব্যর প্রতিষ্ঠা করতে হয়, সাথে ইন্টারপ্রিটেশনটাও জরুরী, লেখার সময়ে সেই সময়ে চলে যেতে হয় আর আজকের ক্যাটেগরি ঐ সময়ে ব্যবহার করা যায় না, এরকম কিছু কথা আছে। এইসব বিষয়গুলি ঘিরে অনেক ক্ষেত্রেই খামতি থেকে যাচ্ছে বলে মনে করি আর কার মনে কী ছিল, কে বদমাইশ, কার মনে প্যাঁচ, কে স্টুজ বা দালাল সেসব সিদ্ধান্তে আসা মনে হয় না ইতিহাস লেখকের কাজ। অন্তত আমি সেভাবেই দেখি, যদিও সেরকমভাবে ইতিহাস লেখা হয়েছে এবং হবেও কারণ সেসবে অ্যাজেন্ডা পূরণ হয় অথচ বিভিন্ন ফোর্স যা ঐ সময়ে ক্রিয়া করছিল সেগুলো লেখা থেকে মুছে যায়, জটিলতা মুছে যায়, বোঝা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু এরকম করলে তখন ঐ ব্যক্তির আর তার পরিবারের ইতিহাস লিখতে বসতে হবে, ইতিহাস লেখা যদিও সেসব থেকে বেরিয়ে এসেছে। অবশ্য হতে পারে এসব অনলাইনে বা ফেসবুকে তর্ক করে করে ইতিহাস লেখার কুফল।
-- পার্থ চাটুজ্যের বইয়ের ইন্ট্রোটা থেকেই বোঝা যায় যুক্তিগুলো কী এরকমই পড়লাম, সেটাই অ্যাটেম্প্ট করতে হবে। হার্ডকপি না পিডিএফ, সেটাই বিচার্য।
 b | 14.139.196.11 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৯:১২454214
b | 14.139.196.11 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৯:১২454214- কফি রহস্য ভেদ করা গেলো। ১+১+২+২
১) এক কাপ গরম জল।
২) নেসকাফের দু-টাকার পাউচ একটা।
৩) দুটো সুগার কিউব।
৪) দুই ছোটো চামচ দুধ। কফির রং মোটামুটি আমার গায়ের রঙের মতো।
 এলেবেলে | 202.142.71.225 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৮:০৮454213
এলেবেলে | 202.142.71.225 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৮:০৮454213খ, "আইডিয়ার ভ্যালিডেশন চাইবার প্রয়োজনীয়তা কেউ বোধ করে নি"। এটা আপনি আমাকে এর আগেও বলেছেন এবং বিশ্বাস করুন আদৌ আমি সেই ভ্যালিডেশন এখানে চাইছি না। মানে আপনি আমার সঙ্গে একমত হলেন কি না কিংবা হবেন কি না - এসব ভেবে-টেবে এখানে কেউ লেখে বলে মনে হয় না। আমি আমার জায়গা থেকে বলছি, সে জিনিস আপনি মানতেও পারেন। না মানতেও পারেন।
এখানে সবাই কৃতবিদ্য মানুষ। ভালো অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার, জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রায় সবাই বিদেশে পড়াশোনা করেছেন। তাঁদের অধিকাংশই ওখানেই চাকরি নিয়ে থিতু হয়ে গেছেন দীর্ঘদিন। এখন সবার তো আর একই বিষয়ে আগ্রহ থাকতে পারে না। কাজেই ওসব কথা মাঝে-মধ্যে বেরিয়ে আসে।
'amount of hostility'-র কারণ খুব সোজা। এক, আপনি যেটা জানেন সেটা আমি জানি না, বা জানলেও সম্পূর্ণ উল্টো জানি - এটা স্বীকার না করতে পারার সততা। দুই, আমি নিছকই ডিগ্রি ও পেডিগ্রিহীন এক লোক। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি মুখে বললে কী হবে, এ বিষয়ে তার অহং জ্ঞান টনটনে। ফলে...
আমি শুধু আশ্চর্য হই জেন্ডার স্টাডিস যেখানে বর্তমানে ইতিহাসচর্চার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন্ড, সেখানে মানুষজন কি উইডো ম্যারেজ অ্যাক্টটা পড়ে অবধি দেখেননি? রঘুনন্দনের দায়তত্ত্ব না-ই পড়তে পারেন। তাহলে এত উলুতপুলুত কেন? কেন শিক্ষাবিস্তারের ডিসকোর্সে মহসীন, সাবিত্রী ফুলে কিংবা গুরুচাঁদ-হরিচাঁদ চিরদিনই প্রান্তিক অবস্থানে থাকেন? সে কি জীবনেও তাঁরা প্রান্তিক হতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে? কে জানে।
kc | 37.39.144.141 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৩:২১
না পাইনি। নামের পরে 'বাবু'টা স্বচ্ছন্দে বাদ দিয়ে দিন।
 S | 2a0b:f4c1::7 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:৪৮454212
S | 2a0b:f4c1::7 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:৪৮454212- আর এইসব অর্থনীতি ইত্যাদি যদি আসল কারণ হত তাহলে ট্রাম্প রাশ লিম্বোকে মেডাল অব ফ্রীডম দিত না বা নিজের বেসকে ফক্স নিউজ না দেখে ওএনেন দেখতে বলতো না। হি নোজ হোয়াট হিজ মার্জিনাল ভোটার্স ওয়ান্ট।
 S | 2a0b:f4c1::7 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:৪৫454211
S | 2a0b:f4c1::7 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:৪৫454211- আমেরিকাতে আবার কে হলুদ হয়ে যাওয়া বই নিয়ে বসে ছিল?
 aka | 143.59.211.4 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:৩৯454210
aka | 143.59.211.4 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:৩৯454210- এস, মূল প্রতিপাদ্য হল ট্রাম্প প্রেসিডেন্সি জিতেছে গরীবের ভোটে, ট্রাম্প বড় হবার সময়ে হরলিক্স খেয়েছে কিনা সে জরুরী নয়।
ট্রাম্পের ভোটারদের মধ্যে রেসিস্ট আছে? সিওর, সেটা কি ডিসাইডিঙ্গ ফ্যাক্টর ? নয়।
বৃহত্তর রাজনীতিটা মিস করে গেলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না। ব্লু কলার, এলিট ডেমরা আবার বুক চাপড়াবে। ট্রাম্প আবারও জিতবে।
 aka | 143.59.211.4 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:৩৩454209
aka | 143.59.211.4 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:৩৩454209- দুনিয়া জুড়ে দক্ষিণ পন্থীদের উত্থান কারণ বামেরা রেটরিক হারিয়েছে, এই বিপুলা পৃথিবীর ভার রোবট বেসড ইকনমি আর নিতে পারছে না। বামেরা এখনও সেই হলুদ হয়ে যাওয়া বই আর থিওরীতে আটকে আছে। গরীবদের কোন চয়েজ নেই, যেই তাদের কথা বলবে, সে ডেমাগগই হোক আর কন-ম্যানই হোক তারা তাকেই ভোট দেবে।
 S | 2a0b:f4c1::7 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:৩২454208
S | 2a0b:f4c1::7 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:৩২454208- আসল প্রশ্নটা তো সবাই ভুলেই যায়ঃ প্রাইমারি জিতলো কি করে?
 aka | 143.59.211.4 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:২৯454207
aka | 143.59.211.4 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:২৯454207- কেন?
 S | 2a0b:f4c1::7 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:২৩454206
S | 2a0b:f4c1::7 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:২৩454206- "ট্রাম্প রেসিজমের জন্য যেতে নি, জিতেছে রাস্ট বেল্টের ৫৫,০০০ ভোটে। ট্রাম্প শুধু রেসিজমের জন্যই জিতেছে ওটা এলিট ডেমদের দাবী, নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য ব্যবহার করে।"
এই কথার কোনই মানে নেই।
 S | 2a0b:f4c1::7 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:২২454205
S | 2a0b:f4c1::7 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:২২454205- আমেরিকাতে লোকেরা টিশার্ট তৈরী করবে? ৮০ ডলার দিয়ে কিনতে রাজী আছে তো? আউটসোর্সিং একসময় কানাডা, আয়ারল্যান্ডেও কম হয়নি। তখন কিন্তু সবাই চুপ করে ছিল। কিন্তু জাপান, চীন, ইন্ডিয়া, মেক্সিকো দেখলেই চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায়। ক্যারিয়ার এয়ারকন্ডিশনিং একটা প্লান্ট মেক্সিকো পাঠাচ্ছিলো বলে ট্রাম্প ট্যাক্স ব্রেক দিল, সবাই ট্রাম্পের বাহ বাহ করলো। সিইও সোজা বলে দিলো যে ঐ ট্যাক্স ব্রেক দিয়ে অটোমেশান হবে। কেউ কোনও কথা বলেনা। ৯০এর দশকে যখন ভারতের গলা দিয়ে গ্লোবালাইজেশান গেলানো হচ্ছিলো, তখন কিন্তু কত্ত লেখাপত্তর বেড়ত যে ফ্রী ট্রেড, ওপেন বর্ডার, ক্যাপিটালিজমই নাকি মানুষের মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায়। এখন অন্যদেশগুলো একটু ভালো করছে, কারোর সহ্য হচ্ছে না। সবেতেই তাই। পেটেন্ট, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি নিয়ে কত্ত জ্ঞানদান, যেই বাসমতীর কথা এলো ওমনি ওসব আর মেনে চলতে ভালো লাগেনা।
 aka | 143.59.211.4 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:১৮454204
aka | 143.59.211.4 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:১৮454204- ট্রাম্প রেসিজমের জন্য যেতে নি, জিতেছে রাস্ট বেল্টের ৫৫,০০০ ভোটে। ট্রাম্প শুধু রেসিজমের জন্যই জিতেছে ওটা এলিট ডেমদের দাবী, নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য ব্যবহার করে।
 S | 2a0b:f4c1::7 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:১২454203
S | 2a0b:f4c1::7 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:১২454203- "গ্লোবালাইজেশন এর ফলে হোয়াইট ওয়ার্কিং ক্লাস জব হারিয়ে মন খারাপ করে পপুলিস্ট হয়ে গেল সেটা ফর অল প্রাকটিকাল পারপাসেস বকোয়াজ।"
রেসিস্ট অ্যাঙ্গেলটা তো সবাই গুলিয়ে দিতে চায়। এমনকি পিকেটির পেপারেও তো "রেসিজম তেমন বড় কিছু নয়" টাইপের একটা অ্যাপলজেটিক ভিউ ছিল। জন স্টিউয়ার্টও তো প্রথম প্রথম বলেছিল যে রেসিজম ছাড়াও ট্রাম্পের জিতে আসার আরো কারণ রয়েছে, যেমন ওবামাকেয়ার।
 বোধিসত্ত্ব | 2405:201:8008:c82b:4434:edc1:28a9:6129 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:১১454202
বোধিসত্ত্ব | 2405:201:8008:c82b:4434:edc1:28a9:6129 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:১১454202- খাওয়া, শিওর , এগ্রিড। পার্থ চট্টোপাধ্যায় এর ব ই কার রিভিউ কেউ করবে নাকি
 aka | 143.59.211.4 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:০৯454201
aka | 143.59.211.4 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:০৯454201- ধৈর্য্য ধরুন সমাজতন্ত্র ক্রমে আসিতেছে। ক্যাপিটালিজম অটোমেশনের এমন জায়গায় পৌছেছে যে মাছের তেলে মাছ ভাজা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অটোমেশন বা রোবট ট্যাক্স এলো বলে, সেই থেকে নতুন সেফটি নেট আর সমাজের বৃহত্তর অঙ্গশে অনেক বেশি প্রফিট শেয়ারিঙ্গ।
সমাজতন্ত্রে উত্থান এই ক্যাপিটালিজম থেকেই হবে। লাল সেলাম
 aka | 143.59.211.4 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:০৪454199
aka | 143.59.211.4 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৬:০৪454199- পশ্চিমের মানে আম্রিগার এই আর্গুমেন্টটা ট্রাম্প ব্যবহার করে আর ওর বেস সেটা খায়।
আমেরিকার ম্যানুফ্যাকচারিঙ্গ প্রোডাকশন পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশি, কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারিঙ্গ এ এমপ্লয়মেন্ট খুব কম - কারণ? অটোমেশন
 বোধিসত্ত্ব | 49.37.4.59 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৫:৩৯454198
বোধিসত্ত্ব | 49.37.4.59 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৫:৩৯454198- তাছাড়া তথাকথিত গ্লোবালাইজেশন এর (চীন ও ভারত এ নতুন জব্স) আরম্ভ র আগে থেকেই, ব্রিটেনে অন্তত ডি ইনডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অফ ম্যানুফাকচারিং শুরু হয়েছে, আর ম্যানুফাকচরইং এর এদিক ওদিক সরানো নানা ভাবে আগে হয়েছে, ট্যাকস রেজিম ম্যানেজ করা হয়েছে , বাই ল্যাটারাল এগ্রিমেন্ট দিয়ে।
অতএব পার্থবাবু প্রাথমিক ভাবে ঠিক , যে পোলিটিকাল ফিলোসোফি র আঙ্গিকেই এটা দেখা ভালো, কিন্তু প্রবন্ধটি তে নতুন কিছু পেয়েছিলাম কিনা মোনে পড়ছে না। বোধিসত্ত্ব
 বোধিসত্ত্ব | 49.37.4.59 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৫:৩২454197
বোধিসত্ত্ব | 49.37.4.59 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৫:৩২454197- আমি এই বই পড়ি নি। কিন্তু যেটা পশ্চিমে আর্গুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়, গ্লোবালাইজেশন এর ফলে হোয়াইট ওয়ার্কিং ক্লাস জব হারিয়ে মন খারাপ করে পপুলিস্ট হয়ে গেল সেটা ফর অল প্রাকটিকাল পারপাসেস বকোয়াজ। কারণ তাতে দুটো জিনিস্ট এক্সপ্লেন করা যায় না, সেটা হল , যখন তাদের ইকোনোমির ফুলে ফলে প্রস্ফুটিত, তখন অ্যান্টি ইমিগ্রেশন রেটোরিক কিছু কম ছিল না, ব্রিটেন এবং ইউরোপে, এবং আমেরিকার সোশাল সার্ভিসের ইনক্লুসন বরাবরি সাদার্ন লিডারশিপের সংগে নানা ধরণের কম্প্রোমাইজ করেছে।
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এর সুপার স্টেট এর ধারণা ন্যাশনালিজম কে আহত করেছে, এই ধারণাও কিছু প্রশ্ন অ্যাড্রেস করতে অক্ষম, যেমন দুটি উদা মোটামুটি এরকমঃ
-- ফাইনানসিয়াল সারভিসেস এবং মেডিয়া র বিজনেস এ ব্রিটেন এবং ইউ এবং আমেরিকান মার্কেট অপারেটর রা যথেষ্ট ইন্টিগ্রেটেড ছিল, প্রোটেকশনিজম এর কথা উঠতো, ট্রেডিং এ বা স্পেকুলেশন এ ফাইনানশিয়াল স্ক্যান্ডালে কোম্পানি ভিত্তিক শাস্তির সময়। মানে ধরুন এইচ এস বি সি কে আমেরিকায় ফাইন করা হলে ই ইউ বা লন্ডন থেকে আপত্তি উঠতো, জে পি এম সি ফাইন পেলে, আমেরিকা আপত্তি করতো, সাদা দাদা দের এইটা উইংক উইংক বিষয় ছিল, গল্ফ টুর্নামেন্ট এর মত।
তো ইকোনোমিক রেশনাল অফ ডেমগোগারি (হিলি বিলি কান্ট্রি ইত্যাদি বই এ যেরকম আছে) একটু দুর্বল। এবার বাকি রইলো রিল্জিয়াস ফান্ডামেন্টালিজম এর উত্থান, আর চীন ও রাশিয়ার নতুন অ্যাম্বিশন।
কিন্তু পার্থ বাবু র একটা প্রবন্ধ, হয় বারোমাসের কোনো বিশেষ সংখ্যায় , বছর দশেক আগে বেরিয়েছিল। আমি সেটা নিয়ে এখানে লিখেও ছিলাম, গণতন্ত্র র রিপ্রেজেন্টেশন এর সমস্যা নিয়ে কিছু কথা বলেছিলেন বটে, কিন্তু সেটা আমার খুব ইম্প্রেসিভ কিছু লাগে নি। প্রবন্ধ টি যদি কেসি বা সৈকত পড়ে থাকো, তাহলে এই বইয়ে এর সংগে ঐ প্রবন্ধ র সিড আইডিয়া গুলির কোন মিল আছে কিনা নাকি আরেকটু ফার্ম আপ কিছু করেহ্হেন, সেটা জানতে পারতাম। বোধিসত্ত্ব
 kc | 37.39.144.141 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৪:৫৯454196
kc | 37.39.144.141 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৪:৫৯454196পড়ুন, আলেকজান্ডার দুগিন'এর সঙ্গে মিল পাবেন।
 সিএস | 2405:201:8803:bf86:2dea:4b57:4d25:42b1 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৪:৩৬454195
সিএস | 2405:201:8803:bf86:2dea:4b57:4d25:42b1 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৪:৩৬454195- আপনারা কেউ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের I Am the People বইটা দেখেছেন নাকি ?
এখন যে বিশ্বজুড়ে পপুলিস্ট রাজনীতি আর রাষ্ট্রপ্রধানদের বাড়াবাড়ি, সে ব্যাপারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, রিভিউ পড়ে সেরকমই বুঝলাম।
(লক্ষ্য করে দেখলাম, বইয়ের নামটিতে যেন সেই প্যারাগুয়ের উপন্যাসটি, I, The Supreme-এর ছায়া আছে।)
 বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত। | 49.37.4.59 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৪:০৪454194
বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত। | 49.37.4.59 | ৩০ আগস্ট ২০২০ ১৪:০৪454194- এই উদারতার স্কেল আজকাল কার ক্যানসেল কালচার এ ভাবা প্রায় অসম্ভব। বোধিসত্ত্ব দাশগুপ্ত।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... Somnath Pal, রমিত চট্টোপাধ্যায়, পোল খুলে গেল)
(লিখছেন... Prabhas Sen, Argha Bagchi, সিক্যুয়েল চাই)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Argha Bagchi)
(লিখছেন... )
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... মোহাম্মদ কাজী মামুন, দ)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... haridas, এরাও তাই বলছে, Prativa Sarker)
(লিখছেন... Kishore Ghosal, সমরেশ মুখার্জী, kk)
(লিখছেন... পাগল পাগল বোধ )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... অরিন, অরিন, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, ছোট মুখে , সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... :|:, পাপাঙ্গুল, পাপাঙ্গুল)
(লিখছেন... kk, দীপ, dc)
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।