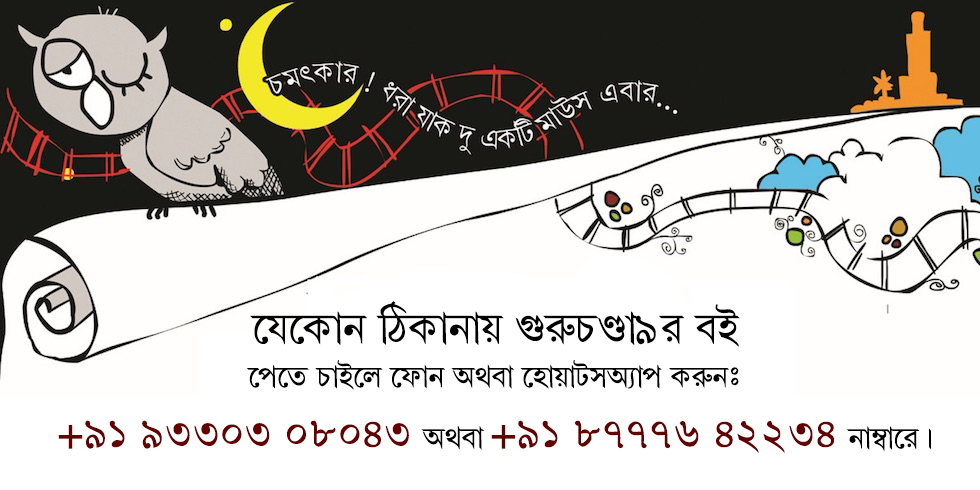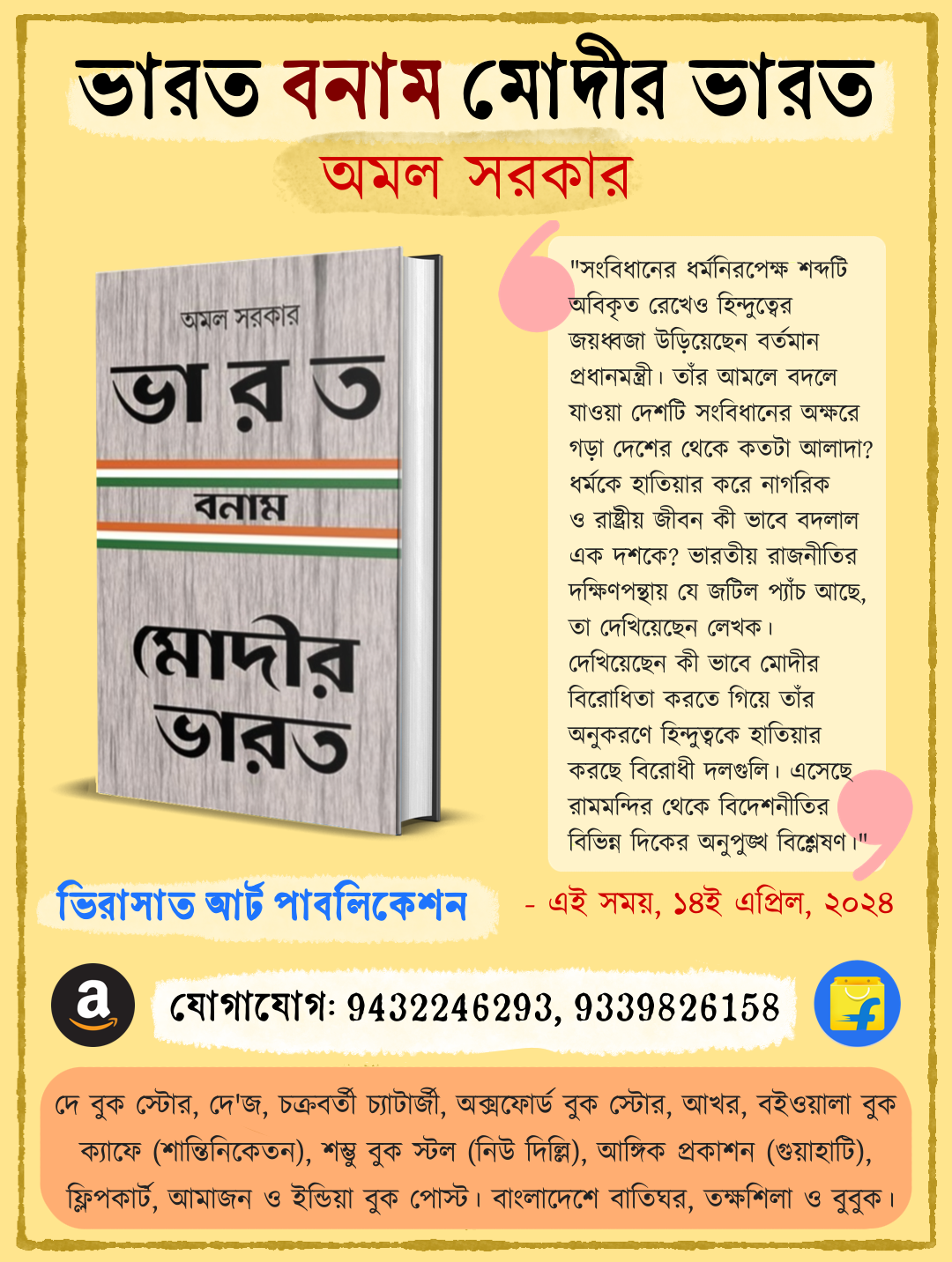- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 aja | 207.47.98.129 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ০৪:৩৫409333
aja | 207.47.98.129 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ০৪:৩৫409333- ন্যা:, ঝালা না। তারানা হোক।
 dri | 75.3.201.181 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১১:০২409344
dri | 75.3.201.181 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১১:০২409344- একটা কথা ছোট করে বলে আমি ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে যাব। যে আম্রিকায় চিরদিন প্রাইভেট সে¾ট্রাল ব্যাঙ্ক ছিল না। সোয়া দুশো বছরের ইতিহাসে সে¾ট্রাল ব্যাঙ্কের ক®¾ট্রাল হাত বদলেছে কয়েকবার। এখন যেটা ফেডারাল রিজার্ভ সেটা প্রতিষ্টিত হয়েছিল ১৯১৩ সালে। আম্রিকার ইতিহাসে তৃতীয় প্রাইভেট সে¾ট্রাল ব্যাঙ্ক। এর আগে দুবার প্রাইভেট সে¾ট্রাল ব্যাঙ্কের ক®¾ট্রাল সরকার কেড়ে নিয়েছিল। এই নিয়ে পরে বিশদে কচলানো যাবে।
কিন্তু এবার আমরা চলে যাব একটু অন্য জায়গায়, অন্য সময়ে।
 dri | 75.3.201.181 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১১:১৮409355
dri | 75.3.201.181 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১১:১৮409355- মিড্ল এজে ইউরোপে কারেন্সি হিসেবে নোটের চলনের আগে অনেক জায়গায় প্রেশিয়াস মেটাল ব্যবহার হত। সোনার বদলে লোকে জিনিষপত্র কিনত। স্বর্ণকারদের সেই থেকেই একটা বিজনেস ছিল। আর সোনার কারবার করত বলে গোল্ডস্মিথদের কাছে বড় বড় ভল্ট থাকত। সাধারণ লোকেদের কাছে টাকা অর্থাৎ সোনার পরিমাণ বেশী হয়ে গেলে অনেক সময় এরা এই স্বর্ণকারদের লকারে সোনা গচ্ছিত রাখতে আসত একটা নমিনাল ফির বিনিময়ে। সোনা জমা দিলে স্বর্ণকার একটা কাগজে লেখা রিসিট ফেরত দিত।
এইবার হল কি, লোকে দেখল এ তো ভারী কনভিনিয়েন্ট! কেনাকাটি করতে সোনার কয়েন আদানপ্রদানের কি দরকার? স্বর্ণকারের রিসিট গুলো অদলবদল করলেই তো হয়। ওগুলো ক্যারি করা অনেক সোজা। এইটাই হল পেপার মানির প্রথম প্রোটোটাইপ।
(লক্ষ্য করুন, এই ব্যবস্থায় কোন সে¾ট্রাল মানি ক্রিয়েটিং এজেন্সি নেই। যে সোনার কারবার করতে রাজি সেই সে¾ট্রাল ব্যাঙ্কার হতে পারবে। কারণ সোনাই বেসিকালি মানি।)
 dri | 75.3.201.181 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১১:৩৪409366
dri | 75.3.201.181 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১১:৩৪409366- এই ব্যবস্থা কিছুদিন চলার পর ব্যাঙ্কারদের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে ভাবল যে এই যে সোনা (মানি) আমার কাছে লোকে জমা রাখল সেইটা তো আমি অন্য লোককে ধার হিসেবে দিতে পারি। আমাকে তো আর সোনাটা ফিজিকালি দিতে হবে না। আমি জাস্ট একটা পেপার সার্টিফিকেট লিখে দেব ব্যাস। সেইটাই লোকে এক্সচেঞ্জ করতে পারবে। এর ফলে হল এই যে প্রতি একটা জমা রাখা সোনার কয়েন বাজারে দুটো করে গোল্ড সার্টিফিকেট ঘুরতে লাগল। এতে করে গোল্ডস্মিথরা রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেল। যদিও এই ব্যবস্থার একটা সমস্যা হল সবাই যদি একই সঙ্গে সার্টিফিকেট ভাঙ্গিয়ে সোনা তুলতে যায়, তাহলে জালিয়াতিটা ধরা পড়ে যাবে। (এখনকার পরিভাষায় যাকে বলে ব্যাঙ্ক ফেল করবে)। তবে সাধারনত সবাই একসাথে টাকা তুলতে আসে না। আজকের দিনের ব্যাঙ্কগুলোও সব এই প্রিন্সিপ্লে চলে। একে বলে ফ্র্যাকশানাল রিজার্ভ ব্যাঙ্কিং। তবে কিছু কিছু সময়ে এমনও হয়েছে লোকেরা স্বর্ণকারদের এই ট্রিকটা ধরে ফেলেছে এবং আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। এরকম ধনী ব্যাঙ্কারদের পুড়িয়ে মারার কিছু পেন্টিং পাওয়া যায়।
তবে আজকালকার দিনে যেমন এইসব ছোট ছোট ট্রিক বহুচর্চিত, তখনকার দিনে এগুলো ছিল মূলত ফ্যামিলি সিক্রেট।
 dri | 75.3.201.181 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১২:০২409377
dri | 75.3.201.181 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১২:০২409377- তো যাই হোক, সব মিলিয়ে, মানে যাকে বলে অন অ্যান অ্যাভারেজ ইন দা লং রান, স্বর্ণকারদের ব্যাবসা ফুলে ফেঁপে উঠল।
আঠেরোশো শতকে জার্মানীতে এরকমই একজন স্বর্ণকারের নাম ছিল মেয়ার অ্যামশেল রথসচাইল্ড। এনার মাথায় একটা গ্র্যান্ড প্ল্যান এল। ইনি এনার পাঁচ ছেলে এবং আরো কিছু লাইকমাইন্ডেড বন্ধুদের নিয়ে পুরো পৃথিবীটা কব্জা করার একটা ব্লুপ্রিন্ট বানালেন।
কিভাবে? শুধু ইন্ডিভিজুয়ালকে লোন দিয়ে লাভ হয়, কিন্তু অত লাভ হয় না। আমরা রাজাদের লোন দেব। রাজারা বড় বড় অ্যামাউন্টে লোন নেবে। আর রাজাদের থেকে টাকা আদায়টা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। রাজার সবচেয়ে বড় কোল্যাটারাল হল প্রজার খাজনা। এছাড়াও, আরেকটা ব্যাপার। রাজাকে লোন দিলে রাজার পলিসিকে আমরা ইনফ্লুয়েন্স করতে পারব। আমরা বলতে পারব অমুকটা করল তবেই আমরা লোন দেব। নইলে নয়। আর রাজা যদি বেশী ট্যান্ডাইম্যান্ডাই করে? তাহলে আমরা রাজার কোন এক অ্যাভারসারিকে লোন দেব যে পরে রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে পারবে।
 dri | 75.3.201.181 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১২:৪৫409388
dri | 75.3.201.181 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১২:৪৫409388- মেয়ার রথসচাইল্ড উইলিয়ামস নামে এক জার্মান প্রিন্সের সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চার করেছিলেন। প্রিন্স উইলিয়ামসের ছিল সৈন্য ভাড়া দেবার বিজনেস। সৈন্য ভাড়া দেওয়াটা অনেকটা এখনকার দিনের বডি শপিংএর মত ব্যাপার। যে রাজা সৈন্য রেন্ট করবে তাকে সৈন্য প্রতি একটা বড় অ্যামাউন্ট দিতে হত। আর প্রিন্স তার থেকে একটি ছোট অ্যামাউন্ট সৈন্যকে দিতেন মাইনে বাবদ। এছাড়াও ছিল ব্লাড মানি। অর্থাৎ সৈন্য মরলে একটা হেফটি ফাইন কালেক্ট করা হত। রথসচাইল্ড প্রিন্স উইলিয়ামসের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন।
যুদ্ধবিগ্রহ সৈন্য ভাড়া বিজনেসের পক্ষে ভালো ছিল। প্রিন্স উইলিয়ামস তার রয়্যাল কানেকশান কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন যায়গায় যুদ্ধে উশকানি দিতেন। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে রাজা তৃতীয় জর্জ প্রিন্স উইলিয়ামসের থেকে সৈন্য ভাড়া করেছিলেন। তাতে বহু সৈন্য মারা যাওয়ায় রথসচাইল্ডদের খুব লাভ হয়েছিল। আর নেপোলিয়ান ফ্র্যাঙ্কফুর্ট আক্রমণ করলে প্রিন্স উইলিয়ামস প্রাণের ভয়ে ডেনমার্কে পালান। যাবার আগে তাঁর সৈন্যদের প্রাপ্য থোক টাকা তিনি রথসচাইল্ডের কাছে রেখে যান। বলেন পরে সময় মত দিয়ে দিতে। কিন্তু রথসচাইল্ড সেই টাকা সৈন্যদের না দিয়ে আত্মসাৎ করেন।
 dri | 75.3.201.181 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১২:৪৬409399
dri | 75.3.201.181 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১২:৪৬409399- (ক্রমশ)
 r | 125.18.104.1 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১৫:৫৬409410
r | 125.18.104.1 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১৫:৫৬409410- দ্রি প্রচন্ড গম্ভীর বিষয় নিয়ে গল্প করছেন। ভাল লাগে না।
যাক গে। ব্যাপার হলএই- যে কোনো দেশের মনিটারি পলিসির দায়িত্ব সেই দেশের সে¾ট্রাল ব্যাঙ্কের। অর্থাৎ, অর্থনীতিতে টাকার জোগান বাড়ানো হবে, না কমানো হবে, সেই সিদ্ধান্ত সে¾ট্রাল ব্যাঙ্ক নেয়- ভারতে আর বি আই, আমেরিকায় ফেড। এবার টাকার জোগান বাড়ে কমে কি করে? টাকার জোগান বাড়ানো মানে কিন্তু টাকা ছাপানো নয়। ফিজিকালি যে টাকা ছাপানো হয়, তা টাকার জোগানের বৃদ্ধির এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। বাকিটা হয় হিসেবের খাতায়, ক্রেডিট ও ডেবিট কমিয়ে বাড়িয়ে। যে কোনো সে¾ট্রাল ব্যাঙ্ক মূলত: তিন উপায়ে টাকার জোগান নিয়ন্ত্রণ করে:
প্রথম, ওপেন মার্কেট অপরেশন।
দ্বিতীয়, সুদের হার। সুদের হার কমলে টাকার জোগান বাড়ে, বাড়লে টাকার জোগান কমে।
তৃতীয়, রিজার্ভ, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক কত টাকা বাধ্যতামূলকভাবে সে¾ট্রাল ব্যাঙ্কে জমা রাখবে। রিজার্ভের রিকোয়ারমেন্ট বাড়লে টাকার জোগান কমে, কমলে টাকার জোগান বাড়ে।
এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হল ওপেন মার্কেট অপারেশনস।
 anaamik | 196.15.16.20 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১৬:২২409421
anaamik | 196.15.16.20 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১৬:২২409421- অ্যাবসল্যুট সুদের হার? না, সে¾ট্রাল ব্যাঙ্ক যে হারে সুদ দিচ্ছে এবং যে হারে সুদ নিচ্ছে তাদের ব্যবধান? (মানে বাংলা ভাষায় জিগালে Repo আর Reverse Repoর ডিফারেন্স?)
পরে আরো প্রশ্ন আসবে !!!
 r | 125.18.104.1 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১৬:৩৬409433
r | 125.18.104.1 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১৬:৩৬409433- ওপেন মার্কেট অপারেশন মানে, টাকার জোগান বাড়াতে গেলে সে¾ট্রাল ব্যাঙ্ক সরকারের থেকে সরকারী বন্ড কেনে। কমাতে গেলে উল্টোটা করে। পাতি বাংলায় ওপেন মার্কেট অপারেশন মানে সে¾ট্রাল ব্যাঙ্ক সরকারকে ধার দিল। পৃথিবীর সমস্ত সে¾ট্রাল ব্যাঙ্ক ও সরকারের মধ্যে এই টাকা এবং সিকিওরিটির লেনদেন চলে। যে ধার দেয়, সে সুদও নেয়। ধরুন, আপনি বন্ড কিনলেন মানে যে কোম্পানির থেকে বন্ড কিনলেন তাকে টাকা ধার দিলেন। এই বন্ডের যে কুপন পেমেন্ট সেটা হল এই বন্ডের উপর আপনার সুদ। একই ব্যাপার সে¾ট্রাল ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এইবার দ্রি-এর প্রশ্ন হল- সে¾ট্রাল ব্যাঙ্কের এই যে সুদের পয়সা পাওনা হয়, তা দিয়ে সে¾ট্রাল ব্যাঙ্ক কি করে? ফেড সাধারণত: এই পয়সা রিবেট হিসেবে সরকারকে ফেরৎ দেয়। অন্তর্জাল ঘেঁটে তাই দেখতে পাচ্ছি। বেশি কচকচিতে না গিয়ে লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম-
http://www.publiceye.org/conspire/flaherty/Federal_Reserve.html
লিঙ্কটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আসন্ন কিছু কনস্পিরেসি তঙ্কেÄর বিরুদ্ধ যুক্তি এতে থাকতেও পারে। :-)
 r | 125.18.104.1 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১৬:৪০409444
r | 125.18.104.1 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১৬:৪০409444- ওটা নিয়ে অন্য থ্রেডে পড়াশুনো হতে পারে। নইলে দ্রি-এর মূল প্রতিপাদ্যের আলোচনা খেই হারিয়ে ফেলবে।
 r | 125.18.104.1 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১৬:৪১409455
r | 125.18.104.1 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১৬:৪১409455- আর বি আই ফেডের মত করে, নাকি অন্য কিছু করে জানতে গেলে আর বি আই-র অ্যানুয়াল স্টেটমেন্টের ব্যালান্স শীট দেখতে হবে। এখন এন্থু পাচ্ছি না। এনিওয়ে, ফেডই এখানে আলোচ্য।
 ranjan roy | 122.168.230.221 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১৯:১৮409466
ranjan roy | 122.168.230.221 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১৯:১৮409466- সে¾ট্রাল ব্যাংকিংএর ওপর ঈশেন ও প্রো বৈ চ মহত্বপূর্ণ ফিচার গুলো নিয়ে বলেই দিয়েছেন।
আমার চোখে ( অম্রিকান ব্যাংকিং এর কিস্যু জানিনে। রিজার্ভ ব্যাংক নিয়ে দু'চার কথা কইতে পারি। তবু ভুলের সম্ভাবনা থেকে যাবে।
আমার চোখে সরকার আর রিজার্ভ ব্যাংকের সম্পক্কো হল মালিক আর ড্রাইভারের সম্পর্ক।
গাড়ির মালিক ড্রাইভারকে চাকরি দেয়, আবার তাড়িয়ে ও দেয়।
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর এদের ভারত সরকার নিযুক্ত করে( অর্থাৎ তাড়াতেও পারে।)
মালিক ড্রাইভারকে বলে -- গড়িয়াহাট মার্কেট লে চলো।
ড্রাইভারের বলার স্বাধীনতা আছে -- স্যার, ওদিকে জ্যাম আছে, বা ওদিকে কার্ফু লেগেছে, বা ওপাড়ায় দাঙ্গা হচ্ছে, বা ওমুক দিকে ওয়ান ওয়ে, গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে হবে।
এও বলতে পারে--- স্যার, টায়ারটা আর না বদলালেই নয়। বা দশ লিটার পেট্রোল ভরাতে হবে। বা, রোববারের দিন গ্যারেজে পাঠাতে হবে। ওদিনটা আপনাকে ট্যাক্সি চড়তে হবে।
তেমনি প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক সরকারের একটি নির্দিষ্ট কালখন্ডে বিশিষ্ট মনিটরি ও ফিস্ক্যাল পলিসি থাকে। সেই পলিসি ফর্মেশনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দেয়া ফীডব্যাকেরও কিছু ভাগিদারী থাকে।
রিজার্ভ ব্যাংক কোন স্বয়ম্ভু পাতালফোঁড় শিব নয়। ওর কাজ ড্রাইভারের মত সরকারের আর্থিক নীতির( যার মহত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট হল মৌদ্রিক ও রাজস্ব নীতি) এফেক্টিভ ইমপ্লিমেন্টেশন যাতে হয় তা' দেখা।
ফলে ঠিক ড্রাইভারের মত ও সরকারকে পরামর্শ দেয়, সতর্ক করে--- অর্থনীতির গাড়ি ঠিক রাস্তায় চলছে, না কি কাঁচা রাস্তায় নেমে পড়েছে।
এখন টাকার যোগান ,যেমন রঙ্গন বলেছেন, শুধু কয়েন ও নোট ছাপানোর ওপর নির্ভর করে না।
খেয়াল করুন, আপনাদের ছোটবেলায় একটাকার নোট রিজার্ভ ব্যাংক নয়, মিনিস্ট্রি অফ ফাইনান্স ছাপাতো। আর তাতে আর বি আই এর গভর্নরের বদলে ফাইনান্স সেক্রেটারির নাম ও দস্তখত থাকতো।
সবচেয়ে বড় কথা--এইনোট ছাড়া অন্য দুটো হচ্ছে ব্যাংক মানি আর তারই সাব গ্রুপ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সরকারের নেয়া ধার।
আবার মানি সাপ্লাই মাপতে গেলে আর একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে----ভেলোসিটি অফ মানি। অর্থাৎ একটি নোট( দশ, বিশ বা একশ' যাই হোক না কেন) একটি একক সময়ে ক'হাত ঘুরছে। তেমনি একটি ব্যাংক চেক এনক্যাশ্ হওয়ার আগে ক'হাত ঘুরছে।
অর্থাৎ যদি দশবার হাতবদল হয় তাহলে একটি চেক বা একটি নোট দশ্টার কাজ করছে। অর্থাৎ মানি সাপ্লাই দশগুণো বেড়ে গেল।
দ্রি'র প্রশ্ন আর বি আই সরকারকে ধার দিলে সুদ নেবে কেন? সুদ নামক এই চেকটি লাগিয়ে রিজার্ভ ব্যাংক সরকারের লোলুপ দৃষ্টির সামনে লোনেবল ফান্ডকে মাহাঙ্গা করে দিচ্ছে।
খতিয়ে দেখুন, সমস্ত সরকার, কিবা রাজ্য, কিবা দিল্লি, কিবা বাম, কিবা ডান--- ধার করে খরচা করার জন্যে মুখিয়ে আছে।
নিজের নিজের ভোট ব্যাংককে খুশি রাখতে এমপি-এমএলএ রা সরকারি পয়সাকে লার্গেসির মত ব্যবহার করে।
তেমনি সুদের হার কমিয়ে রিজার্ভ ব্যাংক সরকারকে দরকারি (ব্যাংকের মতে) ব্যয় করতে মোটিভেট করতে পারে। এবং প্রাপ্ত সুদের ফলে রিজার্ভ ব্যাংকের কোর ফান্ড বাড়ে।(চলবে)
 ranjan roy | 122.168.230.221 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১৯:৪০409477
ranjan roy | 122.168.230.221 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ১৯:৪০409477- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটা প্রধান কাজ হল ইনফ্লেশন( বা তার বিপরীতে ডিফ্লেশন) কে নিয়ন্ত্রণ করা।
সেটা করতে গিয়ে রিজার্ভ ব্যাংক টোটাল মানি সাপ্লাইকে নিয়ন্ত্রণ করে বা, কোন বিশেষ দিকে বা সেগমেন্টে মানি সাপ্লাইয়ে ডান্ডা চালায়।
ধরুন, মুদ্রাস্ফীতির একটা বড় ফিচার হল too much money chasing too few goods.
কাজেই মুদ্রার সার্বিক যোগান কম করাও। তখন রিজার্ভ ব্যাংক--- ব্যাংক রেট (অর্থাৎ, যে হারে ও অন্য ব্যাংকের সিকিউরিটি কেনা বেচায় ডিস্কাউন্ট দেয়)। ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও( অর্থাৎ কোন ব্যাংক তার সমস্ত ডিপোজিটের যে প্রতিশত রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে নগদ জমা রাখে) আর স্ট্যাটুটরি লিকুইডিটি রেশিও( অর্থাৎ কোন ব্যাংক ঐভাবে মোট জমার যতটুকু অন্য ব্যাংকে বা সিকিউরিটিতে সরকারি বন্ডে লগ্নি করে রেকেছে) তার দর বাড়িয়ে দেয়। ফলে ব্যাংকের কাছে লোনেবল ফান্ড অর্থাৎ ক্লায়েন্টদের ঋণ দেবার মত ফান্ড কমে যায়। ফলে ব্যাংক সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। লোন মাহাংগা হয় । লোকে লোন কম নেয়। বাজারে মানি সাপ্লাইয়ে চেক লাগে। রিসেশনের সময় রিজার্ভ ব্যাংক ঠিক উল্টোটি করে । আর্থাৎ প্রথম স্থিতিতে ডিয়ার মানি পলিসি, দ্বিতীয় স্থিতিতে চীপ মানি পলিসি।
আর সার্বিক মানি সাপ্লাইয়ে কমবেশি না করে কোন একদিকে কাড়ি করলো। ধরুণ, সব ব্যাংককে নির্দেশ দিল--- হাউস বিল্ডিং লোনে সুদের হার কম বা বেশি কর। যেমন চিদাম্বরম ইদানীং ফরমান জারি করে সমস্ত ব্যাংককে বাধ্য করেছেন ঐ লোনে সুদের হার কমিয়ে আনতে। সবাই করেছেও। ভাবছি মেয়ের নামে একটা ছোট্ট বাড়ির লোন নিয়ে নেব। আপনারাও নিন। ইন্কাম ট্যাক্সে মূলের শোধের উপর একলাখ ও সুদের ওপর একলাখ পঞ্চাশ হাজার অব্দি ছাড় পাবেন। মন্দ কি!
আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো। এবার কনস্পিরেসি?
ডি: আর বেশি মুখ খুল্লে আমার বিদ্যের ফাঁক ধরা পড়ে যাবে।
 arjo | 168.26.215.13 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ২৩:২৭409488
arjo | 168.26.215.13 | ১৬ জানুয়ারি ২০০৯ ২৩:২৭409488- মর্যাল - কনস্পিরেসি থিওরী বুঝতে হলে অর্থনীতির ছাত্র হতে হবে। কি কঠিন রে বাবা। মাথার অনেক উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।
 dri | 129.46.154.185 | ১৭ জানুয়ারি ২০০৯ ০৩:৫৩409499
dri | 129.46.154.185 | ১৭ জানুয়ারি ২০০৯ ০৩:৫৩409499- রঞ্জনদা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোর ফান্ডের টাকা ফাইনালি কার পকেটে যায়? বা ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করতে গেলে, কিসে খরচ হয়?
 dri | 75.3.201.181 | ১৭ জানুয়ারি ২০০৯ ১২:২১409510
dri | 75.3.201.181 | ১৭ জানুয়ারি ২০০৯ ১২:২১409510- যাই হোক, রথসচাইল্ডের গল্পটা আর একটু আগে বাড়ানো যাক।
রথচাইল্ডের তাঁর পুঁজি পাঁচ ছেলের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে তাদের পাঁচটি শহরে পাঠিয়ে দেন, লন্ডন, প্যারিস, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, নেপল্স আর ভিয়েনা। উদ্দেশ্য, ব্যবসার মাধ্যমে প্রতিপত্তি বাড়িয়ে পুরো ইউরোপকে নিজেদের ক®¾ট্রালে আনা। এদের মধ্যে সবচেয়ে স্মার্ট দুভাই ছিলেন লন্ডনের নেথান এবং প্যারিসের জেমস। এরা দুজন দুপাশ থেকে উশকানি দিয়ে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের যুদ্ধ বাধান। রাজাদের লোন দিয়ে, অস্ত্রের ব্যাবসা করে প্রচুর লাভ করেন। রথসচাইল্ডদের প্রাইভেট ইনফর্মারের নেটওয়ার্ক খুব ভালো ছিল। তখনকার দিনের অফিশিয়াল কুরিয়ারদের থেকে বেশী তাড়াতাড়ি খবর এরা পাঠাতে পারত, এবং সেজন্য এরা ওয়েল ট্রেনড্ পায়রা ব্যবহার করত। তাই ওয়াটারলুর যুদ্ধের খবর নেথান রথসচাইল্ডের কাছে একদিন আগে পৌঁছে গেছিল। কিন্তু নেথানের এজেন্টরা রটিয়ে দেয় যে ইংল্যান্ড যুদ্ধে হেরে গেছে। স্টক মার্কেট ক্র্যাশ করে। তখন নেথান খুব সস্তায় প্রচুর স্টক কিনে নেন। পরের দিন আসল খবর আসায় স্টক মার্কেট রিবাউন্ড করে এবং নেথান রাতারাতি ধনকুবের বনে যান। ফাইনালি সেই পয়সা দিয়ে ইংলিশ স্টক এক্সচেঞ্জ, ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড এবং মিন্ট এবং গোল্ড ট্রেডে বিরাট আধিপত্য স্থাপন করেন।
পরে রথসচাইল্ড ফ্যামিলি রয়টার্স কেনেন, এবং আরো অনেক পরে এ পির সঙ্কÄও কেনেন, যারা আজকের দিনের খবরের অন্যতম প্রধান সোর্স।
 ranjan roy | 122.168.21.32 | ১৭ জানুয়ারি ২০০৯ ২০:৩৫409521
ranjan roy | 122.168.21.32 | ১৭ জানুয়ারি ২০০৯ ২০:৩৫409521- দ্রি,
কারও পকেটে কেন যাবে? সুদ বা সার্ভিস চার্জ থেকে কোন ব্যাংক বা রিজার্ভ ব্যাংক যা কামাবে তা ওর কোর ফান্ড বা পুঁজিতে যোগ হবে, হয়ে ব্যালান্স শীটে দেখা যাবে। রিজার্ভ ব্যাংকের হর্তাকর্তারা সবাই চাকরিপেশা। কাজেই লাভের গুড়ের ভাগ ওদের কাছে যেতে পারে মাত্র বেতন ও ভাতার মাধ্যমে, অন্যভাবে নয়।
এবার বলি-- রাজ্যসরকারকে রিজার্ভ ব্যাংক নামমাত্র সুদে ওভারড্রাফট্ দেয়, কিন্তু ১৫দিনের স্টিপুলেশনে। ওর মধ্যে রাজ্যসরকারকে ওসব ক্লিয়ার করে খাতা শুন্য করতে হবে।
ডি: এসব ম্যাক্রো ইকনমিকস্ এর পরীক্ষায় আসে না। তাই কেউ আওয়াজ দেবে না, বলে দিলাম।:)))
কেন্দ্রীয় সরকারকে যখনই দেয় নামমাত্র সুদেই দেয়। বাকি ঐ কুপন বন্ড- যা ঈশেন বলেছে। এর বেশি জানি না।
র্যাপো- রিভার্স র্যাপো:---------- কোন ব্যাংকের যখন হঠাৎ কোন টাকায় টান পড়ে, ধরুন এক-দুদিনের জন্যে, ধরুন,কোন বড় প্রোজেক্ট ফাইনান্স করতে গিয়ে, তখন ঐ ব্যাংক সিকিউরিটি না বেচে এক দুদিনের জন্যে রিজর্ভ ব্যাংক থেকে ধার নেয়। কমার্শিয়াল দরে। তখন আর বি আই যে সুদের হারে এক-দুদিনের জন্যে কোন ব্যাংককে ধার দেয় তা'হল র্যাপো রেট। আবার ঐ টাকা যদি রিজার্ভ ব্যাংক অন্য ব্যাংক থেকে অতি স্বল্পকালীন সুদে ধার নিয়ে প্রথম ব্যাংকটিকে দেয়, তাহলে দ্বিতীয় ব্যাংকটি রিজার্ভ ব্যাংক থেকে যে হারে সুদ পাবে তাহল রিভার্স র্যাপো রেট। যেমন স্যাকরা সস্তায় সোনা কিনে বেশি দামে গয়না বেচে।
আর কিস্যু বলবো না। বিদ্যের বহর সবাই বুঝে ফেলবে। এবার কনস্পিরেসি???
 ranjan roy | 122.168.21.32 | ১৭ জানুয়ারি ২০০৯ ২০:৩৭409532
ranjan roy | 122.168.21.32 | ১৭ জানুয়ারি ২০০৯ ২০:৩৭409532- প্রো বৈ চ,
কোথাও ভুল চোখে পড়লে নি:সংকোচে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিও।
 dri | 75.3.201.181 | ১৮ জানুয়ারি ২০০৯ ১০:২৮409544
dri | 75.3.201.181 | ১৮ জানুয়ারি ২০০৯ ১০:২৮409544- ফেড আর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কম্প্যারিজনে আমরা পরে ফিরে আসব। বিশেষ করে প্রফিট কার পকেটে যায় সেই পার্টটা। কিন্তু আপাতত গল্পটা আর একটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক। গাড়ী খুব লেটে চলছে।
 dri | 75.3.201.181 | ১৮ জানুয়ারি ২০০৯ ১২:২৩409555
dri | 75.3.201.181 | ১৮ জানুয়ারি ২০০৯ ১২:২৩409555- ইওরোপে তখন একটু একটু করে সে¾ট্রাল ব্যাঙ্কের ক®¾ট্রাল চলে যাচ্ছে প্রাইভেট ব্যাঙ্কারদের হাতে। রাজারা একটু একটু করে সে¾ট্রাল ব্যাঙ্কারদের পোষ মানতে শুরু করেছে। যুদ্ধ মারামারি যত বাড়ছে, ব্যাঙ্কারদের লাভও বাড়ছে। কলোনী বাড়ছে। চলছে কলোনিস্টদের ধার দেওয়া। মেয়ার রথসচাইল্ডের প্ল্যানের একটা ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট ছিল পৃথিবী জয় করার প্রথম ধাপ হল একেকটা দেশের সে¾ট্রাল ব্যাঙ্ক দখল করা, দেশে দেশে যুদ্ধ বাধানো। তিনি বলেছিলেন, "লেট মি ইস্যু অ্যান্ড ক®¾ট্রাল আ নেশান'স মানি, অ্যান্ড আই কেয়ার নট হু রাইট্স দা ল'জ।"
এমন সময় শুরু হল আমেরিকান ওয়ার অব ইন্ডিপেন্ডেন্স। যুদ্ধের অনেক কারণ ছিল। অন্যতমটি ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের ছাপা নোট কলোনিস্টদের ব্যবহার করতে বাধ্য করা। চড়া সুদে। টমাস জেফারসন বলেছিলেন, "আই সিনসিয়ারলি বিলিভ দা ব্যাঙ্কিং ইনস্টিচিউশানস হ্যাভিং দা ইস্যুয়িং পাওয়ার অব মানি আর মোর ডেঞ্জারাস টু লিবার্টি দ্যান স্ট্যান্ডিং আর্মিজ।" যে পনেরো বছর ধরে যুদ্ধ হয়েছিল সে সময় কলোনিস্টরা নিজেদের নোট নিজেরা ইস্যু করত। যুদ্ধে হার হল, কিন্তু ব্যাঙ্কাররা হাল ছাড়ল না। ওরা অন্য পথ ধরল। আলেক্সান্ডার হ্যামিলটনকে দিয়ে ফেডারাল ব্যাঙ্কের জন্য লবি করালো, এবং সফল হল। ১৭৯১এ আমেরিকার প্রথম ফেডারাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হল। প্রেসিডেন্টরা মোটামুটি সবাই ব্যাঙ্কারদের ব্যপারটা বুঝতেন। কিন্তু কিছু প্রেইডেন্ট রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অ্যান্ড্রু জ্যাকসন। ১৮৩৬ সালে তিনি দ্বিতীয় ফেডারাল ব্যাঙ্কটি বন্ধ করে দেন এবং বলেন যে ইন্টারন্যাশাল ব্যাঙ্কারদের সব লোন শোধ করে দেওয়া হবে। পরের মাসেই জ্যাকসনের ওপর একটা অ্যাসেসিনেশান অ্যাটেম্পট হল। কিন্তু অ্যাহ্ম মোমেন্টে পয়েন্ট ব্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে রিভলভারের ট্রিগার জ্যাম হয়ে গুলি বেরোলো না।
 nyara | 64.105.168.210 | ১৮ জানুয়ারি ২০০৯ ১৪:০৯409566
nyara | 64.105.168.210 | ১৮ জানুয়ারি ২০০৯ ১৪:০৯409566- দ্রির গপ্প পড়তে ভাল লাগছে। কিন্তু উইকির সঙ্গে ডেট-টেটগুলো ঠিক মিলছে না। যদি ১৮৩৬-এ ব্যাঙ্ক বন্ধ করা হয়, তাহলে অ্যাসাসিনেশন অ্যাটেম্পট দেখা যাচ্ছে তার আগে হয়েছে। আর যদি রিচার্টার ভেটোইং বা ফান্ড উইথড্রয়ালকে ব্যাংক বন্ধ করা বলে বলা হয়ে থাকে, তাহলে অ্যাসাসিনেশন অ্যাটেম্পট, এক মাস নয়, প্রায় বছর-দেড দুই পরের।
তার থেকেও বড় কথা, সাম্ভাব্য অ্যাসাসিন গুলি করার যে কারণগুলো দিয়েছিল, তার মধ্যে একটিমাত্র ব্যাংক-সংক্রান্ত। যেমন আর একটা কারণ হিসেবে লোকটি জানায় যে সে রিচার্ড দা থার্ড, এবং জ্যাকসন তার কেরানি ছিল। লোকটি অবশ্য পাগল বলে বিবেচিত হওয়ায় সাজা থেকে রেহাই পেয়ে যায়। ব্যাংকারদের কনস্পিরেসির প্রতি যে ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেটা ধোপে খুব একটা টিঁকছে না। অবশ্য আমার সোর্স শুধুই উইকি।
On January 30, 1835, what is believed to be the first attempt to kill a sitting President of the United States occurred just outside the United States Capitol Building. When Jackson was leaving the Capitol Building out of the East Portico after the funeral of South Carolina Representative Warren R. Davis, Richard Lawrence, an unemployed and deranged house-painter from England, either burst from a crowd or stepped out from hiding behind a column and aimed a pistol at Jackson which misfired. Lawrence then pulled out a second pistol which also misfired. It has since been postulated that the moisture from the humid weather of the day contributed to the double misfiring. [41] Lawrence was then restrained, with legend saying that Jackson attacked Lawrence with his cane, prompting his aides to restrain him. Others present, including David Crockett, restrained and disarmed Lawrence.
Richard Lawrence gave the doctors several reasons for the shooting. He had recently lost his job painting houses and somehow blamed Jackson. He claimed that with the President dead, "money would be more plenty"—a reference to Jackson’s struggle with the Bank of the United States—and that he "could not rise until the President fell." Finally, he informed his interrogators that he was actually a deposed English King—Richard III, specifically, dead since 1485—and that Jackson was merely his clerk. He was deemed insane, institutionalized, and never punished for his assassination attempt.
 dri | 75.3.201.181 | ১৮ জানুয়ারি ২০০৯ ১৪:৪৬409577
dri | 75.3.201.181 | ১৮ জানুয়ারি ২০০৯ ১৪:৪৬409577- তারিখে গোলমাল হয়েছে। আসলে সবকিছু লিখতে গেলে এত বড় হয়ে যায়, তাই শর্টে মারার জন্য আমি মাঝেমাঝেই অ্যাপ্রক্সিমেট ডেট বসাই, যাস্ট মোটামুটি সময়ের ধারণা দেবার জন্য। অ্যাকিউরেটলি বলতে গেলে এরকম হবে ১৮৩৪ ডিসেম্বারে জ্যাকসন তাঁর প্ল্যানের কথা ঘোষনা করেন। তার পরই খুনের চেষ্টা হয়। তারপর প্রস্তাব কংগ্রেসে যায়। কংগ্রেস মেম্বারদের ব্যাঙ্কাররা কিনে নেয় এবং কংগ্রেস প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। তারপর ১৮৩৬ এ কংগ্রেসের রায় অগ্রাহ্য করে জ্যাকসন প্রেসিডেনশিয়াল পাওয়ার লাগিয়ে ব্যাঙ্ক বন্ধ করেন। সুতরাং ক্রোনোলজি ঠিকই আছে।
আর খুনের মোটিভের সরকারি ভার্সান বরাবরই ব্যাঙ্কাররা ক®¾ট্রাল করে। কারণ, কি মিডিয়ায়, কি পুলিশে, কি জুডিশিয়াল সিস্টেমে ব্যাঙ্কারদের প্রভাব খুব বেশী। এখানেই আসে 'কনস্পিরেসি'। এ পর্য্যন্ত আমেরিকায় যত প্রেসিডেন্টকে খুনের চেষ্টা হয়েছে সবগুলোকেই কনস্পিরেসি থিওরিস্টরা ব্যাঙ্কারদের যোগ দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু সরকারী ভার্সান সবসময়ই অন্য। তো আপনি কোনটা বিশ্বাস করবেন সেটা আপনার ব্যাপার।
 dri | 75.3.201.181 | ১৮ জানুয়ারি ২০০৯ ১৪:৫৫409588
dri | 75.3.201.181 | ১৮ জানুয়ারি ২০০৯ ১৪:৫৫409588- এরপর আসে সিভিল ওয়ার। যুদ্ধের সময় ব্যাঙ্কাররা লিঙ্কনকে ২৪% রেটে সুদ দেবে বলায়, লিঙ্কন নিজেই নিজের নোট ছাপান এবং সেটাকে লিগাল টেন্ডার বলে ঘোষনা করেন। সেই নোটের পিঠে সবুজ কালি দিয়ে লেখা ছিল বলে সেটাকে বলা হত 'গ্রীনব্যাক'। আজও ডলারকে অনেকে গ্রীনবাক বা বাক বলে। যুদ্ধ জেতার খুব অল্প দিন পরেই লিঙ্কন আততায়ীর গুলিতে খুন হন। এবং যথারীতি নিন্দুকেরা বলেন এটা ব্যাঙ্কারদের কাজ। ব্যাঙ্কারদের জিজ্ঞেস করলে অবভিয়াসলি তারা অন্য কথা বলবে।
 dri | 75.3.201.181 | ১৮ জানুয়ারি ২০০৯ ১৫:৪২409599
dri | 75.3.201.181 | ১৮ জানুয়ারি ২০০৯ ১৫:৪২409599- এরপর ব্যাঙ্কাররা উঠে পড়ে লাগে আমেরিকার সে¾ট্রাল ব্যাঙ্কের ওপর দখল পাকা করতে। রথসচাইল্ডের কিছু এজেন্ট আমেরিকার কিছু সিলেক্ট ফ্যামিলির সাথে হাত মিলিয়ে খুব সাইলেন্টলি নিজেদের পোজিশান কন্সলিডেট করে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, জে পি মরগ্যান ফাইনান্সে, কুন অ্যান্ড লোব কোম্পানীর মালিক হিসেবে জেকব শিফ, রকাফেলার ফ্যামিলি তেলে, কার্নেগী স্টীলে এবং হ্যারিসন রেলরোডে।
১৯০৭ সালে নিউ ইয়র্কে একটি ব্যাঙ্কিং কোল্যাপ্স ইঞ্জিনিয়ার করান জে পি মরগ্যান, পাবলিকলি রটিয়ে দিয়ে যে অমুক ব্যাঙ্ক ইনসলভ্যান্ট। তারপর একটা মহাকেওস হয়। তখন ব্যাঙ্কাররা প্রস্তাব দেয় যে ফাইনান্সিয়াল অস্থিরতা দূর করতে আমাদের চাই একটি প্রাইভেট সে¾ট্রাল ব্যাংক যা সব সমস্যার সমাধান করবে। একটি কমিশান বসে। ইলেকশান ক্যাম্পেনে ব্যাঙ্কাররা উড্রো উইলসনকে সাপোর্ট করেন এই শর্তে যে জিতলে তিনি ফেডারাল রিজার্ভ অ্যাক্ট পাস করবেন। ১৯১৩ সালে ফেডারাল রিজার্ভ অ্যাক্ট পাস হয়।
পরে উইলসন দু:খ করে বলেন --
"I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the civilized world no longer a Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men. "
 dri | 75.3.201.181 | ১৮ জানুয়ারি ২০০৯ ১৬:০১409610
dri | 75.3.201.181 | ১৮ জানুয়ারি ২০০৯ ১৬:০১409610- পেছনে ব্যাঙ্কারদের ইনফ্লুয়েন্সে যে আছে এটা পরিস্কার হবে কিচু কিছু প্রেসিডেন্টের ভাষণে।
যেমন উইলসন বলেছিলেন --
"Since I entered politics, I have chiefly had men’s views confided to me privately. Some of the biggest men in the United States, in the field of commerce and manufacture, are afraid of somebody, are afraid of something. They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they had better not speak above their breath when they speak in condemnation of it."
আইজেনহাওয়ারের এই স্পীচটাও শুনে দেখতে পারেন। এই ফেয়ারওয়েল স্পীচে উনি বলেছিলেন আমেরিকার মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স ভুল লোকেদের ক®¾ট্রালে চলে যাবার পোটেনশিয়াল আছে এবং সিটিজেনদের ইনফর্মড থাকার উপদেশ দিয়েছেন।
আর কেনেডির এই স্পীচটা হয়ত আপনারা সকলেই শুনেছেন।
 dri | 75.3.201.181 | ১৮ জানুয়ারি ২০০৯ ১৬:১০409621
dri | 75.3.201.181 | ১৮ জানুয়ারি ২০০৯ ১৬:১০409621- কেনেডির স্পীচটা দিয়েই দেখি, ইউটিউব ভিডিওটা সরিয়ে নিয়েছে :-)।
এনিওয়ে, আরো আছে। এইটা শুনুন।
 nyara | 64.105.168.210 | ১৯ জানুয়ারি ২০০৯ ০৩:৩৭409632
nyara | 64.105.168.210 | ১৯ জানুয়ারি ২০০৯ ০৩:৩৭409632- ইয়ে, মানে শুধু প্রেসিডেন্ট খুনের চেষ্টাই নাকি সব কনস্পিরেসি থিওরিই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে? প্রমাণসাপেক্ষ কি কিছুই পাওয়া যাবে না?
এক্সপেক্টেশন ঠিকমতন সেট করে নিতে চাইছি।
 dri | 75.3.201.181 | ১৯ জানুয়ারি ২০০৯ ০৮:৪৭409643
dri | 75.3.201.181 | ১৯ জানুয়ারি ২০০৯ ০৮:৪৭409643- প্রমাণসাপেক্ষ কিছু পাওয়া মুস্কিল। কারণ প্রমাণ কে করবে? এখানে আমি কনস্পিরেসি থিওরিটা কি একটু স্পষ্ট করে বলে নি। সেটা হল, পৃথিবীর গোপন রুলার হল একটা ছোট গ্রুপ। তার মধ্যে ইন্টারন্যাশানাল ব্যাঙ্কাররা আছে, আরো কিছু কিছু পাওয়ারফুল লোক আছে। তারাই দুনিয়া চালায়। কিন্তু এরা আড়ালে থাকতে চায়। এরা পাবলিক অ্যাটেনশান চায় না। ইলেকশান, পোলিটিকাল পার্টি, প্রেসিডেন্ট এগুলো এদের কাভার। এক ধরণের সং অ্যান্ড ডান্স পাবলিককে এনগেজ রাখার জন্য। এতে সুবিধা হল পাবলিক আউটরেজের টার্গেট কখনো এদের হতে হয় না। টমেটো আর পচা ডিমগুলো পলিটিশিয়ানরাই সামলায়, আর এরা আড়ালে নিজেদের কাজ করতে পারে শান্তিতে। মিডিয়া, লেজিসলেটিভ বডি, এক্সিকিউটিভ বডি, জুডিশিয়ারিতে এদের অসম্ভব ইনফ্লুয়েন্স।
তা এই যদি হয়, তাহলে এদের এক্সপোজ করবে কে? প্রমাণের যে রিগার থাকে সেই রিগারে কিছু করতে গেলে মিডিয়া, পুলিশ, জাস্টিস সিস্টেমের সহযোগিতা চাই। এদের কিনে নিলে কে প্রমাণ করবে? এরকম ক্ষেত্রে ছোট ছোট মিডিয়া লিক, ঘটনার পারম্পর্য্য, বা চাউর করা মেইনস্ট্রীম ঘটনা বা এক্সপ্লানেশানে ফাঁক, এগুলোই ভরসা।
একটা ছোট এগ্জাম্পল দি। এই সাতশো বিলিয়ান ডলারের বেইলাউট। এই কিছুদিন আগেই হল। আমাদের সবারই মনে আছে। একটা সময় ছিল যখন বিলটা পাস হবে কি হবে না বোঝা যাচ্ছিল না। কংগ্রেসে বিলটা পাস হল না। তারপর সেনেটে পাস হল। তারপর কংগ্রেসে বিলটা ঘুরে যাবার আগে বিবিসিতে এভেলিন ডি রথসচাইল্ডের ইন্টারভিউ দেখিয়েছিল। উনি সাধারনত মিডিয়ায় আসেন না। আগে তো একেবারেই আসতেন না। এই ডাউনটার্নের পর থেকে দু একবার এসেছেন। উনি বলেন যে 'ইফ ইট ডাজন্ট গো থ্রু, উই হ্যাভ অ্যান অ্যাম্পাস দ্যাট ইজ ভেরি সিরিয়াস ... হোয়াট ডাজ ইট মীন উই হ্যাভ টু লার্ন। দেখুন এই ভিডিওটি। । বেসিকালি এটা হল মিষ্টি করে বলে দেওয়া যে বাবা বিল যদি পাস না কর, বহুত বাম্বু আছে কপালে। আবার একই সময়ে সিস্প্যানে দেখিয়েছিল, ক্যালিফোর্নিয়ার কংগ্রেসম্যান ব্র্যাড শেরম্যান হাউসে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে বিল না পাস করালে আমাদের মার্শাল লয়ের ভয় দেখানো হয়েছিল। এই রইল তার ভিডিও, । কিন্তু এরপর কংগ্রেসম্যান ব্র্যাড এই কথার ক্ল্যারিফিকেশান জানতে চাওয়া সব জার্নালিস্টকেই ইন্টারভিউ রিফিউজ করেছিলেন।
কেন করেছিলেন? আমরা জানি না। জানা সম্ভব নয়। আমরা গেস করতে পারি মাত্র। কিছু কি প্রমাণ হল? হল না।
প্রমাণ খুব গোলমেলে জিনিষ। ধরুন আপনাকে আমি যদি বলি নীল আর্মস্ট্রং ১৯৬৯ এ চাঁদে গেছিলেন এটা প্রমাণ করুন। কি বলবেন আপনি? করুন তো দেখি ইন্টারনেট ঘেঁটে যে আর্মস্ট্রং চাঁদে গেছিলেন।
এদিকে আমার মূল গপ্পো কিন্তু একহনো সেষ হয় নি। শুধু ল্যাদ খেয়ে লিখছি না। একটু টাইম দিতে হবে।
আরো একটা কথা, এসব বিশ্বাস করতেই হবে এমন কথা নেই।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... kk, দ)
(লিখছেন... Prativa Sarker, kk, প্রতিভা)
(লিখছেন... অরিন, kk, সন্তোষ সেন )
(লিখছেন... Somnath Pal, রমিত চট্টোপাধ্যায়, পোল খুলে গেল)
(লিখছেন... Prabhas Sen, Argha Bagchi, সিক্যুয়েল চাই)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... রঞ্জন , রঞ্জন , r2h)
(লিখছেন... মোহাম্মদ কাজী মামুন, দ)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... এরাও তাই বলছে, Prativa Sarker, বিপ্লব রহমান)
(লিখছেন... Kishore Ghosal, সমরেশ মুখার্জী, kk)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... অরিন, অরিন, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, ছোট মুখে , সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... :|:, পাপাঙ্গুল, পাপাঙ্গুল)
(লিখছেন... kk, দীপ, dc)
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : [email protected] ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত