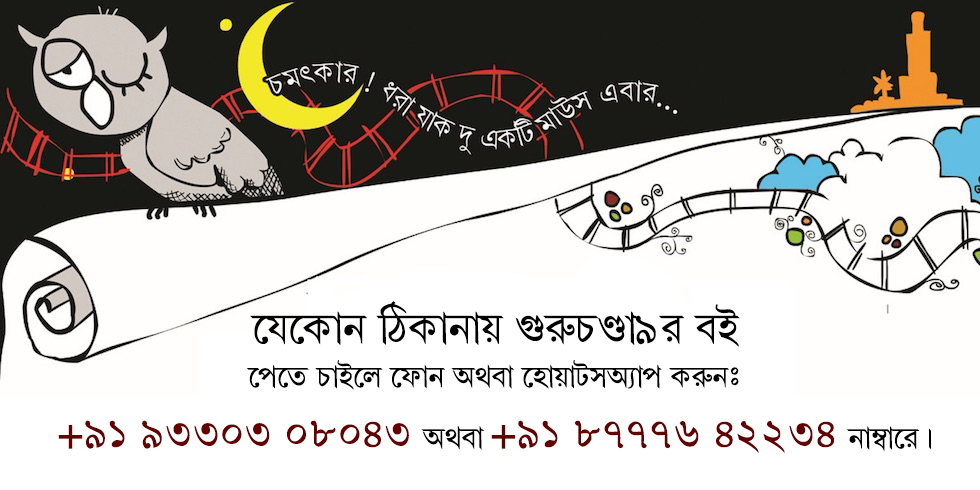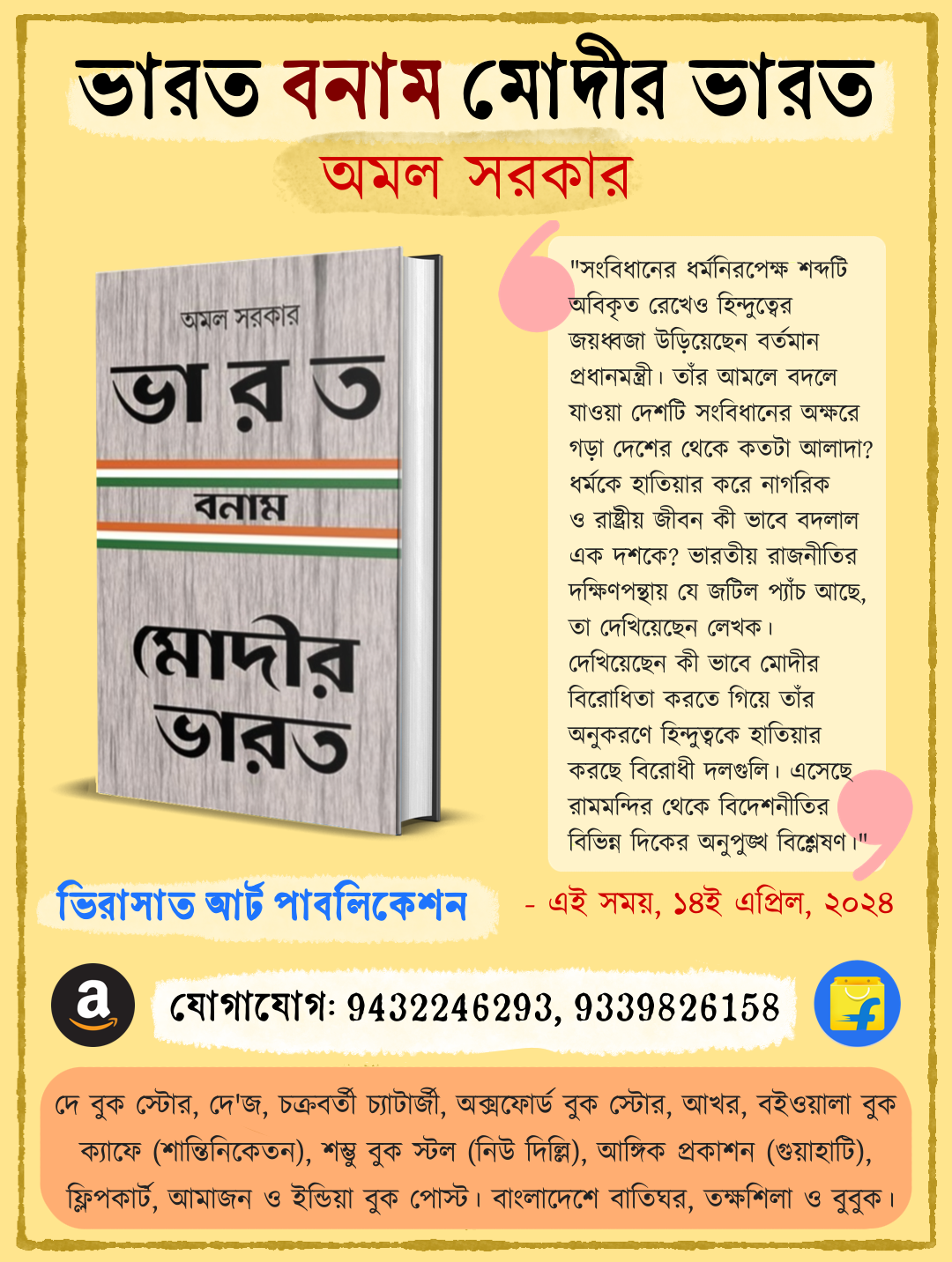- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 pi | 118.22.232.90 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:০৭525787
pi | 118.22.232.90 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:০৭525787- শ্রমনিবিড় শিল্প বানানোর আগে একটা পরামর্শ ছিল, ল্যাণ্ড ইউজ ম্যাপ বানানো, সেটা বোধহয় মিস করে গেছেন। ঃ)
 Ishan | 202.43.65.245 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:০৭525786
Ishan | 202.43.65.245 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:০৭525786- সিকি সিকি। ভাট না দিলে বাংলাপ্লেন থেকে এট্টু কনভার্ট করে দিক। আমার কনভার্টারটা খুঁজে পাই না।
 pi | 118.22.232.90 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:০৮525788
pi | 118.22.232.90 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:০৮525788- এগুলো নিয়ে আগে মতামত শুনি, বাকি ক্রমে আসিতেছে।
 PT | 213.110.243.23 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:০৯525789
PT | 213.110.243.23 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:০৯525789- ও পাই দিদি - এই সব "কাতারে কাতারে বন্ধ কারখানা নিয়ে বা কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে" বিরোধী নেত্রী বিস্তর অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। গত দু বছরে একটিরও কোন গতি হয় নি। শুধু আবেগ দিয়ে এসব করা যায় না-দেশে অকর্মণ্য কোর্ট ইত্যাদি আছে -BIFR না কি একটা যেন আছে। সর্বোপরি আমার জমিতে আমি চাষ না করে ফেলে রাখলে কিংবা আমার কারখানায় আমি উৎপাদন না করে জমি আটকে রাখলে সরকারের বোধহয় বিশেষ কিছু করার নেই। আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি তাই না? তাই আমরা সব রকম "জোর" খাটানোর বিরুদ্ধে। সরকারের "আইন আইনের পথ নেবে" বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছড়া কিস্যু করার নেই।
 pi | 118.22.232.90 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:১৪525790
pi | 118.22.232.90 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:১৪525790- শুধু আবেগ দিয়ে করার কথা কে ই বা বলেছে ? উল্টোটাই তো বলা হচ্ছে। উদ্যোগ নিতে। সেটা আগের সরকারের জন্য যেমন প্রযোজ্য, এই সরকারের জন্যেও ঃ)
আর সরকার চাইলে কী করতে পারে, তার জন্যই হিন্ন্দমোটরের উদাঃ টা দিয়েছিলাম।
 pi | 118.22.232.90 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:২০525791
pi | 118.22.232.90 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:২০525791- কাগজ মিল।
কল্যাণীর প্যাপিরাস মিল। ২০০৯ এর খবর।
দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে কারখানায় তালা। একসময় প্রায় হাজার শ্রমিকের কাজের ঠিকানা কল্যাণীর প্যাপিরাস মিলের।
শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা কী করেছেন ? মেশিন পাচার করে নিজেদের পকেট ভরেছেন।
যেমন ভরেছেন মালিকেরাও। পার্টির সহযোগিতায় সরকারি অনুগ্রহণে জমি অধিগ্রহণ হয়েছিল। সেই জমি দেখিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে কোটি কোটি লোন সংগ্রহ,অতঃপর কিছুদিন শিল্প শিল্প নাটকের আড়ালে সেই টাকা ও শ্রমিকদের বকেয়া মাইনে লুঠ, এবং অবশেষে দায়িত্ব নিয়ে "রুগ্ন' সাজিয়ে সাত বছরের মধ্যে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া ।
শ্রমিকেরাও অবশ্য পকেট ভরেছেন,কারখানা খোলার আশায়। এতদিন ধরে। আর তাঁদের অজান্তেই নিলাম হয়ে বিক্রি হয়ে গেছে কারখানা। যাঁদের জমি অধিগ্রহণ করে কারখানা তৈরি হয়েছিল, তাঁদের পরিবারের একজন করে কাজ পেয়েছিলেন কারখানায়। কৃষক থেকে শ্রমিক হওয়ার পরবর্তী ধাপে আজ তাঁরা কেউ স্টেশনে বাদাম বিক্রেতা, কেউ ট্রেনের হকার, কেউ বেকার। জমি নিলামের টাকা গে®ছে মূলত ব্যাংকের লোন শোধ করতে। আর নিলাম হয়ে যাওয়াতে বন্ধ হবার মুখে সরকারি ভাতাও।
রাজ্য জুড়ে যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও প্যাপিরাস পেপারের মিল বন্ধ হল কেন সেটা আজ ও প্রশ্ন। আশির দশকে দ্রুত বিস্তারিত হতে থাকা কল্যাণী শিল্পাঞ্চলের আড়াইশো তিনশো কারখানার প্রায় সবাই একে একে খাতা বন্ধ করার পিছনেও মালিকদের এরকম ই দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ আর কারখানার ফাঁদ পেতে টাকা বানাবার ছক আছে কিনা, প্রশ্ন জাগে তা নিয়েও।
তবে প্যাপিরাসের কর্মচ্যুত শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছেন , সরকারী ভাতা, ও ঐ জমিতে তৈরি হওয়া মেডিকাল কলেজের অধস্তন বিভাগ গুলিতেকর্মসংস্থানের দাবী তে। সংগ্রামে সামিল অন্যান্য কারখানার জনতাও। "বন্ধ কারখানার সংযুক্ত সংগ্রাম সমিতি' তাদেরই মুখপাত্র ।
-----------------------------------------------
২০১২ র খবর।
কল্যানী স্পিনিং মিলের শ্রমিকরা অনির্দিষ্টকালীন অনশনে, তাদের পাশে দাঁড়ান
অনিন্দ্য পাত্র
----------------------------------------------------
নোনাডাঙার ঘটনার রেশ মিটতে না মিটতেই আরো একটা অনির্দিষ্টকালীন অনশন। এবার ঘটনাস্থল কল্যানী। গত ২৩ শে এপ্রিল, ২০১২ থেকে কল্যানী স্পিনিং মিলের চারজন অস্থায়ী শ্রমিক আর এক সহযোগী, সব মিলিয়ে পাঁচজন অনির্দিষ্টকালীন অনশন শুরু করেছেন। শহর কলকাতার পরিধির মধ্যে থাকা নোনাডাঙা যেভাবে খবরের শিরোনাম হয়েছে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে দূরবর্তী কল্যানী কিন্তু সেভাবে সাধারণ মানুষের নজর কাড়েনি। অনশনের ছয়দিন অতিক্রান্ত। কিন্ত মিল কর্তৃপক্ষ বা সরকার কারো তরফেই কোনোরকম আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। এই অবস্থায় স্পিনিং মিলের শ্রমিকরা তাঁদের দাবীদাওয়া, তাঁদের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট মানুষের কাছে যতদূর সম্ভব পৌঁছে দিতে চান। সেই কারণেই এই লেখার অবতরণা।
প্রথমত ঃ বলা দরকার কল্যানী স্পিনিং মিলের আজকের এই অনশন কোনো ভুঁইফোড়, হঠাৎ গজিয়ে ওঠা আন্দোলন নয়। নয় নয় করে তারও একটা দুবছরের ইতিহাস আছে। ঘটনার শুরু ২০১০ সালের গোড়ার দিকে। কোনো এক সময়ের শিল্পাঞ্চল কল্যানীতে সেইসময় মৃত শহরের মত সার সার বন্ধ কারখানা। তারই মধ্যে টিমটিম করে জ্বলতে থাকা সলতের মত যে দু-একটা চালু কারখানা দেখা যেত, তার একটা হল এই স্পিনিং মিল। ওদিকে তখন ""শিল্প আমাদের ভবিষ্যত"" শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত আর ন্যানোর শোকে দিবারাত্র অশ্রুপাত। অথচ একই সময়ে কল্যানী স্পিনিং মিলে আমরা দেখব "শ্রমিকবন্ধু" সরকার শ্রম-আইনকে ছোটো করে বক দেখিয়ে চালু করেছেন ""আউটসাইডার"" (এটা কামু দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে, সংস্কৃতিবান মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তো, কিছুই বলা যায় না) নামে নতুন এক অস্থায়ী শ্রমিকের ক্যাটেগরি। যাঁরা স্থায়ী শ্রমিকদের মত একই কাজ করবেন, অথচ তাঁদের এমনকি কোনো পরিচয়পত্রও দেওয়া হবে না, পি এফ, ই এস আই তো দূরস্থান। আর মাইনে? যে কাজে স্থায়ী শ্রমিকরা পান দৈনিক প্রায় সাড়ে চারশো টাকা, সেখানে ঐ একই কাজে ঐ ""আউটসাইডার""রা পেতেন দৈনিক আশি টাকা। এখানে মনে রাখতে হবে কল্যানী স্পিনিং মিল কিন্তু কানোরিয়া বাজোরিয়াদের মত ব্যক্তিপুঁজির চটকল নয়, যেখানে এই ধরণের শ্রম আইন না মানা আর অরাজকতা দেখে আমরা অভ্যস্ত। কল্যানী স্পিনিং মিল হল রীতিমত একটা সরকারী কারখানা। সেখানেই শ্রম আইনের এই অবস্থা! কার আমলে? না, একটি 'বাম' সরকারের আমলে।
তো যাই হোক, সুখের কথা হল, ২০১০ সাল নাগাদ কল্যানীতে বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে কিছুটা নড়াচড়া দেখা যায়। সিটু, আইএনটিইউসির বাইরে বেরিয়ে নতুনভাবে সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করতে থাকেন কিছু শ্রমিক। যে নড়াচড়ার একটা আঁচ এসে লাগে স্পিনিং মিলের অস্থায়ী শ্রমিকদের মধ্যেও। ২০১০ এর মাঝামঝি তাঁরা গড়ে তোলেন তাঁদের নিজেদের ইউনিয়ন। এটাকে আমরা বলব আন্দোলনের প্রথম ফেজ। যে সময়ে দাবী ছিল - ১) বেতন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস, ২) পিএফ, ইএসআই এবং পরিচয়পত্র দেওয়া। নড়াচড়া শুরু হতেই ২০১০ এর জুলাই-অগাস্ট নাগাদ সরকার একটি সার্কুলার দিয়ে এই "আউটসাইডার'দের মাইনে ১৫০ / ১৬০ টাকা করে দেয়। সরকারের ধারণা ছিল এতে হয়তো শ্রমিকদের প্রাথমিক ক্ষোভটা প্রশমিত হবে। তাদের উপর সিটুর প্রভাবও বজায় রাখা যাবে। কিন্তু হিতে বিপরীত হল। ইউনিয়নে সংগঠিত হওয়ার সাথে সাথেই মাইনে বেড়ে যাওয়াতে উদ্দীপ্ত হয়ে শ্রমিকরা আরো বড় আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করলেন। এবং ঠিক তখনই আন্দোলনের উপর প্রথম আঘাতটা এল। ২০১০ এর ডিসেম্বরে দুশোরও বেশী অস্থায়ী কর্মীকে এক ধাক্কায় কারখানার গেটের বাইরে বের করে দেওয়া হল।
এইখান থেকে আন্দোলন প্রবেশ করল তার দ্বিতীয় ফেজে। এই বেআইনি ছাঁটাই এর বিরুদ্ধে এবং সবাইকে পুনর্বহালের দাবীতে আন্দোলন চলতে থাকে। সমস্ত দপ্তরে চিঠি পাঠানো, অবস্থান, ধর্না, গেট মিটিং ইত্যাদি যা যা করার সবই করা হয়। এর মধ্যে এসে পড়ে "ঐতিহাসিক' ২০১১। নির্বাচনের ঠিক আগে, মার্চ মাসে, সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য শ্রমিকরা প্রথমবার অনির্দিষ্টকালীন অনশন শুরু করেন। অনশনের পাঁচ দিনের মাথায় মহাকরণ থেকে হস্তক্ষেপ করা হয়। সরকারের উদ্যোগে নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং এ একটি ত্রিপাক্ষিক মীটিং ডাকা হয়। কিন্তু সেই মীটিং এ মিল ম্যানেজমেন্ট অনুপস্থিত থাকে। তাদের পক্ষ থেকে একটি চিঠি দিয়ে সরকারকে জানানো হয় ওরকম "আউটসাইডার' নামক কোনো শ্রমিক নাকি মিলে কখনও ছিলই না। অর্থাৎ কলমের একটি খোঁচায় দুশোরও বেশী জ্বলজ্যান্ত মানুষের অস্তিত্ব জাস্ট "নেই' হয়ে যায়।
ইতিমধ্যে বাংলায় বহু আকাঙ্খিত "পরিবর্তন' হয়ে গেছে। পরিবর্তন হয়েছে মিল ম্যানেজমেন্টেও। পরিবর্তন হয়নি শুধু শ্রমিকদের অবস্থার। তাই নতুন উদ্যমে নতুন সরকারের সবকটি দপ্তরে, সমস্ত ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া চলতে থাকে। যে সমস্ত মন্ত্রী ও আধিকারিকদের সাথে দেখা করে অভিযোগ জানানো সম্ভব হয়, শ্রমিকদের দাবীর যৌক্তিকতা মেনে নেন সকলেই। কিন্তু সমস্যার কোনো সুরাহা হয় না। আন্দোলনকারী শ্রমিকদের কাছে একটা ব্যাপার ক্রমশ ঃ পরিষ্কার হতে থাকে - আসলে এই মিলটা সরকার বন্ধ করার দিকে এগোতে চাইছে। এই ধারণাটা হওয়ার কিছু বাস্তব ভিত্তিও ছিল। অস্থায়ী "আউটসাইডার'-দের বাদ দিলে মিলের বাকি স্থায়ী শ্রমিকদের গড় বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাদের উৎপাদনশীলতা কম, অথচ মাইনে বেশী। অন্যদিকে স্থায়ীপদে নতুন নিয়োগ বন্ধ। মূল উৎপাদনটা করত এই অস্থায়ীরাই। কাজেই তাদের বের করে দেওয়ার একটাই অর্থ - সরকার উৎপাদনে আর অত উৎসাহী নয়। শ্রমিকরা এই ব্যাপারটা আঁচ করতে পারার কিছুদিনের মধ্যেই তাদের অনুমানকে সত্যি করে ২০১১-র অক্টোবর মাস থেকে কল্যানী স্পিনিং মিলে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্থায়ী শ্রমিকদের বসিয়ে রেখে মাইনে দেওয়া চলতে থাকে। সেখানেই শেষ নয়। তিনমাস আগে মিলের বিদ্যুৎ সংযোগও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। আর এইখান থেকেই আন্দোলনও তার তৃতীয় ফেজে প্রবেশ করে।
আন্দোলনের এই দফায় শ্রমিকদের মূল দাবী হল কল্যানী স্পিনিং মিলের পুনরুজ্জীবন। তার সাথে পুরোনো দাবীগুলো তো আছেই। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বন্ধ কারখানা খোলার। তা তো হলই না, উল্টে একটা চালু সরকারী কারখানাকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে ধীরে ধীরে। একদিকে ট্রাফিক সিগনালে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নামে, ট্রাইডেন্ট লাইট লাগানোর নামে কোটি কোটি টাকা ফালতু খরচা করা চলছে, অথচ একটা সরকারী কারখানা, যার উপর এতগুলো পরিবারের রুটি-রুজি নির্ভরশীল, সেটাকে পুনরুজ্জীবনের জন্য কোনো বিনিয়োগের চিহ্নমাত্র নেই। মিল পুনরুজ্জীবনের দাবীতে চিঠি দেওয়া হয়েছে শ্রমমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুকে, এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। চিঠি দেওয়ার পরে একমাস অপেক্ষা করা হয়েছে উত্তরের জন্য। উত্তর মেলে নি।
আমরা জানি উত্তর মেলে না। তাই শ্রমিকদের সামনে অনশন ছাড়া প্রতিবাদের আর কোনো শান্তিপূর্ণ পথ জানা ছিল না। তাঁরা সেই পথই নিয়েছেন। অনশনের আজ সপ্তম দিন। নোনাডাঙার মত এখানেও সরকারের তরফে এখনো অব্দি কোনো হস্তক্ষেপ নেই। দেখলে মনে হবে তাঁরা নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেছেন। এসব তুচ্ছ জাগতিক ব্যাপার তাঁদের স্পর্শ করে না। অথচ একটু মস্তিষ্ক প্রয়োগ করলে বুঝতেন কল্যানী স্পিনিং মিল তাঁদের সামনে একটা অ্যাসিড টেস্ট রেখেছে। সত্যিই কি তাঁরা কর্মসংস্থানমুখী শিল্প চান? নাকি পুরোটাই ফাঁকা বুলি? কল্যানী কিন্তু একটাভাবে এই প্রশ্নটার ফয়সালা করে দেবে। শুধু বচনে কি চিঁড়ে ভিজবে তার পরেও? বোধহয় না।
-----------------------------------------------------------
সেই একই ট্র্যাডিশন সমানে ...
এনিওয়ে, কল্যাণীর আপডেট কেউ দিতে পারবে(ন) ?
 b | 135.20.82.166 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:২১525792
b | 135.20.82.166 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:২১525792- বন্ধ কারখানার ব্যাপারে কি ধরণের পলিসি এখানে গভর্ণমেন্ট নিতে পারে? প্রাইভেট কোম্পানীর কস্ট কমিয়ে? না তাদের প্রফিটেবিলিটি বাড়িয়ে?
আমি সিরিয়াস এখানে।
১। মজদুর আন্দোলন কমিয়ে। তা হ এর লেখায় অনেকদিন আগে পড়েছিলাম এই জাতীয় মজদুর আন্দোলনগুলো বেশিরভাগই ছিলো প্রভিডেন্ট ফান্ড মেরে দেওয়া মালিকের বিরুদ্ধে।
২। চট ইত্যাদি শিল্পগুলি পুনরুজ্জীবিত করে। এখানে তো চটের ডিমান্ড কমে গেছে, তাছড়া প্রধান সাপ্লাই সোর্স দেশভাগের ফলে অন্য দেশে। সেখানে গভঃ কি করতে পারতো?
৩। চেনাশোনা বড় কারখানার মধ্যে আমার জীবনের মধ্যে বসে যেতে দেখলামঃ হিন্দমোটর্স আর ডানলপ। হিন্দমোটর্স জানি না (মানে কেন লোকে হঠাৎ অ্যাম্বাসাডর ছেড়ে পাগলের মত অন্য গাড়ি কিনতে লাগলো, বা এখনো কিনে চলেছে কে জানে?), ডানলপ খুব কাছ থেকে দ্যাখা। সরকার কেন, তার প্রপিতামহেরো ক্ষমতা ছিলো না ম্যানেজমেন্টের চুরির হাত থেকে ডানলপ বাঁচানো।
৪। বড় থিওরী (কাতারে কাতারে বন্ধ কারখানা) ছেড়ে কেস বাই কেস, ইন্ডাস্ট্রী বাই ইন্ডাস্ট্রী দেখলে বোধ হয় সুবিধা হতে পারে।
 b | 135.20.82.166 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:২৪525793
b | 135.20.82.166 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:২৪525793- দাঁড়ান, পাইয়ের 9:05 এর পোস্ট লিখতে লিখতে মিস করে গেছি। পড়ে দেখি।
 Ishan | 202.43.65.245 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:২৫525796
Ishan | 202.43.65.245 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:২৫525796- বন্ধ কারখানার জমিতে শিল্প হয়েছে তো। বেলঘরিয়ার মোহিনী মিল, দক্ষিণ কলকাতার বন্ধ কারখানার (উষা তো?) জমিতে সাউথ সিটি মল ও আবাসন। তবে সবই প্রোমোটারি শিল্প। লাভের গুড় পেলে কোনোকিছুই আটকায়না।
 PM | 59.248.251.234 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:২৯525797
PM | 59.248.251.234 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:২৯525797- ইশান কাল এতো বড় করে শিল্প চাড়াই কেরলের উন্নতির "উদাহরন" দিলো, আমি তার প্রত্তুত্তরে কিছু ডেটা দিয়ে কটা প্রশ্ন করলাম---ওমা ইশান কেরালা ছেড়ে চলে গেলো ব্রজিল, আমেরিকায় ঃ)
যাকগে, এর পরে আর আর কেরালার উদাহরন দেবেন না কিন্তু। ঃ)
 PT | 213.110.243.23 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:৩৩525798
PT | 213.110.243.23 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:৩৩525798- "ল্যাণ্ড ইউজ ম্যাপ"-এ ঠিক কি আছে পাইদিদি জানেন? আমি যা বুঝলাম এতে রাজ্যের কোথায় কোথায় কি ধরণের জমি আছে তার একটা পরিচিতি আছে। এটা পুর্ব মেদিনিপুরের "ল্যাণ্ড ইউজ ম্যাপ"-

এ দিয়ে ব্যবসায়ীর কোন উপকার হবেনা। কেননা প্রয়োজন হলে ব্যবসায়ী তিন ফসলী জমিই চাইবে। আর যদি দরে পোষায় তাহলে চাষী সেই জমিই বেচবে। আর দরে না পোষালে কোন ব্যবসায়ী পুরুলিয়ার ঊষর জমিতে কারখানা বানাতে যাবেই সস্তায় জমির জন্য এমন ভাবার কোন কারণ নেই।
উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে চর্মশিল্পে প্রচুর জল লাগে-কাজেই সেই কারখানাটি কোন জলের সোর্সের ধারে হতে হবে। আর পব-তে কোন জলের ধারের জমি উর্বর হয়না? তদুপরি ট্যানারি থেকে কিভাবে পরিবেশের ক্ষতি হয় সে নিয়ে এই পেপারের শুধু কনক্লুসান পড়ে ফেলুনঃ http://home.iitk.ac.in/~sgupta/tannery_report.pdf। আর ট্যানারি কানপুরে কিভাবে গঙ্গার সর্বনাশ করছে পড়ুনঃ In the historic city of Kanpur, a thriving leather industry is central to the crisis facing the Ganga. http://ibnlive.in.com/news/kanpurs-leather-industry-a-bane-for-the-ganga/256834-3.html।
 PT | 213.110.243.23 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:৪০525799
PT | 213.110.243.23 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:৪০525799- "বেলঘরিয়ার মোহিনী মিল, দক্ষিণ কলকাতার বন্ধ কারখানার (উষা তো?) জমিতে সাউথ সিটি মল ও আবাসন।"
এ নিয়ে বেশ কিছুদিন আগে অন্য কারো সঙ্গে চাপান-উতোর হয়েছিল। শুধু ঊষার উদাহরণ নিয়েই বলা যায় যে ২০১৩-তে ঊষা চালু থাকলে তাতে যত লোক কাজ করত তার চাইতে সাউথ সিটি মল ও আবাসন অনেক বেশী শ্রমনিবিড়। এবং সেখানে বর্তমানে অনেক বেশী লোকের কর্ম সংস্থান হয়েছে। এটা চোখে দেখছি বলে বলতে পারলাম।
 Ishan | 202.43.65.245 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:৫৭525800
Ishan | 202.43.65.245 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:৫৭525800- ওমা কেরালা তুলবনা কেন? যেটা লিখেছি সেটাই আরেকবার লিখব। আপনার পয়েন হল কেরালার পার ক্যাপিটা জিডিপি পঃবঃএর চেয়ে বেশি। এবং গড় আয়ুও বেশি। আমার পয়েন হল, কেরালার পার ক্যাপিটা জিডিপির চেয়ে ব্রাজিল অনেক অনেক এগিয়ে। কিন্তু গড় আয়ুতে পিছিয়ে। অতএব ওটি কার্যকারণ সম্পর্ক নয়। এতে ভুলটা কোথায়?
 Ishan | 202.43.65.245 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:৫৯525801
Ishan | 202.43.65.245 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২১:৫৯525801- শ্রমনিবিড়তাটা এখানে পয়েন না, বন্ধ কারখানার জমিতে অন্য কিছু করা যায় কিনা, সেটা হল কোচ্চেন। আমার বক্তব্য হল প্রোমোটারি হলেই সব করা যায়। নইলেই "একটি অঙ্গরাজ্যে সীমিত ক্ষমতায়" -- এইসব অজুহাত চলে আসে।
 PT | 213.110.243.23 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২২:০৬525802
PT | 213.110.243.23 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২২:০৬525802- শ্রমনিবিড়তা কেন কোন পয়েন নয়? বন্ধ কারখানার জমিতে আবাসন হলে সেখানে যদি বেশী লোকের কর্ম সংস্থান হয় তাহলে আবাসনই হোক।
 Ishan | 214.54.36.245 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২২:১২525803
Ishan | 214.54.36.245 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২২:১২525803- শ্রমনিবিড়তা অবশ্যই পয়েন্ট। কিন্তু প্রোমোটারি শিল্প বেশি শ্রমনিবিড় নাকি বিড়িশিল্প, সে আলোচয়ায় ঢুকছিনা। আপনি লিখেছিলেন "সরকারের "আইন আইনের পথ নেবে" বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছড়া কিস্যু করার নেই।" -- সেই প্রসঙ্গে বললাম, যে উপায় ঠিকই বেরোয়, কিন্তু শুধু প্রোমোটারি হলেই বেরোয়। অন্য সব ক্ষেত্রে "হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া কিস্যু করার নেই"।
ক্লিয়ার করা গেল?
 PT | 213.110.243.23 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২২:২৫525804
PT | 213.110.243.23 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২২:২৫525804- না গেল না।
সরকার আপনার পছন্দমত পথে হেঁটে ঊষা কারখানার জমি নিয়ে নিল তারপর দোসা কারখানাকে জমি দিল। তখন সেই সিঙ্গুরের প্রশ্ন এখানেও উঠবে যে দোসা কারাখানাতে কটাই বা লোক চাকরী পাবে-কেননা দোসার মন্ডটাও আজকাল মেশিনে বানানো হয়। সেইজন্য শ্রমনিবিড়তা বাদ দিয়ে রামের জমি শ্যামকে হস্তান্তর করে কোন লাভ নেই। আমরা একই বৃত্তের মধ্যে ঘুরে তক্ক করতে থাকব।
 Ishan | 202.43.65.245 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২২:২৮525805
Ishan | 202.43.65.245 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২২:২৮525805- তাহলে বন্ধ কারখানার জমিতে অন্তত প্রোমোটারি শিল্প করা যায় এটা মানছেন তো?
 pi | 118.22.232.90 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২২:৩২525807
pi | 118.22.232.90 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২২:৩২525807- একটা একটা ক'রে পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা হোক। এই তো বললেন, বন্ধ কারাখানার জমিতে কিছু করা যাবেনা। সেই পয়েন্টটা প্রত্যাহৃত তো। ট্যানারিতে আসছি।
 pi | 118.22.232.90 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২২:৩২525808
pi | 118.22.232.90 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২২:৩২525808- *প্রত্যাহৃত তো ?
 a x | 138.249.1.198 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২৩:৪৮525809
a x | 138.249.1.198 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২৩:৪৮525809- পিটি এই হিসেবটা কোত্থেকে পেলেন - উষা, হিন্দমোটর থেকে সাউথ সিটি মল, আবাসন বেশি শ্রমনিবিড়?
 a x | 138.249.1.194 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২৩:৫২525810
a x | 138.249.1.194 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২৩:৫২525810- আর শ্রমনিবিড় কি না তার সাথে সাথে শ্রমিকদের বকেয়া এবং কত টাকায় রাজ্য সরকার জমি বেচেছে ও কিনেছে সেই হিসেবগুলোও করবেন।
 ranjan roy | 24.96.69.162 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২৩:৫৭525811
ranjan roy | 24.96.69.162 | ৩১ জুলাই ২০১৩ ২৩:৫৭525811- সরি আকা! ঙ মানে কী?
 aka | 76.168.177.5 | ০১ আগস্ট ২০১৩ ০০:১৪525812
aka | 76.168.177.5 | ০১ আগস্ট ২০১৩ ০০:১৪525812- ক এর উল্টো ঃ)
ক খ গ ঘ ঙ
 ranjan roy | 24.96.69.162 | ০১ আগস্ট ২০১৩ ০০:৩০525813
ranjan roy | 24.96.69.162 | ০১ আগস্ট ২০১৩ ০০:৩০525813- দুঃখ পেলুম আকা! ঃ))))আমি নতুন কিছু কালাপাহাড়ী থিওরি ঝাড়ি নি তো? শুধু দেখছিলাম পি এম ও ঈশানের বিতর্কের সুরটা ঠিক বুঝেছি কি না!
এত চটে গেলে কেন?
 ranjan roy | 24.96.69.162 | ০১ আগস্ট ২০১৩ ০০:৩২525814
ranjan roy | 24.96.69.162 | ০১ আগস্ট ২০১৩ ০০:৩২525814- মানে বোঝার চেষ্টা করছিলাম যে তর্কের ঝোঁকে টাইপ-১ বা টাইপ-২ ভুল হচ্ছে কি না! নতুন নতুন পড়েছি, তাই ছোট বাচ্চার দাঁত বের হওয়ার মত সব তাতেই টাইপ-১/২ দেখছি আর কিঃ)))
 aka | 76.168.177.5 | ০১ আগস্ট ২০১৩ ০২:২৭525815
aka | 76.168.177.5 | ০১ আগস্ট ২০১৩ ০২:২৭525815- রঞ্জন দা রাগব কেন। ডেভলপমেন্ট উইথ ডিগনিটি নিয়ে ঙ দিয়েছি। সীমিত সামর্থ্য দিয়ে সরকারের পক্ষে কল্যাণমূলক কাজে ইনভেস্টমেন্ট সম্ভব এই তত্ত্বে ঙ।
আজ অবধি এর কোন উদাহরণ নেই। উন্নতি তারাই করেছে যারা ইনভেস্ট করেছে। আবার তারাই ইনভেস্ট করেছে যাদের ট্যাক্স পেয়াররা ট্যাক্স দেয়, মানে অনেক লোক ট্যাক্স দেবার মতন অবস্থায় আছে, মানে অনেকের চাকরি বাকরি আছে। আবার চাকরি হতে গেলে শিল্প ইত্যাদির দরকার। সমস্যা গভীর, কোনটা আগে কোনটা পরে বলা সহজ নয়। ইন জেনারাল শিল্প না হলে চাকরি বাকরি হবে না। সেটাই আগে বলে আমার মনে হয়।
বাকি পরে।
 T | 24.139.128.15 | ০১ আগস্ট ২০১৩ ০২:৫৬525816
T | 24.139.128.15 | ০১ আগস্ট ২০১৩ ০২:৫৬525816- পাই দি যে পেপারের রেফারেন্স দিল, অর্থাৎ http://economics.mit.edu/files/2490 এর কিছু অংশবিশেষ পড়লাম। অথররা প্রত্যেকেই নামজাদা। কিন্তু যতটুকু পড়লাম তাতে মনে হল, এ পেপার কি আরো একটু গবেষকের চোখে লিখলে ভাল হত না? অবশ্য স্রেফ পপুলার সায়েন্সের ঢঙে লেখার উদ্দেশ্য থাকলে আলাদা কথা। এবং এ অবশ্যই ব্যক্তিগত মতামত।
প্রথমেই যেটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার সেটা হল এই পেপারের প্রকাশের তারিখ। ১২ই অক্টোবর ২০০২। ইন্টারেস্টিং এই কারণে, যে পেপারের 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্র্যাটেজি:ফিউচার অপশন' সেকশনে যেসব মন্তব্য করা হয়েছে তা কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল তা এই সময়ে দাঁড়িয়ে বিচার করা যাবে। যে সমস্ত পথনির্দেশের কথা বলা হয়েছে সেগুলো কতটা সরকার মেনেছে বা মানেনি, ফলে কি ক্ষতি বা কি লাভ হল সেটাও হয়তো দেখা যেত।
কিন্তু, কিছু সাব্জেক্টিভ গোলগোল মন্তব্য এবং কন্ট্রাডিকটরি অংশ দেখে মনে হয়, এতজন অথরের সবার মতামতের ঠিকঠাক এডিট করা বোধহয় হয়ে ওঠে নি। ফলে যতটুকু পড়লাম তাতে বিরক্তির একশেষ।
অথরদের বক্তব্য, 'এইসময়কার (মানে অবশ্যই সেইসময়কার) প্রেক্ষিতে নলেজ ইন্টেন্সিভ ইন্ডাস্ট্রীতে বা হাই টেক সেক্টরে উন্নতির আশা 'অতিরিক্ত' না করাই ভাল। কলকাতা রাতারাতি ব্যাঙ্গালোর বা হায়দারাবাদ হবে না। এইসব জায়গায় ইন্ডাস্ট্রীতে হাই স্কিলড লেবার দরকার এবং ক্লাস্টারড অবস্থায় থাকার ফলে বেনিফিট বেশী। একটা ওয়ে আউট হচ্ছে একটা মেগা ফার্মকে ডেকে একটা হাব মতন তৈরী করা। যেমন উইপ্রো, বা সি আই আই এর আইটি ট্রেনিং ইত্যাদি। কিন্তু যেহেতু এই ক্লাস্টারগুলো আদৌ আশানুযায়ী পারফর্ম করতে পারবে কিনা সেটাতে সন্দেহ আছে, (কারণ পশ্চিমবংগ দেরীতে শুরু করেছে) তাই এটার দিকে বেশী গুরুত্ব না দেওয়াই ভাল।'
২০০২ সালের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে, নলেজ বেসড ইন্ডাস্ট্রী বলতে মেনলি আইটি হাবকে বোঝানো একপ্রকার ক্লিশে নয়? বা খুব কমন মিসটেক নয়? রিয়েল নলেজ বেসড ইন্ডাস্ট্রী তো বরং আইটি র থেকে অনেক বৃহত্তর, এবং ইন্টারেস্টিং যেটা, সেটা হল একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রীর হার্ডওয়্যার ডেভেলপমেন্ট অন্য ধরণের শিল্পে প্রয়োগের জায়গা থাকে। ইম্প্রোভাইজেশনের স্কোপ থাকে, ফলে নতুন শিল্প ক্ষেত্রও তৈরীর সুবিধে রয়েছে। এবং মেগা ফার্মকে ডেকে হাব করার মত আইডিয়া স্রেফ আই টির ক্ষেত্রেই থেমে থাকবে কেন? ম্যানুফাকচারিং শিল্পের ক্ষেত্রেও চলতে পারে। নয় কি? ফলে সিঙ্গুর প্রকল্পের বৈধতার ক্ষেত্রও একরকম তৈরী হয়। মানে অটোহাব ইত্যাদি।
এরপর হায়ার এডুকেশনে কি করা উচিত সেই বিষয়ে মতামত রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের হায়ার এডুকেশনের ক্ষেত্রে একটা অ্যাডভান্টেজ রয়েছে। নেট কোয়ালিফাই করে অনেকে। সায়েন্স এবং আর্টসের পাশে প্রচুর কোয়ালিফায়েড ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট রয়েছে যারা হাইটেক ইন্ডাস্ট্রীতে (মানে অথরদের মতানুযায়ী আই টি) কাজ করতে পারে। শিক্ষার প্রতি বাঙালীদের ন্যাক, রিচ এডুকেশন ট্র্যাডিশন (!) ইত্যাদি ইত্যাদি। আশে পাশের রাজ্যগুলোর শিক্ষায় দূরবস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি। হায়ার এডুকেশনে ইনভেস্টমেন্ট আসা উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি। বিহারের বাপ মা তার ছেলে মেয়েকে দিল্লী পড়তে পাঠালে কলকাতায় কেন নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।
এরপর কি করতে হবে তার হদিসও দেওয়া আছে। সেন্টার অব এক্সেলেন্স গড়ে তোলো যা কিনা সেরা ট্যালেন্টদের এবং রিসার্চারদের আকর্ষণ করবে। শিক্ষায় পলিটিসাইজেশন চলবে না। ক্যাডার নয় এমন শিক্ষাবিদ নিয়োগ করতে হবে। প্রাইমারী থেকে ইংরেজী সরিয়ে দেওয়ার ফলে ধ্বসে গেছে অনেক কিছু। এরপর ঘানার উদাহরণ এবং তারা কেমন সুন্দর বিপিও চালাচ্ছে তার উল্লেখ।
এছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিষ্টানগুলিকে অটোনমি দিতে হবে। প্রাইভেট সেক্টর থেকে কলেজ নির্মাণে উৎসাহ দিতে হবে। সেন্টার অব একেলেন্স গুলির সাথে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় গুলির যোগাযোগ, রিসার্চ গ্রান্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। সমস্ত এডুকেশন স্তরে প্রাইভেট বিনিয়োগ আসলে আসুক। দিল্লী পাবলিক স্কুল যদি চায় সেন্টার খুলতে তবে তাদের খুলতে দেওয়া হোক।
আর হচ্ছে গিয়ে ইন্ডাস্ট্রীর সাথে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। রিসার্চ ল্যাব স্থাপন করে হাইটেক ইন্ডাস্ট্রীর সাথে যোগাযোগ বাড়াতে হবে। এবং ইন্টারেস্টিংলি, Given that there is still some demand for careers in research among Bengali families, there could be a future for privately funded research institutes that teach advanced students and do research on contractual basis, in biotechnology for instance.
আর এরপর হচ্ছে স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রী নিয়ে নানান বক্তব্য। যেটা অথরদের মতে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট।
তো, এতটুকুই পড়েছি, এবং বাকিটা পড়ার কোনো ইচ্ছে হয় নি। কারণ এতে নতুন কিছু নেই। এডুকেশন সংক্রান্ত এইরকম কিছু বক্তব্য মফস্বলের কোনো কলেজের ইকোনমিক্সের স্টুডেন্টও বলে দেবে। কিন্তু এতে কিছু পরস্পর বিরোধী ব্যাপার উঠে আসছে।
মনে হচ্ছে হায়ার এডুকেশন বলতে এই পেপারের অথরগন নির্ঘাত মনে করেন যে, বি এস সি বা বিটেক হচ্ছে সুপ্রিমাম। নানান লেয়ারড হায়ার এডুকেশন সিস্টেমের গোটাটার জন্য একই সমাধানের হদিস দেওয়া মানে আসলে কিছুই না বলা। এবং লক্ষ্য করুন প্রাথমিকে ইংরেজী নেই, তবু 'কোয়ালিফায়েড' সায়েন্স আর্টস ইঞ্জিনিয়ারিং এর জনতার অভাব নেই। খালি একটু গড়ে পিঠে নিতে হবে। সেরা ট্যালেন্ট আকর্ষণ করতে হবে, ইন্ডাস্ট্রীর সাথে যোগাযোগ বাড়াতে হবে, এইসব দাবী কিন্তু তাও নলেজ বেসড ইন্ডাস্ট্রী ফ্লারিশ করবে কি করবে না সেই নিয়ে সংশয় থাকছে। এ তো অদ্ভুত!
এই হাইটেক রিসার্চের সাথে স্মল স্কেল শ্রমনিবিড় শিল্পের যোগাযোগ থাকবে কি করে? অর্থাৎ, even if hi-tech industry and Haldia were to take-off, how would that ensure that the resulting benefits spread widely, in terms of employment creation and wage growth for semi-skilled and unskilled workers throughout the state? সঙ্গত প্রশ্ন, তাই না! এবং উত্তর হ'ল, There is a big market potential for West Bengal small-scale units in the supply of cheap toys, stereos, watches and household implements to the rest of India. This is what China supplies to the rest of the world, and has formed the basis of their phenomenal industrial success in the past two decades. One can add to the list of high potential consumer products the following as well: garments, leather, food processing, spare parts and metal-working, industries all of which have had a long tradition in West Bengal। মানে রিসার্চ ল্যাবে খুব সস্তার এমন অটোমেশন টেকনোলজি তৈরী হবে যা কিনা ইমপ্লিমেন্ট করে প্রচুর লোক কাজ করবে, টেকনোলজি হবে খুব সস্তা, শ্রমনিবিড় ঘড়ি এবং খেলনাপাতিতে আমরা ক্রমে চীনকে ছাড়িয়ে যাব! উৎপাদন বাড়ছে, টেকনোলজি বা অটোমেশনও রয়েছে আবার শ্রমনিবিড়ও এটা যাস্ট কি করে সম্ভব? এই নিদান কি ভাবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে খাটবে? হাওড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ফ্যাক্ট হচ্ছে ২০০০ সালের পর থেকেই কারখানা গুলি ধুঁকতে শুরু করেছে, এবং এখন তো অস্তিত্ব বিলোপের পথে। কারণ ঐ প্রোডাক্টিভিটি কম। বাইরে একই জিনিস অনেক লার্জ স্কেলে অনেক কম সময়ে তৈরী হয়। সাইকেল বা খেলনা শিল্পে হাইটেক রিসার্চের ফল মানে ফাইবার গ্লাসের সাইকেল, হাওয়া ভরতে হয় না এমন টায়ার, সস্তার থ্রীডি প্রিন্টারে বায়োডিগ্রেডেবল খেলনা তৈরী, বিড়ির সুতো বাঁধার কল, এইসব নিশ্চয়ই? শ্রমনিবিড়তা পাওয়া যাবে তো তাতে? চীন বা বাংলাদেশের শ্রমনিবিড়তা কি ব্যবহৃত টেকনোলজির সাথে ব্যাস্তানুপাতিক নয়? আর একটু জটিল যন্ত্রাংশ তৈরী করার প্রকল্পে বেশী শ্রমনিবিড়তা থাকবে না এটা তো এক্সপেক্টেড। সেইসব ইন্ডাস্ট্রীর বিকশিত হওয়ার ফরমান তাহলে কি? স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রীর শ্রমিকদের লেখাপড়ার যোগ্যতামান বেশী থাকার দরকার নেই যেহেতু, এবং যেহেতু পঃবঃ তে ক্ষুদ্রশিল্পের ব্যাপক প্রসারণ কাম্য, এই লজিক্যাল প্রেমিস ঠিক থাকলে খুব বেশী উচ্চশিক্ষার বিস্তার থাকারও দরকার নেই বোধহয়। এটা আবার কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে গেল না।
গোলমালটা কি বি এস সি বিটেক কে হায়ার এডুকেশনের সুপ্রিমাম ধরার ফলে হল না?
আর পড়ি নি। জানিয়ে রাখি দিল্লী পাবলিক স্কুল কলকাতায় বোধহয় ব্রাঞ্চ খুলেছে। ২০০৬ নাগাদ দেখেছি বলে মনে পড়ছে। আর নাগাড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অবশ্য ১৯৯৮ থেকেই খোলা হয়েছে, সবাই জানে। কিন্তু সরকার বা মেধাবীরা ঠিক কি নিত্যনতুন রিসার্চ করলে সাইকেল ও বিড়ি শিল্পে জোয়ার আসবে সেটা বোধহয় এখনো ভেবে উঠতে পারে নি।
 Sibu | 84.125.59.177 | ০১ আগস্ট ২০১৩ ০৩:০৭525818
Sibu | 84.125.59.177 | ০১ আগস্ট ২০১৩ ০৩:০৭525818- ঐ পেপার থেকেই (হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে)ঃ
One way out seems to be to attract one mega-firm, which provides a hub for the industry, as Microsoft has done for Seattle.
কেমন সিঙ্গুর মনে করিয়ে দিল।
 aka | 76.168.177.5 | ০১ আগস্ট ২০১৩ ০৩:২৭525819
aka | 76.168.177.5 | ০১ আগস্ট ২০১৩ ০৩:২৭525819- এই পেপারটা খসড়ার সময়েও দেখেছি। খাপছা খাপছা পছন্দ মতন কোট করা।
The effects of poor infrastructure are much more palpable. A recent study puts West Bengal 14th among
Indian states in 1997-98 in terms of an index of infrastructure, as compared with 4th position in 1971-72.2
The index comprises (a) roads, railways, ports, (b) irrigation, (c) electricity, (d) telephone, (e) loan-deposit ratios of banks and (d) tax collection of the state government. In terms of each of these individual items,
West Bengal has fallen below the national average whereas in 1964-65 it either came first or second.
These facts therefore suggest infrastructure to be a key factor explaining the decline of West Bengal’s industrial performance relative to the rest of the country
ইনফ্রাস্ট্রাকচারে উন্নতি না হলে কিসুই হবার নয়।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Shamik Roychowdhury, upal mukhopadhyay, যোষিতা)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, অরিন, অরিন)
(লিখছেন... Subhas, b, Amit)
(লিখছেন... যোষিতা, Muhammad Sadequzzaman Sharif, যোষিতা)
(লিখছেন... হীরেন সিংহরায়)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... অরিন, অরিন, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, ছোট মুখে , সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... কই কই, উঃ বড্ড লেগেছে , কই কই)
(লিখছেন... kk, দীপ, dc)
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : [email protected] ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত