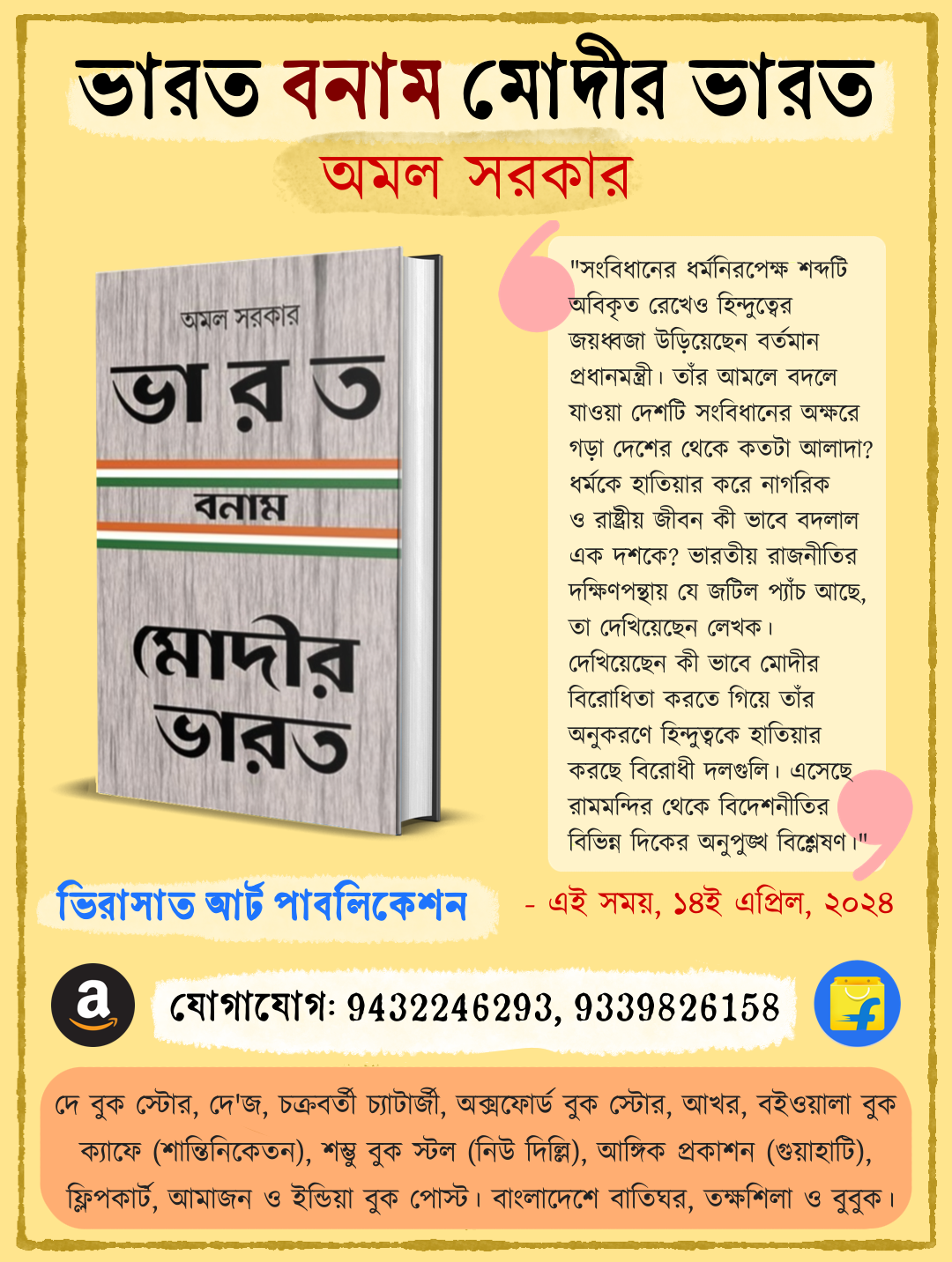- হরিদাস পাল স্মৃতিচারণ স্মৃতিকথা

-
মহম্মদগঞ্জ
Sukdeb Chatterjee লেখকের গ্রাহক হোন
স্মৃতিচারণ | স্মৃতিকথা | ০৩ জুলাই ২০২৪ | ৮১ বার পঠিত | রেটিং ৫ (২ জন) - মহম্মদগঞ্জ
শুকদেব চট্টোপাধ্যায়
স্টেশনের নাম মহম্মদগঞ্জ। প্রথম যেদিন ট্রেন থেকে নেমে ঐ স্টেশনে পা রাখি, ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। আলো আঁধারে আকাশের গায়ে কিছু আঁকা বাঁকা রেখা চোখে পড়েছিল। আলো ফোটার সাথে সাথে সেগুলো এক একটা ছোট, বড়, মাঝারি, পাহাড়ের রূপ নিল। এর আগে পাহাড় দেখা দূরে থাক কোনদিন সামনে থেকে টিলাও দেখিনি। অবাক বিস্ময়ে ঘন জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ের সারির দিকে অনেকক্ষণ চেয়েছিলাম। জীবনে অনেক পাহাড়ে, জঙ্গলে ঘুরেছি। সেইসব জায়গার অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা দু চোখ ভরে উপভোগ করেছি। কিন্তু শিশুকালের সেই প্রথম পাহাড় দেখার অনুভূতি কোন কিছুর সাথেই তুলনীয় নয়।
মহম্মদগঞ্জ। পালামৌ জেলার একটা ছোট্ট গ্রাম। গ্রামের নামেই স্টেশনের নাম। রেল লাইনের একদিকে গ্রাম আর অন্য দিকে জঙ্গল আর পাহাড়। স্টেশনের পাশেই রেল কমর্চারীদের কোয়ার্টার। তার পিছনদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল গ্রামের ঘরবাড়ি। অধিকাংশই মাটির। গ্রামের শেষে বয়ে চলেছে কোয়েল নদী। দূরের পাহাড় থেকে নেমে আসা দুটি ঝর্ণা গ্রামের দুপাশ দিয়ে বয়ে কোয়েলে গিয়ে মিশেছে। রেল লাইন পার হয়ে কাছের পাহাড়টার গা বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠলে ঝর্ণা আর নদী দিয়ে ঘেরা গ্রামের পুরোটাই দেখা যেত। সে এক অপরূপ দৃশ্য। বিশেষত কোয়েলের ওপারে রোটাস পাহাড়ের কোলে যখন সূর্য ঢলে পড়ে তখন গোধূলির আলোয় যে মোহময় পরিমণ্ডল তৈরি হয় তা যেন কোন চিত্রকরের সৃষ্টির এক জীবন্ত রূপ।
পালামৌ জেলা তখন বিহারের ছোটানাগপুর কমিশনারির মধ্যে ছিল। গুমো থেকে একটা লাইন বরবাডি, কেচকি, ডাল্টনগঞ্জ হয়ে সোননগরএ এসে গ্র্যান্ড কর্ড লাইনে মিশেছে। এর পুরোটাই পালামৌ। তখন, অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালে দিন রাত মিলিয়ে দু জোড়া প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছিল। একটি যাতায়াত করত ডেহরি-অন-সোন থেকে বরবাডি, সংক্ষেপে বলা হত বি ডি। আর একটি গুমো থেকে ডেহরি-অন-সোন, সংক্ষেপে জি ডি। আর মাঝে সাঝে চলত দু একটা মালগাড়ি। রাস্তা ঘাট সবই ছিল লাল মাটির কাঁচা পথ। কেবলমাত্র মূল সড়কটি ছিল কিছুটা চওড়া আর বড় বড় পাথরের টুকরো বসানো। জঙ্গলের কাঠ আর পাথর নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু লরি ছাড়া অন্য কোন গাড়ি সচরাচর চোখে পড়ত না। যান বাহন চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা ঘাট প্রায় ছিল না বললেই চলে। মুদি মশলার দু একটা দোকান থাকলেও আনাজপাতির কোন বাজার ছিল না। রবিবার দিন হাট বসত। হাটে কাঁচা আনাজ ছাড়াও মিষ্টি, ভাজাভুজি, গৃহস্থালির টুকি টাকি জিনিসপত্র পাওয়া যেত। হাট থেকে সাতদিনের রসদ সংগ্রহ করতে হত। শীতকালে সমস্যা ছিল না কিন্তু গরমকালে নষ্ট হয়ে যেত অনেক আনাজ। খুব প্রয়োজন হলে ক্ষেতে গিয়ে চাষির থেকে শাক সবজি যোগাড় করতে হত। হাটবারে চাষিরা আসত বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। আমাদের কোয়ার্টারের সামনে দিয়েও অনেক দেহাতি স্ত্রী পুরুষ মাথায় ঝুড়ি নিয়ে হাটে যেত। কি নিয়ে যাচ্ছে জানার জন্য ‘কৌচি হই হো’ জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিত –আলু, লৌকি, পেকচি ইত্যাদি। প্রয়োজনমত মাঝে মাঝে কেনা হত।
বষার্কালে দু-এক মাস ছাড়া মাছ চোখেও দেখা যেত না। পাঁঠার মাংস কদিচ কখনো জুটত। মুরগির মাংস বাড়িতে ঢুকবে না। ফলে সারা বছর আমিষ বলতে কেবল ডিম। এক আনা জোড়া। হাফ বয়েল, ফুল বয়েল, কালিয়া, কোন না কোন রূপে প্রায় প্রতিদিনই পাতে ডিম পেতাম। অধিক ব্যবহারের ফলে ডিমে কোন আকর্ষণ তো ছিলই না বরং না পেলে খুশি হতাম। দুধ আর ঘি খুব ভাল পাওয়া যেত। সারাদিনের খাওয়া দাওয়ায় দুগ্ধজাত সামগ্রী অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকত।
গ্রামে কোন ডাক্তার ছিল না। ওষুধ দেওয়ারই যখন লোক নেই তখন ওষুধের দোকান থাকারও প্রশ্ন নেই। অনেকগুলো স্টেশন পার হয়ে বরবাডিতে রেলের ডাক্তার থাকতেন। পনের কুড়িটা স্টেশনের রেলের সব লোকের চিকিৎসার ভার একা তাঁর ওপর। ফলে রুগী দেখার জন্য কল দিলে সেদিন তো নয়ই অনেক সময় পরের দিনও ডাক্তারের দেখা পাওয়া যেত না। রুগীর ঈশ্বর ভরসা।
মার একটা হোমিওপ্যাথির বাক্স ছিল। তার থেকে দরকার হলে ফেরাম ফস, কেলি ফস, নাক্স ইত্যাদি আমাদের ওপর প্রয়োগ করতেন। তাতে উপকার হোক বা না হোক উভয়েরই কিঞ্চিৎ মানসিক শান্তি হত। অবস্থা খুব বেগতিক হলে রুগিকে ট্রেনে চাপিয়ে ডাল্টনগঞ্জ নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাতে হত।
একদিন দুপুর বেলা মা হঠাৎ যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। জিজ্ঞেস করে জানলাম যে হাতে কিছু কামড়েছে। মার খুব সহ্যশক্তি ছিল। স্টেশন থেকে বাবা ছুটে এলেন, সঙ্গে আরো লোকজন। উনুন পরিষ্কার করার সময় মা কামড় খেয়েছেন। অনেক খোঁজার পর জীবটির সন্ধান পাওয়া গেল। পাতা উনুনের ভেতরে একটা প্রমাণ সাইজের কাঁকড়া বিছে। পাহাড়ি কাঁকড়া বিছের বিষ সাংঘাতিক। যন্ত্রণার কারণ তো বোঝা গেল, এবার উপশমের কি হবে ? গ্রামে ডাক্তার বা ওষুধ কোনটাই তো নেই।
ওখানে স্টেশন মাস্টারকে লোকে বলত ‘বড়া বাবু’। ওই সব অঞ্চলে স্টেশন মাস্টারকে লোকে বেশ খাতির করে। তার ওপর বাবার ব্যবহার ছিল খুব মধুর। গ্রামের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয় মানুষ। এহেন একজনের বিপদে চারিদিকে শোরগোল পড়ে গেল। ডাক্তার যেখানে নেই সেখানে মানুষের হাতুড়ে অথবা ঝাড়ফুঁকের ওপরেই নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোন গতি নেই। অনেকেই বলল কালী সিং কে খবর দিতে, ওর এ ব্যাপারে নাম ডাক আছে। ঐ অঞ্চলে কিছু মাঝারি ও ছোট জমিদার ছিল। বিরাট বিত্তবান না হলেও গ্রামের আর পাঁচটা মানুষের থেকে এদের অবস্থা ছিল অনেক ভাল। এরা মূলত ছিল রাজপুত সম্প্রদায়ের। ফলে বর্ণগত সুবিধাও এরা ভোগ করত। সমাজে এদের আসন ছিল কিঞ্চিৎ ভয় মিশ্রিত সম্মানের। কালী সিং ছিল এমনি এক ছোট জমিদার। লোকে তাঁর কাছে আসে, তিনি সাধারণত এ ধরণের কলে কারো বাড়িতে যান না। ছোট হলেও জমিদারের তো, একটা ইজ্জত আছে। কিন্তু বড়া বাবুর স্ত্রীকে বিছে কামড়েছে শুনে কাল বিলম্ব না করে চলে এলেন। মার যন্ত্রণা তখন চরমে উঠেছে।
কালী সিং ওনার চেলাদের সামনের মাঠ থেকে কিছু ‘চকওয়র’ তুলে আনতে বললেন। চকওয়র একপ্রকার ছোট ছোট গাছ যা ওখানকার মাঠে ঘাটে প্রচুর পাওয়া যেত। উনি নিজেও সঙ্গে করে কিছু ঘাস পাতা এনেছিলেন। সব কিছু আসার পর ওনার নিদের্শমত সেগুলো বেটে মলম তৈরি করা হল। তার পর মুখে বিড় বিড় করতে করতে সেই মলম তিনি মার হাতে মালিশ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ মালিশ করার পর যন্ত্রণার তীব্রতা কিছুটা কমল। কয়েক ঘণ্টা কাটার পর কষ্ট অনেকটাই কমে গেল। যে গাছ গাছড়ার সাহায্যে কালী সিং এর মত একজন প্রায় অশিক্ষিত মানুষ চমক দেখাল, তার ওপর বিজ্ঞান সম্মত ভাবে গবেষণা হলে অনেক মানুষই উপকৃত হতে পারে।
স্কুল
গ্রামের একমাত্র স্কুলের নাম ছিল ‘মহম্মদগঞ্জ মিডল স্কুল’। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়ান হত। এরপর এগোতে হলে অন্যত্র যেতে হবে। আমার জীবনের প্রথম স্কুল। বাবার সাথে প্রধান শিক্ষক রাম সেবক সিং এর ঘরে গেলাম। ওনার নির্দেশে আমাকে সরাসরি ক্লাস ফোরে ভর্তি করে নেওয়া হল। প্রথম দিন ক্লাশ টিচার কামেশ্বর সিং হিন্দিতে দু একটা কথা জিজ্ঞেস করলেন। তখনও হিন্দিতে খুব একটা সড়গড় হইনি। আমার মত করে উত্তর দিলাম। এরপর তিনি ইংরাজিতে জিজ্ঞেস করলেন- What is your name?
আমি নাম বললাম। ক্লাসের সমস্ত ছাত্র ছাত্রী এমনকি মাস্টার মশাই নিজেও হতবম্ব। ক্লাস ফোরের ছেলে একটা সম্পূর্ণ বাক্য ইংরাজিতে কি করে বলল! বাবার নামটাও ইংরাজিতে বলায় বিস্ময় আরো বাড়ল। আমার ইংরাজিতে অগাধ জ্ঞানের কথা সারা স্কুলে ছড়িয়ে গেল। একে বড়বাবুর ছেলে তায় আবার ইংরাজি জানা বলে অন্য ছাত্রদের থেকে আমাকে একটু পৃথক ভাবে দেখা হত। এর কিছুদিন আগের কথা। আমি তখন তালতলায় আমার মামার বাড়িতে। দাদু একদিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে, তাঁর সাহেব বন্ধু, ক্যালকাটা বয়েজ স্কুলের হেডমাস্টারের কাছে গেলেন। উদ্দেশ্য ছিল আমাকে পরবর্তীকালে ঐ স্কুলে ভর্তি করা। দাদু, নাতি সম্পর্কে প্রশংসা সূচক অনেক ভাল ভাল কথা ভদ্রলোককে বললেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অগাধ বিস্ময়ে সাহেবের সাথে দাদুর কথোপকথন শুনছিলাম। একমাত্র ‘ইন্টালিজেন্ট’ ছাড়া আর কোন কথার মানেই বোধগম্য হয়নি। এরপর ভদ্রলোক পরম স্নেহে বন্ধুর নাতিকে কাছে টেনে নিলেন। মাথায় গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে কিছু জিজ্ঞেস করলেন। কামেশ্বর সিং এর সহজ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যে শিশুটি অজ গ্রামের এক প্রাইমারি স্কুলের সকলকে হতবাক করেছে, সে সাহেবের কথা কিছুই বুঝতে না পেরে বোকার মত দাঁড়িয়ে ছিল। দাদুই সে যাত্রায় নাতিকে ঐ সংকট থেকে উদ্ধার করলেন।
আমাদের স্কুলটি ছিল কো-এডুকেশন স্কুল। এলাকার একমাত্র স্কুল হওয়ার ফলে অবস্থাপন্ন ও গরিব উভয় ঘরের ছাত্র ছাত্রীরাই এখানে পড়তে আসত। দুঃস্থ ঘরের ছেলে মেয়েই বেশি ছিল। দারিদ্রের তাড়নায় অনেকেই মাঝপথে স্কুল ছেড়ে দিত। একটা ঘটনার উল্লেখ করলেই এদের পারিবারিক অবস্থার ছবিটা পাওয়া যাবে। একদিন ক্লাশের ফাঁকে হুড়োহুড়ি করতে করতে আমি আমার সহপাঠী রামেশ্বর রামের জামা ধরে টান মারি। অনিচ্ছায় হলেও ঐ টানে রামেশ্বরের জামা খানিকটা ছিঁড়ে যায়। ছেলেটা শান্ত প্রকৃতির ছিল বলে কোন প্রতিবাদ করেনি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে জামার ছেঁড়া অংশটা বারবার দেখছিল। একজন শিক্ষক ঘটনাটা লক্ষ্য করেন। তিনি আমাকে ডেকে বলেন যে রামেশ্বরদের মত গরিবের ঘরে ঐ একটা বা দুটো জামাই সম্বল। আমি ঘটনার জন্য খুবই অনুতপ্ত হয়ে রামেশ্বরের কাছে বারে বারে দুঃখ প্রকাশ করি।
ওয়ান আর টু, এই দুটো ক্লাস নিতেন লালা গুরুজি। তিনি একই সঙ্গে স্কুল সংলগ্ন একটা পোস্ট অফিসের দায়িত্বেও ছিলেন। বয়সেও ছিলেন বৃদ্ধ। এতটা ধকল ঐ বয়সে তাঁর পক্ষে সামলানো বেশ কঠিন ছিল। ছাত্রদের জোরে জোরে পড়তে বলে তিনি অকাতরে ঘুমোতেন। ঘুমোতে ঘুমোতে যাতে পড়ে না যান তার জন্য এক পা চেয়ারে তুলে আর এক পা টেবিলে ঠেকা দিয়ে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতেন। পঞ্চম শ্রেণীতে একাধারে শ্রেণী শিক্ষক ও আমার গৃহ শিক্ষক ছিলেন রাম নরেশ সিং। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন। শেখানো আর শেখার মধ্যে যা কিছু ব্যবধান থাকত তা তিনি মুছে ফেলতেন পরীক্ষার আগে প্রশ্ন পত্রগুলো অত্যন্ত যত্ন সহকারে আগাম সমাধান করিয়ে দিয়ে। পরীক্ষার উত্তরপত্র মুল্যায়নের ক্ষেত্রেও কোন রকম কার্পণ্য থাকত না। ফলে যে কয় বছর ওখানে পড়েছি প্রথম স্থানটা আমার বাঁধা ছিল।
স্কুলের শিক্ষাদানের পদ্ধতির মধ্যে মারের একটা বড় ভূমিকা ছিল। শিক্ষকদের মারের এত বৈচিত্র আর ছাত্রদের মার সহ্য করার এত ক্ষমতা আমি আর কোথাও দেখিনি। স্কুলের মাঝখানে খাপরার চাল দিয়ে ঢাকা কিছুটা জায়গায় সভা বা অনুষ্ঠান হত। নাম ছিল ‘গান্ধী মঞ্চ’। ওইখানেই একবার পরীক্ষায় প্রথম হওয়া এবং পরিচ্ছন্নতার জন্য পুরস্কার পেয়েছিলাম। যত সামান্যই হোক না কেন, জীবনের প্রথম ঐ পুরস্কার, আজও আমার কাছে দুর্মূল্য। ঐ স্কুলই ছিল ঘন জঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট গ্রামে একমাত্র আলোর দিশারী।
ছোটু
ছোট্ট ছিল বলে বোধহয় ছোটু নাম রাখা হয়েছিল। প্রথম যেদিন বাবা কোলে করে মাস খানেকের শাবকটিকে বাড়িতে আনলেন, তখন ও কাঁপছে। খয়েরি রং, পায়ে খুর, টানা টানা চোখ—ছাগল নয় এটা বুঝতে পারলেও ওটি যে কি তা তখন বুঝতে পারিনি।
বাবা বললেন — হরিণ, আমাদের বাড়িতে থাকবে।
স্কুলে যাওয়া মাথায় উঠল। সারাদিন ছোটুর পরিচর্যাতেই কাটল। দুধ খাওয়ানটাই সমস্যা। চামচে করে অল্প অল্প করে দিলেও ঠিকমত খেতে পারছে না। বেশিটাই বাইরে পড়ে যাচ্ছে। গ্রামে কিছুই পাওয়া যায় না। ডাল্টনগঞ্জ থেকে ফিডিং বোতল আসার পরে সমস্যা মিটল। দুধ খেয়ে পেট না ভরলে মুখে চুক চুক শব্দ করে আরো চাইত। অল্প সময়ের মধ্যেই ও আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গেল। ছোটুর আমাদের বাড়িতে আসাটাও এক মজার ঘটনা। স্টেশনে ডিউটি করার সময় বাবা এক বুড়ির কোলে হরিণ ছানাটাকে দেখতে পান। ওটি বিক্রি করবে কিনা জানতে চাইলে সে ছানাটাকে বাবাকে দিয়ে অনুরোধ করে ডেহরি- অন- সোনের একটা টিকিট কেটে দিতে। টিকিটের মূল্য কয়েক আনা ছিল। ওটাই আমাদের ছোটুর ক্রয়মূল্য। এরপর আমাদের মাঝে আমাদের মত করে ও বড় হতে লাগল। আমরা যখন জঙ্গলে বেড়াতে যেতাম ছোটুও আমাদের সাথে যেত। আমরা জঙ্গলে গিয়ে কোথাও বসলে ছোটু মনের আনন্দে এ পাহাড় ও পাহাড়ে ঘুরে বেড়াত। সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় ছোটু ছোটু করে ডাকতাম। আমাদের ডাক পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে। কিন্তু যাকে ডাকা সে কোথায়? কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দূর থেকে লাফাতে লাফাতে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াত আর আমাদের সাথে সেও তার বাড়ি ফিরে আসত।
কেবল মানুষ নয় পশুও অভ্যাসের দাস। হরিণ তৃণভোজী, কিন্তু ভাত, রুটি, তরকারি এগুলো খেতে খেতে বড় হওয়ার ফলে ঘাস পাতার থেকে ওগুলোই ওর বেশি পছন্দের ছিল। মা পোস্তর তরকারি বা আচার দিয়ে ভাত মেখে খাওয়াতেন আর ছোটু হাঁটু মুড়ে বসে তৃপ্তি করে তা খেত। অপরিচিত জনের কাছে এ এক দুলর্ভ দৃশ্য। কেবল একটা জিনিসে তার ঘোরতর আপত্তি ছিল। আমার মা খাওয়ানোর পর জল দিয়ে ছোটুর এঁটো মুখ ধোয়াতেন। এটা সে একেবারেই পছন্দ করত না। রাতে মশারির মধ্যে আমাদের পাশে শুত। নিচে নামার দরকার হলে মুখে আওয়াজ করত। মশারির একটা পাশ একটু তুলে ধরতাম, ও সাবধানে নেমে যেত। অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে আমাদের কারো গায়ে পা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে মুড়ে সরিয়ে নিত। বাবা আর আমি যখন অফিস আর স্কুলে বেরতাম তখন ছোটু কোয়ার্টারের বাইরে বাগানে বেরিয়ে এসে আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য ছটফট করত। আবার যখন আমরা ফিরে আসতাম তখন ওর কি আনন্দ। দৌড়ে এসে গায়ে গা ঘসে আহ্লাদ প্রকাশ করত। স্নেহ, ভালবাসা, মায়া, মমতা, এগুলোর ক্ষেত্রে বোধহয় মানুষ এবং মনুষ্যেতর জীবে বিশেষ তফাৎ নেই। হরিণ গৃহপালিত পশু নয়। তবু যে জঙ্গলে তার জন্ম, যা তার স্বাভাবিক আশ্রয়স্থল, সেখানে সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত অবস্থায় বিচরণের সুযোগ পেয়েও কোনদিন পালিয়ে যায়নি। দিনের শেষে গুটি গুটি পায়ে ফিরে এসেছে চার দেওয়ালের মাঝে কয়েকজন ভাল লাগা মানুষের সান্নিধ্যে। কোন বগলস অথবা শিকলের প্রয়োজন হয়নি। কারণ, সে তখন ভালবাসার অনেক শক্ত বাঁধনে আটকা পড়েছে। সে তখন আর বন্য নয়। আমাদের বাড়ির একটি শিশু। আমাদের বাড়িই তার মাতৃক্রোড়, সে সেখানেই সুন্দর।
ঋতু
পালামৌতে শীত এবং গ্রীষ্ম দুটোই খুব তীব্র ছিল। তুলনায় বর্ষা কম হত। শীতে গাছপালার পাতা ঝরে গিয়ে পাহাড় জঙ্গলের সবুজ ভাব অনেকটাই ফিকে হয়ে যেত। এরপর গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহে মনে হত যেন সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। পাহাড় জঙ্গল রুক্ষ ধূসর বর্ণ ধারণ করত। এই সময় গভীর জঙ্গলে জলের অভাবে বন্য প্রাণীরা জল খেতে নদীর ধারে আসত। গরমের সন্ধ্যায় অথবা রাতে একটু সজাগ থাকলে অনেক জীব জন্তু দেখতে পাওয়া যেত। নেকড়ে( স্থানীয় ভাষায় ‘লকরা’), সজারু, বুনো শুয়োর, সম্বর, ছোট হরিণ(কোটারি), খরগোশ, বন মুরগী, বাঁদর প্রভৃতি জন্তু প্রচুর ছিল। কখন সখন চিতার দেখাও পাওয়া যেত। নেকড়ের দল মাঝে সাঝে গ্রামের গোয়ালে এসে হানা দিত। নেকড়ে অত্যন্ত হিংস্র আর চতুর। ভয়ে গরু মোষ গুলো দড়ি ছিঁড়ে পালালে তাদের এমনভাবে তাড়া করত যে তারা যেন পাহাড়ের দিকে দৌড়োয়। কারণ, গ্রামে বসে শিকার ধরলে লোকজন জেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর তাতে বেঘোরে প্রাণটাও যেতে পারে। কিন্তু পাহাড়ের দিকে একবার নিয়ে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত। এইরকমই কোন অভিযানের সময় মালগাড়িতে ধাক্কা খেয়ে একবার একটা নেকড়ে মারা গিয়েছিল। সকালবেলা আমরা নেকড়েটাকে দেখতে গিয়েছিলাম। ঐ প্রথম কোন হিংস্র জন্তুকে এত কাছ থেকে দেখি (যদিও মৃত)।
বিদ্যুৎ না থাকার জন্য গরমকালে রাতে মা ছাড়া আমরা বাকিরা কোয়ার্টার সংলগ্ন বাগানে খাটিয়া পেতে শুতাম। আবহাওয়া শুকনো বলে খোলা আকাশের নিচে শুলে শরীর খারাপ হত না। ঘামও প্রায় হত না বললেই চলে। রাতে তাপমাত্রা অনেক কমে যেত আর ফুরফুরে হাওয়া চলত বলে পাখার অভাব বুঝতে পারতাম না। চারিদিক ঘন অন্ধকার। ওপরে খোলা আকাশে তারা মিট মিট করছে। নিস্তব্ধতা ভেঙে গভীর জঙ্গল থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে নানা রকম চেনা-অচেনা জন্তু জানোয়ারের ডাক। দূরের পাহাড়ে দাবানল আলোর মালার মত লাগছে। শুয়ে শুয়ে সেই মায়াবী জগত প্রত্যক্ষ করতে করতে কখন যেন দু চোখের পাতা এক হয়ে যেত।
সকালবেলা ‘তাড় চড়ো’ ডাকে ঘুম ভাঙত। তালের রস পাড়তে তালগাছে ওঠার আগে লোকটি ঐ হাঁকটা দিত। মাঝে মাঝে আমাকে তালের রস দিয়ে যেত। তবে ঐ রস রোদের তাপ বাড়ার আগে খেয়ে না নিলে মেতে গিয়ে তাড়ি হয়ে যেত। তখন এমন বোটকা গন্ধ বেরত যে আর খাওয়া যেত না। তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে সকাল এগারটার পর থেকে আগুনের হল্কা বইতে শুরু হত। ঘরের মধ্যে বসে ‘লু’ চলার সোঁ সোঁ আওয়াজ শুনতে পেতাম। ‘লু’এর প্রতিষেধক হিসাবে আমপোড়া, পুদিনা ইত্যাদির সরবত খেতাম। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে প্রখর রৌদ্রতাপের ফলে দূরের জিনিসগুলো কাঁপছে মনে হত। কাজের তাগিদে যারা রাস্তায় ঘুরত তাদের নাক, কান, মুখ সব গামছা দিয়ে ঢাকা থাকত। ‘লু’ একবার লেগে গেলে নিস্তার নেই। স্থানীয় মানুষেরাও ঐ সময় অত্যন্ত সাবধানে চলাফেরা করত। গ্রীষ্মের এমন রুদ্র রূপ আর কোথাও দেখিনি।
আমাদের কোয়ার্টার আর রেলের প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে বেশ খানিকটা ফাঁকা জমি ছিল। মাঝে মাঝে ওখানে যাযাবর সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ তাঁবু খাটিয়ে কিছুদিন করে থাকত। ওরা লোহার ছুরি কাঁচিতে শান দিত এবং টুকটাক কিছু জিনিস বিক্রি করে অতি কষ্টে অন্নের সংস্থান করত। মা মাঝে মাঝে ওদের ডেকে খাবার দাবার দিতেন। একবার গরমকালে ওইরকম দু একটা পরিবার তাঁবু খাটিয়ে কিছুদিন ছিল। গরমের সময় আমি প্রায় প্রতিদিনই খাওয়ার পর দুপুরবেলা জানলার ফাঁক দিয়ে প্রকৃতির ভয়ংকর রূপ দেখতাম। সব কিছু যেন ভস্ম হয়ে যাবে।
ওইরকমই একদিন, রাস্তায় তখন মানুষ নেই বললেই চলে, চোখ গেল ঐ তাঁবু গুলোর দিকে। ‘লু’ এর দাপট বাড়ির ভেতর থেকেই টের পাওয়া যাচ্ছে। তারই মধ্যে একটা দুধের বাচ্চা হামা দিয়ে তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে মাটি পাথর বালি নিয়ে আপন মনে খেলছে। মুখে এক গাল হাসি। কিছু পরে ওর মা এসে ওকে তুলে নিয়ে গেল। ততক্ষণ ‘লু’ এর তাণ্ডবকে হেলায় উপেক্ষা করে শিশুটি খোলা মাঠে খেলা করল। আহার, আচ্ছাদন, সব কিছুর অভাবের মধ্যেও কি অসাধারণ জীবনীশক্তি। এস্কিমোদের যেমন চরম ঠান্ডার সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্মগত ক্ষমতা আছে, এদেরও বিধাতা চরম দারিদ্র আর প্রতিকুল পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করার মনোবল দিয়েই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।
বিকেলের দিকে গরম হাওয়া আর তাপমাত্রা দুটোই কমে আসত। আমরা জঙ্গলে অথবা কোয়েলের দিকে বেড়াতে যেতাম। কোয়েল ওখানে কোন পাহাড়ি নদীর মত ছোট নয়, যথেষ্ট চওড়া। বছরের অধিকাংশ সময় জল প্রায় থাকত না বললেই চলে। সরু ধারায় দু এক জায়গা দিয়ে বইত। পায়ের পাতা হয়ত কোনরকমে ডুববে। মানুষ তো বটেই গরু মোষে টানা গাড়ি গুলোও মালপত্র নিয়ে নিত্য নদী পারাপার করত। বর্ষাকালে হঠাৎ একদিন প্রায় শুকনো ঐ নদী লাল ঘোলাটে জলে ভরে যেত। কাল বিকেলে যে নদীর মাঝখানে ঘুরে বেরিয়েছি আজ তার কাছে যেতেও ভয় লাগবে। নদীতে ‘বাড়’ (বান) আসার সময় প্রতি বছরই কিছু জীবজন্তু এমনকি কখনও কখনও মানুষও মারা যেত। বান আসার পর থেকে প্রায় দু আড়াই মাস কোয়েল নদীতে দুকুল ছাপান জল থাকত। ঐ সময়টাতে কিছু মাছ খেতে পেতাম। কোয়েল নদীতে জল মাপার জন্য একজন সরকারি কমর্চারী ছিলেন। তাঁর নাম ‘দুলু বাবু’। তিনি বাঙালি। দুলুবাবু তাঁর সরকারী নৌকায় আমাদের কোয়েল নদীতে অনেক ঘুরিয়েছেন। একটা ব্যাপার আজও বুঝতে পারিনি। যে নদীতে বছরে ন দশ মাস জল প্রায় থাকে না বললেই চলে সেখানে সারা বছর নদীর জল মাপার জন্য একজন সরকারী কমর্চারীর কি প্রয়োজন!
ঐ অঞ্চলে তখন বিদ্যুৎ আসেনি। সূর্যাস্তের পর রাস্তাঘাট সব অন্ধকার হয়ে যেত। হ্যারিকেন বা লম্ফও বেশিক্ষণ জ্বালাবার ক্ষমতা সকলের ছিল না। তাই সন্ধ্যার পরেই গ্রামটা যেন ঘুমিয়ে পড়ত।
গ্রীষ্মকালে কিছু জীব জন্তু আমাদের নিত্যসঙ্গী ছিল। এরা গৃহপালিত না হলেও গৃহে সর্বদাই ছিল এদের অনাকাঙ্খিত বিচরণ। একটি হল কাঁকড়া বিছে আর একটি সাপ। সাপের দেখা রোজ না মিললেও বিছে পিঁপড়ের মত চারিদিকে ঘুরে বেড়াত। গল্প কথা মনে হলেও, রাতে যখন মাটিতে খেতে বসতাম তখন সকলের পাশে বাড়িতে পরার একপাটি চটি রাখা থাকত শুধু বিছে মারার জন্য। প্রায়ই মেঝেতে, বিছানায়, মশারির চালে, এমনকি জামাকাপড়েও বিছে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। মাঝে মাঝে সাপ বেরত। হাঁক পাড়লেই স্টেশন থেকে খালাশিরা লাঠি নিয়ে দৌড়ে এসে মশা-মাছি মারার মত অবলীলায় ঐ বিষধর সাপ মেরে দিত। ঐরকম একটা পরিবেশে বেঁচে থাকাটাই বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় মার একটি মাত্র ঘটনা ছাড়া আমাদের কাউকে আর কোনদিন এদের দংশন খেতে হয়নি। তবে এসব যায়গায় একবার এলে লালমোহন বাবুর অ্যাডভেঞ্চারের আগ্রহ যে চিরতরে ছুটে যেত তা নিয়ে সংশয় নেই। গ্রীষ্মের দাপটে নদীনালা যখন সব শুকিয়ে গেছে, চাষের জমিতে দেখা দিয়েছে বড় বড় ফাটল, তখন আকাশ কালো হয়ে নামত বর্ষা। ভরে উঠত নদীর দুকুল। ন্যাড়া বা প্রায় শুকিয়ে যাওয়া গাছগুলোতে হত প্রানের সঞ্চার। কচি কচি পাতায় কঙ্কালসার দেহগুলো ঢেকে যেত। পাহাড়ের রুক্ষ ধূসর ভাব কেটে গিয়ে ফিরে আসত শ্যামল সবুজ রূপ। পাহাড়ের নিচে লাল মাটিতে বোনা ছোলাগাছের চারা গুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। চাষের জমি ভরে যেত শাক সবজিতে। বাংলার মত বর্ষা ওখানে অতটা ব্যাপক না হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকৃতির রূপের আমূল পরিবতর্ন ঘটত। ওখানে প্রতিটি ঋতুই শ্রীরূপা। শুধু দেখা আর উপভোগ করার জন্য চাই উপযুক্ত চোখ আর মন।
গরমের মত শীতও ছিল খুব তীব্র। অক্টোবরের মাঝা মাঝি থেকে ঠান্ডা পড়া শুরু হত। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী এই কয় মাস হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা থাকত। শীতই ঐ অঞ্চলে সব থেকে আরামদায়ক সময়, বিশেষত বহিরাগতদের কাছে। বহিরাগত বলতে কোন পযর্টক নয়, আমাদের মত দু একটা পরিবার যারা চাকরি সূত্রে ওখানে বসবাস করছে। থাকা, খাওয়া, যানবাহন, কোন কিছুরই সুব্যবস্থা না থাকায় ঐ মনমোহিনী প্রাকৃতিক পরিবেশ সাধারণ পযর্টকদের কাছে প্রায় অধরাই ছিল। হয়ত সেই কারনেই জঙ্গলের আদি, অকৃত্তিম, ভয়ংকর সুন্দর, অনাঘ্রাত রূপ নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছে। শীতকালে সাপ, বিছে, মশা, মাছির উৎপাত থাকত না বললেই চলে। শাক সবজিও ভালই পাওয়া যেত। ছোট ছোট লাল কুচ ফলে গাছ ভরে থাকায় জঙ্গলের কিছু কিছু জায়গা লাল হয়ে থাকত।
রেল লাইনটা মহম্মদগঞ্জ স্টেশন থেকে মাইল দুয়েক দূরে পাহাড় ফুঁড়ে ডাল্টনগঞ্জের দিকে চলে গেছে। মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে জঙ্গলে ঘেরা অন্ধকার টানেলে ঢুকতাম। বেশ রোমাঞ্চ হত। ওখানে পাহাড় কোয়েলের কোলে গিয়ে মিশেছে। নদীর ধারে পাহাড়ের খাড়াই খুব কম। আর প্রায় পুরোটাই পাথর। ঐ পাথরেতে অনেক জন্তু জানোয়ারের পায়ের ছাপ, এমনকি স্বাভাবিকের থেকে অনেক বড় মানুষের পায়ের ছাপও বেশ কয়েকটা ছিল। ওগুলো নিয়ে ওখানে অনেক গল্প কথা প্রচলিত আছে। শোনা যায় পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসের কিছুটা সময় ঐ অঞ্চলে কাটিয়েছিলেন। পায়ের ছাপগুলো ঐ সময়ের। ওখানেই এক যায়গায় চতুর্ভুজের আকারে বিরাট উঁচু চারটে পাথর ছিল। প্রত্যেকটার মাথায় ছিল সাদা দাগ। ওটা ছিল ভীমের উনুন। তাই ঐ অঞ্চলটার নাম ছিল ‘ভীম চুলহা’। ভীম চুলহাতে শীতকালে কোয়েলের ধারে পাহড়ের গায়ে একটা মেলা বসত। ওখানে অনেক দূরে দূরে এক একটা গ্রাম। ভিমচুলহার নিকটবর্তী গ্রামের নাম কাদল। কাদল, মহম্মদগঞ্জ, ভজনিয়া, এমনকি কোয়েলের ওপারের দূর দূরান্তের গ্রামগুলো থেকে মেলার দিন সকাল থেকেই বহু মানুষ বেচা কেনার জন্য জড় হত। বাচ্চাদের খেলনা, খাবার দাবার, হাতা-খুন্তির মত রান্নার সরঞ্জাম—এমন আরো কত কিছুর পসরা সাজিয়ে দোকানিরা পাহাড়ের গায়ে বসত। ঐ মেলায় দু পয়সার ভেঁপু বা ডুগডুগি কিনে যে নির্মল আনন্দ পেয়েছি আজ বহু মূল্যবান জিনিসেও তা পাই না। আসলে সেই গ্রাম্য শিশু মনটাই তো কবে হারিয়ে গেছে। কনকনে ঠান্ডায় রৌদ্রস্নাত দিনে পাহাড় আর নদীর সঙ্গমস্থলে নৈসর্গিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত দরিদ্র গ্রামবাসীদের মেলবন্ধনের এই মেলা ছিল কৃত্তিম নামী দামী মেলার থেকে অনেক বেশি সুন্দর।
কিছু মানুষ যাদের ভুলতে পারিনি।
মহম্মদগঞ্জে আমার প্রথম যার সাথে আলাপ হয় তার নাম ‘বুধন’। বুধন রাম। বেকার ছেলে। স্থানীয় অধিকাংশ মানুষের মতই বুধনও দরিদ্র ঘরের সন্তান। তবে ওর দাদা রেলে কাজ করত বলে অন্য অনেকের থেকে ওদের অভাব কিছুটা হলেও কম ছিল। নিজেই কোয়ার্টারে এসে আলাপ করেছিল। আমি হিন্দি জানি না আর ও বাংলা জানে না। অথচ ভাবের আদান প্রদানে ভাষা কোন সমস্যা হয়নি। প্রথম দিনই ওর সাথে পাহাড়ে নুড়ি কুড়োতে যাই। কিছুদিন বাদে বাবা আমাকে হিন্দি শেখাবার দায়িত্ব ওকে দিলেন। অত্যন্ত গোবেচারা ছেলে। বয়সে আমার থেকে অনেকটা বড় হলেও ওকে আমি কোনদিন আমার বন্ধু ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারিনি। ফলে আমার শিক্ষক হওয়াটা ওর কাছে ছিল এক চরম বিড়ম্বনা। গম্ভীর হয়ে যতই পড়াবার চেষ্টা করুক না কেন, আমার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ‘মাইজি দেখিয়ে না’ বলে মার কাছে মাঝে মাঝেই নালিশ করত। এতদসত্ত্বেও আমার হিন্দি অক্ষর জ্ঞান আর হিন্দিতে কথা বলার ক্ষমতা বুধনের দৌলতেই হয়েছিল। বাবা-মা বাদ দিলে বুধনই আমার জীবনে প্রথম শিক্ষক। বুধনকে বাবা রেলের খালাসিতে বহাল করেন। পরে নিজের চেষ্টায় ও কেবিন ম্যান হয়েছিল।
মহম্মদগঞ্জে যাওয়ার কিছুদিন বাদে একদিন সকালে লাঠি হাতে এক বৃদ্ধ আমাদের কোয়ার্টারে এলেন।
---শুনলাম তোমরা বাঙালি, তাই আলাপ করতে এলাম বৌমা।
বাংলা কথা শুনতে পেয়ে মা খুব খুশি হয়ে ভদ্রলোককে আপনজনের মত আন্তরিক ভাবে আপ্যায়ন করলেন। আলাপচারিতায় জানা গেল ভদ্রলোকের নাম প্রবোধ কুমার গাঙ্গুলী। বয়স আশীর থেকে কিছুটা বেশিই হবে। যৌবন কাল থেকেই ঐ অঞ্চলে আছেন। একাই থাকেন। স্থানীয় এক শিক্ষক ওনার দেখাশুনো করেন। অবশ্য দেখাশুনো বলতে তার বাড়িতে থাকেন আর খাওয়া দাওয়া করেন। এমনিতে ঐ বয়সেও তিনি যথেষ্ট স্বাবলম্বী। শিক্ষক আর তাঁর পরিবার গাঙ্গুলীবাবুকে নিজের বাড়ির লোকে মতই যত্ন করতেন। উনি নিজেই আমাকে বাংলা পড়াবার দায়িত্ব নিলেন। তাতে ওনার কিছুটা সময় কাটত আর আমার মাও পিতৃতুল্য বৃদ্ধকে সাধ্যমত সেবা যত্ন করে তৃপ্ত হতেন। বহুদিন এভাবে চলার পরেও কিন্তু দুজনের কারো মধ্যে কোনরকম বিরক্তিভাব লক্ষ করিনি। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ ছাত্রটিকে বহুদিন সকালে বেশ কিছুটা বিরক্তিকর সময় কাটাতে হয়েছে। লোকমুখে শুনেছি, একসময় গাঙ্গুলীবাবু কাঠ, পাথর ইত্যাদির ব্যবসা করে প্রচুর রোজগার করেছিলেন। তখন সপরিবারেই থাকতেন। পরে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলেই জীবিত থাকা সত্ত্বেও কেন যে একা ঐ বনবাসে ছিলেন তার কোন কারণ জানতে পারিনি। শুনেছিলাম কোন এক সময় পরিবারের লোকজন তাঁকে কোলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য মহম্মদগঞ্জে এলে তিনি পরের ট্রেনেই ওদের বিদায় করে দিয়েছিলেন। এলাকার সকলেই ওনাকে ভালবাসত এবং শ্রদ্ধা করত। শীতকালে দুপুরবেলাটা স্টেশনে বসে বাবাদের সাথে গল্প গুজব করে কাটাতেন। একটা চেয়ার নিয়ে রোদ্দুরে বসে ছুরি দিয়ে পাকা টম্যাটোর ডিসেকশন করে নুন ছিটিয়ে খেতেন। বাবাকে, আর আমি থাকলে আমাকেও, দু এক টুকরো দিতেন। যত লোক ওখান দিয়ে যেত সকলেই ওনাকে ‘গোড় লাগি বাবা’ বলে শ্রদ্ধা জানাত। উত্তরে উনি ‘খুশ রহ’ অথবা ‘জিতে রহ’ বলতেন। গ্রামের মানুষের কাছে ঐ বাঙালি বৃদ্ধ ছিলেন অভিভাবকের মত। নানা সমস্যায় পড়ে লোকে ওনার কাছে আসত পরামর্শ নিতে। গ্রামের মানুষের শ্রদ্ধা আর ভালবাসাই বৃদ্ধকে পরিবার পরিজন ছেড়ে এই জঙ্গলে একা থাকার সাহস আর প্রেরনা জুগিয়েছিল। ওই অদ্ধর্শিক্ষিত, অশিক্ষিত, হতদরিদ্র মানুষগুলোই ছিল তাঁর পরিবার।
আমাদের বাড়ির কাজকর্ম করত নন্দু রাম। লম্বা, স্বাস্থবান বাইশ-তেইশ বছরের যুবক। কোয়ার্টারের কাছেই থাকত। বাড়ির কাজের মধ্যে সব থেকে পরিশ্রমের কাজ ছিল জল ভরা। বিশেষ করে গরমকালে। আর মার জন্য আমাদের জলের খরচ একটু বেশি হত। গ্রীষ্মকালে গ্রামের হাতে গোনা যে কটা ইঁদারায় জল থাকত, তার মধ্যে একটা ছিল রেলের জমিতে আমাদের কোয়ার্টারের ঠিক সামনে। বেশ বড় ইঁদারা । সকালে ও বিকেলে নন্দু আমাদের দুটো বড় চৌবাচ্ছায় জল ভরে দিত। ফলে চারিদিকে যখন জলের অভাব তখনও আমরা যথেচ্ছ ভাবে জল খরচ করেছি। আসলে সুখ, স্বাচ্ছন্দ, দুঃখ, কষ্ট, অনেকটাই নির্ভর করে সমাজে আমাদের অবস্থানটা কোন স্তরে তার ওপর। অনেকদিন কাজ করার ফলে ওর সাথে আমাদের একটা ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বাবা ওকেও রেলে অস্থায়ী খালাশির কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ওর একটা সমস্যা ছিল। ওর মনটা ছিল যাযাবর প্রকৃতির। কয়েক মাস বাদে বাদেই নন্দু নিখোঁজ। রেলের চাকরি, আত্মীয় পরিজন , কোন কিছুই তাকে আটকে রাখতে পারত না। কিছুদিন বাদে কখনও খবর পাওয়া যেত যে নন্দুকে গুমো বা লাতেহারে দেখা গেছে। শখ মিটে গেলে কয়েক মাস বাদে ফিরে এসে আসামীর মত মাথা নিচু করে বাবার সামনে দাঁড়াত। এমন ঘটনা আর কখনও হবে না এরকম বহু প্রতিশ্রুতি আর শপথের মাধ্যমে বাবাকে বাধ্য করত ওকে মার্জনা করতে। কিছুকাল কাটলেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হত। তবে ওর গন্তব্যস্থল কখনও এক থাকত না। বাবাকে সাহস করে কিছু না বললেও আমাকে কোথায় গিয়েছিল, কি করত, সব গল্প করত। হাতে পয়সা থাকত না। তাই কখনও কুলিগিরি করে কখনও বা হোটেলে কাজ করে খাবার পয়সা যোগাড় করত। অজানা অচেনাকে দেখার ও জানার তীব্র আকর্ষণই বোধহয় নন্দুকে নিশ্চিন্ত জীবন থেকে মাঝে মাঝেই অনিশ্চিতের পথে টেনে নিয়ে যেত।
গ্রামে মোটামুটি একটা শান্তির পরিবেশ ছিল। টুকটাক গণ্ডগোল যে হত না তা নয়, তবে তা মোড়ল বা গ্রামের মাতব্বরদের হস্তক্ষেপে মিটে যেত। অনেকবার গ্রামের নানা সমস্যায় লোকেদের বাবাকেও সালিশি মানতে দেখেছি। দুঃখ, দারিদ্র, অভাব অনটন সব থাকলেও মোটের ওপর লোকজন বেশ শান্তিপ্রিয় ছিল। আজকের পালামৌ এর মতন এমন হিংসার পরিবেশ ছিল না। শিক্ষা ও সম্যক চেতনার অভাবে মানুষগুলোর মধ্যে তখনও প্রতিবাদ বা হিংসার লক্ষণ তেমন ভাবে দেখা দেয়নি। যে যেভাবে ছিল সেটাকেই তার স্বাভাবিক জীবন এবং নিয়তি হিসেবে মেনে তার মধ্যেই খোঁজার চেষ্টা করত বাঁচার রসদ। সর্বোপরি মানুষগুলো ছিল অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। কেবল সারল্যই নয়, ওখানে অনেক দরদী ও সহানুভুতিশীল মানুষের সান্নিধ্য পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে।
সেনবাবু ছিলেন সহকারী স্টেশন মাস্টার। ছাপোষা মানুষ। সন্তান সন্ততিও সংখ্যায় একটু বেশি ছিল। ওই সামান্য মাইনেতে বড় সংসার প্রতিপালন করার পর সঞ্চয় তেমন কিছু থাকার কথা নয়। ওই অবস্থাতে ওনার ঘাড়ে হঠাত নিকট আত্মীয়া এক অনাথ মেয়ের বিয়ের দায়িত্ব এসে পড়ে। নীচ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না বলে পাশ কাটাতে পারেননি। অথচ একার পক্ষে খরচ সামলানো অসম্ভব। বাবাকে সমস্যার কথা জানালেন। বাবা তাঁর সাধ্যমত সাহায্যের আশ্বাস দিলেন বটে কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে না।
বিকেলে আমরা মাঝে মাঝে ভিমচুলহার দিকে বেড়াতে যেতাম। মহম্মদগঞ্জের পরে ভজনিয়া গ্রাম। ওই গ্রামের পাশ দিয়েই ভিমচুলহা যেত হয়। ভজনিয়া গ্রামের শেষে একটা বড় বাড়ি ছিল। ওখান দিয়ে যখন যেতাম তখন প্রায়ই বাড়ির সামনে সুঠাম দেহের পক্ককেশ পঞ্চাশোর্ধ এক প্রৌড় চারপাইয়ের ওপর সপার্ষদ বসে থাকতেন। ওনার নাম বাবু অওধেশ সিং। সকলে বাচ্চু বাবু বলে ডাকত। উনি ওই অঞ্চলের নাম ডাক ওয়ালা জমিদার। আমাদের দেখতে পেলেই উঠে এসে খুব খাতির করে বসাতেন। আমাকেও খুবই স্নেহ করতেন। কিছুক্ষণ গল্প করে সরবত খাইয়ে তবে ছাড়তেন। বাচ্চু বাবু স্টেশনের দিকে এলে বাবার সাথে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করতেন। বাচ্চু বাবুকে বাবা একদিন সেন বাবুর অসহায় অবস্থার কথা জানালেন। ব্যাপারটা শুনে কোন রকম চিন্তা না করেই বাচ্চু বাবু বললেন যে চিন্তার কিছু নেই। লোক খাওয়ানোর দায়িত্ব ওনার। শুধু নিমন্ত্রিতর সংখ্যাটা তাঁকে যেন একটু আগে জানিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের দিন বরযাত্রীর আপ্যায়ন থেকে শুরু করে খাওয়া দাওয়ার পুরো তদারকি উনি এবং ওনার লোকজনেরা করেছিল। এমন আপন জন মানুষের জীবনে খুব কমই আসে।
১৯৬৫ সালে বাবা মহম্মদগঞ্জ থেকে বদলি হয়ে যান। তারও প্রায় বছর খানেক আগে আমি পড়াশুনোর জন্য কোলকাতায় চলে আসি। চার পাঁচ বছর খুব নিবিড়ভাবে ওই জঙ্গলে ঘেরা অঞ্চলটাকে উপভোগ করেছিলাম। শহুরে জীবনের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, নিশ্চয়তার কোন উপকরণই ওখানে ছিল না। সাপ, বিছে, শ্বাপদসংকুল পরিবেশ আর গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহ যে কোন মানুষকেই আতঙ্কিত করবে। তবু প্রকৃতির যে নির্মল সুন্দর রূপ প্রত্যক্ষ করেছি তার কোন তুলনা নেই। ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন সাজে তার রূপের ছটা বিচ্ছুরিত হত। জঙ্গলের মাঝে ছোট ছোট গ্রামগুলোকে কখনই পরিবেশের সাথে বেমানান মনে হয়নি। কারণ, এদের অস্তিত্ব কখনই জঙ্গল বা বন্য প্রাণীর অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলেনি। গ্রামের মানুষেরাও ছিল প্রকৃতির মতই সুন্দর। এতদিন পর জীবনের অনেকটা পথ অতিক্রম করেও শিশুকালে দেখা প্রকৃতি ও মানুষজনের স্মৃতি এতটুকু মলিন হয়নি। চেনা মানুষেরা অনেকেই হয়ত আজ আর বেঁচে নেই। বড় দেখতে ইচ্ছে করে আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়া কতটা লেগেছে ওই প্রত্যন্ত প্রান্তরে, এবং তার ফলে তারা কি পেয়েছে আর কি হারিয়েছে।
[email protected]
পুনঃপ্রকাশ সম্পর্কিত নীতিঃ এই লেখাটি ছাপা, ডিজিটাল, দৃশ্য, শ্রাব্য, বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিলিপিকরণ বা অন্যত্র প্রকাশের জন্য গুরুচণ্ডা৯র অনুমতি বাধ্যতামূলক। লেখক চাইলে অন্যত্র প্রকাশ করতে পারেন, সেক্ষেত্রে গুরুচণ্ডা৯র উল্লেখ প্রত্যাশিত। - আরও পড়ুনভাগের মজা - Sukdeb Chatterjeeআরও পড়ুনবিকল্প - Sukdeb Chatterjeeআরও পড়ুনপক্ষীর দল - Sukdeb Chatterjeeআরও পড়ুনমারাঠা ডিচ - Sukdeb Chatterjeeআরও পড়ুনবর্তমানে বাঁচা - সমরেশ মুখার্জীআরও পড়ুনকাজলের ঘনত্ব - ইন্দ্রাণীআরও পড়ুনপরাশর উপত্যকা - পাপাঙ্গুলআরও পড়ুনছেঁয়াবাজীর ছলনা - ২১ - দ
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
Kishore Ghosal | ০৩ জুলাই ২০২৪ ১৬:৪৬534117
- বাঃ ভারি সুন্দর স্মৃতিচারণ।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... পলিটিশিয়ান, কুমিরের কান্না, আশ্চর্য বটে)
(লিখছেন... Argha Bagchi, Sudipta Acharyya, Naresh Jana)
(লিখছেন... Naresh Jana, Sudipta Acharyya, Argha Bagchi)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... অসিতবরণ বিশ্বাস )
(লিখছেন... Mira Bijuli, Sukdeb Chatterjee)
(লিখছেন... দ, রমিত চট্টোপাধ্যায়, পাপাঙ্গুল)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... দীপ, দীপ, Ranjan Roy)
(লিখছেন... আবার আলাদা করে কপালভাতি কেন?, syandi)
(লিখছেন... প্রাণায়াম, Ranjan Roy, nb)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Ranjan Roy)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : [email protected] ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত