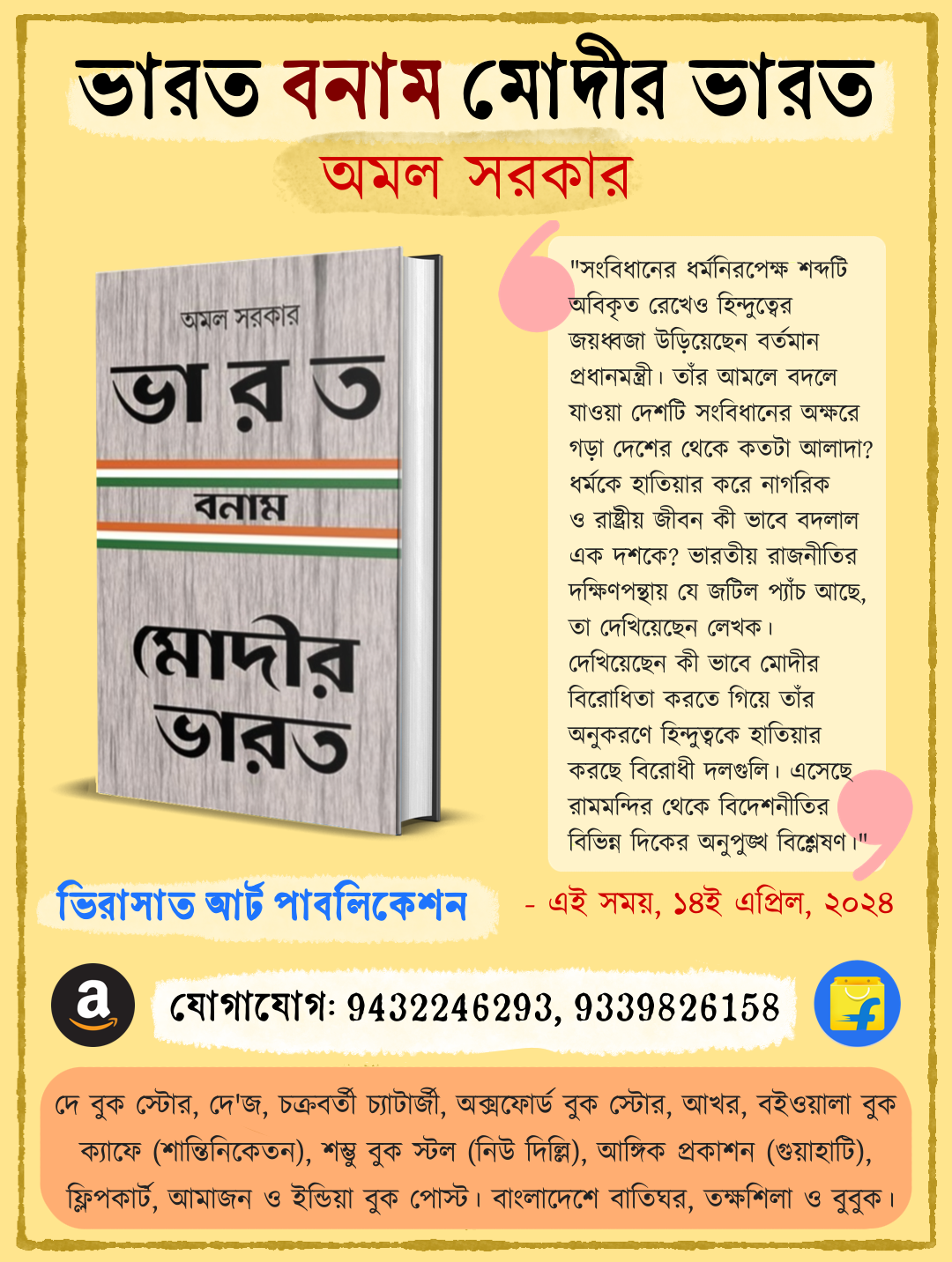এক
ছোটোবেলা আর যুববেলার সবকিছু পালটে গেছে ; ইমলিতলা পাড়ার গোলটালির চালাবাড়িগুলো হয়ে গেছে ইঁটের দাঁত বেরোনো একতলা-দুতলা । আমাদের বাড়িটা চেনা যায় না । সামনের লাল রোয়াক, যার ওপরে বসে কপিলের দাদু বাচ্চাদের গালাগাল শেখাতেন, সেখান থেকেই দেয়াল উঠে গেছে ; যারা থাকে, তারা উঠোনে গরু পুষেছে, দেয়ালময় ঘুঁটে দেয়া, খোলা ছাদ নেই, ঘর উঠে গেছে, বাঁদরগুলোর দল শহর ছেড়ে চলে গিয়ে থাকবে । কপিলের প্রজন্মের কেউ বেঁচে নেই, আর নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা আমার নাম জানে ভুখি পিঢ়ি আন্দোলনের সংবাদ পড়ে । গলির ভেতরের চালাবাড়িগুলোও ইঁটের ; সব নতুন মুখ । চোর-ডাকাতদের শুয়োর মারবার আর গাঁজার ঝোপের বস্তিতে উঠেছে একতলা বাড়ি । মহাদলিতদের পাড়া দখল করে নিয়েছে মধ্যবিত্ত মধ্যজাত চাকুরে পরিবার । কুলসুম আপাদের বাড়ি ভেঙে শিয়া মুসলমান চারতলা আবাসন , মহিলারা বোরখায় । নাজিম-কুলসুম আপারা অন্য কোথাও চলে গেছে । কুলসুম আপা, আভাসে মনে হলো, আরব দেশে চলে গেছেন । মসজিদটায় কেউ আর খেলতে ঢোকে বলে মনে হলো না, কেমন যেন ঘিঞ্জি আর নোংরা, যদিও বিশাল মিনার উঠেছে । ইমলিতলায় বাবা-জেঠার প্রজন্মের কেউই নেই, আমার প্রজন্মেরও কেউ নেই । পুরোপুরি অপরিচিত আমার নিজের ছোটোবেলার পাড়া ।
ছোটোবেলার ব্রাহ্ম স্কুল রামমোহন রায় সেমিনারি হয়ে গেছে বিশাল, ইউনিফর্ম পরতে হয় ছাত্রছাত্রীদের, দুটো শিফট হয়, বাংলামাধ্যম উঠে গেছে, ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাব ফুরিয়ে গেছে ; ব্রাহ্ম কবি-লেখকদের বাংলা বই আর সম্পাদিত পত্রিকাগুলো আর নেই । পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়েও বাংলা বিভাগ আছে কেবল পিএইচডি করার জন্য ।
যুববেলার দরিয়াপুরও পালটে গেছে, আমাদের বাড়িটা তিনতলা পর্যন্ত দাদার বড়ো ছেলের ফোটোর জিনিসপত্রে ঠাশা, এখন বাবার স্টুডিও নেই, ক্যামেরায় ফোটোতোলার দিনকাল বিদায় নিয়েছে, ছোটো ক্যামরাও লাখ খানেকের বেশি দাম, বেশির ভাগ কাজ কমপিউটারে। বাবা এই পরিবর্তন দেখে যেতে পারলেন না । সামনের বারান্দা ভেঙে ফেলা হয়েছে । ওই বাড়িতে দাদার ছেলে থাকে না । শশুরের দেয়া ফ্ল্যাটে কদমকুঁয়ায় থাকে । আমার আর ছেলে-মেয়ের কোনোকিছুই সেখানে নেই। পাশের চুড়িঅলা, যার কাছে মা মুর্গি রাঁধতে শিখেছিলেন, জায়ফল দিয়ে, তার পরিবার চলে গেছে পাকিস্তানে । চুড়ির দোকানের ওপরে শিখ সরদার থাকতেন, যিনি প্রতি রাতে একজন বেশ্যাকে নিয়ে ফিরতেন, তিনি বহুকাল আগে মারা গেছেন । বাড়ির মালিক, যার পাশেই ছিল বাঁশের আড়ত, চারতলা বাড়ি তুলে ভাড়া দিয়েছে । সামনের কবরমাঠের জায়গায় সুন্নি মুসলমানদের বাড়ি আর দোকান । আল্লু মিয়াঁ আর ওর বারবার বিয়ে-দেয়া মেয়েদের খবর জানে না কেউ ।
উত্তরপাড়ার সাবর্ণভিলা ভেঙে আবাসন তৈরি হয়েছে । আমি, দাদা, বড়দি, ছোড়দি, ডলি, মনু আমাদের অংশ বিক্রি করে দিয়েছি । যারা থাকে তারা আমার দুর্নামের সঙ্গে পরিচিত বলে দেখতে এসেছিল । আমি কাউকেই চিনতে পারলুম না । কাকাবাবু, মানে বিশেখুড়োর কোতরঙের জমিজমা আর বাড়ি বেচে দিয়েছে ওনার পোষ্যকন্যা ; কে জানে কোথায় চলে গেছে ! পাণিহাটিতে মামার বাড়ির অর্ধেকের বেশি, পুকুর আর জমিজমাসুদ্দু, বেচে দিয়েছিলেন ছোটোমামা ; সেই জায়গায় আবাসন উঠেছে । ‘নিলামবাটি’ লেখা পাথরটা আছে, একটা বাড়ির দরোজার সামনে, কিন্তু সেটায় দাদামশায় থাকতেন না । দাদামশায় যে সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেখানকার দেয়াল থেকে ওনার ফোটো গুদামঘরে চালান করা হয়েছে । পাণিহাটির মোচ্ছবতলা, চৈতন্যদেব বিশ্রাম নিয়েছিলেন বলে খ্যাত, এখন মনে হয় বোষ্টমদের নিয়মিত উৎসবের প্রাতিষ্ঠানিক জমঘট। এখন পাণিহাটি থেকে ভুটভুটি যায়, কেবল ওপারে কোন্নোগরে নয়, বিভিন্ন জায়গায় । ছোটোবেলায় দাঁড়-বাওয়া নৌকো করে কোন্নোগর থেকে পাণিহাটি যেতুম । কোন্নগরে বড়জেঠিমার বাপের বাড়িতে কেউই আর নেই, তবে জগদ্ধাত্রী বারোমেসে মন্দির আছে ; সেখানকার কেউই চিনতে পারলো না আমাকে । ওনারাও অনেকটা জমি বিক্রি করে দিয়েছেন, যার ওপর আবাসন উঠেছে । বড়োজেঠিমার ভাইঝি আলো, সুন্দরী বলতে যা বোঝায়, তাইই ছিল, দাদা বিয়ে করতে চায়নি, কেননা দাদা চাইবাসায় এক বিবাহিতা যুবতীকে ভালোবাসতো, পরে যার এক বোনকে দাদা বিয়ে করেছিল — ব্যাপারটা আছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর উপন্যাস ‘কিন্নর কিন্নরী’তে ।
আমি নাকতলার ফ্ল্যাট বিক্রি করে চলে এসেছি মুম্বাই । ওই পাড়ায়, ওই ফ্ল্যাটে, ওই পরিবেশে জীবন কাটানো, এই বয়সে অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল ।ছেলের এক বেডরুম ফ্ল্যাট আছে মুম্বাইতে । বুড়ো-বুড়ি চালিয়ে যাচ্ছি যেমন-তেমন । দাদা মারা গেছে । দাদার সাহিত্যিক বন্ধুরাও মারা গেছে । আমার ছোটোবেলার স্কুলের বন্ধু সবাই মারা গেছে, তরুণ শুর যুববেলাতেই লিউকোমিয়ায় মারা গিয়েছিল, বারীন গুপ্ত মারা গিয়েছিল মাথায় রক্তক্ষরণের দরুণ, সুবর্ণ উপাধ্যায়-এর সঙ্গে শেষ দেখা কলকাতায় পাঁচ বছর আগে – প্রোস্টেটের ভুল অপারেশনে রক্ত ঝরে, বলেছিল বেশিদিন বাঁচবে না । স্কুলের বন্ধু রমেণ ভট্টাচার্য আর অনিমেষ গুপ্ত নাকতলার কাছেই থাকতো, বাঁশদ্রোণী বাজারে দেখা হতো প্রায়ই, শুনেছি মারা গেছে । যুববেলার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র কয়েকজন টিকে আছে । সাহিত্যিক সঙ্গীদের মধ্যে টিকে আছে সুবিমল বসাক, প্রদীপ চৌধুরী, সুবো আচার্য, দেবী রায় আর ত্রিদিব মিত্র-আলো মিত্র।সুবিমল মাঝে-মধ্যে ফোন করে । স্ত্রী মারা যাবার পর সুবো আচার্য পুরোপুরি অনুকূল ঠাকুরের আশ্রমের সেবায় লেগে আছে ; ‘নারী নরকের দ্বার’ বলে ছেলেদের বিয়ে দেয়নি । প্রদীপের স্ত্রী মারা গেছে ; প্রদীপের দুটো চোখই খারাপ । ত্রিদিব বাড়ি করেছে হাওড়ায় । সুবিমল বাড়ি করেছে বেলঘরিয়ায়, দুই ছেলে, নাতি-নাতনি নিয়ে থাকে । দেবী রায় ফ্ল্যাট কিনে হাওড়ায় কোথাও থাকে ; স্ত্রী মারা যাবার পর সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। শৈলেশ্বর ঘোষ অপারেশান থিয়েটারে মারা গেছে, ওর স্ত্রী, মেয়ে-জামাই সবাই মারা গেছে, সুন্দর বাংলোবাড়ি একেবারে ফাঁকা, ভুতুড়ে । সুভাষ ঘোষ মারা গেছে ; এখন বাড়িতে ঢুকতেই সামনে সুভাষের বিশাল ফ্রেমে বাঁধানো ছবি, আগে ছিল জ্যোতি বসুর ছবি ।অবনী ধর আর বাসুদেব দাশগুপ্ত অশোকনগরে মারা গেছে । অরুণেশ ঘোষ জলে ডুবে মারা গেছে ; হয়তো আত্মহত্যাও করে থাকতে পারে । অনিল করঞ্জাই আর করুণানিধান মুখোপাধ্যায় মারা গেছে দিল্লিতে । উত্তরবঙ্গের হাংরি আন্দোলনকারী অলোক গোস্বামী আর রাজা সরকার কলকাতায়, দেবজ্যোতি রায় উত্তরবঙ্গেই আছে। ত্রিপুরা থেকে অরূপ দত্ত চলে এসেছে কলকাতায় ।
বড়দি-ছোড়দির বিশাল জমিদারি বাড়ি, ‘সিলভ্যান হাউজ’, গেট দিয়ে ঢুকতেই দুইধারে ছিল বকফুল গাছের সারি, ফুলের বাগান, সব উধাও । সেখানে বিশাল আবাসন উঠেছে । কোটিপতি হয়ে ভাগ্নে পাটনা ছেড়ে চলে গেছে বিহারের বাইরে, লালু যাদবের স্যাঙাতদের কিডন্যাপগ্যাঙের ভয়ে । ভাগ্নি জয়ার ছেলে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের চ্যানেল চালায়, নিজেও ভালো গায় ।
পিসেমশায় তিনকড়ি হালদার, ওনাকে নিয়ে আমার একটা গল্প আছে “অপ্রকাশিত ছোটোগল্প” বইতে, আহিরিটোলার বাড়ি শরিকরা বিল্ডারকে দিয়ে দেবার ফলে ওই বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেন, পকেটে যে চিরকুট পাওয়া গিয়েছিল তাতে লেখা, “আনন্দধারা বহিছে ভূবনে” । পিসেমশায়ের ছেলেদের ঠাকুমা একটা জমি দিয়েছিলেন হিন্দমোটরে, সেখানে ভাইয়েরা একটা করে ঘরে থাকে, আর আরেকটা ঘর রান্নার কাজে লাগে । সবচেয়ে বড়ো ভাই অজয় হালদার মানে সেন্টুদার বিয়ে দিয়েছিল দাদা দ্বারভাঙ্গার এক ঘি ব্যবসায়ীর মেয়ের সঙ্গে ; ঘি আর দিশি বিহারি মদ ঠররা খেয়ে ঘরজামাই সেন্টুদা সেখানেই মারা গেছে । পরের দিকে দাদার সঙ্গে কোনো কারণে সেন্টুদার বনিবনা ছিল না বলে পাটনায় এলে সেন্টুদা উঠতো দিদিদের বাড়ি । ছোটোবেলা আর যুববেলার কলকাতার বহু রাস্তার নাম পালটে গেছে, মামলার সময়ে ঘুরে বেড়াতুম সেই সব রাস্তায় ।
নাগপুরে শশুরবাড়িও ভেঙে ফেলে তার মুসলমান মালিক, আমার মামাতো শালাদের মোটা টাকা দিয়ে, সেখানে হজ যাত্রীদের জন্য আশ্রয় তৈরি করছে, পাশেই নিজের জমিতে বিশাল মসজিদ তুলেছে যাতে এক সঙ্গে এক হাজার মানুষ নামাজ পড়তে পারে । আমার স্ত্রীর এক মুসলমান বন্ধু, প্রতিবেশি বাড়ির মেয়ে, হিন্দু যুবককে বিয়ে করে নাম পালটিয়ে মুম্বাইতে নাতি-নাতনিদের সঙ্গে থাকে । যে শালির আমি পাটনায় বিয়ে দিয়েছিলুম, সে, তার স্বামী পরপর মারা যাবার দরুন তাদের লেক গার্ডেনসের বাড়ি ভেঙে ফেলে ফ্ল্যাটবাড়ি উঠছে ।
দুই
আজকে, এখন, মুম্বাইতে এসে, আয়না দেখা ছেড়ে দিয়েছি, বাইরে বেরোলেও চুল আঁচড়াই না, পায়জামায় পেছনদিকে ছেঁড়া থাকলেও তাই পরেই বেরোই, কেননা কেউই আমার পেছন দিকে তাকানো দরকার মনে করে না, নিঃসঙ্গতা আর একাকীত্বের গাড়ি পার্ক করার বেসমেন্টে অটোরিকশায় বসে টের পাচ্ছি যে স্মৃতি একেবারে ধুলোপড়া ত্যাবড়ানো, স্ফটিক-স্বচ্ছ নয়, আমার, আমার আসেপাশের মানুষদের, অনেকের দেহে শ্মশানে জলভরা হাঁড়ি পড়ার শব্দসহ, বিজলি-চুল্লীতে চর্বি ফাটবার শব্দসহ, হুকবোতামের ছেদ-যতি-সেমিকোলনসহ, বয়স্ক-অল্পবয়স্ক ঘটনা নিজস্ব চরিত্র নিয়ে উদয় হচ্ছে, আর যা ভুড়ভুড়ি কেটে ভেসে উঠছে, সেগুলোই, তড়িঘড়ি, উবে যাবার আগে, লিখে ফেলব, শাড়ির ভাঁজে পাট করে রাখা সুমিতা চক্রবর্তীর গ্রীষ্মশীত, রাতে ওনার বাগানের গাছেরা নিজেদের পরিচর্যা করতো, আমি ওনার সাম্যবাদী কিউবার লঝঝড় মোটরগাড়িতে, “আমি তোর অ্যামেচার বান্ধবী” ; তারপর যখন বুড়ি থুথ্থুড়ি, “কলকাতায় সবাই পার্টিকর্মী, দৃশ্য বা অদৃশ্য ঝাণ্ডা হাতে।” “শুধু কমিউনিস্টরাই বলতে পারবে কেন কমিউনিজম ফেল মারলো।” “মানববোমারা মরতেই থাকবে, এর আর শেষ নেই, দেখেনিস ।” “হিরোহিতোর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করুন বা হিটলারের সঙ্গে, সুভাষচন্দ্র বোস আমার হিরো, আমার স্বপ্নের প্রেমিক ।” “লিখতে বসে সবচেয়ে আগে ভুলে যাবি তোর স্কুল-কলেজের ভাষা-শিক্ষকদের, নয়তো এগোতে পারবি না ।” “বাঙালি মার্কসবাদীরা, যারা নিহিলিজমের বিরোধিতা করতো, তারাই পশ্চিমবঙ্গে নিহিলিজম ডেকে আনলো।” “অনুসরণকারীরা পিঠে ছোরা মারে কেন জানিস ? তারা তো পিছন থেকে অনুসরণ করে।” “ভিতুরা ভয়ার্ত কবিতার তত্ব বানায় আর সেই তত্বকে সমর্থন করে পরাজিতরা।” “আত্মহত্যার কোনো কারণ হয় না।” এখন একমাত্র রুটিন হল রাতে টয়লেটে পেচ্ছাপ করতে যাওয়া, প্রস্টেটের ঘড়িধরা চাপে ।
নাড়ি তৈরির ম্যাজিক শুধু নারীই তো জানে। সেক্স করার সময়ে বার বার “আই হেট ইউ” বলার উপাদেয় রহস্য । আমি আগের জন্মে ঘুর্ণিঝড় ছিলুম পরের জন্মে গোরস্হান হবো । বহু ঘটনা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবে, যেতে দিতে হবে, পাশাপাশি গুরুত্বহীন ঘটনা হঠাৎই ঘা দিয়ে নিজেকে জাহির করবে , যাই হোক, সময়ের ধ্যাবড়া অনুক্রম জরুরি বলে মনে হয় না । চাকুরিসূত্রে ভারতের এতো গ্রাম আর শহর ঘুরেছি যে হাতির পিঠে চেপে কোন গ্রামে গিয়েছিলুম, কোথায় উটের দুধ খেয়েছিলুম যেমন স্মৃতি থেকে ঝরে গেছে, তেমনই কোন নদীর পাশ দিয়ে মাথার ওপর ট্যুরের ক্যাঁদরা চাপিয়ে কোন গঞ্জে গিয়েছিলুম, মনে করতে পারি না, অথচ ঘটনাগুলো ঝাপসা হয়নি আজও ; অমন অজস্র টুকরো-টাকরা, বহুগ্রাম জলহীন বলে কেমন করে শিখে গিয়েছিলুম টয়লেট পেপারের রোল সঙ্গে রাখতে, আলের ওপরে বসে হাগতে, জল না খেয়ে বহুক্ষণ টিকে থাকতে । কে বলেছিল, “মাতৃভূমিতে শুধু গরিবরাই মরে?” মনে নেই । কে বলেছিল, “রাস্তার কুকুরদের কান নিয়ে জন্মেছিস?” মনে নেই । কে বলেছিল, “তুই বামপন্হী? শুনলেই সন্দেহ হয় তোর বাপ সোভিয়েত রুবল খেয়েছে !” মনে নেই । কে বলেছিল, “তোর ডানদিকে সিঁথে কাটা উচিত।” মনে নেই । কে বলেছিল “ঈশ্বরপ্রদত্ত বলে কিছু হয় না ?” মনে নেই । কে বলেছিল, “রাষ্ট্র চিরকাল লিবার্টি ইকুয়ালিটি ফ্র্যাটারনিটির বিরোধিতা করবে”, মনে নেই । কে বলেছিল, “লাথি না খেলে বিজ্ঞ হওয়া যায় না”, মনে নেই। কে বলেছিল, “ফাংশানাল লিঙ্গ না থাকলে জিনিয়াস হওয়া যায় না”, মনে নেই।
১৯৬৪ সালে যখন পুলিশ কমিশনারের কাছে জানতে পারলুম যে আমার বিরুদ্ধে নালিশকারীদের তালিকায় সন্তোষকুমার ঘোষ আর আবু সয়ীদ আইয়ুব আছেন, শুনে বুঝতে পারলুম যে ছিপে ঠিক-ঠিক বঁড়শিই বেঁধেছি । ১৯৬২ সালে কলেজ স্ট্রিটে একটা মিছিলে উৎপল দত্তের হাতে হাংরি বুলেটিন দিতেই উনি আঁৎকে বলে উঠলেন, “হাংগরি জিন্নাড়িশন”, লিফলেটটা দুমড়ে ফেলে দিলেন রাস্তায়, দেখে, অন্য একজন মিছিলকারী সেটা তুলে পড়তে আরম্ভ করলে, চেয়ে নিয়ে বললুম, আপনার জন্যে নয় । ১৯৬৩ সালে গল্পকার শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাওড়ার বাড়িতে গিয়েছিলুম । বললেন, “ওহে, একেবারে তোলপাড় করে ফেলেছ যে, ক্ষমতাবানদের চটিয়ে দিচ্ছ, তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে, জানো কি ?” বলেছিলুম, যা করার তা তো করে যেতে হবে, ডিরোজিও তো যা করার তাই করে গেছেন। জানি না কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশকরা কেন শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেপে দিলে । উদয়ন ঘোষ, শান্তি লাহিড়ির মতন ওনারও দুর্বলতা ছিল সন্দীপন, শক্তি, সুনীলের সঙ্গে চিপকে থেকে আনন্দ পাবার ।
১৯৭১ সালে শঙ্খ ঘোষ একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, “শব্দ আর সত্য” শিরোনামে, ১৯৭১ সালে, রিমেম্বার ১৯৭১ সালে । কী লিখেছেন শুরুতেই তাঁর সাহিত্যিক-রাজনৈতিক গদ্যে ? লিখেছেন, রিমেম্বার ১৯৭১ সালে, যে, “কবিতা লেখার অপরাধে এই শহরের কয়েকজন যুবককে যে একদিন হাজতবাস করতে হয়েছিল, এটা আজ ইতিহাসের বিষয়।” ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৫ সালে আমার এক মাসের কারাদণ্ডের আদেশ হয়ে গিয়েছিল তা উনি ১৯৭১ সালে জানতেন না ! পঁয়ত্রিশ মাস ধরে আদালতের চক্কর কাটতে হয়েছিল, তা উনি ১৯৭১ সালে জানতেন না, জানতেন কেবল একদিনের হাজতবাস । কী বলব ? হাংরি আন্দোলনের যাঁরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছেন, আবু সয়ীদ আইয়ুবের পর শঙ্খ ঘোষ, আর বাহুল্য বলা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম করতে হয় । শঙ্খবাবু শৈলেশ্বর ঘোষকে টেনে নিয়ে গেছেন প্রতিষ্ঠানের কয়েদখানা বাংলা অ্যাকাডেমিতে । শঙ্খবাবুর সঙ্গে আমার একবারই দেখা হয়েছে, ওই বাংলা অ্যাকাডেমিতেই, হ্যাণ্ডশেকের জন্যে হাত এগিয়ে দিয়ে বলেছিলুম, আমার নাম মলয় রায়চৌধুরী, শুনে, নিজের কানে মনে হল যেন বলছি, আমি মিশরের ফ্যারাও দ্বিতীয় র্যামাসেজ । আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমেরিকায় বসে ভাবছিলেন মলয়টা কলকাতার সবকিছু লুটেপুটে খেয়ে ফেললো আর আমেরিকা থেকে ফিরে ‘আত্মপ্রকাশ’ নামে একটা তড়িঘড়ি উপন্যাস লিখেছিলেন সাগরময় ঘোষের হুকুমে যাতে ভয়ের চোটে লেখেননি যে বেশ্যালয়ে গিয়ে কী করতেন আমি কিন্তু উকিলের জানলা দিয়ে দেখেছি ষাটের দশকে পুরো কৃত্তিবাসের দল ঢুকছে অবিনাশ কবিরাজ লেনে, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় শকুনের কাঁধ উঁচু করে ।
১৯৭২ সালে, চেন্নাইয়ের গিণ্ডিতে একটা জ্যান্ত কেউটে সাপকে আমার হাতে জড়াতে দিয়েছিল পার্ক কর্তৃপক্ষ, ওঃ কি ঠাণ্ডা, নিজের সম্পর্কে ইপিফ্যানির গর্ব হয়েছিল । তারপর একটা পাইথনকে গলায় ফেলে দিল উত্তরীয়ের মতন করে, কী যে আনন্দ হয়েছিল, এই হল আমার সম্বর্ধনার সত্যিকারের উত্তরীয় । আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট বলেছিল, ব্রাহ্মণ হয়ে জ্যান্ত সাপে হাত দিলেন, দেখুন বংশরক্ষা হয় কিনা । কী করেই বা কারাগারে আটক সাপদুটোর বংশরক্ষা হবে, বললুম তাকে, ছোবল দিয়ে । ১৯৭৫ সালে ফালগুনী রায়ের সঙ্গে শেষবার দেখা । পাটনায় অফিসে এসেছিল, তখন আমার লেখালিখি আঙুল ছেড়ে উধাও, বলল, সবাই আলাদা হয়ে গেছে, ও এখন দীপক মজুমদারের সঙ্গে, মাদক আর সোনাগাছি নিয়ে ভালোই আছে । হাংরি আন্দোলনের সময়ে প্রায়ই পাটনায় আসত ফালগুনী, ওর জামাইবাবু ছিলেন আমার ইকোনমিক্সের অধ্যাপক, অত্যধিক মোটা আর বেঁটে, রিকশায় চাপার আগে নাড়িয়ে দেখে চাপতেন, তা দেখে হাসতুম বলে চটা ছিলেন আমার ওপর, ফালগুনীর দিদি এসে আমার মাকে বলে গিয়েছিলেন যে, আমি ফালগুনীকে কুপথে নিয়ে গিয়ে নষ্ট করে দিয়েছি । ফালগুনীর প্রেমিকার বিয়ে হয়েছিল পাটনায়, ওর জামাইবাবুর বাড়ির কাছেই প্রেমিকা থাকতো লোহানিপুর পাড়ায় । আমরা দুজনে পাটনার গুলফি ঘাটে গিয়ে কিংবা গোলঘরের ওপরে বসে সরকারি দোকান থেকে কেনা গাঁজা-চরস ফুঁকতুম, মহেন্দ্রুঘাটে বসে ঠররা খেতুম । ফালগুনীর মৃত্যুর খবর পেয়েছিলুম লখনউ থাকতে ।
১৯৮৯ সালে মেয়ে অনুশ্রীর গোদরেজ টাইপরাইটার খারাপ হয়ে যেতে অনেক খুঁজেপেতে একজন মেকানিকের বাড়ির ঠিকানা পেয়েছিলুম । তখন থাকতুম সান্টাক্রুজে আর মেকানিক থাকতেন জুহুর গোয়ানিজ কলোনিতে । এখন অবশ্য সেই সান্টাক্রুজ-জুহু আর নেই, ধনীদের বিশাল অট্টালিকা আকাশে উঠে গেছে সর্বত্র। মেকানিকমশায় যেদিন সারিয়ে দেবেন বলেছিলেন, সেই দিন আমি টাইপরাইটারটা নেবার জন্যে ওনার কুঁড়েঘরে গিয়ে অপেক্ষা করছিলুম, ওনার বুড়িবউ বললেন, এক্ষুনি এসে যাবে । আমার মুখ দাড়ি-গোঁফে ঢাকা, নাম এম আর চৌধারী । গাউনপরা বিশালবপু বুড়ি চুপচাপ বসেছিলেন । সামনের বাড়িতে গিটার বাজিয়ে হইচই গান গাইছিল যুবক-যুবতীরা । গোয়ানিজ বুড়ি হঠাৎ বলে উঠলেন, “এই প্রটেস্ট্যান্টগুলো আর হিন্দুগুলো, অত্যন্ত নোংরা আর ডিসিপ্লিনহীন, তাই তো দেশটার এমন অবস্হা, যখন ব্রিটিশরা ইনডিয়ায় ছিল আর পোর্তুগিজরা গোয়ায় ছিল তখন এদের এরকম দৌরাত্ম্য ছিল না ।” নিজেকে ফাঁস করলে বুড়ি মুষড়ে পড়বে ভেবে মুখ বুজে রইলুম । ২০০০ সালে কাণ্ডিভিলি মুম্বাইতে হার্ট অ্যাটাকের পর প্রতিদিন সকালে জগার্স পার্কে হাঁটতেযেতুম, সেখানে লাফটার ক্লাবের বুড়ো সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় হল । সকলের মতন আমিও ওয়ান টু থ্রি হলেই ওপরে দুহাত তুলে জোরে-জোরে অকারণে হাসতুম, এছাড়া আর বুড়ো বয়সে হাসির সুযোগ নেই । একজন গুজরাটি আমার সঙ্গেই ফিরতেন, কী করেন জিগ্যেস করতে বলেছিলুম অবসর নিয়েছি, যা পেনশন পাই তাতেই চালাই। উনি কী করেন জিগ্যেস করতে বললেন যে, “সকালে-বিকেলে ক্লায়েন্টদের কুকুর হাগাতে নিয়ে যাই আর রাতের বেলায় মদ খেয়ে কবিতা লিখি, মাসে পঞ্চাশ হাজার হয়ে যায়।”
—কুকুর হাগাতে ?
—হ্যাঁ, কারোর তো সময় নেই, সবাই এ-শহরে টাকার ধান্দায় ছুটছে ।
—আপনি তাদের কুকুরগুলোকে সকাল-বিকেল হাগাতে নিয়ে যান ?
—হ্যাঁ, সকাল পাঁচটা থেকে শুরু করি । কোন কুকুর কখন হাগতে প্রেফার করে প্রথম কয়েক দিনেই জেনে যাই, ক্লায়েন্টরাও আইডিয়া দেন ওদের হাগবার-মোতার সময়ের ।
—কিরকম চার্জ করেন ?
—কুকুরের ব্রিডের ওপর নির্ভর করে । রটউইলার হলে হাজার পাঁচেক প্রোপোজ করি, তারপর তিন হাজারে সেটল করি । অন্য ব্রিডের হলে কম নিই । তবে আমি নিজেকে ডগ ট্রেনার বলি, কুকুরগুলোকে আধঘণ্টা খেলাতেও হয় ।
—একদিন আপনার কবিতা শুনব ।
—আসবেন, ড্রিংক করেন তো ?
—না, আপাতত বন্ধ, হার্ট অ্যাটাক থেকে সবে উঠেছি ; হার্ট অ্যাটাকের সময়েও হাগা পায়, বীর্য বেরিয়ে আসে । আত্মহত্যাকারীদের যেমন হয়, গু আর বীর্য বেরিয়ে আসে । আত্মহত্যাকারিনীদের কি কিছু বেরিয়ে আসে ?
কুকুর হাগানোর সঙ্গে কবিতার যোগাযোগ আছে জেনে বেশ ভাল্লাগলো । কবিদের রেটও ব্রিড অনুযায়ী।
তিন
২০০৭ সালে আমস্টারডমের ডি ওয়ালেন খালপাড়ে গাইড মিস মারিসকা মাজুরের সঙ্গে আমরা একদল বিদেশী পর্যটক বেশ্যালয় দেখতে বেরিয়েছিলুম । মারিসকা এককালে নিজেও যৌনকর্মী ছিলেন । রেড লাইট শব্দটা এই বেশ্যালয় থেকেই ছড়িয়েছে । নেপোলিয়ানের আইনি অনুমতিপ্রাপ্ত বেশ্যালয়, মানুষের চেয়েও বড়ো কাচের শোকেসে লাল আলো জ্বেলে অপেক্ষা করছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসে জড়ো হওয়া যৌনকর্মীরা, রেট, সময় এবং পদ্ধতি বাঁধা ; তার বাইরে কিছু করতে চাইলে দরাদরি করতে হবে । প্রতিটি ঘরে লাল আলো । যে ঘরে নীল রঙের আলো সেঘরে অপেক্ষা করছে পুরুষ যৌনকর্মী । খালপাড়ে নানা রকমের যৌনকর্মের আর যৌনবস্তুর দোকান, ঘুরে-ঘুরে দেখলুম । চাবুক, চেস্টিটি বেল্ট, লিঙ্গের আকারের সিটঅলা সাইকেল, পর্নোগ্রাফির বই আর ফিল্ম, গাঁজা ফোঁকার দোকান, আবসাঁথ খাবার রেস্তরাঁ ইত্যাদি । দেখতে-দেখতে এগোচ্ছিলুম । হঠাৎ একজন মধ্যবয়সী হোঁচোট খেয়ে পড়ল আমাদের সামনে, ওপরে মুখ তুলে চলার ফল । মারিসকা মাজুর তাকে দুহাত ধরে টেনে তুলে দেখালেন রাস্তার ওপর ব্রোঞ্জের একটা ভাস্কর্য, অজস্র মানুষের চলার দরুণ চকচকে হয়ে গেছে । ভাস্কর্যটা হলো একজন পুরুষের ডান হাত একটি যুবতীর বাঁদিকের মাই টিপছে, ব্যাস ওইটুকুই, হাত আর একটা মাই । মারিসকা বললেন, আগে এই ভাস্করের নাম জানা যায়নি, এখন জানা গেছে ওনার নাম রব হজসন, লুকিয়ে ভোররাতে পুঁতে দিয়ে গেছেন।
১৯৬১ সালে একবার খালাসিটোলায় পাশের লোকটা হাতে গেলাস নিয়ে কাঁদছিল দেখে আমারও কান্না পেয়ে গিয়েছিল ; পিসেমশায় খালাসিটোলায় গেলে নির্ঘাৎ কাঁদতেন, মা ওগো মা, বলে বলে কাঁদতেন; তারপর যেতেন সোনাগাছি । আমিও কেঁদে নিয়েছিলুম, পিসতুতো দাদা সেন্টুদার সঙ্গে অবিনাশ কবিরাজ লেনে গিয়েছিলুম; সেন্টুদা বলেছিল, এখানেও স্কুল ফাইনাল, বিএ, এমএ করতে-করতে এগোতে হয়, সব শিখিয়ে দেবো তোকে, নিরোধ জানিস তো নিরোধ, সঙ্গে নিয়ে আসবি, ঠোঁটে চুমু খাবি না, ওখানে চাটবি না, দিনে-দিনে আসবি, দিনে-দিনে চলে যাবি, কেউ দেখতে পাবে না, রেটও দুপুর বেলায় হাফ, তখন কেউ শ্যাম্পু করা চুল আঁচড়ায়, কেউ পায়ের নখে নেলপেলিশ লাগায়, কেউ বারান্দায় বসে হাই তোলে, দিল খুশ হয়ে যাবে, ইচ্ছে করলে তুই পায়ে নেলপালিশ লাগিয়ে দিতে পারবি, চুল আঁচড়ে দিতে পারবি, এমনকি সেক্স করার আগে যদি গিল্টি ফিল করিস তাহলে সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিতে পারবি, কালবৈশাখির ঝড় উঠলে আহিরিটোলা ঘাটে নেমে দুজনে চান করার ভান করতে পারবি । ১৯৬৪ সালে যখন হাংরি মামলায় গ্রেপ্তার হলুম তখন বড়োজেঠিমা বলেছিলেন, যারা পরীর গপপো জানে, যারা দত্যিদানোর গপপো জানে, যারা পুরাণের ভগবানদের গপপো জানে, তাদের কাছে নোংরা বই, নোংরা গপপো বলে কিছু হয় না, কোনো বইকেই অচ্ছেদ্দা করা উচিত নয়, পুরাণের গপপো পড়লেই জানা যায় আমরা কোনো একজনের মতন ওই সব গপপোতে লুকিয়ে আছি, আমরা কি মহাভারতের গল্পতে নেই ? আছি, আছি রে আছি ।
১৯৬৩ সালে অ্যালেন গিন্সবার্গ যখন পাটনায় আমাদের বাড়িতে ছিল, একটা শতচ্ছিন্ন বই পড়তে দিয়েছিল, ওর পড়া হয়ে গিয়েছিল বইটা, “জার্নি টু দি এন্ড অফ দি নাইট”, লুই ফার্দিনাঁ সেলিন-এর লেখা, কালো রঙের মলাট, দারুন উপন্যাস। পরে সেলিন সম্পর্কে খোঁজখবর করে জানতে পেরেছিলুম যে লোকটা ঘোর ইহুদি-বিদ্বেষী ছিল আর ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্যামফ্লেট ছাপিয়ে গালমন্দ করতো । গিন্সবার্গের বাবা-মাও ইহুদি, তবু, উপন্যাসটা অসাধারণ বলে, গিন্সবার্গের মনে হয়েছিল, আমার পড়া উচিত । বইটা সুভাষ ঘোষকে পড়তে দিয়েছিলুম তারপর কী হলো কে জানে, ওরা মুচলেকা লিখে, দলবেঁধে ক্ষুধার্ত, ক্ষুধার্ত খবর, ক্ষুধার্ত প্রতিরোধ থেকে আমায় ভেন্ন করে দিলে, কেন কে জানে ! । দলটার ত্রিদিব মিত্র নাম দিয়েছিল “মুচলেকাপন্হী”, ত্রিদিব আর আলো মিত্রকেও বাদ দিয়েছিল রাজসাক্ষীরা । আমিও ১৯৬৭ সালে কেস জিতে ছেড়ে দিলুম ওদের ‘গরিব-হওয়া-ভালো’ সঙ্গ । এই হওয়া, হয়ে-ওঠা যে কি জিনিস তা আজও বুঝুনি । ১৯৬৬ সালে বাসুদেব দাশগুপ্তকে দিয়েছিলুম লেনি ব্রুসের লেখা “হাউ টু টক ডার্টি অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স পিপল” বইটা । ১৯৬৮ সালে, যখন আমি লেখালিখি ছেড়ে দিয়েছি, কৃষ্ণগোপাল মল্লিকের পত্রিকা “গল্পকবিতায়” বাসুদেব দাশগুপ্ত লিখেছিল “লেনি ব্রুস ও গোপাল ভাঁড়কে” । বাসুদেবের লেখাটা আমার পড়া হয়নি । কোনো কিছুই আর পড়তে ভালো লাগে না ।
১৯৯৪ সালে প্রথম উপন্যাস লিখলুম, “হাওয়া৪৯” পত্রিকার জন্যে, “ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস”, পাটনাইয়া বন্ধুদের নিয়ে । আমি প্রুফ দেখতে একেবারেই পারি না । দাদা কৃষ্ণগোপাল মল্লিককে বললেন প্রুফ দেখে দিতে । কৃষ্ণগোপাল ডেকে পাঠালেন ওনার বাড়িতে, বললেন, “টাকার ব্যাগটা অতনু রেখেছিল আলমারির ওপরে, বাড়ি ছেড়ে যখন চলে যাচ্ছে, তখন ব্যাগটা খাটের তলায় গেল কি করে ?” বার-বার চোখ চলে যাচ্ছিল মেঝেয়, ওনার পড়াশুনার টেবিলের পাশে মাকে চেন দিয়ে বেঁধে রেখেছেন, তিনি মাটিতে বিছানায় শুয়ে, চেন বাঁধা । বললেন, “প্রথম এসেছো তো, তাই অবাক হয়ে গেছো, আমার মায়ের খাই-খাই ব্যারাম, তাই বেঁধে রাখতে হয়ে।” শুনে, গায়ের লোম বেয়ে শিরশিরে হাওয়া বয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমহার্স্ট স্ট্রিটে এসে আচমকা ফুঁপিয়ে উঠলুম ।
ওই সময় নাগাদই এডওয়ার্ড সাইদ এসেছিলেন কলকাতায়, নেতাজি ভবনে, সৌগত বসুর ডাকে, বক্তৃতা দিতে । বক্তৃতা দিতে-দিতে সাইদ বার বার প্রতিষ্ঠানবিরিধিতার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করছিলেন । আমি বসে ছিলুম পেছনের সারিতে কেননা সামনের সারি ছিল কলকেতিয়া কেঁদোদের জন্য । আমন্ত্রিতরা, বলা বাহুল্য, সবাই ছিল কলকাতার প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার চাঁই । প্রশ্নোত্তরের সুযোগ আসতেই আমি বললুম যে, “স্যার, আপনি এতোক্ষণ প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার কথা বলছিলেন, অথচ এখানে তো সামনের সারিগুলোয় বসে আছেন পশ্চিমবাংলার তথা ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক কর্তারা ।” সৌগত বসু, আশা করেননি যে এরকম একটা প্রশ্ন কেউ ছুঁড়ে দিতে পারে । উনি তড়িঘড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন যে, “এই কনট্রোভার্সি ডিসকাস করার মতো আমাদের হাতে সময় নেই, পরের বার উনি আসলে আমরা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব ।”
চার
১৯৮৮ সালে যখন নাকতলার ফ্ল্যাটটা কিনলুম, মাত্র দু লাখ টাকায়, তখন ওই মাপের ফ্ল্যাট মুম্বাইতে কম করে হলেও পঁচিশ লাখ, তাই লোকে যেভাবে আলুপটল কেনে, কিনে নিলুম, সাত পাঁচ না ভেবে । আসলে একটুকরো পশ্চিমবঙ্গ কিনেছিলুম, চারিদিক খোলা, অথচ কোনো বাড়ি থেকে কেউই দেখতে পাবে না যে আমি অনেক সময়ে ল্যাংটো হয়ে থাকি, সলিলা চেঁচামেচি করলেও ল্যাংটো থাকতে ভাল্লাগে । বাড়ির পেছনে পলাশের জঙ্গল, গাছে-গাছে কতো রকমের পাখি যাদের অধিকাংশকে চিনি না, মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকার পক্ষী সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি পাখিগুলোর নাম কী হতে পারে, পেছনে বিশাল পুকুর, পুকুরে মাছেরা চাঁদের আলোয় ঘাই মারে, দিনের বেলায় পানকৌড়িরা মাছ খেতে নামে, উড়ে গিয়ে নারকেল গাছে জাপানি পাখার মতন ডানা ছড়িয়ে শোকায়, অনেক সময়ে পলাশের বনে শেয়াল আসে, শেয়ালের ডাক শোনা যায় রাতে, প্রচুর বেঁজি, বাড়ির সিঁড়িতে সাপ লুকিয়ে থাকে, মশারির ওপর ফ্যানের ব্লেডে লেগে জোনাকিরা ঝরে পড়ে, দূরে দেখা যায় কালবৈশাখীর মেঘ এদিকেই আসছে । হায়, সব ক্রমশ উধাও হয়ে গেল, পলাশগাছগুলো কেটে ফেলা হল, পুকুর হয়ে গেল জঞ্জাল ফেলার ডোবা, তার পাশে বাঁশের আড়ত, মেট্রো রেল এলো, বাড়ির পর বাড়ির পর দেশলাই-বাড়ি, তারপর পশ্চিমবঙ্গের পাড়া-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় হলো একটু-একটু করে, বাড়ির সামনেই, প্রথম দিনেই, কচ্ছপ কেটে বেআইনি মাংস বিক্রি, কেনার জন্য কী ভিড় আর ঠেলাঠেলি, তারপর কমরেডরা এলেন পুজোর চাঁদা চাইতে, তাদের মনের মতন না হওয়ায়, একজন হুমকি দিয়ে গেল দুর্গাপুজো-কালীপুজোয় এই বাড়ির ছাদে চারটে লাউডস্পিকার লাগানো হবে ।
মেজমাসির সঙ্গে নিমতায় দেখা করতে গেলে বলেছিলেন, “ওখানে ফ্ল্যাট কিনেছিস ? আনওয়ার শা থেকে গড়িয়া পর্যন্ত তো রিফিউজিদের জঞ্জাল-পাবলিকে ঠাশা !” মেজমাসি রিফিউজিদের ওপর চটা ছিলেন কেননা তারা ওনার পুকুর থেকে মাঝরাতে মাছ ধরে নিয়ে চলে যেতো, সুপুরিগাছ থেকে সুপুরি আর নারকেল গাছ থেকে নারকেল পেড়ে নিয়ে যেতো । মেজমাসি মারা গেছেন ; ওনাদের জমিজিরেত পুকুর আর নেই নিমতায় ; ফ্ল্যাটবাড়ি উঠেছে । ২০০০ সালে পাঁচ লাখ টাকায় ফ্ল্যাট বেচে দিলুম, পঞ্চাশ বছরের পুরোনো ফ্ল্যাট। বেচে, ১৯৮৮ সালে করা নিজের বোকামি থেকে মুক্ত হওয়া গেল । বেচার দু বছর পর গিয়েছিলুম ওই পাড়ায়, দেখলুম আর শুনলুম পাড়ার ছেলেরা ক্রেতার সঙ্গে আপোষ করতে না-পেরে বারান্দার কাচে ঢিল মেরে-মেরে ভেঙে দিয়েছে, যিনি কিনেছেন তিনি কাগজ সেঁটে রোদবৃষ্টি থামাচ্ছেন । ক্রেতা ‘সিপিএম করতেন’ ; হয়তো পালটি খেয়ে ঘাসফুলে যাননি ।
নাকতলায় অতিতরুণ কবি সুশান্ত দাশ আর কমরেড-কবি গৌতম নিয়োগী ১৯৯৫ সালে আমাকে ওদের পাড়ায় আবিষ্কার করে অবাক, হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে মেলাতে পারছিল না আমাকে, ভেবেছিল শতচ্ছিন্ন পোশাকে একজন টিংটিঙে ভবঘুরেকে দেখবে, নাকে শিকনি চোখে পিচুটি, চামড়ায় চামউকুন, চুলে মৌমাছির চাক, দেখবে বাড়ি একেবারে আঁস্তাকুড়, কাকেরা শকড়ি খুঁটে খাচ্ছে । অফিসের বদান্যতায় কেনা সিনথেটিক কার্পেট, সোফা, টিভি ইত্যাদি দেখে আরও ঘাবড়ে গিয়ে থাকবে, রাজা সরকার আর অলোক গোস্বামীর মতন । তারপর যখন অফিস-প্রধানের কাজ করতে আরম্ভ করলুম, তখন অফিসের গাড়ি নিতে আসতো আর ফিরতুম তাতে । তবে গৌতম-সুশান্তর সঙ্গে পরিচয়ের পর পাড়ার লোকে আমাকে সিঁড়ির ওপরের পাদানিতে চাপিয়ে দিয়েছিল । সুশান্তর মা ছিলেন সিপিএম সমর্থক, দেয়ালে “গণশক্তি” সাঁটা হতো প্রতিদিন । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গদিতে বসার পর বললেন, সিপিএম তো আমাদের জন্য কিছুই করল না, সেই দেশভাগের সময়ের দুবেলা দুমুঠোর দারিদ্র্যেই পড়ে আছি। ভাতের হোটেল খুলে সংসার চালাতেন, আমরাও আনিয়ে খেতুম মাঝে-সাজে, রান্নার হাত খুবই ভালো।
পশ্চিমবাংলার টেকটনিক প্লেটে যখন ধ্বস নামছিল, তখনই মুম্বাই চলে এলুম, শীতের পোশাক, বইপত্র আর আসবাব বিলিয়ে দিয়ে, গাড়িটা বেচে দিয়ে । বেচে, গাড়িকেনার বোকামি থেকে ছাড়ান পেলুম। বইপত্র নিতে কোনো লোকাল গ্রন্হাগার রাজি হল না, শেষে সপ্তর্ষি ভট্টাচার্য ওর অ্যামবাসাডর গাড়ির ডিকিতে ভরে-ভরে কয়েক খেপে নিয়ে গিয়েছিল । তারপর মা-মাটি-মানুষ করতে গিয়ে সিনডিকেটের হাতে এমন প্যাঁদানি খেয়েছিল সপ্তর্ষি যে ভেলোরে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল; কিন্তু ভেলোরের প্রভাবে এখন যিশুখ্রিস্টের গুণগান করে বেড়ায়, কেউ-কেউ বলে খ্রিস্টান হয়ে গেছে । সিনডিকেটের লোকেরা আমার দেয়া বইগুলোও অন্য বইপত্রের সঙ্গে ছিঁড়েখুড়ে নষ্ট করে দিয়েছিল । নাকতলা, শ্রীপল্লী, যাদবপুরের যে লাইব্রেরিগুলোয় বই দিতে চেয়েছিলুম, তারা টিটকিরি মেরে বলেছিল, হেঁঃ হেঁঃ, কবিতার বই, এসব কে পড়ে মশায়, আপনি একটা র্যাক দান করলেও ওসব বই রাখার জায়গা আমাদের নেই । নবারুণ ভট্টাচার্য তাই বলেছিলেন এই চুতিয়াদের ‘দেশ’ আমার নয়, উনি বোধহয় স্তালিনের সোভিয়েত রাষ্ট্রকে নিজের দেশ মনে করতেন ।
শীতের পোশাক, ডবল-ব্রেস্ট স্যুট, সিঙ্গল-ব্রেস্ট স্যুট, থ্রিপিস স্যুট, টেরিউলের প্যাণ্ট, উলের সোয়েটারগুলো, ফুলশার্ট, সবই দিয়ে দিলুম পাড়ার বিহারি ধোপাকে । বললে, উঁচু জাতের লোকেরা এগুলো আমাদের গাঁয়ে পরতে দেবে না, ওদের মধ্যে যারা একটু গরিব তাদেরই বেচবো এগুলো । বেচে আমাদের পরার মতন সোয়েটার-চাদর কিনে মা আর বউকে দিয়ে আসবো । দোকান বন্ধ করে চলে গিয়েছিল পনেরো দিনের জন্যে, পাড়ার অনেকের জামা-কাপড় প্রেস করার জন্যে বাসায় রেখে কেটে পড়েছিল
নিচেতলার ফ্ল্যাটমালিক ফণীবাবুর কাছে গ্যারেজ ভাড়া নিয়ে গাড়িটা রাখতুম ; একদিন গ্যারাজ খুলে দেখি গাড়ি থই-থই-গুয়ে ভাসছে ; নিচেতলার ভাড়াটেরা স্যানিটারি ন্যাপকিন ফেলে-ফেলে গু বেরোবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে । কর্পোরেশান বললে পার্টি অফিসে যান, কর্মিদের সেখানেই পাবেন । পার্টি অফিস যিনি সামলাচ্ছিলেন তিনি বললেন, বাড়ির ভেতরের কোনো কাজের দায়িত্ব আমাদের নয়, ধাঙড়দের দিয়ে পরিষ্কার করান, বাঁশদ্রোণী বাজারে ভোরবেলা যে ধাঙড়রা কাজ পাবার জন্যে বসে থাকে তারা বলল, ও কাজ আমাদের নয়, মেথরদের কাজ, গাঙ্গুলিবাগানে মেথর কলোনিতে গেলুম, বাসিন্দারা বলল, ওরা শুধু ম্যানহোলের কাজ করে, গুয়ের কাজ করে না । অগত্যা ডাণ্ডালাগানো দুটো সুইপার কিনে, আমি খালি গায়ে গামছা পরে, সলিলা ব্লাউজ-শায়া পরে, গুয়ের পাঁক ঠেলে-ঠেলে, তিনতলা থেকে জলের পাইপ নামিয়ে গুয়ের ইঞ্চি দুয়েক হলুদ-সবুজ-কালচে চাদরকে পথে বের করে নর্দমায় ঢোকালুম । শিবুর চায়ের দোকানে তখন বামপন্হী দর্শকের পাল, শিবু অবশ্য হাওয়া বুঝে তৃণমূলে চলে গিয়েছিল । নর্দমার মুখটা গ্যারেজের কোনেই ছিল বলে রাস্তা নোংরা করতে হয়নি । মানুষের গু ধোবার ধান্দায় সেদিন দুপুরে তো রান্না হয়নি, পার্ক স্ট্রিটে মোক্যামবোতে লাঞ্চ আর হুইস্কি খেতে গেলুম। জানি না আর কোনও সাহিত্যিকের দু-ইঞ্চি পুরু গু ধোবার অভিজ্ঞতা আছে কিনা । সেই যে হয়ে-ওঠা, এটা বোধ হয় মহাপুরুষ আর মহানারী হয়ে ওঠায় উত্তরণ ।
নাকতলার লেটারবক্স পাড়ার আরেকটা ঝামেলা ছিল যখন-তখন মোহোল্লা কমিটির এক কমরেড ক্লাবের মাঠে তাঁবু খাটিয়ে, ভিয়েন বসিয়ে, লাউডস্পিকার লাগিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অনুকুল ঠাকুরের শিষ্যদের দিয়ে বিটকেল বেসুরো গান গাওয়াতেন, খাবার জন্যে কি-ভিড় কি-ভিড়, তারপর মাঠময় স্টায়রোফোমের এঁটো থালা । এই গডম্যান জিনিসটা কিছুতেই বুঝতে পারি না ; যতোগুলো গডম্যানের কথা শুনি সকলেই তো পিঁজরেপোলের মালিক । বিজেপি এসে গডম্যানদের আর দ্যাখে কে ! মাঠের মাঝখানে একসময় পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের লেটারবক্স ছিল বলে পাড়াটার নাম লেটারবক্স, কোনো এক সময়ে মাঠের একপাশে কেবল আমাদের বিল্ডিঙটাই ছিল । হাংরি আন্দোলনের সুবো আচার্য গডম্যানের ওই প্রাতিষ্ঠানিক পিঁজরেপোলে ঢুকে চোপোররাত্তির অনুকুল ঠাকুরের গুণগান করে বেড়ায় । সুবোর বাড়ি বিষ্ণুপুরে গিয়েছিলুম আমি সুবিমল আর ত্রিদিব, তখন ও ত্রিপুরার গোপন ডেরা থেকে ফিরেছে, কেননা আমার বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়ে গেছে, সে ছিল এক ভিন্ন সুবো আচার্য, বিষ্ণুপুরে ঘোরাঘুরি করে ধানখেতের ভেতর দিয়ে ল্যাংটোপোঁদে চারজনে একটা নদী পার হয়েছিলুম মাথায় পোশাক চাপিয়ে, গাছতলায় ল্যাংটোপোঁদে চারজনে গাঁজা টেনেছিলুম । এখন সুবো অনিশ্চয়তাকে এতো ভয় পায় যে কথায় কথায় গুরুদেব গুরুদেব ভজন গায় অথচ আগে ওর গুরুদেব ছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় । “সুনীল বলেছে মলয় লিখতে জানে না”, সেকথা জানিয়েছিল আমাকে। প্রদীপ চৌধুরী বলেছিল, ওটা সুবো আচার্যের ডিএনএতে রয়ে গেছে, গুরু, মন্ত্র, মনুসংহিতা, রক্ষণশীলতা ইত্যাদি, বংশানুক্রম অবদান ।
পাঁচ
নাকতলায় একদিন টেলিফোন পেলুম, “মলয়, আমি উদয়ন বলছি, উদয়ন ঘোষ, আপনাদের পাড়ায় এসে গেছি, রিকশঅলাকে বলবেন ট্রান্সফরমার স্ট্যাণ্ড” । ২০০১ সালে আমার ছোটোগল্প নিয়ে একটা প্রবন্ধে উদয়ন লিখেছিলেন, “যত দিন যাচ্ছে, মলয়ের লেখা যত পড়ছি, ততই মনে হচ্ছে, তাঁকে নিয়ে মহাভারত লেখা যায়।” তখনও পর্যন্ত ওনার সঙ্গে আমার সামনাসামনি দেখা হয়নি । ভাবলুম, যাক, কেদার ভাদুড়ির মতন আরেকজনকে পাড়ায় পাওয়া গেল মোদো-আড্ডা দেবার জন্য । একটা পিটার স্কটের বোতল কিনে হাজির হলুম, দেখি উদয়ন শয্যাশায়ী, মন খারাপ হয়ে গেল । আমায় দেখে বিছানা থেকে ধড়মড় করে উঠতে যাচ্ছিলেন, বারন করলেন ওনার স্ত্রী । হাঁপানিতে ধরেছে, লিখতে পারছেন না বলে ডিপ্রেশান, নানা রকম যন্ত্রপাতি ওনার বিছানা ঘিরে। আড্ডা হল কিছুক্ষণ, আমি যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে বই ছাপাবার টাকা দিয়েছিলুম, উনিও দিয়েছিলেন, আমাদের দুজনের একই অভিজ্ঞতা । মাঝে-মাঝে যেতুম, উনি শয্যাশায়ী । ওনার আর শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আর শান্তি লাহিড়ীর একই অবস্হা, পঞ্চাশ দশকের তিনতিকুড়ি কবি-লেখকদের সঙ্গে চিপকে থেকে গর্ব বোধ করার দরুন নিজের লেখার সময় দুমড়ে ছোটো করে ফেলতে হয়েছিল । একদিন উদয়নের মেয়ের টেলিফোন পেলুম যে মারা গেছেন ।
২০১৪ সালে যখন “নখদন্ত” বইটার নতুন সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন কাকে দিয়ে করানো হবে জানতে চাইলেন গুরুচণ্ডালীর কর্ণধার ঈপ্সিতা পাল, আমি বলেছিলুম, বইমেলায় যারা জিনিসপত্র ফিরি করে বেড়ায়, তাদের কাউকে দিয়ে । তেমনই একজনকে দিয়ে করিয়েছিলেন উনি । কলকাতায় থাকতে তরুণ কবিদের দেখেছি আগের দশকের কোনো টাকমাথা বা চুলে কলপদেয়া কাঁধে-চাদর কবি বা লেখককে দিয়ে “মোড়ক উন্মোচন”এর অনুষ্ঠান করিয়ে গদগদ হন, যেন ফুলশয্যায় কনডোমের প্যাকেট খোলাচ্ছে । আমার মনে হতো এইসব তরুণ কবি সারাটা জীবন অন্যের চিন্তাজগতে বসবাস করে কাটাবে, বেঁচে থাকার চারিদিকে যে সন্ত্রাস আর নোংরামি, তার সঙ্গে এদের পরিচয় হবে না কখনও । একজন ফিরিঅলাকে দিয়ে বইয়ের “মোড়ক উন্মোচন” করিয়ে কী যে আনন্দ কী বলব ।
১৯৯৬ সালে নাকতলায় বেশ আনন্দ হয়েছিল পাটনার এক ফুচকাঅলাকে দেখে, ফুচকা ভেজে, মশলা নিয়ে রোজ ময়দানে বিক্রি করতে যেতো । “পাটনাইয়া ফুচকাই বেচো, নাকি মশলায় অদল-বদল ঘটিয়েছো?” জিগ্যেস করতে বলেছিল, মিষ্টি সামান্য বেশি খায় বাঙালিরা, বাদবাকি পাটনাইয়া, পুরো কলকাতায় যতো ফুচকাঅলা আছে সবাই ভোজপুরি, বিহার আর পূর্ব উত্তরপ্রদেশের, তাই যতো ফুচকা বিক্রি হয় সব পাটনাইয়া । আমাকে কেউ যদি জিগ্যেস করে আপনার কী খেতে সবচেয়ে ভালো লাগে, তাহলে আমি ইলিশ-চিংড়ির কথা বলব না, ফুচকার কথা বলব । ফুচকায় আইরিশ ক্রিম ভরে খেতে দারুণ । যদি আমিষের কথা জিগ্যেস করে কেউ তাহলে বলব যে সুইডেনের আইকিয়ার মিট বল খেতে সবচেয়ে ভালো লাগে, গোরু-শুয়োরের মাংসকে জানিনা কী ভাবে স্পঞ্জের মতন নরম করে তোলে, এক ইউরোতে দশটা মিট বল, এক প্লেট আলুভাজা, একটা তিনকোনা প্যাসট্রি আর কফি, প্রতি রবিবার সকালে, আহা, আহা, আহা, তারপর আর লাঞ্চ করার প্রয়োজন হয় না । তবে ইউরোপের মাংসের প্রিপারেশন ভালো লাগে না, মনে হয় কাঁচা, অনেক সময়ে রক্ত বইতেও দেখেছি প্লেটের ওপর । হাংরি আন্দোলনের সময়ে শৈলেশ্বর ঘোষ আর সুভাষ ঘোষ গোরুর মাংস খেতে চাইত না, বেঁচে থাকলে বিজেপি দলের কর্মী হতে পারতো ।
১৯৬৬ সালে অনিল করঞ্জাই আর করুণানিধান মুখোপাধ্যায়কে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে দরিয়াপুরে আমার ঘরে একটা পেইনটিঙ তৈরি করে রেখেছিলুম ওরা দুজনে কাঠমাণ্ডু থেকে ফিরলে দেখাবো বলে, নাম দিয়েছিলুম “পেইনটিঙের ভাষাকে আক্রমণ” । কাজটা ছিল একটা সাদা কার্ডবোর্ডে আমার নুনুর চারিপাশের জমানো বাল, যাকে হিন্দিতে বলে ঝাঁট, আঠা দিয়ে সেঁটে তৈরি আমার আত্মপ্রতিকৃতি । ওরা দুজনে দেখেই থ, করুণা বললে, “শালা একেবারে ক্লাসিকাল আর্ট, যেন ইউলিসিস, বেনারস নিয়ে যাবো, হিপিগুলো দেখেই লেড়িয়ে যাবে, দশ-পনেরো ডলারে ঝেঁপে দেবো, বুঝলে, তোমার ইন্সটলেশান আর্ট পৌঁছে যাবে ইউউউউউ এসসসসসস এএএএএএএএ”। করুণা চুলগুলোতে উপযুক্ত রঙ লাগিয়ে মুখকে আকর্ষক করে তুলল । ওদের সঙ্গে আমিও গেলুম বেনারস, কোর্টে কেস কবে উঠবে ঠিক নেই, সুবিমল বসাক যোগাযোগ রেখেছে হাইকোর্টের অ্যাডভোকেটের সঙ্গে । বেনারসে যাবার লোভ করুণাই দেখিয়েছিল, “গাঁজা-চরস-আফিম মিশিয়ে চারমিনারে পুরে ফোঁকো আর হিপিনীসেক্স করো, একজন মোটা হিপিনী আছে, যাকে কেউ সঙ্গিনী করতে চায় না, এক ব্যাটা হিপি তাকে বেনারসে ছেড়ে আরেকজনকে নিয়ে চলে গেছে, তাকে পাইয়ে দেবো, অনিল ওর নিউড আঁকতে ডাকবে, তখন চাক্ষুষ করে নিও।” দেখলুম মোটা হিপিনীকে, ম্যাডেলিন করিয়েট, পোশাকহীন, ঝলমলে হলুদ আলোয়, অনিলের স্টুডিওতে, আর আবার শুরু হল আমার লুচ্চাপ্রেমিক অ্যাডভেঞ্চার, “অরূপ তোমার এঁটোকাঁটা”। করুণা তিরিশ বছর আগে, অনিল দশ বছর আগে মারা গেছে।
১৯৪৭ সাল থেকে, কী খাবো আর কী খাবো না তা প্রকাশ করার স্বাধীনতা আমিও নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলুম । কুমড়ো, ঝিঁঙে, ধুঁধুল, কুচোপোনা, মৌরলা, ট্যাঙরা, বিউলির ডাল আমি ইমলিতলায় খেতুম না । দরিয়াপুরে রান্নার বউ রাখলুম ১৯৭০ সালে আর সবকিছুই খাওয়া আরম্ভ করলুম, কেননা রান্নার বউ ছিল বরিশালের আর আমি তাকে বলতুম ধুঁধুলে গোটা মশলা দাও আর কিমা দিয়ে রাঁধো, কুমড়োয় হিং ফোড়ন আর প্রচুর টোম্যাটো দাও, ঝিঁঙেতে রসুন দাও আর কাবলি ছোলা বাটা, বিউলির ডালে আস্ত রসুনকোয়া, বড়ি আর পালংশাক। সেই থেকে রান্নার রেসিপির একটা বই লেখার পরিকল্পনা মাথায় ঠাঁই করে নিয়েছে । ঠাকুমা ঠিকই বলতেন যে রান্নায় উচিত মশলা দিতে জানলে পাথরের টুকরোর তরকারিও খাওয়া যায় । আমি আসলে বেশ পেটুক । নোলা-সকসকে মানুষ বলতে যা বোঝায়। খিদে না থাকলেও ভালো খাবার দেখলে বা স্কচ বা সিঙ্গল মল্ট দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে । খিদে ব্যাপারটা মনের স্হিতি, পেটের নয়।
ছয়
১৯৭৯ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে সিনিয়ার অ্যানালিস্ট হিসেবে অ্যাগ্রিকালচারাল রিফাইনান্স অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশানের লখনউ দপতরে যোগ দিয়ে কয়েকদিন স্টেশানের কাছে হোটেলে ছিলুম আর প্রতিদিন রাতে ওল্ড মংক খেয়ে পাঞ্জাবি সরদারের দোকানে পুরো চিকেন তন্দুরি খেতুম কুড়ি টাকায় । আরও চারজন সিনিয়ার অ্যানালিস্ট, সকলেই ধনী চাষিবাড়ির কৃষি-বিজ্ঞানী, আবদুল করিম, শেট্টিখেড়ে প্রভাকর, ডক্টর কুরকুটে আর মদন মোহন যোগ দিলে, যতোদিন না বাড়ি পাচ্ছি, আমাদের থাকার ব্যবস্হা হল উত্তরপ্রদেশ ভূমি বিকাশ ব্যাংকের গেস্ট হাউসে । রান্নার ব্যবস্হা নিজেদের। প্রভাকর সম্পুর্ণ শাকাহারি, পেঁয়াজ রসুনও খায় না, আর করিমের আমিষ না হলে চলবে না । সিদ্ধান্ত হল একদিন প্রভাকর রাঁধবে একদিন করিম । আমরা বাসন মাজবো, ঝাড়ু দেবো, পোঁছাপুছি করব চারটে ঘর আর ড্রইং রুম । এই চাকরিতে প্রথমেই যেতে হয়েছিল হিমালয়ের তরাইতে আর্টেজিয়ান কুয়োগুলোকে কাজে লাগাবার প্রজেক্ট তৈরির কাজে, তার আগে জানতুম না যে মাটির তলা থেকে কনকনে ঠাণ্ডাজল আপনা থেকে ফোয়ারার মতন বেরোতে থাকে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চাকরিটা না ছাড়লেই ভালো হতো ; ষাট হাজার টাকা পেনশন বেশি পেতুম ।
করিমের মাংস রাঁধা দেখে আমাদের মাংস খাওয়া টঙে উঠল । মাংস কিনে এনে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জলে ভিজিয়ে রাখত যাতে শেষ রক্ত ফোঁটাও বেরিয়ে যায়, তবুও খেলুম মাংস, তাতে সজনে ডাঁটা মুলো বেগুন দেয়া । মাংসের সাম্বর, হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি আর হালিম রাঁধা অন্ধ্রের আবদুল করিমের কাছে শিখলুম । ওকে তারিফ করে হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি আর হালিম রাঁধায় টেনে নিয়ে গিয়ে আমাদের স্বস্তি । মুর্গি কিনে এনে করিম তাকে উনুনে ঝলসে নিতো যাতে রক্তের রেশ না থাকে । আর তার ফলে গ্যাসের উনুন থেকে আগুন বেরোনো চৌপাট হয়ে যেতো । অবসর নেবার পর নাভি পর্যন্ত পাকা দাড়ি নিয়ে করিম পাঁচবেলা নামাজ পড়তো, অন্ধ্রের গ্রামে একটা বাড়ি করেছিল সাতটা ঘরের, বিশাল বাংলো, ভেবেছিল বউ আর নাতিপুতি নিয়ে থাকবে, তা বউটাই মারা গেল ক্যানসারে । একটাই ছেলে হাসন্যায়েন হিন্দু মেয়ে বিয়ে করে থাকতে চায়নি বাপের সঙ্গে । লখনউ থাকাকালে করিম যেখানেই ট্যুরে যেতো, আমার ছেলের জন্য কোনো উপহার সেই জায়গা থেকে আনতো, নাকতলার ফ্ল্যাট বেচার সময়ে সবই পাড়ায় বিলি করে দিতে হয়েছে ।
প্রভাকর ব্রেকফাস্টে দোসা সাম্বর বা ইডলি বানিয়ে দিতো । দোসা ইডলি আর সাম্বর বানাতে শিখে গেলুম, শিখে ফেলার পুরস্কার হিসেবে ও কর্ণাটকে নিজের গ্রাম থেকে একটা দোসা বানাবার চাটু এনে দিয়েছিল, যা এতো ভারি যে এখন আর তুলতে পারি না । তিন মাস পরে ইন্দিরানগরে বাংলোবাড়ি পেয়ে নতুন আস্তানায় গিয়ে পাটনা থেকে সলিলা, ছেলে-মেয়ে আর জিনিসপত্র নিয়ে এলুম । যে বাংলো পেয়েছিলুম, তাতে প্রচুর সাহায্য পেলুম চার কৃষি বিজ্ঞানী বন্ধুর, নিজে চাষ করার, বাগান করার, এমনকি ঘাস লাগাবার। আর প্রচুর বই, চাষবাসের বই, কিছুই জানতুম না আগে । সেই থেকে আমার মস্তিষ্ক হয়ে গেছে ক্যালাইডোস্কোপিক । নতুন চাকরিটাও এমন যে গ্রামে-গ্রামে চাষের উন্নতির রিপোর্ট দিতে হতো । গোরু, ছাগল, মোষ, বলদ, ষাঁড়, শুয়োর, হাঁস, মুর্গির যে কতো রকম প্রজাতি হয় সেই প্রথম জানলুম । মোষ-ষাঁড়-শুয়োরের সিমেন বের করার টেকনিক, সেই সিমেন মাদিদের যোনিতে পোরার টেকনিক, দেখতে দেখতে বেশ উত্তেজনা হতো । তার আগে তো দূর থেকে বাজরা আর জোয়ার খেতের তফাত টের পেতুম না।এই নতুন চাকরির দরুন সাহিত্যের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল । পাটনায় থাকতে তো চাষবাসের কিছুই জানতুম না, একটা গাছে এলাচ কোথায় হয় তা জানতুম না ।
১৯৫০ সাল থেকেই ঠাকুমা গরমকালে কেবল একটা গামছা কোমরে জড়িয়ে উত্তরপাড়ার খণ্ডহরে ঘুরে বেড়াতেন, ভাড়াটেদের সঙ্গে গ্যাঁজাতেন, ওনার মাইদুটো শুকিয়ে আমসি হয়ে গিয়েছিল । যখনই যেতুম কিংবা ঠাকুমা পাটনায় আসতেন, বলতুম, “তোমার মাই নিয়ে খেলবো” । ঠাকুমার মাইয়ের বোঁটা দুটো দুহাতে ধরে জুড়ে ছেড়ে দিতুম আর বলতুম, “ঝমমমম”। ঠাকুমা বলতেন, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে তোর, “এবার বে-থা কর আর বউয়ের মাই নিয়ে ঝম ঝম কর দিকিনি।” বলতুম, “বউয়ের মাই তো আর তোমার মতন হবে না যে এক বোঁটার সঙ্গে আরেক বোঁটাকে মেলাবো।” ঠাকুমা বলতেন, “আমার মাইও এককালে তোর বড়োজেঠিমার চেয়ে পেল্লাই ছিল, বুঝেছিস, তোর দাদুর কতো গর্ব হতো।” ঠাকুমা মারা যাবার চার বছর পরে বিয়ে করলুম, নয়তো ওনাকে বলতুম, আমিও আমার বউয়ের মাই নিয়ে গর্ব করি , তোমাকে দেখাতে বলব একদিন ।
২০১০ সালে মালাডের ইনঅরবিট মলের ফুড কোর্টে বসে অপেক্ষা করছিলুম এক দম্পতির, সেদিন তাদের বিবাহবার্ষিকী, খাওয়াবে বলে কয়েকজনকে ডেকেছে । প্রায় সকলেই পৌঁছে গিয়েছিলুম । একজন যুবতী এগিয়ে এলো আমার দিকে, দুহাতে বিয়ের মেহেন্দি, এক হাতে প্লাস্টিকের চালুনি, আরেক হাতে বাঙলা পাঁজি আর দামি ব্যাগ । ইংরেজিতে আমাকে বলল, স্যার আপনাকে বাঙালি বলে মনে হচ্ছে, আমি এই ফোরটিন গ্রিনস কিনতে বেরিয়েছি কিন্তু কোথাও পাচ্ছি না, ক্রফোর্ড মার্কেটেও পাইনি; আপনি কাইন্ডলি বলতে পারবেন কি যে এই গ্রিনগুলো কোথায় পাবো ? জিগ্যেস করে জানলুম ও কানপুরের মেয়ে, বিয়ে করেছে বাঙালি যুবককে, শশুর-শাশুড়িকে ইমপ্রেস করার জন্য চোদ্দশাক খুঁজে বেড়াচ্ছে । চালুনিটা করওয়া চৌথের জন্যে । পাঁজি খুলে দেখলুম শাকের নাম দেয়া আছে, ওলপাতা, কেঁউ, বেতো, সরিষা, কালকাসুন্দে, নিম, জয়ন্তী, শাঞ্চে, হিলঞ্চ, পলতা, শৌলফ, গুলঞ্চ, ভাটপাতা আর সুষণী । বললুম, এই ফোরটিন গ্রিনসের কথা আমি নিজেই আগে জানতুম না, আমাদের বাড়িতে যে চোদ্দশাক হতো তাতে পালংশাকের সঙ্গে নটে, ধনে, সোয়া, লাউ, কুমড়ো, পালং, কলমি, যার কোনোটাই এই লিস্টে নেই । আমার স্ত্রী যুবতীটিকে বলল, পালংশাক কিনে নাও আর যা-যা গ্রিনস পাওয়া যাচ্ছে কিনে নাও আর তা শ্রেডিং করে রেঁধো, তোমার ইনলজ আনন্দিত হবেন । নিজেরা যে বাঙালিত্ব ছেড়ে দিয়েছি একজন অবাঙালী যুবতীকে তা করতে দেখে, করুণার ভাষায়, লেড়িয়ে গেলুম ।
মুম্বাই থেকে ফিরে সুভাষ ঘোষের বাড়ি চন্দননগরে গিসলুম ১৯৯৬ সালে, বহুকাল পর দেখা করার ইচ্ছে দমিয়ে রাখতে পারিনি বলে, স্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখি সিপিএম-এর মিছিলে ঝাণ্ডা নিয়ে স্লোগান দিতে-দিতে যাচ্ছে সুভাষ ঘোষ, মন খারাপ হয়ে গেল । ওর বাড়ি গিয়ে দেখি বারান্দার এক কোণে সিপিএম-এর ঝাণ্ডার স্তুপাকার গোছা, ভেতরের ঘরে দেয়ালে ঝুলছে জ্যোতি বসুর ছবি, মনে হল ওর বাড়ি আসা বড্ডো ভুল হয়ে গেছে । প্রতিষ্ঠানবিরোধী ঢুকে গেছে প্রতিষ্ঠানের খাঁচায় । অবশ্য যখন ও মুচলেকা দিয়ে আমার বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হয়েছিল, তখনই হদিশ পেয়েছিলুম যে ও একা লড়তে ভয় পায়, ওর চাই মিছিলের আশ্রয়, ওর চাই কফিহাউসের তরুণদের জমঘট । বলল, “মফসসলে থাকলে বুঝতে এসব না করে টিকে থাকা কতো কঠিন”। নিজের বউ কণক ঘোষকেও হাংরি আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছে, যদিও কণক ঘোষের লেখার স্তর বাচ্চাদের । এদিকে সিপিএমের লুম্পেনরা তখন গ্রামে-গ্রামে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাচ্ছে, বাড়ি-ধানের গোলা পোড়াচ্ছে, মুণ্ডু নিয়ে ফুটবল খেলছে, পেট্রল ঢেলে মানুষ পোড়াচ্ছে, মানুষদের জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে দিচ্ছে, সুভাষের লেখায় তাদের দেখা মেলে না।
মুম্বাই থেকে ফিরে ১৯৯৫ সালে প্রদীপ চৌধুরীর বাড়ি গিসলুম, দাদাকে আমাকে সলিলাকে শ্যাম্পেন খাওয়াবার নেমন্তন্ন করেছিল, শুনেছিলুম ফি বছর ফ্রান্সে কবিতা পড়তে যায় । শ্যাম্পেনের বোতলে ভরে দিশি বাংলা খাওয়ালো, ভেবেছিল আগে শ্যাম্পেন খাইনি কখনও । বহুকাল পর পুরোনো প্রদীপকে পেয়ে গেলুম, দেশ-বিদেশ ঘুরেও টসকায়নি, দি সেম ওল্ড কুমিল্লা ব্লোক, জিভের আড় ভাঙেনি । “হাওয়া ৪৯” পত্রিকায় প্রদীপ সম্পর্কে একটা লেখা লিখেছিলুম, প্রদীপের রাস্টিকেশানের যাবতীয় ডকুমেন্টসহ, প্রদীপ বলেছিল আমার গদ্যটার মতন আর কেউ ওকে বিশ্লেষণ করতে পারেনি । কিন্তু মুচলেকাপন্হীরা ওকে একঘরে করে দিতে পারে এই ভয়ে, লেখাটার সঙ্গে দেবার জন্যে একটা ফোটো তুলিয়ে দিয়ে গেল, যেন আমাকে লাথি দেখাচ্ছে । ওই ফোটোসহ ছেপে দিয়েছিলুম গদ্যটা । জানি না রাজসাক্ষীদের ও কেন এতো ভয় পেতো । তাদের অন্তর্ধানের পর পুরোনো প্রদীপ খোলোশ থেকে বেরিয়ে এসেছে । অভিমন্যু সিংহের সাইটে ইনটারভিউ দিয়ে যে ফোটো দিয়েছে তাতে প্রদীপের গলায় ঝুলছে বিজেপির পদ্মফুল ।
মুম্বাই থেকে ফিরে ১৯৯৬ সালে শৈলেশ্বর ঘোষের বাড়ি গিসলুম, বেশ অনেকখানি জায়গা নিয়ে বাড়ি, পাঁচিলের গা ঘেঁষে দেবদারুর সারি বসিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পত্রিকার মলাটে ভিকিরির ছবি কেন, জিগ্যেস করতে বলল, ‘পাতা ফুঁকবে নাকি’ । আলমারি জুড়ে কেবল নিজের বই, সারি-সারি । মারা গেল অপারেশান থিয়েটারে । একে-একে মারা গেল ওর বউ, জামাই, মেয়ে । কিন্তু প্রচুর এনটিটি পয়দা করে গেছে ওর লেখাপত্তর সামলাবার ।
আমি তো চিনতুম না, তাই প্রদীপ চৌধুরী বলেছিল শৈলেশ্বরের বাড়ি নিয়ে যাবে । যেদিন যাবার সেদিন গাপ মেরে শৈলেশ্বরকে আগাম খবর দিয়ে এলো, যাতে ও তৈরি থাকে। আমি আর দাদা ওর অপেক্ষায় গড়িয়ার বাস ডিপোয় দাঁড়িয়ে রইলুম ঘণ্টা দুয়েক । পরের দিন নিয়ে গিয়েছিল । মারা যাবার কয়েকদিন আগে শৈলেশ্বরের মেয়ে জীজা ঘোষ চিঠিতে প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছে যে, যে-পত্রিকায় মলয় রায়চৌধুরী আর সমীর রায়চৌধুরীর লেখা থাকবে তাতে যেন ওর বাবার লেখা প্রকাশ না করা হয় । মন্দ নয়, মারা যাবার আগে মুচলেকা-লেখক মেয়েকেও রাজসাক্ষ্যের দুর্গন্ধ মাখিয়ে যেতে পেরেছে। বেচারি । অনেক বকাসুর চেহারার অ্যাণ্ডাবাচ্চাও ছেড়ে গেছে আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করার জন্য।
মুম্বাই থেকে ফিরে ১৯৯৬ সালে অবনী ধরের গল্পগুলো নিয়ে একটা বই যাতে বেরোয় তার চেষ্টা করলুম । বাসুদেব, সুভাষ, শৈলেশ্বর, প্রদীপ কেন যে অবনী ধরের গল্পগুলো নিয়ে বই করতে চায়নি জানি না। অবনীও, সোনাগাছিতে বাসুদেবের সঙ্গে গিয়ে বেবি-মীরা-দীপ্তির সঙ্গে শোবার আর ধেনো টানার খরচাপাতি করেছে, বই বের করার কথা ভাবেনি । অবনীর বই বের করার প্রস্তাবটা দিতেই রাজি হয়ে গেল শর্মী পাণ্ডে, আমি একটা ভূমিকা লিখে দিলুম । বাচ্চা হচ্ছে না বলে শর্মী পাণ্ডের তখন বেজায় মন খারাপ, নানা হাসপাতালে নানা টেস্ট করিয়ে চলেছে, বেশ ব্যস্ত । তা সত্বেও আগ্রহ নিয়ে বের করে দিল বইটা । অবনী ধর এক কপি দিতে এসেছিল আমায়, বলল বইটার নাম “ওয়ান শট” এর বদলে “ওয়ান সট” হয়ে গেছে। বললুম শর্মীও বোধহয় আমার মতন ঘটি । বইটা বের করার পূণ্য হিসেবে একটা সুন্দর বাচ্চা পেয়েছে শর্মী, নাম রেখেছে “রূপকথা” । দারুণ । অবনী ধর যে মারা গেছে তা ওর ছেলের টেলিফোনে জেনেছিলুম।
সাত
১৯৪৪ সালে ইমলিতলার গঞ্জেড়িরা কেউই বিশ্বাস করতে চায়নি যে ধবধবে শাদা শুয়োর হয় আর তার মাংস খেতে দিশি কালো শুয়োরের চেয়ে ভালো, ওরা ভেবেছিল আমি ইয়ার্কি করছি, “হাঃ হাঃ হমনিকে বুড়বক সমজ লইল কা ববুয়া” । আমি তাই আর ওদের ভুল ভাঙাইনি যে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে না ; জানি ওদের নাতিরা স্কুলে যেতে আরম্ভ করলে পাকা ভুরু কুঁচকে বসে থাকবে ।
১৯৬৫ সালে বেনারসে আমার “জখম” কবিতার হিন্দি অনুবাদ, যা কাঞ্চনকুমার করেছিল, তা লুকিয়ে সরকারি প্রেসে ছাপানোর ব্যবস্হা করে দিয়েছিলেন হিন্দি আর মৈথিলি ভাষার কবি নাগার্জুন । বাঁধানো অবস্হায় বইটা হাতে নিয়ে দেখলুম সাজাবার সময়ে কবিতার লাইন একেবারে ওলোট-পালোট হয়ে গেছে । এই-ই হল আমার কবিতার ফর্ম, বললুম নাগার্জুনকে, যেখান থেকে ইচ্ছে লাইন তুলে যেখানে চান বসিয়ে নিন, টোটাল কবিতায় কোনো হেরফের হবে না, আপনার বৌদ্ধধর্মের চত্বারি আর্যসত্যানি দুঃখই তো কবিতাটার বনেদ । ১৯৯৮ সালে মারা গেছেন নাগার্জুন ।
১৯৯৯ সালে ঈশ্বর ত্রিপাঠী এসেছিলেন নাকতলার ফ্ল্যাটে, একহাজার টাকা নিয়ে, আমাকে পুরস্কৃত করতে চান, ‘প্রমা’ পত্রিকায় প্রকাশিত আমার “উত্তরদার্শনিকতা” প্রবন্ধ পড়ে এতোই অভিভূত । আমি পুরস্কার নিই না বলে ওয়ান-টু-ওয়ান পুরস্কার দিতে এসেছিলেন, যাতে কেউ জানতে পারবে না, অথচ পুরস্কারও দেয়া হবে । টাকার তোড়াটা উনি সোফার কুশনের তলায় রেখে চলে যেতে চাইছিলেন । বললুম, আমি তো রামকৃষ্ণ নই, বইবাজারের কেষ্টবিষ্টুও নই, লেখার জন্যে পুরস্কার নিই না, সম্বর্ধনা নিই না । উনি মুষড়ে পড়লেন, তুলে নিলেন টাকাটা আর কোনো কথা না বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন । ওনার মৃত্যুর খবর পেয়েছি বেশ দেরিতে । “কবিতা পাক্ষিক” পত্রিকার প্রভাত চৌধুরীও সম্বর্ধনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আবার বলতে হল যে, আমি এই সবেতে নেই । হয়তো ওনার পছন্দ হয়নি ; তারপর থেকে ওনার পত্রিকায় আমার লেখা ছাপা হয় না ।
ইমলিতলার গঞ্জেড়িদের জমায়েতে ইঁদুর পুড়িয়ে খাওয়া হতো ; ১৯৪৫ সালে আমি পুরোটা খাইনি, বমি করে ফেলব আঁচ করে, তবু একটুকরো মুখে দিয়ে চেখেছিলুম, বিটকেল সোঁদা গন্ধ, চেখে বমি করলুম । দাদা খেয়ে দেখেছিল, তাড়ি দিয়ে । তাড়ি আর ঠররা খাবার ট্রেনিঙ তো ইমলিতলায় । এখন যারা থাকে তারা হয়তো আংরেজি শরাব খায় ।
১৯৬২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহকর্মী শিউচন্দরের বাড়িতে ওর গ্রাম ছপৌলিতে গিয়েছিলুম। ওদের অনেক জমিজিরেত, ছাগল বলদ গোরু মোষ ঘোড়া । আমায় একটা ঘোড়ানীর পিঠে বসিয়ে, ঘোড়ানীর পিঠে জিন ছিল না, ঘোড়াটাকে শিস দিয়ে ওরা নিয়ন্ত্রণ করছিল, আমার লিঙ্গের তলায় ঘষটানি লেগে দাঁড়িয়ে গেল, ব্যাটারা জানতো কি হতে চলেছে, তাই শিস দিতে থাকলো, আর আমার বীর্যপাত ঘটা আরম্ভ হলে ঘোড়ানীর গলা জড়িয়ে ধরলুম, ঘোড়ানীর সঙ্গে এভাবে প্রেম করে ব্যক্তিগত প্রেমের ইতিহাস তৈরি করলুম। শিউচন্দর মারা গেছে কুড়ি বছর আগে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে দিতে হয়েছিল নোটের বিষাক্ত গন্ধ আর ছোঁয়াচে রোগের জন্য ।
রাতে শিউচন্দরদের বারদেউড়ির যে ঘরে আমাকে শুতে দিয়েছিল, হঠাৎ তার মধ্যে একজন বিহারি যুবতীকে ঠেলে দিয়ে শিউচন্দরের বাবা বললে, “লে রে ববুয়া, দেশি ঘোড়ি পর চঢ়” । মেয়েটার গন্ধে আমার হাড়-হিম করা ভয় দেখা দিল, দরোজা খুলে বললুম, যাও এক্ষুণি পালাও । ভিতু ছিলুম বেশ । যৌনকর্মে নারীও ভীতির কারণ হতে পারে ।
১৯৮৯ সালে মুম্বাইতে ফিয়াট গাড়ি কিনেছিলুম অফিস থেকে লোন নিয়ে । ড্রাইভ করতে বেরিয়ে রিভার্স করার সময়ে একটা ট্রাককে ধাক্কা মারলুম, গাড়ির পেছন দিক চুরমার । ডিলারের কাছে নিয়ে যেতে, বলল, প্রথম গাড়ি কিনে ড্রাইভ করতে বেরিয়ে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোক অমন দুর্ঘটনা ঘটায়, আপনার ভাগ্য যে সামনে থেকে কাউকে ধাক্কা মারেননি ।
১৯৮৯ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত সান্টাক্রুজের ফ্ল্যাট থেকে নারিমন পয়েন্ট পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সকালে আধ ঘন্টায় পৌঁছে যেতুম, মেরিন ড্রাইভে বসে হাওয়া খেতুম । নানা জায়গায় বেড়াতে যেতুম । এখন মুম্বাইতে এতো গাড়ি যে চালানো অসম্ভব, এখন সান্টাক্রুজ থেকে নারিমন পয়েন্ট যেতে তিনচার-ঘণ্টা লাগে। ১৯৯৫ সালে কলকাতায় গিয়ে গাড়ি চালাতে বেশ মুশকিল হতো কেননা নাকতলায় থাকতুম গলির ভেতরে আর সিপিএম দলের পাবলিক রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গ্যাঁজাতো, গাড়ি দেখেও সরে যেতো না, কেউ-কেউ বলতো, “বাঞ্চোৎ গাড়ি দেখাতে এসেছে”, অর্থাৎ রিফিউজিদের মার্কসবাদ ব্যাখ্যা, এরাই পুরো পশ্চিমবাংলাকে ডুবিয়ে দিয়েছে ; লোকগুলো বুঝতেই পারেনি যে কিছুদিনেই গদি থেকে উৎখাত হয়ে যাবে । প্রায়ই ক্লাচ খারাপ হতো । বেচে দিলুম গাড়ি ।
২০০০ সালে নাকতলার ফ্ল্যাটও বেচে দিলুম, এমনই একজনকে যে নিজের নামের মাঝখানে “হার্মাদ” লিখে সিপিএম করতো । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গদিতে বসতেই, সাঙ্গোপাঙ্গোদের নিয়ে তৃণমূলে পালিয়েছে । বললুম, কি, শেষ পর্যন্ত হার্মাদকে হমদর্দ করে ফেললেন, তৃণমূলে যোগ দিলেন ; প্রত্যুত্তরে উনি হেঁঃ হেঁঃ দিয়ে নিজের ক্ষুদ্রতা মুখময় ছড়িয়ে দিলেন । বিল্ডিংটা ছিল পঞ্চাশ বছরের পুরোনো ।
২০১৬ সালের ঘটনা, আরেকজন হার্মাদকে নিয়ে, তিনি চিরঞ্জীব বসু, নামের মাঝে ‘হার্মাদ’। জীবনানন্দের “অন্ধকার” কবিতা থেকে এই উদ্ধৃতি দিয়েছিলুম ফেসবুকে : “আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর।” চিরঞ্জীব মন্তব্য করলেন, “আপনি এতো আধুনিক কিন্তু বাল ‘ভিতর’ লেখেন কেন ?” আরও অনেকের মন্তব্য ছিল, সকলেই ভেবেছেন, লাইনটা আমার । বুঝতে অসুবিধে হল না যে জীবনানন্দকে পড়াও ছেড়ে দিয়েছে বাঙালি পাবলিক । মন্তব্যগুলো পড়ে “কল্কি” পত্রিকার তরুণী সম্পাদক কৃতী ঘোষের উক্তিটা মনে পড়ে গেল, ‘ঝাঁট জ্বলে যায়। আচ্ছা, মেয়েদের কি ঝাঁট হয় ? কেমন যেন আনরোমান্টিক । তার চেয়ে লোমনাশক লাগিয়ে জায়গাটায় আলতা মাখিয়ে রাখলে শরীর বেয়ে গান বইতে থাকবে ।
২০০০ সালে মুম্বাইতে দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাকের পরে যখন নানাবতী হাসপাতালে থিতু হলুম, কার্ডিওলজিস্ট আমার স্ত্রীকে বললে, তিন লাখ টাকা তাড়াতাড়ি যোগাড় করুন, বাই পাস করতে হতে পারে। প্রথম হার্ট অ্যাটাকের পর অ্যানজিওপ্লাস্টি করিয়েছিলুম । তিন লাখ টাকা চাইলেই তো আর পায়খানা বা পেচ্ছাপের মতন হাসপাতালে জমা দেয়া যায় না । কলকাতা পাড়ি মারলুম । প্রভাত চৌধুরী আমার হার্ট অ্যাটাকের খবর শুনে ভূমেন্দ্র গুহকে নিয়ে এলো, তার আগে আমার সঙ্গে ভূমেন্দ্র গুহর পরিচয় ছিল না । উনি এক মাসেই সারিয়ে তুললেন, বাংলায় প্রেসক্রিপশান লিখে দিতেন, আমার জন্য ওয়েইং স্কেল আর ব্লাড প্রেশার মেশিন কিনে এনে দিয়েছিলেন ; পরিবর্তে আমি মাছ ভাজা আর স্কচ খাওয়াতুম । প্রতি সপ্তাহে একবার দেখতে আসতেন । হঠাৎ আসা বন্ধ করে দিলেন । হয়তো শরীর খারাপ হয়েছে ভেবে,ওনার বাড়ি গিয়েছিলুম, ভালো ব্যবহার করলেন না, প্রেসক্রিপশান-রিপোর্ট ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন । চুপচাপ ফিরে এলুম, মনখারাপ করে । একবার মদের ঘোরে বলেছিলেন যে সরকারি হাসপাতালে এক্স রে করে করে ওনার শুক্রকীটগুলো বাঁচে না, তাই আর বাচ্চা হয়নি । দাদা পরে খবর নিয়ে জানতে পারল যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ভূমেন্দ্র গুহকে বলেছেন, “মলয়ের জন্য অতো করার কি আছে, ওর তো কোনো সাহিত্যিক গুণই নেই।” এই একই কথা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন মারাঠি লেখক-অনুবাদক অশোক সাহানেকে, মারাঠি নাট্যকার দিলীপ চিত্রেকে, ইংরেজি কবিতা লিখিয়ে আদিল জুসসাওয়ালাকে । আর অ্যালেন গিন্সবার্গকে তো বটেই ।
ভূমেন্দ্র গুহর মৃত্যুর খবর জেনেছি ফেসবুকে ।
১৯৬২ সালে “ইল্লত” নামে একটা নাটক লিখেছিলুম, পড়ে প্রশংসা করেছিলেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উনি “বহুরূপী” পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য দিলেন । বেশ কিছুকাল রেখে কুমার রায় বললেন, “আবোল-তাবোল হয়েছে, কোনো কল্পনা নেই, আধুনিকতার ছায়া নেই”। ফেরত নিয়ে “গন্ধর্ব” পত্রিকার নৃপেন সাহাকে দিলুম । উনি পড়ে বললেন ছাপবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাপলেন না, পাণ্ডুলিপি ফেরত নিয়ে আসার সময়ে দেখলুম ওর ওপরে চায়ের কাপ বা বিয়ারের বোতল রেখেছিলেন, টাকনা রেখেছিলেন । আমার পাণ্ডুলিপির প্রথম রিজেকশান । ফেরত নিয়ে নিজে একটা পত্রিকা বের করলুম, “জেব্রা” নামে, আর তাতে প্রকাশ করলুম । সুভাষ আর বাসুদেবের হিংসে হল নাটকটা পড়ে । আমার লেখা উতরেছে কিনা জানার প্রধান মাপকাঠি ছিল হাংরি আন্দোলনের চার-চৌকড়ির হিংসে । ওদের দাঁতক্যালানে হিংসুটে হাসি দেখে বুঝলুম যে নাটকটা তাহলে ভালোই লিখেছি ।
বহুকাল পরে, ‘চন্দ্রগ্রহণ’ পত্রিকার সম্পাদক প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, যিনি পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায় নামে গল্প-উপন্যাস লেখেন, ‘গাঙচিল’ নামে এক প্রকাশন সংস্হার সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার প্রকাশিত বইগুলো আরেকবার প্রকাশ করার তোড়জোড় করেছিলেন । কোন লেখাগুলো প্রকাশ করতে হবে আমি তার তালিকা তৈরি করে দিয়েছিলুম । সংস্হার কর্ণধার অধীর বিশ্বাস ২০১৬ সালে একটা প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করে, আর কোনও সংকলন প্রকাশ করলেন না । অথচ তিনি তিনটি উপন্যাস আর সাক্ষাৎকারসমগ্র ইতিমধ্যে কমপোজ করিয়ে ফেলেছিলেন । দেড় বছর ফেলে রাখার পর বললেন আর আমার বই বের করবেন না । প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় ডিটিপি করার খরচ দিয়ে সিডিগুলো কিনে নিলেন অধীর বিশ্বাসের কাছ থেকে । আমার বেশ অপমানজনক মনে হয়েছিল ব্যাপারটা । উনি আর প্রকাশ করতে চাইলেন না কেননা যেসব এনটিটি আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করার জন্য বকাসুর এণ্ডাবাচ্চা ছেড়ে গেছে তারা অধীর বিশ্বাসের ঘাড়ের ওপর পচা লাশের গন্ধ ছড়াতে আরম্ভ করেছিল। জানতে পারলুম, যে-সংবাদপত্র গোষ্ঠিকে লোকে প্রতিষ্ঠান বলে মনে করে, তাদের খোচরদের চাপে উনি আর এগোননি, এদিকে উনি সুবিমল মিশ্র, সুভাষ ঘোষের বই বের করতে কিপটেমি করেননি । একদিক থেকে এটাকেও রিজেকশান বলতে হবে । রিজেকশানও আনন্দদায়ক হতে পারে, কেননা তা লেখকের বিরুদ্ধে তৈরি প্রাতিষ্ঠানিক ঘোঁটকে সহজেই ফাঁস করে ।
১৯৯০, ১৯৯৭, ২০০০ সালে সবসুদ্ধ তিনবার অ্যানজিওগ্রাফি করিয়েছি, ১৯৯৭ সালে একবার অ্যানজিওপ্লাস্টি । প্রতিবার নুনুর চারিধারের জঙ্গল পরিষ্কার করেছে একজন নার্স । তারপর অ্যানজিওগ্রাফি আর অ্যানজিওপ্লাস্টি করার সময়ে নুনু নিয়ে এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করেছে কয়েকজন যুবতী নার্স । তাদের আচরণ দেখে মনে হতো যে নানারকম নুনু নিয়ে স্হাপত্য গড়ার অভ্যাস হয়ে গেছে । তাদের হাতে পড়ে নুনুর চরিত্রে বদল ঘটে গিয়েছিল, তা আর লিঙ্গ ছিল না ; হাসপাতাল থেকে ফিরে নুনুর লিঙ্গ হয়ে উঠতে কয়েকমাস লেগে গিয়েছিল ।
১৯৯৭ সালে যখন কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালের আইসিইউতে ছিলুম প্রায় কুড়ি দিন, সেখানে যে ধরণের কাণ্ডকারখানা হতো তা লিখেছি “নামগন্ধ” উপন্যাসে । আমি সেসময়ে অফিসপ্রধান ছিলুম, আর বিকেলে একজন অফিসারকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করানো হয়েছিল, হেপাটাইটিস-বিতে আক্রান্ত, তার স্বাস্হ্য কেমন আছে জানাবার জন্য মাঝরাতে অ্যাডমিনিসট্রেটিভ ইনচার্জ ফোন করেছিল, ঘুমের ঘোরে ফোন তুলতে গিয়ে পড়ে গেলুম আর বাঁদিকের কানটা খাটের কোনায় লেগে রক্তারক্তি হয়ে গেল, রক্তচাপ নেমে গেল, সলিলা ট্যাকসি ডেকে ওই হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিলে । কান সেলাইয়ের পর ডাক্তাররা বললেন, ইসিজি নেয়া হয়েছে, এনার হার্টে ব্লকেজ আছে মনে হচ্ছে । ফলে প্রথমে অ্যাঞ্জিওগ্রাফি আর তারপর অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি । আই সি ইউতে, প্রত্যেকদিন কোনো-না-কোনো যুবতী নার্স লাঞ্চ আর ডিনার খাইয়ে যেতো, অতি যত্নে, হাসপাতালটায় মেয়েগুলোকে বলে সেবিকা । মুখের ভেতরে একজন কচি যুবতীর আঙুলের স্পর্শেই বোধহয় পনেরোদিনে চনমনে হয়ে গেলুম । মনে হতো, এদের জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকার মতন আনন্দ আর নেই, এদের সঙ্গে সেক্স করা যায় না, জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে ফোঁপানো যায় ।
১৯৮৮ সালে মারাঠি কবি অরুণ কোলাটকর বলেছিলেন ওনার বাড়ি যে গলিতে তার মোড়ে একটা ‘নেকেড স্ট্যাচু’ আছে । বাস থেকে নেমে নেকেড স্ট্যাচু আর নংগা মুর্তি জিগ্যেস করে ঘণ্টাখানেক ঘুরেও যখন হদিশ পেলুম না তখন একজনকে জিগ্যেস করলুম অরুণ কোলাটকর কোথায় থাকেন ? সে বলল, মারাঠি কবি তো ? চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি । কোলাটকর মারা গেছেন ২০০৪ সালে । বিয়ে করেছিলেন একটি পার্সি যুবতীকে । বাচ্চা হলে সে অসুবিধায় পড়বে বলে বাচ্চা হয়নি ওনাদের । একটা ছোট্ট ঘরে থাকতেন । সবকিছু খাটের তলায়, টেনে বের করলে ডাইনিং টেবিল, লেখার টেবিল । ঘরের চৌকাঠে বসে কবিতা লিখতেন । কারোর সঙ্গে বিশেষ মিশতেন না ।
যে বছর জন্মেছিলুম, ১৯৩৯ সালে, সেই বছরে জন্মের এক মাস আগেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে, সংসারে টানাটানি, রাতে অন্ধকার । বাড়ির সবাই আমার জন্মকে দুষেছিল, দ্বিতীয় যুদ্ধ আর বোমার ভয় আর অনটন আনার জন্য, কলকাতা থেকে আত্মীয়-জ্ঞাতিরাও এসে উঠেছিল আমাদের বাড়িতে । বড়জ্যাঠা তখন থেকেই লুঙ্গির চারখুঁটে গিঁট বেঁধে মুসল্লাপুর হাট থেকে ঝড়টি-পড়তি সব্জি কেনা আরম্ভ করেছিলেন, সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়ে আনতেন । ইমলিতলার বাড়িতে বিজলিবাতি ছিল না, কলের জলও ছিল না । সকলকে রাস্তার কলে গিয়ে স্নান করতে হতো, খাবার জল ভরে আনতে হতো ।
ইমলিতলা পাড়া ছাড়ার কয়েক বছর পরে ওই পাড়ায় গেলে অনেকে আমাকে চিনতে পারছিল না, কিন্তু পাড়ার চারটে কুকুর, মোতি, টাইগার, ভুতুয়া, দিলের, বুড়ো হয়ে লোম প্রায় উঠে গেছে, আমাকে দেখেই ছুটতে-ছুটতে এসে ল্যাজ নাড়ানো আরম্ভ করে দিয়েছিল । চারটে কুকুরই মারা গেছে ; ওদের পুঁতে দেয়া হয়েছে গঞ্জেড়িদের মাটির উঠোনে । ১৯৬৬ সালে বড়োজ্যাঠা মারা যাবার পর কিছুদিন ইমলিতলার বাড়িতে একা ছিলেন বড়জেঠিমা, স্টোভে রান্না করতেন, হরি হে হরি হে হরি হে বলে বলে স্টোভে পাম্প করতেন, ১৯৭৯ সালে একদিন স্টোভ ফেটে বেশ পুড়ে গিয়েছিলেন । দশ বছর পর ইমলিতলায়, নিজের পরিচয় দেবার আগে, কপিলের চাচিকে জিগ্যেস করেছিলুম, এই বাংগালি লোগ কোথায় চলে গেল । কপিলের চাচি, চিনতে পারেনি আমাকে, বলেছিল, ভস্মাসুরের বংশ, সবাই নিজের দৃষ্টিতে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গেছে । রাক্ষসের বংশ ! বাঙালিরা যাকে বলে ভস্মলোচন, তাকে বিহারিরা বলে ভস্মাসুর । ইমলিতলার বাড়িতে একটা ফোটো ছিল বড়ো জ্যাঠাইমার, দুহাতে ব্লাউজ দুদিকে মেলে আছেন, টপলেস দেখিয়ে, কেননা ওনার মাপের মাই আর কারোর ছিল না বাড়িতে, পাড়াতে শুধু কালুটুয়ার চাচির ছিল, তামাটে, জেঠিমার মতন গোলাপি-ফর্সা নয় । কে তুলেছিল জানি না, হয়তো বাবা, হয়তো কোনও কাকা, হয়তো মেজ-জ্যাঠা । ফোটোটা যদি সঙ্গে থাকতো তাহলে নন্দনতাত্ত্বিক আবু সয়ীদ আইয়ুবকে দেখাতে পারতুম, “এই দেখুন স্যার, আমার বড়োজেঠিমা” । বুঝতে পারতেন আমি কেমনধারা পরিবারের প্রডাক্ট ।
আট
আমি আরেকবার প্রেমে পড়ে দুর্ভোগের জাঁতিকলে আটকাতে চাইনি বলে সলিলার সঙ্গে পরিচয়ের তিন দিনের মাথায়, ১৯৬৮ সালে বলেছিলুম,আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই, এ-ব্যাপারে কার সঙ্গে কথা বলতে হবে । ও বলেছিল মামাদের সঙ্গে । মনোনয়নে ইপিফ্যানির গর্ব হল । ১৯৬৮ সালে সলিলাদের বাড়িতে সাজানো কাপ আর শিল্ড দেখে প্রশ্ন করে জেনেছিলুম, ওগুলো সলিলার, হকি খেলে পাওয়া, স্টেট প্লেয়ার ছিল, কালার হোল্ডার, ম্যাচ জিতলে কাপে রাম ভরে খেতো । বেশ আনন্দ হয়েছিল যে টিপিকাল বাঙালি মেয়ের মতন নয় ।
ইমলিতলার বাড়িতে মা বেশির ভাগ সময়ে রান্নাঘরে, দুটো মাটির উনোনে রান্না করছেন, বাসন-কোসনের বিশেষ শব্দ নেই । রান্নার কতো রকমের সুবাস । রাতে কেরোসিনের লম্ফ জ্বেলে রান্না, উনোনের আলোয় মায়ের গনগনে মুখ । ঝুলকালি ভুষো পড়ে রান্নাঘর এতো অন্ধকার যে ছয়মাস অন্তর রামরস দিয়ে রঙ করানো হতো। সব ঘরের চেয়ে রান্নাঘরকে মা বেশি ভালোবাসতেন । জ্যাকসন পোলকের বহু আগেই মা রান্নাঘরের দেয়ালে অমন তুলিহীন পেইনটিং এঁকেছিলেন’কড়াই থেকে দেয়ালে ছিটকে লাগা হলুদ-লংকার দরানি । কোনো ধার্মিক অনুষ্ঠান না হলে মা সিঁদুর পরতেন না, সলিলাকেও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে প্রতিদিন সিঁদুর পরলে চুল পেকে যায় আর ঝরে পড়ে, তাই পরার দরকার নেই, শাঁখা-ফাঁকাও দরকার নেই । ফলে সলিলা সিঁদুর-শাঁখার পাট চুকিয়ে দিয়েছে বিয়ের পর-পরই । কিন্তু কোনো বাঙালি বামুন পরিবার আমাদের বাড়িতে ভিজিট দিতে আসছে শুনলেই একটা টিপ আর সিঁদুর পরে নেয়, কেননা কেউ-কেউ কথা শোনাবার সুযোগ ছাড়ে না ।
বউদির শালীরা, যারা দাদার বাড়ির কাছে বাঁশদ্রোণীতে থাকে, তাদের রক্ষণশীল টিটকিরির ভয়ে সলিলা বেশ কিছুকাল দাদার বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। যখন নাকতলার ফ্ল্যাট বেচা ফাইনাল করে ফেলেছি, তখন দাদাকে বলেছিলুম, তোমার ওপরতলাটা আমাদের ভাড়া দাও, আমি মার্কেট রেটই দেবো, তা বউদি বললেন, কোথাও একতলা ভাড়া করে থাকগে যাও । অগত্যা চলে এলুম মুম্বাই । দাদার ছোটো ছেলে বিটু দাদার কাছে জানতে চেয়েছিল যে কেন আমাদের ওপরতলাটা ভাড়া দেওয়া হয়নি, উত্তরে দাদা ওকে বলেছিল, পরে প্রবলেম হতো । দাদার বোধহয় ভয় ছিল যে যেহেতু পাটনার বাড়ির ওপর আমি আর আমার ছেলে-মেয়েরা কোনো দাবি-দাওয়া জানাইনি, তাই ওপরতলায় থাকলে হয়তো ছাড়তে চাইবো না । ওপরতলায় থাকলে দাদাকে বাজে মারোয়াড়ি হাসপাতালে ভর্তি হতে দিতুম না, তাড়াতাড়ি মৃত্যুর পথে যেতে দিতুম না ।
১৯৫০ সালে রামমোহন রায় সেমিনারিতে ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি খেলায় আমার মাথা ফেটে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম, সেই দাগ এখনও আছে । আক্রান্ত হবার চিহ্ণ । বিরূপ সমালোচনা পড়ে কপালের দাগটায় হাত বুলিয়ে আলোচককে ভুলে যাই । বাবা যখন মারা গিয়েছিলেন, শ্রাদ্ধের সময়ে আমি ন্যাড়া হইনি । কিছুকাল পরে বাবার জন্য এতো মনকেমন করছিল যে একটা সেলুন দেখতে পেয়ে সোজা ঢুকে গিয়ে ন্যাড়া হয়েছিলুম, আর ফেরার সময়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, কেঁদেছিলুম । পথচারীদের মাঝে দাঁড়িয়ে কেঁদে, ভালো লেগেছিল, যা সমবেত শোকের কান্নায় হয় না । আমি পাটনা থেকে লখনউ চলে যাবার পর দাদা সপরিবারে পাটনায় চলে এসেছিল। বড়ো ছেলে পড়াশোনায় ভালো ফলাফল করতে পারেনি বলে তাকেই দোকানে বসিয়ে দিয়েছিল । বাবা আমার কাছে চলে এসেছিলেন লখনউতে । মা লখনউতে মারা যেতে বাবা পাটনায় কিছুদিনের জন্য ফিরে গিয়েছিলেন, তারপর কোতরঙের ভদ্রকালীতে ছোটোকাকা বা বিশেখুড়োর বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে শেষজীবন কাটাবেন ভেবে । ছোটোকাকা বেশ প্যাঁচালো মানুষ ছিলেন, বাবার কেনা জমিজিরেত ঠাকুমাকে দিয়ে নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছিলেন । শেষে পাটনার বাড়িও ছোটোকাকা বাবাকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পারেন আঁচ করে দাদা বাবাকে পাটনায় নিয়ে চলে যান । আমি বাবাকে মুম্বাইতে নিয়ে আসিনি এটা আমার জীবনের একমাত্র রিগরেট হয়ে থেকে গেছে ।
আমার বাবা রঞ্জিত রায়চৌধুরী জন্মেছিলেন বর্তমান পাকিস্তানের লাহোর শহরে, ১৯১২ সালে । পাঞ্জাবের মহারাজা রঞ্জিত সিংহ সম্পর্কিত গালগল্পে প্রভাবিত হয়ে ঠাকুমা বাবার অমন নাম রেখেছিলেন। রঞ্জিত সিংহ জন্মেছিলেন ১৩ই নভেম্বর ১৭৮০ । বাবাও জন্মেছিলেন ১৩ই নভেম্বর । ছয় ভাই আর এক বোনের মধ্যে বাবা ছিলেন তৃতীয় বা সেজ ভাই । অন্যান্য ভাইদের পোশাকি আর ডাক নাম দুটিই থাকলেও, বাবার ওই একটি নামই ছিল, রঞ্জিত । ঠাকুর্দার আদি নিবাস ছিল হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায় । ১৭০৯ সালে উত্তরপাড়া শহরটির পত্তন করেছিলেন দাদুর পূর্বপুরুষ রত্নেশ্বর রায়চৌধুরী ।
ঠাকুর্দা লক্ষ্মীনারায়ণ রায়চৌধুরী, পোরট্রেট আঁকতে পারতেন, এবং সেই সূত্রে তিনি বিভিন্ন রাজপরিবারের ডাকে সপরিবারে ভারতের এক রাজ দরবার থেকে আরেক রাজ দরবারে চলে যেতেন । লাহোরে গিয়ে তিনি ড্যাগেরোটাইপ ক্যামেরায় ফোটো তুলতে শেখেন, যাতে ফোটো তুলে তা থেকে ছবি আঁকতে সুবিধা হয় এবং রাজ পরিবারের মহিলাদের এক নাগাড়ে বসে থাকতে না হয় । সেসময়ে মেয়ো স্কুল অফ আর্টসের অধ্যক্ষ এবং লাহোর মিউজিয়ামের কিউরেটার ছিলেন রাডিয়ার্ড কিপলিঙের বাবা জন লকউড কিপলিঙ, যাঁর সঙ্গে পরিচয়ের ও তাঁর অধীনে কাজ করার সূত্রে তাঁর কাছ থেকেই তিনি ফোটো তোলা শেখেন । ফোটো তোলা হতো সরাসরি ব্রোমাইড পেপারে । পরে, কাচের প্লেটে নেগেটিভ ফিল্ম তোলা হতো, সেই নেগেটিভকে রসায়নে চুবিয়ে রেখে ফোটো গড়ে উঠত; তারপর সেই প্লেটের ওপর ফোটোর কাগজ রেখে, প্রয়োজনীয় আলো দেখিয়ে ফোটো প্রিন্ট করা হতো, আর সেই প্রিন্টকে রসায়নে চুবিয়ে, শুকিয়ে, স্হায়ীত্ব দেয়া হতো ।
ড্যাগেরোটাইপ ক্যামেরা ছিল বেশ ভারি ; বাইরে গিয়ে ফোটো তুলতে হলে তাকে বয়ে নিয়ে যাবার লোক দরকার হতো । বাইরে তোলা হচ্ছে বলে একসঙ্গে অনেকগুলো তুলে যেটা ভালো হল সেটা থেকে ফোটো তৈরি করা হতো । ফোটো তোলা হতো ক্যামেরা স্ট্যাণ্ডের ওপরে ক্যামেরা রেখে । ফোটো তোলার সময়ে হাত দিয়ে লেন্সের ঢাকনা খুলে, ‘স্মাইল প্লিজ’ বলে দু’এক সেকেণ্ডে আবার লেন্স পরিয়ে দেয়া হতো । স্টুডিওতে ফোটো তুলতে হলে প্রথম দিকে কুঁজোর মাপের হাজার-দুহাজার ওয়াটের বাল্বের আলোয় ফোটো তুলতে হতো, পরে অবশ্য বাল্বের মাপ ছোটো হয় । এখন প্রযুক্তির এত উন্নতি হয়েছে যে ড্যাগেরোটাইপের ঝঞ্ঝাটকে মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক । বাবা এই ডিজিটাল প্রযুক্তি দেখে যেতে পারলেন না । শৈশবে তাঁকে দেখতুম শহরের বাইরে ফোটো তুলতে যাচ্ছেন কাজের লোক রামখেলাওন সিংহের কাঁধে ক্যামেরার বাক্স চাপিয়ে, নিজে ক্যামেরা তিন-ঠেঙে স্ট্যান্ড আর মাথায় চাপা দেবার কালো মোটা কাপড় । বাবা মারা যাবার পর যখন পাটনার বাড়ি ছেড়ে চলে আসলুম, দেখেছিলুম তিনতলার একটা ঘরে থাক-থাক কাচের প্লেট, কড়িকাঠ থেকে র্যাকে সাজানো । ইতিহাসবোধ না থাকলে যা হয়, আমি বা দাদা আমরা কেউই সেগুলো সংরক্ষণের প্রয়াস করিনি । দাদার ছেলেরা কাচঅলাকে ওজন দরে বিক্রি করে দিয়েছে ।
দাদুর ছেলেরাও ফোটো তোলা আর ছবি আঁকায় সড়গড় হলে দাদু ১৮৮৬ সালে ফোটোগ্রাফির ভ্রাম্যমান ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন, এবং সংস্হাটির তিনি নাম দেন ‘রায়চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং’ । হুগলি জেলায় গঙ্গা নদীর ধারে উত্তরপাড়ার পাশে এখন যেখানে বালি ব্রিজের সংলগ্ন ফ্লাইওভার, তখন একটা রাস্তা ছিল, সেখানে একটা দপতর খুলে নকাকাকে চালাতে বলেছিলেন । কিন্তু নকাকা তা সামলাতে পারেননি, স্ত্রীর সঙ্গে অবনিবনার দরুণ হঠাৎ বৈরাগ্যে আক্রান্ত হবার কারণে । দাদুর অমন ঘোরাঘুরির কারণে বড়জেঠা, মেজজেঠা, বাবা, পিসিমা আর নকাকার স্কুলে পড়া হয়ে ওঠেনি । দাদু হঠাৎ মারা যাবার পর তাঁর ছেলেরা পাটনায় থিতু হতে বাধ্য হন এবং তখন নতুনকাকা আর বিশেখুড়ো মানে ছোটোকাকাকে স্কুলে ভর্তি করা হয় । নতুনকাকা নিয়মিত স্কুল করলেও ছোটোকাকার আগ্রহ না থাকায় তিনি পড়াশোনা ত্যাগ করেন । জেঠাকাকাদের যেটুকু পড়াশোনা হয়েছিল তা রাজদরবারগুলোর শিক্ষকদের অবদান । দাদু সংস্কৃত আর ফারসি লিখতে-পড়তে পারতেন । বাবা ইংরেজি ভাষা আয়ত্ব করে ফেলেছিলেন ।
দাদু বিভিন্ন সময়ে আফগানিস্তানের কাবুল-কান্দাহার এবং পাকিস্তানের বাহাওলপুর, চিত্রাল, হুনজা, ফুলরা, মাকরান ও লাহোরে ছিলেন। আফগানিস্তানে ব্রিটিশদের যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর লাহোরে চলে যান । বড়জেঠার মুখে শুনেছি যে বাহাওলপুরের সেই সময়ের ডাকটিকিটে আমিরের পোরট্রেট ছিল দাদুর আঁকা । ওই অঞ্চলের ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদির মাংস আর শুঁটকিমাংস খাওয়ার সঙ্গে ঠাকুমা আর বাবার ভাইরা নিজেদের মানিয়ে নিলেও বাবা পারেননি, এবং তিনি সারা জীবন শাকাহারী হয়ে যান । বাবার মুখে শুনেছি যে বাজারে ঝোলানো গোরু, মোষ, ইয়াক আর কাটা উটের মাংস দেখার পর উনি আর মাংস খেতে পারতেন না, তাই নিরামিশাষী হয়ে যান । দুম্বা একরকমের ভেড়া যার ল্যজের জায়গায় বাড়তি মাংস গজায়, আর বাড়তি লেজের মাংস, বড়জেঠার বক্তব্য অনুযায়ী, ছিল খুবই সুস্বাদু ।
ফোটোগ্রাফির সূত্রেই দাদুর সঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগণার পাণিহাটি-নিবাসী আমার দাদামশায় কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় হয়েছিল । কিশোরীমোহন ছিলেন ম্যালেরিয়া রোগের উৎস আবিষ্কারক রোনাল্ড রসের সহগবেষক । রোনাল্ড রস স্বদেশে ফিরে যাবার পর কিশোরীমোহন ম্যালেরিয়া রোগের কারণ ও তা প্রতিরোধ করার জন্য গ্রামে-গঞ্জে ম্যাজিক লন্ঠনে স্লাইড দেখিয়ে প্রচার করতেন । এই স্লাইডগুলো তৈরি করে দিয়েছিলেন দাদু । কিশোরীমোহন তাঁর বড় মেয়ে অমিতার সঙ্গে বাবার বিয়ে দেন । বিয়ের সময়ে মায়ের বয়স ছিল ১৪ বছর আর বাবার ১৮ বছর । কিশোরীমোহন সম্পর্কে উইকিপেডিয়া আর নেটে অন্যত্র তথ্য আছে । বাবা নিজে শাকাহারী হলেও মাকে বাধ্য করেননি তাঁর আহারের রুচি অনুসরণ করতে ; আমি আর দাদা দুজনেই আমিষাশী । দাদু প্রতি বছর দুর্গা পুজোর সময়ে উত্তরপাড়া ফিরে যেতেন ; ছেলেদের বিয়ে দেয়ার কাজটাও সেরে নিতেন সেই সময়টুকুর মধ্যে ।
দ্বারভাঙ্গা মহারাজের পরিবারের সদস্যদের ছবি আঁকার জন্য ডাক পড়লে দাদু সপরিবারে পাটনায় যান, আর সেখানেই হৃদরোগে মারা যান । পুরো পরিবার নির্ভরশীল ছিল দাদুর ওপর ; তিনি মারা যেতে ঠাকুমা বিপদে পড়েন । পাটনায় তাঁরা একটি মাটির দেয়ালের ওপর টালির চালার বাসা ভাড়া করে বিভিন্ন উপায়ে টাকা রোজগারের চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই সফল না হতে পারায় বাবা দাদুর প্রতিষ্ঠিত সংস্হা ‘রায়চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং’ এর সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে ছবি আঁকা আর ফোটো তোলার একটি স্হায়ী দোকান চালাবাড়ির কাছেই, বিহার ন্যাশানাল কলেজের সামনে, খোলেন । ঠাকুমার জাঠতুতো ভাই কলকাতা মিউজিয়ামের সহকিউরেটার লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুপারিশে বড়জেঠা পাটনা মিউজিয়ামে চতুর্থ বর্গের একটি চাকরি পান । পরে অবশ্য তিনি নিজের যোগ্যতার দরুন পদোন্নতি পেয়ে পাটনা মিউজিয়ামের ‘কিপার অব পেইনটিংস অ্যাণ্ড স্কাল্পচার’ হয়েছিলেন। বড়জেঠা মাটির মূর্তি তৈরি করায় আর অয়েল-পেইন্টিং আঁকায় দক্ষ ছিলেন । ছোটোবেলায় ছুটির দিনে আমি মিউজিয়ামের এক থেকে আরেক প্রান্ত ঘুরে বেড়াতুম, চৌকাঠ ডিঙোতেই প্রাগৈতিহাসিক থেকে মহেঞ্জোদরোয়, সেখান থেকে অশোকের রাজত্বে !
দাদু মারা যেতে, ঠাকুমা উত্তরপাড়ার বসতবাড়িতে, যা অবহেলায় খণ্ডহরের চেহারা নিয়ে ফেলেছিল, থাকতে চলে গেলে, পরিবারের আর্থিক ভার পুরোপুরি এসে পড়েছিল বাবার কাঁধে । ঠাকুমা ছেলেদের আর তাদের বোউদের বলে দিয়ে যান যে আমার মা সংসারটাকে সামলাবেন । যেকোনো কারণেই হোক মেজজেঠা, নকাকা আর বিশেখুড়োর স্বভাব আর আচরণ এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে আমরা শৈশবে শুনতুম যে এঁরা কিছুটা অপ্রকৃতিস্হ, আধপাগল । দোকানের কাজে তাঁদের তেমন আগ্রহ ছিল না ; তাঁরা প্রকৃতই শিল্পীচরিত্রের বিপন্ন বিস্ময়ে আক্রান্ত অস্বাভাবিকতা পেয়েছিলেন । মেজজেঠা ঘুম থেকে উঠতেন দুপুরবেলা, তারপর জলখাবার খেতেন কোনো দোকান থেকে লুচি আলুর তরকারি কিনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, কখনও চুল আঁচড়াতেন না, বাড়ি ফিরে দাঁত মেজে স্নান করে বিকেলের দিকে দোকানে পৌঁছোতেন, এবং একটি ফোটোর সামনে বসে তাকে মাসখানেকে আঁকা অপূর্ব ছবিতে দাঁড় করাতেন । নকাকা অনেক ভোরে উঠতেন, সবাইকে, শিশুদেরও ‘আপনি’ সম্বোধন করতেন, স্ত্রীর সঙ্গে বিশেষ কথা বলতেন না, জুতো পরার অভ্যাস ছিল না, কোরা ধুতি পরতেন, নিজের ধুতি-শার্ট নিজেই কাচতেন, কোনো এক ফাঁকে দোকানে গিয়ে বাড়িতে করার জন্য বাবার কাছ থেকে ‘কাজ’ চেয়ে আনতেন । ছোটোকাকা মাঝরাতে নিজের ঘরে ছোটোকাকিমার নানা আঙ্গিকের পোশাকহীন ফোটো তুলতেন আর দোকানে গিয়ে বাবাকে সাহায্য করার নাম করে ডার্করুমে ঢুকে সেই ‘অপ্সরা’ ফোটোগুলো প্রিন্ট করে নিতেন । উনি যখন উত্তরপাড়ায় পাকাপাকি চলে গেলেন তখন তাড়াহুড়োয় অ্যালবামগুলো নিয়ে যেতে ভুলে যান । আমি আর পিসতুতো দাদা সেগুলো আবিষ্কার করেছিলুম । ছোটোকাকা ৯০ বছর বয়সে মারা যান, নিঃসন্তান ; উত্তরপাড়ার বাড়ির অংশ ছোটো শালার প্রথম পক্ষের মেয়েকে দিয়ে গেছেন ।
নয়
বাবা ভোরবেলা বেরিয়ে যেতেন আর ফিরতেন বেশ রাত করে । ফোটো তোলা, জিনিসপত্র বিক্রি আর ডার্করুমের কাজ তাঁকে একা করতে হত বলে ভোরবেলা জলখাবার খেয়ে সোজা গিয়ে ডার্করুমে ঢুকতেন, তারপর রাতে দোকান বন্ধ করার পর আবার ঢুকতেন ডার্করুমে । বিহারে সেসময় তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, তাই কাজ পেতে অসুবিধা হতো না । মা আর বাবা দুজনের চরিত্রেই যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তা হল সবায়ের সঙ্গে মানিয়ে চলা । বাবা বাড়ির প্রধান রোজগেরে হলেও নিজের ভাইদের আর তাদের ছেলে-মেয়েদের, মানে আমাদের জাঠতুতো খুড়তুতো ভাইবোনদের, সমান চোখে দেখতেন। বড়জেঠা ইমলিতলা বাড়ির ট্যাক্স দিতেন আর সবজি কিনতেন, বাবা বাদবাকি সমস্ত খরচ করতেন, ঠাকুমাকে টাকা পাঠাতেন, উত্তরপাড়ার বাড়ির ট্যাক্স দিতেন । চালগমের দোকানদারকে মাসে একবার, মায়ের তৈরি ফিরিস্তির কাগজ, দোকানে যাবার পথে বাবা দিয়ে যেতেন আর সে ইমলিতলার বাড়িতে পাঠিয়ে দিত । পরিবারের সদস্যদের পোশাকের জন্য বাবা দর্জিকে বলে রেখেছিলেন, তার দোকানে গিয়ে মাপ দিয়ে দিতে হতো, সে তৈরি করে বাড়ি পাঠিয়ে দিত । একইভাবে ছিল জুতোর দোকানের সঙ্গে বন্দোবস্ত । চুল কাটার জন্য মাসে একবার নাপিত আসত, পরে বাবার কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে নিত ।
ইমলিতলার বাড়িতে বাবা-মা-দাদা-আমি যে ঘরটায় থাকতুম সেটাই ছিল বাড়ির সবচেয়ে ছোটো ঘর । লন্ঠনের আলোয় পড়াশুনা করতে হতো । চেয়ার-টেবিল ছিল না, দোকানের মালপত্র যে প্যাকিংবাক্সতে আসত তার ওপর চাদর পেতে বই রাখার ব্যবস্হা ছিল । পাড়ার কুসঙ্গ-কুখ্যাতির প্রভাব দাদার ওপর পড়তে পারে অনুমান করে ম্যাট্রিক পাশের পর ১৯৪৯ সালে দাদাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল পাণিহাটিতে থেকে কলকাতায় পড়াশোনা করার জন্য । কলকাতায় দাদা সিটি কলেজে ভর্তি হন । কলেজে বন্ধু হিসেবে পান সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার, আনন্দ বাগচী প্রমুখ তরুণ কবিদের । দাদা বিহার সরকারের মৎস্য বিভাগে চাকরি পেলে তাঁর পোস্টিঙের জায়গায় বন্ধুরা একা বা দলবল নিয়ে পৌঁছোতেন । ছোটোবেলায় আমি একবার তাড়ি খেয়েছিলুম, মানে পাড়ার এক সর্বজনীন দাদু খাইয়ে দিয়েছিল । মুখে তাড়ির গন্ধ পেয়ে মা আমায় আমাদের ঘরে শেকল তুলে বন্ধ করে দিয়েছিলেন ; বাবা রাতে বাড়ি ফিরলে শেকল খোলা হয় । মায়ের সব সময় আশঙ্কা ছিল যে আমরা দুই ভাইও মেজদার মতন অসামাজিক চরিত্রের মানুষ হয়ে যেতে পারি । পাড়ায় মেলামেশায় কোনো নিষেধাজ্ঞা কিন্তু ছিল না । ছোটোবেলায় চোর-পুলিশ খেলতে গিয়ে অনেকের শোবার ঘরে ঢুকে খাটের তলায় লুকোবার স্মৃতি আছে ।
ইমলিতলার বাড়িতে জলের কল ছিল না ; বড়জেঠা তো অফিস চলে যেতেন, জল ভরে এনে দেবার লোক না এলে দুপুরে বাবা যখন দোকান থেকে আসতেন, অনেক সময়ে নিজের স্নান করার জল নিজেই কল থেকে ভরে আনতেন। শীতকালেও ঠাণ্ডা জলে স্নান করতেন । দাদা আর আমি ইমলিতলায় রাস্তার কল থেকে জল ভরে এনেছি, রাস্তার কলে স্নান করেছি । বাবার নির্দেশ ছিল যে বাড়ির সব কাজ আমাদেরও করতে হবে, প্রয়োজনে কয়লা ভাঙা আর উনোন পরিষ্কার, জঞ্জাল ফেলে আসাও । বাবা রাস্তার কলে স্নান করতে লজ্জা পেতেন । ২০০৫ – ২০০৮ নাগাদ আমি কলকাতার রাস্তা থেকেও খাবার জল ভরে আনতুম পেপসির বোতলে করে, কেননা তিন তলায় কোনো ভারি জলের টিন নিয়ে বা মিনারাল ওয়াটারের বড়ো বোতল নিয়ে রিকশাঅলা উঠতে চাইত না । মাঝে-মাঝে দাদার বাড়ি গিয়ে দুটো থলেতে পেপসির বোতলে জল ভরে আমি আর আমার স্ত্রী সলিলা রিকশা করে নিয়ে আসতুম নাকতলার বাড়িতে। এই সমস্ত অসুবিধার জন্যেই নাকতলার ফ্ল্যাটটা বেচে মুম্বাইতে একরুমের ফ্ল্যাটে চলে আসতে হয়েছে ।
বাবা চিরকাল শাদা পাঞ্জাবি, ধুতি আর পায়ে পামশু পরতেন । তাঁর ভাইয়েরা শাদা ছাড়া অন্যান্য রঙের শার্ট বা পাঞ্জাবি পরলেও বাবার পোশাকের অন্যথা হতো না, শীতকাল ছাড়া, যখন উনি নস্যি রঙের শাল গায়ে দিতেন, বা ওই রঙের উলের পাঞ্জাবি পরতেন । দোকানে যাবার তাড়ায় বাবার দ্রুত হাঁটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল । ইমলিতলায় থাকতে দুবার ওনার পা দোকানে যাবার পথে ভেঙে গিয়েছিল ; বাবার পা ভাঙা মানে আর্থিক দিক থেকে বেশ বিপজ্জনক অবস্হা ; দাদাকে গিয়ে দোকানে বসতে হত । উত্তরপাড়া থেকে চাকুরিহীন কোনো জ্ঞাতির ছেলেকে নিয়ে এলেও তাদের অবাঙালি পরিবেশে মানিয়ে নিতে এতই অসুবিধা হত যে কয়েক দিনেই তারা ফেরত চলে যেত । পরে দরিয়াপুরে গিয়ে বাবার যখন আরেকবার পা ভেঙেছিল তখন আমি দোকানদারি করেছি । গরিব হলে যা হয়, গতি কেবল সরকারি হাসপাতাল, সেখানে কিউ, কেননা প্রায়ভেটে কোনো নার্সিং হোম ছিল না সেসময়ে ; এখন তো প্রতিটি রাস্তায় একজন করে হাড়ের ডাক্তার । বড়জেঠির এক বান্ধবীর স্বামী ছিল ছুতোর ; ওনার পা ভেঙে যেতে, জেঠিমার বান্ধবীর কথামতো বাবার পায়ে বসাবার জন্য ছুতোরকে দিয়ে কাঠের খাপ তৈরি করিয়ে পায়ে বেঁধে রাখার ব্যবস্হা হয়েছিল । প্রথমবার বানিয়ে দেয়া খাপটা দ্বিতীয়বার কাজে লেগে গিয়েছিল ।
বিহার ন্যাশানাল কলেজের সামনে যে দোকান ছিল সেই বাড়ির মালিক উঠে যাবার নোটিস দিলে বাবা পড়েন মহাবিপদে । বিকল্পের সন্ধানে বেরিয়ে তিনি তখনকার বারি রোডে দরিয়াপুরে একটা চালাবাড়ি কেনেন ; সেটা ছিল একজন কামারের হাপর-বসানো ঘর, পেছনে আর পাশে সামান্য জমিতে গাঁজাগাছের ঝোপ । এই এলাকাটাও সেসময়ে গরিবদের পাড়া ছিল, ধারণার অতীত দুস্হ সুন্নি মুসলমানদের পাড়া । বিহার ন্যাশানাল কলেজের সামনে যে দোকান ছিল তার মালিকের বিরুদ্ধে মামলা চলে বেশ কয়েকবছর ; সেই সুযোগে দরিয়াপুরে দোকানঘর তৈরি করে ফেলা হয় । তৈরি হয়ে গেলে পুরোনো দোকানের পাট গুটিয়ে বাবা চলে আসেন দরিয়াপুরে । ‘রায়চৌধুরী অ্যাণ্ড কোং’-এর খ্যাতির কারণে পুরোনো খদ্দেররা দরিয়াপুরে আসত । এখন এই সংস্হা চালায় দাদার বড় ছেলে হৃদয়েশ, জাপানি কোম্পানির প্রস্তাবমতো দোকানের নাম পালটে ফেলেছে ।
দরিয়াপুরে যখন দোকান তৈরি হচ্ছিল তখন আমি ওই বাড়িতে একা থাকতুম, কেননা ইমলিতলার প্রাত্যহিক মাতালদের চেঁচামেচি আর ঝগড়াঝাঁটির দরুন পড়তে বসে বেশ অসুবিধা হত । তাছাড়া দরিয়াপুরে ইলেকট্রিসিটি ছিল, কলের জল ছিল। ছোটোদের হাতখরচের জন্য বাবা টাকা দিতেন না ; বলতেন যার যা চাই জানিয়ে দাও, কিনে এনে দেব । স্কুলের বাৎসরিক ফলাফলের রিপোর্টে বাবা কখনও কাউকে ‘গুড’ দিতেন না । নব্বুইয়ের কোঠায় মার্কস পেলেও দিতেন না ; বলতেন আরও বেশি পেতে হবে । দরিয়াপুরের বাড়িতে একা থাকলে আমার চরিত্রদূষণ ঘটতে পারে অনুমান করে বছরখানেক পরে মা আর বাবা রাতে শুতে আসতেন । মা টিফিন ক্যারিয়ারে করে রাতের খাবার আনতেন । দিনের বেলা ইমলিতলায় গিয়ে খেতে হতো । দরিয়াপুরের বাড়িতে একা থাকার সময়ে বন্ধুদের নিয়ে কিঞ্চিদধিক চরিত্রদূষণ যে ঘটত না তা বলা যাবে না ।
বাবা আর মা দুজনেই মন্দিরে গিয়ে পুজো দেয়া বা তীর্থকর্ম করা ইত্যাদিতে আগ্রহী ছিলেন না ; আমার মনে হয় কাজের চাপে উনি সংস্কারমুক্ত করে ফেলেছিলেন নিজেকে । পরে দোকানের কাজ ছেড়ে দেবার পর বাবা হিন্দুধর্ম আর ঈশ্বর দেবী-দেবতায় আশ্রয় নিয়েছিলেন । আমি কখনও বাবা-মাকে তীর্থক্ষেত্রে বেড়াতে যেতে দেখিনি । জেঠা-কাকারাও কেউ আগ্রহী ছিলেন না ; পাটনার বাইরে যেতে হলে তাঁরা যেতেন কেবল দেশের বাড়ি, অর্থাৎ উত্তরপাড়ায় । তবে বাবা নিয়মিত পৈতে বদলাতেন, একাদশীর দিন লুচি খেতেন । কালীঘাটের কালী আমাদের পারিবারিক দেবতা, যেহেতু তা আমাদের কোনো পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত, সেকারণে বাড়িতে পারিবারিক দেবতা আর তার সেবাযত্ন করার প্রয়োজন হতো না । গলায় মালার মতন ঝুলিয়ে পৈতে পরতেন বড়জেঠা আর ছোটোকাকা, যদিও খাওয়ার কোনো নিষেধ মানতেন না, মেজজেঠা কখনও পৈতে পরতেন আবার কখনও কুলুঙ্গিতে তুলে রেখে দিতেন । দাদার আর আমার ছোটোবেলায় পৈতে হয়েছিল বটে কিন্তু আমরা বছর শেষের আগেই স্বরূপে এসে জলাঞ্জলি দিয়েছিলুম । পৈতেহীন হবার কারণে বাবা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন বলে মনে হয় না ; এই প্রসঙ্গে কখনও কোনো কথা তোলেননি।
মা, বাবা এবং শিক্ষক, যে তিনজন মানুষ ব্যক্তিজীবনের অভিমুখ গড়ে দেয়, আমার জীবনে মা আর বাবার ভূমিকাই প্রধান । প্রকৃত অর্থে আমি কোনো শিক্ষক সেই সময়ে পাইনি যখন তা জরুরি ছিল । প্রাইমারি স্তরে ক্যাথলিক কনভেন্টে পেয়েছিলুম সিসটার আইরিনকে আর যাযক ফাদার হিলম্যানকে । শৈশবের বইতে বর্ণিত সমস্ত জিনিস যাতে নিজের চোখে দেখে যাচাই করতে পারি তার দিকে খেয়াল রাখতেন সিসটার আইরিন আর স্বদেশ আয়ারল্যাণ্ডে গেলে অনেককিছু সংগ্রহ করে আনতেন, স্কুল সংল্গন ফার্মে নিয়ে গিয়ে ফল, ফুল, গাছ, জন্তুতের চাক্ষুষ করাতেন । ফাদার হিলম্যানের সৌজন্যে আমি কনভেন্টে ভর্তি হয়েছিলুম ; উনি ফোটো তুলতে ভালোবাসতেন আর বাবার সঙ্গে ওনার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল, আমাকে দোকানে দেখতে পেয়ে সাড়ে তিন বছর বয়সে নিয়ে গিয়ে ট্রানজিশান ক্লাসে ভর্তি করে দেন; সপ্তাহে একদিন চার্চে বাইবেল ক্লাসে নিয়ে গিয়ে ওল্ড আর নিউ টেস্টামেন্টের কাহিনি শোনাতেন । পরে যখন ব্রাহ্ম স্কুল রামমোহন সেমিনারিতে ক্লাস সিক্সে গিয়ে ভর্তি হলুম, কোনো শিক্ষকের সঙ্গে নৈকট্য গড়ে উঠল না ; এই স্কুলে যিনি আমাকে বাংলা সাহিত্যে আগ্রহী করলেন, তিনি গ্রন্হাগারিক নমিতা চক্রবর্তী , আমার ‘রাহুকেতু’ উপন্যাসের সুমিতাদি।
মা আর বাবার কাছ থেকে যা পেয়েছি তা হল সততা, নিজের বিশ্বাসের সমর্থনে একক লড়াই করার চারিত্র্য । বাবা দোকানদার হয়েও সৎ ছিলেন, যা আজকের দিনে অকল্পনীয় । কেবল সৎ নয়, তাঁর ছিল সৎসাহস । হাংরি আন্দোলনের সময়ে আদালতের মামলায় বন্ধুরা যখন আমার বিরুদ্ধে মুচলেকা লিখে রাজসাক্ষী হয়ে গেল, আর লড়াইটা আমার একক হয়ে দাঁড়াল, তখন আমি আমার চরিত্রগঠনে মা আর বাবার অবদানের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলুম । বাবা কলকাতায় লালবাজারে গিয়ে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে তর্ক করেছিলেন যে অমন মকদ্দমা কেন করা হয়েছে আর তখনই জানা যায় যে কলকাতার কয়েকজন সমাজকর্তা-বুদ্ধিজীবীর নালিশ কাজ করেছে এর পেছনে, যাদের বলা হয় এসট্যাবলিশমেন্টের ধারক-বাহক । মকদ্দমা চলার সময়ে বাবা কয়েকবার পাটনা থেকে দুএক দিনের জন্য দোকান বন্ধ করে কলকাতার ব্যাংকশাল কোর্টে আসতেন । যারা আমার সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছিল আর চামড়া বাঁচাবার জন্য রাজসাক্ষী বা সরকার পক্ষের সাক্ষী হয়ে গেল তাদের পরিবারের কাউকে কোনো দিন আসতে দেখিনি কোর্টে ; অর্থাৎ তাঁরা তাঁদের ছেলের সাহিত্যকর্মকে সমর্থন করতে পারেননি।
বাবা আমাদের বাড়ির ক্ষমতাকেন্দ্র হলেও ছোটোদের কাউকে শাসন করতেন না । তাঁর কাছে অভিযোগ জানালে তিনি বলতেন, “অ, ও শুধরে নেবে ।” তারপর যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে বলতেন, “কী, শুধরে নিবি তো ? বড় হয়েছিস, শুধরে নিতে শেখ।” বড়জেঠা শাসন করতেন, নিজে থেকে নয়, জেঠিমা-কাকিমারা অভিযোগ করলে, কিন্তু অভিযোগ করলে তিনি বিরক্ত হতেন । বড়জেঠার দুই মেয়ের বিয়ে আমার শৈশবেই হয়ে গিয়েছিল । মেজজেঠা আর কাকাদের মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্হা করেন বাবা, তাঁদের শৈল্পিক উদাসীনতায় ওদের বয়স বেড়ে যাচ্ছিল ; তাছাড়া বিয়ের খরচের ব্যাপারটাও ছিল । মেজজেঠার এক মেয়ে মীনাক্ষী একজন বিহারি ছেলেকে বিয়ে করতে চাইলে মেজজেঠা অমত জানান ; মেজজেঠার অমত হওয়ায় বাবা তাঁকে বোঝালেও তিনি রাজি হননি । বাবা তাঁর বিরুদ্ধতা করে মেজজেঠাকে অপমানিত করতে চাননি । শেষে আমাকে টাকাকড়ি দিয়ে বলেন যে ওরা কোথায় গিয়ে বিয়ে করতে চাইছে সেখানে গিয়ে সম্প্রদান করে আয় । আমার ছোটোশালী রমলা এক যুবককে বিয়ে করতে চাইলে নাগপুরে অভিভাবকরা রাজি হলেন না, তখন তার বিয়েও দরিয়াপুরের বাড়ি থেকে হল । রমলা ২০১৬ সালে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে ।
দশ
দাদা যখন চাইবাসায় পোস্টেড ছিলেন সেখানে সুধীর চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে বেলার সঙ্গে পরিচয় হয়, আর দাদা পাটনায় গিয়ে বাবাকে বিয়ের কথা জানাতে তিনি তক্ষুনি রাজি হয়ে যান । দাদা আসলে ওই বাড়ির সাহিত্যানুরাগী বিবাহিতা যুবতী মন্টিদির প্রেমে পড়েছিলেন, মন্টিদি আর দাদা দুজনেই স্হিতাবস্হা বজায় রাখা মনস্হ করেন । পরিবারটির সঙ্গে যাতে চিরকালীন যোগাযোগ থাকে তাই দাদা বেলাকে বিয়ে করেন । শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাস ‘কিন্নর কিন্নরী’তে বিস্তারিত লিখেছেন এ-ব্যাপারে ।
আমি অফিসের কাজে নাগপুরে গিয়ে কয়েকদিনের পরিচয়ের পরই রাজ্যস্তরের হকি খেলোয়াড় আর সহকর্মী সলিলা মুখোপাধ্যায়কে বিয়ের প্রস্তাব দিতে ওর অভিভাবকরা সেদিনেই সায় দেন । বাবাও টেলিগ্রামে অনুমোদন জানিয়ে দেন । কয়েকদিনের পরিচয়ের পরই এই বিয়েকে মা আর বাবা বলতেন, “তোদেরটা বৈপ্লবিক বিয়ে, পরিবারদের মাথা গলাতে হল না, হপ্তার পর হপ্তা রোদ-বৃষ্টি ঠেঙিয়ে প্রেম করতে হল না, ব্যাস, একজন আরেকজনকে বললি বিয়ে করব, করে ফেললি ।”
আমি লেখালিখির চেষ্টা করছি, মায়ের কাছে সেকথা জানতে পেরে ১৯৫৮ সালে বাবা আগফা-গেভার্ট কোম্পানির একটা দামি ডায়েরি দিয়েছিলেন, আর তাতেই আমি কবিতা মকসো করা শুরু করেছিলুম । বাড়িতে ইংরেজি ভাষার পছন্দের বইয়ের সংগ্রহ গড়তে চাই জানতে পেরে বাবা বলতেন বইয়ের তালিকা তৈরি করে দিতে । বইয়ের দোকানে গিয়ে বই পছন্দ করে নিতুম আর পেয়ে যেতুম । বাংলা বই, বিশেষ করে কবিতার বই দাদা কলকাতা থেকে নিয়ে আসতেন । পরে বিদেশি বন্ধুদের কাছ থেকেও প্রচুর বই আর পত্রিকা পেতুম । হাংরি আন্দোলনের সময়ে কলকাতার পুলিশ আমায় গ্রেপ্তার করতে এসে আমার বইগুলো নিয়ে সারা ঘরে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলেছিল । বাবার দোকানের কাচের আলমারি ভেঙে দিয়েছিল । মায়ের বিয়ের তোরঙ্গ ভেঙে লণ্ডভণ্ড করার সময়ে ওনার বিয়ের পুরোনো বেনারসি ভাঁজ থেকে ছিঁড়ে গিয়েছিল । কিন্তু আমাকে যখন কোমরে দড়ি বেঁধে, হাতে হাতকড়া পরিয়ে রাস্তা দিয়ে হাটিয়ে নিয়ে গেল পুলিশ, তখন বাবাকে বেশ বিচলিত দেখেছিলুম, যা উনি সচরাচর হতেন না । ছোটোবেলায় আমি বাড়ি থেকে বেশ কয়েকবার পালিয়েছি ; ফিরে এসে মনে হয়নি যে বাবা বিচলিত ; উনি আমাকে এই প্রসঙ্গে কোনো কথা জিজ্ঞাসাও করতেন না । পরে, আমার মেয়ের কাছে গল্প করেছিলেন যে আমি ওনাদের না জানিয়ে বাড়ি থেকে পালাতুম।
১৯৬৩ সালের এপ্রিলে অ্যালেন গিন্সবার্গ আমাদের দরিয়াপুরের বাড়িতে এসে ছিলেন কয়েক দিন । তিনি নানা শহরে ঘুরে বেশ কিছু ফিল্মে ফোটোম তুলেছিলেন আর সেগুলো বাবাকে দেন ডেভেলাপ করার জন্য । বাবা ডেভেলাপ করে দ্যাখেন গিন্সবার্গ কেবল নুলো, ভিখারি, দুস্হ, পথের পাশে অসুস্হ লোক, কুষ্ঠরোগি– এদের ফোটো তুলেছে । তখন গিন্সবার্গের সঙ্গে ওনার একচোট ঝগড়া হয়েছিল । বাবা গিন্সবার্গকে বলেছিলেন, “তোমরা যতই বড় কবি-লেখক হওনা কেন, আমাদের দেশটাকে এইভাবেই দেখাতে চাইবে ; কেন ? ফোটো তোলার আর কোনো বিষয় কি নেই !” গিন্সবার্গ সম্পর্কে যে গবেষকরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তাঁদের সবাইকে এই ঘটনার কথা জানালেও, কেউই নিজেদের লেখায় এই বিতর্কটা অন্তর্ভুক্ত করেননি । পরে , পাটনার বাড়িতে বা কলকাতায়, বিদেশিরা এলে আমি তাঁদের বলতুম যে ফোটো তুলে থাকলে দেশে ফিরে ডেভেলাপ আর প্রিন্ট করিও ।
আমার মায়ের জন্ম ১৯১৬ সালে, পানিহাটিতে । মায়ের ডাক নাম ভুল্টি । মায়ের বাবা, কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পানিহাটির রামচাঁদ ঘাট রোডে ‘নিলামবাটী’ নামে এক একান্নবর্তি পরিবারের সদস্য ছিলেন । কিশোরীমোহন ছিলেন, কলকাতা ও সেকেন্দ্রাবাদে, ম্যালেরিয়া রোগের কারণ নির্ণয়কারী ও ১৯০২ সালে সেকালে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ডাক্তার রোনাল্ড রস-এর সহকারী । তাঁর অবদানের জন্য ১৯০৩ সালে দিল্লি দরবারের সময়ে কিশোরীমোহনকে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্বর্ণপদক দেয়া হয়েছিল । ২০১৩ সালে প্রকাশিত তাঁদের ‘দি ফ্লাইং পাবলিক হেল্হ টুল : জেনেটিকালি মডিফায়েড মসকিটোজ অ্যান্ড ম্যালেরিয়া কন্ট্রোল’ ( সায়েন্স অ্যাজ কালচার, ল্যাংকাস্টার, ইউ কে ) গবেষণাপত্রে উলি বিজেল এবং ক্রিস্টোফ বোয়েট অধ্যাপকদ্বয় জানিয়েছেন যে উপনিবেশের নেটিভ হবার কারণে কিশোরীমোহনের নাম রোনাল্ড রসের সঙ্গে সুপারিশ করা হয়নি । সমাজ সেবার কাজে স্ত্রীর গয়না এবং পৈতৃক সম্পত্তি বেচে, আর সঞ্চয়ের পুঁজি খরচ করে তিনি দেউলিয়া হয়ে যান, আর মায়ের বিয়ের কয়েক বছর পরই মারা যান ।
সংসারের ক্ষমতা মায়ের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যাবার পর মায়ের চরিত্রে লুকোনো কিশোরীমোহন বেরিয়ে আসে । প্রায়ই দেখতুম ইমলিতলার প্রতিবেশিরা এসে মায়ের কাছে নিজেরদের আর্থিক দৈন্য আর পারিবারিক দুর্দশার গল্প করছে, আর মা তাদের সাহায্য করছেন, পয়সাকড়ি দিয়ে তো বটেই, চাল-ডাল, পুরোনো বাসনপত্র আর ব্যবহৃত জামাকাপড় দিয়ে । মায়ের বোনেদের বিয়ে আরও গরিব পরিবারে হয়েছিল বলে পুজোয় পাওয়া শাড়ি-চটি ইত্যাদি নিজে না পরে বোনেদের বা নিলামবাটীর দুস্হ জ্ঞাতিদের পাঠিয়ে দিতেন বা যখন নিজে যেতেন তখন নিয়ে যেতেন । যদিও মা পরিবারের ডি ফ্যাক্টো কর্ত্রী ছিলেন, কিন্তু ইমলিতলার বাড়িতে মা-বাবা-দাদা-আমি থাকতুম সবচেয়ে ছোটো ঘরটায় । লন্ঠনের আলোয় পড়াশোনা ।
সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে থাকার চারিত্রবৈশিষ্ট্যের দরুণ বড়জেঠা সংসারের সমস্ত ব্যাপারে মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করতেন । আমার মনে আছে, ১৯৫১ সালে যে বছর প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল, কোন দলকে ভোট দেয়া হবে তা নিয়ে আলোচনার শেষে মায়ের নির্ণয় সবাই মেনে নিয়ে ছিলেন, অর্থাৎ যার যে দলকে ইচ্ছে ভোট দেবে । কলকাতায় নাকতলায় থাকতে অবাক লাগত দেখে যে বাড়ির কর্তা যে দলের সমর্থক, পরিবারের সকলেই সেই দলকে ভোট দ্যায়, অথচ তারাই আবার ডাইন্যাস্টিক পলিটিক্সের তর্ক তোলে !
স্কুলে ভর্তি হয়ে টের পাই যে মা শুদ্ধ হিন্দি জানেন না, ইমলিতলার ‘ছোটোলোকি’ বুলি দখল করে ফেলেছেন, আর তার বহু শব্দ যে শুদ্ধ হিন্দিতে অশোভন, এমনকি অশ্লীল, তা উনি অনেক পরে জানতে পারেন, যখন আমরা ইমলিতলা ছেড়ে দরিয়াপুরে সুন্নি মুসলমান পাড়ায় চলে যাই । পানিহাটিতে মেয়েদের স্কুল তখনও ছিল না বলে মা নিরক্ষর ; নিজেকে শিক্ষিত করে তোলেন দাদা স্কুলে ভর্তি হবার পর ।
ইমলিতলার বাড়িতে হিন্দুত্ব সামলাবার কাজ ছিল পুজারী বাড়ি থেকে আসা বড়-জেঠিমার । সেকারণে মা এবং কাকিমারা প্রতিদিনের ধর্মাচরণ থেকে নিজেদের আর আমাদের মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন । জনৈক পাদরির আর্থিক সৌজন্যে প্রাইমারি স্তরে আমি ক্যাথলিক স্কুলে পড়েছিলুম ; মা ঘটিতে গরম জল ভরে আমার শার্ট-প্যান্ট আয়রন করে রাখতেন। আমার বাংলা বনেদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল বলে মায়ের নির্দেশে আমাকে ব্রাহ্ম স্কুলে ক্লাস সিক্সে ভর্তি করা হয়েছিল ।
দরিয়াপুরে পাকাপাকি চলে আসার পরও ইমলিতলার সদস্যদের দায়িত্ব মা ছাড়েননি ; সপ্তাহে এক দিন গিয়ে টাকাকড়ি আর চাল-ডাল-আনাজের ব্যাপারটা সামাল দিয়ে আসতেন । গোলা রোডের এক বানিয়ার দোকানে তালিকা দিলে সে যাবতীয় জিনিস ইমলিতলা আর দরিয়াপুরে পাঠিয়ে দিত । পুজোর সময়ে পোশাকের ভেদাভেদ মেটাতে সবায়ের জন্য ছিল একই কাপড়ের শার্ট আর ফ্রক, এমনকি জেঠা-কাকারাও সেই কাপড়ের শার্ট পরতেন । দাদা চাকরি পাবার পর দাদার চাকুরিস্হলে গিয়ে মা মাঝেমধ্যে সপ্তাহখানেকের ছুটি কাটিয়ে আসতেন । দরিয়াপুরের বাড়িতে কাজের মাসি রান্না করে দিত । নিম্নবর্ণের হাতে রাঁধা ভাত বাবা খেতেন না বলে ভাতটা আমিই বসিয়ে দিতুম । রান্নায় মাকে সাহায্য করতে হতো বলে ডাল-তরকারিও রাঁধতে শিখে গিয়েছিলুম ।
হাংরি আন্দোলনের সময়ে দাদার আর আমার বন্ধুরা কোর্টে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে গেছেন শুনে মা, যিনি ছিলেন অত্যন্ত চাপা প্রকৃতির, নিজের ক্রোধ সামলাতে পারেননি । আমি তাদের চিঠি ইত্যাদি ছিঁড়ে ফেলছি দেখে বলেছিলেন, ‘সব নিয়ে গিয়ে গুয়ের ডাবায় ফ্যাল ; সব কটাই আহাম্মক, অকৃতজ্ঞ ।’ আমার আর দাদার লেখালিখি সম্পর্কে উনিই ছিলেন প্রধান উৎসাহদাত্রী । ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ নামে যে কবিতাটা নিয়ে মকদ্দমা হয়েছিল সেটা মা-বাবা-ঠাকুমা সকলেই পড়েছিলেন । হৃদরোগের লক্ষণগুলোর সঙ্গে তখন আমরা ততটা পরিচিত ছিলুম না, মাও তাঁর কষ্টের কথা বলতেন না । লখনউতে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৮ই নভেম্বর ১৯৮২ মারা যান ।
১৯৫০ থেকে চিনতুম ফণীশ্বরনাথ রেণুকে, হিন্দি ভাষার সাহিত্যিক, যখন তিনি নেপালের রাণাদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে আহত হয়ে ভর্তি ছিলেন পাটনার ভোমরপোখরের নার্সিং হোমে, বড়দিদের বাড়ির ঠিক সামনে, লতিকাদি সেখানে নার্স ছিলেন, লতিকা রায়চৌধুরী, রেণু ওনার প্রেমে পড়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে রাজেন্দ্রনগরের ফ্ল্যাটে থাকতেন, জানতেন না আমি লেখালিখি করি । ১৯৬৪ সালে গ্রেপ্তার হবার পর জানলেন, আর হিন্দি পত্র-পত্রিকায় আমাদের নিয়ে নিয়মিত লিখলেন, যখন কিনা বাঙালা পত্র-পত্রিকা সেসময়ে আমাদের পোঁদে বাঁশ করে চলেছে। রেণু উদ্বুদ্ধ করলেন এস এইচ বাৎসায়ন অজ্ঞেয়কেও, আর উনিও আমাদের হয়ে কলম ধরলেন । রেণুর “বনতুলসী কা গন্ধ” বইতে “রামপাঠক কা ডায়েরি” নামের গদ্যে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন হাংরি আন্দোলন নিয়ে । ওনার রাজেন্দ্রনগরের বাড়িতে প্রায়ই যেতুম সন্ধ্যায় মদ খেতে, আমি নিয়ে যেতুম গাঁজা, বেশ জমতো, আমাদের আড্ডা, অনেক তরুণ হিন্দি কবি-লেখকও আসতো । সকালে পৌঁছোলে তাড়ি খাওয়া হতো, তাড়ির ওপর এলাচগুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে । রেণু মারা গেছেন ১৯৭৭ সালে । লতিকাদিকে রেণুর প্রথম পক্ষের ছেলেরা গ্রামে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে মারা যান ।
১৯৬৫ সালে হিন্দি কবি রামধারীসিং দিনকর ডেকে পাঠিয়েছিলেন ওনার বাড়ি, রেণুর বাড়ি যাবার পথেই ওনার বিশাল বাড়ি, ১৯৬৪ পর্যন্ত এম পি ছিলেন, সবে ফিরেছেন দিল্লি থেকে, বললেন, “আমি তোদের সম্পর্কে শুনেছি আর তোদের বিপ্লবকে সমর্থন করি।” বিপ্লব শব্দটা ব্যবহার করতে শুনে কিছুটা অবাক লেগেছিল, বুঝতে পেরে উনি বললেন, উনি একজন “খারাপ গান্ধীবাদী” কেননা যখন দ্রোহ দরকার তখন গান্ধীবাদে নিজেকে বেঁধে রাখলে চলে না । বলেছিলেন, যেখানে-যেখানে বক্তৃতা দিতে ডাকবে সেখানে-সেখানে তোদের সম্পর্কে বলব।” ওনার বক্তৃতার ফলে বহু হিন্দি পত্রিকায় আমার ফোটো আর হাংরি আন্দোলনের খবর বেরোতো । দিনকর মারা গেছেন ১৯৭৪ সালে ।
১৯৬৪ সালে তারাশঙ্করের টালার বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলুম, তারাশঙ্করের মামারা পাটনার, ওনারা বলেছিলেন দেখা করতে, তারাশঙ্কর কথা বলতে চান আমাদের সঙ্গে । ওনাকে আমাদের বুলেটিনগুলো দিলুম । রেখে নিলেন । মেদিনীপুরে বক্তৃতা দিতে গিয়ে হাংরি আন্দোলনের বিরুদ্ধে বলে এলেন । পরে যখন রামধারি সিং দিনকরকে তারাশঙ্করের বক্তৃতার কথা বলেছিলুম, দিনকর বলেছিলেন, “ওয়হ পুরানে খেয়ালাতকে হ্যাঁয়, জানতা হুঁ উনহে।”
১৯৭৫ নাগাদ কলকাতায় দেবী রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে দেবী জানালো যে অন্নদাশঙ্কর রায় আমার সঙ্গে দেখা করতে চান । জানি না ১৯৬৪-৬৫ সালে দেখা করতে চাননি কেন । আমি তখন লেখালিখি করতে পারছি না, মনেই আসতো না কোনো কথা গুছিয়ে লেখার । ওনার বাড়ি গেলুম । রফিক হায়দার নামে একজন বাংলাদেশী কবি ছিলেন ওনার বাড়িতে, কিন্তু মনে হল তিনি আমাদের আন্দোলনের কথা শোনেননি, সম্ভবত তখন কলকাতা থেকে আন্দোলন চলে গেছে উত্তরবঙ্গে আর ত্রিপুরায় । অন্নদাশঙ্কর নিজের কথাই বলে গেলেন, আমি আর দেবী শ্রোতা, কেন দেখা করতে চেয়েছিলেন বুঝতে পারিনি । ওনার কথাগুলো দেবী লিখে নিয়েছিল একটা খাতায় ।
১৯৪৮ সালে, প্রথম নিল ডাউন হয়েছিলুম রামমোহন রায় সেমিনারিতে, হিন্দি স্যারের ক্লাসের বাইরে বারান্দায়, বৃষ্টিতে হিন্দি বই ভিজে চুপচুপে হয়ে গিয়েছিল বলে, বলেছিলেন, “রাষ্ট্রভাষাকা সন্মান করনা সিখো গধহা কঁহিকা ।” বারান্দার বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছে, তখনও জানতুম না যে ওটা রাষ্ট্রভাষা নয়, সরকারি ভাষা । গাধাদের দেখেছি বটে চুপচাপ দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে, আর ছাতামাথায় মানুষদের দিকে তাকিয়ে কান নাচিয়ে হাসছে ।
এগারো
১৯৮৮ সালে, ট্যুরে যাবো বলে লখনউয়ের বাস স্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করছিলুম ; হঠাৎ অধস্তন এক যুবতী অফিসার যার বয়স আমার অর্ধেক কোথা থেকে উদয় হয়ে আমার হাত ধরে বলে উঠল “চলুন পালাই” । বললুম, আমি রায়বরেলি গ্রামীণ ব্যাংকের বোর্ড মিটিং অ্যাটেণ্ড করতে যাচ্ছি । যুবতী বলল, “তাতে কী হয়েছে, আমিও যাবো আপনার সঙ্গে, অপেক্ষা করব ওদের দপতরে, মিটিং শেষ হয়ে গেলে দুজনে উধাও হয়ে যাবো কোথাও, আমার কাছে যথেষ্ট টাকা আছে, তৈরি হয়েই বেরিয়েছি ।” শুনে, মাথায় আর রগে হাতুড়ির আওয়াজ শুনতে পেলুম । এই অফিসার আমারই বিভাগের, প্রায় প্রতিদিন বাংলা শাড়ি আর শাঁখা-রুলি পরে অফিসে আসে, বলল, “আপনাকে যে ভালোবাসি তা আপনার স্ত্রী জানেন ।” কোনো রকমে ছাড়ালুম । মেয়েটি আত্মহত্যা করে নিলে । নিজের কাপুরুষ চরিত্রের জন্য বেঁচে গেলুম, ওফ । বিয়ের পর আমি আর কোনো লফড়ায় ফাঁসাতে চাইনি নিজেকে, সুযোগ পেলেও, মনে হয়েছিল এবার শান্তি দরকার, তবুও নিজেই অশান্তি ডেকে এনেছি, ভেতরের লোচ্চা-লোফার কামড়ে ধরেছে ।
১৯৯০ সালে,হিমালয়ের তরাইতে দেশি গোরুর সমীক্ষা করতে গিয়ে এক মরা বাঘিনীর প্রেমে পড়েছিলুম, মরা বাঘিনীর গোলাপি যোনি দেখে চাঞ্চল্য ঘটছিল লিঙ্গে । রাতের বেলায় বাঁশে চিৎ করে চার পা বেঁধে বাঘিনীকে রাখা হয়েছিল এক পাঞ্জাবি শিখের গ্যারাজে । প্রচুর ওল্ড মঙ্ক টেনে শুয়ে পড়েছিলুম বাঘিনীর বুকে, মাই চুষেছিলুম, আর কাঁদছিলুম, বাঘিনীকে ভালোবেসে, বীর্য ঝরিয়ে, উত্তরণের আরাম হল। কবিসন্মিলন পত্রিকার সহসম্পাদক শংকর চক্রবর্তী এই ঘটনা নিয়ে লেখা আমার কবিতা পড়ে ব্যোম ; মধ্যবিত্ত বাঙালির কল্পনাজগত আক্রান্ত হলে বুঝতে পারি অস্তিত্ব ফাটিয়ে চৌচির করে আত্মসন্দেহের নীহারিকাপূঞ্জ ভরে দিতে পেরেছি । আসলে তাদের অভিজ্ঞতা বেশ সীমিত, ভারতবর্ষকে দেখেছে পর্যটকের চোখ দিয়ে । এটা নিয়ে আমি একটা গল্প লিখেছিলুম, অজিত রায়ের ‘শহর’ পত্রিকায়, ‘দুধসন্দর্ভ’ নামে।
১৯৮০ সালে, কোমরের তলা থেকে বিকলাঙ্গ এক অপরূপ সুন্দরী তরুণী কেরানিকে বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে আয়া আসেনি একদিন, ও যেতো পেরামবুলেটারের মতন একটা গাড়ি করে, কী করা যায় ভেবে উঠতে পারছিলুম না, কেরানি আর বিভাগীয়প্রধানের শ্রেণি-বিভেদ বেশ দৃষ্টিকটু । অফিস ছুটির পর আরেকজন মুসলমান অফিসারই ছিলেন আমার সঙ্গে, তিনি হিন্দু তরুণীকে তুলতে চাইলেন না, বাবরি মসজিদ তখন ভাঙা হয়ে গেছে, আমি পাছার তলায় হাত দিয়ে তুলে নিলুম, মনে হল তরুণীটি ইচ্ছেকরে নিজের যোনিকে আমার লিঙ্গের সঙ্গে চেপে ধরল, ওর হুইলচেয়ার ঠেলাগাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাবার সময় আমার প্রেমিকা-নিরপেক্ষ লিঙ্গ ফুলে উঠল, তরুণীর ইশারার জন্য আপশোষ হল । ঘটনাটা নিয়ে আমার একটা ছোটোগল্প আছে, সুকুমার চৌধুরীর ‘খনন’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, ‘অনিশ্চয়তা নিয়ে দুটি গল্পের বিনুনি : একটি প্রেমের অন্যটি রঙ্গকৌতুকের’ শিরোনামে ।
১৯৪৯ সালে, প্রথম স্ট্যাণ্ড আপ অন দি বেঞ্চ হয়েছিলুম, ইংরেজি ক্লাসে, ওয়র্ডসওয়র্থের ড্যাফোডিল্স কবিতা ব্যাখ্যা করার সময়ে আমি সিসটার আইরিনের দেয়া শুকনো ড্যাফোডিল্স ফুল দেখিয়ে বলেছিলুম, জানি স্যার, এই যে, বইয়ের ভাঁজ থেকে বের করে । শিক্ষক বলেছিলেন, “ইয়ার্কি মারবার জায়গা পাওনি, স্ট্যাণ্ড আপ অন দি বেঞ্চ।” উনি বুঝিয়েছিলেন যে কচুরিপানার বেগুনি রঙের ফুলকে বলে ড্যাফোডিল্স। যখন ইউরোপে গেলুম তখন পথের ধারে-ধারে দেখলুম ড্যাফোডিল্স ফুল, দেখলুম লাল রঙের ফুল যাকে ইউরোপীয়রা বলে পপি, অথচ যা পোস্তগাছের ফুল নয় । ১৯৪৯ সালে,দরিয়াপুর পাড়ায় সন্ধ্যায় মাতাল আর গঞ্জেড়ি মাস্তানদের মারামারি চেঁচামেচি চিৎকার শুরু হতো বলে, আমি তার চেয়েও জোরে চিৎকার করে পড়া মুখস্হ করার চেষ্টা করতুম। তার ফল হতো । বাইরের চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে যেতো । দরিয়াপুরে আমাদের বাড়িটা ছিল একটা বাতিল গোরস্তানের ধারে ; গোরস্তানের কেয়ারটেকার আল্লু মিয়াঁ ঝুপড়ি তৈরি করে নিজের দুই মেয়েকে দিয়ে রাতের বেলায় ব্যবসা করাতো, তাদের বররা দালালের কাজ করতো, মাঝে-মাঝে টাকার বাঁটোয়ারা নিয়ে শশুর আর জামাইদের ভেতর ঝগড়া হতো, অকথ্য গালাগাল । সেটা ছিল ইমলিতলার পর আমার গালাগাল শেখার উঁচু ক্লাস ।
১৯৯৪ সালে সলিলা চাকরি ছেড়ে দেবার পর ওকে সঙ্গে নিয়ে ট্যুরে যেতুম, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্যে । ১৯৯৫ সালে মালদায় গিয়ে স্তম্ভিত হলুম টেরাকোটা মসজিদ দেখে, তার আগে কেউ এই মসজিদগুলোর সংবাদ দেয়নি, সকলেই বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দিরের কথা বলতো । সুবো আচার্যের বাড়ি বিষ্ণুপুরে, যখন গিয়েছিলুম তখন টেরাকোটা মন্দির দেখেছিলুম, ষোলো থেকে উনিশ শতকের মাঝে তৈরি । মালদায় গিয়ে জানলুম যে মসজিদগুলো তার বহু আগের । আদিনা মসজিদ তৈরি করিয়েছিলেন সুলতান সিকন্দর শাহ ১৩৬৪ থেকে ১৩৭৫-এর মাঝে । লোটন মসজিদ তৈরি হয়েছিল ১৪৭৫ সালে । ১৪৮০ সালে মিরশাদ খান তৈরি করিয়েছিলেন তাঁতিপাড়া মসজিদ । ১৫৩১ সালে কদম রসুল মসজিদ তৈরি করিয়েছিলেন সুলতান নুসরত শাহ ; এই মসজিদের কেয়ারটেকার একটা পায়ের ছাপ দেখিয়ে বলেছিলেন যে ওটা হজরত মোহম্মদের , শুনে পিলে চমকে গিয়েছিল, দেওবন্দিরা জানতে পারলে আস্ত খেয়ে ফেলবে লোকটাকে, সে আবার প্রতি সকালে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে আসতো আর সন্ধ্যায় ফিরে যেতো । মসজিদগুলো দেখতে-দেখতে শৈশবের ইমলিতলা পাড়ার মসজিদের কথা মনে পড়ছিল, তার ভেতরেও আমাদের প্রবেশ অবাধ ছিল, এই মসজিদগুলোর মতন ।
১৯৬৫ সালে কলেজ স্ট্রিটে ছাতার খোঁচা দিয়ে এক ভদ্রলোক বললেন, “এই, তোরা আমার বাড়ি আসিস না কেন রে”? সুবিমল বসাক ওনার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে “আমরা যাবো যে কোনো দিন”, বলার পর উনি বললেন, “সকালের দিকে আসিস।” উনি চলে যাবার পর সুবিমল বলল, “জানো কে ? জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।” গেলুম ওনার বাড়ি, মানিকতলায় নেমে, তারপর ধানখেতের ভেতরে আলের ওপর দিয়ে দূরে একটা চালাবাড়ি, সেরকমই নির্দেশ দিয়েছিলেন । আলের ওপর দিয়ে হাঁটার সময়ে বুঝতে পারলুম যে রাতের বেলায় সাপের ভয়ে ছাতাকে ছড়ির কাজে লাগান । ওনার বাড়িতে পৌঁছোলে, জানতে চাইলেন আমি কি-কি করেছি যে সবাই এতো চটে গেছে । সবই বললুম ওনাকে, মুখোশ, জুতোর বাক্সের রিভিউ, ব্ল্যাংক কাগজে গল্প, বিয়ের কার্ড, স্টেনসিল করা ড্রইং ইত্যাদি । বেশ হাসছিলেন শুনে, যখন শুনলেন যে জুতোর বাক্স রিভিউ করতে দিয়েছিলুম, তখন একেবারে জোরে-জোরে হাসতে লাগলেন । বললেন, “মামলা ঠুকেছে বলে বন্ধ করিসনি, তোরা না করলে কে-ই বা মুখোমুখি প্রতিবাদ করবে।” এখন ওই ধানখেতে আবাসনের পর আবাসন । বেশ কয়েকজন নামকরা কবি থাকেন সেই আবাসন-হয়ে-যাওয়া-ধানক্ষেতে । জানি না ধানক্ষেতের উড়ন্ত বাতাসের সবুজ গন্ধ তাঁরা পান কিনা ।
১৯৯৮ সালে কেদার ভাদুড়ির গাঙ্গুলিবাগানের বাসায় বসে মদ খাচ্ছি, একটি তরুণ প্রবেশ করতেই গম্ভীর হয়ে গেল কেদার, আমাকে বলল, পুরোটা চোঁচোঁ করে খেয়ে বাড়ি চলে যাও, কালকে আবার বসা যাবে। পরের দিন গিয়ে জানলুম তরুণটি কেদারের প্রথম পক্ষের ছেলে । টিউশানি করবার সময়ে কচি এক তরুণীর প্রেমে পড়ে তার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক করে ফেলেছিল কেদার, তারপর তাকে বিয়ে করতে হয়েছিল, প্রথম বউকে ডিভোর্স দিয়ে । প্রথম বউয়ের ছেলে প্রতিমাসে খোরপোষের টাকা নিতে আসতো । কেদারের তরুণী বউ কখনও আসতো না গাঙ্গুলিবাগানের বাড়িতে, প্রতিবেশীদের কেউ একজন বলেছিল, “ও মা আপনার নাতনিও আছে, বলেননি তো !” তরুণী বউয়ের একটা মেয়ে হয়েছিল, তাকেও আসতে বারণ করে দিয়েছিল কেদার । কয়েক পেগের পর বলতো, “বড়ো যন্ত্রণা হে, বড়ো কষ্ট, বড়ো দুঃখ, ও শূলযাতনা তুমি বুঝবে না, কবিতায় লুকিয়ে রেখেছি, কাকেই বা বলব, কবিতাকেই বলি ।” কেদারের একটা চল্লিশ পাতার সাক্ষাৎকারে দ্বিতীয় পক্ষের বউ আর তার সঙ্গে আকস্মিক প্রেমের ঘটনার উত্তর দিতে চায়নি কেদার । কেদারের মৃত্যুর কথা জেনেছিলুম উত্তম দাশের ফোনে ।
অশোক ফকিরের চম্পাহাটির চালাঘরে গিয়েছিলুম আমি আর সুবিমল ১৯৬৫ সালে, উনি পানের পাতায় আফিম চাটতে দিলেন, বেশ সুন্দরী বউ, অজন্তার দেয়ালে আঁকা নারীদের মতন বৌদ্ধ চোখ । ওই বউকে ফেলে অশোক ফকির এক বিদেশিনীর সঙ্গে আমেরিকায় হাওয়া । বিদেশিনী বউটা কিছুদিন আগে ইমেল করে নিজের জটাজুট সঙ্গে হরেকৃষ্ণ ছাপানো উত্তরীয় কাঁধে অশোক ফকির, ওর আর মন্দিরের ছবি পাঠিয়েছিল, গিন্সবার্গের লেখা চিঠি পাঠিয়েছিল যেগুলোর কপি আমেরিকায় অনামিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠিয়েছিলুম । বিদেশিনী বউ বলেছিল অশোক ফকিরের আমেরিকাবাস নিয়ে একটা বই লিখেছে, কোনো পাবলিশার ছাপতে রাজি নয় । মার্কিন কনসুলেটে গিয়ে অশোক ফকির খবর যোগাড় করতো যে কারা-কারা কলকাতায় এসেছে আর কোন হোটেলে আছে । অশোক ফকিরের কারবার শুনে বাঙালি বউটার জন্যে মায়া হল । আমার লম্পট চোখ বুজলেই তার মুখ ভেসে ওঠে। আমেরিকাতেই মারা গেছে অশোক ফকির । শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় অশোক ফকিরকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখেছেন শুনেছিলুম । অশোক ফকিরের দেয়া আফিম খেয়ে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ওভারব্রিজের ওপর নেচেছিলুম আমি আর সুবিমল । অনেক রাত পর্যন্ত, সেসময়ে চম্পাহাটিতে এখনকার মতন নিত্যযাত্রীদের ভিড় ছিল না, একেবারে ফাঁকা স্টেশান, প্ল্যাটফর্মগুলোও ফাঁকা, অন্ধকারে ঢাকা । এখন চম্পাহাটিতে ট্রেন এলে নিত্যযাত্রীদের ঠেলাঠেলিতে অন্ধকার উধাও হয়ে যায়, ওরা সবাই যেন আফিম চেটে দৌড়োয় ।
২০০৭ সালে ইউরোপে গিয়ে নানা রকমের ওয়াইন খেয়ে আমি কোনো তফাত টের পাইনি, নেশার মাত্রাটুকু টের পেয়েছি, মদের চরিত্র নয় । গীর্জাতেও যে ওয়াইন তৈরি হয় তা জানতুম না ; গীর্জার ওয়াইন আর ফরাসিদেশের নাস্তিকদের কোম্পানির ওয়াইনে তফাত টের পাইনি । এদেশে কোনো মন্দিরে মদ তৈরি হলে ধুন্ধুমার বেধে যাবে । আসলে ইমলিতলার আর খালাসিটোলার দিশি মদ ঠররা আর বাংলার কয়েকটা আস্তরণ জমে গেছে আমার জিভের ওপর । বাংলা মদকে পিসেমশায় বলতেন ধান্যেশ্বরী । ১৯৬৫ সালে বেনারসে একজন হিপি চরস দিয়ে হনুমান তৈরি করত আর তার ল্যাজ ভেঙে ফুঁকতে দিতো । আরেকজন হিপি গঙ্গাজলের ঘটিতে এল এস ডি মিশিয়ে আনতো, তার সামনে জিভ বের করলে সে কয়েক ফোঁটা ফেলে দিতো । গঙ্গা তখন থেকেই ভিষণ নোংরা অথচ হিন্দুরা হোলি গ্যাঞ্জেস বলে বলে দুয়েকজন হিপি ওই জলে স্নান করতো । তার আগে অ্যালেন গিন্সবার্গ ওই নোংরা জলে স্নান করে ফোটো তুলিয়ে হিপিদের জন্য পথ দেখিয়ে গেছে । পাটনায় গঙ্গার ধারে হিসি করতে বললে, গিন্সবার্গ বলেছিল, তোমার হোলি রিভার, আর তুমি বলছ তার তীরে হিসি করতে !
১৯৮১ সালে লখনউতে চম্বল অঞ্চলের ট্যুরে বাবা মুস্তাকিম নামে এক ডাকাতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, যে আমার মাথায় হাত রেখে বলেছিল, “জিতে রহো” । ডাকাতের আশীর্বাদের দরুণ স্হানীয় কৃষি আধিকারিক বলেছিল, চম্বলে আর কেউ আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যে গ্রামে ইচ্ছে যেতে পারবেন । সত্যিই, বহুবার চম্বলে ট্যুরে গেছি, প্রতিটি গ্রামে লোকেরা বেশ আপ্যায়ন করেছে, জমিদাররা তাদের বাড়ির পায়খানায় হাগতে দিয়েছে । ১৯৮৩ সালে গোরখপুরে ট্যুরে গিয়েছিলুম, সেখানকার মন্দিরে শিবের পুজোয় ত্রিশূল উৎসর্গ করতে হয়, যা আমার অধস্তন অফিসার করতে চাইছিল । আমি বাইরে বাগানে ছায়ায় অপেক্ষা করছিলুম । আচমকা একজন জটাধারী সাধু, ঠোঁটের কোনে ছিলিমের ফেনা, জড়িয়ে ধরে বলে উঠেছিল, “জো তুমসে দুষমনি করেগা ওয়হ তুমসে পহলে মর জায়গা ।” কারোর মারা যাবার খবর পেলে তার সম্পর্কে সন্দেহ হয়, সাধুটার কথার জন্যে হয় না ।
১৯৫৫ সালে ইনফ্যানট্রির ক্যাম্পে গিয়ে ভোর রাতে উঠে কুড়ি-তিরিশজন সবাই ল্যাংটো হয়ে হাগতে যেতুম, গোল হয়ে হাগতে বসতুম, পাদবার খেলা খেলতুম, ছোঁচাতুম চা খাবার অ্যালুনিমিয়াম মগ দিয়ে, যৌথভাবে উলঙ্গ হতুম, কোনো লজ্জা-বালাই নেই, প্রাগৈতিহাসিক কালখণ্ডে ফেরার সুযোগের জন্য সকলে মিলে হইচই করতুম । ১৯৬১ সালে অফিসের সহকর্মী সুশীল কুমার, মণিমোহন মুখোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায় আর আমি চারজনে মিলে গিয়েছিলুম শিমুলতলায় । রাতের বেলায় একটা পাহাড়টিলায় চারজনে উলঙ্গ হয়ে ওঠার প্রতিযোগীতা করেছিলুম । সম্ভবত সুশীল কুমার জিতেছিল । পরের দিন একটা ছোট্টো পুকুর বা হাঁটুজল ডোবায় আমি, সুশীল আর অরুণ তিনজনে জলের তলায় লুকিয়ে লিঙ্গ দাঁড় করিয়ে জলের ওপরে ভাসিয়েছিলুম ; মণিমোহন চেঁচিয়ে উঠেছিল, “সাপ সাপ জলে সাপ আছে” । মণিমোহনকে সেই থেকে বলা হোতো “চপড়গাণ্ডু”; জল থেকে উঠে মণিমোহনকে বলেছিলুম, আপনাকে ওয়াটার অর্কিড দেখাতে চাইছিলুম। “ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস” উপন্যাসে আছে ঘটনাটা । ওয়াটার অর্কিড প্রদর্শনীর কথা বুড়ো বয়সেও মনে রেখেছিল মণিমোহন । সুশীল লিভারের ক্যানসারে মারা গেছে, মণিমোহন কিডনির । অরুণ পাগলিয়ে গেছে ওর জামাইয়ের পাল্লায় পড়ে, ও অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পাটনায় চাকরির সময়েও পাগলিয়ে ছিল, ঘটনাটা আছে আমার ‘ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস’ উপন্যাসে । মণিমোহনের মেয়ের সঙ্গে দাদা নিজের বড়ো ছেলের বিয়ে দিয়েছিল । অরুণের সঙ্গে দাদা বিয়ে দিয়েছিল নিজের এক শালির ।
১৯৯৫ সালে মুম্বাই থেকে ফিরে সন্দীপনের সঙ্গে দেখা করতে গিসলুম ওনার চেতলার ফ্ল্যাটে, কি-নোংরা কি-নোংরা, ঘরে বসে আছেন মেঝেয়, সামনে একটা জলচৌকি, পাশে একটা থলে থেকে “আজকাল” সংবাদপত্রে জড়ো হওয়া পাঠকদের চিঠিতে চোখ বোলাচ্ছিলেন আর বাছাই করছিলেন । বললুম, লেখালিখি না করে এসব ফালতু কাজে সময় নষ্ট করছেন কেন, সামান্য টাকার জন্যে । উনি বললেন গল্পের ম্যাটার পেয়ে যাই । ভেতরে গিয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন, স্ত্রী সেজেগুজে বেরিয়ে গেলেন । যেমন কিপ্টে ছিলেন তেমনই, জামা-প্যান্ট পরে নিয়ে, দরোজায় তালা ঝুলিয়ে, বললেন, “চলো, সুকৃতিতে গিয়ে চা খাওয়া যাবে”। ট্যাকসির ভাড়া আমিই দিলুম, চা-কাটলেটের পয়সা আমিই দিলুম । মনে হল, এই একবার আড্ডাই যথেষ্ট, ওনার সেই উইট ফুরিয়ে গেছে, সেই যখন হাওড়ায় সাইকেলে চেপে ভোরবেলায় দেবী রায়ের বাড়িতে হাংরি বুলেটিনের জন্যে লেখা দিতে আসতেন । সন্দীপন মারা গেছেন ২০০৫ সালে । এখন বুড়ো হয়ে টের পাই যে এই বয়সে পৌঁছে ঘরদোরের ধুলোবালি জমে থাকাটা কোনো গুরুত্বের ব্যাপার নয় ।
১৯৬৪ সালে হাতকড়া পরাবার সময়ে, কোমরে দড়ি বাঁধার সময়ে, পুলিশের মুখময় আলো খেলা করছিল, যেন আধুনিকতার ওপর ওদের একচ্ছত্র অধিকার, যেন এনলাইটেনমেন্ট কাকে বলে ওরাই কেবল জানে । কোমরে দড়ি বাঁধা আর হাতে হাতকড়া পরানোর ব্যাপারটা এনলাইটেনমেন্টের সঙ্গেই এসেছিল। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, পাড়ার কুকুরগুলোও আমার পেছন-পেছন কৈলাশযাত্রায় হেঁটেছিল । ২০১১ সালে সৃজিৎ মুখোপাধ্যায় “বাইশে শ্রাবণ” ফিল্মে গৌতম ঘোষকে একজন পাগল হাংরিয়ালিস্ট কবি হিসাবে তুলে ধরলে, নিবারণ, যার লেখা কোথাও কেউ ছাপতে চায় না, রবীন্দ্রনাথ নামে পুলিশের এক খোচরকে, যে আবার লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক, মোবাইলে বারবার কবিতা ছাপানোর অনুরোধ করে, সেই চারশোবিশ ফিল্ম দেখে সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছিল শুভা । কেন ? হাংরি আন্দোলনের কবিকে সৃজিৎ বদনাম করে, তাকে দিয়ে বইমেলায় আগুন ধরিয়ে, ধ্বসিয়ে দিয়েছে, তাই । না, সৃজিৎ আমার বা অন্য কোনো হাংরি কবির অনুমোদন নেয়নি, সম্ভবত এসট্যাবলিশমেন্টকে খুশ করার জন্য হাংরি আন্দোলনের কবিকে অহেতুক ঢুকিয়েছে কাহিনিতে । কাহিনি লেখককে অত্যন্ত অসৎ বলা ছাড়া আর কীই বা করা যেতে পারে। ফিল্মটায় যাদের নাম উল্লেখ করেছিল পরমব্রত, তাতে শৈলেশ্বরের নাম ছিল না, ও নিজের টাকলা গুরুদেবকে ধরে সৃজিৎকে দিয়ে আন্দোলনকারী হিসেবে নামটা ঢুকিয়েছিল, অথচ আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুচলেকা দিয়ে মামলায় রাজসাক্ষী হয়েছিল ।
সৃজিৎ ফিলমটায় একজন লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদককে পুলিশের খোচর হিসেবে দেখিয়েছে, এই ঘটনাটা সত্যি । পবিত্র বল্লভ নামে কুঁজো এক যুবক “উপদ্রুত” নামে একটা লিটল ম্যাগাজিন বের করত, বাসুদেব দাশগুপ্তের সঙ্গে বসত কফিহাউসে, সে ছিল পুলিশের ইনফরমার, হাংরি আন্দোলনের বুলেটিন, বই ইত্যাদি গিয়ে জমা দিত লালবাজার প্রেস সেকশানে । বাসুদেব মাঝে-মাঝে বলত বটে যে মুখোশ পাঠানো ঠিক হয়নি, জুতোর বাক্স দেয়া উচিত হয়নি, স্টেনসিল-ড্রইং কফিহাউসে বিলোনো ঠিক দেখায় না, ইত্যাদি-ইত্যাদি, কিন্তু সেই কথাগুলো যে পবিত্র বল্লভের, তা জানতে পারি যখন পবিত্র বল্লভ পুলিশের পক্ষের সাক্ষী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বেমালুম বলে গেল যে সে আমাকে চেনে, কফিহাউসে আমার সঙ্গে আড্ডা দিয়েছে, তার কাছে আমি লেখা চেয়েছি, ইত্যাদি ।
বারো
১৯৯২ সালের ৭ই ডিসেম্বর, তখন আমি মুম্বাইতে, ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস থেকে ডান ডিকে টার্ন নিয়ে মাহিমে ঢুকবো, দেখি দু দল মানুষ লাঠি, তরোয়াল, বর্শা, বন্দুক নিয়ে মারামারি করছে, পুলিশের দেখা নেই, মানুষ তরোয়ালের আঘাতে লুটিয়ে পড়ছে দেখে আর এগোলুম না, সোজা ব্যাক করে বাড়িতে । তার আগের দিন বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছে বলে দুএক জায়গায় মারপিট হয়েছিল, কিন্তু এরকম খুনোখুনি আমি আগে দেখিনি । দাঙ্গা কাকে বলে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল । ভাগ্যিস গাড়িটা ছিল, তাই পালাতে সুবিধে হল, কেননা রাস্তায় বাস, অটো, ট্যাক্সি কিছুই দেখিনি ফেরার সময়ে, কেবল পলায়নকারীদের গাড়ি । কেন যে দাঙ্গা হয়, কেন একজন মানুষ ভিড়ের অংশ হতে রাজি হয়, অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে কাটতে বেরিয়ে পড়ে, জানি না ।
১৯৯৩ সালের ১২ই মার্চ, আমি ভিলে পার্লে বিল্ডিঙের অফিসের অ্যাডমিনিসট্রেটিভ ইনচার্জ । অধস্তন অফিসার কয়েকজন, “বাড়িতে কাজ আছে”, বলে ছুটি নিয়ে কেটে পড়ল । একটু পরে মহিলা অফিসাররা এসে বলল যে শহরে গোলমাল চলছে স্যার আমরা বাড়ি যেতে চাই, কী গোলমাল জানে না, বললুম ঠিক আছে, যাও । তারপর শিব সেনা করে এমন একজন এসে বলল যে, স্যার শহরে পর-পর বোমা ফাটছে, কিছু একটা গোলমাল শুরু হয়েছে, হয়তো ট্রেন-বাস সব বন্ধ হয়ে যেতে পারে । হেড অফিসে ফোন করে জানতে পারলুম যে, হ্যাঁ, পুলিশ থেকে জানিয়ে দিয়েছে নানা জায়গায় বোমা ফাটানো হয়েছে, অফিস ছুটি করে বন্ধ করে দিন । পরের দিন কাগজে পড়লুম যে সন্ত্রাসবাদীরা ষড়যন্ত্র করে বোমা ফাটিয়েছে, অনেক মানুষ মারা গেছে । তার কিছুদিন পরে জানলুম কাণ্ডটা দাউদ ইব্রাহিম নামে একজন মাফিয়ার চেলাদের, যারা ঘটনার আগেই দুবাই পালিয়েছে । ঘটনাটার কথা মনে পড়লে ভয়ার্ত মহিলাদের মুখগুলো মনে ভাসে, তাঁদের কয়েকজন বুড়ি হয়ে স্বাস্হ্যের অবনতির কারণে মারা গেছেন ।
আমাদের বাড়িতে, ইমলিতলায়, দরিয়াপুরে, উত্তরপাড়ায়, জোরে পাদা আর ঢেঁকুরতোলায় কোনো বিধিনিষেধ ছিল না, বড়ো-ছোটো নির্বিশেষে সকলেই জোরে পাদতো আর ঢেঁকুর তুলতো । আমি এখনও জোরে পাদি, চেপে যাই না । এই এখন লিখতে-লিখতে পাদলুম বলে ইপিফ্যানির গর্ব হলো । কলকাতায় যে সাহিত্যসভাগুলো হয়, তাতে কাউকে পাদতে শুনিনি, কেউ কেউ পোঁদ একপাশে উঁচু করে, কবিতার শ্বাস নিচ্ছে তা দেখেছি । ৩০শে এপ্রিল ২০০৪ সাহিত্য অকাদেমির টেলিগ্রাম পেলুম যে ওরা আমাকে পুরস্কৃত করেছে ধর্মবীর ভারতীর “সুরজকা সাতওয়াঁ ঘোড়া” অনুবাদের জন্যে । পেয়েই মাথা গরম হয়ে গেল, নিজেকে শুনিয়ে বললুম, “কোন ইডিয়ট আমার নাম সুপারিশ করেছে, স্কাউণ্ড্রেলরা তো জানে আমি এইসব সাহিত্যিক তিকড়মবাজিতে নেই”। তার আগে আর পরেও, বহু মানুষকে, যাদের ইনটেলিজেন্ট বলে চালানো হয়েছে, তাদের মনে হয়েছে স্টুপিড । প্রত্যাখ্যান করে সঙ্গে-সঙ্গে একখানা চিঠি দিলুম সাহিত্য অকাদেমিকে জানিয়ে যে, As a matter of priciple I do not accept literary and cultural prizes, awards, lotteries, grants, donations, windfalls etc. They deprave sanity. প্রত্যাখ্যান করে, ইপিফ্যানির গর্ব হল । পুরস্কার যে প্রত্যাখ্যান করেছি তা শঙ্খ ঘোষ জানতেন না, প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, তাই বুঝি, আমি জানতাম না তো ! প্রণব আবার চটে গিয়ে একটা কপি পাঠিয়েছিল ওনাকে!
১৯৬৪ সালে পিসেমশায় যে উকিলকে হাংরি মামলার জন্যে বাছাই করেছিলেন, তার দপতর সোনাগাছির ঠিক উল্টো দিকে । উনি অঞ্চলের রেগুলার ভিজিটার ছিলেন বলে তাদের উকিলকে চিনতেন । পিসেমশায় বলেছিলেন, “এর মতন ফৌজাদরি উকিল সস্তায় পাবিনে।” উকিলের ঘরে বসে দেখতে পেতুম ফি শনিবার পার্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুরো কৃত্তিবাস গ্যাঙ চলেছে ভেতরে । সেন্টুদা একবার বললেন, চল চল, ওরা যে বাড়িটায় ঢুকবে তার উল্টো দিকের বাড়ির বারান্দায় উঠে ওদের কারবার দেখতে পাবি । সত্যিই তাই । উল্টোদিকের বাড়ির দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম বুদ্ধদেব বসুর বদল্যার বইয়ের প্রভাব । অর্ধেক জীবন, সম্পূর্ণ জীবন, টুকরো জীবন ইত্যাদি স্মৃতিকথায় এনারা সবকিছু চেপে গেছেন।
১৯৭৬ সালে ট্যুরে যাচ্ছিলুম হাজারিবাগে, একটা গাড়ি ভাড়া করে, সঙ্গে আমার অধস্তন অফিসার। অফিসের এক পিওন, তার নাম “ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস” আর “জলাঞ্জলি” উপন্যাসে দিয়েছি রসিক পাসওয়ান। আসলে পিওনটা ছিল রাজপুত, গোপাল সিং, কিন্তু এক পাসওয়ান মেয়েকে বিয়ে করার ফলে উঁচু জাতের পিওনরা ওর সঙ্গে মিশত না, রাজপুত-ভূমিহার অফিসাররাও ওর সঙ্গে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত । ও বলল ওকে ওর গ্রামে ড্রপ করে দিতে, আমাদের যাবার পথেই পড়বে । এক জায়গায় গাড়ি থামাতে বলে ও বলল, জঙ্গলের ভেতরে ওর গ্রামে যেতে । চললুম ওর সঙ্গে, এতো ভেতরে তো গ্রাম দেখিনি তখনও । একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে দেখলুম কিশোর-কিশোরীদের বিয়ে হচ্ছে । গোপাল সিং তখন জানালো যে ও “মালে পার্টি” করে । তখন মাওবাদীদের উদ্ভব হয়নি, মার্কসিস্ট-লেনিনিস্টদের সংক্ষেপে বলা হতো মালে । বলব না যে শুনে কিছুটা অস্বস্তি হয়নি । দেখলুম যে জোড়ায়-জোড়ায় কিশোর-কিশোরী আর যুবক-যুবতীরা বসে আছে আর তাদের বিয়ে দিচ্ছে একজন বাঙালি যুবক, ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি, কাঁধে ব্যাগ, যে বইটা থেকে মন্ত্র পড়ছে সেটা “রেড বুক” । আমি নেপাল থেকে “রেড বুক” কিনে এনেছিলুম বলে দেখেই টের পেলুম । আদিবাসী যুবক-যুবতীর বিয়ে হচ্ছে ইংরেজি মন্ত্র পড়ে । বিয়ে দিয়েই যুবকটি উধাও হয়ে গেল । গোপাল সিং ওর নাম বলতে চাইল না । আমি “ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস” আর “জলাঞ্জলি” উপন্যাসে এই যুবকটির নাম দিয়েছি অতনু চক্রবর্তী, অবশ্য অতনু চরিত্রে বহু পরিচিত বন্ধুসহ আমার নিজের জীবনের উপাদান আছে । গোপাল সিং ওই বিয়ের পর অফিসে ফেরেনি। আমিও অফিসে ফিরে চেপে গেলুম যে ওকে আমরা লিফ্ট দিয়েছি ।
১৯৬৫ সালে ডেভিড গারসিয়া নামে এক হিপি এসেছিল, গ্রিসে জুতোর দোকানে কাজ করে টাকা যা জমিয়েছিল তা নিয়েই এসেছিল, বলল, বাঙালি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে চায় । দুদিনে কোথ্থেকে পাওয়া যাবে বাঙালি প্রেমিকা । অগত্যা সোনাগাছিতে ঢুঁ, কিন্তু দুপুরে নয়, ভিজিটিং আওয়ার সন্ধ্যায় । একটা কচি মেয়েকে পছন্দ হল ডেভিডের । মেয়েটার নাম মনে আছে, বেবি । বেবি বলল, ও বাবা, এতগুলো হাঘরেকে সামলাতে পারবো না, এই সায়েব আর কোনো একজন । সকলে প্রস্তাব দিল ফষ্টিনষ্টি করতে দিতে হবে। তাতে বেবি রাজি । ঘরে ঢুকে মাটিতে পাতা বিছানায় বেবি বসতেই বাসুদেব চকাচক চুমু খেয়ে নিল জড়িয়ে। বেবির অনুরোধে আনানো হল দু-বোতল বাঙলা । খেলুম সবাই মিলে, টনক গোলমেলে হয়ে উঠলে কে যে বেবির কোথায় হাত ঢোকাচ্ছিল তার ঠিক নেই। বিপদ দেখে বেবি বলল, তোমরা বেরোও, আমি সায়েবের সঙ্গে পিরিত করে নিই । ডেভিড বেরোলো পিরিত করে, বলল, সাচ এ টিনিউইনি কান্ট অ্যান্ড স্মল বুবস, ইট ওয়াজ ওয়ানডারফুল । বেবি বুকের ওপর আঁচল ফেলে দরোজার ফাঁক থেকে মুখ বের করে বলল, আরেকজন কে আসবে চলে এসো । ঘোষভাইদের মধ্যে একজন তড়াক করে ঢুকে গেল আর মিনিট পাঁচেকেই সেরে বেরিয়ে এলো । হাঘরেদের খরচটা আমি দিয়েছিলুম । পরে, বেবির ঘরে বাসুদেব-অবনী-শৈলেশ্বর প্রায়ই যেতো, বাসুদেবের চিঠিতে বেবির বাড়ি বদলের দুঃখও আছে ।
ডেভিড গারসিয়াকে নিয়ে দুমকা গিয়েছিলুম, দুমকায় দাদার বাড়িতে পায়খানার সামনে যে কাঁঠালগাছ ছিল তাতে এঁচোড়ের গা্য়ে প্যান্ট-শার্ট ঝুলিয়ে পায়খানায় ঢুকতে হতো । ডেভিড বলল ওদের গ্রামে ফিরে গিয়ে ও এই ধরনের বন্দোবস্ত করবে যাতে গাছে হয়ে থাকা ফলের গায়ে পোশাক ঝোলানো যায় । ভাঙের শরবত খেয়ে আমাদের সঙ্গে দোল খেলে ডেভিড জানতে চাইল এটা কি রিলিজিয়াস ফেসটিভাল । ওকে জানালুম যে হ্যাঁ, এটা একজন পলিগ্যামিস্ট ব্ল্যাক গডের স্প্রিং সিজন সেলিব্রেট করার ফেস্টিভাল ।
পালামৌয়ের সদর শহর ডালটনগঞ্জে দাদার বাড়িতে ছিলুম ১৯৬৭ সালে, হরিণের ঠ্যাং দিয়ে গেল একজন সাঁওতাল, বঁটি দিয়ে কেটে রান্না হলো আর মহুয়ার রুটিসহ মহুয়ার মদ দিয়ে খাওয়া হলো, আমি কলকাতা থেকে কেস জিতে পৌঁছে গিয়েছিলুম ডালটনগঞ্জে, তাই সেলিব্রেট করা হলো বিহারি স্টাইলে, যদিও এখন শহরটা ঝাড়খণ্ডে । ডালটনগঞ্জে পৌঁছেছি শুনে স্হানীয় কবিরা একটা আড্ডার ব্যবস্হা করেছিল, যাকে ওদের ভাষায় বলে “গোষ্ঠী”, তাতে আমি আর দাদা মহুয়ার মদ খেয়ে বেশ ভালো বক্তৃতা দিয়েছিলুম ; ওখানেই একটা প্রেসে ছাপিয়েছিলুম অশ্লীলতা সম্পর্কে ম্যানিফেস্টো, “ইন ডিফেন্স অফ অবসিনিটি” পরে যেটা নানা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে, শুনেছি গবেষক ড্যানিয়েলা লিমোনেলার কাছে। ড্যানিয়েলা ইতালীয় ভাষায় আমাদের আন্দোলন নিয়ে গবেষণা করছেন, তথ্য সংগ্রহ করতে কলকাতায় এসেছিলেন ২০১৪ সালে । ১৯৬৯ সালে আমি আর সলিলা গিয়েছিলুম ডালটনগঞ্জে, দাদা তখন অন্য একটা বাড়িতে, পিসতুতো দাদা সেন্টুদাও ছিল; আমাদের আপ্যায়ণের জন্যে গেঁড়ি-গুগলি দিয়ে বিরিয়ানি বানিয়েছিল, তা রাত জেগে খাওয়া হলো মহুয়ার মদ দিয়ে ।
২০১৪ সালে বিবিসির পক্ষ থেকে ডোমিনিক বার্ন এসেছিলেন হাংরি আন্দোলন নিয়ে রেডিও প্রোগ্রাম করার জন্য । হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে উনি এতই ওয়াকিবহাল ছিলেন যে প্রশ্ন করলেন বঙ্গসংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাথ, উনিশ শতক নিয়ে । পরে, ফোটোতে ওনার ঘামে ভেজা শার্ট দেখে সলিলা বলল, “এসিটা চালিয়ে নাওনি কেন ?” আসলে প্রতিটি ব্যাপারে অভ্যাস থাকা জরুরি । ১৯৭৯ থেকে গ্রামীণ উন্নয়নের ট্যুরে ইংরেজি-বাংলা-হিন্দিতে বক্তৃতা দিতে হতো। একটা গ্রামে বক্তৃতা দিচ্ছিলুম, একজন চাষি বলে উঠল, “ এই চিন্তাটা আগে আসেনি কেন মাথায়, তাহলে গ্রামের কাজ এগিয়ে যেতো, পড়ে থাকতো না বছরের পর বছর।” বলে ফেললুম, “আপেল কেন গেছ থেকে পড়ে, তা তো আমরা আগে জানতুম না, নিউটন নামে একজন সায়ের বলার পরে জানতে পারলুম।” চাষি বলল, আপেল কেন, আম, কাঁঠাল, নারকেল পেকে গেলে সবই আপনা থেকে পড়ে যায়, ভগবান সেরকমই নিয়ম করেছেন।” টের পেলুম যে নিউটন সর্বত্র চলে না, অভিকর্ষও সকলকে বোঝানো যায় না । বললুম,”ঠিকই বলেছো, যতক্ষণ না কোনো চিন্তায় পাক ধরছে ততোক্ষণ কেউই তার বিষয়ে জানতে পারে না ।”
১৯৬৫ সালে, সুবিমল বসাকের মাসির বাড়ি গিয়েছিলুম মুর্শিদাবাদের এক গ্রামে । রাতে মশারি টাঙিয়ে শুয়েছিলুম, সকালে দেখি মশারির চালে একটা সাপ, মশারি বেশ ঝুলে এসেছে, আমাদের নড়াচড়া আর চেঁচামেচিতে সাপটা ফণা তুললো, মশারির ভেতরে হাংরি বুলেটিন ছিল কাগজে মোড়া, সেইটে দিয়ে সাপটাকে মশারি থেকে বাইরে ছিটকে ফেললুম । আমাদের চেঁচামেচি শুনে সুবিমলের মাসি আর অন্য আত্মীয়রা জড়ো হয়েছিলেন এসে, তাঁরা সাপটার পিছু নিলেন, সেটা ঢুকে গেল এক গর্তে । বেরোলুম মশারির বাইরে । এক বৃদ্ধা চিনির কৌটো নিয়ে এলেন আর কাঠপিঁপড়ে-ভরা গাছের কাছ থেকে সাপটা যে গাছের গোড়ায় ঢুকেছে সেখান পর্যন্ত লাইন করে চিনি ছড়িয়ে দিলেন, সাপের কোটরেও ছুঁড়লেন । দুপুরে ডেকে দেখালেন আধখাওয়া সাপ আর পিঁপড়ের ঝাঁক গাছের বাইরে, পিঁপড়েরা মাংসকণা নিয়ে নিজেদের বাড়ি নিয়ে যেতে অতিব্যস্ত । প্রেমিক-প্রেমিকার মতনই সাপ আর কাঠপিঁপড়েরা পরস্পরের নৈঃশব্দে আকৃষ্ট হয়।
১৯৭৯ সালে আমার লিঙ্গ দিয়ে পেচ্ছাপের বদলে রক্ত বেরিয়েছিল, রক্তচাপের দরুন, টাকার পাহাড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে রক্তচাপ বেড়ে গিয়েছিল, ডাক্তার বললে ট্র্যাকিকার্ডিয়া, ছাতাপড়া-হিলহিলে-তেলচিটে নোটের পাহাড়, যা জ্বালিয়ে নষ্ট করতে হতো । তারপর দুমাস ছুটি নিয়ে দুবেলা ঘুমের ওষুধ খেতুম । “ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস” উপন্যাসে আমি টাকার পাহাড় জ্বালানোর মারপ্যাঁচ ব্যবহার করেছি । ১৯৯৩ সালে আমি একশো কোটি, দুশো কোটি, পাঁচশো কোটি টাকার চেক সই করতুম, কল মানি মার্কেটে অফিসের হয়ে বাড়তি টাকা খাটাবার জন্যে । অতো টাকার চেকে সই করে-করে মনে হতো রাজার কুর্সিতে বসে আছি । কোটি-কোটি টাকা নষ্ট করেছি এককালে, ১৯৯৩ সালে কোটি-কোটি টাকা খাটিয়ে আয় বাড়ালুম । পরির দেশের কোষাধ্যাক্ষের মতন দিনের পর দিন কোটি-কোটি টাকার চেক সই করতুম ।
২০১০ সালে আমার বাঁ পা ফুলে গেল একদিন । ডাক্তারের কাছে দৌড়োলুম, ডাক্তার দেখে বলল, এই রোগ তো পুলিশ কন্সটেবল, ইশকুল-কলেজের টিচার আর ডাকপিওনদের হয়, আপনার হল কেমন করে । বললেন উরু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত মোজা পাওয়া যায়, একজোড়া কিনে আজ থেকেই পরে থাকুন, কেবল শোবার সময়ে খুলে রাখবেন । ভেরিকোজ ভেইনস আক্রমণ করেছে পায়ে । সেই থেকে ভেরিকোজ ভেইনসের মোজা পরে থাকি, উরু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত । স্বপ্নে অনেকের পোঁদে লাথি মারি, তাই হয়তো।
১৯৯৯ সালে প্রথম অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলুম বাঁশদ্রোণী বাজারে । পাবলিক আমাকে শাক-সবজির ওপর শুইয়ে মাছের জলের ঝাপটা দিতে জ্ঞান ফিরল । অনেকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে টানাটানি করছিল বলে সলিলা কেঁদে ফেলে থামালো । তার পরেও অজ্ঞান হয়েছি প্রায় সাত বার । মাথার এম আর আই করিয়েছি । নিউরোলজিস্ট বললে, মেডিটেশান করো । বাড়িতে বসে মেডিটেশান করায় একাগ্র হতে পারি না । মন উড়তে থাকে, নানা ভাবনায়, নানা মুখশ্রিতে, নানা সংবাদে, অতীতের ঘটনায় । মেডিটেশান ছেড়ে দিতে হল । ছোটো গল্প-লেখিকা ঝুমা চট্টোপাধ্যায় বলল, “সখা হে, সবসময় মাথাকে জাগিয়ে রাখলে অমন রোগ তো হবেই ।”
১৯৯৮ সালে, মুম্বাইতে আমার অফিস পুনম চেম্বার্সের ছাদ সাততলা থেকে একের পর এক যখন ভেঙে-ভেঙে সশব্দে নিচে নেমে আসছিল তখন আমার হাত ধরে কেবিন থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিলেন একজন তরুণী, যিনি প্রথম পরিচয়ে আমাকে বলেছিলেন যে ওনার জরায়ু নেই । ১৯৯৭ সালে অবসর নেবার পর আমি আরেক অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম অথচ তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেনি মীরা। বাড়িটা পড়ার ফলে উনিশজন মারা গিয়েছিল। ইনিই একমাত্র মহিলা যাঁর সঙ্গে অশ্লীল গল্প করেছি, ব্যাপারটা অবশ্য তিনিই আরম্ভ করেছিলেন, “আজকে কলা কিনিনি, বেগুন কিনেছি, কোকোনাট অয়েল কিনেছি”, আমাকে হতবাক করে । নারীর সঙ্গে অশ্লীল কথাবার্তা ! ওর সঙ্গে কথা বলার সময়ে মনে হতো এই ধনী-তনয়াকে আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে পারলে ভালো হতো ।
তেরো
৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৬৮ বিয়ের পর ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে হনিমুন করার পরিকল্পনা করলুম শিমলা যাবার, শুনে সহকর্মী সুশীল বলল ওর গ্রাম চণ্ডীগড়ের কাছে রোপড় হয়ে যেতে, রোপড় যাবার পর ও আর ওর বউ-বাচ্চা আমাদের সঙ্গ নিল । রোপড়ে মাঠে হাগতে হতো ; আমার তো এনসিসির সময়ে মাঠে প্রতিদিন হাগার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল । সলিলার ছিল না, কিন্তু নতুন অ্যাডভেঞ্চার মনে করে মাঠে গিয়ে ভোর রাতে হেগে নিয়েছিল যে কয়দিন ছিলুম । নতুন বউ মাঠে হাগতে যাচ্ছে, গ্রামীণ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞের বউ বলে কথা। শিমলায় গিয়ে বাস থেকে নামতেই হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে গেল তুষারে । বাসের ছাদে রাখা ছিল বেডিং আর স্যুটকেস, তার ওপর তিন ইঞ্চের তুষার । পিছল পথে গিয়ে উঠলুম হোটেলে, সেই হোটেলের ওপর তলায় আমাদের হনিমুন স্যুট, সেখান থেকে বেরোলেই রাস্তা । দুজনে মিলে দুটো ওল্ড মঙ্ক খেয়েও শীত গেল না, তখন জড়াজড়ি করে অবিরাম সঙ্গম করলুম সারা রাত । সুশীল আর ওর বউ একটা ঘরে ছিল, বেয়ারা বলল রাতভর ওরা ঝগড়া করেছে । শিমলা থেকে ফেরার পর সুশীলের বউ একজন পাঞ্জাবির সঙ্গে পালিয়ে গেল । লোকেদের বউ পালিয়ে যায় কেন ? মনে হয় দুর্বল যৌনতা তার মুখ্য কারণ । “কৌরব” পত্রিকার কমল চক্রবর্তীর বউও কারোর সঙ্গে পালিয়ে যাবার ফলে পত্রিকাটাই রোশনাই হারিয়ে ফেলল । কমল ওর পুরো যৌনতা লাগিয়ে দিয়েছিল পত্রিকায়, বউয়ের দিকে খেয়াল দেয়নি । তবে বউ পালিয়ে গেলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেয়া সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছে, বউয়ের বদলে পুরস্কার পেলুম টাক ডুমাডুম ডুম । এককালে কৌরবে লিখতুম । আর ডাক পাই না ।
শিমলা থেকে ফেরার পথে চণ্ডীগড়ে বাসস্ট্যাণ্ডে এসে একদল পাঞ্জাবি আর হিন্দি কবিলেখকরা ঘিরে ধরল কয়েকদিন থেকে যাবার জন্যে, ওরা আমার জন্যে সাহিত্যসভা করবে, ওরা যাকে বলে “গোষ্ঠী”, মদ-মুর্গি খাবার লোভে থেকে যেতে রাজি হলুম । এদিকে লেখালিখি তখন আমাকে ছেড়ে উধাও হয়ে গেছে, সঙ্গে কবিতাও নেই । হিন্দি আর পাঞ্জাবি পত্রপত্রিকায় ছবিসহ আমার সম্পর্কে খবর পড়ে ওদের উৎসাহ । নিজেরাই যোগাড় করে ফেলেছে আমার কবিতার হিন্দি অনুবাদ । গোষ্ঠীতে একজন যুবতী কবি মাতাল হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, চুমু খাবার উপক্রম করেছিলেন । স্ত্রী সলিলা বেজায় খাপ্পা, যুবতীকে বলল, “সাহিত্যসভা করছেন না অন্যকিছু !” সলিলার পজেসিভনেস দেখে আহ্লাদে আটখানা হলুম ।
১৯৬৭ সালে হিন্দি আর মৈথিলি ভাষার কবি রাজকমল চৌধারী, ভর্তি ছিল পাটনার রাজেন্দ্র সার্জিকাল ব্লকে, অত্যধিক মদ আর মাদকের দরুণ শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল । ওকে একটা আলাদা ঘরের ব্যবস্হা করে দিয়েছিল সরকার । হাসপাতালে বিছানায় শুয়ে রাজকমল বলেছিল, “ডাক্তার বলেছে অপারেশান করা যাবে না, অপারেশান করলে পুরো হাসপাতালে গাঁজা আর চরসের ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়বে।” মদ আর মাদকের লাইনে আমিই ওকে নিয়ে গিয়েছিলুম বলে প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে প্রায়ই সন্ধ্যায় ওর সঙ্গে দেখা করতে যেতুম । একদিন ও বলল ওকে এক প্যাকেট কনডোম এনে দিতে। কনডোম কী করবে, শরীরের এই অবস্হায় ? বলল ওই তো নার্সকে জিগ্যেস করো, ও রাজি আছে । নার্স মাথা নেড়ে সায় দিল । পরের দিন কনডোমের প্যাকেট নিয়ে গিয়ে দেখি বিছানা খালি, নতুন চাদর আর বালিশের খোল, ওষুধ কিছুই নেই, ঘর ফাঁকা । সেই নার্সকে খুঁজে তাকে জিগ্যেস করতে সে বলল, আজ সকালেই উনি মারা গিয়েছেন, ওনার প্রথম পক্ষের স্ত্রী এসে শব নিয়ে গেছেন । কনডোমের প্যাকেটটা পাশেই গঙ্গায় ফেলে দিলুম ।
১৯৮৫ থেকে যখন আবার লেখা আরম্ভ করলুম ঢাকা থেকে মীজানুর রহমান বললেন ওনার পত্রিকার জন্যে হাংরি আন্দোলন নিয়ে ধারাবাহিক লিখতে । লেখা আরম্ভ করলুম “হাংরি কিংবদন্তি” । প্রতিবছর আসতেন আমার নাকতলার ফ্ল্যাটে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে কষ্ট হলেও । মীজানুর যাতে লেখাটা আর না ছাপেন তাই শামসুর রাহমানের মাধ্যমে সুনীল, শক্তি, তারাপদ অনুরোধ করলেন মীজানুরকে । উনি ওনাদের বললেন, ঠিক আছে, আপনাদের কার্টুন আর ছাপবো না, তবে লেখাটা চলবে । শামসুর রাহমান ওনাকে বললেন, “প্লিজ, ঢাকা থেকে “হাংরি কিংবদন্তি” গ্রন্হাকারে প্রকাশ করবেন না । মীজানুর “হাংরি কিংবদন্তি” গ্রন্হাকারে প্রকাশ করলেন না কিন্তু আমার উপন্যাস “নামগন্ধ” প্রকাশ করলেন ঢাকা থেকে । আমাকে নিয়ে সাংস্কৃতিক রাজনীতি কেবল পশ্চিমবাংলাতেই হয় না, তা বাংলাদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে । মীজানুর রহমান মারা গেছেন দশ বছর হল । ঢাকা থেকে আরেকজন নিয়মিত আসতেন, তিনি বাংলাদেশের বিদ্যাসাগর সোসায়টির প্রধান । প্রতিবার এসে বলতেন যে তাঁকে হুমকি দেয়া হচ্ছে বন্ধ করে দেবার জন্য, বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরের প্রয়োজন নেই । জানি না ওনার কী হল । আমি কলকাতা ছাড়ার পাঁচ-ছয় বছর আগেই ওনার আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ।
২০০৪ সালের পর থেকে আমি এক ভ্যাবাচাকা মানসিকতায় ভোগা আরম্ভ করেছিলুম ; নিজের ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরোবার বিপজ্জনক আনন্দ ? যেন মানব-বোমা হবার জন্য তৈরি হয়ে আছি, উদ্দেশ্যহীন, কী বলব একে? রাস্তার ধারে ইঁটের ওপর বসে তেলমালিশ করাবার মতন নিঃসঙ্গতা এটা নয় । বা, হয়তো, বর্তমানে আমি সেই স্হিতিতে বসবাস করছি, যে পরিসরে একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতা মিলেমিশে গেছে । আমি অস্তিত্ববাদী নই যে আমার এই একাকীত্ববোধকে ‘হিউমান কাণ্ডিশন’ হিসাবে মেনে নেবো ; হিন্দু পরিবারে জন্মে একাকীত্ববোধের খ্রিস্টধর্মী ‘হিউমান কন্ডিশন’ সম্ভব বলে মনে হয় না । কিয়ের্কেগার্দ, জাঁ পল সার্ত্রে, আলবেয়ার কামু, মরিস মার্লো পন্টি, কার্ল জাসপার্স প্রমুখের ভাবনাচিন্তার সঙ্গে খাপ খায় না আমার ভাবনাচিন্তা । ১৯৯৭ সালে যে আরথ্রাইটিস হয়েছিল তার রেশ থেকে গেছে গাঁটে-গাঁটে, সবচেয়ে বেশি বুড়ো আঙুলে, যে কারণে কলম ধরে লিখতে পারি না । সইসাবুদের যাবতীয় কাজ আমার বুড়ি স্ত্রীকে করতে হয়, যে আমার চেয়ে মাত্র দু’বছরের ছোটো ।
এখানে বলে নিই, আমি একজন ইন্সটিঙ্কটিভ হিন্দু, কেননা দুর্গাপুজো দোল কালিপুজোর সময়ে আমার প্রবৃত্তিগতভাবে ভালো লাগে, অথচ আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, মনুস্মৃতিতে বিশ্বাস করি না, ঋগ্বেদের দেবী-দেবতায় বিশ্বাস করি না, কেননা ওটা আমার ভেতরে কাজ করে না, ওটা আপনা থেকে গড়ে-ওঠা ব্লকেজ। কমিউনিস্টদের মতন আমি ভেবেচিন্তে বা বই পড়ে দেয়াল তুলিনি, বলেছি তো আমি বুদ্ধিজীবি নই । কলকাতায় অনেককে দেখেছি, “আপনি কি হিন্দু” জিগ্যেস করলে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়, উত্তর দিতে পারে না, কেউ-কেউ বোবা সাজে, কেউ-কেউ ভেবেচিন্তে মরে যাবার পর দেহের গতি নিয়ে কথা বলে । মরে যাবার পর ? ডেড বডিও তাহলে চিন্তাভাবনা করে ! বুঝতে পারি যে তারা নিজের সম্পর্কে খতিয়ে দেখে না, নিজেকে যাচাই করে না, কেবল অন্যে কী করছে আর বলছে তা-ই নিয়ে কিচাইন ।
মৃত্যু সম্পর্কে, এই বয়সে যে ভীতি অনেকের হয়, তা দেখা দেয়নি এখনও । শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সত্যিই ভীতি হয়েছিল, নাকি কবিতা লেখার জন্য মৃত্যুকে বিষয় করেছিলেন, মৃত্যু বিষয়ক কবিতা লিখেও তারপর চনমনে থাকতেন, মদ খাওয়াবার জন্যে আবদার করতেন । আমার তো যেন মনে হয় নিঃসঙ্গতার সঙ্গে মিশে-যাওয়া আমার বর্তমান একাকীত্বটা সহজাত, অন্তর্মুখ, স্বকীয় আত্মজ্ঞানের স্বনির্মিত ডামাডোল কারাগার, উন্মাদ প্রেমে আটক ব্যক্তিএককের মতন ; আমি যেন পুনরুদ্ধারের অযোগ্য এমন কোনো আত্মপরিসরে নিরুদ্দেশ হয়ে রয়েছি, আমাকে কেউ আর খুঁজে পাবে না । আমি নিজের বানানো স্বপ্রেমের বেদনাময় জেলখানা থেকে বেরোবার চেষ্টা করি, কয়েক দিনের জন্যে বেরোই, আবার নিঃসঙ্গতাময় একাকীত্ব কাবু করে ফ্যালে আমাকে । ইনটারনেটের অধিবাস্তব জগতে তৈরি মানব-সম্পর্কের মাধ্যমে দূর করার চেষ্টা করি নিঃসঙ্গতার একাকীত্ব ; অথচ পাঁচ হাজার বন্ধুর কেউ তো বাস্তব নয়, রক্তমাংসের নয় । তাছাড়া রক্তমাংসের মানুষ তো রয়েছে আশে-পাশে, কই কোনো রদবদল তো ঘটছে না আমার সন্ত্রস্ত আত্মবোধে ।
নিঃসঙ্গতার সঙ্গে একাকীত্বের পার্থক্য হল যে নিঃসঙ্গতার স্হিতি স্বীকার করে নেয় যে ব্যক্তিএককের পাশে প্রচুর লোকজন রয়েছে, কয়েকজন স্বজনও রয়েছে । অর্থাৎ সেই স্হিতিটা সাময়িক, তাকে বদলে ফেলা যায়, অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে অর্থবহ যোগাযোগের মাধ্যমে । এমনকি ব্যক্তিএকক নিঃসঙ্গতার আনন্দ উপভোগ করতে পারে, সৃষ্টিশীল হয়ে উঠতে পারে । কিন্তু একাকীত্বকে সে উপভোগ করতে পারে না, তা আত্মপ্রেমের গিলোটিনে মাথা রাখার ফলে যন্ত্রণাদায়ক, দুর্দশাসৃষ্টিকারী, হাহাকারময় । একাকীত্বের স্হিতি ব্যক্তিএককের বাইরের নয় বলেই মনে হয় ; তা ব্যক্তিএককের মনে গড়ে ওঠে, কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। একা, আলাদা হয়ে বসে থাকার ব্যাপার নয় একাকীত্ব । একাকীত্ব হল ফোঁটায় ফোঁটায় সঞ্চারিত উপলব্ধি, বিপত্তিমূলক উপলব্ধি । শৈশব থেকে বাইরের সাময়িক নিঃসঙ্গতাগুলোর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আর সেগুলো স্মৃতিকে খামচে ঘায়ের মতন রয়ে গেছে । বাইরের এজন্য বলছি যে সেসব নিঃসঙ্গতা ছিল সম্পর্কজনিত । ওই আত্মভঙ্গুর ঘটনাগুলোর কথা আমি মাঝে-মাঝে রোমন্হন করে নিরাময় খুঁজি, এখন স্মৃতির জাবর কেটে দেখি ট্রমা থেকে কতোটা নিরাময় ঘটে ।
আমি মনে-মনে ফিকশানগুলো মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে ছকে নিই, যেমন চোর-ডাকাতরা রাতের বেলায় পরিকল্পনা করে, তারপর যখন লিখতে বসি তখন নিজেকে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে আবিষ্কার করতে থাকি, ফিকশানের চরিত্রগুলোর সঙ্গে নিজের সমস্যা ভাগ-বাঁটোয়ারা করি, লিখতে বসার আগে নিজের ভেতরে হারিয়ে যাবার চেষ্টা করি, তখন মনে হয় লেখালিখিই আমার প্রেমিকা, আমার লেখার শিকড় আমার চেতনায়, কেননা আমি একই ঘরে, একই বাড়িতে, একই পাড়ায়, একই রাস্তায়, একই শহরে, একই রাজ্যে সারা জীবন কাটাইনি । যখন গাঁজা-চরসের নেশা করতুম তখন নিজের আহ্লাদের জন্যেই করতুম, এখন লেখালিখির নেশা করি নিজের আহ্লাদের জন্যেই করি, পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে সেই আহ্লাদের দুঃখ-কষ্ট ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিই । কেউ মনে রাখুক, এই ভেবে লিখি না । মরে যাবার পর আমার লেখার কি হবে তা নিয়ে চিন্তিত নই । লেখা শেষ হয়ে গেলে সাপের খোলোশ থেকে বেরিয়ে আসি টাটকা ত্বক নিয়ে ।
চোদ্দ
আমি কবে জন্মেছিলুম, ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেটে ১৯৩৯ থাকলেও, জানি না, তার কারণ, পাটনার মহাদলিতদের পাড়া ইমলিতলার বাড়িতে বয়স্করা মনে করতেন, ব্যাপারটা যে জন্মেছে তার হর্ষোল্লাসের নয়, যিনি প্রসব করেছেন তাঁর ; সুতরাং প্রসবদিন বলে কিছু হতে পারে, জন্মদিন আবার কি ? যে জন্মেছে তার তো কোনো অবদান নেই যে তার জন্মদিন নিয়ে হুজুগ করতে হবে, সে কি নয় মাস কষ্টে ভুগেছিল, সে তো দিব্বি মায়ের পেটে হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার শিখেছে, চব্বিশঘণ্টা খেয়েছে, তারপর তার মায়ের প্রসব বেদনা উঠলে তার মা তাকে প্রসব করেছে। জীবনে কক্ষুনো সে মায়ের কষ্ট বুঝবে না । ঠিকই তো, নাড়ি শুধু মায়েদের গর্ভেই তৈরি হয় । প্রসবের জন্য বাড়ির বউরা যেতেন নিজের বাপের বাড়ি, প্রসবের দিনক্ষণের হিসেব রাখার দায়দায়িত্ব বাপের বাড়ির লোকেদের ; এখন তারা যদি মুকখু হয় তো কি আর করা যাবে ! তারা প্রসবের দিনটা লিখে রাখতে পারেনি ।
আমার বাবা ছিলেন ছয় ভাই, প্রমোদ, সুশীল, রঞ্জিত, অনিল, সুনীল আর বিশ্বনাথ, এবং এক বোন কমলা । ঠাকুমা প্রসবের সময়ে নিজের বাপের বাড়ি যেতেন, কলকাতার পটলডাঙায়, বিরাট আঁতুড়ঘর ছিল সেখানে, আর সেই আঁতুড়ঘরে তাঁর পরপর ছেলে হয়েছে, মেয়ে হচ্ছে না বলে যখন ঠাকুর্দার মনখারাপ, তখন ঠাকুমা ওই আঁতুড়ঘরে মেয়ে প্রসব করেন । আমাদের আদি নিবাস, বড়িশা-বেহালা হলেও, ১৭০৯ সাল থেকে আদি নিবাস গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায় চলে এসেছিল ; সেখানে “সাবর্ণ ভিলা” নামে একটা জমিদারি বাড়ি তৈরি করেছিলেন পূর্বপুরুষ রত্নেশ্বর রায়চৌধুরী, যে বাড়িটি শরিকি অবহেলায় এমনই পোড়োবাড়িতে রূপান্তরিত হয়েছিল, অশথ্থের শেকড়ের আলিঙ্গনে হাড়গোড়-ভাঙা যে, আবাসন তৈরির জন্য প্রোমোটারকে দিয়ে দেয়া হয়, আমিও তার ভাগ পেয়েছিলুম, ষাট হাজার টাকা ।
বড়োজ্যাঠা, মানে প্রমোদের স্ত্রী নন্দরাণীকেও পাঠানো হয়েছিল বাপের বাড়ি হুগলি জেলার কোন্নোগরে । তাঁর মেয়ে হল, নাম রাখা হল সাবিত্রী বা সাবু । দ্বিতীয়বার প্রসবের জন্য গেলেন কোন্নোগর, আবার মেয়ে হল, ধরিত্রী বা ধাবু । ঠাকুমা হুকুম দিলেন যে নন্দরানীর আর বাপের বাড়ি গিয়ে প্রসব করা চলবে না, বড়োই অলুক্ষুণে ওনাদের আঁতুড়ঘর, ওদের বাড়ি ছেলে জন্মায় না । নন্দরাণীর ভাইয়ের বউ বাপের বাড়ি যাননি, কোন্নোগরের আঁতুড়ঘরেই পরপর দুটি মেয়ের জন্ম দিয়েছিলেন, আলো আর পূরবী, এবং তারপর আর সাহস করেননি, ভয়ে, যদি আবার মেয়ে হয় । নন্দরাণীও আর বাচ্চা প্রসব করতে রাজি হননি, কোন্নোগরে গিয়ে হোক বা ইমলিতলায়, যদি আবার মেয়ে হয় । সাবু-ধাবুর জন্মদিন বা নন্দরাণীর দুটি প্রসবের দিন মনে রাখা দরকার মনে করেননি ইমলিতলার বয়স্করা । ছেলে হল না বলে বড়োজেঠা একজন বেশ্যার কাছ থেকে দেড়শো টাকা দিয়ে মেজদাকে কিনেছিলেন ।
মেজজ্যাঠা, মানে সুশীলের স্ত্রী করুণা আমাদের আদিবাড়ি উত্তরপাড়ার মেয়ে, তিনি প্রসবের জন্য গেলেন নিজের বাপের বাড়ি । ঠাকুমা আপত্তি করেননি, প্রসবের সময়ে করুণা বাপের বাড়ি গেলে, তিনি গঙ্গাস্নানে যাবার সময়ে একবার করুণাকে দেখে যেতেন, মাগঙ্গাকে রিকোয়েস্ট করতেন যেন করুণা অন্তত বংশরক্ষা করেন । মা গঙ্গা রিকোয়েস্ট রিফিউজ করে দিয়ে করুণাকে দিয়ে মেয়ে প্রসব করিয়েছিলেন, তাও মৃত । ঠাকুমা যাকে বলে আতঙ্কিত । স্ত্রী করুণাকে নিয়ে মেজজ্যাঠা চলে গেলেন ছাপরায় থাকতে, সেখানে তাঁর জন্য একটা ফোটোগ্রাফির দোকান খুলে দেয়া হয়েছিল । মেজজেঠিমার যখন যক্ষ্মারোগ হল তখন দোকানপাট লাটে উঠিয়ে দুই মেয়ে ডলি আর মনুকে নিয়ে পাটনায় চলে এলেন ।
এরপর সেজভাই রঞ্জিতের স্ত্রী অমিতার পালা । ঠাকুমা নিষেধ করলেন না, কেননা আমার মায়ের বাপের বাড়ি ছিলই না, মায়ের বাবা কম বয়সে মারা যান, দিদিমা তিন ছেলে আর তিন মেয়ে নিয়ে ওঠেন গিয়ে তাঁর বাপের বাড়ি, মানে মায়ের মামার বাড়ি । বাপের বাড়ি তো আর নয়, মামার বাড়ি, ওদের ঘরের আঁতুড় ঘরে ছেলের পর ছেলে হবার রেকর্ড আছে । এবং লো অ্যাণ্ড বিহোল্ড, মা একটি ছেলে প্রসব করলেন। মামার বাড়িতে দাদার নাম রাখা হয়েছিল বাসুদেব । মামাদের দেয়া নাম, যে মামারা নিজেরাই নিজের মামার বাড়িতে থাকতেন । অমন নাম ঠাকুমার পছন্দ হল না, দাদার নাম রাখা হল সমীর, আদর করে সবাই মিনু বলে ডাকতেন ।
বাড়ির পারিবারিক রাজনীতিতে মাকে অনেক ওপরে তুলে দিলেন ঠাকুমা, রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘরের কর্তৃত্ব মায়ের, খরচের নির্দেশে দেবার অধিকার মায়ের । বলতেন, অজাতশত্রুদের মা । তখনও অজাতশত্রুর গল্প শুনিনি, লোকটা কে তাও জানতুম না, মানে বলা হয়েছিল, যার কোনো শত্রু নেই । আমরা শোত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে পৃথিবীতে এসেছি ।
আমাকে প্রসব করার সময়ে মায়ের মামার বাড়িতে আমাদের আর তেমন সামাজিক গুরুত্ব ছিল না। ইমলিতলার বাড়ি আর মহাদলিতদের কুঁড়েঘরের সারি, ওপচানো নর্দমা, পাড়ার বাচ্চাদের গলির নর্দমায় হাগা দেখে মায়ের ভাইদের, আর তাঁদের মুখে শুনে মায়ের মামাদের, আমাদের পরিবার সম্পর্কে ধারণাটা ঘা খেয়েছিল । ওনারা ভেবেছিলেন সাবর্ণ চৌধুরী পরিবার, বিরাট রোশনাই আর ঝালরঝোলানো ঝিকমিকে ব্যাপার হবে । সাবর্ণ চৌধুরীরা যে ষষ্ঠ শতকের অরিজিনাল সাবর্ণ চৌধুরী পুরুষটার পরের প্রজন্মে বিয়োতে বিয়োতে জ্যামিতিক লাফে তত দিনে তিরিশ হাজারে পৌঁছে গেছে, আর তাদের বেশিরভাগই দারিদ্দিরে পটকান্তি খেয়েছে, কেউ-কেউ রিকশা চালায়, মুটেগিরি করে, তা হদিশ করতে পারেননি ওনারা। মাকে দ্বিতীয়বার পাঠাতে রাজি হলেন না বাবা । মা আমাকে প্রসব করলেন হাসপাতালে, পাটনার প্রিন্স অব ওয়েল্স হাসপাতালে । ইমলিতলার বাড়িতে কোনো আঁতুড়ঘর ছিল না, মায়ের শরীরও, আমার কারণে, সুস্হ ছিল না । হাসপাতালের সেই বিলডিঙ, যে-হাসপাতাল বাড়িতে আমাকে মা প্রসব করেছিলেন, স্বাধীনতার পর তা ভেঙে ফেলে সেখানে রাজেন্দ্র সার্জিকাল ব্লক গড়ে উঠেছে । বড়োজ্যাঠা ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হয়ে এই সার্জিকাল ব্লকে ছিলেন বেশ কয়েক মাস । আমার ছেলের মাথা ফাটলে কপালে স্টিচিঙের জন্যে গিয়েছিলুম এই হাসপাতালে ।
—তোমরা হাসপাতালের কাগজপত্র রাখোনি ? রাখলে তো তা থেকে জানা যেত কবে কোন সালে মা আমাকে প্রসব করেছিলেন ।
—ওসব কাগজপত্তর আবার বাড়িতে রাখে নাকি ? হাসপাতালের কাগজ, নার্সরা কতো রুগিকে ছুঁচ্ছে দিনভর, কাগজের সঙ্গে বাড়িতে আবার কোন ব্যামো ঢোকে তার কোনো নিশ্চয়তা আছে ?
অন্তত আমার জন্মদিনের একটা পোক্ত প্রমাণের সম্ভাবনা ছিল ; কিন্তু জন্মদিনটা তো আর গুরুত্বপূর্ণ নয়, প্রসবের রুগি ভালোয়-ভালোয় বাচ্চা নিয়ে বাড়ি ফিরেছে, তাও দ্বিতীয়বারও কোলে ছেলে নিয়ে, এই তো যথেষ্ট ।
—তোর ভাগ্য ভালো যে মেয়ে প্রসব করেনি তোর মা ।
নককা, অনিলের বিয়ে হল কলকাতার ভবানীপুরের সেসময়ের আধুনিকা অমিয়ার সঙ্গে । প্রসবের জন্য তিনি গেলেন ভবানীপুরে । তাঁর মেয়ে হল, খুকু । দ্বিতীয়বার গেলেন । আবার মেয়ে হল, রাখি ।
নতুনকাকা সুনীলের বিয়ে হল উত্তরপাড়ার মেয়ে কমলার সঙ্গে । তিনি প্রসবের জন্য বাপের বাড়ি গেলেন । মেয়ে হল, পুটি ।
দাদা আর আমি জন্মাবার পর ঠাকুমা আর জোর দিতেন না ; ছেলেদের বলে দিয়েছিলেন যার যেখানে ইচ্ছে বউদের পাঠাও, ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, তোমরা নিজেরা বুঝো । নতুনকাকা ঠাকুমাকে বলেছিলেন, উনি অনেকগুলো বাচ্চা চান, প্রথম মেয়ের পর ওনার ছেলে তারপর মেয়ে, এইভাবে ছেলে-মেয়ের ছন্দ মিলিয়ে ছয়টা মেয়ে আর তিনটে ছেলে হল । ঠাকুমা বলেছিলেন এবার ক্ষান্তি দে, তিনটে ছেলে যথেষ্ট, এই উত্তরপাড়ার বারো ঘর-চার সিঁড়ির বাড়ি ভাগ-বাঁটোয়ারা হলে সকলের ভাগ্যে একটা করে নোনা ইঁট জুটবে ।
ছোটোকাকা বিশ্বনাথ বিয়ে করলেন, উত্তরপাড়ার বাড়িতে ভাড়া থাকতেন গঙ্গোপাধ্যায় পরিবার, চিৎপুরের যাত্রা দলের ছোটো ফণী নামে যিনি খ্যাত ছিলেন, তাঁদের বড়ো মেয়ে কুচির সঙ্গে প্রেম করে । ওনাদের কোনো বাচ্চা হল না । ঠাকুমা বলেছিলেন, প্রেম করে বিয়ে করলে বাচ্চা হয় না, তার ওপর এক গোত্তরের বিয়ে ; ভাড়াটের মেয়ের তো আঁতুড়ঘরও নেই । প্রসবের দিন আর বাচ্চার জন্মদিনের হিসেব রাখার ঝক্কিঝামেলা পোয়াতে হল না ওনাদের । তবে বিয়ে হয়ে যাবার পর ঠাকুমা বেয়াইকে চব্বিশঘণ্টার নোটিস দিয়েছিলেন উত্তরপাড়ার বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে বাড়ি ভাড়া নিতে । ওনারা আদপে কোথাকার লোক ছিলেন জানি না, তবে উত্তরপাড়াতেই বিভিন্ন পাড়ায় বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন ।
ছোটোকাকার ছোটোশালী ক্ষ্যামাঙ্করী বা খেমি ফ্রকের ওপর তার উঁচু বুক আর ফ্রকের তলায় খোলতাই উরু নিয়ে গরমের ছুটিতে বেড়াতে আসতো ইমলিতলার বাড়িতে, জড়াজড়ির খেলা খেলে পরস্পরের চরিত্র আলোয় আলো করার এইটিই আমাদের প্রথম সুযোগ ছিল । গ্রীষ্মকালে, ইমলিতলার বাড়িতে, রাতের বেলায়, ছাদে মাদুর পেতে, গড়াগ্গড় শুতুম আমরা সবাই, মাঝরাত থেকে ঠাণ্ডার জন্য পায়ের কাছে গায়ে দেবার চাদর । আমার বয়স এগারো, খেমির তেরো । সবায়ের সামনে খেমিমাসি বলে ডাকতুম । ১৯৫০ সালে, মাঝরাতে, খেমির ঠেলা, কি রে, তোর বাপ তো রোজ-রোজ টাকা রোজগার করে, দাঁত মাজার মলম বেরিয়েছে আজকাল, তাই দিয়ে দুজনে দাঁত মাজবো, তাহলে গন্ধ হবে না । আমাদের দুজনের গায়ে একটাই চাদর, আর আমাদের হাত দুজনের শরীরের রহস্য খুঁজে বেড়াতে ব্যস্ত । আমার মাথা ওর ফ্রকের তলায় , ওর হাত আমার প্যান্টুলের ভেতর । তারপর একজন আরেকজনের ঠোঁট খাওয়া আরম্ভ করলুম, আপনা থেকেই ঘটে গেল প্রথম দিন, তাই খেমি বললে, মুখ মাজার মলমের ব্যবস্হা করতে । পাকা তালশাঁসের ঠোঁট । খেমির কথা বলার ঢঙ আর বেপরোয়াভাব আমি ব্যবহার করেছি আমার ‘অলৌকিক প্রেম ও নৃশংস হত্যার রহস্যোপন্যাস’ নামের ডিটেকটিভ উপন্যাসের মিলি চরিত্রে ।
কবে খেমি আবার গরমকালের ছুটিতে আসবে, এই আশায় থাকতুম । তিনবার তিন বছর এসেছিল, প্রতিবার বুকের তাপ আর তরাই বাড়িয়ে । তারপর খবর এলো যে খেমি মায়ের দয়ায় ভুগে মারা গেছে । মায়ের দয়া ! কোন মা ? শেতলাদেবী, দক্ষিণভারতে মারিআম্মান দেবী । রোগের বেলায় দেবী কেন জানি না, রোগ সারাবার বেলায় দেবতা । সাপে কামড়ালে, কিংবা যাতে না কামড়ায়, তাই মনসাদবীকে পুজো দাও । যাতে না মহামারী আরম্ভ হয় তাই ধূমাবতীর পুজো দাও, পর্ণশবরীর পুজো দাও । আর দেবতারা সকলের স্বাস্হ্য রক্ষা করে। অশ্বিনী যমজভাইরা, ধন্বন্তরী, ধাত্রীদেবতা আয়ুর্বেদের ডাক্তার ! খেমির মা ওকে আমার মায়ের আগে প্রসব করেছিলেন, তাই খেমি অনেক কিছু জানত, শিখিয়ে দিয়েছিল, যা পরে কাজে লেগেছে আমার, নিজেকে হাঁদা-গঙ্গারাম, যা খেমি আমাকে বলত, তা আর হতে হয়নি । খেমির জন্মদিন-মৃত্যুদিন জানা হল না আমার । কুচি-খেমির মায়ের নাম ছিল বিবসনা । ভাবা যায় এরকম অতিআধুনিক নাম, যার দেহে বসন নেই ? জানি না ইনি কোন পুরাণের দেবী । আমাদের দুজনের গা গরম হয়ে ওঠে, সেই গরমের যোগফল দুজনের গায়ের গরমের তিনচার গুণ বেশি । আকাশে তারায় তারা, দেখা যায় সপ্তর্ষি মণ্ডল, দেখা যায় চাঁদ । ইমলিতলা ছাড়ার পর অমন পরিষ্কার আকাশ কোথাও পাইনি আর ; খেমি ওই আকাশ নিয়ে গেছে নিজের সঙ্গে আর দিয়ে গেছে ধোঁয়াটে ডিজেলের কারখানার চিমনির শ্বাসের আকাশ । ফিসফিস করে, খেমি অর্থাৎ মিলি : এরকম হয় বুঝি ? এই ফুলে যাচ্ছে রে, গরমও হয়ে যাচ্ছে, আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে রে, বুক ঢিপঢিপ করছে ; তোর কিছু হচ্ছে না ? মানে এখানে নয়, যেটা ধরে আছি? মনের মধ্যে কিছু? কিংবা বুকে ? আমি হাত চালিয়ে দিতে ন্যাকড়া বাঁধা পেলুম । চাপা উত্তেজনায় বললুম, ও, নিজেরটা বেঁধে এনেছিস । কেন, চাস না যে হাত দিই ?
খেমি বা মিলি : ধ্যাৎ বোকা, এখুন ধ্যাড়ানি চলছে, কালকে খুলব, তখন যতো ইচ্ছে হাত দিস ।
খেমি বা মিলি ন্যাকড়া ঢিলে করতে হাত ঢোকালুম, কীরকম চটচটে । আমার হাতটা নিজের ফ্রকে পুঁছে খেমি বলেছিল, দেখলি তো ! কালকের দিনটা অপেক্ষা করতে পারলি না । তুই কিন্তু সত্যিই ষাঁড় । বড়বাজারে গিসলুম একবার, তখন দেখেছিলুম একটা ষাঁড় ওই করছে । একদম গোলাপি । কেন বলতো? তুই তো ফর্সা ।
পরের দিন, মিলি বা খেমি আমার বাঁ হাতের মধ্যমা আঙুলটা নিয়ে বলেছিল, এইতে রাখ, শুধু রাখবি, নাড়াবি না কিন্তু, নাড়ালে কাল থেকে অন্য জায়গায় শোবো ।
আমি আঙুলটা নাড়াতে-নাড়াতে বলেছিলুম, নাড়ালে কী হয় ?
মিলি বা খেমি আমার বোতাম-খোলা প্যান্টে হাত ঢুকিয়ে টিপে-তিপে ফোলাতে লাগল আর বলতে লাগল, এই হয়, এই হয়, এই হয়, এই হয়, এই হয়, এটা আমার এটা আমার ।
—কালকে দিনের বেলায় একটু দেখতে দিস ।
—দেখে আবার কী করবি ? চুল দেখতে চাস ?
খেমি দেখিয়েছিল, ছাদেতেই, দুপুর বেলায়, যখন সবাই ভাত খেয়ে ঝিমোচ্ছে । দেখেই বেশি ভালো লাগলো, হাত দেয়াদিয়ির চেয়ে । রগের কাছে দপদপানি ।
খেমির আগে, ইমলিতলা পাড়ায়, কুলসুম আপার সঙ্গে একই ধরনের ব্যাপারে, আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, আমি জানতুম যে বাড়াবাড়ি করলে ছড়ে গিয়ে কষ্ট হতে পারে ; ১৯৪৯ সালে, কুলসুম আপার সঙ্গে সম্পর্কের সময়ে আমার বয়স দশ । কুলসুম আপাদের ঘরটা ছিল অন্ধকার, ছাগল হাস মুর্গিদের ঘর, তাই দেখা হয়নি, তাছাড়া উনি ছিলেন বেশ কালো । কুলসুম আপার চরিত্র আমি ব্যবহার করেছি ‘রাহুকেতু’ উপন্যাসে । ওনারা ছিলেন শিয়া মুসলমান পরিবার. ওয়াজেদ আলি শাহের পতনের পর পাটনায় পালিয়ে এসেছিলেন, বেশ গরিব হয়ে গিয়েছিলেন, একই শতচ্ছিন্ন পোশাক দিনের পর দিন, বোরখা পরতেন না কেউ, বাড়ির বউরা বিড়ি বাঁধতেন, হাসের ডিম, মুর্গির ডিম, হাস, মুর্গি, ছাগলের বাচ্চা বিক্রি করতেন । আমাদের বাড়িতে মুর্গির ডিম সেসময়ে নিষিদ্ধ ছিল বলে ওনাদের বাড়ি থেকে হাসের ডিম আনতে যেতুম । কুলসুম আপা গালিব আর ফয়েজ আহমদ ফয়েজ শোনাতে ভালোবাসতেন, আমার মতো নির্বাক মুগ্ধ শ্রোতা আর কোথায় পাবেন, যে ওনার কালো গভীর চাউনি গোল মোটা ঠোঁট গালে টোল দেখার নেশায় বুঁদ । ওনাদের বাড়িতে যে মাংস রাঁধা হচ্ছিল তার গন্ধে শ্রোতা মোহিত হয়ে খেতে চাইলে কুলসুম আপা বাটি করে এনে খাইয়েছিলেন, বলেছিলেন বাড়িতে কাউকে বলিসনি, পাড়ায় রটে যাবে । বলিনি কখনও যে গোরুর মাংস খেয়েছি । উনি জিভ দিয়ে আমার ঠোঁট পুঁছে দিয়েছিলেন । যেদিনই মাংস রান্না হয়েছে সেদিনই ব্ল্যাকমেল করেছি ঘষাঘষি খেলার আগে ।
একদিন হাস-মুরগির অন্ধকার ঘরে শ্রোতার প্যান্ট খুলে নামিয়ে দিলেন, নিজের চুড়িদার নামিয়ে দিলেন আর শ্রোতাকে কষে জাপটে ধরে নিজেকে ঘষতে লাগলেন । শ্রোতার ভালো লেগেছিল বেশ, তাই রোজ যেতো, যদিও রোজ হাসের ডিম কেনার দরকার হতো না । এ-ব্যাপারেও কুলসুম আপা বলেছিলেন, তোর বাড়িতে কাউকে বলিসনি যেন । একদিন কুলসুম আপা শ্রোতাকে এতো বেশি জাপটে ধরে কাঁপতে লাগলেন যে শ্রোতার নুনু ছড়ে গেল, হাঁটতে অসুবিধা হল দুদিন । ভয়ে শ্রোতা তারপর কুলসুম আপার বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল । শ্রোতার জাঠতুতো-খুড়তুতো বোনরা ডিম কিনে আনতো । মেজজ্যাঠার ছোটো মেয়ে মনু জিগ্যেস করেছিল, “ছোড়দা, ওই কেলটে কালো কুচকুচে কুলসুমটা তুই কবে ওদের বাড়ি যাবি, জানতে চায় কেন রে ?”
‘আমদের জন্মদিন হয় না’ এই তত্ত্ব সম্ভবত ইমলিতলা বাড়ির সৃষ্টি । ঠাকুর্দা লক্ষ্মীনারায়ণ ও তাঁর দুই ভাই হরিনারায়ণ এবং বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত উত্তরপাড়ার সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশলতিকা ১৯১১ সালে ‘বংশ পরিচয়’ নামে প্রকাশ করেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যেটি বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত । ঠাকুর্দার প্রজন্ম থেকে আমাদের আর্থিক ডামাডোল আরম্ভ হয়, আর ইমলিতলায় এসে তো আমরা একেবারে ফেকলু পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলুম । কাগজ দেখিয়ে ভারতীয় আম আদমির আত্মপরিচয় প্রমাণ করার প্রথা বোধহয় স্বাধীনতার পরই আরম্ভ হয়েছে । ঠাকুর্দার পরিচয় উইকিপেডিয়ায় আছে, তা থেকে জানা যায় উনি ১৯৩৩ সালে মারা যান, যে বছর দাদাকে মা প্রসব করেন । মানে, উনি নিজের বংশধরকে দেখে গিয়েছিলেন ।
১৭০৯ সালে উত্তরপাড়া শহরের পত্তন করেছিলেন রত্নেশ্বর রায়চৌধুরী, যিনি বড়িশার একান্নবর্তি জমঘট থেকে বেরিয়ে নিজের একটা আলাদা জমিদারি চাইছিলেন । সাবর্ণ রায়চৌধুরীরা ভঙ্গ কুলীন ছিল, যাদের বাড়িতে খাঁটি-বামুনরা তাদের মেয়ের বিয়ে দিত না । রত্নেশ্বর রায়চৌধুরী টাকা আর জমিদারির অংশ দিয়ে গরিব ব্রাহ্মণ যুবকদের ফুসলিয়ে জামাই করে এনেছিলেন উত্তরপাড়ায় । ছোটোবেলায় দেখেছি যে আমাদের চেয়ে তাদের রমরমা বেশি । ঠাকুমার কথায়, “তোর পূর্বপুরুষরা মাগিবাজি করে আর মদ খেয়ে সব তবিল উড়িয়ে দিয়েছে, ওরা কোম্পানির কাগজ কিনে-কিনে নিজেদের তবিল বাড়িয়ে নিয়েছে ।” কোম্পানির কাগজ যে কেন দামি তা জানতুম না । দাদুর প্রজন্মে পৌঁছে আমাদের তবিল ফাঁকা, বারোঘর চার সিঁড়ির খণ্ডহরের ইঁটে নোনা লাগা আরম্ভ, দিনে পায়রা রাতে চামচিকেতে ছয়লাপ । দাদু প্রথম সুযোগেই উত্তরপাড়া থেকে কেটে পড়েন । ওনার অন্য দুই ভাই খণ্ডহর ছেড়ে পালাননি, তাঁদের নাতিরা কেউ-কেউ হিন্দ মোটরে হাতুড়ি পেটার কাজে নেমে গিয়েছিল ।
এখানে একটা ঘটনার কথা বলি । স্বাভাবিক যে দাদাকে ঠাকুমা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন । আমাকেও বাসতেন, তবে তা যে দাদার চেয়ে কম তা ওনার আচরণে টের পাওয়া যেতো । কলকাতার সিটি কলেজে পড়ার সময়ে দাদা ঠাকুমার সঙ্গে থাকতেন । হাংরি আন্দোলনে দাদার গ্রেপতারির সংবাদে ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বরে ঠাকুমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল, আর তিন দিন কোমায় থাকার পর মারা যান । দাদার গ্রেপ্তারির কথা যাতে ওনার কানে না যায় তা বড়োজ্যাঠা আগে থেকেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন । কিন্তু গ্রেপ্তারির পর ব্যাংকশাল কোর্ট থেকে জামিন নেবার ব্যাপারে বাবা-কাকা-জ্যাঠা-পিসেমশায় উত্তরপাড়ার বাড়িতে একত্রিত হয়েছিলেন । এতোজনকে দেখে ঠাকুমার সন্দেহ হয় । তাঁকে জানানো হয় মামলার কথা । শোনামাত্রই তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল । ওনার শুকনো মাইয়ের বোঁটা ওপরে তুলে তার তলায় স্টেথোস্কোপ রেখে ডাক্তার ঘোষণা করেছিল, “ডেড”।
ঠাকুমার মৃত্যুদিন মনে রাখার অসুবিধা হয় না, তার সঙ্গে জুড়ে আছে আমাদের কোর্টে দৌড়োনোর অভিজ্ঞতা । কিন্তু পরিবারের অন্য কারোর মৃত্যুদিনেরও, যেমন ঠাকুর্দার বা ঠাকুর্দার ভাইদের, জ্যাঠা-বাবার, কাকিমা-জেঠিমাদের, কোনো হদিশ নেই ।
—মৃত্যু দিনগুলো কেন মনে রাখোনি তোমরা ?
—তুই বোকা না গাধা ; মৃত্যু দিন মনে রাখার আবার কি দরকার ।
—বাঃ, মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করবে না তোমরা ?
—ওসব নাটোক-নবেলে হয় । পূর্বপুরুষরা মারা গেলে বছরে একটা দিনই তর্পণ করতে হয়, তিল-গঙ্গাজল দিয়ে, আত্মাদের অশান্তি করার মানে হয় নাকি, ওনারা যে যেখানে আছেন সেখান থেকে আমাদের সবাইকে আশির্বাদ করেন, তোকেও ।
তার মানে, আমাদের যেমন জন্মদিন হয় না, তেমনিই, মৃত্যুদিনও হয় না । ইমলিতলার বাড়ির তত্ত্ব অনুযায়ী আমরা যেমন জন্মাই না, তেমনিই আমরা মরি না । আমরা অজাতশত্রু ।
অজাতশত্রু, জানা গেল, এই পাটনা শহরেরই লোক, রাজা ছিলেন, এই শহরের পত্তন করেছিলেন, তখন এই শহরের নাম ছিল পাটলিপুত্র । পাটলিপুত্রর ধ্বংসাবশেষ দেখতে বড়োজ্যাঠা নিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের । গাইডের কাছে জানা গেল যে অজাতশত্রু ছিলেন মগধের রাজা, যিশুখ্রিস্টের জন্মের চারশো বছরেরও বেশি আগে গঙ্গার ধারে একটা ছোটো দুর্গ তৈরি করেছিলেন ।
—পাটলিপুত্র নাম কেন ?
—পাটলি হল এক ধরণের চাল আর পুত্র মানে ছেলে ।
—চালের ছেলে ? অমন হয় নাকি ?
—তা নয়, পাটলিপুত্র মানে পাটলির ছেলে, যিনি রাজা সুদর্শনের মেয়ের সন্তান ।
—যিশুখ্রিস্টের জন্মের তিনশো বছর আগে গ্রিক ইতিহাস-লেখক লিখেছিলেন যে পাটলিপুত্র বেশ বড়োসড়ো শহর ।
—এ তো দেখছি আমাদের জন্ম হয় না আমাদের মৃত্যু হয় না ধরণেরই গল্প, বড়োজ্যাঠা ।
—তবে আর ইতিহাস বলেছে কেন । তুই গাইডকে জিগ্যেস কর, অজাতশত্রু কবে জন্মেছিল, কবে মারা গিয়েছিল, বলতে পারবে না ।
আমি জিগ্যেস করা আরম্ভ করেছিলুম, গাইড আবার গল্প ফাঁদতে আরম্ভ করল ; পাটলিপুত্র ছিল একটা জলদুর্গ, গঙ্গা, গণ্ডক আর শোন নদীর তৈরি ত্রিভুজের মধ্যে, নন্দরাজত্ব, মৌর্যরাজত্ব, শুঙ্গরাজত্ব, গুপ্তরাজত্ব আর পাল রাজাদের রাজধানী । নানা জায়গা থেকে জ্ঞানীগুণিরা এখানে এসে জড়ো হতেন, যেমন এসেছিলেন চাণক্য ।
—তাদের ছেলেরা সব বাহুবলি,ডাকাত, খুনি, চোরছ্যাঁচোড় আর রাজনীতিক হয়ে জন্মাচ্ছে ।
বাবার ফোটোগ্রাফির দোকানের চাকর রামখেলাওন সিং ডাবর, দেয়ালে হেলান-দেয়া বড়জ্যাঠার সাইকেলের সিটে আমাকে বসিয়ে ধরে থাকে, আরি আমি, অজাতশত্রু, হাতির ওপরে বসে রাজ্য জয় করতে বেরোই, হাতে তরোয়াল, যা ডাবরই তৈরি করে দিয়েছে, ফিলমে পাকানো লাল কাগজ মুড়ে-মুড়ে, ছড়ির মতন । তরোয়াল ঘোরাই, হাতির পিঠে সামলাতে না পারলে রামখেলাওন সিং ডাবর হুকুম করে, ‘ঠিক সে বয়ঠিয়ে মহারাজ’ ।
দাদা, দেখতে পেয়ে বলে ওঠে, ওঃ, আমাকে সিংহাসন দিয়েছিলেন ঠাকুমা, তুই বেদখল করে রাজত্ব চালাচ্ছিস, জানিস কি যে অজাতশত্রুর একটা হাতে কড়ে আঙুল ছিল না ; আর অজাতশত্রুর নাক উঁচু ছিল বলে প্রজারা ওনাকে বলতো পীনোন্নত ।
দাদার সঙ্গে আমার পাঁচ বছর বয়সের তফাত, ভয় দেখাবার অধিকার আছে মনে করে এড়িয়ে যেতে ডাবর বলে, ‘হাঁ, সচ্চিমুচ্চি, লোগ কহতে হ্যাঁয়, উ চার উংগলিকে রাজা থে; হমরে বৈশালি মেঁ সবকোই জানত হ্যায়।’
ঠাকুমাকে জিগ্যেস করা যাবে না, উনি উত্তরপাড়া ফিরে গেছেন । ক্লাসে হিসি পেলে অজাতশত্রু কেমন করে পারমিশান চাইতো তাহলে, কাকে জিগ্যেস করি ? সিসটার আইরিনের ক্লাসে আমি তো ওই ভাবেই অনুমতি চাই । কনভেন্টে কেউই পীনোন্নতর বাংলা বলতে পারবে না, অজাতশত্রুর নামই শোনেনি হয়তো মাদার সুপিরিয়র, সিসটাররা, সিসটার আইরিন আর ফাদার হিলম্যান ।
ছোটোকাকাকে জিগ্যেস করলুম । তখনও উনি উত্তরপাড়া গিয়ে প্রেমে পড়েননি, বউ কুচিকে পাটনায় আনেননি । “আরে ধ্যুৎ, সব গাঁজাখুরি, রাজাদের নিয়ে ওদের দরবারিরা নানা গপপো ফাঁদে।”
—আর উনি নাকি পীনোন্নত রাজা ছিলেন ?
ছোটোকাকার হাসি, গমকে গমকে পেট চেপে ধরে হাসি, ডেকে আনল জেঠিমা আর মাকে । ছোটোকাকা ব্যাপারটা ওনাদের বোঝাতে, জেঠিমা বললেন, “নাক উঁচুদের উন্নাসিক বলে রে, আর যাদের মাইয়ের বোঁটা উঁচু, তাদের বলে পীনোন্নত, এই যেমন আমার, এই দ্যাখ, একে বলে পীনোন্নত, এখনও পীনোন্নত আছে। তুই তো অনেক কাল অব্দি পাড়ার বউদের মি খেয়ে বেড়িয়েছিস, পীনোন্নত জানিস না ?”
—মি-এর উঁচু বোঁটাকে বলে পীনোন্নত ? সুদামিয়ার, কপিলের মায়ের, কৃষ্ণন্নার মায়ের, কালুটুয়ার চাচির, বিরজুর মায়ের, মুনসিজির বউয়ের সকলের মি-ই তো পীনোন্নত । দাদা আমাকে পিটুনি খাওয়াবার জন্যে বলেছে, তার মানে !
আমার মায়ের বুকে পর্যাপ্ত দুধ হতো না বলে আমি পাড়ার নার্সিং মাদারদের কোলে পৌঁছে যেতুম ছোটো বেলায় । জেঠিমার কথায়, আমি ভোরবেলা উঠেও কান্না জুড়তুম, “মি খাবো, মি খাবো”, আর ছোড়দি, ধরিত্রী, কোলে করে নিয়ে যেতো পাড়ার কোনো বাড়িতে আর সঁপে দিত তার কোলে ।
অজাতশত্রুর কড়ে আঙুল ছিল কিনা তার ফয়সালা করার জন্য দুপুরে, বাবা যখন দোকানের কাজ সেরে লাঞ্চ খেতে এসেছেন, তখন জিগ্যেস করলুম ওনাকে । বাবা খেতে বসে গম্ভীর মুখে বললেন, “মা তোদের অজাতশত্রু খেতাব দিয়ে ভালো কাজ করেনি, অজাতশত্রুটা বাজে লোক ছিল, নিজের বাবা বিম্বিসারকে জেলে পুরে খুন করেছিল, কাকার রাজ্য কাশি আক্রমণ করে তাকে হারিয়ে দিতে, কাশির রাজা নিজের মেয়ের সঙ্গে অজাতশত্রুর বিয়ে দিয়ে দিলে, আর কাশি রাজত্বও দিয়ে দিলে, নিজের খুড়তুতো বোনকে বিয়ে করে নিলে, ছি ছি । ষোলো বছর যুদ্ধ করে গঙ্গার ওপারে লিচ্ছবিদের রাজত্ব দখল করে নিলে, এখন যাকে হাজিপুর বলে, নিজের ভাইদের রাজত্ব আক্রমণ করে সেগুলো দখল করে নিলে, অতো রক্তপাত ভালো নয় ।” বাবা শাকাহারি, তাই রক্তপাতের বিরুদ্ধে ।
ডাবর বলেছিল, হাজিপুরের কলাকে বলে চিনিয়া কেলা, সবচেয়ে ছোটো মাপের কলা, অজাতশত্রুর ভয়ে কলাগুলো নাকি ছোটো আর একটু টোকো হয়ে গিয়েছিল ।
—তাহলে বৈশালী আর মুজফফরপুরে এতো ভালো মিষ্টি লিচু কী করে হয় ?
—চিন থেকে এনেছিল একজন পরিব্রাজক, তাই ওখানকার লিচুকে বলে শাহি লিচু, চায়না লিচু , আম্রপালী নামে একজন সুন্দরী ছিল, তার ছোঁয়া পেয়ে ওখানকার লিচু মিষ্টি।
ঠাকুমা পাটনায় এলে বলেছিলুম, তুমি আমাদের অজাতশত্রু খেতাব ফেরত নাও ; বাবা বলেছে লোকটা বাজে ছিল। ঠাকুমা বললে, তোর দাদু তোর দাদাকে সমীর নাম দিয়ে গেছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে তোর নাম তোর বাপ রেখেছে মলয়, আর কি, এই নামেই বংশের মুখ উজ্জ্বল কর ।
—বংশের মুখ উজ্জ্বল ? সেটা কী ?
—বড়ো হলে টের পাবি, অন্য লোকেরা যদি তোকে হিংসে করে তাহলে বুঝবি বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পেরেছিস । ।
ঠাকুমা মারা গেলেন বলে আর বলার সুযোগ হয়নি যে, বড়ো হয়ে মুখ যা করেছি, বাড়ির লোকে তাকে মুখ উজ্জ্বল মনে করলেও, ব্যাঁকা মানুষরা তা মনে করে না । তারা নানারকম লেখালিখি করে, হিংসে করে ।
বলেছিলুম, তুমি তোমার ছেলেদের ডাকনাম রাখোনি কেন ? ঠাকুমা বললে, “কেন ? তোর জ্যাঠাকে খোকা বলে ডাকি এখনও, তোর মেজজ্যাঠাকে মেজখোকা বলি, তোর বাপকে রঞ্জা বলি, তারপর আর কারোর ডাকনাম রাখিনি । তোর বাপের নাম তো মহারাজা রঞ্জিত সিং-এর নামে রেখেছিলুম, যখন তোর বাপকে প্রসব করেছিলুম, তখন লাহোরে থাকতুম, রঞ্জিত সিং এক-চোখ অন্ধ ছিল, ওর অনেকগুলো বউ ছিল, বাঁদিও ছিল, তাই বলে তোর বাপের রঞ্জিত খেতাব কি ফিরিয়ে নেবো ?
—বাঁদি কি ?
—যে বউদের লোকে বিয়ে করে না কিন্তু তাদের নিজের বাড়িতে বউদের মতন রাখে । অজাতশত্রুরও অনেকগুলো বউ আর বাঁদি ছিল ।
—দারুণ ব্যাপার ; আমিও বড়ো হলে অনেকগুলো বাঁদি রাখব ; বাচ্চা হলে বাঁদিদের দুধ খেতে পারব।
—তা রেখো, কিন্তু আমার বারো ঘর চার সিঁড়ির সাবর্ণ ভিলায় এনোনি তাদের ।
আমার অজাতশত্রু হবার শখের এখানেই ইতি । ঠাকুমাকে বললুম, “অজাতশত্রু কতোদিন রাজত্ব করেছিল লোকে হিসেব রেখেছে, ওর বাবা বিম্বিসার কতোদিন রাজত্ব করেছিল তার হিসেব রেখেছে লোকে, কিন্তু ওদের জন্মদিনের আর মৃত্যুদিনের হিসেব রাখেনি । তুমিও কবে তোমার ছেলেদের প্রসব করেছিলে তার হিসেব রাখোনি।”
পনেরো
ঠাকুমা জেনে যেতে পারেননি যে এখন একজন লোক যে আসলে সেই লোকটাই, তা প্রমাণ করার জন্য কতো কাগজপত্র সামলে রাখতে হয়, হাসপাতালের বার্থ সার্টিফিকেট, কর্পোরেশানের বার্থ সার্টিফিকেট, ভোটার কার্ড, র্যাশান কার্ড, আধার কার্ড, টেলিফোনের বিল, পাসপোর্ট, ইলেকট্রিক বিল । ভাগ্যিস বিম্বিসার আর অজাতশত্রুর সময়ে ওসব বালাই ছিল না ।
বড়ো জ্যাঠা মারা যেতে জেঠিমার পেনশন তুলতে গিয়ে কি হ্যাঙ্গাম; হাতেখড়ির মতন কষ্ট করে শেখা কম বয়সের সইয়ের সঙ্গে বুড়ি বয়সের সই মেলে না, পঁয়তাল্লিশ টাকা পেনশন তোলার জন্য আদালতে গিয়ে এফিডেভিট করতে হয়েছিল যে উনিই নন্দরানি, বড়োজ্যাঠার বউ । আজকালকার মতন, কোনও কাগজে বড়োজ্যাঠাও জন্মাননি, বড়োজেঠিমাও জন্মাননি । বড়োজ্যাঠার চাকরি ছিল পাটনা মিউজিয়ামে মূর্তিদের আর পেইনটিঙগুলোর ঝাড়াই-পোঁছাই, যার জন্য কোনো কাগজের দরকার হয়নি, ধ্যুৎ ভাল্লাগে না বলে মাঝে চাকরি ছেড়ে দিলেও, কিউরেটার বাড়িতে লোক পাঠিয়ে বাবা-বাছা করে আবার চাকরিতে বহাল রেখেছিল, অথচ বড়োজ্যাঠা চাকরি পেয়েছিলেন ঠাকুমার জাঠতুতো দাদার সুপারিশে, তিনি কলকাতা মিউজিয়ামের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কিউরেটার ছিলেন, লেখক ছিলেন, ওনার নাম ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় । ইংরেজরা যাবার পরে বড়োজ্যাঠার চাকরির নাম হয়ে গেল কিপার অফ পেইনটিংস অ্যাণ্ড স্কাল্পচার, মাইনেও বেড়ে গেল, রিটায়ার করার সময়ে নব্বুই টাকা । মিউজিয়ামে বড়োজ্যাঠা একটা ঘর পেয়েছিলেন, গরমকালে ঘরের কল খুলে দিয়ে মেঝেয় জল ভরে দিতেন আর দুপুরে ইজি চেয়ারে শুয়ে নাক ডাকতেন । অফিস যেতেন পাঞ্জাবির ওপরে ধুতি, মাথায় হ্যাট, সাইকেলে তিন কিলোমিটার । আমার স্কুলের ছুটি পড়লে আমি ওনার সাইকেলের পেছনে ক্যারিয়ারে বসে চলে যেতুম ওনার অফিসে, দুপুরে খাবার জন্য টিফিনের কৌটো নিয়ে । টিকিট না কেটেই সারা মিউজিয়াম ঘুরে বেড়াতুম । বড়োজ্যাঠা অনেকসময়ে আমাকে সঙ্গে করে ঘরগুলোয় নিয়ে গিয়ে দেখাতেন কোনটা কার মূর্তি, কোন জিনিস কতো হাজার বছর আগেকার । একজন অপ্সরার মাই আর একজন গলাকাটা পুরুষের মূর্তির নুনু চকচকে ছিল, কেন তা জানতে দেরি হয়নি, দেখি মহিলা দর্শকরা গলাকাটা মূর্তির নুনুতে হাত দিয়ে টুক করে কেটে পড়ছে, আর একই কাজ করছে পুরুষ দর্শকরা অপ্সরার মাইতে হাত বুলিয়ে । আমি অপ্সরার মাইতে হাত দিতে পারতুম না, কেননা আমার হাত পৌঁছোত না । খেমির মাই অপ্সরাদের চেয়ে ছোটো ছিল; কুলসুম আপার মাই অপ্সরাদের চেয়ে কালো ।
বড়োজ্যাঠার টয়লেটে গিয়ে প্যান্টুলের বোতাম খুলে দেখেছিলুম, শ্বেতপাথরের গলাকাটা মূর্তির চেয়ে আমার নুনু বড়ো । গলাকাটা মূর্তি, পরে বলেছিলেন বড়োজ্যাঠা, আলেকজাণ্ডারের । শুনে বেশ ভালো লেগেছিল ; তার মানে আমিও আমার নুনু নিয়ে পৃথিবী জয় করতে যেতে পারব । খেমি যদি বেঁচে থাকত তাহলে ওর মাইও হাতের পালিশ খেয়ে অপ্সরার মতন চকচকে আর বড়ো হতো, পীনোন্নত । কিন্তু ওর তো বিয়ে হয়ে যেত, ওর বরকে লুকিয়ে খেমির মাইয়ে হাত বোলাতুম, ওর ঠোঁট চেবাতুম, তালশাঁসের মতন খেতুম । বড়োজ্যাঠা মারা গেছেন, আমরা সেই দিনকার ঘটনা জানি । তবে তারিখটা কেউ মনে রাখেনি । বড়োজ্যাঠার জন্মদিন নেই, বড়োজ্যাঠার মৃত্যুদিন নেই । আলেকজাণ্ডারেরও নেই । বড়োজেঠা যেদিন মারা গেলেন, বাবা আমাকে অফিস থেকে ডেকে পাঠালেন জরুরি কাজ আছে, জানিয়ে । বাড়ি ফিরে দেখি কেবল নকাকিমা রয়েছেন, বললেন তাড়াতাড়ি খেয়ে নে, তোকে এক্ষুনি দিদিদের বাড়ি যেতে হবে । খেয়ে নিয়ে দিদিদের বাড়ি ছোটালুম সাইকেল । গিয়ে দেখি বড়োজেঠাকে বাঁশের মাচানে বেঁধে ফেলা হয়েছে । আমাকে যেতে হবে মুখাগ্নি করতে । সেই প্রথম শবকে ঘি মাখানো, পুরুত সতীশকাকার হুকুম অনুযায়ী মন্ত্র বলা আর কুশকাঠি-শরকাঠিতে আগুন ধরিয়ে মুখাগ্নি করার অভিজ্ঞতা, চিতাকে ঘিরে কাঁধে হাঁড়ি নিয়ে ফেলে দেয়া। শ্মশানে দাঁড়িয়েই কান্না পেয়ে গেলো, কাঁদলুমও, সতীশকাকা বললেন, হ্যাঁ, একে বলে শ্মশানবৈরাগ্য । হিন্দু মারা গেলে তার জ্বলন্ত দেহ থেকেও শেষবারের মতন শব্দগুলো পোড়া কাঠের সঙ্গে আকাশে ওড়ে, যাদের শব গোর দেয়া হয় তারা এই শেষ শব্দের গুঞ্জনের আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত ।
আমার এখন তিনটে জন্মদিন ; এগারোই কার্তিক, মায়ের বক্তব্য অনুযায়ী । উনত্রিশে অক্টোবর, স্কুলের সার্টিফিকেট অনুযায়ী । দোসরা নভেম্বর, ফাদার হিলম্যানের নির্ণয় অনুযায়ী । তিনদিন শুভেচ্ছা পাবার জন্য জন্মদিনের আর কীই বা চাই ।
আমাদের বাড়িতে জন্মদিনকে উৎসব করায় আমার স্ত্রী সলিলার ভূমিকা আছে ; আমার মেয়ে হলে তার জন্মদিন পালন করা আরম্ভ হয় । তার আগে জন্মদিন যে অনুষ্ঠান হিসেবে আমোদ-আহ্লাদ করার দিন তা জানতেন না কেউ । মেয়ের জন্মদিন পালন করা আরম্ভ হলে দোসরা নভেম্বরকে আমার জন্মদিনের স্বীকৃতি দিয়ে খানাপিনার ব্যবস্হা আরম্ভ হয় । রেস্তরাঁয় গিয়ে ককটেল পার্টি করার সেই সূত্রপাত। এমনকি জন্মদিনে যে কেক কাটতে হয়, মোমবাতি নিভিয়ে হ্যাপি বার্থডে টু ইউ গাইতে হয়, তারও ।
ষোলো
বড়োজ্যাঠার দুই মেয়ে, সাবিত্রী আর ধরিত্রীর বিয়ে আমার শৈশবেই হয়ে গিয়েছিল, তার কোনো স্মৃতি ধরে রাখতে পারিনি । মেজজ্যাঠা আর কাকাদের মেয়ের বিয়ের ব্যবস্হা করেছিলেন বাবা, কেননা তাঁদের শৈল্পিক উদাসীনতায় ওদের বয়স বেড়ে যাচ্ছিল ; তাছাড়া বিয়ের খরচের ব্যাপারটাও ছিল । মেজজ্যাঠার ছোটো মেয়ে মনু বা মীনাক্ষী একজন বিহারি ছেলেকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চাইলে, মেজজ্যাঠা অমত জানান । মেজজ্যাঠার অমত হওয়ায়, বাবা তাঁকে বোঝানো সত্ত্বেও তিনি রাজি হননি ; তাঁর বিরুদ্ধতা করে বাবা নিজে অংশ নিতে চাননি, আমাকে টাকাকড়ি দিয়ে বলেন, “ওরা কোথায় গিয়ে বিয়ে করতে চাইছে, সেখানে গিয়ে সম্প্রদান করে আয়।” সে এক মজার অভিজ্ঞতা, যেতে হয়েছিল খুসরুপুর নামে একটা ধাদ্ধাড়া গোবিন্দপুরের মন্দিরে, গিয়ে দেখি, সার বেঁধে বিয়ে হচ্ছে চত্ত্বরে । আমাকে একটা গোলাপি ধুতি দেয়া হয়েছিল, প্যাণ্ট খুলে পরে নিয়েছিলুম, তারপরে সম্প্রদান, বাঙালিদের বিয়ের মতন নয়, বা শহুরে বিহারিদের বিয়ের মতন নয় । ফেরার সময়ে পাটনা স্টেশানে নেমে রঙিন ধুতি খুলে প্যান্ট পরে নিয়েছিলুম ।
মা মারা যান লখনউতে আমার কাছে থাকার সময়ে, ১৯৮২ সালের ১৮ই নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে । বাবা মারা যান পাটনায়, ১৯৯১ সালের ৮ই অক্টোবর, তখন তিনি কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন আর দোকান চালানো আরম্ভ করেছে দাদার বড়ো ছেলে টোটোন বা হৃদয়েশ । আমার এটাই প্রধান রিগরেট যে বাবাকে আমি মুম্বাইতে নিয়ে আসিনি, তখন তো আমি মুম্বাইতে চাকরি করছি, বেশ বড়ো ফ্ল্যাট পেয়েছি সান্টাক্রুজে, আশেপাশে নামকরা হাসপাতাল । মায়ের মৃত্যু সম্পর্কেও রিগরেট থেকে গেছে যে প্রতিবেশী হায়দার আলিকে না জানিয়ে প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি করেছিলুম । নবাব পরিবারের হায়দার আলির প্রভাব ছিল সরকারি হাসপাতালে, আর লখনউতে সেসময়ে প্রাইভেট হাসপাতালের তুলনায় সরকারি হাসপাতালে যন্ত্রপাতি আধুনিক ছিল, ডাক্তাররা ছিল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ।
আমার চরিত্রগঠনে বা বিগঠনে খাঁটি অবদান মহাদলিতদের পাড়া ইমলিতলা ; সেখানকার অভিজ্ঞতা আমাকে শিক্ষিত করে তুলেছে, শিখিয়েছে মানসিক-ঔদার্য, সারগ্রাহীতা, তার প্রতিটি বাসিন্দা ছিল প্রতিষ্ঠানবিরোধী, বেপরোয়া, গোলমালকারী, স্হিতাবস্হাবিরোধী, যারা নিজেদের বলতো “দুনিয়াকা নাসুর”, মানে পৃথিবীর এমন নালি-ঘা যা সারে না, প্রথমে বিদেশি ও পরে স্বদেশি সরকার তাদের জীবনযাত্রার লড়াইকে মনে করেছে প্রতিরোধ-প্রতিবাদ, মনে করেছে মৌরসি-পাট্টার শত্রু, তাদের মনে করেছে বিপজ্জনক, অথচ তা ছিল ওদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা । জীবনকেচ্ছা প্রায় প্রতিদিনই ঘটতো ইমলিতলা পাড়ায় কিন্তু সেসব নিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্তের মতন কেউই খিক-খিকে হাসি হাসতো না ।
আর অবশ্যই বাড়ির-দোকানের দুই কাজের লোক, শিউনন্নি আর ডাবর । ১৯৫৫ সালে বি এন কলেজের ছাত্র ইউনিয়ানের জুলুসে আমি সামনের দিকে হাঁটছিলুম, আমার আর তরুণ শুরের হাতে ব্যানার, কোথা থেকে ডাবর ছুটে এসে আমার হাত ধরে বলল, “ই সব মত কিজিয়ে, মারে যাইয়েগা।” কয়েকদিন আগেই পুলিশের গুলিতে দীনানাথ পাণ্ডে নামে এক ছাত্র মারা গিয়েছিল, অকারণেই পুলিশ গুলি চালিয়েছিল, কেননা ছাত্রদের দাবি ছিল বাসের সংখ্যা আর সময় বাড়ানোর । প্রতিবাদ করতে বেরিয়েছিলুম আমরা, দাবি ছিল জুডিশিয়াল এনকোয়ারির । শেষে নেহেরুকে এসে বক্তৃতা দিয়ে ছাত্রদের শান্ত করতে হয়েছিল ; মুখ্যমন্ত্রী এস কে সিং অবস্হা সামলাতে হেগে ফেলার পর । তখনই নেহেরুকে একেবারে সামনে থেকে দেখেছিলুম । হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল বেশ উন্নাসিক মানুষ ।
আমি আমার সহ্যশক্তি আর যুঝে যাবার ক্ষমতা ইমলিতলা পাড়া থেকেই পেয়েছি : হাতকড়া, কোমরে দড়ি, জেলহাজত, শত্রুদল, কুখ্যাতি, অপমান, অপপ্রচার, বিরোধিতা, কটূ মন্তব্য, বিশ্বাসঘাতকতা । ইমলিতলাতেই জেনেছি, প্রতিটি নারীর দেহে নিজস্ব সুগন্ধ থাকে যা শহুরে মহিলারা পারফিউম মেখে নষ্ট করে ফ্যালে , পারফিউম জিনিসটা তাই আমার পছন্দও নয় , পাড়ার সকলের বাসার মতনই আমাদের বাড়িতেও কলিং বেল ছিল না, বাড়ির কারোর সঙ্গে দেখা করতে হলে তার নাম ধরে ডাকতে হতো , নাম ধরে ডাকার এই বাচনিক সম্পর্ক হারিয়ে গেল ইমলিতলা ছাড়ার পর , ইমলিতলার দিনগুলো নিজস্ব রঙে আর গন্ধে দেখা দিতো, রাতগুলো দেখা দিতো কেরোসিন লন্ঠন আর রেড়ির তেলের লম্ফর শিখায় । কাউকে কখনও সোনার গয়না পরতে দেখিনি ইমলিতলায়, রুপোর গয়না কেবল বিয়েতে । আমি সোনার আঙটি পেয়েছিলুম আমার উপনয়নে, যা আমি খুলে পরিয়ে দিয়েছিলুম আমার প্রথম আর শেষ রোমান্টিক প্রেমিকাকে, সে পরে ওই আঙটি পরিয়ে দিয়েছিল তার নতুন প্রেমিককে, যাকে সে বিয়ে করেছিল আর পরে ডিভোর্স দ্যায় ; জানিনা সেই আঙটির কী হল শেষ পর্যন্ত, কেননা ওর বর ছিল স্মাগলার । স্মাগলারকে বিয়ে করে ওর বিখ্যাত বক্তব্য মনে রেখেছি, “টাকা হল ডলারের বেজন্মা বাচ্চা”। ইমলিতলার মসজিদে লাউডস্পিকার ছিল না ; রমজানের সময়ে একজন ফকির ভোর রাতে গান গাইতে-গাইতে যেতো যাতে পাড়ার মুসলমান পরিবারের সদস্যদের ঘুম ভেঙে যায় । সেই ফকিরের এক হাতে সাপের মতন ব্যাঁকা ছড়ি আর অন্য হাতে লাউয়ের মোটা খোসা শুকিয়ে তাতে লোবানের ধোঁয়া।
মা, বাবা আর শিক্ষক, যে তিনজন মানুষ ব্যক্তিজীবনের অভিমুখ গড়ে দ্যান, আমার জীবনে মা আর বাবার ভূমিকাই প্রধান । প্রকৃত অর্থে প্রাইমারি স্তরে কনভেন্ট ছাড়া, রামমোহন রায় সেমিনারি স্কুলে এবং পরে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমি কোনো শিক্ষকের নৈকট্য এবং পথনির্দেশ ও বন্ধুত্ব পাইনি, সমাজে শিক্ষকের অবদানের অবনমন তখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়ে থাকবে । এখন তো শিক্ষকতা ব্যবসায়ের পর্যায়ে চলে গেছে । স্কুল শিক্ষকরা স্কুল ছেড়ে কোচিং আর প্রাইভেটে পড়ানোয় বেশি রোজগার করছেন । রামমোহন রায় সেমিনারিতে আমি ক্রমশ মূর্খ হয়ে যাচ্ছিলুম ; বেঁচে গিয়েছিলুম উঁচু ক্লাসের ছাত্রী আর স্কুলের লাঞ্চ পিরিয়ডের সময়ের গ্রন্হাগারিক নমিতা চক্রবর্তীর কারণে ; সিসটার আইরিনের পর উনিই আমার প্রকৃত শিক্ষক । সিসটার আইরিন আর নমিতা চক্রবর্তীকে মনে করলেই আঁচ করতে পারি যে ওনাদের অস্তিত্বে কোথাও অবিনশ্বরতা ছিল, যার কিছুটা ধুলো আমায় মাখিয়ে দিয়ে গেছেন ওনারা ।
কনভেন্ট বা ক্যাথলিক ইশকুলে ভর্তি হবার ঘটনাটাও ঐন্দ্রজালিক কেননা স্হানীয় ক্যাথেড্রালের যাযক ফাদার হিলম্যান, যিনি প্রচুর ফোটো তুলতেন, প্রায়ই আসতেন বাবার ফোটোর দোকানে, ওনার তোলা ফোটো ডেভেলাপ ও প্রিন্ট করাবার জন্য আর উনি বলতেন ভারত হল রামধনুর সাতটি রঙের বিস্ফোরণ । বাবার সঙ্গে ওনার প্রায় বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল । একদিন বাবা আমাকে দোকানে নিয়ে গিয়েছিলেন, খেলছিলুম, অসিযুদ্ধ করছিলুম অদৃশ্য দৈত্য-দানবদের সঙ্গে, সেসময়ের বক্স ক্যামেরায় ব্যবহৃত ফোটোর নেগেটিভের আস্তরণ, লম্বা লাল রঙের কাগজ দিয়ে পাকানো লাঠি নিয়ে, যা বাবার দোকানের কাজের লোক রামখেলাওন সিং ডাবর তৈরি করে দিয়েছিল। সেসময়ে ডিজিটাল ফোটোগ্রাফি আবিষ্কার হয়নি, শৌখিন ফোটো-তুলিয়েরা ক্যামেরাগুলো দিয়ে সাধারণত বারোটা বা ষোলোটা সাদা-কালো ফোটো তুলতো । ফিল্মের রিলগুলো হতো কাচকড়ার আর তার ওপরে লাল কাগজের আস্তরন । ফাদার হিলম্যানের মতন ধবধবে ফর্সা মানুষ আমি তার আগে দেখিনি ; মানুষের গায়ের রঙ এরকমও হয়, জেনে অবাক লেগেছিল ; ওনার পোশাকও এমন যে পুরো শরীর শাদা কাপড়ে ঢাকা, শুধু হাত দুটো বেরিয়ে, চুল সোনালী, চোখ কটা, এরকম চুলও দেখিনি আগে ।
ফাদার হিলম্যান বাবাকে বলেন, “একে স্কুলে ভর্তি করেননি কেন এখনও ? এই বয়সে যা পড়বে স্মৃতিতে আজীবন থেকে যাবে ।” বাবা জানান, “কোনো স্কুলে তো এতো ছোটো বাচ্চাকে ভর্তি করা হয় না, আর কনভেন্টে পড়াবার সামর্থ আমার নেই, কেননা আমার আর আমার ভাইদের খরচের পর কিছুই বাঁচে না । আমার বড়ো ছেলে যে সরকারি স্কুলে পড়ে সেখানেই একে ভর্তি করব দুই বছর পরে।” ফাদার হিলম্যান বাবাকে বলেছিলেন. কনভেন্টে এতো ছোটো বাচ্চাদের একটা ক্লাস আছে, তার নাম ট্র্যানজিশান ক্লাস, আপনি কালকে একে নিয়ে আসুন আমি ভর্তি করে নেবো, নেভি ব্লু হাফপ্যান্ট, শাদা হাফ শার্ট আর নটিবয় শুজ কিনে নিন আজকে, টাই স্কুল থেকেই দেয়া হয়, ফিসের কথা ভাববেন না, মুকুব করার ক্ষমতা আমারই । সেদিনই বিকেলে স্কুলের ড্রেস কিনে দিলেন বাবা, এতো বাবুলাট পোশাক আগে পরিনি কখনও, জুতো পরে বাড়িতে গটগটিয়ে হেঁটে দেখালুম সবাইকে । রান্নাঘরের সারাদিনের কাজ সত্ত্বেও মা ঘটিতে গরম জল ভরে শার্ট-প্যান্ট ইস্তিরি করে দিতেন ।
পরের দিন সকাল নটায় গিয়ে ভর্তি হয়ে গেলুম কনভেন্ট স্কুলে । জন্মদিন নির্ধারণ করলেন ফাদার হিলম্যান, দোসরা নভেম্বর । ভর্তি হয়ে টের পেলুম যে ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বললে শাস্তি পেতে হয় । ইংরেজি কেন, আমি তখন বাংলা আর হিন্দিও ভালো করে বলতে পারতুম না । চুপ থেকে, মাথা নেড়ে, কাজ চালাতে চালাতে রপ্ত হল ভাঙা-ভাঙা ভাষা । ফাদার হিলম্যান ছিলেন জার্মান, কিন্তু ইংরেজি আর হিন্দিতে কথা বলতে পারতেন । ভর্তি করিয়ে বাবা বলেছিলেন, “দুপুরে রাম খেলাওন সিং ডাবর টিফিন নিয়ে আসবে, আর ছুটির সময়ে ওর সাইকেলে করে বাড়ি ফিরবি । রোজই রামখেলাওন নিয়ে আসবে আর নিয়ে যাবে, কাল থেকে টিফিন নিজের সঙ্গে আনবি ।” এই স্কুলটা দাদার পাটনা কলেজিয়েট স্কুল থেকে আলাদা ; দাদার স্কুলে ঢুকেই দুধারে দুতলা ক্লাসবাড়ি, মাঝখানে সোজা পিচরাস্তা, বাড়ির পেছন দিকে দুটো বিশাল খেলার মাঠ, যেখানে ফুটবল আর ক্রিকেট খেলা হয়, আমি ওই মাঠে স্কুটার চালাতে শিখেছিলুম । ক্যাথলিক স্কুলে ঢুকেই একজন বউয়ের পাথরের মূর্তি, তার কোলে বাচ্চা, পেছনদিকে একজন লম্বা-দাড়ি মানুষ দাঁড়িয়ে, তার পায়ের কাছে দুটো ভেড়ার বাচ্চা । পরে ফাদর হিলম্যান হিন্দিতে জানিয়েছিলেন যে মাদার মেরির কোলে যিশু আর পেছনে সেইন্ট জোসেফ । মাদার মেরি ভার্জিন আর যিশুর বাবা হলেন ঈশ্বর স্বয়ং, মাদার মেরির বিয়ে হয়নি কেননা ঈশ্বরের সঙ্গে তো বিয়ে হতে পারেনা । ভার্জিন বলতে যে কী বোঝায় তার জ্ঞান হয়েছিল পরের স্কুল রামমোহন রায় সেমিনারিতে গিয়ে ।
কনভেন্টের গেটের ভেতর ঢুকলে বাঁদিকে একটা সবুজ ঘাসের মাঠ, ছাত্র-ছাত্রীরা খেলছে, ডানদিকে ফুলের বাগান। যে ছাত্র-ছাত্রীরা খেলছে, কয়েকজনের গায়ের রঙ ফাদার হিলম্যানের মতন ফর্সা, চুলও সোনালী, কালো তো নয়ই । কেউই ওই বাগানে যাচ্ছে না, ফুল তুলছে না দেখে অবাক লাগল । ইমলিতলার ছেলেরা দেখতে পেলে সব ফুল উজাড় করে তুলে নিয়ে গিয়ে দুর্গামাতার মন্দিরের সামনে বিক্রি করতে বসে যেতো, বিক্রি না করলেও চিবিয়ে মুচড়ে নষ্ট করে হাহা হিহি হাসতো সবাই মিলে । দাদার স্কুলে মাঠগুলো কনভেন্টের মাঠের চারগুণ বড়ো, তাতে বিশেষ ঘাস নেই । কনভেন্টের মাঠের মাঝখানে একটা গাছ, তার তলায় অজস্র ছোটো-ছোটো সাদা ফুল পড়ে রয়েছে, সেগুলোও কেউ তুলছে না । বাবা বলেছিলেন, ওটা বকুল ফুলের গাছ । তার আগে আমি বকুল ফুল দেখিনি ; ডানদিকের বাগানে যে ফুলগুলো হয়ে আছে সেগুলোও দেখিনি আগে । বাড়িতে দেখেছি শুধু গ্যাঁদা, গোলাপ, রজনীগন্ধা, বেলি, জবা আর জুঁইফুল, যখন বড়োজেঠিমা সত্যনারায়ণ পুজোর ব্যবস্হা করেন সংক্রান্তির দিন তখন; রামখেলাওন সেসব ফুল গিয়ে গঙ্গায় ফেলে আসে । কনভেন্টের ফুল গাছেই শুকিয়ে ঝরে যায় ।
ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতেই, ছাত্র-ছাত্রীরা, কোথায় সবাই এতক্ষণ ছিল জানি না, ছুটে এসে ডানদিকের বকুলগাছের মাঠে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ; ছোটোরা সামনে আর বড়োরা পেছনে, পাঁচটা সারি। একজন সিসটার, তিনিও ধবধবে সাদা, আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে একটা সারির সামনের দিকে ছোটোদের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দিলেন আর আমার হাত দুটো নিয়ে হাতজোড় করিয়ে দিয়ে চলে গেলেন । সিসটাররা আর ফাদার হিলম্যান আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে মুখ করে ইংরেজিতে গানের মতন করে কথা বলা আরম্ভ করলেন আর ছাত্র-ছাত্রীরা সকলে তাঁদের সঙ্গে সেগুলো বলতে লাগল । প্রতিদিন শুনে-শুনে একসময়ে মুখস্হ হয়ে গেলে আমিও বলতুম, কিন্তু তখন মানে জানতুম না, জানতুম না যে একে বলে প্রেয়ার বা প্রার্থনা। না জেনে যে ঈশ্বরের বন্দনা গান গেয়েছি, জানার পর যাঁর সম্পর্কে আমি আজও কিছুই জানি না, তার প্রার্থনাটা এরকম :-
আওয়ার ফাদার ইন হেভেন
হোলি বাই ইয়োর নেম
ইয়োর কিংডাম কাম
ইয়োর উইল বি ডান অন আর্থ অ্যাজ ইন হেভেন
গিভ আস টুডে
আওয়ার ডেইলি ব্রেড
অ্যাণ্ড ফরগিভ আস আওয়ার সিনস
অ্যাজ উই ফরগিভ দোজ
হু সিন এগেইনস্ট আস
ডু নট ব্রিং আস টু দি টেস্ট
বাট ডেলিভার আস ফ্রম ইভিল
আমেন ।
প্রার্থনা শেষ হতেই সবাই নিজের ক্লাসের দিকে দৌড়োলো । আমাকে একজন সিসটার হাত ধরে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে সেই ঘরে যে সিসটার তখনই এসেছিলেন, তাঁকে কিছু বললেন ।
‘সিন’ ব্যাপারটা যে কি তা তখন জানতে পারিনি, এখনও জানি না । এখন যা জানি তার নাম গিল্ট।
স্কুলে আমার ট্র্যানজিশান ক্লাসের শিক্ষিকা ছিলেন সিস্টার আইরিন, আমার প্রথম ক্রাশ, যাঁকে পরে সেকেন্ড স্ট্যাণ্ডার্ডেও পেয়েছিলুম । উনি এসেছিলেন আয়ারল্যাণ্ড থেকে । ফাদার হিলম্যানের মতন উনিও ধবধবে ফর্সা, কিন্তু ওনার মাথা পুরোপুরি ঢাকা, শরীরও শাদা কাপড়ে ঢাকা । ওনার চোখের তারা কালো আর গভীর ছিল, দাঁত ঝকঝকে সাদা, ঠোঁট গোলাপি । প্রথমদিন উনি নিচু হয়ে আমার মুখের কাছে মুখ এনে যা বলেছিলেন তা আমি বুঝতে পারিনি ; মনে আছে সিসটার আইরিনের চোখের তারায় আমার প্রতিচ্ছবি । উনি কয়েকটা পুস্তিকা আর একটি বই দিলেন, সবই ব্রিটেনে ছাপা, কার্ডও দিলেন একগোছা। মনে আছে, সেগুলো ছিল যিশুখ্রিস্টের, মাদার মেরির আর সান্টাক্লজের । বইটিতে প্রায় প্রতিটি পাতায় ছবি আঁকা ছিল । অন্য একটা পুস্তিকায় প্রতিটি পাতায় একটা করে ইংরেজি অক্ষর ছিল, সেগুলোর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সবাই সময় কাটাচ্ছিল, সিস্টার আইরিন আমার হাত থেকে পুস্তিকাটা নিয়ে খুলে ইশারায় দেখালেন যে সবাই যা করছে আমিও যেন তাই করি । পাতা উল্টে অক্ষর আর সঙ্গের ছবিগুলো দেখলুম ।
পরে আরেকটা রঙিন পুস্তিকা খুলে সিসটার আইরিন নিজেই শোনাতে লাগলেন, পরের ক্লাসে যাকে নার্সারি রাইম বলে জেনেছি, “হে ডিডল ডিডল, দি ক্যাট অ্যন্ড দি ফিডল, দি কাউ জাম্পড ওভার দি মুন, দি লিটল ডগ লাফড টু সি সাচ স্পোর্ট, অ্যান্ড দি ডিশ র্যান অ্যাওয়ে উইথ দি স্পুন।” আরেকটা, “পিটার পিটার পাপ্মকিন ইটার, হ্যাড এ ওয়াইফ অ্যাণ্ড কুড নট কিপ হার, হি পুট হার ইন এ পাম্পকিন শেল, অ্যাণ্ড দেয়ার হি কেপ্ট হার ভেরি ওয়েল।” এই দুটো আমার মনে থাকার কারণ পরের ক্লাসেও এগুলো সবাই মিলে আবৃত্তি করতে হয়েছে, অভিনয় করে, আর তিন দশক পরে আমার মেয়েকে যখন এই স্কুলে ভর্তি করি, তখন তাকেও একই নার্সারি রাইম মুখস্হ করতে হয়েছে, অথচ ততদিনে পুরো স্কুলে কেরালিয় সিসটারদের নিয়ন্ত্রণ, বিদেশিনী কেউ নেই । পরের ক্লাসে এবিসিডি শিখতে হয়েছিল গেয়ে গেয়ে । ওয়ান টু থ্রি ফোরও গেয়ে । একটা নার্সারি রাইম মনে আছে, যেটা পরেও কাজে লাগত, “থার্টি ডেজ হ্যাথ সেপ্টেম্বর, এপ্রিল জুন অ্যাণ্ড নভেম্বর, থার্টি ওয়ান দি আদার্স ডেট, এক্সেপ্ট ইন ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি এইট, বাট ইন লিপ ইয়ার উই অ্যাসাইন, ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি নাইন।” তখন এগুলোর মানেই বুঝতে পারতুম না । নার্সারি রাইমের ছন্দ মনের ভেতরে বিরক্তির বীজ হয়ে থেকে গিয়েছিল, যে কারণে কবিতা লিখতে আরম্ভ করে ছন্দ ব্যাপারটাকে পছন্দ হতো না । দাদা শিখিয়েছিল গুণে-গুণে পয়ার ছন্দে লেখার কায়দা, কিন্তু তাতে আমি স্পিড বা গতি খুঁজে পাইনি ।
বাংলা “আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি, যদুমাস্টার শশুর বাড়ি, রেলকম ঝমাঝম, পা পিছলে আলুর দম”, আমার জাঠতুতো-খুড়তুতো বোনেরা মাটিতে হাঁটুমুড়ে বসে খেলতো, হাঁটুতে চাপড় মেরেমেরে, এক একটা হাঁটু আউট হয়ে গেলে যার হাঁটু বাঁচতো সে জিতে যেতো । সেরকমই, “ঝাঁকড়া চুলে তালগাছ তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই, আমার মতো পড়া কি তোর মুখস্হ হয় নাই, দাঁড়িয়ে আছিস কান ধরে ঠায়, একটুখানি ঘুমায় না তোর পণ্ডিত মশাই”, এটাও ছিল ওদের খেলা, কে এক পায়ে কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, যে সবচেয়ে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতো সে জিতে যেতো । এগুলো তাই আমার কখনও নার্সারি রাইম মনে হয়নি।
কনভেন্ট স্কুলে, টিফিনের সময় গেটের কাছে ছোট্ট দরোজা দিয়ে রামখেলাওন আমাকে টিফিনকৌটো এগিয়ে দিয়ে জিগ্যেস করল, “ইংরেজিতে কথা বলতে শিখে গেছেন তো, এবার থেকে আমার বাড়িতে টাকা পাঠাবার মানি অর্ডার আপনি ভরে দেবেন ।” আমি মাথা নাড়িয়ে সায় দিয়েছিলুম । স্কুলে টিফিন খাবার হলঘরে ঢুকে খালি জায়গা দেখে খেতে আরম্ভ করেছিলুম ; অন্য ছাত্ররা প্রায় সবাই ইংরেজিতে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। একটা মেয়ে আমার পাশে এসে বসে ফিসফিসিয়ে বলল, হিন্দিতে, ও ইংরেজি বলতে পারে না, এমন করে হিন্দিতে কথাগুলো বলল, যে মনে হল বাঙালি, আমি বাঙলাতেই জিগ্যেস করলুম, “তোর নাম কী” । হাসি ফুটল ওর মুখে, ওর নাম নন্দিতা, ন্যানডি । আমিও আমার নাম বললুম । ন্যানডি বলেছিল, “ওঃ, তোর নাম ময়লা !” ফিসফিসিয়ে কথা বলার সম্পর্ক তৈরি হল আমাদের । এই সম্পর্ক বহুদিন বজায় ছিল, তার কারণ নন্দিতাও কনভেন্ট ছেড়ে আমার সঙ্গেই রামমোহন রায় সেমিনারিতে গিয়ে ভর্তি হয়েছিল । সেখানে গিয়ে আমাকে ময়লা নামে ডাকার ফলে বেশ কয়েকজন সহপাঠী ময়লা বলে ডাকতো । ধনী পরিবারের ছিল নন্দিতা, হাইকোর্টের জজ ছিলেন ওর ঠাকুর্দা, টিফিনে আনতো অমলেট-টোস্ট আর স্যালাড, প্রতিদিন, তাই আমার আলুছেঁচকি বা আলুপটল বা টমেটো-কুমড়োর সঙ্গে রুটি ওর খেতে ভালো লাগত, যেমন আমার লাগত ওর অমলেট-টোস্ট-স্যালাড । আমরা দুজনে কনভেন্ট ছেড়েছিলুম আর রামমোহন রায় সেমিনারিতে গিয়ে বাংলা মিডিয়ামে ভর্তি হয়েছিলুম একই কারণে, ভারত স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল আর আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, ইংরেজির দাপটে আমাদের জিভ থেকে খসে-খসে ভুল পথে চলে যাচ্ছিল।
টিফিনের পরের ক্লাসে ফাদার হিলম্যান এসে আমাদের নিয়ে চললেন স্কুল সংলগ্ন গীর্জায়, বাইবেল ক্লাস করার জন্য । গীর্জার ছাদ অনেক উঁচু, বিরাট হলঘর, দুপাশে বসার বেঞ্চ আর সামনে টেবিল, চারিদিকের দেয়ালে সন্তদের ছবি, তাদের সকলের মাথার পেছনে গোল জ্যোতি, আরও ওপরে, রঙিন কাঁচ দিয়ে তৈরি ভেড়া, দাড়িওলা মানুষ, ঘোমটা-দেয়া বউ, আরও নানা রঙের নকশা । একেবারে সামনে একজন মানুষের মূর্তি, তার হাতে পেরেক মেরে আর দুই পা জোড়া করে পেরেক মেরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে । দেখে, সবচেয়ে প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, এই ভাবে হাতে-পায়ে পেরেক ঠুকে কি একজন মানুষকে ঝুলিয়ে রাখা যায়, লোকটা কি খসে পড়বে না, লোকটা তো কাঠের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা নেই !
ফাদার হিলম্যান একবার ইংরেজিতে, আরেকবার হিন্দিতে বুঝিয়ে বললেন যে যাঁকে অমনভাবে দেখা যাচ্ছে তাঁর নাম জিজাস খ্রাইস্ট, আর তার গল্প, তার বলা কথাগুলো, তিনি প্রতিদিন আমাদের শোনাবেন । যে কাঠে ওনাকে বিঁধে রাখা হয়েছে তার নাম ক্রস । আমাদের বললেন, হাতজোড় করে এক বুড়ো আঙুলের ওপর আরেক বুড়ো আঙুল রেখে ক্রস তৈরি করে টেবিলের ওপরে রেখে ওনার গল্প শুনতে । উনি একথাও বললেন যে টিফিনের পর সকলেরই একটু ঘুম পায়, তাই এই বাইবেলের গল্পের ক্লাস, ঘুম পেলেও ক্ষতি নেই । তারপর ওপরে রঙিন কাচে গড়া সন্তদের নাম বললেন ; প্রতিদিন বলতেন বলে মনে রয়ে গেছে, আরও মনে থেকে গেছে এইজন্য যে পাড়ার শিয়া মুসলমান পরিবারের মেয়ে কুলসুম আপাকে যখন কনভেন্ট স্কুলের আর সন্তদের বিষয়ে গল্প করেছিলুম, তখন উনি বলেছিলেন যে ওই সন্তরা ইসলাম ধর্মেও আছে, কিন্তু নামগুলো উচ্চারণ করা হয় আরবিতে, যেমন এনোখ হল ইদ্রিস, নোয়া হল নুহ, অ্যাব্রাহাম হল ইব্রাহিম, জেকব হল ইয়াকুব, অ্যারন হল হারুন, মোজেস হল মুসা, ডেভিড হল দাউদ, জোনা হল ইউনুস, জন হল ইয়াহায়া, জিজাস খ্রাইস্ট হল ইসা মসিহ । বেশ ভালো লেগেছিল শুনে, কনভেন্ট আমার আর কুলসুম আপাদের বাড়ির মাঝে সেতুবন্ধনের কাজ করেছে যেন ।
পরে আজব লাগত যে জেকব লোকটার নামেই পাকিস্তানের ইয়াকুব খান, জন লোকটার নামে পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খান । ডেভিড লোকটার নামে মাফিয়া-নেতা দাউদ ইব্রাহিম । ফাদার হিলম্যান এসব গল্প জেনে যেতে পারলেন না । দাউদ ইব্রাহিম দাঙ্গা, ডাকাতি, র্যানসাম, হুমকি, চোরাচালান করেও হিরো, ফিলমের পর ফিলম হয়ে চলেছে, খবরের কাগজের পাতা জুড়ে, টিভির পর্দাজুড়ে তাকে নিয়ে হইহই রইরই, আর গরিবগুলো দুটো রুটি চুরি করলেই প্যাদানির নাম গঙ্গারাম, লকআপে মৃত্যু । আসলে নিজের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা খিদে প্রকাশ করার জন্যে শিক্ষা দরকার, চাকরি না পেলেও ক্ষতি নেই, যেমন দাউদ ইব্রাহিম, যৎসামান্য শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে পোঁদে বাঁশ করে দিতে পেরেছে । মানুষ “শব্দ” আবিষ্কার করেছে মৃত্যুদণ্ড লেখার জন্য ; তারপর মৃত্যুদণ্ড লিখে কলমের নিব ভেঙে ফেলার খেলা, এদিকে কলম কবেই তামাদি হয়ে গেছে, টিকে আছে কেবল মৃত্যুদণ্ড লেখার জন্য ।
সতেরো
কুলসুম আপার গভীর প্রভাব থেকে গেছে আমার জীবনে ; কবিতার জগতে প্রবেশ ওনার মাধ্যমেই। কনভেন্টের গির্জায় গাওয়া গান যেমন শৈশবে বুঝতে পারতুম না, অথচ শুনতে ভালো লাগতো, তেমনি কুলসুম আপার বলা কবিতা বুঝতে পারতুম না, অথচ ওনার গলায় শুনতে ভালো লাগত । রামখেলাওন সিং ডাবর রহিম, দাদু, কবীরের কিছু-কিছু দোহা জানত আর আমাদের শাসন করার জন্য সেগুলো সময়মতন বলত ; শিউনন্দন কাহার বা শিউনন্নি নামে বাড়ির কাজের লোক তুলসীদাসের রামচরিতমানস মুখস্হ বলতে পারত, শিউনন্দনও রামচরিতমানস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শাসন করত আমাদের । শিউনন্নি বজরংবলীর ভক্ত ছিল, বিয়ে করেনি, পাড়ার আখাড়ায় গিয়ে কুস্তি লড়ত, মুগুর ভাঁজত, চেহারা ছিল কুস্তিগীরের, অনেক বয়সে বিয়ে করেছিল, যাকে বিয়ে করেছিল তার দুটো বাচ্চা ছিল আগের পক্ষের । শিউনন্নি আমাকে ওর কুস্তি লড়ার আখাড়ায় নিয়ে গিয়েছিল আমার বয়সীদের সঙ্গে কুস্তি লড়ে স্বাস্হ ফেরাবার জন্য, কেননা আমি রোগাটে ছিলুম । কুস্তি শেখার ড্রেস, মানে ল্যাঙোট, মায়ের কাছ থেকে দাম চেয়ে নিয়ে কিনে এনেছিল শিউনন্নি । ল্যাঙোট পরা বেশ কঠিন ছিল ওই বয়সে, কয়েকবার পেছনে নিয়ে গিয়ে সামনে এনে বাঁধতে হয় । কুস্তি শিখতে অসুবিধা ছিল না, অসুবিধা হতো কুস্তির আখাড়ার গেরুমাটি গা থেকে ধুয়ে তোলবার জন্য রাস্তার কলে গিয়ে স্নান করার, পাড়ার বউদের জল ভরা হয়ে গেলে তারপর আমার পালা, যদিও শিউনন্নি আমাকে কলের তলায় ঠেলে দিত যাতে স্নানটা সেরে ফেলতে পারি । কয়েকটা রবিবারের পরই পালোয়ান হবার উচ্চাকাঙ্খা ছেড়ে দিতে হলো । কুস্তির প্যাঁচ কাজে দিত যখন পাড়ার কারোর সঙ্গে লাট্টু বা গুলি খেলা নিয়ে বচসা আরম্ভ হতো ।
সাঁতারও পুরো শেখা হয়ে ওঠেনি আমার । মামার বাড়িতে দাদা যখন ছিল, ১৯৫১ সালে,একবার পুকুরে শেখানোর চেষ্টা করেছিল, পুরো শেখার আগেই পাটনা ফিরতে হয়েছিল । দাদা মামার বাড়ি ছেড়ে উত্তরপাড়ায় থাকতে চলে গেলে, ১৯৫৩ সালে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়ে শেখানোর চেষ্টা করেছিল, তা সত্ত্বেও শেখা হয়ে ওঠেনি । আরেকটু হলে তলিয়ে যাচ্ছিলুম, তাই ।
ডাবর আর শিউনন্নির উদ্ধৃতি শুনতুম, কিন্তু পরোয়া করতুম না, কিন্তু গালে টোল ফেলে কুলসুম আপার কবিতা বলায় এমন আবহ গড়ে উঠত যেন উনি কবিতার মধ্যে দিয়ে নিজের দিকে টেনে নিয়ে চলেছেন । ফয়েজ আহমদ ফয়েজ আর গালিব ছিল ওনার প্রিয় কবি। কুলসুম আপা ইশতিমালিয়তের কথা বলতেন, যা পরে জেনেছিলুম, সাম্যবাদ ; ইশতিরাকিয়াতের কথা বলতেন, যা পরে জেনেছিলুম, সমাজবাদ ; মাসাওয়াতের কথা বলতেন যা পরে জেনেছিলুম সকল মানুষকে সমান মনে করা । ওনাদের পরিবারের কারণেই ইমলিতলা পাড়ায় দেশভাগের দাঙ্গার কোনো প্রভাব পড়েনি। স্কুল থেকে পাওয়া দুটো কার্ড উনি চেয়ে নিয়েছিলেন, একটা মুসার অন্যটা ইসা মসির ।
কুলসুম আপার স্মৃতি জেগে উঠলেই ফয়েজের এই বিখ্যাত কবিতাটা মনে পড়ে যায়, যদিও কুলসুম আপা বেশির ভাগ প্রেমের কবিতা শোনাতেন :
“মাতা-এ-লৌহ-ও-কলম ছিন গয়ি তো ক্যা গম হ্যায়
কি খুন-এ-দিল মেঁ ডুবো লি হ্যায় উংগলিয়া ম্যায়নে
জুবাঁ পে মোহর লগি হ্যায় তো ক্যা, কি রখ দি হ্যায়
হর ইক হলকা-এ-জঞ্জির মেঁ জুবাঁ ম্যায়নে”
যৌনতা ও স্পন্দিত ছোঁয়ার মাধ্যমে একজন কৌতূহলী বালকের মর্মে কবিতার গভীর ছাপ রেখে দেবার প্রথম শিক্ষাও কুলসুম আপার কাছে পেয়েছিলুম, আর বহুকাল পরে, তাঁর স্মৃতিতে, তাঁর খোঁজে ইমলিতলা পাড়ায় গিয়ে তাঁকে না পেয়ে, লিখেছিলুম এই কবিতাটা, “প্রথম প্রেম : ফয়েজ আহমদ ফয়েজ” শিরোনামে । কবিতাটার প্রথম লাইনটা মনে ছিল, এতোবার উনি শুনিয়েছিলেন, লেখার সময়ে ফয়েজের সংকলন থেকে বাকি অংশটা সংগ্রহ করেছিলুম :-
গরমের ছুটিতে খালি-গায়ে যখন নাজিমদের বাড়িতে
লুডো খেলতে যাই, কুলসুম আপা রাস্তা পেরোবার ঢঙে
বাঁদিক-ডানদিক তাকিয়ে দুহাতে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দ্যান
আমার অন্ধকার স্যাঁতসেতে ঘরে এক হ্যাঁচকায় টেনে নিয়ে ।
আমি বলি, ‘ভোজপুরি বলবেন, আমি উর্দু বুঝতে পারি না ।’
উনি বলেন, ‘তুই চোখ বোজ, তাহলেই বুঝতে পারবি,
এ তো খুব সহজ রে ।’ আমি চোখ বুজে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি
একগাদা হাঁসমুর্গির মাঝে ।
কুলসুম আপা বলেন, ‘মুঝে দে দে রসিলে হোঁঠ, মাসুমানা
পেশানি, হসিঁ আঁখেঁ কে ম্যায় একবার ফির রঙ্গিনিয়োঁ মেঁ
গর্ক হো জাউঁ…’
আমি বলি, ‘ধ্যাৎ, কী করছেন কী, আমার লজ্জা করে।’
উনি ওনার কালো মোটা ঠোঁটে বলতে থাকেন, ‘মেরি হস্তিকো
তেরি ইক নজর আগোশ মেঁ লে লে হমেশা কে লিয়ে
ইস দাম মেঁ মহফুজ হো জাউঁ জিয়া-এ হুস্ন সে জুল্মত-এ দুনিয়া
মেঁ ফির না আউঁ…’
আমি বলি, ‘আঃ, ছাড়ুন না, এরকম করছেন কেন আপা ?’
উনি বলেন, ‘গুজিশতাঁ হসরতোঁ কে দাগ মেরে দিল সে
ধুল জায়েঁ…’
আমি বলি, ‘ না না না…’
আপা ওনার ঘুমন্ত কন্ঠস্বরে, ‘ম্যায় আনে ওয়ালে গম কি
ফিকর সে আজাদ হো জাউঁ মেরে মাজি ও মুস্তকবিল সরাসর
মাভ হো যায়েঁ মুঝে ওয়হ ইক নজর, ইক জাভেদানিসি
নজর দে দে ।’
আমি বললুম, ‘রোজ রোজ এরকম করেন কেন ?’
উনি বললেন, ‘তবে যে তুই বলছিলিস উর্দু বুঝতে পারিস না !’
এখন জানি পেশানি মানে কপাল, গর্ক মানে ডুবে যাওয়া, রঙ্গিনিয়োঁ মানে অলঙ্কৃত, হস্তি মানে অস্তিত্ব, আগোশ মানে আলিঙ্গন, দাম মানে ফাঁদ, মহফুজ মানে সঞ্চিত, জিয়া-এ-হুস্ন মানে সৌন্দর্য্যের আলো, জুল্মত-এ-দুনিয়া মানে অত্যাচারী জগত, গুজিশ্তা মানে অতীত, হসরতে মানে দুঃখ প্রকাশ, মুস্তকবিল মানে ভবিষ্যত, মাভ মানে মুগ্ধতা, সরাসর মানে পুরোপুরি, জাভেদানি মানে অনন্তকালীন । কবিতা কিন্তু তখনও আমাকে আকৃষ্ট করেনি, আকৃষ্ট করেছিল কুলসুম আপার বড়ো-বড়ো চোখ, গালের টোল আর বুকের দেহতাপ । কবিতা বলতে বাড়িতে সকলের ধারণা ছিল গান । কবিতার কোনো বই ছিল না ইমলিতলার বাড়িতে, বস্তুত কোনো বইই ছিল না । উত্তরপাড়ার খণ্ডহরে ফারসি আর সংস্কৃতভাষার বই ছিল, ঠাকুর্দার সময়কার । ঠাকুর্দার আগের পূর্বজদের তালপাতায় লেখে পুঁথি ছিল, আমাদের ইতিহাসবোধ না থাকায়, সেগুলো উত্তরপাড়া থেকে পাটনায় নিয়ে আসিনি, শরিকরা গেঁড়িয়ে বেচে দিয়া থাকবে ।
কুলসুম আপাদের বাড়িতে রাস্তার সামনে বিড়ি-সিগারেটের যে ঘুপচি দোকানঘর ছিল, সেখানে বসে পরিবারের সবাই বিড়ি বাঁধত । আমার বিড়ি বাঁধার শিক্ষাও ওনাদের পাশে বসে ওই ঘরে । আরেকটা ব্যাপার জেনেছিলুম, ওনাদের দোকানের ঘরে ফ্রেমে বাঁধানো একটা মন্দিরের ছবি, আমি একদিন বলেছিলুম, তোমরা তো মুসলমান, মন্দিরের ছবি টাঙিয়েছ কেন ? কুলসুম আপার আব্বু বলেছিলেন, ওটা মন্দির নয়, ওটা আমাদের তীর্থক্ষেত্র কারবালা, পয়গম্বরের নাতি ইমাম হোসেনের সমাধি, যেমন তোদের কাশি । কুলসুম আপার দাদা মানে ঠাকুর্দা ওই তীর্থ করতে গিয়ে ছবিটা এনেছিলেন, নজাফ নামে একটা তীর্থ থেকে কারবালা পর্যন্ত তিরিশ ক্রোশ, মানে ষাট মাইল, হাঁটতে হয়েছিল, হাজার-হাজার তীর্থযাত্রীর সঙ্গে, রাতে রাস্তার ধারে ঘুমোতো সবাই । আরেকটা ছিল ফ্রেমে বাঁধানো সোনালী রঙের টিনের ডানাঅলা উড়ন্ত ঘোড়া, যার মুখটা মেয়েদের মতন ; ঘোড়াটার নাম ওনারা বলেছিলেন বুরাক, যাতে চেপে পয়গম্বর মক্কায় গিয়েছিলেন ।
কুলসুম আপাদের বাড়িতে সময় কাটাতে ভালো লাগত তার কারণ আমাদের বাড়িতে দাদা আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়ো, ওনার নিজের বন্ধুদের দল ছিল, বাঙালিদের পাড়া কদমকুঁয়ায় । মেজদা আমার চেয়ে তিন বছরের বড়ো, পাড়ার যে-সব ছেলেদের বখাটে বলে মনে করা হতো, মেজদার বন্ধু ছিল তারা, আমাকে তাই মেজদা পাত্তা দিত না । বড়োজ্যাঠার দুই মেয়ে আমার চেয়ে অনেক বড়ো, তাঁরা বিয়ে হয়ে শশুরবাড়ি চলে গিয়েছিলেন । অন্য বোনেরা সকলেই আমার চেয়ে বেশ ছোটো, ওরা নিজেদের মেয়েলি খেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতো । বাড়িতে নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্য পাড়ার সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে চোর-পুলিশ, গুলি বা লাট্টু বা ড্যাঙগুলি খেলতুম কখনও-সখনও। গু আর পাঁকের নর্দমায় লাট্টু বা গুলি পড়ে গেলে তুলে নিয়ে কলের জলে ধুয়ে নিতুম, অনেক সময়ে জাঠতুতো বা খুড়তুতো বোনেরা দেখে ফেললে বড়োজেঠিমাকে নালিশ করতো আর শুদ্ধ হবার জন্যে আমাকে সন্ধ্যাবেলায় ঠাণ্ডাজলে চান করতে হতো ।
মনে পড়ছে, কুলসুম আপার সঙ্গে আমার যৌন সম্পর্কের কথা কেবল ঠাকুমাকে বলেছিলুম কেননা কেবল ওনার সঙ্গেই গোপন ব্যাপার শেয়ার করতে পারতুম । শুনে উনি বলেছিলেন, জীবনে আর কখনও একথা কাউকে বলিসনি, আমাকে বলেছিস বলেছিস, আর কারো কানে যেন না যায় । খেমির কথা চেপে গিয়েছিলুম ওনার কাছে, কেননা খেমির বেলায় কোনো অপরাধবোধ ছিল না । প্রথম রোমান্টিক প্রেমিকার বেলাতেও অপরাধবোধ ছিল না, তবুও ঠাকুমাকে বলিনি ।
আরেকটা ঘটনা মনে পড়ছে । পাঁচ বছর বয়সে মা আমাকে ইমলিতলার একটা ঘরে শেকল তুলে বিকেল থেকে বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলেন, তার কারণ পাড়ায় আমাকে তাড়ি খাইয়ে দিয়েছিল, ‘পি লে পি লে, কুছ না হোতউ’ বলে । ইমলিতলার অন্য বিহারি বাচ্চাদের সঙ্গে আমিও দু-ঢোঁক খেয়েছিলুম, আর তাড়ির গন্ধে ধরা পড়ে গিয়েছিলুম । তাড়ি খাবার জন্য মা শাস্তি দেননি, দিয়েছিলেন যাতে আমি মেজদার মতন কুসঙ্গে পড়ে কুপথে না যাই । ইমলিতলায় বিজলিবাতি ছিল না । অন্ধকার ঘরে রাত দশটা পর্যন্ত একা বসেছিলুম এক কোণে । বাবা রাতে কাজ থেকে ফিরলে শেকল খোলা হয়েছিল । হয়তো এই ঘটনার আর এই রকম আরও কিছু ঘটনার চাপে আমি ক্রমশ অমিশুকে, হিন্দু-নাস্তিক, অন্তর্মুখ, অন্তেবাসী, সীমালঙ্ঘনকারী, দ্রোহী হয়ে গিয়ে থাকব ; গ্রন্হকীট হয়ে গিয়ে থাকব । আত্মসন্ত্রস্ত থাকার উদ্বেগ ও উৎকন্ঠার বীজ পোঁতা হয়ে গিয়ে থাকবে মনের ভেতরে ।
ক্যাথলিক স্কুলে ফিরি । একদিন ক্লাসের সবাইকে রাস্তার অন্য পারে একটা বাগানে নিয়ে যাওয়া হল , সেটার নাম ফার্ম, সেখানে দেখলুম সাদা রঙের শুয়োরদের লোহার জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে একটা জায়গায়, তার আগে আমি সাদা রঙের শুয়োর দেখিনি, বাচ্চা শুয়োর যাদের আস্ত পুড়িয়ে ‘সাকলিং পিগ’ রান্না হয় ক্রিস্টানদের ভোজে । নন্দিতা বলেছিল, এই শুয়োরগুলো সিসটাররা খায়, এদের গা্য়ে এতো চর্বি যে চোখ বুজে আসছে, এর সসেজ খুব ভালো হয় খেতে, একদিন তোকে খাওয়াব । ইমলিতলায় গঞ্জেড়ি-জমঘটে কালো ছোটো মাপের শুয়োর এনে কানাগলির লোকেরা খায় জানি, পুড়িয়ে খায়, সেগুলোকে দেখে নোংরা লাগত । আমরা বাচ্চা শুয়োরদের সঙ্গে খেলার জন্য একটা আলাদা ঘেরায় ঢুকলুম, বেশ লাগছিল জড়িয়ে ধরতে, নাদুস-নুদুস ফর্সা শুয়োর । দেখলুম বিদেশি গোরু, কখনও দেখিনি আগে এতো বড়ো গোরু, বাঁটও অনেক বড়ো, দুধে ভর্তি মনে হল । তার মানে খাঁটি দুধ খায় সিসটার আইরিন আর ফাদার হিলম্যান ; আমাদের বাড়িতে রাজু গোয়ালা দুধ দিতে আসে যখন, মা ওকে জিগ্যেস করেন, আজকে কতোটা জল মিলিয়েছিস, জল মেলালে নোংরা জল মেলাবি না, কলের পরিষ্কার জল মেলাবি ।
ফার্মে দেখেছিলুম কালো রঙের, প্রায় শকুনের মতন মাথা, ততই বড়ো পাখি, ওড়ে না, জাল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় । ন্যানডি বলেছিল, ওগুলো টার্কি পাখি, খ্রিসমাসের বড়োদিনে যে ভোজ হয় তাতে খায়, বেশ নরম আর ভালো খেতে । ফার্মের মুর্গিগুলোও বড়ো মাপের । আমাদের ইমলিতলার বাড়িতে মুর্গির ডিম আর মুর্গি খাওয়া বারণ । নন্দিতার বাড়িতে কিছুই বারণ নয় । ওর টিফিনের দৌলতে প্রায় রোজই মুর্গির ডিমের অমলেট খেয়েছি ।
ফাদার হিলম্যানের কাছে যিশুখ্রিস্টের গল্প শুনে আমি একদিন প্যাকিং বাক্সের দুটো কাঠ পাড় দিয়ে বেঁধে ক্রুসকাঠ বানিয়ে ইমলিতলার সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে পাড়ার গলিতে ঘোরা আরম্ভ করেছিলুম । পছনে যারা অনুসরণ করছিল তারা নিজেরাই “হিপ হিপ হুররে” স্লোগান দেয়া আরম্ভ করল, কেননা পাড়ার ফুটবল দল, কাবাড্ডি দল বা কুস্তিগির জিতলে এই ভাবেই স্লোগান দেয়া হতো । স্লোগান দিতে-দিতে দলবল নিয়ে বিরজুর বাড়ির কাছে পৌঁছোলে দেখলুম ওর মা মুখ গোমড়া করে বসে আছে, অন্যদের মতন আমায় দেখে হাসলেন না, আমি কী হয়েছে জানতে চাইলে বললেন ওনার ছোটো ছেলে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেল খাটতে চলে গেছে, ছোলা ভেজে বিক্রি করার মতন কাঠ নেই । আমি ওনাকে ক্রুসকাঠ পিঠ থেকে নামিয়ে দিয়ে দিলুম, উনি জানতে চাইলে যতোটা পারি জিজাস খ্রাইস্টের গল্প বললুম, উনি শুনে বললেন, তুইই আমার ‘জিজুয়া’ । স্কুল থেকে ফিরে প্রতিদিনই জিজাসের ‘জুলুস’ বের করতুম দুটো কাঠ দড়ি দিয়ে বেঁধে আর নানা গলি ঘুরে দিয়ে আসতুম বিরজুর মাকে ।
স্ট্যাণ্ডার্ড ফোরে উঠলুম ভারতের স্বাধীনতার সময়ে । কনভেন্টের মাঠে বিশাল সিল্কের ঝাণ্ডা টাঙানো হলো । সবাইকে এক প্যাকেট করে খাবার দেয়া হল । কিন্তু লক্ষ্য করলুম যে ফর্সা-সোনালী চুল ছাত্রীরা নেই, সিস্টার আইরিন আর ফর্সা সিসটাররা নেই, ফাদার হিলম্যানও নেই । বাড়ি ফিরে বাবাকে জিগ্যেস করতে উনি বলেছিলেন যে ওনারা আর ইনডিয়ায় থাকতে চান না, এতো দাঙ্গা আর গণ্ডোগোল হয়েছে আর চলছে, ওনারা নিরাপদ মনে করেননি, নিজেদের দেশে চলে গেছেন । শুনে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল । কনভেন্টে আর ভালো লাগছিল না । বাবা-মা নির্ণয় নিলেন যে আমার বাংলা কথাবার্তায় বিটকেল ইংরেজি আর পাটনাই হিন্দি বুলি ঢুকে গেছে, আমকে এবার বাংলা মাধ্যম স্কুলে দেয়া হবে, দাদার স্কুলে নয়, দাদার স্কুলে হিন্দি আর ইংরেজিতে পড়ানো হয় । স্বাধীনতার পরের বছর ভর্তি হলুম গিয়ে রামমোহন রায় সেমিনারিতে।
আঠারো
বাংলা মাধ্যমের একটাই স্কুল ছিল পাটনায়, রামমোহন রায় সেমিনারি, ভর্তি হয়ে গেলুম । ভর্তির সময় আমার জন্মতারিখের কথা মনে পড়ল বাবা-মার, কেননা এই জন্মতারিখ ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেটে থাকবে । কনভেন্টে ভর্তির সময়ে জন্মদিন নিয়ে ভাবেনি কেউ ; ফাদার হিলম্যান জন্মতারিখ জানতে চেয়েছিলেন, বাবা ওনাকে বলেছিলেন, আমার বড়োছেলের পাঁচ বছর পর ও জন্মেছে, শীতকালে, বোধহয় তখন নভেম্বর মাস । ফাদার হিলম্যান আমার জন্মদিন ধার্য করলেন দোসরা নভেম্বর ১৯৩৯ ।
রামমোহন রায় সেমিনারিতে ভর্তি হবার সময়ে সেই বছরের পাঁজি খুলে দেখা গেল যে দোসরা নভেম্বর পড়ছে অমাবস্যা, ১৯৩৯-এর বছর নয়, যে বছর ভর্তি হতে গেলুম সেই বছরের পাঁজি দেখে । ২৯ অক্টোবর সব দিক থেকে ভালো পাওয়া গেল, পুরুতমশায় সতীশ ঘোষালও বললেন, এই দিনটা অনেক শুভ। ব্যাস, আমার জন্মদিন ধার্য হয়ে গেল ২৯ অক্টোবর ।
কনভেন্টে ছিলুম স্ট্যাণ্ডার্ড ফোরে । ইংরেজিতে কথা বলতে পারার দরুন রামমোহন রায় সেমিনারিতে ভর্তি হয়ে গেলুম ক্লাস সিক্সে, বাংলা মিডিয়ামে । বড়ো হয়ে গিয়েছিলুম বলে ডাবরকে পৌঁছে দেবার আর নিয়ে আসার কর্তব্য থেকে মুক্তি দেয়া হল । বাড়ি থেকে স্কুল প্রায় দেড় কিলোমিটার, হেঁটেই যাতায়াত করতে লাগলুম, কী শীত কী বর্ষা । বর্ষাকালে ভিজে-ভিজেই ইশকুলে যেতুম, তখন কিন্তু অমন ভিজলে জ্বর হতো না । জ্বরজারি হবার জন্যেও বোধহয় যৎসামান্য পয়সাকড়ি হওয়া দরকার ।এই ইশকুলের কোনো ইউনিফর্ম ছিল না, এখন হয়েছে শুনি । তখন বাড়ির পোশাক পরেই স্কুলে যাওয়া যেতো ; ইচ্ছে হলে ইস্তিরি করা পোশাকে, নয়তো যার যেমন ইচ্ছে । আমার কনভেন্টের পোশাক যতোদিন চলেছিল ততোদিন ওই পোশাকেই যেতুম । ভর্তির সময়ে বাঙালি কেরানিবাবু, যাঁর ছেলে রতন আমাদের ক্লাসে পড়তো, বলেছিলেন, “এই স্কুল অনেক পুরোনো, ১৮৯০ সালে ব্রাহ্মসমাজের স্হাপন করা, ওপরে ওই দুই ছাত্রের ফোটো দেখছো, ওরা ১৯৪২ সালের অগাস্ট ক্রান্তির সময়ে রাজ্যের অ্যাসেমব্লি ভবনে জাতীয় পতাকা টাঙাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা যায়, ক্লাস নাইনের উমাকান্ত প্রসাদ সিনহা আর রামানন্দ সিংহ, অমন ডাকাবুকো হতে হবে তোমাকেও।” ইশকুলে যাবার পথে আর ফেরার পথে রাস্তার ইঁটে নটি বয় শু দিয়ে লাথি মেরে-মেরে ডাকাবুকোপনা ফলাতুম ।
এই কেরানিবাবুর সামনে, ১৯৫১ সালে, শাস্তি পেয়ে, ওনার ঘরে, সারাদিন ঠায় একা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল, দেয়ালে হেলান দেবারও অনুমতি ছিল না । এই শাস্তি ছিল আরেক ধরণের ডাকাবুকোভাব দেখাবার ফল । কয়েকজন সহপাঠী ক্লাসের একটি মেয়েকে বিরক্ত করছিল বলে আমি জিওমেট্রি বক্স খুলে কম্পাস হাতে মোকাবিলার চেষ্টা করতে গিয়ে আহত করে দিয়েছিলুম দুজনকে । ইশকুল ছুটি হয়ে যাবার পর বিভিন্ন ক্লাসের ছেলে-মেয়েরা চলে গিয়েছিল, সন্ধ্যাও নেমে এসেছিল, শীতের সন্ধ্যায় অন্ধকারও ঘনিয়ে আসছিল, কেরানিবাবু চলে গিয়েছিলেন, একাই দাঁড়িয়েছিলুম, ভয়াবহ একাকীত্বের মাঝে, তারপর হেডমাস্টার ক্ষেত্রমোহন পোদ্দার মশায় স্কুল সংলগ্ন কোয়ার্টার থেকে এসে বাড়ি যাবার অনুমতি দিলেন । কনভেন্টে নানরা কখনও একা বোধ করতে দেননি, যদিও ইংরেজিতে কাজ চালাবার মতন সড়গড় হতে সময় লেগেছিল, তবুও ।
রামমোহন রায় সেমিনারিতে, সবকটা ক্লাসঘরের বাইরে কালো বোর্ডে লেখা ছিল সেটা কোন ভাষার মিডিয়ামের কোন ক্লাস । আমি বাংলা মিডিয়ামের ক্লাস সিক্স বোর্ড দেখে পেছনের দিকে একটা সিটে বসতে যাচ্ছিলুম, একজন সহপাঠী বললে, তুই নতুন এসেছিস বোধহয়, এটা আমার সিট, তুই সামনের বেঞ্চে চলে যা। ক্লাসের দুটি সারিতে মেয়েরা, প্রায় সকলেই শাড়ি পরে, কয়েকজনের বয়স ছেলেদের তুলনায় বেশি ।এই স্কুলে ঘণ্টা বাজলে ক্লাস ঘরেই প্রেয়ার আরম্ভ হল, বাংলায় প্রার্থনা, কাউকে হাত জোড় করতে হলো না, বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী ক্লাস ফোর থেকে পড়ছে বলে তাদের মুখস্হ, গাইতে অসুবিধে হলো না, গলা ছেড়ে গাইতে লাগল সবাই, মনে হচ্ছিল স্কুলবাড়িটাই যেন গাইতে আরম্ভ করেছে । এই গান সম্পর্কে পরে আমাকে বোঝান ক্লাস নাইনের নমিতা চক্রবর্তী, যিনি সেসময়ে স্কুলের বাংলা লাইব্রেরির গ্রন্হাগারিকের দায়িত্বও টিফিনের সময় পালন করতেন । জীবনে প্রথমবার, ক্লাস সিক্সে আমি রবীন্দ্রনাথের গান আর কবিতার কথা শুনলুম ওনার কাছে । এখন স্কুলটির দুটো ভাগ হয়ে গেছে, সিনিয়ার আর জুনিয়ার; শুনেছি যে কেবল জুনিয়ার বিভাগেই প্রার্থনাটি সীমিত :-
আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর ।।
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে ।।
গ্রহতারক চন্দ্রপতন ব্যাকুল দ্রুত বেগে
করিছে পান, করিছে স্নান, অক্ষয় কিরণে ।।
ধরণী পরে ঝরে নির্ঝর, মোহন মধুশোভা
ফুলপল্লব-গীতবন্ধ-সুন্দর বরণে ।।
বহে জীবন রজনীদিন চিরনূতন ধারা
করুণা তব অবিশ্রাম জন্মে মরণে ।।
স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ,
কতো সান্ত্বন করো বর্ষণ সন্তাপ হরণে ।।
জগতে তব কী মহোৎসব বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে ।।
আমার পাশে দাঁড়িয়ে যে ছেলেটা গাইছিল, তার নাম তরুণ শূর, বেঁটে, দোহারা, কালো তেল চুকচুকে চেহারা, গলায় যেন কিছু আটকে আছে বলে মাঝে-মাঝে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে, তার মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের বন্ধুত্ব বজায় ছিল, তাকে গানটা এতো খটমট কেন, আর গানটার মানে কী, জিগ্যেস করতে, বলেছিল, ওসব জেনে কী করবি, গাইতে হয় গেয়ে যা, এটা পরীক্ষায় আসে না, এটা বেমমোদের গান, রবিবাবুর লেখা ।
—রবিবাবু আবার কে ?
—রবিবাবু জানিস না ? ওই যিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, লম্বা দাড়ি আর চুল ।
বুঝতে পারলুম, স্কুলটা ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত, তাই এই গান । এই প্রার্থনার মাধ্যমে আমি গলা ছেড়ে গান গাইবার সাহসও জুটিয়ে ফেলেছিলুম। আরও দুজন সহপাঠী বারীন গুপ্ত আর সুবর্ণ উপাধ্যায়, আমরা চারজন মিলে দরিয়াপুরের ফাঁকা বাড়িতে একসঙ্গে জড়ো হলে বাংলা হিন্দি গানের আসর বসিয়ে ফেলতুম । কিন্তু বড়োজ্যাঠা আর ঠাকুমা যদি জানতে পারেন যে আমি বেমমোদের স্কুলে ভর্তি হয়েছি, রবিবাবুর গান গাইছি, তাহলে গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে স্নান করাবেন, বাবাকেও নির্ঘাত গঙ্গাস্নান করাবেন, নতুন পৈতে পরাবেন ।
ইমলিতলার বাড়িতে, পাটনায়, উত্তরপাড়ার বসতবাটিতে আর মামার বাড়ি পাণিহাটিতে, রবিঠাকুর নিষিদ্ধ ছিলেন ; তাঁর লেখা আর গানের প্রবেশাধিকার ছিলনা বাড়িতে । পাটনা আর উত্তরপাড়ায়, ঠাকুমা আর বড়োজ্যাঠা-জেঠিমার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার সাহস বয়স্কদেরও ছিল না । রবিঠাকুর লোকটি যে ঠিক কে, আর কেনই বা তাঁর নাম বা কাজ মুখে আনা যাবে না সে কৌতূহল নিরসনের প্রয়াস বড়োরাও করতেন না ।
রবিবাবু লোকটিই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তা আমরা ভাইবোনরা, ইমলিতলায় টের পাই, আমি এই ব্রাহ্ম স্কুলে ভর্তি হবার দরুণ । রবিবাবুদের সম্পর্কে উষ্মার বীজ দাদু-ঠাকুমা বয়ে এনেছিলেন রাওলপিণ্ডি লাহোর কোয়েটা কোনো এক শহর থেকে । প্রথম আভাস মেলে একটি গানকে কেন্দ্র করে। বড়দি-ছোড়দি পণ্ডিত বুলাকিলালের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিখতেন । বড়োজেঠিমা সংক্রান্তির দিন ইমলিতলার বাড়িতে সত্যনারায়ণের পুজো করতেন আর সেই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ সমাবেশ হতো । পুরুতমশায় সতীশ ঘোষালের চাঁদ সদাগর হিতোপোদেশ শেষ হলে দিদিরা ঈশ্বর বন্দনার গান গাইতেন, ব্রজভাষা বা হিন্দি বা সংস্কৃতে । পুরুতমশায়ের অনুরোধে পণ্ডিত বুলাকিলাল একটা বাংলা ঠুংরি, সিন্ধু ভৈরবী রাগিনীতে, শিখিয়েছিলেন ছোড়দি সাবিত্রীকে । ছোড়দি সেতার বাজিয়ে গেয়েছিলেন, সঙ্গতে পণ্ডিতজি:-
কে ভুলালে হায়
কল্পনাকে সত্য করি জান, এ কি দায়,
আপনি গড়হ যাকে
যে তোমার বশে তাঁকে
কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায় ?
কখনো ভূষণ দেও, কখনো আহার ;
ক্ষণেকে স্হাপহ, ক্ষণেকে করহ সংহার ।
প্রভূ বলি মান যারে, সন্মুখে নাচাও তারে–
হেন ভুল এ সংসারে দেখেছ কোথায় ?
গান শেষ হলে বড়োজ্যাঠা আর পুরুতমশায় দুজনেই দুষলেন পণ্ডিতজিকে, অমন ম্লেচ্ছ গান শেখাবার জন্য । পণ্ডিতজি তর্ক দিয়েছিলেন যে শহরের বহু গণ্যমান্য পরিবারে তিনি এই গান শিখিয়েছেন । তাঁকে জানানো হয়েছিল যে তারা ম্লেচ্ছ । ইমলিতলা পাড়ার কাউকে কিন্তু কখনও ম্লেচ্ছ তকমা দেয়া হতো না । গানটা ভুলেই যেতুম, যদি না রামমোহন রায় সেমিনারিতে ভর্তি হতুম । এই স্কুলে প্রতিবছর ভাদ্রোৎসব হতো, কোনও এক রবিবারে, ছাত্রছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকারা নৃত্যগীত ও নাটকের সন্ধ্যানুষ্ঠানে অংশ নিতেন, এবং অভিভাবকদের বলা হতো সেই অনুষ্ঠান দেখার জন্য । আমাদের বাড়ি থেকে মা-কাকিমারা আর বড়দি-ছোড়দি ছিলেন দর্শকাসনে । তাঁদের স্তম্ভিত আর আনন্দিত করে এই গানটি গেয়ে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়েছিল । ক্ষেত্রমোহন পোদ্দার যতকাল হেডমাস্টার বা প্রিন্সিপাল ছিলেন, ততদিন এই অনুষ্ঠান হতো ; তাঁর অবসরের পর, হিন্দিভাষীদের সংখ্যাধিক্যে, বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বসন্ত উৎসব ।
পুরুতমশায়-বড়োজ্যাঠার গানটি সম্পর্কে উষ্মার কারণ জানতে পারি বাবাকে জিগ্যেস করে । দাদু-ঠাকুমা যে-সময়ে লাহোর ইত্যাদি অঞ্চলে ট্যুর করে বেড়াচ্ছেন, সে-সময়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক নবীনচন্দ্র রায়ও ওই অঞ্চলে প্রচারে গিয়েছিলেন, এবং তাঁর মতাদর্শ, দাদু ও আরও কয়েকজন, বাঙালি ও পাঞ্জাবি, মেনে নিতে পারেননি। দাদু-ঠাকুমা নিজেদের গোঁড়ামি চাউর করে দিতে পেরেছিলেন বড়োজ্যাঠার মনে, আর বড়োজেঠিমা তো এসেইছিলেন পুরুতবাড়ি থেকে ।
আমার শৈশবে পাটনার অধিকাংশ বাঙালি এলিট পরিবার ছিলেন ব্রাহ্ম, আদিধর্মের ব্রাহ্ম । পণ্ডিত নবীনচন্দ্র রায় সেই অংশেরই প্রতিনিধি ছিলেন । দাদু যখন আপার ইনডিয়ায় ছিলেন, তখনই পাঞ্জাব হাইকোর্ট আর ব্রিটেনের প্রিভি কাউন্সিল রায় দিয়েছিল যে আদি ধর্মের বা ‘আনুষ্ঠানিক’ ব্রাহ্মরা হিন্দু নয় । কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান ব্রাহ্মরা ছিলেন ‘আনুষ্ঠানিক’ । প্রথমত, একান্নবর্তী পরিবারের গৃহকর্তা ও কর্ত্রীর ধার্মিক গোঁড়ামি এবং দ্বিতীয়ত বাঙালি এলিটসমাজ থেকে দূরত্বের কারণে, টুকরো হতে থাকা যাবতীয় ব্রাহ্মদের ‘বেমমো’ তকমা দিয়ে পরিত্যাজ্য করে দিয়েছিল ইমলিতলার বাড়ি। রামমোহন রায়ের লেখা ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পর্কে সেকারণেই উষ্মা। ‘বেমমোদের’ হেয় করার বীজ আমার মাও এনেছিলেন পাণিহাটির ওনার মামার বাড়ি থেকে । তার কারণ সেকালের স্নাতকোত্তর, মায়ের মামারা বা আমার দাদুরা, ব্রাহ্মদের বিরোধীতা করতেন, কারণ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের বিরোধিতা করে ব্রাহ্মসমাজের প্রায় প্রতিটি ট্রাস্টি ইংলণ্ডেশ্বরকে সমর্থন করে বিদ্রোহী সেপাইদের কড়া শাস্তি দাবি করেছিলেন ; ১৮৭১ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা প্রথমে ব্রাহ্ম, তারপর ভারতীয় । ১৮৭২এর ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী একজন ব্রাহ্মকে লিখে দিতে হয় যে, “আমি হিন্দু বা মুসলিম বা খ্রিস্টান বা ইহুদি নই ।” মায়ের মামার বাড়ির লাইব্রেরিঘরে উনিশ শতকের মনীষীদের ছবি টাঙানো থাকতো, কিন্তু নোবেল প্রাইজ পাবার পরও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি টাঙানো হয়নি । মায়ের বড়োমামা অনাদিনাথ চট্টোপাধ্যায় বলতেন যে, “রবিবাবু ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে বিকৃত করেছেন” ; যতোদিন তিনি বেঁচেছিলেন, ওই বাড়িতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কদর হয়নি ।
বাবা দরিয়াপুরে চলে আসার পর, কালক্রমে কাকারা কোতরঙ আর উত্তরপাড়ায় চলে যাবার পর, মেজো জেঠিমাও তখন মারা গেছেন, ইমলিতলার বাড়ি প্রায় ভুতুড়ে হয়ে গিয়েছিল বলে বড়োজ্যাঠা আর জেঠিমা দিদিদের বাড়িতে থাকতে চলে গিয়েছিলেন । দিদিদের বাড়িতে প্রায়ই গানের আসর বসত । ক্লাস নাইনের পর আমি বড়ো একটা যেতুম না, ভাইফোঁটা ছাড়া । কেননা গেলেই দিদিরা বলতেন, তোর বিষয়ে অনেককথা কানে আসছে । বড়োজেঠিমা বলতেন, কুপথে যেওনি বাপু ।
একবার বড়োজ্যাঠা দিদিদের বাড়িতে ওনার পরিচিতদের ডেকেছিলেন সত্যনারায়ণ পুজোর সান্ধ্যবাসরে । গিয়ে দেখি হলঘরে কার্পেটে বসে গান গাইছে বড়ো ভাগ্নি মঞ্জু, ওর সামনে ‘গীতবিতান’ খোলা, ছোড়দি সেতার বাজাচ্ছেন, হারমোনিয়ামে বড়দি আর তবলায় সঙ্গত দিচ্ছেন বৃদ্ধ বুলাকিলাল । ইজিচেয়ারে চোখ বুজে গান শোনায় বিভোর বড়োজ্যাঠা । বড়োজেঠিমা দেয়ালে ঠেসান দিয়ে হাতজোড় করে বসে আছেন। গানটা এই, গীতবিতান পূজা পর্যায় থেকে, এখন সর্বত্র গেয়, ব্রহ্মসঙ্গীত :
অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে ।
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো
সুন্দর করো হে ।
জাগ্রত করো, উদ্যত করো,
নির্ভয় করো হে ।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে ।
অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে ।
যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে
মুক্ত করো হে বন্ধ,
সঞ্চার করো সকল মর্মে
শান্ত তোমার ছন্দ ।
চরণপদ্মে মমচিত্ত নিস্পন্দিত করো হে,
নন্দিত করো, নন্দিত করো,
নন্দিত করো হে ।
অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে ।
বাড়ির বয়স্কদের অজান্তে, রবীন্দ্রনাথ, রবিবাবু থেকে রবিঠাকুর হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে পৌঁছে আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করে গিয়েছিলেন । ভারতীয় সংবিধান লাগু হবার পর, সমাজে ক্রমশ ক্ষমতা-নকশায় রদবদল ঘটতে থাকে, পাটনার সমাজকর্তাদের আসন থেকে বিদায় নিতে থাকেন ব্রাহ্মরা । ব্রাহ্মমন্দির মেয়েদের স্কুল, যে স্কুলে আমার জাঠতুতো-খুড়তুতো বোনেরা পড়ত, তা বন্ধ হয়ে যায়, মন্দির ভেঙে মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ে ওঠে । বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতিষ্ঠিত তাঁর বাবা-মায়ের নামাঙ্কিত মেয়েদের হাতের কাজ শেখার সংস্হা “অঘোর-কামিনী বিদ্যালয়” অবহেলায় ধুঁকতে থাকে । অথচ কেবল আমাদের আর আত্মীয়দের বাড়িতেই নয়, ব্রহ্মসঙ্গীত ওপরতলা থেকে চুয়ে গরিব বাঙালিদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল । পাণিহাটিতেও, একান্নবর্তী পরিবার যখন ভেঙে গেল, দাদুদের প্রজন্মের তিরোধানের পর, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন । অবশ্য ততদিনে রবীন্দ্রসঙ্গীত হয়ে গিয়েছিল পণ্যায়নের অন্তর্গত ।
উনিশ
আমাকে নিজেকে কিছু একটা হয়ে উঠতে হবে, সেই হয়ে ওঠার জন্যে থাকা প্রয়োজন দার্শনিক পরিকল্পনা এবং স্বপ্ন, তাকে বাস্তবায়িত করার মতন প্রজ্ঞা ও ক্ষমতা, এই ধরণের ভাবনাচিন্তা ভারতবর্ষে ইংরেজরা আসার আগে ছিল না । ব্যক্তির হয়ে ওঠার তত্ত্বটা ইউরোপের, খ্রিস্টধর্মের । অতীত বাঙালিসমাজের পৃষ্ঠভূমিতে যে নামগুলো আমরা পাই, এবং যাঁদের আমরা মনে করি “হয়ে উঠেছিলেন”, যেমন অদ্বয়বজ্র, ক্রমদীশ্বর, ইন্দ্রভূতি, অতীশ দীপঙ্কর, চৈতন্যদেব, জগৎমল্ল, জহুরি শাহ প্রমুখ, তাঁরা কেউই নিজেদের কিছু একটা “হয়ে ওঠার”, অথবা প্রতিস্ব নির্মাণের, অথবা সাবজেক্টকে অবজেক্ট জগৎ থেকে পৃথক ও স্বনির্ভর মনে করার, কিংবা ব্রহ্মাণ্ডপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতি নামের কৃত্রিম জ্ঞানপরিধির কথা চিন্তা করেননি । তাঁদের তত্ত্ববিশ্বে তা সম্ভব ছিল না । তাঁদের আমরা যে কারণে জানি ও শ্রদ্ধা করি, ইউরোপীয় তত্ত্ববিশ্বে নির্মিত হলে তা সম্ভব হতো না ।
ব্যক্তিসৃজনশীলতা ও ব্যক্তিস্বপ্নের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ইউরোপীয় মননবিশ্বের বাইরে বেরিয়ে, প্রজ্ঞাকে কৌমনিরপেক্ষ ব্যক্তিলক্ষণ হিসেবে আঁকড়ে না থেকে, ব্যক্তির কাজকে সমাজসৃজনরূপে কীভাবে আবার প্রতিষ্ঠা দেয়া যায়, আমার পক্ষে, কলেজে ঢোকার সময়ে তো বটেই, এখন সাতাত্তর বছর বয়সে পৌঁছেও, ভেবে কুলিয়ে ওঠা অসম্ভব । প্রাক ইংরেজ যুগের প্রকৃতি ও প্রকৃতিসঞ্জাত অজস্র দেবীদেবতাকে তাঁদের সিংহাসন থেকে তুলে ফেলে দিয়ে, ব্যক্তিমানুষকে অস্তিত্বের কেন্দ্রে বসিয়েছে ইউরোপীয় দর্শন । গ্রামীণ উন্নয়নের কাজে সারা ভারতে ঘোরাঘুরি করে, সাধারণ ভারতীয়দের দেখে এখন টের পাই কী ভয়ংকর সংকট তৈরি করে দিয়ে গেছে ইউরোপীয় দর্শন । পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির সমাজ এখন ইউরোপীয় দর্শনে নির্মিত প্রতিস্বের ব্যক্তিএককে গড়া । আমার শৈশব যেহেতু ব্যক্তিএকক নির্মাণের কারখানায় গড়ে ওঠেনি, ইমলিতলা আর রামমোহন রায় সেমিনারি ইশকুলকে তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলতে পারি যে ব্যাপারটাকে আমি বেশ দূরত্ব থেকে অনুধাবন করতে পারি । তার মানে এই নয় যে আমি নিজস্ব একটা দার্শনিক স্হিতি গড়ে তুলেছি । আমার সাহিত্যকর্ম, সাহিত্যের প্রচলিত ধারণাকে ছাপিয়ে বৃহত্তর এলাকায় একারণেই প্রবেশ করে ।
সনাতন বাঙালিসমাজে যাঁরা কিছু হয়ে উঠেছিলেন বলে এখন আমরা মনে করি, যাঁদের নাম আমি একটু আগে উল্লেখ করেছি, কিংবা বাউল, ফকির, সন্ন্যাসী, যা ইউরোপে ছিল না, নেই, তাঁরা এবং তাঁদের কাজকর্ম, আমরা সমাজ বলতে এখন যা বুঝি, তার বাইরে ঘটেছে । অর্থাৎ নিজের সামনে “অপর” মানুষকে দাঁড় করিয়ে নিজেদের “হয়ে ওঠা” প্রতপন্ন করতে হয়নি তাঁদের । তার মানে ইউরোপীয় স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্যে আসেপাশে লোকজন দরকার । ঠিক যেমন নেতা “হবার” জন্যে সভায় বক্তৃতা জরুরি ; লেখক “হবার” জন্য পুরস্কার ; কবি “হবার” জন্যে সম্বর্ধনা ।
নিজের কাছে নিজে সৎ হওয়া ছাড়া আর কোনোকিছু কেনই বা হতে যাবে মানুষ ? অপরের জন্যে কিছু করা, এবং নিজের “হবে ওঠার” জন্যে নিজের সামনে অপর বা অপরদের দাঁড় করানো, দুটো একেবারে আলাদা ব্যাপার । অপরদের নিজের মালমশলা মনে করাটা মোনোসেন্ট্রিক, ইউনিপোলার, ইউনিলিনিয়ার । কেবল মানুষ নয়, সমস্ত ধারণাই দেখা যায় তাদের অপরের বিপরীতে নির্মিত । আমি বড়ো হয়ে “অমুক হবো” ভাবতে গেলে শৈশব থেকে আমার সামনে তমুক-তুসুক থাকা জরুরি । সবাই সৎ হলে কারোর আর আলাদা ভাবে সৎ হবার দরকার হয় না । ভাবনাটাই আসবে না মাথায় । সত্যি কথা বলতে কী, হয়ে ওঠার খপ্পরে পড়লে, বাঙালির আর সনাতন বাঙালিত্ব টেঁকে না ।
চাকরি করার সময়ে দেখেছি, একজন নবযুবক অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সতত চিন্তিত থাকে কীভাবে ম্যানেজার “হবে”, ম্যানেজার “হয়ে গেলে” অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনেরাল ম্যানেজার, ডেপুটি জেনেরাল ম্যানেজার, জেনেরাল ম্যানেজার, চিফ জেনেরাল ম্যানেজার ইত্যাদি “হবার” চিন্তায় বিভোর থাকে । অবসরপ্রাপ্তি ঘটলেই যাবতীয় “হওয়াহয়ির” হাওয়া বেরিয়ে যায় । কবি-লেখকরা দেখি একইভাবে নানা পুরস্কারের সিঁড়ি বেয়ে কবি থেকে সুপারকবি “হবার” দিকে দৌড় দ্যান । প্রতিস্ব ব্যাপারটাই শেষে ফালতু হয়ে দাঁড়ায় । এ প্রসঙ্গে বলা চলে যে, ইংরেজরা আসার পর, বাঙালি ভাবুক ও শিল্পীসাহিত্যিক “চেতনা” নিয়ে যে সমস্ত গর্ব প্রদর্শন করেছেন, তার পৃষ্ঠভূমিটি ছিল দান-বিলোনো বলবান উপনিবেশবাদীর এবং অধীনস্হ সহজবশ্য গ্রাহীর । অনুশাসন কাঠামোটাই তো হেলেনিক । সে অনুশাসনের উৎসসূত্র ইউরোপের জ্ঞানভাণ্ডার, এবং ওই জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল তাঁদের শাসনক্ষমতা । তাঁদের জ্ঞানকাঠামো দিয়ে, তাঁদের নির্মিত বাস্তব দিয়ে তাঁরা জ্ঞানী, মনীষী, পপতিভাবান, নায়ক, ভাবুক, দার্শনিক ইত্যাদি চিহ্ণিত করার নকশাজাল বানিয়ে দিয়েছিলেন । ওই সমস্তের কোনোকিছু “হবার” স্বপ্ন কারোর থাকলে, তাঁকে ক্ষমতাজালটিকে মেনে নিয়ে, নিজের প্রতিস্বকে সেইমত নথি করাতে হবে । বলাবাহুল্য যে আমি শৈশব থেকে ওই ক্ষমতাজালটিকে অস্বীকার করার চেষ্টা করে গেছি, প্রান্তিক থেকেছি ।
প্রান্তিকতার কারণে, যা আমার “ছোটোলোকের ছোটোবেলা” পড়লে জানা যাবে, ইংরেজরা আর ভারতীয় জাতিয়তাবাদীরা ভূমিপুত্রদের পিটিয়ে নিজেদের প্রতিবিম্ব বানাবার যে বিশাল জাল ফেলেছিল, তাতে ধরা দিতে অস্বীকার করার প্রবৃত্তি আমার আপনা থেকেই গড়ে উঠেছিল । যে দার্শনিকতা সবাইকে পিটিয়ে সমান করতে চায়, সেখানে বাউল, ফকির, সাধু-সন্ন্যাসীর উদ্ভব ঘটে না । ইংরেজদের সরবরাহ করা বাঙালি আত্মপরিচয়ের জগৎটিতে, আমাদের ইমলিতলার একান্নবর্তী পরিবারটি, তার অদ্ভুত ও অযাচিত প্রান্তিকতার দরুণ, প্রবেশ করার সুযোগ পায়নি । তা ছিল “নতুন”, এবং যাঁরাই সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরাই আশ্রয় নিয়েছেন অবধারণাটিতে । অবধারণাটি বিশাল সময়প্রবাহে একটি প্রাথমিক মুহূর্ত চিহ্ণিত করতে চেয়েছিল, এবং তাতে শামিল হয়েছিলেন, কেন্দ্রস্হানীয় বাঙালি ; যখন কিনা আমাদের পরিবার ছিল প্রান্তিক।
একজন মানুষের এই আকাঙ্খা যে, “আমি অমুক হবো”, অনিশ্চয়তার এলাকায় লুকিয়ে থাকে । কিছু একটা “হতে চেয়ে” সফল হতে হলে তো নিখুঁত হতে হবে । সর্বজনীনতার কারখানায় গড়া নিখুঁত । নিখুঁত হবার প্রধান বাধা অনিশ্চয়তা । আমার শৈশব-কৈশোর কেটেছে অমন অনিশ্চয়তার পরিমণ্ডলে । যা অনিশ্চিত তা অন্যরকম । যারা অন্যরকম তারা অপর । তারা ব্যবস্হাটিতে খাপ খায় না । অপর হতে হবে এই ভাবনা অপর লোকটি ভাবে না নিশ্চয়ই । আমি জানতুম যে আমি মিসফিট, গোলমাল সৃষ্টিকারী, স্হিতাবস্হার বিরোধী ; কিন্তু তাই বলে নিজেকে অপর ভাবিনি । কুলসুম আপাদের পরিবারকে অপর মনে হয়নি । পাড়ার মহাদলিতদের অপর মনে হয়নি । তারা নানা জীবিকার মাধ্যমে সংসার চালিয়েছে, যেমন বাবা ফোটোর দোকানের মাধ্যমে চালিয়েছেন ইমলিতলা, দরিয়াপুর আর উত্তরপাড়ার সংসার । ফলে আমার জীবনকে একটি ইউনিলিনিয়ার গল্পে বেঁধে ফেলা কঠিন । একজন মানুষের জীবনী সেহেতু বিভিন্ন লেখকের হাতে বিভিন্ন হতে বাধ্য । কেননা সময়প্রবাহ মালটিলিনিয়ার, এই ধারণা আমি ১৯৫৯ সালে পেয়েছিলুম অসওয়াল্ড স্পেংলারের “ডিক্লাইন অফ দি ওয়েস্ট” বই থেকে । কেন্দ্র থেকে বৃত্তপরিধির দিকে যে পরিবর্তনশীল রেখাগুলো টানা যায় তা অসংখ্য, তা গোনা যায় না । কেউ যদি হয়ে ওঠার বা আকাঙ্খাপূর্তির কাহিনি বাঁধতে চান, তাহলে ওই অজস্র পরিবর্তনশীল রেখা থেকে যে কোনো একটি বেছে নিয়ে বৃত্তের মাঝখান থেকে বেরিয়ে পরিধিতে পৌঁছোবার গল্প লিখতে হয় । অথচ যতোগুলো পরিবর্তনশীল রেখা সম্ভব ততোগুলো গল্প দিয়ে তো লোকটা গড়ে উঠেছে ।
ধরা যাক শৈশব থেকে আমি বহু প্রাণী ও বস্তুর দিকে কেবল তাকিয়েছি, তাকাই, কারণে-অকারণে । শুধুমাত্র তাকাবার ইতিহাস আছে আমার । শুধুমাত্র স্পর্শের ইতিহাস আছে । কথা বলার ইতিহাস আছে । শোনার ইতিহাস আছে । সাক্ষাতের ইতিহাস আছে । বহু বাড়িতে ঢোকার আর বেরোনোর ইতিহাস আছে । হাঁটার ইতিহাস আছে । পোশাক পরার ইতিহাস আছে । চুল কাটার ইতিহাস আছে । তা থেকে কী-কী ছাঁটাই করে আমি আমার “হয়ে ওঠার” গল্প লিখব ? যে গল্পই লিখি না কেন, তা হবে সময়ের প্রতি একচোখোমি। স্হান বা স্পেসকে গুরুত্বহীন করে দেবে, এমন গল্প ।
“হয়ে ওঠার” একটা পথ হিসাবে দাদা, কলকাতায় বহুকাল কাটিয়েছে, বলল কলেজে ইকোনমিক্স আর ম্যাথামেটিক্স নিয়ে পড় । কলেজে ভর্তি হয়ে গেলুম আর ভর্তি হয়ে বুঝলুম ম্যাথামেটিক্স ব্যাপারটা আমার আয়ত্বের বাইরে তো ছিলই, ইকোনমিক্সেও গণিত লুকিয়ে আছে, তার নাম ইকনোমেট্রিক্স ।
কুড়ি
১৯৫৬ সালে এই বেড়া টপকে বেরিয়ে ইকোনমিক্সে স্নাতক পড়তে ঢুকলুম । মুখস্হ করতে আমি কোনো কালেই পারি না, তাই একটা বই ধরে-ধরে পুরোটা কয়েকবার লিখে নিতুম যাতে মনে থাকে । এই লেখালিখির দরুণ আকর্যণ করতে পারলুম নেপালি সহপাঠিনী ভূবনমোহিনী রাণা নামে মোটা কাচের চশমা পরা মোঙ্গোল সুন্দরীকে ; তার খাতাগুলো দরকার। দুজনে বন্ধু হয়ে গেলুম, আমার চুমু খাবার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল ভূবনমোহিনী, ‘রাহুকেতু’ উপন্যাসে যার নাম রাণো । ওর জন্যে ইংরেজিতে একটা কবিতা লিখেছিলুম, সেটাই আমার শেষ ইংরেজি কবিতা । মেয়েরাও যে মদ খায় তা ভূবনমোহিনীকে চুমু খেতে গিয়ে টের পাই । পরে ঘটনাটা হিন্দি লেখক ফণিশ্বরনাথ রেণুকে বলতে, উনি বলেছিলেন, কী করেছ কি, জানো কি রাণারা নেপালে কতো ক্ষমতাবান, জানতে পারলে তোমায় জ্যান্ত পুঁতে দেবে । আমি ভূবনমোহিনীকে তাড়ি খাইয়েছিলুম । চুমুর প্রতিদানে ওর জন্যে ‘এক্সচেঞ্জ এ কিস’ নামে এই কবিতাটা লিখেছিলুম :
লেট ইওর পারফিউমড হ্যালো
ফল ফর এ ফিউ সেকেণ্ডস
টু এনাবল মি ইন পিকিং আপ
দি মেমরি অফ ইওর গ্ল্যানসেস
ইউ লেফ্ট ইন দি নোটস আই লেন্ট ইউ
নট ফর নাথিং ! অ্যাট লিস্ট ইউ শুড
এক্সচেঞ্জ এ কিস, ইভন ফ্লাইং উইল ডু ।
ভূবনমোহিনী রাণা একমাত্র যুবতী যে আমাকে চুমু খাবার প্রতিদানে চড় মেরেছিল, কষে চড় । ‘রাহুকেতু’ উপন্যাসে লিখেছি ঘটনাটা । ফরাসি যুবতীকে চুমু খাবার ইচ্ছে পুরো হলো না, ওদের চুমুতে ফরাসি ভাষার নাকিসুর বাজনা থাকে বলে জানিয়েছিল উলিয়াম গথ নামে এক হিপি, কাঁচা মাছের সুবাস থাকে, কাঠমাণ্ডুতে একজনও ফরাসী যুবতী হিপি পাইনি, নইলে নির্ঘাৎ চুমু খেতুম, কচি ডাবের জল খাবার মতন করে, যে ভাষার সঙ্গে পরিচয় নেই সেই ভাষার যুবতীদের যোনি থেকেও গোপন সঙ্গীত ভেসে বেড়ায়, এটা আমার অভিজ্ঞতা।
স্নাতকস্তরে দ্বিতীয় হয়ে বেরোলুম ১৯৫৮ সালে । ১৯৫৯ সালে বাংলায় লেখা কবিতায় বাবার দেয়া ডায়েরির পাতা ভরে উঠেছিল, যা ইচ্ছে লিখছিলুম, বেপরোয়া হয়ে, ইমলিতলার বেপরোয়াভাব চলে এসেছিল কবিতা লেখাতেও । স্নাতকোত্তরে ইকোনমিক্সে স্পেশাল পেপার নিলুম মনিটারি থিয়োরি, আর সেখানেও গণিতের ভুত পিছু ছাড়লো না । ১৯৬০ সালে স্নাতাকোত্তরেও দ্বিতীয় হলুম । আমার মতন আমার প্রিয় দুই অধ্যাপক, ডক্টর আর এন ত্রিপাঠী আর ডক্টর জে এন সিনহার মনও খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার ফলাফলে । জীবনে পরীক্ষায় প্রথম হওয়া আর হলো না । নমিতাদির চাপানো মার্কসবাদ তখন মাথায় পোকা হয়ে ঘুরছে, হয়তো কুলসুম আপার প্রভাবও থাকতে পারে, ইমলিতলার জীবন তো বটেই। ডক্টর জে এন সিনহা একবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসে এসেছিলেন জমিদারি বণ্ড ভাঙাবার জন্যে, আমাকে দেখে বললেন, “ইকোনমিক্স পড়ে শেষে এই কাজ করতে হচ্ছে!” ওই সময়টা, ১৯৫৬ সালে ইনটারমিডিয়েট পাশ করে বেরিয়ে স্নাতকোত্তর হওয়া পর্যন্ত, আমি জীবনকে যতোটা পারা যায় জটিল করে তোলার চেষ্টা করে গেছি, যৌনতা, মাদক,যৌনতা, মাদক,যৌনতা, মাদক, যৌনতা, যখন কিনা সহপাঠীরা সবাই স্নাতক পড়তে ঢুকেই আরম্ভ করে দিয়েছে আইপিএস আইএএস আইএফএস, নিদেন স্টেট সার্ভিস কমিশনে ঢুকে যেতে । অনেকেই মাঝপথে পড়ে ছেড়ে আইপিএস আইএএস “হয়ে” গেল, আমি যখন স্নাতকোত্তর পাশ করলুম তখন ওরা প্রায় সবাই ঘুষের প্রাসাদ খাড়া করে ফেলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দরোজা দিয়ে বেরিয়েই ঘুষ নিতে পারা চাড্ডিখানি কথা নয় । আমার কোনো উচ্চাকাঙ্খা ছিল না, হবি ছিল না, পার্কে দৌড়োনো ছিল না, রোয়াকে বসে মেয়েদের সিটি বাজানো ছিল না । ছিল না ছিল না ছিল না ছিল না । অতীত জিনিসটাই যেন পচধরা । অতীতের কিছু ঘটনা থেমে যায়, কিছু ঘটনা চলতেই থাকে চলতেই থাকে চলতেই থাকে ।
কলকাতার পুলিশ কমিশনার আমাকে বলেছিলেন, “সো ইউ আর দি টপ ডগ” । তখন “টপ ডগ” এর মানে জানতুম না বলে খারাপ লেগেছিল, মনে করেছিলুম কুকুর বলছেন । উকিলকে কথাটা বলতে উনি যখন মানে বোঝালেন তখন মন্দ লাগেনি । তবে উকিল বলেছিলেন যে, “পুলিশ কমিশনারের কথা থেকে মনে হচ্ছে আপনাকে একাই কেস লড়তে হবে ।”
দরিয়াপুরের দেয়াল আলমারি জুড়ে আমার ব্যক্তিগত গ্রন্হাগার বন্ধুদের ঈর্ষার ব্যাপার হয়ে উঠল। বিরল বই থাকলে নানান কিসিমের বন্ধুরা জুটে যায় । পুস্তক মহল থেকে সাম্প্রতিক ইংরেজি বই কিনে আনতুম আর বাবা বিল পেমেন্ট করে দিতেন । আমার মামলার সময়ে আমার অনুপস্হিতিতে অনেক বই চুরি হয়ে গিয়েছিল, মার্কুইস ডি সাডের “হানড্রেড টৌয়েন্টি ডেজ অফ সোডোম”, হ্যাভলক এলিসের “কমপ্লিট ওয়র্কস”, জঁ জেনের “আওয়ার লেডি অফ দি ফ্লাওয়ার্স”, ম্যালকম এক্সের জীবনী, ডস্টয়েভস্কির “কমপ্লিট ওয়র্কস”, বিট আন্দোলনের পত্র-পত্রিকা, অভিধানগুলো, অনেক বই । অনেক জীবন একই সঙ্গে অনেক আমি, জিততে হবে অথচ জানি না কি জিততে হবে, পারতে হবে অথচ জানি না কি পারতে হবে, পৌঁছোতে হবে অথচ জানি না কোথায় পৌঁছোতে হবে, কারণ নেই, মগজে মৌমাছির ঘামগান, জীবনের মানে খুঁজতে চোখ বুজে লাফিয়ে-পড়া, হয়তো, হতে পারে, পোশাকের আগ্রহ ছিল না, নিয়মিত কাচার দরকার ছিল না, জুতোর আগ্রহ ছিল না, নিয়মিত পালিশের দরকার ছিল না, হাতঘড়ির আগ্রহ ছিল না, কেবল মনে হচ্ছিল দেশে-দেশে স্টুপিডরা রাষ্ট্রকে চালায়, ইমলিতলার লোকগুলো সপরিবারে গরিবই থেকে যাবে হাজার বছর । মনুস্মৃতির পাহাড় মাথায় চাপিয়ে লোকে কী করে সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখে জানি না, ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গীয় আঁতেলদের কোনো ধারণাই নেই , স্বাধীনতার ছয়টা দশক পেরিয়েও গ্রামগুলো জাতিপ্রথা দিয়ে ভাগবাঁটোয়ারা করা, জলভরার কুয়ো আলাদা, উঁচু জাতে প্রেম করলে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয় বা কোতল করা হয়, কলেজে তারা ব্র্যাণ্ডেড জুতো, পোশাক, চশমা, পারফিউমসহ গেলে ধনী উঁচুজাতের আক্রমণে পড়ে, যুবতীরা নখপালিশ লাগিয়ে মুখ ব্লিচিং করে গেলে কুকথা শুনতে হয় । তাই আমার কাছে লেখালিখি আর সাহিত্য-শিল্প এক জিনিস নয় । আমি লেখালিখির শুরু থেকেই নিজেকে যাচাই করে নিয়েছিলুম।
একুশ
দরিয়াপুরে, রান্নাঘরে মায়ের কষ্ট কমাবো ভেবে, মা এবার জীবন উপভোগ করুন ভেবে, ইনডেন গ্যাস সিলিণ্ডার কিনে দিলুম, ফ্রিজ কিনে দিলুম যাতে রোজ না রান্না করতে হয়, যাতে ওনার প্রিয় মাছের স্টক করে রাখতে পারেন, রাইস কুকার কিনে দিলুম যাতে ভাতের দিকে তাকিয়ে ঠায় বসে থাকতে না হয়, প্রেশার কুকার কিনে দিলুম যাতে রান্না তাড়াতাড়ি হয় । এই জিনিশগুলোকে রপ্ত করতে মায়ের অনেকদিন লেগে গেল, প্রায় বছর চারেক, ভয় পেতেন ওগুলোকে ; যুক্তি দিতেন যে ওগুলোর দরুণ রান্নায় স্বাদ হয় না । গ্যাস থাকতেও মা কয়লার উনুনের সামনে উবু হয়ে বসে রান্না করতে ভালোবাসতেন, পরে আমাকে বলতেন গ্যাসটা জ্বালিয়ে দিয়ে যা, নিভিয়ে দিয়ে যা । ফ্রিজ খুলতেন দূর থেকে একটা তোয়ালে দিয়ে হাতল ধরে, যদি শক মারে তার ভয়ে । প্রেশার কুকারের সিটির সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে পুড়িয়ে ফেলতেন । রাইসকুকার কোনোদিন ব্যবহার করলেন না । তবু মায়ের আনন্দ হল যে ওনার শ্রম কমাবার জন্য খেয়াল রেখেছি, বুড়ি বান্ধবীরা বেড়াতে এলে তাদের দেখাতেন । রান্নাঘর থেকে মাকে বের করে আনার জন্যে শেষে রান্নার বউ রাখতে হল, তারও যথেষ্ট বয়স হয়েছিল, তবু সিলিণ্ডারের গ্যাস, ফ্রিজ, প্রেশার কুকারে সড়গড় । পাটনা শহরে টিভি আসতেই, তখন শাদা-কালো, রঙিন হয়নি, মায়ের জন্যে একটা টেলিরামা টিভি কিনেছিলুম, প্রোগ্রাম সরকারি হলেও, দেখে আনন্দ পেতেন আর পাড়ার যতো বাচ্চারা, বেশিরভাগই দরিয়েপুরের মুসলমান পরিবারের, এসে জড়ো হতো ওনার চারিধারে মেঝের ওপর ।
মা বলেছিলেন, একটা গাড়ি কেন এবার, লোকেদের বাড়ি যাই । কিন্তু কেনা হয়নি, পাটনার বাড়িতে গ্যারাজ তৈরির জায়গা ছিল না । কিনলুম বটে, ফিয়াট, পরে মুম্বাইতে, নাবার্ডে অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনেরাল ম্যানেজার হয়ে, অফিস থেকে লোন নিয়ে । মা আর বাবা দুজনেই তখন মারা গেছেন । যখন লখনউতে বদলি হয়ে গেলুম তখন লখনউয়ের হেড পোস্টঅফিসে গিয়ে প্রতি শনিবার মাকে এসটিডিতে ফোন করতুম; পোস্ট অফিসে বুক করে অনেকের সঙ্গে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করতে হতো, আধঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে ডাক আসতো । এখনকার মতন মোবাইল হলে মায়ের সঙ্গে প্রতিদিন দুবেলা কথা বলা যেতো ।
উত্তরপাড়ার চিলেকোঠার ঘরে, কলকাতায় পড়াশুনার সময়ে আস্তানা নিয়েছিল দাদা, বইয়ের স্তুপ, বন্ধুদের গ্যাঞ্জাম, সিগারেটের ধোঁয়া, আমি গিয়ে পড়েছি অনেক সময়ে, পরিচিত হয়েছি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার, আনন্দ বাগচির সঙ্গে । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে মনে হতো ঘরণী টাইপের মানুষ । তার আগে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর শক্তি চট্টোপাধ্যায় আমাদের দরিয়াপুরের বাড়িতে এসে পাটনার ঠররা খেয়ে বারান্দায় বমি করে গেছেন । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলে গেছেন ওনাকে পাঠালে উনি আমার লেখা প্রকাশ করার ব্যবস্হা করবেন । দাদা চাকরি পাবার পর ধানবাদে থাকার সময়ে দীপক মজুমদারের সঙ্গে আড্ডায় উনি বলেন “ফিলজফি অফ হিসট্রি” পড়তে, দীপক মজুমদারকে দেখেছি ধানবাদে দাদার বাসন মাজছেন । দীপক মজুমদারকে মনে হয়েছে চাষি টাইপের মানুষ । ওনার বলা বিষয়ে বই পড়া আরম্ভ করি, আর লিখে ফেলি “ইতিহাসের দর্শন” যা পরে “বিংশ শতাব্দী” পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল, সম্পাদক যদি জেনে যেতেন আমার বয়স কতো তাহলে ছাপতেন কিনা সন্দেহ । তারপর নমিতা চক্রবর্তীর প্ররোচনায় আরম্ভ করলুম মার্কসবাদ নিয়ে একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ, যা বিমান মজুমদারের ছেলে, দাদার বন্ধু বুজলুদাকে পড়তে দিলে, বললেন, বই করে ফেলতে পারিস ।
দাদা কলকাতার কলেজে পড়ার সময়ে প্রায়ই যেতুম উত্তরপাড়া, পাণিহাটি, কোন্নোগর আর আহিরিটোলা । পাণিহাটি থেকে আহিরিটোলা যেতে হলে শেয়ালদা স্টেশান হয়ে যেতে হতো । শেয়ালদা স্টেশান তখন উদ্বাস্তুদের ভাঙা সংসারে ছয়লাপ, কলকাতার রাস্তায় মিছিল, বাস-ট্রাম পুড়ছে, দেখে মনে হতো কেউ শোনার নেই । সেসময়ে সদ্য-সদ্য ট্র্যাজেডি থেকে জন্ম হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের, আর নিজেকে মনে হতো শেকসপিয়ারের ট্র্যাজেডিগুলোর ভাঁড়দের মতন, কিং লিয়ারের ফুল, হ্যামলেটের কবরখুঁড়িয়েরা, ওথেলোর ক্লাউন, ম্যাকবেথের পোর্টার, অ্যাজ ইউ লাইক ইটের টাচস্টোন, টুয়েল্থ নাইটের ফেসটে । কলকাতার ওই সময়ের দুর্দশার জোয়ারের ঢেউগুলোকে আমি ধরার চেষ্টা করেছি আমার ‘নামগন্ধ’ উপন্যাসে । মানুষের পীড়া দুর্ভোগ বাঁচার লড়াইয়ের যন্ত্রণা দেখে, তাদের অসহায় গোঙানি শুনে, নিজের ব্যর্থতা অনুভব করা সহজ হয়, টের পাওয়া যায় যে আমি একটা গাছের পাতাও নড়াবার সামর্থ রাখি না । শহরের হাওয়ায় তাদের বিলাপ আজও অভিশাপ হয়ে ভেসে বেড়ায় । নিজেকেই প্রশ্ন করি, কী করা যেতে পারে ? কলম দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় বিষের চোলাই !
দাদার সব বন্ধুদের দেখেছি তো ! কাউকেই মনে হয়নি দাদার মতন আর আমার মতন মিসফিট, গোলমালকারী, স্হিতাবস্হাবিরোধী ইমলিতলা-মার্কা ইনসেন টাইপের ; ওনাদের উচ্চাকাঙ্খা সাহিত্যকে আঁকড়ে কেরিয়ার করার । অথচ আমার আর দাদার মতন ইমলিতলাপন্হী ইনসেন না হলে আন্দোলন গড়ে তোলা যাবে না । এনাদের বহু বাক্যের সঙ্গে মুখের দুর্গন্ধ লেগে থাকে, পায়োরিয়ার, বদহজমের, বায়ুর, দাঁতের ফাঁকে পচা ছাগলের, শব্দের অর্ধেক মানে তাতেই আটকে যায় । পরে এনাদের কাজকারবার দেখে পায়খানাগুলো পর্যন্ত লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা । আর সেই মোক্ষম দর্শন । টাকা হল ডলারের বেজন্মা বাচ্চা । ওনাদের সমবেত বা একক কাজকারবার দেখে মনে হয়েছে, আমি বোধহয় একরকম স্টুপিড গর্ববোধে ভুগি, সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে, যাকে অ্যালেন গিন্সবার্গ বলেছিল “নাঈভ”, যার দরুন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্হান, প্রেমে লাথি, বন্ধুদের বিশ্বাসঘাতকতা, জোচ্চুরি, টাকা হাপিশ। পৃথিবীর সঙ্গে আমিও পাক খাই । ওহ, বলতে ভুলে গেছি, দাদার রোলেক্স ঘড়িটা এক বন্ধু হাপিশ করে দিয়েছিল চাইবাসায়, তারপর থেকে দাদা ঘড়ি পরা ছেড়ে দিলো ।
পশ্চিমবঙ্গ কি সেই পঞ্চাশ-ষাটের ট্র্যাজেডি থেকে বেরোতে পেরেছে ? না, পারেনি, জানি না কখনও পারবে কিনা । তা থেকে গেছে, স্হায়ী বিশৃঙ্খলা, অকারণ ক্রোধ, অরাজকতা, নৃশংসতা, গণধর্ষণ, নারীপাচার আর ঘৃণা নিয়ে । ওপর থেকে চুয়ে-চুয়ে পৌঁছে গেছে নিচের তলায়, যেখানে সামান্য কিছু নড়ে উঠলেই মানুষ ভয়ে আঁৎকে ওঠে, আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে, প্রতিপক্ষ থাকুক বা না থাকুক । যারা নায়ক হয়ে উঠতে চেয়েছিল তারাও কালক্রমে খোলোশ থেকে বেরিয়ে নির্মল জোকারের চেহারার সঙ্গে জনগণের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে , জনগণ জোয়ারের সঙ্গে আসে ভাটার সঙ্গে যায়, তাদের জানা নেই যে শহর আর শহরতলিগুলো থেকে সৌন্দর্য্য কবেই পালিয়েছে, কেউই আর প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না, বহু পরিবার ওই ট্র্যাজেডিকে পারিবারিক স্মৃতির আনন্দের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে, মাছের বদলে সেই আনন্দে তারা নিয়ে এসেছে বিরিয়ানি, স্টিউ, সসেজ, পাস্তা, হ্যামবার্গার, হটডগ — মাছেরাও বিদায় নিচ্ছে এক-এক করে, তৈরি হয়েছে চাষের মাছ, বিয়েতে টকটকে লাল ধুতি আর উত্তর ভারতের শেরোয়ানির মতন, যেগুলো কবি অজিত দত্তের মেয়ে শর্বরী দত্তের অবদান ।
বাইশ
প্রথম উপন্যাস ‘ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস’ লেখার সময়ে নমিতা চক্রবর্তীকে যেমন দেখেছি তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলুম মানসী বর্মণ নামের চরিত্রে । ওই উপন্যাসেই বারীন গুপ্তের মহেন্দ্রু মোহোল্লার বাড়ি আর পাড়া ব্যবহার করেছি অতনু চক্রবর্তীর বেলায় । রাঘব আর রমা চরিত্র হল আমার সহকর্মী সুশান্ত চক্রবর্তী আর টেলিফোন অপারেটার রত্না আতর্থী । অরিন্দম চরিত্রটা সহকর্মী অরুণ মুখোপাধ্যায়ের আদলে, যে পরে দাদার শালিকে বিয়ে করে, ও সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিল বিবাহিতা মহিলার প্রেমে পড়ে, যে ওকে নিজের সঙ্গে শুতে দিলেও যৌনকর্ম করতে দিচ্ছিল না । মৌলিনাথ চরিত্রটা হল সহকর্মী মণিমোহন মুখোপাধ্যায়, যার মেয়ের সঙ্গে দাদার ছেলের বিয়ে হয় । আর আছে বিহারের জাতপাতের লড়াই, মাওবাদি-লেনিনবাদিদের লড়াই ।
‘ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস’ উপন্যাসে মিজোরামের উল্লেখ না থাকলেও, পার্থসারথী চৌধুরী, আইএএস, ধরে ফেলেছিলেন যে জুডি-জুলির সঙ্গে অতনুর যৌনজীবনের ঘটনা মিজোরামে ঘটেছে । আমাকে আরও জেরা করেছিলেন জানার জন্য যে ওগুলো আমার জীবনের ঘটনা কিনা । পার্থসারথী চৌধুরীর কসবার বাড়ি গিয়েছিলুম একবার, উনি ম্যাজিশিয়ান পি সি সরকারের জামাই । পাত্র বইপত্র পড়তে ভালোবাসে শুনে পি সি সরকার একঘর বইসুদ্দু একটা বাড়ি দিয়ে দিয়েছিলেন পার্থসারথীকে । সারাদিন বইয়ে মলাট দেয়া, নম্বর দিয়ে তালিকা তৈরি করা, আলমারি অনুযায়ী সাজানোয় এমন জড়িয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর লেখার অভ্যাস চলে গিয়েছিল । বলেছিলেন, তোমার লেখা কোনো বই কখনও দরকার হলে বোলো, সব আছে আমার কাছে । এতো তাড়াতাড়ি মারা গেলেন যে যখন রচনাসংগ্রহের জন্যে দরকার তখনই উনি নেই ।
‘ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস’ পড়ে একদিন লাল টিশার্ট আর জিনস পরে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এসে হাজির । নিজে ফিকশান লিখলেও, আমার উপন্যাসের ঘটনাগুলোকে সত্যি মনে করে ‘আজকাল’ দৈনিকের জন্য ফিচার লিখতে চান । বললুম বাঙ্গালোরে যান, পাবেন হয়তো, তখন অবশ্য বেঙ্গালুরু হয়নি । ফিরে এসে বললেন, কিছুই ঘটেনি ওখানের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে । বললুম, আপনিও তো উপন্যাস লেখেন, আমি তো পড়ার পর খুঁজতে যাই না, কোনো পাঠকই যায়না । ক্রুদ্ধ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ‘আজকাল’ দৈনিকে লিখলেন, বিয়েতে উপহার দেবার জন্য ‘ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস’ উপযুক্ত বই ।
স্নাতক পড়ার সময়ে সহপাঠী রাজনারায়ণ দাসের ডাকে গেলুম ওর চিলতে ঘরে, পাটনা মার্কেটের পেছনে, ঘরের আলো নিভিয়ে একটা টেলিস্কোপ দিয়ে বলল, দ্যাখো জানলা দিয়ে । দেখলুম দুজন চিনা যুবতী, ভারতীয় চিনা, পোশাক খুলে, এখন যাকে বলে, লেসবিয়ান প্রেম, তাই করছে । রাজনারায়ণ বলল, দেখলি তো, চিনা মেয়েদের স্লিট হরাইজনটাল হয়, ভারতীয় মেয়েদের মতন ভার্টিকাল নয় । আমি কেবল ওদের গোলাপি মাই আর চুলহীন যোনি দেখে উত্তেজনা সামলাচ্ছিলুম । রাজনারায়ন এম এ পড়া ছেড়ে দিয়ে আইপিএস হয়ে চলে গিয়েছিল, দ্বারভাঙ্গা বিলডিঙের গেটে সরকারি গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমাদের মনে করিয়ে দিত যে ও রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপরতলায় আর আমি তার বাইরে, ফেকলু, উচ্চাকাঙ্খাহীন।
উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত মুসলমান যুবতীর মুখ দেখার লোভে স্নাতক ক্লাসের বন্ধুনি ভূবনমোহিনী রাণাকে পটিয়েছিলুম, ওদের হোস্টেলে উম্মা হাবিবা নামে একজন সুন্দরী ধনী বাড়ির যুবতী আছে শুনে । উচ্চবিত্ত ছাত্রীরা সেময়ে বোরখা পরত । হোস্টেলের গেটের কাছে এসে উম্মা হাবিবা বোরখার নকাব মাথার ওপর তুলতে ওর লিপ্সটিক বোলানো ঠোঁট আর সুর্মামাখা গভীর চোখ দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলুম, বেশ ফর্সা, অত্যন্ত ফর্সা, বলেছিল, “দেখ লিয়া ?” আমি বলেছিলুম “জি”। আর মনে হয়েছিল, আহা, এই মেয়েটা যদি কুলসুম আপা হতো একে নির্ঘাৎ প্রেম নিবেদন করতুম, লিঙ্গের চামড়া ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই হয়ে গেলেও ছাড়তুম না একে, মার খেলেও, দাঙ্গা হলেও, ছাড়তুম না ।
১৯৬৪ সালে লালবাজারে পুলিশ কমিশনার বলেছিলেন, “আপনারা সাহিত্য করছেন নাকি হ্যাণ্ডবিলে দাঁতের মাজন বিক্রি করছেন ।” একফালি কাগজে কবিতা ছাপিয়ে যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিলি করা যায়, দাঁতের মাজনের প্রচারের মতনই, তা ওনার ধারণায় ছিল না । সেসময়ে কোনো সাহিত্যিকেরই ছিল না, ব্যাপারটা ওনাদের মতে “শিল্পের দেবীকে পথের মাঝে নামিয়ে আনা”। কেবল ভাষাকে আক্রমণ করিনি, তার প্রণালীকেও আক্রমণ করেছি ।
২০০০ সালে ইমলিতলা পাড়ায় দাদার ছোটোবেলাকার বন্ধু বদ্রি পাটিকমার হয়ে গেল বাহুবলি, কেমন করে লোক যোগাড় করে লন্দিফন্দি করে রাজনৈতিক দলে সেঁদিয়ে ও পকেটমার থেকে নেতা হয়ে গেল সে এক রহস্য ; নেতারা নিজে কিছু করে না, ওকে দেখে টের পেয়েছি, সবকিছুর জন্য লোক আছে, পেঁদাবার, লোপাট করার, খুন করার, এমনকি ছুঁচিয়ে দেবার। আহা, বদ্রি পাটিকমারের সঙ্গে যদি জীবন অদল-বদল করে নেয়া যেতো । “হয়ে ওঠা” স্পষ্ট হতো ।
বুজলুদাকে জিগ্যেস করেছিলুম, কে পড়বে আমার বই ?
—কেন ? রবীন্দ্রনাথ যেমন খামে ভরে-ভরে একে-তাকে বই পাঠাতেন, তুইও পাঠাবি ।
জনে-জনে পাঠাবার এই আইডিয়াটা বেশ ভালো লেগেছিল । হাংরি আন্দোলনের সময়ে কাজে লাগিয়েছিলুম , লিফলেট কার্ড আর প্যামফ্লেট ছাপিয়ে বিলি ।
বইয়ের জন্য, লেখালিখির জন্যে টাকা তো দরকার । শিলঙে একটা কলেজে দরখাস্ত করে অধ্যাপনার চাকরি পেলুম, ইকোনমিক্স পড়াবার জন্য । তখন “বঙাল খেদা” চলছিল, বাবা বললেন, ‘পাটনাতেও খুঁজে দ্যাখ না কোনো চাকরি পাওয়া যায় কিনা, এখানে তো তোর দাদাও নেই, তুইও চলে যাবি, আমাদের জ্বরজারি অসুখ-বিসুখ হলে কে দেখবে ?’ স্কুলের সহপাঠী নেপালের দাদা সমরেন্দ্র চক্রবর্তী, রামমোহন রায় সেমিনারিতে আমার চেয়ে দু’ক্লাস উঁচুতে, একদিন এসে বলল, ‘তুমি এই কাগজটায় সই করে দাও দিকিনি, চাকরির দরখাস্ত লিখেই এনেছি, আমার অফিসে লোক নেয়া হচ্ছে, নতুন অফিস খুলবে, বেশি লোকেরা জানে না, কাউকে বোলো না যেন ।’ আমার অফিস মানে রিজার্ভ ব্যাংক, উনিও নোট পোড়াবার দপতরে তখন, দুপুর বেলাতেই ছুটি হয়ে যায়, তারপর টিউশানি করে বেড়ান, সংসার ওনাকেই চালাতে হয়, বাবা ওনার ছোটোবেলায় আত্মহত্যা করেছিলেন, কোনো বিদেশি কোম্পানির ওষুধ জাল করে বিক্রির জন্য ধরা পড়েছিলেন ।
খড়ি-স্লেটের কৃষ্ণগহ্বরের আহ্লাদ শুষে নিচ্ছিল আমাকে, বইয়ের হাঙরেরা আমার ছাড়ানো দেহ থেকে মাংসের টুকরো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে আনন্দে ভোগাচ্ছিল আমায়, অক্ষরের জোঁকেরা চামড়ায় বসে রক্ত চুষে আমার হরমোন বাড়িয়ে তুলছিল । চোখ, কান আর জিভ দিয়ে লেখা আরম্ভ করলুম । আর পড়া, বই বই বই বই বই বই, বাছবিচার নেই, এ-বই, সে-বই, অমুক বই, তমুক বই, জ্ঞান জ্ঞান জ্ঞান জ্ঞান । আরেক লাইন, আরেক বাক্য, আরেক প্যারা, বেঁচে থাকার আনন্দ আর দুঃখ, সারাজীবন বেঁচে থাকার ইচ্ছে। আমি শব্দপূঞ্জ আর অ্যাকশানের মাঝে ঝুলছিলুম, শান্তিময় আরামপ্রদ জীবন অসম্ভাব্যতার পথে ছুটতে লেগেছিল, জীবনের এক চতুর্থাংশ কাটিয়ে সব কিছুই জানা হয়ে গিয়েছিল, কৌতুহলে লুকোনো নোংরামি অনৈতিকতা অবৈধতা থেকে আরম্ভ করে অনিশ্চয়তার ভীতি পর্যন্ত, ফুরিয়ে গিয়েছিল অজ্ঞানতার পর্ব ।
বাবাকে তো প্রতিদিন দেখছিলুম, নিজেকে শিল্পী বলে মনে করছেন না, মনে করছেন, তাঁর কাজ হল মৃতদের প্রাণ দেয়া যা পেয়ে তাদের বংশধরদের আহ্লাদ হয়, কিন্তু এও দেখছিলুম যে শিল্পীদের মতন মানসিক-শারীরিক অসুস্হতায় আক্রান্ত হয়ে ওনার স্বাস্হ্য ভেঙে পড়ছে ক্রমশ । উনিও যেন প্রতিটি ছবিতে বিষের চোলাইকারীর ভূমিকা নিচ্ছেন, যা আমি তখন করছিলুম আমার ডায়েরিতে আর নোটখাতার পাণ্ডুলিপিতে । এখন যখন জীবনের বাঁকবদলগুলোর কথা ভাবি, মনে হয় যেন তা কয়েক বছর অন্তরই ঘটেছে ।
সিনেমা দেখার অভ্যাস ছেড়ে যেতে লাগল, কেননা সিনেমা তো দেখতুম যৌন আবেদনের জন্যে, শ্বেতাঙ্গিনীর উরু আর ক্লিভেজের আকর্ষণে, সত্যজিৎ রায় ঋত্বিক ঘটক মৃণাল সেন আকিরো কুরোসাওয়া ফগেদেরিকো ফেলেনি রোমান পোলানস্কি ইঙ্গমার বার্গম্যান জাঁ লুক গোদার লুই বুনুয়েল ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো ফেদেরিকো ফেলিনির জন্য নয় । সাবটাইটেল দেয়া ফিল্ম আমি দেখতে পারি না ; পড়া আর ফ্রেম দেখা আর শোনা এক সঙ্গে তিনটে ব্যাপার সম্ভব হয়নি কখনও ।
অড্রে হেপবার্ন, ব্রিজিত বার্দো আনা কারিনা মারিনা ভ্লাদি বেরুয়াদেতে লাফোঁ ক্লদ জেড জিন মোরেয়া ভেরগানো মারিয়ন কিকা মারখাম শার্লি আমাগুচি মিসা উয়েহারা অ্যানিটা একবার্গ জিউলিয়েতা মাসিনা সান্দ্রা মিলো ক্লদিও কার্দিনাল অনুক আইমি ক্যারোল বোক অ্যানজেলা মোলিনা ক্যাথারিন দেনেউভ সোফিয়া লোরেন এলিজাবেথ টেলর আরও কতো আরও কতো আরও কতো আরও কতো , তাদের ঠোঁট নড়া দেখলে আমি পায়ের ওপর পা রেখে লিঙ্গকে সামাল দিই ।
কাজলচোখ গাঢ় ভুরু মিষ্টি হাসি কাঁপানো ঠোঁট সুচিত্রা সেন সাবিত্রী দেবী সুপ্রিয়া চৌধুরী সন্ধ্যা রায় মাধবী মুখার্জি আরও কতো আরও কতো আরও কতো । নিজেকে সামাল দিই ।
স্তনের ভাঁজ কাঁচা গোলাপি ঠোঁট দীর্ঘ উরু শিফন শাড়ি মধুবালা মীনাকুমারী নিম্মি নার্গিস শ্যামা মীনা শোরে রেহানা কুলদীপ নায়ার গীতাবালি নূতন সুরাইয়া আশা পারেখ সাধনা মুমতাজ ওয়াহিদা রহমান হেলেন নলিনী জয়ন্ত বীনা রায় বৈজয়ন্তিমালা মালা রায় আরও কতো আরও কতো । নিজেকে সামাল দিই ।
ফিল্ম পরিচালকদের ভাবনাচিন্তার সঙ্গে আমার লেখালিখির কোনো যোগসাজস কখনও গড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি, নিজের মগজে যা আসে তাই কলমে চলে আসে । কলম চাইলে মগজ তাকে ইরটিক হয়ে ওঠার বন্দোবস্ত করে দ্যায় । আমার তো বিশ্বাস নেই, যা আছে তা প্রত্যয় । সমসাময়িকদের বিরুদ্ধে আমি একাই দাঁড়িয়ে থেকেছি, কোনো ফিল্ম নয়, বই নয়, নির্দেশ নয়, তত্ত্ব নয় । জানতুম ইর্ষনীয়-গন্তব্যে শত্রুসংখ্যা বাড়বে, এও জানতুম যে লড়ে যেতে হবে । নমিতা চক্রবর্তী উত্তর দিতে পারেননি যখন ওনার দেয়া তোড়া-তোড়া পত্রিকা হাতে নিয়ে জানতে চেয়েছিলুম যে সোভিয়েত দেশের এতো চকচকে প্রচারের কাগজপত্র কেন, প্রপাগাণ্ডা কেন, গোপনীয়তা কেন ? তা সত্ত্বেও যেতুম ওনার ফ্ল্যাটে, প্রেম আমার জীবনের প্রধান সমস্যা বলে, ভালোবাসা পাবার ধান্দায় লালায়িত বলে । কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর আকর্ষণ স্তালিনের ছাড়া গোখরোদের কামড়ে ততদিনে হাপিশ ।
তেইশ
আমার যাবতীয় কাজকারবারের, যাকে কলকাতার লোকে সেসময়ে বলত বোহেমিয়ান জীবন, তার উৎস হল ইমলিতলা ; বাঙালির দৃষ্টিতে সকলেই সেখানে বোহেমিয়ান । ক্রোধ আর অসহায়তার আগ্নেয়গিরির উৎসও ইমলিতলা । ওই পাড়ার গড়ে দেয়া সামুরাইরা আমার মগজে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছিল, উপলব্ধিদের ফাটিয়ে চৌচির করে বেরিয়ে পড়তে চাইছিল জীবন, বুঝে গিয়েছিলুম যে লেখালিখি ওপিনিয়নেটেড হওয়া জরুরি । বলতে হলে বলতে হয়, পৃথিবীর জন্মই তো হয়েছে বিশ্বজাগতিক সন্ত্রাস থেকে। আর আমার লেখালিখি তো আপামর জনসাধারণকে খুশি করার জন্য নয় । মৌমাছির কথা ভাবলে কেবল তার গুনগুন আর মধুর কথা ভাবলেই তো হবে না, তার হুলের কথাও মনে রাখতে হবে । আপনি যদি মনে করেন যে আপনার বিশ্বাসই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহলে রক্তের বহু নদী বইতে থাকবে, আর তাতে ভেসে যাবে আপনার ঘৃণার শবের পর শবের পর শব ।
ইমলিতলা থেকে দরিয়াপুরে যাবার পর, দাদার বিয়ে হয়েছে, নতুন বউ এসে তো খাটা পায়খানায় হাগবে না, তাই ফ্লাশ-পায়খানা তৈরি হল, একতলা-দুতলায়, দাদা একতলার দরোজায় ভেতরের দিকে আয়না লাগিয়েছিল, যাতে হাগতে-হাগতে নিজেকে দেখা যায়, হাতেমাটির জন্যে গঙ্গামাটির বদলে লাক্স টয়লেট সাবান । বিহারি বন্ধুদের তো বটেই বাঙালি সহপাঠীদেরও অনেকের বাড়িতে খাটা পায়খানা ছিল বলে আমাদের পায়খানা দেখতে আসতো, একটু হেগে নেবার অনুমতি চাইতো । ইমলিতলার বাড়িতে হেগো হয়ে যাবার যে বিধিনিষেধ ছিল তা তামাদি হয়ে গেল, পোশাক পরেই হাগো, নো প্রবলেম, হেগো বলে গঙ্গাজল ছেটাবার আর দরকার নেই । একের পর এক সীমার পাঁচিল ভেঙে পড়ছিল, আপনা থেকেই, আর সেই ভাঙনের স্রোতে বাড়ির সবাই শামিল ছিলুম, মা, বাবা, দাদা, আমি, সবাই । মুর্গির ডিম, মুর্গির মাংস, বিনা-আঁশের মাছ, তাড়ি খেয়ে মদ খেয়ে গাঁজা টেনে বাড়ি ফেরা, যা-যা বারণ ছিল তা লোপাট হয়ে গেল। তরুণ শূরের টাকায় মহঙ্গুর দোকানে বসে চেবাতুম বটের, বগেড়ি, কোয়েল, চাহা পাখির দেহ, পায়রার ঠ্যাং। পায়রা খেয়ে তরুণ বলত এই মাংস বড্ডো গরম, আজকে শালা কয়েক বার হাত মারতে হবে গরম বের করার জন্যে ।
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল । বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোনো অধ্যাপককে পেলুম না যিনি আমায় লেখালিখি করতে আগ্রহী করবেন । রামমোহন রায় সেমিনারীর চেয়েও গোলমেলে অবস্হা। যাঁরা বিভিন্ন কলেজে সেসময়ে বাংলা পড়াতেন, তাঁরা কেউই বাংলা ভাষাসাহিত্যে স্নাতকোত্তর ছিলেন না । সায়েন্স কলেজে রমাপতি ঘোষ ছিলেন রসায়নের শিক্ষক, বি এন কলেজে রঙিন হালদার ছিলেন মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক, পাটনা কলেজে ত্রিদিব চৌধুরী ছিলেন ইতিহাসের শিক্ষক । বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের বাংলাভাষা আর সাহিত্য পড়াবার দায়িত্ব এই জন্যে দিয়েছিল যে প্রথমত তাঁরা বাঙালি, এবং দ্বিতীয়ত তাঁরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিজের বিষয়টিতে স্নাতকোত্তর । যে বছর আমি বি এন কলেজে ভর্তি হলুম সে-বছর রামমোহন রায় সেমিনারি থেকে বিজয় কর্মকার বাংলার অধ্যাপক হয়ে এলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দেয়াতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন, ব্রাহ্ম যুবক-যুবতীদের বিয়ে দেয়া, মাঘোৎসব-পৌষোৎসব তদারকি করা ইত্যাদি । কলেজে দ্বিতীয় বছরে বাংলার অধ্যাপক হয়ে এলেন জীতেন্দ্রনাথ ঘোষ, পণ্ডিচেরিপ্রেমি, যিনি ছাত্রদের জান্তব আস্ফালন দেখে প্রথম থেকেই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, তিনি কতো তাড়াতাড়ি আমাদের চাষাড়ে কলেজ ছেড়ে ভদ্রছেলেদের কলেজে চলে যাবেন তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন । রবীন্দ্রনাথের পর যে তোলপাড় ঘটে গেছে বাংলা কবিতা ও গল্প-উপন্যাসে তার সঙ্গে জীতেন্দ্রনাথ ঘোষ নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি। সিলেবাস বানাতেন রমাপতি ঘোষ, রঙীন হালদার, ত্রিদিব চৌধুরী প্রমুখ, যাঁরা তিরিশের কবিদের পছন্দ করতেন না । পুলিশ যখন হাংরি আন্দোলনের কারণে আমাকে গ্রেপ্তার করে তখন জীতেন্দ্রনাথ ঘোষ জনে-জনে বলে বেড়াতেন, “মলয় যে অধঃপতনে যাবে তা জানতাম।”
বারীন চাকরি পেয়ে গেছে মার্টিন অ্যাণ্ড হ্যারিস নামে জিৎপল-সৎপলদের কোম্পানিতে, তরুণ শূর পেয়ে গেছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকে স্নাতক হবার পরেই । অধ্যাপক ত্রিপাঠি, যিনি আমার স্পেশাল পেপারের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন, বললেন পিএইচ ডি করতে, বসে থাকার চেয়ে ভালো, একটা সিনপসিস উনিই তৈরি করে দিয়েছিলেন ; ছেড়ে দিলুম । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চাকরিটা পেয়ে গেলুম, বেশ সহজেই । কিন্তু চাকরিতে ঢুকেই বুঝলুম প্রচণ্ড চাপের কাজ, যেখানে টাকার পাহাড় গোনা হয়, যেখানে অজস্র খুচরো পয়সা বেলচা দিয়ে থলের ভেতরে ঢুকিয়ে ওজন হয় । তবে চাকরি পেয়ে সুবিধা এই হল যা দাদার পোস্টিঙের শহরে যখন ইচ্ছে চলে যাওয়া যায়, বাবার কাছে টাকা চাইতে হয় না ।
চাইবাসায় দাদার চালাবাড়িটা ছিল একটা পাহাড়টিলার ওপরে, দেখা যেতো দূরের উপজাতি গ্রামগুলো, চালাবাড়ির সামনে নিচের পথ দিয়ে সার বেঁধে কাঁখে মাটির হাঁড়িতে জল ভরে নিয়ে যাচ্ছে উপজাতি যুবতীরা, রাতের বেলায় উড়ন্ত জোনাকিতে ভুতুড়ে পরিবেশ, শুকনো পাতার গন্ধ, রোরো নদীর জলপ্রবাহের শব্দ, মহুয়া ফুলের ফিকে সুবাস, টিলার ওপর রাখা কেরোসিনের লম্ফও অন্ধকারে হয়ে উঠতো চাঁদের সোডিয়াম ভেপার আলো, দূরে শালের জঙ্গল । একা বসে চিন্তা করার অফুরন্ত অবসর । এখানে আমি আমার পাণ্ডুলিপির গভীর কন্ঠস্বর শুনতে পেতুম । বসে-বসে মনে হতো, গুহানিবাসীরা তো জানতোই না কাকে বলে পঙ্কিলতা আর কাকে বলে বিশুদ্ধতা । ইমলিতলায় দেখেছি গরিব মানুষ ধনীর আনন্দকে ভয় পায়, যেন কোনো বৈভবশালীর বাড়িতে আচমকা ঢুকে পড়েছে ; তাদের কাছে আনন্দ বলতে ছিল সমাজ-বহির্ভূত হওয়ার আহ্লাদ । আসলে যারা বিপথগমণের কথা বলে তারা সঠিক পথের হদিশ দিতে পারে না । নিমডির টিলায় রাতের অন্ধকারে বসে আমি উপভোগ করতুম পেরুর মাচু পিচু, রোমের কলোসিয়াম, আথেন্সের পারথেনন, নালান্দার ধ্বংসাবশেষের আ্হ্লাদ ।
দাদার সঙ্গে, দাদার বিয়ের কয়েক বছর আগে থেকেই, ভারতবর্ষ আর পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতুম, নেহেরুর সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে, পশ্চিমবাংলার ডামাডোল নিয়ে। তখন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৃষিসেচ পথঘাট নির্মাণ ছোটো আর মাঝারি ইনডাস্ট্রি থেকে সরে গিয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হয়েছে অনেকটা বোম্বাই মডেলের দিকে, বড়ো ইনডাস্ট্রির দিকে, সমাজসেবার খাতে কমিয়ে দেয়া হয়েছে খরচ এদিকে কৃষি এলাকায় ব্যর্থতা আর খরার জন্য খাবার জিনিসের দাম চলে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে বড়ো ইনডাস্ট্রিগুলো ওপড়াতে আরম্ভ করেছে উপজাতিদের । উত্তরঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের ভয়াবহ ছবি গড়ে উঠছিল আমাদের সামনে । কলকাতা থেকে দাদার যে বন্ধুবান্ধব চাইবাসায় দাদার বাড়িতে ছুটি কাটাতে আসতো তারা সকলেই ছিল ‘আর্ট ফর আর্টস সেক’ মানসিকতার যুবক যা পরে জেনেছি বুদ্ধদেব বসুর কবিতাভবনের ফসল, স্হিতাবস্হাপন্হী । তাঁদের অনেকের সঙ্গেই মতের মিল হতো না আমার ।
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, দীপক মজুমদার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী প্রমুখের সঙ্গে দাদার মাধ্যমে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল আমার । শংকর চট্টোপাধ্যায় কালো ট্রাউজার আর কালো শার্টে মনে হতো জেমস বণ্ড টাইপের মানুষ । উৎপলকুমার বসুকে মনে হতো কর্পোরেট বোর্ডের সদস্য টাইপের । অরণ্যের দিনরাত্রী ফিল্মে রবি ঘোষ তারাপদ রায়ের ভূমিকায়, আমারও তাই মনে হয়েছে, রবি ঘোষের চরিত্র টাইপের । হাংরি আন্দোলনে গ্রেপ্তার হবার আগে একমাত্র শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় একটা পোস্টকার্ড লিখে আভাস দিয়েছিলেন যে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়েছে ।
শক্তি চট্টোপাধ্যায় তর্কে অংশ নিতেন না নিজের ‘কুয়োতলা’ উপন্যাস নিয়ে ব্যস্ত । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমার ডায়েরির কবিতাগুলো সম্পর্কে পজিটিভ রেসপন্স দিলেন বলে দাদা কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে ওনাকে কৃত্তিবাস পত্রিকার জন্য কবিতা দিলেন, সেগুলো ১৯৫৯ সালে ছাপা হয়েছিল । আমি প্রচলিত কবিতার মতো লিখতে চাইছিলুম না, গতি আনতে চাইছিলুম, পরে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে পাণ্ডুলিপি তৈরি করে পাঠিয়েছিলুম, বইয়ের নাম রেখেছিলুম “শয়তানের মুখ’ ওনার পছন্দ হয়নি, আসলে কনভেন্ট স্কুলের স্যাটান থেকে গিয়েছিল আমার মগজে, আসেপাশে লোকেদের দেখে আমার মনে হতো তারা শয়তানের মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ায়। আমি ঔপনিবেশিক নন্দন-বাস্তবতা থেকে, মানে কলোনিয়াল ইসথেটিক রেজিম থেকে, বেরোতে চাইছিলুম ।
“মার্কসবাদের উত্তরাধিকার” নামে যে পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছিলুম, সেটা শক্তি চট্টোপাধ্যায় পাটনায় এলে ওনাকে দিয়েছিলুম আর টাকাও দিয়েছিলুম বইটা ছাপাবার জন্য । বইটার প্রূফ না দেখে উনি মাত্র কয়েক কপি বের করেছিলেন, দেখে আমার মেজাজ গরম হয়ে গিয়েছিল, আর ওনার উল্টোডাঙার বস্তিবাড়ির সামনে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলুম । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দাদাকে বলেছিলেন, তুই আমাকে দিলেই পারতিস, শক্তির চরিত্র তো তুই ভালো করেই জানিস । “শয়তানের মুখ” কৃত্তিবাস প্রকাশনী থেকে বের করার জন্য রেখে নিলেন উনি, বললেন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে দেবেন । “শয়তানের মুখ” বেরোবার পর উনি আমার বিরুদ্ধতা আরম্ভ করলেন, কেননা তখন হাংরি আন্দোলনের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র ।
দাদা আর আমি বুঝতে পারছিলুম যে কলকাতায় আমাদের পরিচিতি নেই বলে দাদার এই বন্ধুদের ওপর নির্ভর করে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী খোলাখুলি প্রকাশ করা কঠিন, তাই নিজস্ব মুখপত্র দরকার । এরা সবাই আখের নিয়ে চিন্তিত, খ্যাতির জন্য লালায়িত, পরস্পরের বিরোধিতা করতে চায় না, বিতর্ক এড়িয়ে ভাই-ভাই ক্লাব গড়ে তোলে । একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, আরেকজন করে না, তবু তর্ক করে না ।
উত্তরঔপনিবেশিক ভারতে সময়ের তুলনায় স্হানিকতা যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, ঔপনিবেশিক ইংল্যাণ্ডের পোঁ-ধরে থাকলে চলবে না, ভারতের সমাজের দিকে তাকিয়ে গড়তে হবে একটা গতিময় আন্দোলন, তা আমরা দু-জনে টের পাচ্ছিলুম, কিন্তু কলকাতায় আমাদের ঘাঁটি দরকার । দাদা শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে রাজি করাতে পারলেন, সম্ভবত তখন শক্তি চট্টোপাধ্যায় দাদার যে কোনো প্রস্তাবেই রাজি হয়ে যেতেন কেননা উনি দাদার শালি শীলার সঙ্গে গভীর প্রেমে পড়েছিলেন আর দাদার চাইবাসার বাড়িতেই থাকতেন, দাদা ট্যুরে গেলে দাদার শশুরবাড়িতে গিয়ে থাকতেন । একবার সুনীল-সন্দীপন চাইবাসায় শক্তির খোঁজে এসে দাদার শশুরবাড়িতে উনি ঘাঁটি গেড়েছেন দেখে বলে ওঠেন, “কিরে শালা, এখানে ইস্টিশান পুঁতে ফেলেছিস?”
১৯৬০ সালে একটি লিটল ম্যাগাজিনে আমি হারাধন ধাড়া নামে একজন তরুণ লেখকের নাম-ঠিকানা পেলুম আর মনে হল এই নামটির একটি নিজস্ব প্রতিভা আছে, এই ধরণের নামের কবি বা লেখক এখনও স্বীকৃতি পান না । ১৯৬১ সালে তাঁর হাওড়ার বাড়িতে, যা বস্তিবাড়ি ছিল, গিয়ে ডেকে আনলুম পাটনায় । দাদাও শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে ডেকে আনল পাটনায় । আমাদের চারজনের মধ্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় তুলনামূলকভাবে কলকাতায় বেশি পরিচিত । আমি আর দেবী রায় তো একেবারেই অখ্যাত ছিলুম ।
“ইতিহাসের দর্শন” আর “মার্কসবাদের উত্তরাধিকার” লেখার সময়ে আমি অসওয়াল্ড স্পেংলারের দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলুম । ততো দিনে স্তালিনের অত্যাচারের ঘটনাগুলো আশঙ্কা তৈরি করে ফেলেছে। চিনের সিংকিয়াং আর তিব্বত দখলও মার্কসবাদ সম্পর্কে সন্দেহের কারণ হয়ে উঠেছে । হাংরি আন্দোলন চলাকালীনই চীন ভারত আক্রমণ করে বসল, তাও বিভ্রান্ত করার জন্য ছিল যথেষ্ট । কলকাতায় তখন চীনকে সমর্থন করে মার্কসবাদীদের লেখালিখির চল, এখন তারা অনেকেই করে-কম্মে নিয়েছে, মার্কসবাদ গেছে চুলোয়, সকলেই বুঝে গেছে যে “প্রগতি” হল সবার চেয়ে ভূয়ো তত্ত্ব । প্রথমে দলের দুটো টুকরো হল, তারপর অজস্র ভাগাভাগিতে জড়িয়ে পড়ল, বোঝা গেল না যে একই স্বপ্নের এতোগুলো ন্যারেটিভ কেন । “ইতিহাসের দর্শন” লেখাটার ফাইল-কপি কলকাতা পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করতে এসে “রাষ্ট্রবিরোধী” রচনা মনে করে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গিয়েছিল, কেননা আমার বিরুদ্ধে ১২০ ( বি ) ধারাতেও এফআইআর ছিল । এই ধারাটা যোগ করা হয়েছিল কোমরে দড়ি আর হাতে হাতকড়ার সুবিধার জন্য ।
আমার বাবা নেহেরু আর গান্ধীকে পছন্দ করতেন না । তার রেশ শৈশব থেকে চুয়ে আমার মধ্যেও ঢুকে গিয়েছিল । খ্যাতিমানদের সন্দেহ করার বীজ বাবা পুঁতে দিতে সফল হয়েছিলেন আমার আর দাদার মনে । এমনকি যারা সোভিয়েত দেশে সোভিয়েত টাকায় গিয়েছিল, সে তারা যতোই নামকরা কবি-লেখক-নেতা হোক, সন্দেহ থেকে তাদের বাদ দিতে পারিনি । তারা যে “আশাবাদ”-এর বুকনি কপচাতো তাকে মনে হতো বই-পড়া মুখস্হ বুলি ।
দাদার সঙ্গে আলোচনা করেছিলুম স্পেংলারের দর্শন নিয়ে আর আন্দোলনের নামকরণ নিয়ে চিন্তা করছিলুম । স্নাতকস্তরে ইংরেজি কোর্সে জিওফ্রে চসার ছিলেন, তাঁর একটা লাইন বেশ স্ট্রাইক করেছিল, “ইন দি সাওয়ার হাংরি টাইম” । হারাধন ধাড়া আর শক্তি চট্টোপাধ্যায় রাজি হলেন যে আমাদের আন্দোলনের নাম রাখা হোক “হাংরি জেনারেশন “ বা “হাংরি আন্দোলন” । ঠিক হল আমি আর দাদা খরচ দেবো, হারাধন ধাড়ার বাড়ির ঠিকানা দেয়া থাকবে যাতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন । ঠিক হল এক পাতার বুলেটিন প্রকাশ করা হবে । বিলি করবে হারাধন ধাড়া, বিক্রি করা হবে না । শক্তি চট্টোপাধ্যায় বললেন, সুনীলকে আপাতত জানাবার দরকার নেই, উনি আঁচ করে নিয়েছিলেন যে আমার মতামতের সঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরোধ অনিবার্য, তা এড়াতে চাইছিলেন । বর্ষাকালে নদীরা যুবক হয়ে ওঠে, আর কোনো-কোনো লোক বৃষ্টি-বাদলার ভয়ে বুড়িয়ে যায় । কেবল মধ্যবিত্তরাই কেন কবিতা লেখে !
চব্বিশ
স্পেংলার বলেছিলেন যে একটি সংস্কৃতির ইতিহাস কেবল একটি সরলরেখা বরাবর যায় না, তা একযোগে বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়; তা হল জৈব-প্রক্রিয়া এবং সেকারণে সমাজটির নানা অংশের কার কোন দিকে বাঁকবদল ঘটবে তা আগাম বলা যায় না । যখন কেবল নিজের সৃজনক্ষমতার ওপর নির্ভর করে সংস্কৃতিটি নিজেকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করতে থাকে, তার নিত্যনতুন স্ফূরণ ও প্রসারণ ঘটতে থাকে । কিন্তু ঠিক সেই সময় থেকে একটি সংস্কৃতির অবসান আরম্ভ হয় যখন তার নিজের সৃজনক্ষমতা ফুরিয়ে গিয়ে তা বাইরে থেকে যা পায় তাই আত্মসাৎ করতে থাকে, খেতে থাকে, তার ক্ষুধা তৃপ্তিহীন । আমার মনে হয়েছিল, দেশভাগের পর এবং ফলে পশ্চিমবঙ্গ এই ভয়ংকর অবসানের মুখে পড়েছে, এবং উনিশ শতকের মনীষীদের পর্যায়ের বাঙালির আবির্ভাব আর সম্ভব নয় । বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতিতে একটা হ্যাঁচকা-টানের আন্দোলন জরুরি ।
“ইতিহাসের দর্শন” লেখার সময়ে এডওয়ার্ড গিবনের ‘দি হিসট্রি অফ দি ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল অফ দি রোমান এমপায়ার’ বইয়ের এই কথাগুলো বেশ স্ট্রাইক করেছিল, যদিও তিনি রোম সাম্রাজ্যের পতনের কারণ দর্শিয়েছিলেন, কিন্তু কথাগুলো আমাদের সমাজের ক্ষেত্রেও লাগসই । সেগুলো হল, এক ) সম্পদ বৃদ্ধির বদলে বৈভব প্রদর্শনের আদিখ্যেতা ; দুই ) যৌনতার বিকৃতি আর অবসেশন ; তিন ) আর্ট ব্যাপারটা আকস্মিক হয়ে ওঠে, মন ভোলাবার চেষ্টা, সৃজনশীলতার দিকে দৃষ্টি দেয় না কেউ ; চার ) ধনী আর গরীবের মধ্যে অসেতুসম্ভব পার্থক্য ; এবং পাঁচ ) রাষ্ট্রকে চুষে জোঁকের মতন লিপ্টে থাকার নেশা ।
স্পেংলারের এই ভাবনা নিয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৯৬২ সালে, বিনয় মজুমদারের বই “সম্প্রতি” পত্রিকায় রিভিউ করার সময়ে “ক্ষুৎকাতর আক্রমণ” নামে একটা প্রসঙ্গ তুলেছিলেন, কিন্তু তার আগেই দাদা সমীর রায়চৌধুরী ওই একই শিরোনামে অতুল্য ঘোষের পত্রিকা “জনসেবক”-এ একটা নিবন্ধ লিখেছিলেন, “জনসেবক” সংবাদপত্রের রবিবারে পাতার সম্পাদক ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ; দাদার এই নিবন্ধটা পরে হাংরি বুলেটিনে প্রকাশিত হয়েছিল । শৈলেশ্বর ঘোষ, মুচলেকা দিয়ে রাজসাক্ষী হবার পর নানা জায়গায় লিখে বেড়িয়েছিল যে আমি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আইডিয়া চুরি করে হাংরি আন্দোলনের তত্ত্ব গড়েছি । পরে বকাসুর চেহারার সব্যসাচী সেন নামে এক পাতিবুর্জোয়া ছোকরা , শৈলেশ্বরের শিষ্য, নানা পত্রিকায় এই ধুয়ো গে্য়ে চলেছে । শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পড়াশুনা নিয়ে এনাদের জ্ঞান সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই, কেননা স্পেংলার সম্পর্কে এনাদের এলেম যে ইশকুল মাস্টারের পার্টিকর্মী হয়ে ওঠার চৌহদ্দিতে আটক তা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ওলোটপালোট থেকে টের পাওয়া যায় ।
এখানে বলার যে ইউরোপের সাহিত্য আর ছবি আঁকার আন্দোলনগুলো সংঘটিত হয়েছিল একরৈখিক বনেদের ওপর, অর্থাৎ আন্দোলনগুলো ছিল টাইম-স্পেসিফিক বা সময়কেন্দ্রিক । কল্লোল গোষ্ঠী এবং কৃত্তিবাস গোষ্ঠী তাঁদের ডিসকোর্সে যে নবায়ন এনেছিলেন সে কাজগুলোও ছিল কলোনিয়াল ইসথেটিক রিয়্যালিটি বা ঔপনিবেশিক নন্দন-বাস্তবতার চৌহদ্দির ভেতরে, কেননা সেগুলো ছিল যুক্তিগ্রন্হনা-নির্ভর, এবং তাদের মনোবীজে অনুমিত ছিল যে ব্যক্তিপ্রতিস্বের চেতনা ব্যাপারটি একক, নিটোল ও সমন্বিত । সমায়ানুক্রমী ভাবকল্পের প্রধান গলদ হল যে, তার সন্দর্ভগুলো পুর্বপুরুষদের তুলনায় নিজেদের উন্নত মনে করে, এবং স্হানিকতা ও অনুস্তরীয় আস্ফালনকে অবহেলা করে । যে কারণে হারাধন ধাড়ারা গ্রাহ্য হন না, তাঁদের এফিডেভিট করে দেবী রায় হতে হয় ।
পাটনায় বাংলা প্রেসগুলো কেবল বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পৈতে আর শ্রাদ্ধর কার্ড ছাড়া আর কিছু ছাপত না, আমার লেখা প্রথম বাংলা ম্যানিফেস্টো পাটনায় ছাপানো যাচ্ছে না দেখে আমি ইংরেজিতে একটা কবিতার ম্যানিফেস্টো লিখে ছাপালুম ১৯৬১ সালের নভেম্বরে আর তাড়া বেঁধে পাঠিয়ে দিলুম হারাধন ধাড়ার হাওড়ার বস্তিবাড়ির ঠিকানায় । নিজেও কয়েকজনকে ডাকে পাঠালুম । কলকাতায় বিলি করা মাত্রই হইচই আরম্ভ হল, যাকে বলা যায় আশাতীত প্রতিক্রিয়া ।
প্রথম বুলেটিন থেকেই হাংরি আন্দোলন চেষ্টা করল “সময়তাড়িত চিন্তাতন্ত্র” থেকে সম্পূর্ণ আলাদা “পরিসরলব্ধ চিন্তাতন্ত্র” গড়ে তুলতে । সমায়ানুক্রমী ভাবকল্পে যে বীজ লুকিয়ে থাকে, তা যৌথতাকে বিপন্ন আর বিমূর্ত করার মাধ্যমে যে-মননসন্ত্রাস তৈরি করে, তার দরুন প্রজ্ঞাকে যেহেতু কৌমনিরপেক্ষ ব্যক্তিলক্ষণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়া হয়, সমাজের সুফল আত্মসাৎ করার প্রবণতায় ব্যক্তিদের মধ্যে ইতিহাসগত স্হানাঙ্ক নির্ণয়ের হুড়োহুড়ি পড়ে যায় । গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ব্যক্তিক তত্ত্বসৌধ নির্মাণ । ঠিক এই কারণেই, ইউরোপীয় সাহিত্য আর ছবি আঁকার আন্দোলনগুলো খতিয়ে যাচাই করলে দেখা যাবে যে ব্যক্তিপপ্রজ্ঞার আধিপত্যের দামামায় সমাজের কান ফেটে এমন রক্তাক্ত যে সমাজের পাত্তাই নেই কোনো । কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর দিকে তাকালে দেখব যে পুঁজিবলবান প্রাতিষ্ঠানিকতার দাপটে এবং প্রতিযোগী ব্যক্তিবাদের লালনে সমসাময়িক শতভিষা গোষ্ঠী যেন অস্তিত্বহীন ; কতো লজ্জার যে অলোক সরকার সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেলেন এখন ২০১৬ সালে ! প্রাতিষ্ঠানিকতার দাপটে এমনকি কৃত্তিবাস গোষ্ঠীও সীমিত হয়ে গেছে দু-তিনজন মেধাস্বত্ত্বাধিকারীর নামে । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর কৃত্তিবাসের ব্রাণ্ড নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি ওই পুঁজি আর দাপটের ভাগবাঁটোয়ারার ঝগড়া ।
প্রথম বুলেটিন থেকেই তখনকার প্রাতিষ্ঠানিক সন্দর্ভের সঙ্গে হাংরি আন্দোলনের প্রতিসন্দর্ভের সংঘাত আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল এবং তার মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রতিটি বুলেটিন, স্টেনসিল-করা ড্রইং, পোস্টার, কোলাঝ, কার্ড, মুখোশ বিলি করার পর-পরই, যা আমি জানতে পারি বহু পরে, কাউনসিল ফর কালচারাল ফ্রিডাম-এর সচিব এ বি শাহ, পি ই এন ইনডিয়ার অধ্যক্ষ নিসিম এজেকিয়েল, এশিয়া সোসায়টির বনি ক্রাউন, ইলাসট্রেটেড উইকলির সম্পাদক খুশওয়ন্ত সিং, এবং ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা পুপুল জয়াকরের কাছ থেকে । আমার বিরুদ্ধে আবু সয়ীদ আইয়ুব যে ভীষণ খাপ্পা তা এ বি শাহ জানিয়েছিলেন, তাই দেখা করতে গিয়েছিলুম সয়ীদ সায়েবের সঙ্গে ; উনি এমন ভান করলেন যেন কিছুই জানেন না, এদিকে ওনার কাছে তখন অ্যালেন গিন্সবার্গের লেখা চিঠি একের পর এক পৌঁছে গেছে, যা ওনার মেজাজ আরও বিগড়ে দিয়েছিল। অ্যালেন গিন্সবার্গকে ৩১ অক্টোবর ১৯৬৪ যখন আবু সয়ীদ আইয়ুব এই চিঠিটি লিখছেন তখন লালবাজার পুলিশ সাক্ষাীসাবুদ যোগাড় আর মামলা সাজানোয় ব্যস্ত :
Dear Mr. Ginsberg,
I am amazed to get your pointlessly discourteous letter of 13th. That you agree with the communist characterization of the Congress For Cultural Freedom as a fraud and bullshit intellectual liberal anti-communist syndicate, did not, however, surprise me ; for I never thought the Congress had any chance of escaping your contempt of everything ‘Bourgeois’ or ‘respectable’.
If any Indian litteratur or intellectual come under police repression for their literary or intellectual work, I am sure the Indian Committee For Cultural Freedom would move in the matter without any ungraceful prompting from you. I am glad to tell you that no repression of that kind has taken place here currently. Malay Roychoudhury and his young friends of the Hungry Generation have not produced any worthwhile work to my knowledge, though they have produced and distributed a lot of self advertising leaflets and printed letters abusing distinguished persons in filthy and obscene language ( I hope you agree that the word “fuck” is obscene and “bastard” filthy at least in the sentence “Fuck the bastards of the Gangshalik School of poetry”, they have used worse language in regard to poets whom they have not hesitated to refer to by name ). Recently they hired a woman to exhibit her bosom in public and invited a lot of people including myself to witness this wonderful avant garde exhibition. You may think it as your duty to promote in the name of cultural freedom such adolescent pranks in Calcutta from halfway around the world. You would permit me to differ from you in regard to what is my duty.
It was of course foolish of the police to play into the hands of these young men and hold a few of them in custody for a few days ( they have all been released now ) thus giving the publicity and public sympathy — publicity is precisely what they want to gain through their pranks.
I do not agree with you that it is the prime task of the Indian Committee For Cultural Freedom to take up the cause of these immature imitators of American Beat Poetry. I respect your knowledge of European literature but can not permit myself to be guided by your estimation of writers in my language — a language of which you choose to remain totally ignorant.
With all good wishes in spite of your grave disagreements and in admiration of some of your wonderful poems.
Yours Sincerely
Abu Sayeed Ayyub
জবাবে অ্যালেন গিন্সবার্গের ৬ই অক্টোবর ১৯৬৪-এর চিঠিখানায় চোখ বোলান এবং আবু সয়ীদ আর অ্যালেনের চিন্তাপার্থক্য থেকে আঁচ করুন বাংলা সাহিত্য কেন ইউরোপের সাহিত্যকে টক্কর দিতে পারেনি রবীন্দ্রনাথের পর থেকে। আবু সয়ীদ আইয়ুবকে মিথ্যাবাদীও বলা চলে কেননা প্রথমত কারোর বিরুদ্ধেই মামলা তুলে নেয়নি পুলিশ তখনও পর্যন্ত, এবং দ্বিতীয়ত, কোনো নারীর টপলেস প্রদর্শনী করা হয়নি, টপলেস অর্থে মস্তিষ্কহীন কথাটা তাঁকে স্ট্রাইক করেনি সম্ভবত । বলা বাহুল্য আবু সয়ীদ, গিন্সবার্গের চিঠি পাবার পরও কুটোটি নাড়েননি, নাড়বেন কি করে যখন উনি নিজেই একজন নালিশকারী । তবে এটা ফাঁস হয়ে যায় যে আবুসয়ীদ আইয়ুব সায়েবদের কমিটির পত্রিকা ‘কোয়েস্ট’ আমেরিকার সিআইএর টাকা খায়, আর বদনাম হবার ফলে মামলার কাছাকাছি পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায় ।
Dear Mr Sayeed,
Obviously my note to you was stupidly peremptory or short witted and am sorry it got your goat, possibly or probably I deserve to be put down for the irritant discourtesy of my writing & the presumption in it, telling you what to do, etc. butting in where it is not my affair and possibly ignorant of the quality of the texts. And chiding a senior. For which I do wish to apologize, offering as excuse that I wrote in great haste — many letters on the same subject the same afternoon — and that the situation that I understand it is a little more threatening to the young scribes than you understand to be. May be it is settled a lot after I wrote. But from what I understood, from letters from Malay as well as Sunil Ganguly & Utpal Basu ( and the latter two seemed to be mature in judgement ) ( Malay I like as a person & do actually admire the liveliness of his englished manifestos — to my mind a livelier prose wit than any other Indian English writing ) ( tho I realise he is inexperienced & impetuous and part of the charm is the naivete of the manifestos, or better, innocence in them. ( this simply being a matter of gut taste preference intuition & certainly not the sort of literary matter to be settled by police action ) : the police situation at one time was that not only Malay but his brother Samir ( an excellent young philosopher ) as well as Debi Roy as well as two boys I never met Saileswar & Subhash Ghose were all arrested. Then let out on bail. In addition a general police investigation, and according to Utpal, “Those arrested are already suspended from their jobs & if they are convicted they may lose it.” Further Ananda Bazar Patrika, Jugantar, Janata and other Bengali papers fanned the fire against “obscene literary conspiracy.” Simultaneously the Supreme Court judgement of ‘Lady Catterley’ as obscene also, has, according to a clipping I read from Times of India “led many people to complain about the lewdness in the writings of many Bengali poets and novelists. Says Basu, “impossible to get another job if one is lost.” The arrested five were tied and locked up for one or two days each. Utpal Basu was detained by police and questioned for five hours. I understand also that Sunil was questioned by police. As far as I know it is still not decided whether or not the police will actually prosecute, and that decision will depend on the support given to the younger writers by older established writers and Cultural groups like Congress ( for Cultural Freedom ). Everyone I hear from has said the Congress has not spoken up in any way. All told, the situation, whether or not one approves of the literary quality of the texts, is much more threatening than I would gather from your letter. My own experience of the bureaucratic complications of police investigations in India — it’s endless and Kafkian grimness — led me to a much less light hearted view of the matter than yourself. As you may remember I was followed for months in Benares, visited by the police, threatened by Marxists, given a ten day quit India notice on vague charges of distributing obscene literature & corrupting the young. It took intervention by friends in Home Ministry in Delhi & a letter from Indian Consulate in NY to begin to straighten it out. So I have no confidence that a dismal legal process on literary matters once started, is so easily to be dismissed. Particularly where young apolitical inexperienced enthusiasts are concerned.
I don’t agree with you at all in your evaluation as obscene and filthy the sentence “Fack the bastards of the Gangshalik school of Poetry.” Not that I even know which school that is. But it’s common literary parlance both in speech and published texts from cafes of Paris or Calcutta to old manifestos by Tristan Tzara. The style, the impetuousness, the slight edge of silly ill-will, the style of “Burn the libraries”, an old charming XX century literary cry. I don’t really feel very “shocked” to hear that they let a lady show people her breasts in public. Do you seriously find that offensive ? I suppose it’s a little bit against the law — of course they had a woman completely naked on the balcony last year of the Edinburgh Festival — brightest moment of the Fete I hear tell — Yes certainly I do approve. However, I didn’t think myself nor “promote” it from halfway around the world. And I don’t really think that mere publicity is the deepest motive one can find in such typical Dada actions. In that I think you are really doing them an injustice, however low you grade their literary productions. Because after all there is considerable difference of opinion, as to the literary quality. Ferlinghetti, who does not know these writers is publishing a self-translated section of writings by Malay, Sunil & Basu in his City Lights Journal. The texts were collected by Mrs Bonnie Crown of the Asia Society, who found them as interesting as any translated texts she had been able to collect. The magazine “Kulchur” here — which has considerable avantgarde circulation — also reprinted three of the Manifestos in question ( on prose, poetry and politics ) earlier this year. This is independent of my correspondence with anyone.
In sum, what I do know of translation of the poetry & manifestos of Malay & the other poets arrested or questioned by the police, was pleasing. So, despite half a world difference, and acknowledging your greater familiarity with the literature, I must claim my prerogative as poet and also as critic ( since I edited and acted as agent here for such unpublished writers as Kerouac & Burroughs & Artaud as well as several differing schools of US poetry ) to stand by my intuition and say I do definitely see signs of modern life well expressed in their works. Not claiming they are geniuses or even great — simply that in certain precise areas dissatisfaction with their society, they do well reflect their thoughts, and reflect uniquely — their other contemporaries & seniors being more interested in classical piety or sociological “mature” formulations, Marxism Humanism etc. I don’t think it would be correct to term them Beatnick much less Beatnick imitators, since that’s primarily a journalistic stereotype that never even fit the US supposed “Beatnicks”.
Regarding the Congress ( for Cultural Freedom ) I stand by my fear that it is 1) possibly supported by Foundation funds connected with US government, 2) Less alert to dangers of suppression within the Western world and allies than within the Iron Curtain. In the US we have been all these years undergoing a siege of legal battles over stage works, books, movies, poetry etc. which has nearly crippled the public activity of Avangarde. I contacted the US Committee head Mr A. Beichman who said himself, the Congress is only a skeleton group in the US now inactive. And this year I had to contact John Hunt from NY to move the Congress to defend Olympia Press in Paris. There is a lag. My criticism was more just than you will allow, the overstated.
OK Best of Conscience —- Allen
অমনধারা সংঘাত ইতোপূর্বে ঘটেছিল পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতিতে । ইংরেজরা সময়কেন্দ্রিক মননবৃত্তি আনার পর প্রাগাধুনিক পরিসরমূলক বা স্হানিক ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বাঙালি ভাবুকের জীবনে ও তার পাঠবস্তুতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি আর ছটফটানি, রচনার আদল-আদরায় পরিবর্তনসহ, দেখা দিয়েছিল, যেমন ইয়ং বেঙ্গল সদস্যদের ক্ষেত্রে, এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও আরও অনেকের ক্ষেত্রে । একইভাবে হাংরি আন্দোলন যখন সময়কেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক চিন্তাতন্ত্র থেকে ছিঁড়ে আলাদা হলো, উত্তরঔপনিবেশিক আমলে আবার স্হানিকতার চিন্তাতন্তন্ত্রে ফিরে যাবার চেষ্টা করলো, তখন হাংরি আন্দোলনকারীদের জীবনে, কার্যকলাপে ও পাঠবস্তুর আদল-আদরায় অনুরূপ ঝাঁকুনি, ছটফটানি ও সমসাময়িক নন্দনকাঠামো থেকে নিষ্কৃতির প্রয়াস দেখা দিলো । তা নাহলে আমি সাহিত্য ছাড়াও রাজনীতি, ধর্ম, উদ্দেশ্য, স্বাধীনতা, দর্শনভাবনা, ছবি-আঁকা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে ইস্তাহার প্রকাশ করব কেন !
পঁচিশ
হাংরি মামলার আগে থেকেই পত্র-পত্রিকায় আমাদের, বিশেষ করে আমাকে, লক্ষ্য করে নানা মন্তব্য, চুটকি, সংবাদ, কার্টুন বেরোতে আরম্ভ করেছিল, যুগান্তর, অমৃত, দর্পণ, জনতা, চতুষ্কোণ, আনন্দবাজার, স্টেটসম্যান ইত্যাদি । যাঁরা ওগুলো লিখেছিলেন, এখন বুঝতে পারি, তাঁদের পড়াশুনা তেমন ছিল না, বেশির ভাগই হাফলিটারেট সাংবাদিক যারা নিজেদের সবজান্তা মনে করে । বঙ্গসংস্কৃতিকে যে আক্রমণ করা হচ্ছে, এটুকু বুঝে উঠতে পারেননি এনারা ।
‘দর্পণ’ পত্রিকায় গৌরকিশোর ঘোষেরও অংশীদারি ছিল শুনে ওনার সঙ্গে একটা ফয়সালা করতে গেলে, উনি ওনার বরানগরের বাড়িতে লুচি আলুরদম সহযোগে তর্কাতর্কির আহ্বান জানালেন । খবর দিয়ে গেলুম একদিন সকালে, আমি ত্রিদিব করুণা অনিল । ‘দর্পণ’ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে আমাদের আন্দোলন বিদেশিচিন্তায় প্রভাবিত । ত্রিদিব করুণা অনিল তর্ক করে গেল সুররিয়ালিজমের প্রভাব, সনেট রচনা, কবিতা আর উপন্যাসের ফর্ম, চিত্রকল্প ইত্যাদি । আমি ওই তর্কে না গিয়ে কেবল আলুর দমের আলুর প্রশংসা করে গেলুম । কিছুক্ষণ পরে উনি বুঝতে পারলেন যে কোন দিকে তর্কটা নিয়ে যাচ্ছি, কাঁধে হাত রেখে বললেন, ভালো চাল দিয়েছো, এবার তোমাদের একদিন লাঞ্চ খাওয়াবো । আমি বললুম, হ্যাঁ দাদা, আলু আমাদের দেশের নয়, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আয়ারল্যাণ্ড গিয়ে সেখান থেকে ভারতে এসেছে বেশিদিন হয়নি, ওয়ারেন হেসটিংস প্রথম চাষ আরম্ভ করেছিলেন নৈনিতালে আর এখন তো আলু ছাড়া বাঙালির কোনো রান্না হয় না, আলুপোস্তও এই সেদিনকার।
‘জনতা’ পত্রিকার দপতরে গিয়েছিলুম একটা হেস্তনেস্ত করার জন্যে, কেননা ওই পত্রিকায় প্রথম পাতায় কয়েক সপ্তাহ জুড়ে “পুলিশের নাকের ডগায় হাংরিরা এই করছে ওই করছে” লিখে-লিখে তাতানো হচ্ছিল । ওদের দপতরে তখন ছাপার কাজ তদারক করছিল পেটমোটা একজন মধ্যবয়সী, তাকে বললুম যে সম্পাদক বা মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই, আমার নাম মলয় রায়চৌধুরী । উনি বললেন, দাঁড়ান ডেকে দিচ্ছি, বলে চলে গেলেন । প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষার পরও উনি না আসায় প্রেসের এক কমপোজিটারকে জিগ্যেস করলুম, সম্পাদক কোথায় বসেন । সে বলল, উনিই তো সম্পাদক, আপনাদের দেখেই পালিয়েছেন ।
হাংরি আন্দোলনের কাউন্টার ডিসকোর্সের সঙ্গে তখনকার আধিপত্যবাদী ডিসকোর্সের সংঘাত গুরুতর হয়ে উঠেছিল ১৯৬৩ থেকে, যখন আমরা “হাংরি জেনারেশনের পক্ষ থেকে” “দয়া করে মুখোশ খুলে ফেলুন” ছাপানো কাগজের মুখোশ, রাক্ষস, জোকার, জন্তু-জানোয়ার, মিকিমাউস, দেবতা ইত্যাদির, পাঠালুম বা বাড়িতে চিঠির বাক্সে ফেলে এলুম, মুখ্য ও অন্যান্য মন্ত্রীদের, মুখ্য ও অন্যান্য সচিবদের, জেলা শাসকদের, সংবাদপত্র মালিক ও সম্পাদকদের, বাণিজ্যিক লেখকদের, তখন বঙ্গসমাজের উচ্চবর্গীয় “সংস্কৃতিমান” অধিপতিরা আসরে নামলেন । এর পর তাঁদের মাথায় বোমা ফাটল যখন বিয়ের কার্ড পোঁছোলো তাঁদের ঠিকানায়, কোনায় হলুদ মাখানো, কার্ডে লেখা “ফাক দি বাস্টার্ডস অফ গাঙশালিক স্কুল অফ পোয়েট্রি” । যাঁদের পাঠানো হয়েছিল তাঁরা অনেকেই ভেবেছিলেন যে তাঁরাই গাঙশালিক স্কুল অফ পোয়েট্রির কবি বা ফেলোট্র্যাভেলার । মুখোশের আর কার্ডের আইডিয়া আর খরচ আমার, সুভাষ ঘোষ আর শৈলেশ্বর ঘোষ কফিহাউসে আগেই গেয়ে রেখেছিল । এখন অনেকে নিজেদের প্রতিষ্ঠানবিরোধী তকমা দিয়ে আনন্দ পান, তাঁরা মন্ত্রী-আমলাদের অমন মুখোশ পাঠিয়ে দেখান না একটু । যাকগে, মুখোশ আর কার্ডের আইডিয়া আর খরচ আমার শুনে খচে বোম হয়ে গিয়েছিলেন, কে জানেন, সেই নিরীহ লোকটি, যাঁর নাম আবু সয়ীদ আইয়ুব । পুলিশ কমিশনার আমাকে আর আমার বাবাকে বলেছিলেন যে কলকাতার দুজন লোক জোর দিয়েছেন যাতে আমার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেয়া হয়, তাঁরা হলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব আর সন্তোষকুমার ঘোষ ।
অফিসের কাজে ১৯৬৩ সালের মাঝামাঝি থাকতে হয়েছিল কলকাতায় মাসতিনেক, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটের গেস্ট-হাউসে, বিকেলে যেতুম কফিহাউসে আড্ডা দিতে, তখনই, ১৯৬৩ সালে, সুভাষ আর শৈলেশ্বরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় । বাসুদেব দাশগুপ্তের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ১৯৬২ সালে ।গেস্ট হাউসে থাকার দরুণ পুরো মাইনেটাই বেঁচে যেতো আর তা হাংরি বুলেটিন ইত্যাদি ছাপানোর কাজে লাগাতুম । ছুটিছাটায় যেতুম হিন্দি কবি-লেখক রাজকমল চৌধুরীর কাগজের অফিসে, হ্যাশিশ ফুঁকতে, রাজকমল পাশাপাশি বাংলা উপন্যাসও অনুবাদ করে রোজগার করতো, তার কারণ ওর বাবা যে মেয়েটার সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছিল তার আত্মীয়ের প্রেমে পড়ে দুটো এসট্যাবলিশমেন্ট চালাতে হচ্ছিল ওকে। অমন একদিন হ্যাশিশ ফুঁকে ট্রামে চেপে গড়িয়াহাটে নেমে সামনেই দেখি আমার প্রথমম প্রেমিকা, কাঁথাস্টিচ শাড়িতে, আমাকে দেখে চমকে সামলে নিয়ে এগিয়ে এলো । জানালো একজন স্মাগলারকে বিয়ে করেছে ; প্রথমে বলল ওর আস্তানা যাদবপুরে এইটবি বাস স্ট্যাণ্ডের পেছনে, তারপর ট্যাক্সি ডেকে ড্রাইভারটাকে বলল নিউ আলিপুর যেতে । গেলুম । রাতভর থাকলুম । স্মাগলিঙের সোনার বিসকুট দেখলুম। বিদেশী হুইস্কি খেলুম । একসঙ্গে শুলুম, কিন্তু আমার লিঙ্গ দাঁড়ালো না, অশেষ ভাগ্য, অশেষ ভাগ্য, ঠিক সময়ে লিঙ্গের প্রত্যাখ্যান । প্রেমিকার খেতাব পেলুম “এরেকটাইল ডিসফাংশানের প্রেমিক।”
গেস্ট হাউসে থাকার দরুণ যে টাকা জমছিল, তাই দিয়ে মুখোশ কিনে, ছাপিয়ে, বিলি করা হল, পাঠানো হলো । বিয়ের কার্ডে “ফাক দি বাস্টার্ডস অফ গাঙশালিক স্কুল অফ পোয়েট্রি” ছাপিয়ে পাঠৈআনো হলো । যে লেখাগুলো জড়ো করেছিলুম সেগুলো একত্রিত করে হাংরি বুলেটিন প্রকাশিত হল, আমি কলকাতা ছাড়ার পর, প্রদীপ চৌধুরী ছাপিয়েছিল ওর চেনা প্রেসে, উডকাট দিয়ে প্রচ্ছদ তৈরি করে দিয়েছিল সুবিমল বসাক, পিসেমশায়ের বাড়ির ঠিকানায় দাদাকে প্রকাশক করে । যেমন বিনে পয়সায় বিলোনো হয়, তেমনই বিলোনো হল । কলকাতায় কার্পেট বমিং আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, এলিট কবি-লেখকদের মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত শেয়ালজ্ঞানী ঠেকগুলোয় রীতিমতো হল্লাবোল।
“যুগান্তর” সংবাদপত্রে ১৭ই জুলাই ১৯৬৪ “সাহিত্যে বিটলেমি” শিরোনামে একটা খবর বেরোয়, তাতে স্টাফ রিপোর্টার স্পষ্টভাবে পুলিশকে ওসকাতে চেয়েছিলেন । আমি যুগান্তর দপতরে গিয়েছিলুম ওই সাংবাদিকের খোঁজে, কিন্তু কেউই বলতে চাননি যে বানানো খবরটা কার লেখা । পরে কৃষ্ণ ধর পরপর দু’দিন প্রধান সম্পাদকীয় লিখেছিলেন হাংরি আন্দোলনের সমর্থনে । ওনাকে আমি বলেছিলুম, যদিও ইংরেজিতে, যে আমাদের সাহিত্যিক ক্ষুধা যৌনতার নয়, তা হল ন্যারেটিভের ডিক্যাননাইজেশানের, আঙ্গিকমুক্তির, যুক্তিভঙ্গের, ডিন্যারেটিভাইজেশানের, অনির্ণেয়তার, চিন্তার আকরণের, অপরত্ববোধের, প্রতাপবিরোধিতার, প্রতিস্পর্ধার, বাচনিক নির্মিতির, সত্তাজিজ্ঞাসার, প্রান্তিক-স্বাতন্ত্রের, উপস্হাপনের ব্যাঞ্জনার, অন্তর্ঘাতের ।
আমি গ্রেপ্তার হলুম ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৬৪, পাটনায়, কলকাতা থেকে দুজন শাদা পোশাকের পুলিশ অফিসার এসেছিল গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে, ওরা আমার অফিসে এসে হাজির, অফিস প্রধানের ঘরে ঢুকতে উনি বললেন, আপনি এই দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে বাইরে গিয়ে আলাপ করুন, আপনার সঙ্গে এনাদের কাজ আছে । নিচে রাস্তায় যেতেই দুজনে দুদিক থেকে আমার কাঁধ খামচে বলে উঠল, আপনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আছে, আপনার বাড়িতে নিয়ে চলুন । রিকশ ডেকে দুজনে দুদিক থেকে ধরে রইলো আমাকে, সম্ভবত ভাবছিল যে পালিয়ে যাবো । বাড়ি পৌঁছে দেখি স্হানীয় থানার পুলিশ ঘিরে ফেলেছে বাড়ি, পাবলিক জড়ো হয়ে গেছে মজা দেখতে । রিকশঅলাটা দাঁড়িয়েছিল, বাবা ভাড়া মিটিয়ে দিলেন । আমার জান্তব প্রবৃত্তির বিকাশ সম্পর্কে বাবা সঠিক অনুমান করে ফেলেছিলেন বহু আগেই ।
পুলিশ অফিসারদের একজন, পরে যার নাম জেনেছি বারোড়ি, সে পেপারওয়েট তুলে আচমকা বাবার দোকানের আলমারির কাচ ভেঙে ফেলল ; বাবা বললে, ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ তো ওর ঘরে গিয়ে তল্লাসি করুন না, জবাবে বারোড়ি বললে, আমরা পুরো বাড়িতে তল্লাশি চালাবো । ওপরতলায় যেতে খাটের তলা থেকে মায়ের ট্রাঙ্ক টেনে তালা ভেঙে ফেলে লণ্ডভণ্ড করা আরম্ভ করল, মায়ের বিয়ের বেনারসি পুরোনো ভাঁজ থেকে ছিঁড়ে গেল, আর আমি দেখতে পেলুম শ্রেয়াকণার চিঠি আর ফুলটুকে দেয়া আমার কার্ড ছিটকে বেরিয়ে এলো । তিন তলায় গিয়ে উনিশ শতক থেকে সংগ্রহ করা ফোটোর প্লেটের একটা র্যাক একটানে ফেলে দিল, এখন ওসব ফোটো সংগ্রাহকদের কাছে বেশ দামি । অবশ্য পরে দাদার ছেলেরা অন্য তাকের প্লেটগুলোকে অকেজো মনে করে সের দরে বেচে দেবে ।
টানাহেঁচড়া করে পুলিশ আমার ঘরে ডাঁই করে জড়ো করে ফেলল অনেককিছু, যা পরে মামলায় লাগবে না আর যা ইতিহাস থেকে হারিয়ে যাবে, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের আমাকে লেখা চিঠির দুটি ফাইল, একটায় ষাটটা অন্যটায় চল্লিশটা চিঠি ; আমার কবিতা নাটক ছোটোগল্পের পাণ্ডুলিপি ; আমার দুটো ডায়েরি, ইংরেজি আর বাংলা ; হাংরি আন্দোলনের বিভিন্ন বুলেটিনের বাণ্ডিল ; পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে সমালোচনা করে আমার পুস্তিকার বাণ্ডিল ; প্রচ্ছদে ব্যবহার করার জন্য দুটো ব্লক, মেকসিকোর চিত্রকরের আঁকা ; এভারগ্রিন রিভিউ-এর কপি ; সন্দীপনের উপহার দেয়া ‘বিজনের রক্তমাংস’ ; প্রদীপ চৌধুরী সম্পাদিত ‘স্বকাল’ ; ছোটোগল্প লেখা তিনটে খাতা ; প্রকাশিত ‘ইতিহাসের দর্শন’ লেখার ফাইল কপি ; যৌনতা সম্পর্কে একটি বই ; ত্রিদিব মিত্র সম্পাদিত ‘উন্মার্গ’ পত্রিকার কপি ; হিন্দি পত্রিকা ‘লহর’ যাতে আমার সম্পর্কে প্রবন্ধ বেরিয়েছিল ; একটা করোনা টাইপ রাইটার ; দাদা সমীর রায়চৌধুরীর কাব্যগ্রন্হ ‘জানোয়ার’-এর সব কয়টি কপি । এগুলোর মধ্যে কেবল আমার ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ কবিতার পাণ্ডুলিপি আদালতে পেশ করেছিল সরকারি উকিল । বাকি সব নিপাত্তা । সাক্ষী হিসাবে রাস্তা থেকে তিনজন ঝাড়ুদারকে ধরে নিয়ে এলো কলকাতার পুলিশ ।
হাতে হাতকড়া পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশের দল রাতে নিয়ে চলল বাঁকিপুর বা পিরবহোর থানায়, সোজা লকআপে, অন্ধকার, আলো নেই, পাশের লকআপে বেশ্যার দলের চেঁচামেচি, লকআপে সাত-আটজন কয়েদি, নানা অভিযোগে, ডাকাতি আর খুনও । ফুলপ্যান্টের ভেতরে ইঁদুর ঢুকে এলো, পা ঝেড়ে বের করলুম, বাড়ি থেকে খাবার এসেছিল, কিন্তু একে অন্ধকার, তায়ে লকআপের অভিজ্ঞতা, খাওয়া গেল না । সকালে স্হানীয় খবরের কাগজে গ্রেপ্তারির খবর শুনে নমিতা চক্রবর্তী সাহস যুগিয়ে গেলেন, বহুদিন পর ওনাকে দেখলুম, চোখে চশমা, টিচারি শুরু করেছেন, আমার নকাকিমা যে স্কুলে পড়ান সেখানে। নমিতাদি বেঁচে থাকলে জানতে চাইতুম, ভেঙে পড়া সোভিয়েত রাশিয়ায় কোথা থেকে এতো মহাকোটিপতি আর মহাচোরাকারবারী আচমকা উদয় হল, এতো ভিকিরি, এতো ছিঁচকে চুনোপুঁটি !
হাগবার জন্য কোমরে দড়ি পরিয়ে হাগতে পাঠানো হলো, ঘুড়ি ওড়ানোর মতন করে ঢিল দিয়ে লাটাই ধরে থাকলো একজন কন্সটেবল আর আমি হাগতে গেলুম, চারিদিকে কয়েদিদের গু, জল পড়ে চলেছে কল থেকে, পোঁদ এগিয়ে ছুঁচিয়ে নিলুম । আবার হাতে হাতকড়া আর কোমরে দড়ি বেঁধে কয়েদিদের সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে ফৌজদারি আদালত। বাবা বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে এনেছিলেন, যিনি হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেন । কলকাতার পুলিস রিমান্ড চাইছিল । বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জামিন দিয়ে বললেন কলকাতার ব্যাংকশাল কোর্টে আত্মসমর্পণ করতে । বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন লেখিকা এনাক্ষী ব্যানার্জি আর মীনাক্ষী মুখার্জির বাবা । বাড়ি এসে নিজেকে নবীকরণ করে পৌঁছোলুম উত্তরপাড়ায়, পেছন-পেছন বড়োজ্যাঠা আর বাবা । দাদাও চাইবাসায় গ্রেপ্তার হয়ে চাইবাসা থেকে এসে পৌঁছোলো । জমায়েত দেখে, দাদা গ্রেপ্তার হয়েছে শুনে ঠাকুমার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল । অন্যান্য জেঠা-কাকারা আর পিসেমশায় এসে পৌঁছোলেন ।
ব্যাংকশাল কোর্টে সারেন্ডার করে জানতে পারলুম দেবী রায়, সুভাষ ঘোষ আর শৈলেশ্বর ঘোষও গ্রেপ্তার হয়েছে । জামিনের পর আদালত বলল লালবাজারে গিয়ে প্রেস সেকশানে হাজিরা দিতে । লালবাজারে হাজিরা দিতে গিয়ে কফিহাউসে পুলিশ ইনফরমারদের কথা জানতে পারলুম, যারা হাংরি আন্দোলনের বুলেটিন বই পত্রিকা এনে-এনে জড়ো করেছে প্রেস সেকশানে । আশ্চর্য যে মুখের দিকে তাকিয়েও কেন বুঝতে পারিনি যে অমুক লোকটা, যে আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছে সে ইনফরমার, তমুক যুবক যে আমার কাছ থেকে বুলেটিন চেয়ে নিয়ে গেল, সে পুলিশের খোচর । মামলার সময় যখন এরা কাঠগড়ায় আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালো তখন টের পেলুম । সুভাষ ঘোষ আর শৈলেশ্বর ঘোষের মুখের দিকে তাকিয়েও কি কখনও জানতে পেরেছিলুম যে ওরা পিঠে ছুরি মারবে । অবশ্য আঁচ করা উচিত ছিল, কেননা ওরা দুজনেই লালবাজারে ইন্সপেক্টরের হম্বিতম্বিতে কেঁদে একশা , সেই ইন্সপেক্টর অনিল ব্যানার্জি, পরে নকশাল বিনাশে নাম করেছিল।
আঘাত তো লোকে করবেই, কিন্তু সব আঘাতে আদর করে হাত বোলানো যায় না । বেশির ভাগ আঘাতের দাগ দেহের চামড়ায় পুষে রাখতে হয় ।
ছাব্বিশ
মামলার সময়টা বেশ খারাপ গেছে, কলকাতায় মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না, সাসপেন্ড হবার দরুণ মামলার খরচ, যাতায়াতের খরচ আর খাবার খরচ সামলানো কঠিন হয়ে গিয়েছিল । একই শার্ট-প্যাণ্ট প্রায় পনেরো দিন পরে চালিয়েছি । সবসুদ্ধ পঁয়ত্রিশ মাস মামলা চলেছিল । উত্তরপাড়ার খণ্ডহরে থাকা যেতো কেসের ডেটের মাঝে হাতে সময় থাকলে, কেননা তখন সেরকমভাবে ইলেকট্রিক ট্রেন শুরু হয়নি আর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের কোনো নির্ধারিত সময় ছিল না । সুবিমল বসাকের জেঠার স্যাকরার দোকানে বৈঠকখানা পাড়ায় থাকতুম মাঝেমধ্যে আর হাগতে যেতুম শেয়ালদায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে, রাস্তার কলগুলো এতো নিচু যে তার তলায় প্রায় শুয়ে স্নান করতে হতো । ফলে প্রতিদিন স্নানের অভ্যাস ছাড়তে হয়েছিল । শহরে যাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই তাদের কাছে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল হাগা, কোথায় গিয়ে হাগা যায় । তখন তো সুলভ শৌচালয় আরম্ভ হয়নি । আহিরিটোলায় রাতে থাকতে পেলে অন্ধকার থাকতে গঙ্গার পাড় ছিল সবচেয়ে সহজ । এটা সেন্টুদার শেখানো ; পিসেমশায়ের আটজন বাচ্চা আর একটা পায়খানা, গঙ্গার পাড়ে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে হাগা পেলে পায়জামা বা প্যান্ট নামিয়ে হেগে নাও আর গঙ্গায় পোঁদ ঠেকিয়ে ছুঁচিয়ে নাও । হাগা পেলে হেগে নেওয়ার মতন আর কোনও আনন্দ নেই । সেন্টুদা পরামর্শ দিয়েছিল যে রাতে হোটেলে থাকার চেয়ে ভালো জায়গা হলো অবিনাশ কবিরাজ লেনের কোনো ঘরে কাউকে সারা রাতের জন্যে প্রেমিকার দাম দেয়া । কিন্তু সেখানেও তো ভোরবেলা উঠে হাগার সমস্যা । সেখানে রাত কাটালেও হাগতে ছুটতে হতো বড়োবাজারে হিন্দি পত্রিকা “জ্ঞানোদয়” এর সম্পাদক শরদ দেওড়ার মারোয়াড়ি গদিতে । এই গদিতে শুয়েও রাত কাটিয়েছি, যতো রাত বেড়েছে ততো শোবার লোকের ভিড় বেড়েছে, কেননা বাইরে থেকে যে ব্যাবসাদাররা কলকাতায় আসতো তারা মারোয়াড়িদের গদিতে শোয়া পছন্দ করতো ।
বাদবাকি সকলের বিরুদ্ধে আরোপ তুলে নিয়ে, ৩রা মে ১৯৬৫ আমার বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করল পুলিশ । তার সঙ্গের নথিগুলো থেকে জানতে পারলুম হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্রব অস্বীকার করে মুচলেকা দিয়ে আমার বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হয়েছে সুভাষ ঘোষ আর শৈলেশ্বর ঘোষ, মামলা থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য । এও জানলুম যে আমার বিরুদ্ধে পুলিশের হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় আর উৎপলকুমার বসু, এঁরাও নিজেদের হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্রব অস্বীকার করেছেন । উৎপল চাকরি খুইয়ে গিন্সবার্গের সুপারিশে ইংল্যাণ্ডে চাকরি পেয়ে চলে গেলেন । সুভাষ আর শৈলেশ্বর আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে ক্ষান্ত দেয়নি, একের পর এক লেখায় হাংরি আন্দোলনের ইতিহাসকে বিকৃত করে গেছে, সময়ের সঙ্গে তাল দিয়ে আমার প্রতি ঘৃণার মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছে, এমনকি নিজের বউ-বাচ্চাদেরও এ-ব্যাপারে ট্রেনিং দিয়ে গেছে ; ফলে ওদের নিজেদের মরচে-পড়া ছোরাগুলোই অকালে রোগ হয়ে ওদের বুকে বিঁধেছে।
দীপক মজুমদার আমার সমর্থনে একটা স্টেটমেন্ট লিখেছিলেন, এবং বহু সাহিত্যিকের কাছে গিয়েছিলেন তাতে সই করানোর জন্য । কেউ রাজি হননি । কেবল আনন্দ বাগচি সই করেছিলেন । “প্রথম সাড়া জাগানো কবিতা” সম্পাদনার সময়ে আনন্দ বাগচি আমার “প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার” কবিতাটা তাতে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন । উৎপলকুমার বসু থাকতেন রয়েড স্ট্রিটে, দোতলায়, সাজানো-গোছানো ঘর, কিন্তু রাতে শোবার অনুমতি দিতেন না । হাংরি আন্দোলনের দরুণ ওনার চাকরি চলে যাবার পর, গিন্সবার্গের সুপারিশে লণ্ডনে চাকরি পেয়েছিলেন । পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিকেশানের প্রয়োজনের কারণে হয়তো পুলিশের পক্ষের সাক্ষী হয়েছিলেন । সম্প্রতি বিবিসি রেডিওর ডোমিনিক বার্ন ভারতে এলে তাকে সাক্ষাৎকারে নিজেকে হাংরি আন্দোলনকারী বললেও, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভয়ে, এবং সম্ভবত আনন্দ পুরস্কার আর অকাদেমি পুরস্কার পাবার জন্য, হাংরি বুলেটিনে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত কবিতা “পোপের সমাধি” বাদ দিয়ে দিয়েছেন “শ্রেষ্ঠ কবিতা” থেকে ।
৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ থেকে ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৬৫ পর্যন্ত কাফকায়েস্ক জগতে আমার চলছিল তারিখের পর তারিখ, পেশকারের সোনার দাঁত, উকিলের ফিস, ইনভেস্টিগেশান অফিসারের মুচকি হাসি, তারিখের পর তারিখ, পেশকারের সোনার দাঁত, উকিলের ফিস, ইনভেস্টিগেশান অফিসারের মুচকি হাসি, তারিখের পর তারিখ, পেশকারের সোনার দাঁত,উকিলের ফিস, ইনভেসটিগেশান অফিসারের মুচকি হাসি, তারিখের পর তারিখ, পেশকারের সোনার দাঁত, উকিলের ফিস, ইনভেস্টিঘেশান অফিসারের মুচকি হাসি, তারিখের পর তারিখ, পেশকারের সোনার দাঁত,উকিলের ফিস, ইনভেস্টিগেশান অফিসারের মুচকি হাসি, ক্ষয়ে যাওয়া সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামের ঘর্মাক্ত পরিশ্রম কখনও থামবে না এরকম এক পাগল করা প্রক্রিয়া ।
সুবিমল বসাক, ত্রিদিব মিত্র, ফালগুনী রায় ছাড়া সকলেই কেটে পড়ল আমার পাশ থেকে । আমার বিরুদ্ধে সাক্ষীদের কথা কফিহাউসে চাউর হয়ে গেলে জ্যোতির্ময় দত্ত, সত্রাজিৎ দত্ত আর তরুণ সান্যাল নিজেরা যোগাযোগ করে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে রাজি হলেন । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রথমে রাজি ছিলেন না, যেই শুনলেন যে শক্তি, সন্দীপন, উৎপল আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, উনি তক্ষুনি রাজি হয়ে গেলেন, ওনাদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্য, কেননা সুনীলকে না জানিয়ে ওনারা হাংরি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সন্দীপনকে সুনীল এর জন্য ক্ষমা করতে পারেননি আর গোপনে আমার বিরুদ্ধে প্রচার করে গেছেন, ভারতে বা বিদেশে কেউ আমার কথা জানতে চাইলে “ও তো লিখতেই জানে না” বলে উড়িয়ে দিতেন।
সুনীল যে হাংরি আন্দোলনের বিরুদ্ধে কতো চটে গিয়েছিলেন তা ১০ই জুন ১৯৬৪ তারিখে আয়ওয়া থেকে আমায় লেখা চিঠির এই অংশটুকু থেকেই স্পষ্ট হবে: “চালিয়ে যাও ওসব আন্দোলন কিংবা জেনারেশনের ভণ্ডামি । আমার ওসব পড়তে কিংবা দেখতে মজাই লাগে । দূর থেকে । সাহিত্যের ওপর মৌরসি পাট্টা বসাতে এক-এক দলের অত লোভ কী করে আসে, কী জানি । তবে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভালো । আমাকে দেখেছ নিশ্চয় শান্তশিষ্ট, ভালো মানুষ । আমি তা-ই, যদিও গায়ে পদ্মাপাড়ের রক্ত আছে । সুতরাং, তোমাদের উচিত আমাকে দূরে-দূরে রাখা, বেশি খোঁচাখুঁচি না করা । নইলে হঠাৎ উত্তেজিত হলে কী করব বলা যায় না । জীবনে ওরকম উত্তেজিত হয়েছি পৌনে একবার । গত বছর । দু-একজন বন্ধুবান্ধব ও-দলে আছে বলে নিতান্ত স্নেহবশতই তোমাদের হাংরি জেনারেশন গোড়ার দিকে ভেঙে দিইনি । এখনও সেক্ষমতা রাখি, জেনে রেখো । তবে এখনও ইচ্ছে নেই ও-খেলাঘর ভাঙার।”
মনের ভেতরে সুনীলের যে বিষক্রিয়া চলছিল তা পাঁচ দিন পর ১৫ জুন ১৯৬৪ তারিখে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে লেখা এই চিঠির বিষাক্ত অংশটি থেকে টের পাওয়া যায়, “আপনি মলয়কে এত পছন্দ করছেন—কিন্তু ওর মধ্যে সত্যিকারের কোনো লেখকের ব্যাপার আছে আপনি নিশ্চয়ই মনে-মনে বিশ্বাস করেন না । আমি চলে আসার পরও আপনি হাংরির পৃষ্ঠপোষকতা করছেন — হিন্দি কাগজের জন্য আপনি কি একটা লিখেছিলেন — তাতেও হাংরির জয়গান । ভাবতে খুব অবাক লাগে — আপনার মতো অ্যাবস্ট্র্যাক্ট লেখক কি করে ইলাসট্রেটেড উইকলিতে ছবি ছাপাটাও উল্লেখের ব্যাপার মনে করে । এগুলোই হাংরির গোঁজামিল । এই জন্যই এর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক থাকতে বারবার দুঃখ পেয়েছি, দুঃখ থেকে রাগ, রাগ থেকে বিতৃষ্ণা । একটা জিনিস নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আমি হাংরির কখনও প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করিনি, ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করিনি । পারতুম । করিনি, তার কারণ, ওটা আপনাদের সখের ব্যাপার এই ভেবে, এবং আপনারা ওটাকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিলেন কৃত্তিবাস বা সুনীলের প্রতিপক্ষ হিসাবে । সে হিসেবে ওটাকে ভেঙে দেওয়া আমার পক্ষে নীচতা হত । খুবই । বিশ্বাস করুন, আমার কোনো ক্ষতির কথা ভেবে নয়, আপনার অপকারের কথা ভেবেই আমি আপনার ওতে থাকার বিরোধী ছিলুম । এটা হয়তো খুব সেন্টিমেন্টাল শোনালো, যেন কোনো ট্রিক, কিন্তু ও-ই ছিল আমার সত্যিকারের অভিপ্রায়।” এই চিঠিটা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ।
সন্দীপন যখন কফিহাউসে বসে বলতেন, ইনসাইড জব, ইনসাইড জব, ইনসাইড জব, তখন বুঝতে পারিনি কী বলতে চাইছেন । সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে ১৯৬১ সালে জিগ্যেস করেছিলুম, “আপনার আর শক্তিদার মাথার পেছনটা চ্যাপ্টা অথচ সুনীলদার গোল কেন?” জবাবে উনি বলেছিলেন, “ওই বাড়তি অংশে ওর শাওলিন সিক্রেট আছে।” সন্দীপনের চেতলার বাড়িতে জিগ্যেস করেছিলুম, “শুধু মাগি-মরদ নিয়ে লেখেন কেন ? কর্পোরাশানের যে বিভাগে কাজ করেন তা তো ঘুষখোরদের আড়ত, সেসব দেয়া-নেয়া নিয়ে লেখেন না কেন ?” উনি বলেছিলেন, “তা লিখলে, পেনশান বন্ধ হয়ে যাবে।”
সাতাশ
সুনীলের আমাকে এতো ভয় পাবার কারণ আমি আজও ডেসিফার করতে পারিনি, আমি তো সেসময়ে ছিলুম একজন নাম-না-জানা প্রবাসী, হারাধন ধাড়া নামে যুবকটি তার চেয়ে বেশি অখ্যাত, তারা একটা আন্দোলনের আওয়াজ দিলো আর তাতেই ভয় পেয়ে গেলেন কৃত্তিবাসের সম্পাদক, ভাবলেন ব্যক্তিগত স্তরে তাঁকে বিস্হাপিত করার চেষ্টা হচ্ছে ! আমি নিশ্চিত যে সুনীল এই ধরণের চিঠি উৎপলকেও লিখে থাকবেন । আসলে একজন লোক কী ভাবছে তা শোনবার মতন ক্ষমতা তখনও পর্যন্ত গড়ে তুলতে পারিনি ।
২৮শে ডিসেম্বর ১৯৬৫ আমাকে দুশো টাকা জরিমানা অনাদায়ে একমাসের কারাদণ্ড দিলেন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেট । আমার পক্ষের কোনো সাক্ষ্যকে পাত্তা দিলেন না তিনি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যকেও নয় ; হয়তো তখন যদি পরবর্তী কালের মতন সুনীল সে সময়ে বিখ্যাত হতেন তাহলে জজ সায়েবের দ্বিধা হলেও হতে পারত। গুরুত্ব দিলেন আমার বিরুদ্ধে যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদের সাক্ষ্যকে। জজ সায়েব যে দুশো টাকা জরিমানা করেছিলেন তা ছিল সর্বোচ্চ । আমি চাকরিতে তখন মাইনে পেতুম ১৭০ টাকা, গ্র্যাজুয়েট ছিলুম বলে।
জজ সায়েব “প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার” কবিতাটা নিজেই এভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন, বোঝা যায় সেসময়ে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের সাহিত্যিক মূল্যবোধে, তা সে জজ অমলকুমার মিত্র হোন বা আবু সয়ীদ আইয়ুব, কোনও পার্থক্য ছিল না । জজ সায়েবের বক্তব্য পড়লে স্পষ্ট হবে : It appears to be per se obscene. In bizarre style it starts with restless impatience of a sensuous man for a woman obsessed with uncontrollable urge for sexual intercourse followed by a description of vagina, uterus, clitoris, seminal fluid, and other parts of female body and organ, beasting of man’s innate impulse and conscious skill as to how to enjoy a woman, blaspheming God and profaning parents accusing them of homosexuality and masterbation, debasing all that is noble and beautiful in human love and relationship. It is a piece of self analysis and eroticism in autobiographical or confessional vein when the poet engages himself in mercilessly obnoxious and revolting self-degradation and resorts to sexual vulgarity to a degree of perversion and morbidity far exceeding the customary and permissible limits of candour in description or representation. It is patently offensive to what is called contemporary community standards. Its predominant appeal to an average man considered as a whole is to prurient interest, in a shameful or morbid interest in nudity, sex and excretion. Considering its dominant theme it is dirt for dirt’s sake, or, what is commonly called, hard core pornography suggesting to the minds of those in whose hands it may fall stinking wearisome and suffocating thoughts of a most impure and libidinous character and thus tending to deprave and corrupt them without any rendering social or artistic value and importance. By no stretch of imagination can it be called, what has been argued, an artistic piece of erotic realism opening up new dimension of contemporary Bengali literature or a kind of experimental piece of writing, but appears to be a report of a repressed or a most pervert mind who is obsessed with sex in all its nakedness and thrives on, or revel, in utter vulgarity and profanity preoccupied with morbid eroticism and promiscuity in all its naked ugliness and uncontrolled passion for opposite sex. It transgresses public decency and morality substantially, rather at public decency and morality by its highly morbid erotic effect unredeemed by anything literary or artistic. It is an affront to current community standards of morality and decency. The writing viewed separately and as a whole treats with sex, that great motivating force of human life, in a manner that surpasses the permissible limits judged from our community standards, and as there is no redeeming social value or gain to society which can be said to preponderate, I must hold that the writing has failed to satisfy the time honoured test. Therefore it has got to be stamped out since it comes within the purview of Section 292 of Indian Penal Code. Accused is accordingly found guilty of the offence punishable under Section 292 of Indian Penal Code, is convicted thereunder and sentenced to pay a fine of Rs. 200/- , in default simple imprisonment for one month. Copies of the impugned publication seized be destroyed.
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও, যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত নিমরাজি হয়ে, দাদার অনুরোধে, ৫ই নভেম্বর ১৯৬৫ আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, সাক্ষ্য দিয়ে ফেরার পর দাদাকে ৯ই নভেম্বর যে চিঠিটা লিখেছিলেন তার গুরুত্বপূর্ণ অংশটি জজ সায়েব আর আবু সয়ীদ আইয়ুবের সাহিত্যিক মানসিকতা থেকে ওনার বিশেষ পার্থক্য দেখি না : “সাক্ষীর কাঠগড়ায় মলয়ের কবিতা আমাকে পুরো পড়তে দেওয়া হয় । পড়ে আমার গা রি-রি করে । এমন বাজে কবিতা যে আমাকে পড়তে বাধ্য করা হল, সে জন্য আমি ক্ষুব্ধ বোধ করি — আমার সময় কম, কবিতা কম পড়ি, আমার রুচির সঙ্গে মেলে না এমন কবিতা পড়ে আমি মাথাকে বিরক্ত করতে চাই না । মলয়ের তিন পাতা রচনায় একটা লাইনেও কবিতার চিহ্ণ নেই ।” বুড়ো বয়সে জানতে পেরেছিলেন নিশ্চয় যে ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ কবিতাটা বহু ওয়েবপত্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছে, নেটে কবিতাটা নিয়ে দশ বছর যাবত তর্কাতর্কি চলছে ।
চিঠিটির পরের অংশে তিনি যা লিখেছিলেন তা আরও ভয়ঙ্কর : “যাই হোক, তবু আমি বেশ স্পষ্ট গলাতেই দুবার বলেছি ওর ঐ কবিতা আমার ভালো লেগেছে । এর কারণ, আমার কোনো মহত্ব নয়— আমার সাধারণ, স্বাভাবিক, সীমাবদ্ধ জীবন । যে কারণে আমি আনন্দবাজারে সমালোচনায় কোনো বাজে বইকে ভালো লিখি — সেই কারণেই মলয়ের লেখাকে ভালো বলেছি ।” দেশ-আনন্দবাজারে কতো-কতো বই তিনি আলোচনা করেছেন, সব আলোচনাই তাহলে গুয়েগোবরে ব্যাপার !
সিটি লাইটস বুক স্টোরের মালিক ও বিট আন্দোলনের কবি লরেন্স ফেরলিংঘেট্টি ওনার পত্রিকা সিটি লাইটস জার্নালে প্রকাশ করতে চাইছিলেন বলে ওনাকে একটা কপি পাঠিয়েছিলুম, পড়ে উনি ২৬ মার্চ ১৯৬৬ তারিকে এই চিঠিটা লিখেছিলেন আমাকে:-
Dear Malay,
I have received the legal decision on your case, and thank you very much for sending it. I find it laughable. I want to publish it together with your poem ‘Stark Electric Jesus’ in the next ‘City Lights Journal’ which will be out this coming summer, and I enclose a small payment immediately, since I know you must need it desperately. I am sending a copy of this letter to Howard McCord. Perhaps he knows the answers to the following questions and will send them to me rightaway since time is of the essence, and it may take some time to get a reply from you. I think it is a wonderful poem, and I will certainly credit McCord for having first published it. Bravo.
Allen is in NY and his new address is 480 East, !0 Street ( Apt 4c ), New York, NY.
I need to know the answers to the following questions : 1) Was the poem first written in Bengali and was it the Bengali or the English version which was seized and prosecuted ? 2) Is this your own translation, or whose is it ? 3) Do you wish me to use the typewritten copy of the poem which you sent me last year, or the version printed by McCord ? ( I find differences ).
Let me hear as soon as you can. Holding the press. And good luck. I hope you are still able to survive. With Love
Lawrence Ferlinghetti
আমি কলকাতা হাইকোর্টে রিভিশন পিটিশান করলুম । হাইকোর্টের জন্য আমি পেলুম সদ্য ইংল্যাণ্ড থেকে ফেরা ব্যারিস্টার করুণাশঙ্কর রায়কে, যিনি হাংরি আন্দোলনের মামলার সংবাদ লণ্ডনের কাগজগুলো থেকে পেয়েছিলেন । তিনি যোগাযোগ করিয়ে দিলেন বিখ্যাত ক্রিমিনাল লইয়ার মৃগেন সেনের সঙ্গে । হাইকোর্টে শুনানি হল ২৬ জুলাই ১৯৬৭ আর বেকসুর খালাস হলুম, এই আদেশে: I hold first that the substance of any offence under Section 292 IPC could not have been explained to the petitioner in this case, and secondly, that the finding of the learned Magistrate that the petitioner circulated any obscene matter is not based on any evidence whatsoever. This rule accordingly is made absolute. The order of conviction and sentence passed on the petitioner is set aside and he is acquitted. Fine, if paid, be refunded. ।
হাইকোর্টে রেহাইয়ের পর কেবল একজন সাহিত্যিকের চিঠি পেয়েছিলুম, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের, ৩০ জুলাই ১৯৬৭ তারিখে লেখা, আর কারো নয়, মুচলেকাপন্হীদের তো নয়ই, এই চিঠিটার জন্যে সন্দীপনকে ক্ষমা করে দিয়েছিলুম :
প্রিয় মলয়,
হাইকোর্টের রায় পড়ে তোমাকে মনে-মনে তৎক্ষণাৎ কনগ্র্যাচুলেট করেছি । একটা মামলা হওয়া দরকার ছিল, কাউকে না কাউকে এরকম মামলার আসামী হতেই হত । সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এর ফলাফল আধুনিক সত্য-সাহিত্যের পক্ষে যথেষ্ট ভালো হবে, মনে হয় ।
কৃতিত্ব সবটাই তোমার একার, তবু, লেখক নামের যোগ্য সকলেই একে পুরস্কার বলে মনে করবে ও ভাগ নিতে চাইবে । ব্যক্তিগতভাবে আমি পুরস্কৃত হওয়ার আনন্দ পেয়েছি ।
প্রীতিসহ
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়
আঠাশ
১৯৬৫এর ওই সময় থেকে ১৯৬৭এর রেহাই পর্যন্ত আমাকে ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াতে হয়েছে । রেহাই পেয়ে চাকরি ফিরে পেলুম । চাকরি পেয়ে করুণাশঙ্কর রায়ের মাধ্যমে হাইকোর্টের ব্যারিস্টার মৃগেন সেন ও তাঁর টিমকে নগণ্য ফিস দিতে পারলুম । করুণাশঙ্কর রায় প্রদেয় ফিস প্রায় মুকুব করিয়ে দিয়েছিলেন, নয়তো মৃগেন সেনের যা ফিস ছিল তা আমার পক্ষে দেয়া অসম্ভব হতো ।
আমার মামলা যখন ব্যাংকশাল কোর্টে সাবজুডিস রয়েছে, সেসময়ে আগবাড়িয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কৃত্তিবাস পত্রিকায় এই সম্পাদকীয়টি লিখলেন, দাদার মতে উনি এটা লিখেছিলেন আনন্দবাজার এসট্যাবলিশমেন্টকে সন্তুষ্ট করার জন্য, কেননা ব্যাংশাল কোর্টে মামলা চলার সময়ে তো বুলেটিন বেরোনো বন্ধ হয়ে গেছে, মুচলেকাপনন্হীরা যে-যার কেটে পড়েছে, আমার বিরুদ্ধে জোট বেঁধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছে:
“হাংরি জেনারেশান। অনেকেই প্রশ্ন করছেন বলে আমরা লিখিতভাবে জানাতে বাধ্য হলুম যে হাংরি জেনারেশান নামে কোনো প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের সঙ্গে কৃত্তিবাস সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত । ঐ প্রকার কোনো আন্দোলনে আমরা বিশ্বাস করি না । কৃত্তিবাসের নামও যুক্ত করতে চাইনি কখনও । ‘হাংরি’ নামে অভিহিত কোনো-কোনো কবি কৃত্তিবাসে লেখেন, বা ভবিষ্যতে অনেকে লিখবেন, কিন্তু অন্যান্য কবিদের মতোই ব্যক্তিগতভাবে, কোনো দলের মুখপাত্র হিসেবে নয় । সংঘবদ্ধ সাহিত্যে আমরা আস্হাশীল নই । পরন্তু বাংলাদেশের যে কোনো কবির প্রতিই কৃত্তিবাসের আহ্বান । হাংরি জেনারেশানের আন্দোলন ভালো কি খারাপ আমরা জানি না । ঐ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ বা পরিণাম সম্পর্কে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। এ-পর্যন্ত ওদের প্রচারিত লিফলেটগুলিতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি চোখে পড়েনি । নতুনত্ব-প্রয়াসী সাধারণ রচনা । কিছু-কিছু হাস্যকর বালক ব্যবহারও দেখা গেছে । এছাড়া সাহিত্য সম্পর্কিত কয়েকটি ক্রিয়াকলাপ বিরক্তি উৎপাদন করে । পিজিন ইংরেজিতে সাহিত্য করার লোভ উনিশশো ষাট সালের পরও বাংলাদেশের একদল যুবক দেখাবেন — আমাদের কাছে কল্পনাতীত ছিল । তবে ঐ আন্দোলন যদি কোনোদিন কোনো নতুন সাহিত্যরূপ দেখাতে পারে — আমরা অবশ্যই খুশি হবি ।”
ব্যাংকশাল কোর্টে আমার উকিল চণ্ডীচরণ মৈত্র সম্পাদকীয়টা পড়ে বলেছিলেন, একটা কনটেম্পট অফ কোর্ট মামলা ঠুকে দিতে । তা সম্ভব ছিল না, কেননা মনের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে জোঁক-কাঁকড়াবিছে পুষে রাখলেও উনি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন ।
পরেও, ইংরেজি ভাষার ভারতীয় ঔপন্যাসিক অমিতাভ ঘোষের স্ত্রী ডেবোরা বেকার যখন গিন্সবার্গ আর অরলভস্কিকে নিয়ে ‘দি ব্লু হ্যাণ্ড’ বইটা লেখার জন্যে হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে সুনীলের কাছ থেকে তথ্য চাইলেন, ডেবোরা বেকারকে আমাদের কাছে না পাঠিয়ে ভুলভাল তথ্য সরবরাহ করেন সুনীল, আমার সম্পর্কে তো বটেই। আমার ওপর ওনার রাগ বুড়ো বয়সেও যায়নি । কৃত্তিবাসের জন্যে আমার কাছে কবিতা চাননি কখনও । উনি পঞ্চাশ বছর আমার কাছে কবিতা চাননি
মামলা চলার সময়ে, আর তার পরও অনেকে বলতো, আরে মামলা চলছে তো কি হয়েছে, অমন মামলা তো ফৌজদারি আদালতে চলতেই থাকে । জবাবে আমি বলতুম যে, বাঞ্চোৎ, কলকাতা শহরে বাড়ি আছে, মাথা গোঁজার ঠাঁই আছে, দুবেলা খাবার ব্যবস্হা আছে, তাই অমন কথা বলতে পারছিস । রাতে থাকার ঠাঁই নেই, পাইস হোটেলে খেয়ে-খেয়ে পেটের অবস্হা তথৈবচ, সকালে উঠে কোথায় হাগতে যাবো, খিদে পেলে জলখাবার খেয়ে বাসভাড়া খরচ করে কোর্ট পর্যন্ত হাঁটবো, দিনের পর দিন একটা শার্ট-প্যান্ট পরেই কাটাবো, ঘামে গেঞ্জির অবস্হা এমন যে খুলে জঞ্জালের গাদায় ফেলে দিতে হবে, সামলাবার জন্যে কাউকে ধরে খালাসিটোলায় ধেনো টানবো বা গাঁজা ফুঁকবো, এগুলো ফেস করতিস তো বুঝতিস । মামলার সময়ে দুজন কেবল সাহায্য করেছিলেন, কমলকুমার মজুমদার, খালাসিটোলার কাছে একটা একশো টাকার নোট দিয়ে, যদিও আমার সঙ্গে ওনার তেমন পরিচয় ছিল না, বলেছিলেন, “তুমি তো জুলিয়াস সিজার হে।” তখন ভেবেছিলুম যে কলকাতায় চারিদিকে আমাকে নিয়েই আলোচনা চলছে বলে কথাটা বললেন । মামলার সময়ে যখন বন্ধুরা সাক্ষী হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়ালো তখন টের পেলুম যে কেন বলেছিলেন জুলিয়াস সিজার। আরেকজন, অশোক মিত্র, আই এ এস, ওনার বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, সেই রাতের ভালোমন্দ খাবার খাওয়ার জন্যে ।
ব্যাংকশাল কোর্টে মামলা শেষ হবার আগেই বাসুদেব, সুভাষ, শৈলেশ্বর আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছিল । সুবো আচার্য প্রদীপের সঙ্গে ত্রিপুরায় পালিয়ে গিয়েছিল ; প্রদীপ গ্রেপ্তার হতে ত্রিপুরার এক গ্রামে গিয়ে স্হানীয় কবির বাড়িতে লুকিয়ে ছিল সুবো । ব্যাংকশাল কোর্টে আমার দণ্ডাদেশ হবার পর ফিরেছিল । ত্রিদিব মিত্রর চিঠি থেকে জানতে পারলুম ওরা “ক্ষুধার্ত” নামে একটা পত্রিকা বের করার তোড়জোড় করছে যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমাকে, দেবী রায়কে, ত্রিদিব মিত্রকে, আলো মিত্রকে, অনিল করঞ্জাই, করুণানিধান মুখোপাধ্যায়, শম্ভু রক্ষিত আর সুবিমল বসাককে বাদ দেয়া । এদিকে বাসুদেব আর সুভাষ তখন “মানবতা” “সৌহার্দ্য” “বিশ্বপ্রেম” ইত্যাদি নিয়ে বুকনি ঝেড়ে বেড়াচ্ছে, অথচ নিজের পত্রিকা থেকে বন্ধুদেরই বাদ । জানিনা কেমনধারা মানবতাবাদ ছিল সেটা । পরে ওরা নিজেদের চারিপাশে অনেক চেলা যোগাড় করে ফেলেছিল, নিজেদের বউদেরও হাংরি আন্দোলনের অন্তর্গত করে ফেলেছিল । সম্ভবত ওদের মানবতাবাদ ছিল পরিবারতান্ত্রিক, যা কিছুকাল পরেই দেখা দিল পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে । ঘোষভাইরা গোরু-শুয়োরের মাংস খেতে চাইতো না, আমরা খাবার পরিকল্পনা করলেই কেটে পড়তো । ১৯৬৪ সালে একবার হাওড়া স্টেশানে লোকাল থেকে শৈলেশ্বরকে নামতে দেখে চেঁচিয়ে ডাকলুম ওকে, ও আমাকে দেখতে পেয়েই প্ল্যাটফর্মের অন্য দিকে যে ট্রেনটা ছাড়ছিল তাতে উঠে পড়ল ।
হাইকোর্টে কেস ঝুলে থাকার সময়ে কলকাতা থেকে পাটনা ফিরলুম, কেননা রিভিশন পিটিশনের শুনানি কবে হবে তার নিশ্চয়তা নেই, একমাসে হতে পারে আবার চার বছরও লাগতে পারে । একাকীত্বকে সম্ভবত উপভোগ করা শুরু করেছিলুম, কিংবা তখন থেকে একাকীত্ব আমার মগজের দখল নিয়ে নিয়েছিল । জীবনানন্দ কী করে একাকীত্বকে সামলাতেন ? কবিতার পর কবিতা, উপন্যাসের পর উপন্যাসে লুকিয়ে ফেলতেন ।
শরীরও খারাপ হয়ে আসছিল, কলকাতায় কোর্ট আর এর বাড়ি তার বাড়িতে রাত কাটিয়ে, পাইস হোটেলে খেয়ে । জ্বর দেখা দিচ্ছিল মাঝে-মধ্যে । বাড়ির ডাক্তার অক্ষয় গুপ্তকে দেখাতে গেলুম । উনি স্হানীয় আর কলকাতার কাগজপত্রে আমার সম্পর্কে খবর পড়ে, ছবি দেখে, নাড়ি দেখার বা জিভ দেখার বা রক্ত পরীক্ষা করার কথা বললেন না । সোজা পেনিসিলিন অয়েল ইনজেকশান প্রেসক্রাইব করে দিলেন । যে কমপাউণ্ডারের কাছে একদিন অন্তর পোঁদে ইনজেকশান নিতে যেতুম সে জিগ্যেস করল, এই রোগ বাধালেন কী করে ?
—এই রোগ মানে কী রোগ ?
—যৌন রোগ ?
—ওহ, আর ইনজেকশান দিতে হবে না ।
অক্ষয় ডাক্তার ধরেই নিয়েছিলেন যে আমি নির্ঘাৎ যৌন রোগ বাধিয়েছি ।
উনত্রিশ
পাটনা ফিরেছি জানতে পেরে অফিসের দুই সহকর্মী এরিক পেজ আর মামুদ জোহের দেখা করতে এসে বলল, আরে, মন খারাপ করার কি আছে, কলকাতার বন্ধুরা ল্যাঙ মেরেছে তো কি হয়েছে, আমরা তো আছি, চল, আমরা যাচ্ছি ট্রিপে, তুই তো যাসনি কখনও, ভালো ছেলে সেজে এড়িয়ে যেতিস, চল, মন ভালো হয়ে যাবে । এরিক পেজ আর মামুদ জোহেরদের দলটার কথা আমি লিখেছি “ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস” উপন্যাসে । ওদের একটা নারী-নারকো গ্যাঙ বা না-না গ্যাঙ ছিল । আমি ওদের কথায় রাজি হয়ে গেলুম অংশ নেবার জন্যে, কিন্তু জানিয়ে দিলুম যে আমি টাকাকড়ি দিতে পারব না, হালত একেবারে খাস্তা । অতনু চরিত্রের ওপর চাপিয়ে দিয়েছি এই ঘটনা সংক্রান্ত আমার নিজের অভিজ্ঞতা ।
মামুদ জোহেরের ছিল জানলায় সানফিল্ম লাগানো ফিকে নীল রঙের ম্যাটাডর ভ্যান, ড্রাইভারের পেছনে সানমাইকার দেয়াল । পেছনে কি চলছে দেখা যায় না । পেছনে, দুদিকের সিট টানলে সোফা কাম বেড । ম্যাটাডরে ফার্সট এইড বাক্সে অ্যালুমিনিয়াম পাত, চামচ, ডিস্টিলড জল, সুঁই নেবার পিচকিরি, কাঁচি, লাইটার, টয়লেট পেপার, তুলো, বিদেশি কনডোম । শনিবার-শনিবার ওদের দলটা হল্লাবোল করতে বেরোতো । কেরানি, অফিসার, নোট এগজামিনার অনেকে ছিল ওদের দলে। সন্ধে নাগাদ কোনো হাফগেরস্হ যুবতীকে এই কড়ারে তুলে আনতো যে কয়েকজন তার সঙ্গে ম্যাটাডরের বিছানায় রতিভ্রমণ করবে তারপর তার আস্তানায় ছেড়ে দেয়া হবে কাজ শেষে । আমি ওদের দলে এতোকাল যোগ দিইনি কেননা লেখালিখির পক্ষে ব্যাপারটা বেশ ডিসট্র্যাকটিং । লেখালিখি মগজ থেকে প্রায় উবে গিয়েছিল ; রাজসাক্ষী শৈলেশ্বর, সুভাষের প্রতি সেসময়ে ঘৃণায় কলম ধরার ইচ্ছেটাই চলে গিয়েছিল । ক্রমশ লেখালিখিই ছেড়ে গেল, কেবল আমার নয়, ত্রিদিব মিত্র, করুণানিধান মুখোপাধ্যায়েরও । বেনারসের বাঙালিদের বাংলা বুলিতে করুণা “ক্ষুৎকাতর সানপাকু” নামে আত্মজীবনী লেখা আরম্ভ করেছিল । ১৯৭০ নাগাদ করুণা-অনিল যখন নকশাল আন্দোলনের দিকে ঝুঁকলো, তখন পুলিশ ওদের আস্তানা আর স্টুডিওর সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল, ওরা অবশ্য তার আগেই বেনারস ছেড়ে পালিয়েছিল।
মামুদ জোহের ভোরবেলা ভ্যান নিয়ে হাজির, রাজগিরে সবাই মিলে যাওয়া হবে, “ক্যাচ মি ইফ ইউ ক্যান” খেলতে আর মদমাংস খেয়ে হুল্লোড় করতে । গাড়ি চলল গোলঘরের দিকে, গোলঘরের পেছনে এক ঘিঞ্জি গলিতে, বেশ গরিব এলাকা দেখেই টের পাওয়া যায়, কালচে কাঠ, ফ্যাকাশে প্লাসটিক, ত্যাবড়ানো টিনের দেয়াল,পুরোনো বাঁশের খুঁটি, আধপচা কাতাদড়ি, খরখরে চুনবালি, চটের পর্দা, উদাসীন বুড়ো, টিন নিয়ে গঙ্গার পাড়ে হাগতে চলেছে যুবক, দাঁতনরত লাল ল্যাঙোট-পরা ষণ্ডা ।
“একজনকে পিক আপ করতে হবে”, বলে মামুদ জোহের চলে গেল বস্তিটার ভেতরে, আর মিনিট পনেরো পরে ফিরে এলো, কালো কাকেশ্বরী কুচকুচে, মানে এতো কালো এর আগে দেখেছি বলে মনে হয় না, ছিপছিপে এক যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে, দুহাত ভরা প্লাসটিকের আসমানি চুড়ি, নাকে ফিরোজা পাথরের বা নকল ফিরোজার নাকছাবি, কালো শিফনের শাড়ি, আসমানি ব্লাউজ, চুলে চাঁপা বেলির মালা, চোখে কাজল বা আইলাইনার চোখ দুটোকে বড়ো দেখাবার জন্যে । সত্যিই, ব্যাংকশাল কোর্টে দিনের পর দিন হাজিরা দিয়ে আর শেষে সাজা পেয়ে, মনে হল যে এই মেয়েটার সঙ্গ কিছুক্ষণের জন্য আমার দরকার । এরকম একটা নোংরা বস্তিতে থেকেও মেয়েটা কতো টাটকা উচ্ছল প্রাণবন্ত সপ্রতিভ চনমনে, যা আমার সেসময়ে বড়োই দরকার ছিল ।
গাড়িতে ঢুকে আমাদের দুজনের মধ্যে ঝপাং করে বসে পড়ল মেয়েটা, ওর ছোঁয়াচে প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে অনুসন্ধিৎসু । মামুদ জোহের মেয়েটিকে হিন্দিতে বলল, ও বাঙালি, তুই ওর সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে পারিস ।
—আপনাকে দেখিনি তো আগে কখনো, কোলের ওপর উড়িষ্যার পিপলিগ্রামের ছিটকাপড়ের রঙিন কাঁধব্যাগ নামিয়ে বলল মেয়েটা, কথায় খাঁটি বিহারি টান ।
— না, ও এই প্রথমবার আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে, আগে আমাদের মনে করত লম্পট, এখন কলকাতায় নানা কাজকারবার করে আমাদের রাস্তায় চলে এসেছে, ওর নাম মলয়, মলয় রায়চৌধুরী, তুই তো মুকখু, কাগজ পড়িস না, নয়তো হিন্দি ধর্মযুগে আর এখানকার সার্চলাইট খবরের কাগজে ওর ফোটো আর খবর দেখতে পেতিস, বলল মামুদ জোহের, হিন্দিতে ।
— আর আমার নাম শেফালি, সবাই আমাকে টু বলে ডাকে । তারপর দুহাতে আমার বাঁ হাতটা ধরে বলে উঠল, আরে, তোমার হাত কতো নরম, তোমার কি হাত ঘামে ? মেয়েটার ছোঁয়ায় আমার প্রায় কান্না পেয়ে গিয়েছিল, সামলে নিলুম, বললুম, তোমার কথায় অমন হিন্দি টান কেন ?
শেফালি বলল, ওর বাবা বিহারি আর মা বাঙালি, কলকাতার চটকলে ওর বাবা মজুর ছিল, বাবার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল মা, তারপর যোগ করল, মা কিন্তু বামুন বাড়ির মেয়ে, হুঁ, বাবারা দেওঘরের বাউড়ি।
—দেওঘরের বাউরিদের কথা জানি, পাণ্ডাদের ফাইফরমাস খাটতো, রান্নাবান্না করত আর যা বাঁচত তা খেতো, বললুম আমি। বললুম না যে কলকাতা থেকে যে সাব ইন্সপেকটার আমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল সেও ছিল বাউরি বা বারোড়ি ।
—আর এখনকার দিনে তোমরা আমাদের খাও, না ? অদ্ভুত লাগল শুনে, এরকম ছটফটে মেয়ে তো কলকাতার বেবিও ছিল না, যার কাছে ডেভিড গারসিয়াকে নিয়ে গিয়েছিলুম আমরা ।
মামুদ জোহের বুঝতে পারল মেয়েটার কথা, জবাবে বলল, মিলনে পর খা লেতা হুঁ, সর সে পাঁও তক।
“হুরররররররররে” বলে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা, আর আমাদের দুজনের কাঁধে হাত দিয়ে নিজের দিকে টানল । মামুদ জোহের বলল, কি করছিস কি, আরেকটু হলেই অ্যাকসিডেন্ট হতো।
রাস্তার ধুলো জানলা দিয়ে এসে মেয়েটার মুখে চুলে ভুরুতে ছেয়ে গিয়েছিল । বললুম, তোমার ভুরু, চোখের পাতা আর চুলে ধুলো জমছে । আমার কথা পুরো হবার আগেই মেয়েটা ওর মুখ আর মাথা মুছে ফেলল আমার বুকে, আমি স্তম্ভিত, বলা যায় স্পর্শমুগ্ধ, জড়িয়ে ধরার ইচ্ছে হচ্ছিল, চুমু খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল, মেয়েটার মুখ থেকে মাছের গন্ধ পেলুম, মাছের গন্ধের চুমুর মতন চুমু হয় না । সামলাতে না পেরে, আচরণে যোগানো সাহসে, জড়িয়ে ধরে খেয়েই ফেললুম চুমু । একটা চুমুতেই যেন ব্যাংকশাল কোর্টের ভুত নেমে গেল।
—নট অ্যালাউড, নট অ্যালাউড, বলে উঠল মামুদ জোহের, ইউ হ্যাভ টু উইন হার ইন টুডেজ গেম।
—আনাড়ি হ্যায় বেচারা, জানে দো, জানে দো, মুঝে প্যার সে বহুত প্যার হ্যায়, জোহেরকে বলল মেয়েটা । তারপর আজকে কতোজন, কোথায় যাওয়া হচ্ছে, কোঅর্ডিনেটর কে ইত্যাদি জিগ্যেস করায় বুঝতে পারলুম যে না-না গ্যাঙের কাজকারবারের সঙ্গে মেয়েটা পরিচিত, প্রায়ই একে সঙ্গে নিয়ে ফুর্তি করতে বেরোয় মামুদ আর এরিক পেজরা । মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইছিলুম কেমনতর হাফগেরস্হ যৌনকর্মী ।
—কি দেখছো গো অমন করে ? জিগ্যেস করে শেফালি বা টু আচমকা আমার নাকে নাক ঠেকিয়ে বলে উঠল, আমাকে দেখছো তো, কখনও এরকম কালো রঙের রাধা দ্যাখোনি, না ? এই নাও, দ্যাখো । তারপর বলে উঠল, তুমি প্রেম-টেম করোনি এখনো ?
—আরে উ লন্দিফন্দি কা গুরু হ্যায়, এক নম্বরকা লুচ্চা-লফংগা। বলে উঠল মামুদ জোহের ।
—লন্দিফন্দি । চোখে চশমা, এরকম প্যাংলা চেহারা দেখে তো মনে হয় না তুমি লন্দিফন্দির মানুষ । দেখবো অখন একদিন, তোমার চান্সও আসবে, পালিয়ে তো আর যাচ্ছি না, বলল শেফালি ।
—আমরা কোথায় যাচ্ছি ? কেমনধারা বন্দোবস্ত ? জানতে চাইল কালো মেয়েটা, কৃষ্ণকলি কোনো মেয়ের নাম হলে এর নাম তার চেয়েও কালো কিছু হবে, এতো কালো তবু আমার নিরাময়ের কাজ করছিল মেয়েটা, ভুলিনি আজও, কাউকে-কাউকে নিখুঁত মনে থাকে, কৌমার্যের বিকার থেকে মুক্ত করে দ্যায় তারা, রক্ষণশীলতার ভয় থেকে যে ক্লীবত্ব জন্মায় তা থেকে ছাড়িয়ে আনে, যৌনবিকারই সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলে, তাই হয়তো জমিদারদের ছিল বৌবাজার, রক্ষিতা, সম্রাটদের ছিল বাঁদি, ক্রীতদাসী । আমার পক্ষে অ্যাডজাস্ট করা কঠিন হয়ে চলেছে চারিদিকের ঘটনার সঙ্গে ।
জোহের আগেই জানিয়ে দিয়েছিল যে প্রথমে রাজগিরে গিয়ে সবাই জড়ো হবে দেবেন্দরের বাবার পেল্লাই বাড়িতে, সেখানে এক রাত হইচই করে কাটিয়ে পরের দিন খেলতে যাওয়া হবে নালান্দার ধ্বংসাবশেষে । তখনও নালান্দার ধ্বংসাবশেষকে এখনকার মতন সাজিয়ে তোলা হয়নি । শেফালি ঢুকে যাবে আগে, তারপর পুরো দলটা ঢুকে ওকে খোঁজার চেষ্টা করবে । যে প্রথম খুঁজে পাবে তার সঙ্গেই রাতটা কাটাবে শেফালি, দেবেন্দরের রাজগিরের বাড়ির পালঙ্কে, অন্য সবাই মদ-মাংস খেয়ে মাতলামি করবে, কিংবা গ্রাম থেকে দেবেন্দর কয়েকজন বউকে এনে রেখেছে, ওদের বাড়ির পুরুষদের রাখেল, তাদের সঙ্গে ইচ্ছে করলে শুতে পারে ।
আমি মেয়েটার কাছ থেকে যা পাবার পেয়ে গিয়েছিলুম, নালান্দার ধ্বংসাবশেষের ভেতরে ঢুকে ছায়ায় বসে রইলুম আর দেখলুম সহকর্মীদের দৌড়ঝাঁপ, শেফালিকে খুঁজতে হন্যে হয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে । অভিজিৎ জিতেছিল । আমি কেবল গেঁজিয়ে ছিলুম মেয়েটার সঙ্গে ডাইনিং টেবিলে । পরের বার ওরা খেলতে গিয়েছিল শোনপুর মেলায়, আমি যাইনি, কেননা খেলাটা বেশ ক্লান্তিকর, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দুদিন ধরে হেদিয়ে বেড়ানো । শোনপুর মেলায় যে জিতেছিল সেই সহকর্মী যৌন-নৌকোবিহারের নৌকো থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল ।
তিরিশ
হাতে তো অফুরন্ত সময়, ব্যাংকশাল কোর্টে সাজা আর হাইকোর্টে কেস ওঠার সময় পর্যন্ত । হাংরি আন্দোলন সূত্রেই পরিচয় হয়েছিল দুজন আর্টিস্টের সঙ্গে, করুণানিধান মুখোপাধ্যায় আর অনিল করঞ্জাই। ওরা বেনারসে থাকত । ওদের ডাকে চলে গেলুম বেনারসে, হিপি-হিপিনীদের জমঘটে । গাঁজা, চরস, আফিম, এলএসডি মাখানো ব্লটিং পেপার । করুণানিধান বললে, হ্যাঁ-হ্যাঁ, হিপিনীদের, যাদের পুরুষ সঙ্গী নেই তাদের চুমু খাবার প্রস্তাব দিতে পারো, ওদের কাছে এলএসডি ক্যাপসুলও পাবে বাহাত্তর ঘণ্টার ট্রিপের, তখন তোমার সঙ্গে হিপিনীটা কী করছে টের পাবে না । আমি চাইছিলুম ফরাসি বা জাপানি কোনো যুবতীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে । করুণা বললে, সবকটা মার্কিন মেয়ে, যেসব ছেলেগুলো ভিয়েতনাম যুদ্ধ এড়াতে নানা ক্যারদানি করেছে তাদের সঙ্গে পোঁ ধরে এসেছে আর বদলা-বদলি করেছে বা ছেড়ে দিয়েছে । করুণার সুবিধে ছিল যে ও ইংরেজি জানতো না, হিন্দি-ইংরেজি মিশিয়ে দোভাষী থেকে প্রেমিকে পালটে নিতে পারতো নিজেকে। দ্বিতীয়ত গাঁজা, চরস আর আফিম মিশিয়ে করুণা একটা কনককশান তৈরি করে চারমিনারে ভরে বেচতো হিপিদের, আর হিপিরা তা পাবার জন্যে ওর করায়ত্ত হয়ে গিয়েছিল বলা যেতে পারে । আমি এর কিছুটা হদিশ দিয়েছি “অরূপ তোমার এঁটোকাঁটা” উপন্যাসে।
নতুন ধরণের প্রেমের সঙ্গে পরিচিত হলুম, যেখানে দুপক্ষই জানে যে এই সম্পর্কের নিশ্চিত এক্সপায়ারি ডেট আছে, সারা জীবন বইতে হবে না, মন ভরে গেলে ছেড়ে দাও, বাতাসে যৌবনের মাংসল মাদকের গন্ধ । আমাকে এই পরিস্হিতি ক্রমশ গিলে ফেলতে আরম্ভ করেছিল, সাপের মতন একটু একটু করে গোলাপি অন্ধকারে, স্নান না করা দেহের সুবাস আর বহুদিন না-কাচা পোশাকের সোঁদা স্বর্গীয় সুষমা । সবচেয়ে ভালো লেগেছিল একজন হিপিনীর বগলের সোনালী চুল ; আগে ধারণা ছিল না যে বগলের চুলও সোনালী হয়, চুলের গহ্বরে ভালোবাসার নাচ, গর্ভনোরিধক বড়ি না বেরোলে বোধহয় যুবতীরা হিপিনী হয়ে বাড়ি ছাড়তো না । হিপিনীসঙ্গ করে যে সারকথা মগজে ঢুকেছে তা হলো দুটো দেহের মাঝে পারফিউম ব্যাপারটা বিকৃতির দেয়াল ।
করুণা-অনিল যখন কাঠমাণ্ডু থেকে ফিরে আমাকে ওদের সঙ্গে বেনারসে নিয়ে গিয়েছিল, মোটা যুবতী ম্যাডেলিনের সঙ্গে সময় কাটিয়ে, আর তার আগে কাঠমাণ্ডুতে ক্যারল নোভাকের সঙ্গে স্লিপিংব্যাগে ঢুকে বুঝতে পেরেছিলুম যে লেখালিখি সম্পর্কে হিপিদের তেমন আগ্রহ নেই যেমন ছিল বিটনিকদের, যদিও বিট আন্দোলনের ফলেই ওদের আবির্ভাব, সাইকেডেলিক সঙ্গীত, ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধীতা, যৌনবিপ্লব, মাদক বিশেষ করে গাঁজা, এল এস ডি আর ম্যাজিক মাশরুম, হিন্দু আর বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহ, খ্রিস্টধর্মকে পরিত্যাগ, ভালো খাওয়া, গান্ধির অহিংসা, সাংস্কৃতিক মতবিরোধ ইত্যাদির জন্যে সেসময়ের বেনারস আর কাঠমাণ্ডু ছিল উপযুক্ত শহর । শহরবাসীরা তাদের কাজকারবার নিয়ে চিন্তিত ছিল না, এমনকি রাস্তায় দাঁড়িয়ে চুমু খেলে, জড়িয়ে ধরলেও গা করতো না কেউ। এখন অবশ্য ভয়ংকর অবস্হা । সেসময়ে করুণা একজন যুবতীর সঙ্গে গঙ্গার অপর পাড়ে চড়ায় গিয়ে খড়ের ছাওয়া-পোঁতা বাঁশের খুঁটির কুটিরে থাকতো, দুজনেই একেবারে উলঙ্গ, “প্রিহসটরিক লাইফে”, অবাক হয়ে গিয়েছিলুম নৌকো থেকে নেমে। করুণা উলঙ্গ জীবনের ফোটোও তুলেছিল একাধিক, নিজের বউকেও দেখিয়েছিল সেসব । ওর বউ সম্ভবত বিরোধিতা করেনি, নিয়মিত রোজগার হচ্ছে মনে করে, কেননা করুণা তার আগে বইয়ের মলাট এঁকে টায়েটুয়ে সংসার চালাতো ।
কলকাতা থেকে, ব্যাংকশাল কোর্টে সাজা পেয়ে আর হাইকোর্টে রিভিশন পিটিশন করে, আমি পাটনায় ফিরে আসার কিছুদিন পর করুণা কাঠমাণ্ডু থেকে আহ্বান পাঠালো, “শিগগির চলে এসে অফুরন্ত চরস আর মেয়েছেলে, খামের ভেতরে কিছুটা আফগানি চরস আছে”। খামের ভেতরে ছিল হাই কোয়ালিটি চরস । এখন হলে তো জেল হয়ে যেতো । তখন সরকারি দোকানে সত্যমেব ছাপমারা পুরিয়াতে পাওয়া যেতো, অ্যালেন গিন্সবার্গ যখন এসেছিল, ওকেও নিয়ে গিয়েছিলুম সরকারি দোকানে ।
কাঠমাণ্ডু যাবার আগে রাজকমল চৌধুরী, হিন্দি কবি, আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ওর গ্রামে মাহিষিতে। ফণিশ্বরনাথ রেণু বলেছিলেন, ওর গ্রামে ছিন্নমস্তাদেবীর পুজোর সময়ে যেও, একেবারে পাগল হয়ে যাবে । সত্যিই উন্মাদনা । পুজোর সময়ে মোষ বলি দেয়া হয়েছিল, যারা মানত করেছিল, সকলেই মোষ বলি দেবার জন্য এনেছিল, দেখে আমার বমি পাবার যোগাড়, রাজকমলের দেয়া পানীয় খেয়ে সামলালুম, আর সবাই মৈথিলি গান গাইতে-গাইতে গায়ে-মুখে রক্ত মেখে যেভাবে নাচছিল, আমিও দু’হাত তুলে নাচলুম । পানীয় আর নাচের দৌরাত্ন্যে সন্ধ্যাবেলা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম, এরকম সমবেত ফ্রি ফর অল নাচ, আগে নাচিনি কখনও ।
অ্যালেনের কথাটা আগে বলে নিই তারপর কাঠমাণ্ডুতে করুণার আস্তানায় যাবো । গিন্সবার্গ এসেছিল ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসের গরমে, মাথায় সিঁদুরের টিপ, গঙ্গায় স্নান করে, কাঁধে গামছা, আর বাবাকে হিন্দিতে জিগ্যেস করেছিল, “মলয় হ্যায়” । রোদে পুড়ে ওর গায়ের রঙ তামাটে হয়ে গিয়েছিল বলে বাবা ভেবেছিলেন কোনো সন্ন্যাসী, কেননা মাঝে আনন্দমার্গের কয়েকজন সন্ন্যাসী এসে ঢুঁ মেরেছিল ওদের পত্রিকায় আমার লেখার জন্য, তখন তাদের ভাগিয়েছিলুম । বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন, অ্যালেন নিজের পরিচয় দিতে, নিয়ে গেলুম ওপরে আমার ঘরে । সত্যি বলতে কি তখনও পর্যন্ত আমি বিট আন্দোলনকারীদের বিষয়ে তেমন জানি না, গিন্সবার্গের নাম দাদার কাছে শুনেছি, কাগজে পড়েছি, কিন্তু “হাউল” কবিতার কথা শুনিনি । “হাউল” আর “ক্যাডিশ” আমাকে পাঠিয়েছিল লরেন্স ফেরলিংঘেট্টি, গিন্সবার্গ ফিরে যাবার পর, “ক্যাডিশ”এর লঙ প্লেইং রেকর্ডও পাঠিয়েছিল, যেটা শুনে অনুবাদ করতে সুবিধা হয়েছিল । ম্যাগাজিন ইত্যাদি পরে পাঠিয়েছিল হাওয়ার্ড ম্যাককর্ড, আর সেই সূত্রে বেশ কয়েকজন সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল যারা আমার লেখা প্রকাশ করা আরম্ভ করেছিল ।
গিন্সবার্গ যখন এসেছিল তখন আমাদের বাড়িতে ডাইনিং টেবিল আর বসবার সোফাসেট ছিল না । আমার ঘরে সিলিং ফ্যান ছিল না । মা ওকে মেঝেয় আসন পেতে খেতে দিতেন আর ওর সঙ্গে বাংলা-হিন্দিতেই কথা বলতেন, গরম বলে সামনে বসে হাতপাখায় হাওয়া করতেন । পাটনা দেখার জন্য রিকশা ভাড়া করলুম ; গিন্সবার্গ বলল, এই রিকশাঅলাটা আমার বাবার বয়সী, একে দিয়ে রিকশা টানিয়ে তাতে বসে থাকতে বেশ অপরাধ হচ্ছে । রিকশঅলাকে আমার পাশে বসিয়ে নিজেই রিকশ টানতে আরম্ভ করল, কিছুটা যাবার পর রাস্তায় একজন কন্সটেবলকে দেখে রিকশঅলা বলল, বাবু ওই দেখুন সামনে, আপনি চালাচ্ছেন দেখে ও যদি ধরে তাহলে লাইসেন্স তো যাবেই, হাজতেও পুরে দিতে পারে ।
আমরা স্তুপের আকারের গোলঘরে গেলুম ; স্তুপটা ২৯ মিটার উঁচু, ১২৫ মিটার চওড়া, ওপরে উঠতে ১৪৫টা সিঁড়ির ধাপ। গোলঘর তৈরি হয়েছিল ১৭৮৬ সালে, ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষে লক্ষ-লক্ষ মানুষ বাংলা আর বিহারে মারা যাবার পর, চাল-গম রাখার জন্য, গিন্সবার্গ যখন এসেছিল তখনও চাল-গম মজুত করা ছিল গোলঘরের ভেতরে । এখন অবশ্য বিনোদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। গোলঘরের ভেতরে প্রথমে ঢুকতে দেয়নি কেয়ারটেকার । আমি বললুম যে উনি বিদেশী, তখন ঢুকতে দিল । গিন্সবার্গ ওর “সানফ্লাওয়ার সূত্র” কবিতাটা আবৃত্তি করল । গোলঘরের ভেতরে চেঁচালে একুশবার প্রতিধ্বনি হয়, অবাক গিন্সবার্গ বলল, টেপরেকর্ডার আনলে ভালো হতো । আমার কাছে ছিল না যে পরের দিন এসে রেকর্ড করব। আমাকেও আবৃত্তি করতে বলল আমার কবিতা । আমি আমার কবিতা মুখস্হ রাখতে পারি না । “প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার” কবিতার শেষ চার লাইন যতটুকু মনে ছিল আবৃত্তি করলুম । গিন্সবার্গ বলল, তোমার কন্ঠস্বর আবৃত্তির জন্য বেশ ভালো, রেকর্ড করো না কেন । বললুম না যে গ্যাঁটে তেমন কড়ি থাকে না। গোলঘরের ওপরে উঠলুম, গঙ্গা, গঙ্গার ওপার আর পুরো পাটনা শহর দেখল গিন্সবার্গ । ওপর থেকে বা বাইরে থেকে গোলঘরের ফোটো তুলল না কোনো । আমি নিজেকে কখনও তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করিনি বলে বিখ্যাত লোকেদের পাশে দাঁড়িয়ে ফোটো তোলানো হয়ে ওঠেনি ।
পরের দিন গেলুম গঙ্গার পাড়ে, মহেন্দ্রু ঘাটে, তখনকার দিনে বাচ্চাবাবুর জাহাজ ওই ঘাট থেকে ওপারে শোনপুরে যেতো, এখন তো গঙ্গার ওপর পোল তৈরি হয়ে গেছে, বাচ্চাবাবুর জাহাজও চলে গেছে অন্য কোথাও । কিছুক্ষণ জাহাজে ঘোরাফেরা করার পর ফেরার রাস্তায় ভিকিরিদের আস্তানাগুলোর ফোটো তোলা আরম্ভ করল গিন্সবার্গ, খোঁড়া, নুলো, জটাজুট, কুষ্ঠরোগি, রাস্তায় চিৎ হয়ে পড়ে থাকা প্যাংলা চেহারার লোক, ইত্যাদি । ফিরে, ফিল্মটা বাবাকে ডেভেলাপ করতে দিয়েছিল । বাবা ডেভেলাপ করার পর পুরো ছত্রিশটা ছবি দেখে খেপে গেলেন, গিন্সবার্গকে বললেন, তোমরা বিদেশিরা কবি হও বা ট্যুরিস্ট, ইনডিয়ায় এসে কেবল এই সবই দেখতে পাও, ভালো কিছু দেখতে পাওনা, ফিরে গিয়ে এগুলো নিয়ে ব্যবসা করবে। গিন্সবার্গকে পরে আমি বললুম যে এবার তোমার ফিল্ম অন্য দোকানে ডেভেলাপ প্রিন্টিং করতে দিও । গিন্সবার্গ ছবি তুলে ডেভেলাপ করিয়ে তাড়াগুলো পাঠিয়ে দিতো ওর সৎমাকে, তিনি ওর পাঠানো যাবতীয় জিনিস দেশ অনুযায়ী আলমারিতে সাজিয়ে রাখতেন, তাই কিউরেটার বিল মরগ্যান, যে আমার সঙ্গে নাকতলায় দেখা করতে এসেছিল, তার সুবিধা হয়েছিল । তবে বাবা যা আঁচ করেছিলেন দেখলুম তা সত্যি, ওর “ইনডিয়া জার্নালস” বইতে ওই সমস্ত নুলো, খোঁড়া, জটাজুটদের ফোটো পাতার পর পাতায় ।
তার পরের দিন ওকে নিয়ে গেলুম পাটনা মিউজিয়ামে, কতো বছর পর, মিউজিয়ামের ঘরগুলো আমার চেনা, এখানে বড়োজ্যাঠা চাকরি করতেন, গিন্সবার্গ ঘুরে-ঘুরে দেখলো । মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে খুদাবক্স লাইব্রেরি । হাতে লেখা ফার্সি বইগুলো দেখলো গিন্সবার্গ । অবাক হয়ে গেল দেখে যে আকবরের সমাধির বাইরে তিনটে মাছের দেহ আর তার একটা মাথার যে ড্রইং ও নিজের খাতায় তুলে এনেছে তা খুদাবক্স লাইব্রেরির একটা বইয়ের মলাটে রয়েছে, গ্রন্হাগারিক জানিয়েছিল যে বইটা আকবরের লেখা “দীন-ই-ইলাহি”। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান সহপাঠীরা আকবরের এই বইটার প্রসঙ্গ উঠলেই কটু সমালোচনা করত ।
পাটনায় ওকতাভিও পাজও এসেছিলেন, আমাদের বাড়ি, কিন্তু তাঁর সঙ্গে ডিসট্রিক্ট ম্যাজিসট্রেট আর পুলিশের গাড়ি থাকায় কোনো সাহিত্য আলোচনা হয়নি । উনি চা-বিস্কুটও খেতে চাইলেন না, হয়তো রাষ্ট্রদূতের প্রোটোকল । বাড়িতে পুলিশের গাড়ি আর কয়েকজন বন্দুকধারী দেখে পাড়ার লোকে ভেবেছিল, “ফির সে সরকারকে খিলাফ কুছ লিখা হোগা।” ওকতাভিও পাজ কলকাতায় গিয়ে আমাদের খোঁজ করেছিলেন । বাইরে থেকে কবি-লেখকরা কলকাতায় এলে কনসুলেটগুলো আনন্দবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ করত, আর সন্তোষকুমার ঘোষ তাদের পাঠিয়ে দিতেন নিজের পেটোয়া তরুণ কবি-লেখকদের কাছে; পরে এই একই ট্যাকটিক ধরেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নিজের একটা পেটোয়া ব্যাটালিয়ানই তৈরি করে ফেলেছিলেন ।
মুম্বাই যখন বোম্বে ছিল, তখন এদোয়ার্দো কার্দেনাল-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ; উনি এসেছিলেন ভারত সরকারের অতিথি বিদেশি কবিদের দলের সঙ্গে । আমি কেবল ওনার নামই জানতুম । প্রথমে এয়ারপোর্টে আর তারপর ওনার হোটেলে গিয়ে দেখা করেছিলুম । বলেছিলেন লরেন্স ফেরলিংঘেট্টির ‘সিটি লাইটস জার্নাল’-এ আমার কনট্রোভার্সিয়াল কবিতাটা পড়েছেন । ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ কবিতার অনুবাদ ‘স্টার্ক ইলেকট্রিক জিজাস’ প্রকাশিত হয়েছিল আরও কয়েকটা কবিতার সঙ্গে । আমি তখনও ওনার কবিতা বিশেষ পড়ে উঠিনি । ভারত সরকারের প্রতিনিধি তাগাদা দিতে উঠে পড়তে হয়েছিল ।
আশির দশকে লখনউ-মুম্বাইতে থাকার সময়ে শিলিগুড়ির অলোক গোস্বামী আর রাজা সরকার যোগাযোগ করেছিলেন, জানিয়ে যে কলকাতায় মরে-যাওয়া হাংরি আন্দোলনকে তাঁরা উত্তরবঙ্গে জিইয়ে তুলেছেন, “কনসেনট্রেশান ক্যাম্প” আর “ধৃতরাষ্ট্র” পত্রিকার মাধ্যমে । উত্তরবঙ্গে তাঁরা দুজনে এবং মনোজ রাউত, সমীরণ ঘোষ. পল্লবকান্তি রাজগুরু, চন্দন দে, বিজয় দে, সমর রায়চৌধুরী, শ্যামল সিংহ, দিবাকর ভট্টাচার্য, ত্রিদিব চক্রবর্তী, দীপঙ্কর কর, প্রবীর শীল, রতন নন্দী, কিশোর সাহা, কুশল বাগচি, সুমন্ত ভট্টাচার্য, মলয় মজুমদার প্রমুখ বেশ হইচই ফেলে দিয়েছেন । তাঁরা যে হাংরি আন্দোলনের পালে নতুন হাওয়া আনছেন তা সহ্য হল না শৈলেশ্বর ঘোষের, উত্তরবঙ্গে গিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে পত্রিকাগুলোর বারোটা বাজিয়ে দিলে । শৈলেশ্বরের মনে হয়ে থাকবে যে উত্তরবঙ্গের যুবক কবি-লেখকরা সব লুটেপুটে খেয়ে নিচ্ছে, হাংরি আন্দোলন বুঝি বেহাত হয়ে গেল । সুভাষ ঘোষকেও পিটুনি খেতে হয়েছিল শৈলেশ্বর ঘোষের চামচাদের হাতে, একই কারণে । মানে ‘ক্ষুধার্ত’ পত্রিকাও দুই ভাগ হলো ।
যাক, এবার ফিরে আসি করুণার কাঠমাণ্ডু নিমন্ত্রণে । বাচ্চাবাবুর জাহাজে করে শোনপুর, সেখান থেকে ট্রেনে করে রকসওল । ট্রেনটা ছিল অন্ধকার, একজন হুঁশিয়ারি দিয়ে গেল ‘সবকোই আপনা সামান অপনে সাথ রখিয়ে’ । সামান বলতে থলেতে দুটো প্যান্ট দুটো বুশশার্ট আর টুথব্রাশ-পেস্ট, চুমু খাবার সুযোগ পেলে রোজ দাঁত মাজতে হবে বলে, ওয়াচ পকেটে টাকা । সঙ্গে ছিল দাদা সমীর, সুবিমল বসাক আর বেনারসের কাঞ্চনকুমার মুখোপাধ্যায় যে পরে নকশাল আন্দোলনে যোগ দেবার ফলে প্রথমে বেনারসের আর পরে কলকাতা পুলিশের নেকনজরে পড়েছিল । ওর ছোটোভাই ছিল কলকাতা পুলিশে, ওর নকশাল সক্রিয়তার জন্য ভাইকে চাকরি ছেড়ে দিতে হয়েছিল । হাংরি আন্দোলনের সময়ে যখন মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না তখন কাঞ্চনের ভাইয়ের পুলিশ কোয়ার্টারে, ভবানী ভবনের পেছনে, দু’রাত কাটিয়েছিলুম।
একত্রিশ
রকসওলে পৌঁছে এক্কাগাড়িতে চেপে আন্তর্জাতিক গেট পেরিয়ে ঢুকলুম বীরগঞ্জে ; কাঠমাণ্ডু যাবার বাসের টিকিট আগেই কিনে নেয়া হলো যাতে না পেছনে বসতে হয় । ভারতের দিকের রাস্তাটা একেবারে উবড়োখাবড়া, এখন জানি না কেমন । তবে নেপালে ঢুকে বোঝা গেল ওদের রাস্তাটা ভালো । হাতে সময় ছিল বলে গহওয়া মাই মন্দির দেখতে গেলুম, দুর্গার মন্দির ছিল সম্ভবত, সেখানে ছায়ায় বসে, বেরিয়ে রেস্তরাঁয় খেয়ে বাসে চাপলুম । শোনপুর থেকে ভোজপুরি বুলিতে কথা আরম্ভ হয়েছিল তা চলল বীরগঞ্জ পেরিয়ে অমলেখাগঞ্জ আর হেতারতা পর্যন্ত, সর্বত্র মারোয়াড়িরা ব্যবসা দখল করে ফেলেছে, কর্মচারীরা বিহারি, নেপালিদের কথায় মধেশি । বাসে কাঞ্চনের বমি হল কয়েকবার, ওর পেছনের একজন নেপালি বউ ওর কাঁধে হাত দিয়ে পেছন ফিরে হাঁ করতে বললে কাঞ্চন কোনো প্রশ্ন না তুলে বউটার দেয়া সাদা গুঁড়ো খেয়ে নিল, বউটা বলল, আর বমি হবে না । নেশার কিছু ছিল সম্ভবত, কেননা কাঞ্চন তারপর সারাটা পথ ঝিমিয়েছে, নদীর পাশ দিয়ে, ত্রিভূবন রাজপথের দৃশ্য দেখার সুযোগ পায়নি ।
করুণা অপেক্ষা করছিল বাসস্ট্যাণ্ডে, ওর পেছন-পেছন আমরা চললুম, গিয়ে ঢুকলুম একটা বিরাট চালাবাড়ি চত্ত্বরে, তিনতলা চালাবাড়ি চত্ত্বর, প্রায় একশো মিটার দৈর্ঘ্য আর পঞ্চাশ মিটার প্রস্হ, একটা সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকতে হল, যেটা সব সময় খোলাই থাকে, কখনও হয়তো খোলা-বন্ধর রেওয়াজ ছিল। বাঁশের পাকানো সিঁড়ি দিয়ে উঠলুম দুতলায়, করুণা আগেই বন্দোবস্ত করে রেখেছিল একটা ঘর, মেঝেতে খড়ের ওপর চাদর পাতা বিছানা, বালিশ নেই, ভাড়া মাথাপিছু মাসে একটাকা । পাড়াটার নাম ঠমেল । চারিদিকে সরু-সরু গলি, বেরোতে আর ঢুকতে গোলমাল হয়ে যেতো অনেক সময়ে । বাড়ি চত্ত্বরে একশো জনেরও বেশি ভাড়াটে, তার মধ্যে হিপি-হিপিনীই বেশি । করুনা জানালো, হাংরি আন্দোলনের নাম করে নেপালি সাহিত্যিক বাসু শশীর সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, আমাদের খাবার খরচ নেপালি সাহিত্যিকদের সংস্হা দেবে, থাকার খরচ আমাদের যার-যার । একটা রেস্তরাঁয় গিয়ে খেতুম আর রেজিস্টারে সই করে দিতুম । তবে প্রতিদিন রেস্তরাঁয় খাবার দরকার হতো না, কেননা পাটন, ভক্তপুর, ভরতপুর, পোখরা ইত্যাদি জায়গা থেকে কবিতা পাঠের বা আড্ডার নেমন্তন্ন আসতো, রাতে থেকেও যেতে হতো কখনও-সখনও ।
কাঠমাণ্ডু থেকে বিভিন্ন্ জায়গায় যাতায়াতের জন্যে পেয়ে গিয়েছিলুম একজোড়া হিপি-হিপিনী, তারা একটা ম্যাটাডর ভ্যান লিজ নিয়ে স্কুলের বাচ্চাদের বিনি পয়সায় স্কুলে পৌঁছে দিতো, আমাদেরও পৌঁছে দিতো বিভিন্ন শহরে কবি-লেখকদের জমঘটে । পড়তুম “প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার”-এর ইংরেজি অনুবাদ “স্টার্ক ইলেকট্রিক জিজাস” চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে । নেপালি ভাষায় অনুবাদও করেছিল রমেশ শ্রেষ্ঠ নামে একজন কবি, সে এখন ব্যাংককে থাকে, একজন থাই যুবতীকে বিয়ে করে । থাইল্যাণ্ডের খাবারের বেশ প্রশংসা করে অনেকে, আমার কিন্তু বিস্বাদ লাগে । তার চেয়ে মুম্বাইতে মহেশ লাঞ্চ হোমের অক্টোপাসের বড়া খেতে ভালো লাগে।
কবিতা পাঠের আসরগুলোয় নানা রকমের চোলাই করা নেপালি আর নেওয়ারি দিশি মদ খাবার সুযোগ হয়েছে, খেয়ে মাতাল হবার সুযোগ । যেমন রাক্সি, বেশ নেশা হয়, ভোদকার মতন স্বচ্ছ, চাল পচিয়ে তৈরি, খেতে অনেকটা জাপানি সাকের মতন, জাপানে যাইনি যদিও, সাকে খেয়েছি থাইল্যাণ্ডে । তারপর আরা, চাল ভুট্টা গম পচিয়ে । আয়লা, চাল আর জোয়ার পচিয়ে । ছাং, জানি না কি পচিয়ে । তোংবা, জোয়ার পচিয়ে । আয়লা হল নেওয়ারি মদ, কবি পারিজাতের বাড়িতে খেয়েছিলুম, উনি নেওয়ারি, শিলিগুড়িতে ওনার মূর্তি আছে । মোষের কাঁচা মাংস খেয়েছি কয়েক জায়গায়, হরিণের মাংসের আচার । আর হ্যাশিশ তো বটেই, প্রায় প্রতিদিন, যে কোনো মন্দিরে সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে বুড়োদের জমায়েতে বসলেই, ছিলিম ঘুরে চলে আসতো, তিনচার ফুঁক দিলেই আকাশে ওড়া আরম্ভ ।
সুবিমল বসাক, কাঞ্চন আর দাদা ফিরে যাবার পর আমি থেকে গিয়েছিলুম । করুণা বলেছিল ওদের চলে যেতে দাও, তোমার কথা এখানে চাউর করে রেখেছি, অনেকে টাইম ম্যাগাজিনের খবর জানে আর গিন্সবার্গের বন্ধু শুনে তোমার বসার সিংহাসন তৈরি করে রেখেছে । বাড়িটার সিঁড়ি এমন ছিল যে হ্যাশিশের নেশা করে ফিরে অনেক সময়ে টের পেতুম না কোন পাক দিয়ে কোন তলায় উঠে যাচ্ছি । একবার এরকম পাক দিয়ে উঠলুম আর নামলুম, কয়েকবার অমন ওঠানামার পর একটা ঘরের দরোজার নোংরা পর্দা থেকে একজন লাল-ব্লাউজ যুবতীর হাত আমায় ভেতরে টেনে বলল, প্রতিদিন দরোজা ওব্দি আসো আর ফিরে যাও কেন ; তার টানে আর আমার হ্যাশিশাক্ত টলমলে শরীর গিয়ে পড়ল স্বাস্হ্যবতী নেপালিনীর বুকের ওপর । দেখে বুঝলুম ওটা যৌনকর্মীদের দিশি মদের ঠেক ; মদ খাবার মতন অবস্হা ছিল না, যুবতীর গায়ের গন্ধে টেকা দায়, বুকে মুখ গুঁজে একটা নেপালি টাকা দিয়ে বেরিয়ে এলুম । মোঙ্গোলয়েড তরুণীদের আমার চিরকাল ভালোলাগে । পরের দিন হুঁশ এলে ঘরটা আর খুঁজে পাইনি, গোটাকতক সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করেও ।
করুণা পরিচয় করিয়ে দিল কয়েকঘর হিপি-হিপিনীর সঙ্গে, যারা গিন্সবার্গের আর ফেরলিঘেট্টির ভক্ত, ‘সিটি লাইটস জার্নাল’ এর কথা জানে । ওদের ঘরে আড্ডা মারার, হ্যাশিশ ফোঁকার আর এলএসডি ভেজানো ব্লটিং পেপার খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকার স্বাধীনতা পেয়ে গেলুম । একজন ছিল নিউমেরোলজিস্ট, সে বলল আমার নামের যোগফল হল এক, তাই সব ব্যাপারেই তুমি প্রথম সুযোগটা পাবে । সেইদিন রাতেই একটা স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে টেনে নিল আমাকে জনৈকা হিপিনী, তার নাম ক্যারল নোভাক, ঢুকে গেলুম আর একে আরেকের মাথার দিকে পা করে শুয়ে পড়লুম। এটাই আমার জীবনে বিদেশিনীর প্রথম মুখমেহন । করুণা আমাদের দুজনের জন্যে একটা ঘর ভাড়া করে দিলো, আমি আরেকবার হয়ে গেলুম “অরূপ তোমার এঁটোকাঁটা” উপন্যাসের শিশির দত্ত আর ক্যারল নোভাক হয়ে গেল ম্যাডেলিন করিয়েট । জীবনে যৌনতার আহ্লাদ শিখিয়ে গেছে ক্যারল নোভাক আর ম্যাডেলিন করিয়েট। “অরূপ তোমার এঁটোকাঁটা” উপন্যাসে ম্যাডেলিন করিয়েটের মুখে রসুনের ট্যাবলেট খাবার গন্ধের কথা লিখতে ভুলে গেছি । রসুনের স্বচ্ছ ট্যাবলেট, প্রতিদিন একটা ।
মার্কিন যুবতীটি, ক্যারল নোভাক, আমার ‘ভালোবাসার উৎসব’ কাব্যনাট্যে অন্তর্ভুক্ত করেছি । হাংরি আন্দোলনে বন্ধুদের বিশ্বাসঘাতকতার পর একজন বন্ধুনি পাওয়া গিয়েছিল, যার সঙ্গে করুণার ভাষায় ‘চিউউইংগামের মতন’ চিপকে যেতে পেরেছিলুম । দাদা, সুবিমল ওরা চলে গিয়েছিল বলে আরও ফ্রি ফিল করা শুরু করেছিলুম । ফেমিনিজম বা নারীবাদ ব্যাপারটা ওর কাছেই প্রথম জেনেছিলুম, বডিস পরত না, বলত “উওমেন অন টপ”। প্রেমহীন ভালোবাসা, অসাধারণ অভিজ্ঞতা, কোনো প্যানপানানি নেই । বাঙালি প্রেমিকা সংসর্গের সময়ে বলত, “ভালোবাসি, তোমায় ছাড়া বাঁচবো না, এরকম কথা বলো না কেন এই সময়ে, ভাল্লাগবে” । ক্যারল বলত, “জন্তুদের মতন জান্তব আওয়াজ করো না কেন, আমি যেমন করছি”। দুটোর কোনোটাই সম্ভব হয়নি আমার দ্বারা । বলতো, “চুমু খাবার মতন শ্বাসপ্রক্রিয়া আর দ্বিতীয়টি নেই, ঠিক যেন সার্জিকাল ভেন্টিলেটার ।”
করুণা একজন আফ্রকান আমেরিকান যুবতীর সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েছিল, যার পেইনটিঙের গ্যালারি ছিল, সেখানে প্রদর্শনী করলেও করুণার ছবি বিক্রি হয়নি, অনিলের কয়েকটা ছবি বিক্রি হয়েছিল । কেমন করে যে করুণা যুবতীদের আকর্ষণ করতে পারতো তার ক্লুটা জানতে পারিনি । করুণা ওর পেইনটিঙগুলো জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিলে, সেই আগুন ঘিরে রাক্সি খেয়ে নাচলুম আমরা আর সমবেত হিপি-হিপিনীরা, করুণা সকলের কপালে ছাইয়ের তেলক কেটে দিল । সকলে মিলে এলভিসের ‘জেল হাউস রক’ গাইতে গাইতে ঠমেলে ফিরল, গানটার পঁয়তাল্লিশ আর পি এম রেকর্ড ছিল আফ্রিকান-আমেরিকান যুবতী গ্যালারিস্টের কাছে ।
ক্যারল দেশে ফিরে গেলে আমিও ফিরলুম, চিনে ছাপানো মাও-এর একখানা রেডবুক কিনে । ক্যারলের সঙ্গে হুটোপাটিতে আমার চশমা ভেঙে গিয়েছিল । অনিল-করুণা থেকে গেল আরও মাসখানেকের জন্যে । কাঠমাণ্ডুর গ্যাঞ্জামে আর জীবনকাটানোয় আমার লেখালিখি আমাকে প্রায় ছেড়ে চলে গিয়েছিল, হাইকোর্টের রায়ের অপেক্ষা করতে হচ্ছিল । ক্যারলের সংস্পর্শে এটুকু তো জানলুম যে প্রেম সবসময় বিট্রে করে না, ভালোবাসা থেকে যতো পারা যায় শুষে নিয়ে নিজেকে সন্তুষ্ট করে তোলা যায় । সমস্যা হলো যে প্রথম যৌবনে, শরীরের মতন পেলেও, মনের মতন প্রেমিকা পাইনি, বোধহয় এই দুর্ভোগে প্রথম যৌবনে সকলেই ভোগে, তারপর শিক্ষিত হয়ে এগোয় । আসলে আমি কীভাবে বাঁচবো, কীভাবে থাকব, কীভাবে লিখব, তাতে তো কারোর মাথা গলাবার দরকার নেই ।
অনিল করঞ্জাই আর করুণানিধান কাঠমাণ্ডু থেকে পাটনা হয়ে বেনারস ফিরল, আমিও চুলের ইন্সটেলাশান আর্ট নিয়ে ওদের সঙ্গ নিলুম। আমার ভয় ছিল যে অনিল না আমায় একটা পেইনটিং উপহার দিয়ে বসে, কেননা দরিয়াপুরের বাড়িতে উপযুক্ত দেয়াল ছিল না, দোতলায় আমার ঘরে ছাদ থেকে জল চুয়ে দয়নীয় অবস্হা, তার ওপর সারাদিন ট্রাক আর বাস যাতায়াতের ধুলো । যাক, দেয়ালের অবস্হা দেখে অনিল বুঝতে পেরে গিয়েছিল যে মলয়কে ছবি দিলে বেশিদিন টিকবে না । বেনারসে পেইনটিং গোছা বেঁধে নিয়ে গেল বটে কিন্তু নকশাল আন্দোলনের প্রতি ওদের দুর্বার টানের ফলে স্টুডিওতে পুলিশ ঢুকে সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল । অনিল পালালো দিল্লি হয়ে আমেরিকা আর করুণা দাড়িগোঁফ কামিয়ে সতীশ নাম নিয়ে ১৯৭১ সালে চলে এলো পাটনা ; দাদা ওকে একটা রঙিন মাছের দোকান খুলে দেবার পর বউ বাচ্চাকে নিয়ে চলে এসেছিল ।
সুবিমল বসাকের টেলিগ্রামে আর স্টেটসম্যান সংবাদপত্রে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা থেকে রেহাইয়ের খবর পেলুম । অফিস বলল, রায়ের কপি জমা দিতে । কলকাতা থেকে রায়ের কপি এনে অফিসে জমা দিলুম। মামলায় জিতে যাবার পর লেখালিখি প্রায় ছেড়ে গেল, অথচ মুচলেকাপন্হীরা তখনও প্রচার করে চলেছে যে, “মলয় লেখালিখিকে কেরিয়ার করতে চাইছে।”
বত্রিশ
চাকরি ফিরে পেয়ে সুবিধে এই হল যে ভিন্ন বিভাগে পৌঁছোলুম, গ্রামীণ উন্নয়নের বিভাগে, অবিরাম ট্যুর করার বিভাগে, আরম্ভ হল আমার নতুন অভিজ্ঞতা, তার আগে চাষবাস সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না আমার, জোয়ার আর বাজরা গাছের তফাত জানতুম না, দুটো বলদ না একটা পুং-মহিষ বেশি ওজন টানতে পারে জানতুম না, টিউবওয়েলের রকমফের জানতুম না, জলের গভীরতার সমস্যা জানতুম না, নদীর নিলামের কথা জানতুম না, বঁধুয়া মজুরের দয়নীয় অস্তিত্বের কথা জানতুম না, হাতের কাজে জাতিপ্রথার প্রভাব জানতুম না, তাঁতশিল্পের রাজনীতি জানতুম না, আলু সংরক্ষণের আর পচে নষ্ট হবার দলাদলি জানতুম না, চাষির আত্মহত্যার কারণ আর ফলাফল জানতুম না, বন্ধক জমিতে চাষ আর ফসল ভাগাভাগি জানতুম না, কফি চাষে যুবতীদের যৌনশোষণ জানতুম না, খনিজের কারণে উপজাতিদের উৎখাতের ফলাফল জানতুম না, কতো রকমের গোরু আর ছাগল হয় জানতুম না, মাছের জাল বোনা আর মহাজনদের প্যাঁচপয়জার জানতুম না, সিলকের শাড়ি বোনায় ধর্মের রাজনীতি আর কোরিয়া-চিনের চোরাচালান জানতুম না, বিডিও দপতরে গরিবদের ল্যাঙ মারার গলিঘুঁজি জানতুম না, ঠিকেদারদের বদমায়েসি কেবল কাগজে পড়েছিলুম প্রকৃতপক্ষে তা কী ভয়ানক জানতুম না, নদীতীরের বালিচুরির নেটওয়র্ক জানতুম না, গ্রামের মহাজনদের ঋণ দিয়ে ফাঁদে ফেলার টেকনিক কেবল গল্পের বইতে পড়েছিলুম কিন্তু তার সঙ্গে রাজনীতির যোগাযোগ জানতুম না, কিশোরীরা সকালে মাঠে হাগতে গেলে তাদের ধর্ষণ করা হয় আর তারা তা চেপে যেতে বাধ্য হয় জানতুম না, একজন যুবতীকে কিনে এনে বাড়ির সব কয়টা পুরুষের স্ত্রী করে রাখা হয় জানতুম না, আরও কতো কি জানতুম না, আকাট ছিলুম, আকাট, বই-পড়া আকাট । লেখালিখি ছেড়ে যাবার, বা বলা যায়, রাইটার্স ব্লকে আক্রান্ত হবার, এটাও একটা কারণ, যে, আমি নিজের মূর্খতার সামনাসামনি হলুম, বুঝতে পারলুম যে ভারতবর্ষকে জানি না, একেবারেই জানি না । অভিজ্ঞতার লাথি খেয়ে ক্রমশ অন্য মলয় রায়চৌধুরী হয়ে উঠলুম, বস্তুত লুকিয়েই ফেললুম নিজেকে, দাড়ি-গোঁফ বাড়িয়ে এম. আর. চৌধারী নামের মধ্যে ।
চাষিদের জীবন সম্পর্কে যেটুকু জানতুম তা সহপাঠীদের গ্রামে গিয়ে যতোটুকু জানা যায়, বুঝলুম যে লেখালিখি নিয়ে এতো বেশি শহুরে সময় কাটিয়েছি যে নিজের দেশে নিজেই আমি আগন্তুক, বই-পড়া জ্ঞানের বিভ্রমে আটক থেকে প্রকৃত ভারতবর্ষকে দেখা আর জানা হয়ে ওঠেনি, শহরে বসে কল্পনাজগতকে সীমিত রেখেছি শব্দে-বাক্যে, নিজেকে আবিষ্কার করা শুরু হলো, ছিটকে পড়লুম অপার বিস্ময়ের ব্রহ্মাণ্ডে ।বই পড়ে পাওয়া জ্ঞানের সঙ্গে কোরিলেট করা আরম্ভ করলুম সমাজে ঘটতে থাকা চাপান-ওতোরের । আমার ফিকশান “নখদন্ত”, “ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস”, “জলাঞ্জলি”, “নামগন্ধ”, “অলৌকিক প্রেম ও নৃশংস হত্যার রহস্যোপন্যাস”, “ঔরস” উপন্যাসগুলোর, এবং “অপ্রকাশিত ছোটোগল্প” বইয়ের কয়েকটা গল্পের বীজ, ঘোরাঘুরির চাকরি থেকে পাওয়া, প্রবন্ধ লেখার ধারাও পালটে গেল ঘোরাঘুরি থেকে পাওয়া ভারতীয় জীবনধারার সত্যকে উপলব্ধি করার পর। কমিউনিস্ট কর্মীরা আগেকার দিনে গ্রামে গিয়ে কাজ করতো বলে অনেককিছু জানতে পারতো, কিন্তু গ্রামে-গ্রামে দলটা পৌঁছে গিয়ে কর্মীদের চরিত্র পালটে ফেলল ।
লিখতে বসে ভুলে যেতে পারি, তাই প্রথমেই অবুঝমাড় নামে ছত্তিসগড়ের একটা ঘন জঙ্গলের কথা বলে নিই, যার পৃষ্টপট “ঔরস” উপন্যাসে ব্যবহার করেছি । নারায়ণপুর, বিজাপুর আর বস্তার এই তিন জেলার জঙ্গল এলাকা হল অবুঝমাড় । আমার সহযোগী অফিসারের কথায়, যে, ওই অঞ্চলে ‘সালফি’ নামে একরকমের মদ হয় যা ভারতে আর কোথাও পাওয়া যায় না, কেননা খেজুর গাছের মতন দেখতে যে গাছ থেকে সালফি নামানো হয়, সে-গাছ কেবল ওই জঙ্গলেই হয়, শুনে, সালফি খাবার লোভে যাবার ইচ্ছে হল, যদিও কয়েকজন সহকর্মী ভয়ও দেখিয়েছিল যে মাওবাদীরা কিডন্যাপ করে নিতে পারে । তাছাড়া, জানতে পারলুম, শহরে যাকে আমরা উন্নয়ন বলে মনে করি, তার কোনো প্রয়োজন গোঁড় আর মাড়িয়া উপজাতিদের নেই, বহু শব্দই নেই তাদের ভাষায়, যেমন আনন্দ, দুঃখ, গ্লানি, দারিদ্র্য, সফলতা; মাওবাদীরা ওদের জীবনে ঢুকে ছত্তিশগড়হি, হিন্দি আর তেলেগু শব্দ ঢোকাতে আরম্ভ করেছে । বিপ্লবের মার খেয়ে ভাষাও বিলুপ্ত হয়ে যায় ।
গ্রামীণ উন্নয়নের কাজে বেরিয়ে, এমন একদল মানুষের কথা শুনলুম যাদের কোনো পার্থিব জিনিসের প্রয়োজন নেই । তীর, ধনুক, আর লাঠিই যথেষ্ট ছিল ; বাসা বলতে জঙ্গলের গাছের খুঁটিতে ডালপালা বিছিয়ে ঝুপড়ি । এখন অঞ্চলটা মাওবাদীদের দখলে, আমি যখন গিয়েছিলুম, মাওবাদীরা ছত্তিশগড়ে এতোটা ভেতরে ঢোকেনি । সরকারি কর্মী আর অফিসার ছাড়া সাধারণ মানুষের জন্যে অবুঝমাড় ছিল নিষিদ্ধ এলাকা, কেননা আশির দশকে বিবিসি আদিবাসীদের ঘোটুলের ফিল্ম তুলে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিল, আর ভারত সরকার সেকারণে বেশ অপমানিত বোধ করেছিল। সেসময়ে ঘোটুল বা নগ্ন যুবক-যুবতীদের পারস্পরিক পরিচয়ের হলঘর ধরণের ঝোপড়ি ছিল, সঙ্গমের বাধানিষেধ ছিল না, তাদের মতে প্রেম বা যৌনতা কেনই বা একজনের সঙ্গে সম্পর্কে সীমাবদ্ধ থাকবে, যৌনক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে তারা বিয়ারবহোতি নামে একটা লাল টকটকে পোকা খায়, পরে কালেকটার বলেছিল ওই পোকার নাম ট্রমবিডাইডা, নারায়ণপুরের একআধটা দোকানে শুকনো পোকা পাওয়া যায় ।
এই ভারতবর্ষের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না । অবুঝমাড়ে সবকিছুই বিনিময়ের মাধ্যমে, ইকোনমিক্সের কোনো অস্তিত্ব নেই, শব্দভাঁড়ার ছাড়া । রায়পুর এয়ারপোর্টে নেমে হোটেলে রাত কাটিয়ে পরের দিন নারায়ণপুরের বাস ধরেছিলুম, বাসটার নাম ছিল নৌকরওয়ালা বাস, কেননা দুটো ব্লক নিয়ে সদ্য তৈরি নারায়ণপুর জেলা সদরে যাদের পোস্টিং হয়েছিল তারা প্রায় সকলেই থাকত রায়পুরে । বাসের কনডাকটার সকলের কাছে অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টার নিয়ে গিয়ে সই করিয়ে নিল, মাসের শেষে টাকাটা নেবে । আমরা দুজনেই কেবল বাসভাড়া দিলুম । নারায়ণপুরের রামকৃষ্ণ আশ্রমে থাকার ব্যবস্হা হয়েছিল ;ওনাদের ইশকুলের বীরবল মাড়িয়া নামে এক প্রাক্তন ছাত্রকে গাইড হিসেবে পেয়ে, তার মোটর সাইকেলের পেছনে বসে এগোলুম আমরা । কুরসুনার গ্রামের মুখে, জঙ্গলের ভেতরে ঢোকার আগে কেন্দ্রিয় রিজার্ভ পুলিশকে আমাদের আইডি আর কালকটরের অনুমতির চিঠি দেখাতে হলো ।
বীরবলের কথা অনুযায়ী অবুঝমাড়িয়াদের দেবী হল কাকসার, বস্তারের দেবী হল দান্তেশ্বরী, গোঁড়রা পুজো করে মেঘনাদকে— জানি না এই মেঘনাদ রামায়ণের মেঘনাদ কিনা— বৈগারা পুজো করে রাসনাভাকে ; যতোটা বুঝলুম, দান্তেশ্বরী ছাড়া অন্য দেবী-দেবতাদের নির্দিষ্ট প্রতিমা নেই। জঙ্গলটা চার হাজার একর জুড়ে, তিরিশটা জনবসতি আছে যাকে গ্রাম বলে চালানো যায়, ইংরেজদের সময়ে শেষ সারভে আর সেনসাস হয়েছিল । গ্রামগুলোয় বিজলি নেই, খাবার জল নেই, বাজার-দোকান নেই, শহুরে খাবার নেই, চাল-ডাল নেই, ইশকুল যেটা আছে তাকে বলা যায় মোবাইল, রামকৃষ্ণ আশ্রমের, কারোর অসুখ-বিসুখ হলে মৃত্যু ছাড়া কোনো বিকল্প চিকিৎসা নেই । মরে গেলে গোর দেয়া হয়, পিরামিডের আকারের কিন্তু ধাপ-দেয়া গোরের ওপর চিহ্ণ হিসেবে কাপড় বেঁধে দেয়া আছে, কয়েকটা লাল, সেগুলো মাওবাদীদের । পাকা রাস্তার পর দেখা গেল গেরুমাটির পথ, একটু এগিয়ে দেখলুম, একটা তোরণ, তাতে সবুজের ওপর সাদা দিয়ে লেখা, “ভারতীয় সেনা ওয়াপস যাও, বস্তরওয়াসি বাহরি নহিঁ হ্যায় : জঙ মত লড়ো।” তার পেছন দিকে লেখা, “বস্তরকে যুবায়োঁ, সরকারকে নাজায়জ জঙকে খিলাফ জনয়ুধ মে সামিল হো যাও।”
যে জন্যে এসেছি, সেই সালফি মদের দেখা নেই, গ্রামবাসীদেরও দেখা নেই । আরেকটু এগিয়ে দুটো নিচু-ছাদ চালাঘরের দেখা মিলল, পেছনে খেজুর গাছের মতন একটা চাঁচা গাছে হাড়ি ঝুলছে দেখে বুঝলুম ঠিক জায়গায় এসে গেছি । রোগাটে কয়েকজন পুরুষ, প্রায় উলঙ্গ আর কায়েকজন নারী, বুকে কাপড়ের বালাই নেই, কয়েকটা বাচ্চা যারা কখনও চুল আঁচড়ায়নি, সকলেই সালফির নেশায় নিজস্ব জগতে । একজনের কাছে সালফির হাড়ি ছিল । বীরবল নিজেদের ভাষায় তাকে কিছু বলার পর একটা মিনারাল ওয়াটারের বোতলে সালফি ভরে নিল । আমি একটা কুড়ি টাকার নোট দিতে লোকটা হাত নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে কিছু বলতে বীরবল জানালো ও টাকা নেবে না, সালফি বিক্রির জিনিস নয় । আমরা আরও এগিয়ে হিকানোর গ্রাম আর পেণ্ডা খেতি বা ঝুম চাষ দেখে ফিরে এলুম, ফেরার পথে সালফি খেয়ে ঝিমোতে লাগলুম। সালফির নেশা একেবারে আলাদা, এর আগে যতো রকম নেশা করেছি, সালফি তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, বীরবল মাড়িয়ার কথায়, সালফি খাবার পর লোকে আকাশের মেঘ হয়ে যায় । রাতভর মেঘ হয়ে পড়ে রইলুম বিছানায় ।
দেশভাগের দরুণ নমঃশূদ্রদের যে কী নিদারুণ অবস্হায় পড়তে হয়েছিল, আর তার রেশ যে কবে শেষ হবে বলা কঠিন । নারায়ণপুরে গণেশচন্দ্র সরকার নামে এক স্কুল শিক্ষকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, যিনি আছেন আমার ‘ঔরস’ উপন্যাসে, মরিচঝাঁপির ৩১শে জানুয়ারি ১৯৭৯এর অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েছিলেন, বিয়ে করেছিলেন নিজের চেয়ে প্রায় সাত-আট বড়ো এক যুবতীকে, যাকে ১৯৭১ সালে রেপ করেছিল পাকিস্তানি রাজাকররা, আর তার বাচ্চাকে অ্যাবর্ট করতে দেননি, নারায়ণপুরের আগে মালকানগিরিতে থাকতেন । নমঃশূদ্র বাঙালিদের দেখেছি হিমালয়ের তরাই অঞ্চলেও, তাদের যে জমি দেয়া হয়েছিল তা দখল করে নিয়েছে পাঞ্জাবি জাঠরা, বাঙালিরা আবার ভিকিরি । একই অবস্হা দেখেছি বিহারের মোতিহারিতে, প্রায় বেশিরভাগ লোকই হয়ে গেছে বিহারি, রিকশ চালায় বা ঠেলাগাড়ি টানে বা দিনমজুরি করে । যে নমঃশুদ্রদের গড়চিরোলি, বালাঘাট, ভাণ্ডারা, রাজনন্দগাঁও পাঠানো হয়েছিল, তারা হয়ে গেছে মারাঠি । আমি ওই জায়গাগুলোয় গেছি বলে জানি, এ ছাড়াও ভারতে হয়তো বহু জায়গায় পাঠানো হয়েছিল তাদের । আমি একটা ব্যাপার কমিউনিস্ট দলটার বুঝতে পারি না, একদিকে নমঃশুদ্রদের আন্দামান দ্বীপে যেতে দেয়া হল না, আবার আরেক দিকে তাদের মরিচঝাঁপিতে বসত গড়তে দেয়া হল না, স্ট্রেঞ্জ ।
মুঙ্গের, যেখানে কাট্টা-তামঞ্চা তৈরি হয় ঘরে-ঘরে, সে শহরে গিয়েছিলুম চাষীদের অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে, তখন ইন্দিরা গান্ধির এমারজেন্সি চলছে । কৃষি বিভাগের অধিকর্তা আমাদের নিতে এসেছিল স্টেশানে, ওনার জিপে বসে থানার সামনে দিয়ে যেতে-যেতে দেখি সামনের বারান্দায় গোটা আষ্টেক মানুষকে ল্যাঙটো করে উল্টো টাঙিয়ে রাখা হয়েছে । পুলিশ এতোদিন ওদের গায়ে হাত দেয়নি স্হানীয় মাফিয়া বলে বেশ রমরমা ছিল ওদের । সুযোগ পেয়েই প্রতিশোধ নিতে নিমে পড়েছে । কৃষি অধিকর্তা বলল যে সরকারি গাড়িতে করে গ্রামে যাওয়া যাবে না, মানুষ এতো ভয়ে আছে যে সরকারি গাড়ি দেখতে পেলেই দূর থেকে পালাবে । কী আর করা যায় ! মহাজনদের একদিন ডেকে পাঠালুম আর বোঝাবার চেষ্টা করলুম, তারা মাথা নেড়ে গেল । পরের দিন ব্যাংক ম্যানেজার আর সহকারী কৃষিঋণ সমিতির সচিবদের ডেকে পাঠিয়ে বোঝালুম । তারাও মাথা নেড়ে চলে গেল । পরের দিন ফেরার সময়ে দেখলুম আরেকদল যুবককে একই ভাবে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে । এইসব টাঙানো লোকগুলোই পরে লালু যাদবের দলে ভিড়েছে ।
মুর্শিদাবাদের এক গ্রামে গিয়েছিলুম কৃষিঋণ সমিতির বন্ধক নেয়া জমিজমার খতিয়ান যাচাই করতে। গ্খাতা ওলটাতে-ওলটাতে দেখি তার মাঝে রাখা রয়েছে দাউদ ইব্রাহিম আর ওসামা বিন লাদেনের ছবি । মুখ না তুলে পাতা উল্টে গেলুম । সমিতির সচিব বললেন ‘আপুনাদের জইন্য চা আনি’, বলে কেটে পড়লেন। কারোর কাউকে ভালো লাগে যদি তো করার কিছু নেই । তখনও ওসামা বেঁচে ।
বিহারের বাঢ় শহরে গিয়েছিলুম ইন্সপেকশনে, নথি পরীক্ষা করছি, সামনের বারান্দায় একজন যুবতী সেজেগুজে নাচা আরম্ভ করে দিল, “অভি না যাও চোদ কর কি দিল অভি ভরা নহিঁ” । সামনের দরোজাটা বন্ধ করে দিতে বললেও কারোর কানে গেল না কথাটা । নিজেই বন্ধ করলুম উঠে । লাঞ্চের সময়ে নিচে নেমে একটা ছেঁদো হোটেলে ভাত-ডাল-আলুভাজা খাচ্ছি যখন, পিওনটা এসে ফিসফিস করে বলল, “স্যার ওই রণ্ডিটাকে শাখা অধিকর্তা আগে থেকে শিখিয়ে দিয়েছিল যে আপনারা ইন্সপেকশানে আসছেন, টোপ ফেলে আপনাদের মন অন্য দিকে ঘোরাতে চেয়েছে, অনেক ঘাপলা আছে শাখায়, চাষিরা এলে তাড়িয়ে দেয়।” যে হোটেলে সন্ধ্যাবালা উঠেছিলুম, সেখানেও কয়েকটা বেশ্যাকে নিয়ে হাজির । যখন বললুম যে “ওই রণ্ডিদের সঙ্গে শুয়েও আমি যা রিপোর্ট করার তাই করব”, তখন শাখা অধিকর্তা হাঁটু গেড়ে হাতজোড় করে কাঁদতে আরম্ভ করল । আত্মম্ভরিতা উপভোগেরও কষ্টের দিক আছে ।
ডিটেকটিভ বই “অলৌকিক প্রেম ও নৃশংস হত্যার রহস্যোপন্যাস” বইতে আমি কর্ণাটক-অন্ধ্রপ্রদেশের সীমান্তের একটা উপজাতি অধ্যুষিত জঙ্গল এলাকার উল্লেখ করেছি, যেখানে গিয়ে পরস্পরের অচেনা যুবক-যুবতী বাসা বাঁধে, আমি অফিসের কাজে গেছি ওই উপজাতিদের উন্নতি করার ধান্দায় । যুবকরা সাধারণত কলা পেঁপে লেবু ইত্যাদির চাষমালিকদের দিনমজুর, ঋতুতে, নয়তো বেকার । উচ্চাকাঙ্খীরা ব্যারেটাইস আর অন্যান্য খনিতে কাজ করতে গিয়ে রোগ নিয়ে ফেরে । জঙ্গলের অধিবাসীরা কেউ কখনও ভোট দেয়নি, কারোর কোনো আইডেনটিটি কার্ড নেই । কাঁঠালবিচি, কুমড়ো, কাঁচাকলা পুড়িয়ে খায় । আমার রিপোর্ট কোনো কাজে আসেনি, কেননা জঙ্গল আর বাগানগুলোর মাটির তলায় খনিজের আবিষ্কারের ফলে লোপাট হয়ে গেছে কলা কাঁঠাল লেবু পেঁপের বাগানগুলো ।
তেত্রিশ
আমার আরেক ধাপ ওপরে ওঠা পাওনা হয়ে গিয়েছিল বলে অফিস পাঠালো নাগপুর অফিসে তিন মাসের জন্য । সেখানে আলাপ হকি খেলোয়াড় সলিলার সঙ্গে, আরেকজন যুবতী সুলোচনা নাইডুর মাধ্যমে, কয়েক দিনের পরিচয়ের পরই বললুম, আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই, আপনার বাড়িতে কার সঙ্গে কথা বলতে হবে । ওর বাবা ওর শৈশবে দুই বোন আর পোয়াতি স্ত্রীকে ওদের মামার বাড়িতে রেখে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন, সেই থেকে তিন বোন মামার বাড়িতে মানুষ । অতএব মামাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। বড়োমামা, যিনি অভিভাবক, তিনি ছিলেন না, মেজমামা ছিলেন, তিনি আমার প্রস্তাবে কান দেওয়ার বদলে নিজের বন্দুকের আলমারি খুলে আটটা গান, রাইফেল দেখালেন, কয়েকটার নাম মনে আছে, মজার প্যাটার্ন বোল্ট অ্যাকশান রাইফেল, এসএমএলই প্যাটার্ন ব্রিটিশ রাইফেল, মোজিন ন্যাজেন্ট প্যাটার্ন বোল্ট রাইফেল, বারো গেজ পাম্প অ্যাকশান শটগান, সাবোট স্লাগ হানটিং গান ইত্যাদি, ওনার বাবার । দেয়ালে টাঙানো, হরিণ, লেপার্ড ইত্যাদির মাথা দেখালেন, শিকারের গল্প করলেন ।
বৈঠকখানায় দেখলুম থরে-থরে ইংরেজি পেপারব্যাক যার ওপর ধুলোর আস্তরণ, কেউ কখনও পড়তো হয়তো ওগুলো । কোনও বাংলা বই বা পত্রিকা নেই । আমি যে লেখালিখির সঙ্গে জড়িত তা সলিলাকে বলিনি, সুলোচনা নাইডু হিন্দি পত্রিকায় আমার সম্পর্কে সংবাদ আর ফোটো দেখিয়েছিল । ওদের বাড়িতে কেউই ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেননি । তবে পরে নাগপুরের কারোর সঙ্গে দেখা হলে তিনি জানতে চান, “এখনও রাইটিং করেন ? ইংলিশে লেখেন না কেন ? ইংলিশে লিখলে ইনকাম ভালো হয় ।” বলে ফেলি, “আমি কেবল স্কটল্যাণ্ডের মদ খাই, ওইটুকুই যা ইংলিশ জ্ঞান আমার।”
পরের দিন আবার যেতে হলো, বড়োমামা-মেজমামা ইতিমধ্যে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিয়ে থাকবেন, আমাকে আমার উৎস প্রমাণের জন্য পাটনায় টেলিগ্রাম করতে বললেন । আমি পাটনায় বাবাকে আর চাইবাসায় দাদাকে টেলিগ্রাম করলুম । আমার দেদোল স্বভাবের সঙ্গে মা অতিপরিচিত ছিলেন, সুতরাং চাইছিলেন, যেকোনো একজন মেয়েকে বিয়ে করে হাজির হই। আমার টেলিগ্রাম পেয়ে পিসতুতো দাদা সেন্টুদাকে দাদার কাছে পাঠিয়ে দিলেন, একটা ইনটারেসটিং চিঠি দিয়ে, যে চিঠির প্রধান বক্তব্য ছিল “সিন্দুর পরিয়ে নিয়ে এস, বুঝলে” । লাইনটানা কাগজে লেখা তারিখহীন চিঠিটা দাদা “হাওয়া৪৯” পত্রিকার এপ্রিল ২০০১ সংখ্যায় মায়ের হাতের-লেখাসহ ছেপেছিল :
কল্যানীয়
বাশুদেব আশা করি তুমি ও বেলা নিশ্চয়ই গিয়ে পৌঁছিয়েছ তুমি দাঁড়িয়ে থেকে মলয়ের বিয়ে দাও এবং বাসি বিয়ে দিয়ে সিন্দুর পরিয়ে নিয়ে এস ।
কারণ এখানে মেজজাঠা তোমাদের শয্যাশায়ি তোমরা এলে দেখতে পাবে এবং বাবুর শরীর খুব খারাপ ।
অতএব তুমি সমস্ত কাজ সেরে বৌ নিয়ে এস তোমাদের আসার অপেক্ষায় রহিলাম । তোমরা সকলে আমাদের শুভ আশীর্ব্বাদ নাও । সিন্দুর পরিয়ে নিয়ে এসো বুঝলে ? ।
ইতি
মা
মা বলেছিলেন ‘সিন্দুর পরিয়ে নিয়ে এসো’, মানে বিয়ে করে না আনলেও যেন সিঁদুর পরে আসে। কিন্তু সলিলা সিঁদুর আর শাঁখা-পলা ইত্যাদি বিয়ের পর পরত না কখনও, হকি খেলোয়াড় ওর মধ্যে এমন ভাবে সেঁদিয়ে ছিল যে টিপিকাল মধ্যবিত্ত বাঙালি গৃহবধুর মতো আচরণ করতে পারেনি । পরে দেবী রায়ের স্ত্রী মালা একটা অষ্টধাতুর নোয়া তৈরি করিয়ে প্রেজেন্ট করেছিলেন, সেটাই পরে সারাজীবন চালিয়ে দিলে । মা আর বলতেন না কিছু, কেননা উনি নিজেই প্রতিদিন সিঁদুর পরতেন না, চুল উঠে যাবার ভয়ে ।
আমার টেলিগ্রাম যেদিন পাটনায় পৌঁছেছিল সেইদিনই মেজজ্যাঠা মারা যান । ছেলে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে চাইছে, এই সুযোগ যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায়, তাই দাদাকে পাঠানোর ব্যবস্হা, নয়তো অশৌচ ইত্যাদির আচারে পড়লে দেরি হয়ে গেলে ছেলে হয়তো মত পালটে ফেলতে পারে, ভেবেছিলেন বাবা-মা । দাদা নাগপুরে এসে একদিনের দেখা দিয়ে চাইবাসা ফিরে গিয়েছিল বৌদি আর মেয়ে হনিকে আনতে, সেন্টুদার কাছ থেকে জেনে গিয়ে থাকবে মেজজ্যাঠার মৃত্যুর কথা । নাগপুরে সলিলার মেজ মামার মেয়ে বেলার বিয়ে আর কয়েক দিন পরেই হবার ছিল ; সলিলার ছোটো বোন রমলা চাইছিল যে আগে ওর বিয়ে হোক তারপর সলিলার, অর্থাৎ আমি রমলাকে বিয়ে করি । দুই বোনের ঝগড়ার মাঝে বড়ো মাইমা চাইলেন যে তাঁর বড়ো মেয়েকে আমি বিয়ে করি । আমি ভাবছিলুম যে পার্টিশানের আড়াল থেকে একটা সুন্দর মুখ উঁকি মেরে আমাকে দেখছিল, বেলার বোন নিলীমা, গণ্ডোগোল হলে তাকেই বিয়ে করে নিয়ে যাবো । আমি ওনাদের তর্কাতর্কি এড়াতে হোটেলে চলে এসেছিলুম, সলিলা এসে ডেকে নিয়ে গেল, ফাইনাল করার জন্যে । শেষ পর্যন্ত কার্ড ছাপানো হল আমার আর সলিলার বিয়ের, চোঠা ডিসেম্বর ১৯৬৮ ।
বিয়ের দুদিন আগে দাদা, বৌদি আর মেয়ে হনির সঙ্গে নিজের শাশুড়িকে নিয়ে পৌছোলো । মামার মেয়ে বেলার বিয়ের পরে ওদের পিঁড়ি আর আগুন আমরা শেয়ার করে সংক্ষিপ্ত রিচুয়ালের বিয়ে করলুম। বিয়ে করে পাটনায় গেলুম না, গেলুম চাইবাসায় আর আমাদের ফুলশয্যা হল সেই ঘরটায় যে ঘরে শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রেমিকা শীলাকে অন্ধকারে চুমু খেয়েছিলেন, তার বর্ণনা আছে “কিন্নর কিন্নরী’সহ বেশ কয়েকটা গল্প-উপন্যাসে। চাইবাসা থেকে পাটনা রওনা দিলুম আমি দাদা বৌদি হনি আর সলিলা । পাটনায় গিয়ে মেজজ্যাঠার মৃত্যু সংবাদ পেলুম । মেজজ্যাঠার মেয়ে ডলি চলে এসেছিল কলকাতা থেকে, বলল, “তুমি আর সময় পেলে না, এতোকাল অকাজ-কুকাজ যা চেয়েছো নিজের ইচ্ছেতে করেছো, বাবা তোমায় কতো ভালোবাসতো, আর একটা বছর পরে বিয়ে করলেই পারতে।” ডলি এতোই চটে গিয়েছিল যে তারপর সম্পর্ক-বিচ্ছেদ করে দিয়েছে ।যেদিন সলিলার বউভাত সেই দিনই মেজজ্যাঠার শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজন । সকলেই শ্রাদ্ধ আর বিয়ের ভোজ একই দিনে খেয়ে গেলেন । মৃত্যু দিয়ে নতুন করে জীবন আরম্ভ করলুম । স্বাভাবিক যে চাইবাসা বা পাটনায় কোনো বিয়ের রিচুয়াল হয়নি ; সলিলার মতে, আমরা অর্ধেক বিয়ে-করা আর অর্ধেক লিভ-ইন ।
১৯৭০ সালে সলিলা ওর কুকুর সুজিকে নিয়ে এলো পাটনায়, কেননা নাগপুর থেকে সবাই লিখছিল যে সুজিকে রাখা যাচ্ছে না, সলিলার অবর্তমানে ছোটো বোন রমলা ওকে সামলাতে পারছে না। পাটনার বাড়িতে সুজির খেলবার জায়গা ছিল না, সর্বত্র সিমেন্টের মেঝে, কুকুরটার মন খারাপ হয়ে কাঁদতো, আমি চান করিয়ে দিতুম পছন্দ হতো না, শেষে আবার নাগপুরে রেখে এলো সলিলা । নাগপুরে বছরখানেক থাকার পর একদিন উধাও হয়ে গেল, আর খুঁজে পাওয়া যায়নি, সলিলার বাবাকে যেমন আর খুঁজে পাওয়া যায়নি ।
১৯৫৩ নাগাদ দরিয়াপুরের বাড়িতে একটা দিশি কুকুরের বাচ্চা এনেছিলেন ছোটোকাকার শালা যাঁকে বুজিদা বলে ডাকতুম, আমি কুকুরটার নাম দিয়েছিলুম রব, আর একটা পদবিও দিয়েছিলুম, লিংচিপুলু, ওকে ডাকতে হলে পুরো নামে, মানে রব লিংচিপুলু বলে ডাকতে হতো । পাঁচ-ছয় বছরেই বুড়ো হয়ে গিয়ে কুকুরটা উধাও হয়ে গেল একদিন । রব লিংচিপুলুর জন্যে পাঁঠার ছাঁট মাংস কিনে আনতুম, পাড়ায় একজন পাগল থাকতো, বাঙালি বাড়ির, তাকে বোধহয় মাংস খেতে দেয়া হতো না বাড়িতে, পোশাক দেখেই টের পেতুম যে লোকটা অবহেলায় ভুগছে, রব লিংচিপুলুর ছাঁট মাংস খেতে আসতো প্রতি রবিবার ; বাড়িতে রাঁধা মাংস দিলে খেতো না, বলত ওরকম টেস্টি মাংস খেতে পারি না । কোতরঙের বাড়িতে ফিরে বুজিদাও মারা গেছে তিরিশ বছর আগে ; সেই জমিটাও ঠাকুমার দেয়া ।
পাটনার চাকরি বদলে অ্যাগ্রিকালচারার রিফাইনান্স অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশানের লখনউ শাখায় চলে গেলুম, সেখানে যে বাংলো পেলুম , পেছনের জমিতে আরম্ভ করলুম চাষবাস, নিজের চোখে দেখার জন্য বেগুন, আলু, ঢ্যাঁড়স, ভুট্টা, পেঁয়াজ, রসুন, কপি, ধনে, মৌরি, মুলো, গাজর আর পেয়ারা, কুল, কলা, পেঁপে, সজনে, লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে ইত্যাদি । সামনের জমিতে লাগালুম বারমুডা ঘাস যা কাটাকাটির বালাই নেই, কার্পেটের মতন, তার চারিধারে নানা রঙের গোলাপ, চাঁপা, বেলি, যুঁই আর হ্যাঁ, লজ্জাবতী লতা। চাষের জন্যে বই প্রচুর পড়তুম যাতে ট্যুরে গিয়ে বোকার মতন কথা না বলে ফেলি চাষিদের কাছে । “নামগন্ধ” উপন্যাসে পশ্চিমবঙ্গে আলুচাষীদের জীবন নিয়ে লিখতে গিয়ে কাজে দিয়েছে চাষের আর বইয়ের জ্ঞান । অফিসের অনেকে আসতো আমার বাগান দেখতে । বাবা-মা যখন এসেছিলেন, ওনাদের এতো ভালো লেগেছিল যে, বলেছিলেন, বাংলোটা কিনে নে, তারপর দাম শুনে মুষড়ে পড়েছিলেন । লখনউ থেকে বিভিন্ন কাজে ট্যুরে গেছি, মাটি থেকে আপনা থেকে বেরোনো আর্টেজিয়ান স্রোত যেমন দেখেছি, তেমনই তরাইয়ের বাঙালি উদ্বাস্তুদের দুর্দশা, হিমালয়ের জংলি গোরু যারা দুধ এতো কম দেয় যে পোষা যায় না, লোকে পাহাড় থেকে ধরে এনে খেতো, তাও তো এখন বন্ধ হয়ে গেছে ।
আমার মেয়ে আর ছেলে তখন ছোটো ছিল, ওরাও গাছেদের চরিত্র বোঝার চেষ্টা করত, খুরপি হাতে সাহায্য করতো আমাকে । মেয়ে নিজেই সাইকেল চালিয়ে ইশকুল যেতো আর ছেলের ইশকুল অনেক দূরে ছিল বলে রিকশায় গাদাগাদি করে যেতো আসতো । যে রিকশাঅলা ওদের ইশকুলে নিয়ে যেতো সে-ই ট্যুরে যাবার সময়ে আমাকে রাত-বিরেতে ট্রেনে তুলে দিতে নিয়ে যেতো, শিউনন্নির মতন পালোয়ান ছিল । সেসময়ে বহু জায়গায় ট্যুরে গেছি যেখানে হোটেল নেই ; বরইলিতে এক মুসলমান যুবকের বাড়ি ছিলুম, যতোদিন ছিলুম প্রতিদিন নিজের একটা করে মুর্গি জবাই করে আমাকে খাইয়েছে । আলিগড়ে যখন গিয়েছিলুম সদ্য দাঙ্গা থেমেছে, উঠেছিলুম বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউসে, আমার সহযোগী ভাবতো যে গোরুর মাংস খাইয়ে দিচ্ছে, তাই খাবার অসুবিধা হতো, একদিন বলতে বাধ্য হলুম যে মিস্টার শ্রীবাস্তবের জন্যে মুর্গি রাঁধলে ভালো হয় । লখনউতে উত্তম দাশ এসেছিলেন স্ত্রী মালবিকাকে নিয়ে, দেবী রায় সস্ত্রীক এসেছিলেন, পার্থসারথী এসেছিলেন, কলকাতার খবর নিয়ে । ওনাদের কথাবার্তা শুনে মনে হল যে কিছু মানুষ আমাকে চিরকাল ঘৃণা করবে, ঘৃণার মাধ্যমে মরণোত্তর আয়ু দিয়ে যাবে । শেষবেলায় টের পাই যে কলকাতায় থাকলে উন্মাদ হয়ে যেতুম ।
আমি দুটো গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ডাইরেকটর ছিলুম লখনউ থাকতে, রায়বরেলি আর ফৈজাবাদ । ফৈজাবাদে কর্মীরা ঘেরাও করেছিল মাইনে বাড়াবার দাবী জানিয়ে । রায়বরেলির বোর্ডে একজন টুপি-পরা কংগ্রেস নেতা ছিলেন যিনি প্রায়ই বলতেন কিছু দরকার থাকলে বলবেন, দিল্লিকে বলে করিয়ে দেবো, মানে গান্ধি পরিবারকে । ফৈজাবাদে গিয়ে রামের জন্মভূমি বা বাবরি মসজিদ দেখলুম, তখনও বিজেপি ওটা ভেঙে ফ্যালেনি, ভেতরে ঢোকার আগে পুলিশ কন্সটেবল বলল, চামড়ার বেল্ট আর জুতো খুলে ঢুকুন, অর্থাৎ পুলিশ কর্মীরও রাম সম্পর্কে ভীতি গড়ে উঠেছিল, ভেতরে একটা টেবিলের ওপর রাম-সীতার মূর্তি, তাতে গ্যাঁদাফুলের মালা, একটা থাম অবশ্য কালো পাথরের ছিল, কোনো পুরোনো স্ট্রাকচারের । যখন দেখেছিলুম তখন ধারণা করতে পারিনি যে কিছুকাল পরে ঝোপঝাড়ে ঘেরা এই পোড়ো বাড়িটা নিয়ে এতো হ্যাঙ্গাম হবে । একেবারে ফাঁকা ছিল, একজনকেও পুজো দিতে দেখিনি, তার চেয়ে অযোধ্যার অন্য মন্দিরগুলোয় প্রচুর লোক পুজো দিচ্ছে দেখলুম । আর চারিদিকে বাঁদরের দল । রামায়ণে বানরসেনা আছে বলে কেউ কি কখনও এই শহরে বাঁদরদের এনেছিলেন ? হনুমান আর কাঠবিড়ালি কিন্তু একটাও দেখতে পাইনি সেসময়ে ।
লখনউতে স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে আমি সবাই মিলে সবজি কুটতুম, চিংড়ি মা্ছ বাছতুম । কলকাতার মতন মাছ কেটে পরিষ্কার করার ব্যাপার লখনউয়ের বাজারে ছিল না । প্রভাকর এসে যদি দেখতো যে মাছ কোটা-বাছা চলছে, তক্ষুনি নাকে রুমাল চাপা দিয়ে পালাতো । আবদুল করিমের বাড়ি দিয়ে আসতো আমার ছেলে, মাছ বা মাংস রাঁধা হলে । করিম ট্যুরে গেলে আমার ছেলের জন্যে নানা জিনিস কিনে আনতো, এমনকি অ্যানটিক টেবিল, বই রাখার র্যাক ইত্যাদি । শেষ পর্যন্ত কোনো আসবাবই আর রইলো না, সবই বিলিয়ে দিয়েছি একের পর এক । এখন মনে হয়, বিদেশ থেকে আনা টুকিটাকি জিনিসগুলো কিনে আনা উচিত হয়নি, সবই ফালতু, ধুলোর চাদরে তাদের চেনা দায় । সাকিন পালটেছি আর যা পেরেছি বিদেয় করেছি ।
লখনউতেই মা মারা গেলেন, কী হয়েছে সঠিক বলতে পারতেন না, হৃদরোগের ডাক্তারও ধরতে পারেনি । সেসময়ে ডাক্তারির এতোটা উন্নতি হয়নি, আমাদের জ্ঞানও বেশ সীমিত ছিল, এখন বহু কিছু নিজের অসুখের জন্য জেনে ফেলেছি । তখন মুম্বাইতে থাকলে মায়ের সঠিক চিকিৎসা হতে পারতো হয়তো। মা হাসপাতালে মারা যেতে দাদাকে তক্ষুণি টেলিফোন করে দিয়েছিলুম, দাদা পাটনা থেকে এসে মুখাগ্নি করে ফিরে গেল । শ্মশানে পুরুতের দরকার হয়, কোনো বাঙালি পুরুতকে চিনতুম না, কেননা ধর্মকর্ম তো আমি বা আমার স্ত্রী কেউই করতুম না, ফলে পঞ্চানন ভট্টাচার্য বা চ্যাটার্জি নামে অফিসের এক কর্মীকে ডেকে এনেছিলেন আমার প্রতিবেশি হায়দার আলি, দাদা তার নির্দেশমতো মুখাগ্নি করল । বুঝতে পারলুম যে মৃত্যুর সঙ্গে আমার একটা সৃজনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ।
খুবই অদ্ভুত যে মায়ের মৃত্যুতে আমার রাইটার্স ব্লক সেরে গেল আর ঠিক এই সময়েই ঢাকা থেকে একাধিক পত্রিকায় কবিতা দেবার অনুরোধ আসতে লাগল । আমার কাব্যগ্রন্হ, উত্তম দাশের মহাদিগন্ত প্রকাশনী থেকে বেরিয়েছিল, “মেধার বাতানুকূল ঘুঙুর”-এর প্রায় সব কবিতাই প্রথমে ঢাকার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । এই কাব্যগ্রন্হের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছিলেন যোগেন চৌধুরী । হাংরি আন্দোলনের সময়কার কবিতা থেকে একেবারে আলাদা, উত্তরপ্রদেশের খুংখার ঘটনায় প্রভাবিত কবিতা ।আমার বই পড়বার ঝোঁকও নির্দিষ্ট রইল না, ভারতীয় সমাজকে বুঝতে পারার মতন বই বেশি পড়া আরম্ভ করলুম, অফিসেও প্রচুর সময় হাতে থাকত বই পড়ার, অধস্তন অফিসারদের বললে তারা বইপত্র যোগাড় করে এনে দিতো ।
লখনউ থেকে পৌঁছোলুম নাবার্ডের হেড অফিসে, মুম্বাইতে, তখন ছিল বোম্বে, কনট্র্যাক্ট কিলারদের, এনকাউন্টার স্পেশালিস্টদের আর কিলডদের শহর, যাদের দুপক্ষই একই কারণে শহরটাকে ভালোবাসে, টাকা টাকা টাকা টাকা উপভোগ উপভোগ উপভোগ উপভোগ, একেবারে অবাস্তবতার জগত, প্রতিটি সম্প্রদায় নিজেদের অতীতে ফিরে যেতে চাইছে, হত্যা আর লুটমারের গৌরবের কালখণ্ডে। এখন তা থেকে উতরোতে পেরেছে । এই শহরের গরিবদের অবস্হা অবর্ণনীয় । ইমলিতলায় আমরা গরিব ছিলুম, প্রতিবেশীরা আরও গরিব ছিল, কিন্তু কেউই তাকে দুর্ভাগ্য বলে মনে করত না, আমার মাকে কখনও দেখিনি কাউকে ঈর্ষা করতে । এই শহরে দুর্ভাগারা ভাগ্য ফেরাতে আসে, যুবক-যুবতীরা ভাগ্য ফেরাবার ধান্দায় ধর্ষণকেও মেনে নেয় । হ্যাঁ, যুবকরাও চাকরির জন্য ধর্ষিত হতে রাজি হয়।
মেট্রপলিসগুলো শিখিয়ে দ্যায় কেমন করে ভিড় থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে আর আলাদা হবার প্রক্রিয়ায় কেমন করে নিজেকে দুর্ভেদ্য করে তোলা যায় । আমি টের পেয়ে গিয়েছিলুম যে আমি দুর্ভেদ্য, আমি সমগ্র মানবসভ্যতাকে নিজের ভেতরে নিয়ে ঘুরে বেড়াই ; মানবসভ্যতার জন্যে এটাই সবচেয়ে আনন্দের যে প্রকৃতিজগত মানবসভ্যতার তোয়াক্কা করে না । মুম্বাইয়ের সংবাদপত্রে ধনীদের অসুখের খবর এমনভাবে ছাপা হয় যেন অসুখও এক ধরণের বৈভবশালী প্রাণী । এদিকে গরিবরা হল অবহেলার ক্রীতদাস, মানুষ রাস্তার ধারে রেল লাইনের ধারে সকলের সামনে হাগতে বসে, তাতে কারোরই কিছু এসে যায় না, এই শহরে কতো রকমের যে “অপর” রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই । গণতন্ত্র ব্যাপারটা এখানে অ্যাননিমাস ।
মুম্বাইতে এসেই বাস্তব জগতকে নিংড়ে ফিকশান বের করার কায়দা আবিষ্কার করলুম । এই শহরে প্রেম এমন পর্যায়ে পৌঁছেচে যে তা মানুষ-মানুষীর পরস্পরের অবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে ; যতদিন দৈহিক অবিশ্বাস ততোদিন ভালোবাসা, সম্পর্কের মাঝে চাই কনডোম সুরক্ষা, প্রেমিক জানে না প্রেমিকার দেহে কোন রাক্ষস আছে, তেমনই প্রেমিকা জানে না প্রেমিকের লিঙ্গে কোন রোগের রাক্ষস ওৎ পেতে আছে । “ডুবজলে যেটুকু প্রশ্বাস” উপন্যাসের চরিত্ররা পাটনার হলেও জ্ঞান নিংড়ে পেয়েছি মুম্বাইতে । ‘জলাঞ্জলি” উপন্যাসে চরিত্রদের নিয়ে গেছি পাটনা থেকে কলকাতায় । “নামগন্ধ” উপন্যাসে চরিত্রদের কলকাতা থেকে নিয়ে গেছি পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে, আলু চাষিদের দুর্দশা আর কোল্ড স্টোরেজে আলু রাখার রাজনীতি নিয়ে । “ঔরস” উপন্যাসে নিয়ে গেছি মাওবাদি অধ্যুষিত ঝাড়খণ্ড আর অবুঝমাড়ে । “আলৌকিক প্রেম ও নৃশংস হত্যা” ডিটেকটিভ উপন্যাসে কলকাতা থেকে নিয়ে গেছি অন্ধ্রপদেশ-কর্নাটকের সীমান্তের উপজাতি অঞ্চলে । এগুলো সবই ট্যুরের চাকরিতে পাওয়া অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেশানো কল্পনা । “অরূপ তোমার এঁটোকাঁটা” উপন্যাসে বেনারস আর কাঠমাণ্ডুতে পাওয়া হিপিসঙ্গের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশিয়েছি কল্পনা । “নখদন্ত” সাতকাহনে পাটচাষ আর চটকলের রাজনীতি নিয়ে পশ্চিমবাংলায় ট্যুরে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে মিশেল দিয়েছি সংবাদপত্রে পাওয়া ঘটনা, নিজের নোটবইয়ের টুকরো-টাকরা, তখন হাতে কলম ধরে লিখতে পারতুম । এই বইগুলোর পর আমি কল্পনানির্ভর ফিকশান লেখা আরম্ভ করলুম, “জঙ্গলরোমিও”, “নেক্রোপুরুষ” আর “লাবিয়ার মাকড়ি” । আরেকটা উপন্যাস লিখেছিলুম “অমৃতলোক” পত্রিকায়, তার নাম আমি ভুলে গেছি, কপিটাও জোগাড় করতে পারিনি, উপন্যাসটা ছিল “জিন্নতুলবিলাদের রূপকথা” আর “গহ্বরতীর্থের কুশীলব”-এর ঢঙে, জাদুবাস্তব।
“অমৃতলোক” পত্রিকার কথা মনে আসতে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল । ১৯৯৫ সালে কলকাতায় রটে যায় যে মলয় রায়চৌধুরী মারা গেছেন । ব্যাস লিটল ম্যাগাজিনে শোক প্রকাশ করার ঢেউ উঠলো, “অমৃতলোক” পত্রিকায় বেশ বড়ো করে সম্পাদকীয় লিখেছিলেন সমীরণ মজুমদার । আমি মুম্বাই থেকে ফিরে তখন ছিলুম দাদার বাঁশদ্রোণীর বাড়িতে । একদিন শক্তি চট্টোপাধ্যায় এসে হাজির, বললেন, “সংবাদটার সত্যতা যাচাই করতে এলাম, তুমি এখানে ইজিচেয়ারে বসে ঠ্যাং দোলাচ্ছো আর তোমার বন্ধুরা তোমার মৃত্যুর খবরে খালাসিটোলায় উৎসব করছে । যাক বেঁচেবর্তে আছো, সেলিব্রেট করার জন্য মদ খাওয়াও।” বললুম একদিন যাবো স্মিরনফ নিয়ে আপনার বাড়িতে । গিয়েছিলুম, দাদা আর প্রদীপও সঙ্গে । মীনাক্ষীও সঙ্গ দিলেন আমাদের, ওনার শ্যাম্পেন খাবার গেলাস এনে । ভালোমন্দ খাইয়েছিলেন শক্তি । সন্দীপনের মতন কিপটেমি করেননি ।
অনুবাদে হাত দিয়েছি বেশ দেরিতে । প্রথম অনুবাদ করেছিলুম “হাউল”, আমেরিকার একটা বাংলা পত্রিকার অনুরোধে, নাম ভুলে গেছি, অ্যালেন গিন্সবার্গ তখন ইউ ইয়র্কে । তারপর অনুবাদ করেছিলুম গিন্সবার্গের “ক্যাডিশ” । এই কবিতাটা অনুবাদ করতে সাহায্য নিয়েছিলুম গিন্সবার্গের নিজের আবৃত্তি-করা তেত্রিশ আর পি এম গ্রামোফোন রেকর্ডের, যাতে প্রতিটি লাইনের শ্বাসাঘাত ধরতে পারি, কেননা বাঙালির কথা বলার শ্বাসাঘাতের সঙ্গে মার্কিন ইংরেজির শ্বাসাঘাতের বেশ তফাত আছে । ২০০৯ সালে কলকাতা ছাড়ার সময়ে এই গ্রামোফোন রেকর্ডটা আর এজরা পাউণ্ডের কন্ঠে স্বরচিত কবিতা পাঠের রেকর্ড দিয়ে দিয়েছিলুম শুভঙ্কর দাশকে, ওরা স্বামী-স্ত্রী আমাকে পছন্দ করতো ; তবে ওদের মেয়ে রূপকথাকে আমি আর আমার স্ত্রী এখনও দেখিনি, শুনেছি বাচ্চাটা খুবই সুন্দর হয়েছে । আমেরিকা থেকে গিন্সবার্গ ট্রাস্টের বব রোজেনথাল আর গিন্সবার্গ আরকাইভের কিউরেটার বিল মরগ্যান গিন্সবার্গ সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করতে কলকাতায় এলে শুভঙ্করকে বলেছিলুম গাইড করতে । নিজের আরকাইভ এক মিলিয়ন ডলারে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে বিক্রি করে দিয়েছেন গিন্সবার্গ, তার অর্ধেক সৎ-মাকে দিয়ে গেছেন ।
২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে বিবিসির জো হুইলার আর “নার্কোপলিস”এর লেখক জিত থাইল এসেছিলেন গিন্সবার্গ সম্পর্কে আমার সাক্ষাৎকার নিতে । কলকাতায় যাওয়া সম্ভবপর ছিল না বলে শান্তিনিকেতনের ইংরিজির ছাত্রী ঋতুশ্রী সেনগুপ্তকে বলেছিলুম টিমটাকে গাইড করতে । আমার নানা রোগের কথা শুনে জিত থাইল বললে, “ইওর ব্যাড কর্মা, ইট অলওয়েজ টেকস রিভেঞ্জ।” নিজে চিনাদের আফিমের আড্ডায় বাইশ বছর কাটিয়ে জ্ঞান দেবার মতন উপলব্ধি হয়েছে, আর বইটা বেস্ট সেলার হওয়ায় প্রচুর টাকা, বাড়ি, গাড়ি করে ফেলতে পেরেছে । অরবিন্দ প্রধান আমাকে বলেছিল, “আপনি বাংলায় লেখা ছেড়ে ইংরেজি ধরুন না।” ইংরেজিতে লেখার মতন শব্দভাঁড়ার তো নেই যে লিখব ।
আমি তাঁদেরই অনুবাদ করেছি আর সেই সব বিদেশি সাহিত্যিক আর ছবি-আঁকিয়ে সম্পর্কে লিখেছি যাঁদের ভেতরে ইমলিতলার ইনস্যানিটি ছিল, যাঁরা মিসফিট ছিলেন , যাঁরা আমার ইয়ারদোস্ত । পল গগাঁ আর দালির আত্মজীবনী অনুবাদ করেছি, জাঁ ককতোর দীর্ঘ কবিতা ‘ক্রুসিফিকেশান”, উলিয়াম ব্লেকের “স্বর্গ ও নরকের বিবাহ”, ব্লাইজি সঁদরার “ট্রান্সসাইবেরিয়ান এক্সপ্রেস”, ত্রিস্তান জারার ডাডাবাদী কবিতা আর ডাডাবাদী ইশতেহার, স্যুররিয়ালিস্ট ইশতেহার অনুবাদ করেছি । শার্ল বদল্যার, জাঁ আর্তুর র্যাঁবো আর অ্যালেন গিন্সবার্গের জীবনী লিখেছি । আলোচনা করেছি জেমস জয়েস, মার্সেল প্রুস্ত, আনা আখমাতোভা, জাঁ জেনে, চার্লি চ্যাপলিন, আদুনিস, পাবলো পিকাসো, ওকতাভিও পাজ, কার্লস ফুয়েন্তেস, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ প্রমুখ সম্পর্কে । বিট মহিলা কবিদের অনুবাদ করেছি, যাঁদের সংবাদ এতোকাল বাংলা ভাষায় এসে পৌঁছোয়নি।
ছেলে আর মেয়ে দুজনেই সপরিবারে বিদেশে, তাতে সুবিধা এই যে সিঙ্গল মল্ট, স্কচ আর আবসাঁথ নিয়মিত পাই, তবে করোনার কোপে তাদের আসা-যাওয়া আপাতত বন্ধ । বুড়ো-বুড়ি দুজনে মুম্বাইয়ের এক বেডরুমের ফ্ল্যাটে একে আরেকজনকে ঠেকনো দিয়ে আছি। দেয়ালের পাপড়ি খসে পড়েছে, ঘায়ের পেইনটিঙ প্রতিটি দেয়ালে-সিলিঙে, হাইওয়ের ওপর বলে ধুলোয় ধুলো ; করা যাবে না কিছুই, উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি হাঁপানি, প্রোস্টেট, হার্নিয়া, হাই ব্লাডপ্রেশার, অ্যানজাইনার ব্যথা, ভেরিকোজ ভেইনস, গ্লকোমা, আঙুলে আরথ্রাইটিস, অজ্ঞান হবার সিনকোপি । চিকিৎসার জন্যে এক-একজন ডাক্তারের কাছে এক-একটি অঙ্গ দিয়ে দিয়েছি; যখন যার ডাক পাই তার কাছে গিয়ে হাজিরা দিই ।
আর তো কলম ধরে লিখতে পারি না । ব্যাঙ্কের চেকে সই করতে হয় স্ত্রীকে । এক আঙুলে টাইপ করে কমপিউটারে লিখে চলেছি যতো দিন পারি । ফেসবুকে অজস্র বান্ধবী, হাইপাররিয়াল, যারা অবিরাম লেখার জন্য উৎসাহিত করে, ছোটোলোকের শেষবেলায় যৌবন ফিরিয়ে আনতে প্ররোচিত করে, যেন সাহিত্য জগতের বাইরে ঈথারের মহাবিশ্ব, কোনও দেশের সীমাকে মান্যতা দিতে চায় না ।








 বিশ্বজিত সেন | 223.177.62.180 | ০৭ নভেম্বর ২০২১ ১৯:১৩
বিশ্বজিত সেন | 223.177.62.180 | ০৭ নভেম্বর ২০২১ ১৯:১৩

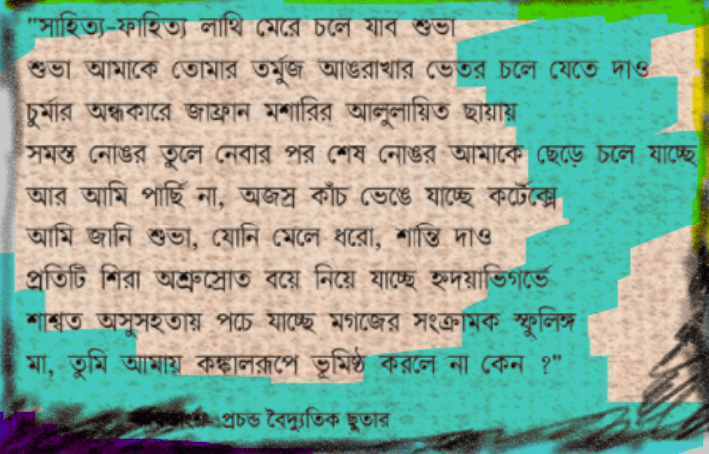
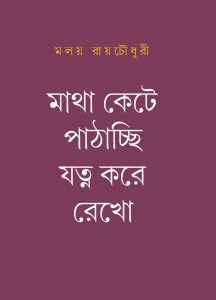 তুমি যদি ইউটিউব দ্যাখো তাহলে সবচেয়ে পঠিত যে কবিতাটা পাবে তা হল ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ আর আমার সাম্প্রতিক কবিতা ‘মাথা কেটে পাঠাচ্ছি যত্ন করে রেখো’। আলোচনা অবিরাম হয়ে চলেছে।
তুমি যদি ইউটিউব দ্যাখো তাহলে সবচেয়ে পঠিত যে কবিতাটা পাবে তা হল ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ আর আমার সাম্প্রতিক কবিতা ‘মাথা কেটে পাঠাচ্ছি যত্ন করে রেখো’। আলোচনা অবিরাম হয়ে চলেছে।