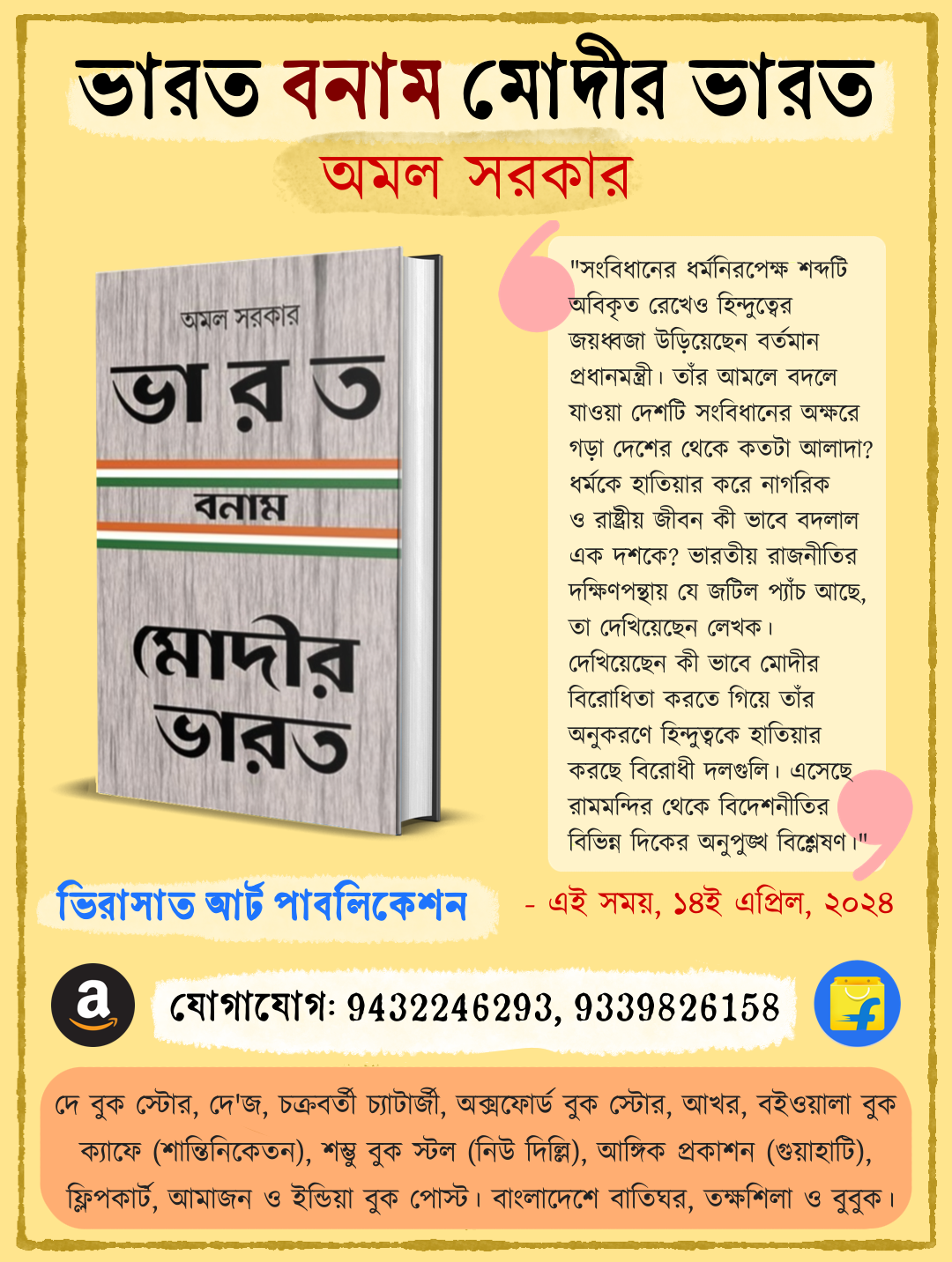- টইপত্তর অন্যান্য

-
১৯৭১ :: মুক্তিযুদ্ধের কথা
বিপ্লব রহমান
অন্যান্য | ০৯ ডিসেম্বর ২০১২ | ৪৯৫৩০♦ বার পঠিত
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
- Biplob Rahman | ২৯ অক্টোবর ২০১৪ ১৯:০৬582787
- বুদ্ধিজীবী হত্যাসহ ৮ অভিযোগ প্রমাণিত
নিজস্ব প্রতিবেদক, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম
Published: 2014-10-29 13:16:25.0 BdST Updated: 2014-10-29 14:07:19.0 BdST
একাত্তরে বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করতে বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা বাস্তবায়নে ভূমিকাসহ জামায়াতে ইসলামীর আমির মতিউর রহমান নিজামীর আট যুদ্ধাপরাধ আদালতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।
ঘটনার চার দশক পর বিচার শেষে বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ বুধবার এই রায় ঘোষণা করে।
প্রমাণিত আট অভিযোগের মধ্যে ২, ৪, ৬ ও ১৬ নম্বর ঘটনায় বুদ্ধিজীবী গণহত্যা, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, সম্পত্তি ধ্বংস, দেশত্যাগে বাধ্য করার দায়ে নিজামীর ফাঁসির রায় হয়েছে।
বিচারক বলেন, এই অপরাধের পরও যদি ফাঁসি না দেওয়া হয়, তাহলে তা হবে বিচারের ব্যর্থতা।
অপরাধে সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হওয়ায় ১, ৩, ৭ ও ৮ নম্বর অভিযোগে আটক, নির্যাতন, হত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের ষড়যন্ত্র ও সংঘটনে সহযোগিতার দায়ে জামায়াত আমিরকে দেওয়া হয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।
বাকি আট অভিযোগ প্রসিকিউশন প্রমাণ করতে না পারায় এসব অভিযোগ থেকে নিজামীকে খালাস দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল।
রায়ে বলা হয়, একাত্তরে জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি ও আল-বদর বাহিনীর প্রধান নিজামী নিজে বিভিন্ন অপরাধের ঘটনায় অংশগ্রহণ করেন। ৩ নম্বর অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের ষড়যন্ত্র ও সংঘটনে সহযোগিতা এবং ১৬ নম্বর অভিযোগে বুদ্ধিজীবী গণহত্যায় নিজামীর ‘সুপিরিয়র রেসপনসিবিলিটি’ প্রমাণিত হয়েছে।
২০১২ সালের ২৮ মে মতিউর রহমান নিজামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মধ্য দিয়ে এই জামায়াত নেতার বিচার শুরু হয়।
অভিযোগ-১: বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার চালানোর কারণে একাত্তরের ৪ জুন পাকিস্তানি সেনারা পাবনা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাওলানা কছিমুদ্দিনকে অপহরণ করে নূরপুর পাওয়ার হাউস ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে নিজামীর উপস্থিতিতে তার ওপর নির্যাতন চালানো হয়। ১০ জুন তাকে ইছামতী নদীর পাড়ে আরো কয়েকজনের সঙ্গে হত্যা করা হয়।
এ ঘটনায় আটক, নির্যাতন ও হত্যার অভিযোগ আনা হয় নিজামীর বিরুদ্ধে, যা আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইন ১৯৭৩-এর ৩ (২) (এ), ৪ (১), ৪ (২) এবং ২০ (২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
অভিযোগ-২: একাত্তরের ১০ মে বেলা ১১টার দিকে পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার বাউশগাড়ি গ্রামের রূপসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি সভা হয়। স্থানীয় শান্তি কমিটির সদস্য ও রাজাকারদের উপস্থিতিতে ওই সভায় নিজামী বলেন, শিগগিরই পাকিস্তানি সেনারা শান্তি রক্ষার জন্য আসবে। ওই সভার পরিকল্পনা অনুসারে পরে ১৪ মে ভোর সাড়ে ৬টার দিকে বাউশগাড়ি, ডেমরা ও রূপসী গ্রামের প্রায় সাড়ে ৪০০ মানুষকে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে। প্রায় ৩০-৪০ জন নারীকে সেদিন ধর্ষণ করে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা।
এ ঘটনায় নিজামীর বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ ও দেশত্যাগে বাধ্য করার অভিযোগ আনা হয়, যা ট্রাইব্যুনাল আইনের ৩ (২) (এ) ও (জি), ৪ (১), ৪ (২) এবং ২০ (২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
অভিযোগ-৩: মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মে মাসের শুরু থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোহাম্মদপুরের ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ব্যবহৃত হয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাম্প হিসাবে। রাজাকার ও আলবদর বাহিনীও সেখানে ক্যাম্প খুলে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালাতে থাকে। নিজামী ওই ক্যাম্পে নিয়মিত যাতায়াত ও মানবতাবিরোধী অপরাধের ষড়যন্ত্র করতেন বলে প্রসিকিউশনের অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।
এখানে মানবতাবিরোধী অপরাধের ষড়যন্ত্র ও সংঘটনে সহযোগিতার অভিযোগ আনা হয় নিজামীর বিরুদ্ধে, যা ট্রাইব্যুনাল আইনের ৩ (২) (এ), (জি) ও (এইচ), ৪ (১), ৪ (২) এবং ২০ (২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
অভিযোগ-৪: নিজামীর নির্দেশনা ও পরিকল্পনায় রাজাকার বাহিনী পাবনার করমজা গ্রামে হাবিবুর রহমান নামে একজনকে হত্যা করে। ১৯৭১ সালের ৮ মে নিজামীর রাজাকার ও আলবদর বাহিনী ওই গ্রাম ঘিরে ফেলে নয়জনকে হত্যা করে। রাজাকার বাহিনী একজনকে ধর্ষণসহ বাড়িঘরে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে।
এ ঘটনায় হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও সম্পত্তি ধ্বংসের অভিযোগ আনা হয় আসামির বিরুদ্ধে, যা ট্রাইব্যুনাল আইনের ৩ (২) (এ) ও (এইচ), ৪ (১), ৪ (২) এবং ২০ (২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
অভিযোগ-৫: ১৯৭১ সালের ১৬ এপ্রিল বেলা ১১টার দিকে নিজামীর সহযোগিতায় পাকিস্তানি সেনারা পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার আড়পাড়া ও ভূতেরবাড়ি গ্রামে হামলা চালিয়ে ২১ জন নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে। সেখানে বাড়িঘরে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগও করা হয়।
নিজামীর এ ঘটনায় হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ আনা হয়, যা ট্রাইব্যুনাল আইনের ৩ (২) (এ) ও (এইচ), ৪ (১), ৪ (২) এবং ২০ (২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
অভিযোগ-৬: নিজামীর নির্দেশে ১৯৭১ সালের ২৭ নভেম্বর পাবনার ধুলাউড়ি গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজতে যায় পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসর রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা। তারা গ্রামের ডা. আব্দুল আউয়াল ও তার আশেপাশের বাড়িতে হামলা চালিয়ে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ৫২ জনকে হত্যা করে।
এ ঘটনায় হত্যার অভিযোগ আনা হয় নিজামীর বিরুদ্ধে, যা ট্রাইব্যুনাল আইনের ৩ (২) (এ), ৪ (১), ৪ (২) এবং ২০ (২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
অভিযোগ-৭: একাত্তর সালের ৩ নভেম্বর মধ্যরাতে নিজামীর দেওয়া তথ্যে রাজাকার বাহিনীকে নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী পাবনার বৃশালিখা গ্রাম ঘিরে ফেলে মু্ক্তিযোদ্ধা আব্দুল লতিফ সেলিমের বাবা সোহরাব আলীকে আটক করে। তাকে রাস্তায় নিয়ে নির্মম নির্যাতনের পর স্ত্রী ও সন্তানদের সামনেই হত্যা করা হয়।
এ ঘটনায় নির্যাতন ও হত্যার অভিযোগ আনা হয় তখনকার বদর নেতা নিজামীর বিরুদ্ধে, যা ট্রাইব্যুনাল আইনের ৩ (২) (এ) ও (এইচ), ৪ (১), ৪ (২) এবং ২০ (২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
অভিযোগ-৮: একাত্তরের ৩০ আগস্ট ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি ও আলবদর বাহিনীর প্রধান নিজামী তার সংগঠনের তখনকার সেক্রেটারি আলী আহসান মুজাহিদকে সঙ্গে নিয়ে নাখালপাড়ার পুরোনো এমপি হোস্টেলে যান এবং সেখানে আটক মুক্তিযোদ্ধা জহির উদ্দিন বিচ্ছু জালাল, বদি, রুমি (শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ছেলে), জুয়েল ও আজাদকে দেখে তাদের গালিগালাজ করেন। পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনকে নিজামী বলেন, রাষ্ট্রপতির সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আদেশের আগেই তাদের হত্যা করতে হবে। নিজামীর পরামর্শ অনুযায়ী পরে জালাল ছাড়া বাকি সবাইকে হত্যা করা হয়।
এ ঘটনায় নিজামীর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়, যা ট্রাইব্যুনাল আইনের ৩ (২) (এ), ৪ (১), ৪ (২) এবং ২০ (২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
অভিযোগ-৯: নিজামী ও রাজাকার বাহিনীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পাকিস্তানি বাহিনী পাবনার বৃশালিখা গ্রাম ঘিরে ফেলে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রফুল্ল, ভাদু, মানু, স্বস্তি প্রামানিক, জ্ঞানেন্দ্রনাথ হাওলাদার ও পুতুলসহ ৭০ জনকে হত্যা ও ৭২টি ঘরে অগ্নিসংযোগ করে।
এ ঘটনায় একটি সম্প্রদায়কে নির্মূল করতে গণহত্যা চালানোর অভিযোগ আনা হয় নিজামীর বিরুদ্ধে, যা ট্রাইব্যুনাল আইনের ৩ (২) (এ), (সি), (আই), ৪ (১), ৪ (২) এবং ২০ (২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
অভিযোগ-১০: মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে পাবনার সোনাতলা গ্রামের অনিল চন্দ্র কুণ্ডু নিরাপত্তার জন্য ভাই-বোনদের নিয়ে ভারতে চলে যান। পরে অগাস্টে তিনি এলাকায় ফিরে আসেন। নিজামীর নির্দেশে রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা তার এবং আশেপাশের বহু মানুষের বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।
এ ঘটনায় নিপীড়নের অভিযোগে আনা হয় আসামির বিরুদ্ধে, যা ট্রাইব্যুনাল আইনের ৩ (২) (এ), ৪ (১), ৪ (২) এবং ২০ (২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
অভিযোগ-১১: একাত্তরের ৩ অগাস্ট চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউটে ইসলামী ছাত্রসংঘের এক সভায় নিজামী বলেন, পাকিস্তান আল্লাহর ঘর। সেনাবাহিনীর মাধ্যমে তিনি প্রিয় ভূমির হেফাজত করছেন। দুনিয়ার কোনো শক্তি পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে পারবে না। সেদিন তার উপস্থিতিতেই নিরীহ বাঙালিদের ওপর হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের জন্য ইসলামী ছাত্র সংঘ, আলবদর, রাজাকারদের মতো সহযোগী বাহিনীগুলোকে উসকানি দেওয়া হয়।
ওই ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের উসকানির অভিযোগ আনা হয় নিজামীর বিরুদ্ধে, যা ট্রাইব্যুনাল আইনের ৩ (২) (এফ), ৪ (১), ৪ (৩) এবং ২০ (ই) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
অভিযোগ-১২: একাত্তরের ২২ অগাস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক একাডেমি হলে আল মাদানীর স্মরণসভায় নিজামী বলেন, যারা পাকিস্তানকে ভাঙতে চায়, তারা ইসলামের শত্রু। পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে ইসলামের শত্রুরা অস্ত্র হাতে নিয়েছে মন্তব্য করে পাকিস্তানের শত্রুদের নির্মূল করার আহ্বান জানান তিনি।
ওই ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের উসকানির অভিযোগ আনা হয় নিজামীর বিরুদ্ধে, যা ট্রাইব্যুনাল আইনের ৩ (২) (এফ), ৪ (১), ৪ (২) এবং ২০ (২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
অভিযোগ-১৩: ওই বছর ৮ সেপ্টেম্বর প্রতিরক্ষা দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে ইসলামী ছাত্রসংঘের সভায় নিজামী বলেন, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় হিন্দুস্তানের মূল ভূখণ্ডে আঘাত হানতে রাজাকার, আলবদর সদস্যরা প্রস্তুত। উসকানিমূলক ওই বক্তব্যে মুক্তিকামী বাঙালিকে ভারতের সহযোগী হিসেবেও উল্লেখ করা হয়।
ওই ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের উসকানির অভিযোগ আনা হয় নিজামীর বিরুদ্ধে, যা ট্রাইব্যুনাল আইনের ৩ (২) (এফ), ৪ (১), ৪ (২) এবং ২০ (২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
অভিযোগ-১৪: মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১০ সেপ্টেম্বর যশোরে রাজাকারদের প্রধান কার্যালয়ে এক সুধী সমাবেশে নিজামী প্রত্যেক রাজাকারকে ইমানদারির সঙ্গে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আল্লাহর পথে কেউ কখনো হত্যা করে, কেউ মারা যায়। এসব বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ছাত্রসংঘের সদস্য, রাজাকার ও অন্যদের মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের উসকানি ও প্ররোচনা দেন নিজামী।
ওই ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের উসকানির অভিযোগ আনা হয় নিজামীর বিরুদ্ধে, যা ট্রাইব্যুনাল আইনের ৩ (২) (এফ), ৪ (১), ৪ (২) এবং ২০ (২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
অভিযোগ-১৫: একাত্তরের মে মাস থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাঁথিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে রাজাকার ক্যাম্প ছিল। নিজামী প্রায়ই ওই ক্যাম্পে গিয়ে রাজাকার সামাদ মিয়ার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়।
ওই ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের ষড়যন্ত্র ও সহযোগিতার অভিযোগ আনা হয় নিজামীর বিরুদ্ধে, যা ট্রাইব্যুনাল আইনের ৩ (২) (জি) ও (এইচ), ৪ (১), ৪ (২) এবং ২০ (২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
অভিযোগ-১৬: মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির বিজয়ের ঊষালগ্নে অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে আলবদর বাহিনী। দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পিতভাবে আলবদর সদস্যরা ওই গণহত্যা ঘটায়। জামায়াতের তৎকালীন ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘ ও আলবদর বাহিনীর প্রধান হিসেবে ওই গণহত্যার দায় নিজামীর ওপর পড়ে।
একটি জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যার ওই ঘটনায় গণহত্যার অভিযোগ আনা হয় নিজামীর বিরুদ্ধে, যা ট্রাইব্যুনাল আইনের ৩ (২) (সি) (আই), ৪ (১), ৪ (২) এবং ২০ (২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
http://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article873429.bdnews
- Biplob Rahman | ২৯ অক্টোবর ২০১৪ ১৯:১৫582788
- WAR CRIMES TRIAL
Death for Nizami
ICT finds the Al-Badr chief guilty in 8 out of 16 charges; defence to appeal
Star Online Report
Law enforcers take war criminal Motiur Rahman Nizami to a police van after on Wednesday. A special tribunal handed death penalty to the Jamaat-e-Islami chief of four charges of war crimes, which include the killings of intellectuals at the fag end of the Liberation War in 1971. Photo: Rashed Shumon
Law enforcers take war criminal Motiur Rahman Nizami to a police van after on Wednesday. A special tribunal handed death penalty to the Jamaat-e-Islami chief of four charges of war crimes, which include the killings of intellectuals at the fag end of the Liberation War in 1971. Photo: Rashed Shumon
A special tribunal in Dhaka today handed death penalty to Jamaat-e-Islami chief Motiur Rahman Nizami of four charges of war crimes, which include the killings of intellectuals at the fag end of the 1971 Liberation War.
The 71-year-old has also been awarded life sentence in four other charges as the International Crimes Tribunal-1 found him guilty in total eight out of 16 charges levelled against him in a historic trial that began almost 40 years after Bangladesh's war of independence.
The court said Nizami, though claimed to be an Islamic scholar, misinterpreted Quran to encourage his followers to conduct a massive genocide, advocate Haidar Ali, a member of the prosecution told journalists after the verdict.
Meantime, the defence termed the verdict "not based on evidence", and said it would appeal against the verdict with the Supreme Court.
"Whatever is being told against me is false," defence counsel Tajul Islam quoted the convict as saying in his reaction after the verdict.
Hailing the verdict, different social-cultural organisations including Gonojagoron Mancha brought out processions in the capital, Dhaka.
Nizami, Jamaat ameer since November 2000, has already been given death penalty in the sensational 10-truck arms haul case in January this year.
President of the then Jamaat student wing Islami Chhatra Sangha that turned into Pakistan army's infamous auxiliary force Al-Badr during the Liberation War, was arrested on June 29, 2010, in a criminal case and later shown arrest in war crimes cases.
With Nizami, six top Jamaat leaders have already been punished for their 1971 crimes. Two other top leaders are now being tried in war crimes tribunals the Awami League-led government formed in 2010 to bring the perpetrators of 1971 to book.
Court sits amid tightened security
Amid tightened security in and around the court premises, law enforcers took Nizami to ICT-1 premises around 9:20am.
Transport movement was halted from Doel Chattar to High Court Mazar area since the morning in a move to ward off any attempt to create violence by Jamaat, which fought tooth and nail against the birth of Bangladesh in 1971, and his associate bodies.
Five minutes after Nizami was produced before the tribunal, the judges took to the dais at 11:05am.
M Enayetur Rahim, chairman of the three-member judges' panel of the International Crimes Tribunal-1, delivered an introductory speech for five minutes on why the judgement was delayed.
He cited resignation of the tribunal chairman and the new chairman's going into retirement as key reasons for the delay in the much-awaited trial.
Later, Justice Anwarul Haque explained the 16 charges levelled against Nizami.
After he completed, the other judge of the panel, Justice Jahangir Hossain, started reading out summary of the 204-page verdict.
Justice Enayetur Rahim pronounced the order.
Earlier yesterday, Nizami was shifted from Kashimpur jail to Dhaka Central Jail around 8:00pm. There, jail doctors conducted a health check-up and found him sound, Farman Ali, senior jail super of Dhaka jail, told The Daily Star last night.
Longest of war trial
The ICT-1 framed 16 charges against Nizami on May 28, 2012. According to the charges, Nizami had conspired with the Pakistani army, planned and incited crimes; was complicit in murders, rapes, looting and destruction of property; and was responsible for commissioning of internationally recognised wartime crimes in 1971.
But, it took around one and a half years for the completion of the trial, thanks to the lack of preparation of the prosecution and a range of dilatory tactics of the defence.
The tribunal first kept the case awaiting verdict on November 13 last year. But the proceeding faced further delay when tribunal's chairman Justice ATM Fazle Kabir went on retirement without delivering the judgment. His successor reheard the closing arguments and kept the verdict waiting again on March 24.
The tribunal could not deliver verdict on June 24 due to Nizami's sudden "illness" forcing the court to keep it waiting again.
The Jamaat chief played a key role in forming the four-party alliance ahead of the 2001 election and led his party to taste state power along with their key ally the BNP.
He and Jamaat's second man, Ali Ahsan Mohammad Mojaheed, who was convicted in war crimes last year, became members of Khaleda Zia's cabinet, amid protests from the country's pro-liberation minds.
EU calls for commuting sentence
The European Union has called for commuting Nizami's death sentence and to introduce a moratorium on executions as a first step towards definitive abolition of capital punishment.
"The case of Motiur Rahman Nizami has now reached a stage where an execution of the death sentence constitutes a serious threat," said a statement of EU Delegation to Bangladesh.
Published: 9:57 am Wednesday, October 29, 2014
Last modified: 7:33 pm Wednesday, October 29, 2014
http://www.thedailystar.net/death-for-nizami-47912
- Biplob Rahman | ২৯ অক্টোবর ২০১৪ ১৯:১৭582789
- 8 charges Nizami found guilty for
Star Online Report
The International Crimes Tribunal has found involvement of Jamaat-e-Islami chief Jamaat-e-Islami chief Motiur Rahman Nizami in eight wartime offences including genocide to eliminate intellectuals and professionals.
Of the eight charges, Nizami has been to death penalty for four charges while life term imprisonment for the other charges.
CHARGES NIZAMI AWARDED DEATH PENALTY FOR
1. Conspiring to commit crimes, and cause the killings of 450 people, rape of 30-40 women and deportation of the villagers of Baousgari, Ruposhi and Demra in Pabna on May 14, 1971.
2. Complicity in murder, rape, looting and destruction of properties at Karamja of Pabna on May 8, 1971.
3. Command responsibility for and involvement in the murder of 30 people of Dhulaura village on November 27, 1971.
4. Act of genocide to eliminate intellectuals and professionals.
LIFE TERM INPRISONMENT FOR
1. Causing the arrest, detention, torture and murder of three people including head maulana Kasim Uddin of Pabna Zilla School on June 4, 1971.
2. Complicity in torture, murder and rape at Mohammadpur Physical Training Institute in Dhaka during the war.
3. Complicity in torture and murder of Sohrab Ali on December 3, 1971.
4. Murder of Bodi, Rumi, Jewel and Azad at the Old MP Hostel on August 30, 1971.
Published: 10:49 am Wednesday, October 29, 2014
Last modified: 5:57 pm Wednesday, October 29, 2014
TAGS: Jamaat-e-Islami war crimes Liberation War Motiur Rahman Nizami International Crimes Tribunal-1 Al-Badr ameer
http://www.thedailystar.net/death-for-nizami-47912
- সিকি | ২৯ অক্টোবর ২০১৪ ১৯:২৪582790
- বিপ্লব ভাই, অনেক অনেক অভিনন্দন। পুরো বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানাই।
- Biplob Rahman | ০৮ ডিসেম্বর ২০১৪ ১৯:২৩582791
- ০১ ডিসেম্বর, ২০১৪ ০২:৫১:২০ | আপডেট : ০১ ডিসেম্বর, ২০১৪ ১৪:৫৭:৫৩
খেতাবপ্রাপ্ত এবং শহীদরাও সনদ হারাতে পারেন
মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, একাত্তরের ২৬ মার্চ মুক্তিযোদ্ধার সর্বনিম্ন বয়স হতে হবে ১৫ বছর।
রাজীব নূর
মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য খেতাবপ্রাপ্তদেরও কেউ কেউ হারাতে পারেন মুক্তিযোদ্ধার সনদ। গত ১৩ অক্টোবর সরকারের মুক্তিযোদ্ধাবিষয়ক যাবতীয় কাজকর্ম দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের (জামুকা) এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, একাত্তরের ২৬ মার্চ মুক্তিযোদ্ধার সর্বনিম্ন বয়স হতে হবে ১৫ বছর। জামুকার এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে একাত্তরে যাদের বয়স ১৫ বছরের নিচে ছিল এমন হাজার বিশেক মুক্তিযোদ্ধা তাদের সনদ নিয়ে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়বেন। মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখসমরে গৌরবোজ্জ্বল লড়াই করে শহীদ হওয়া কিশোররাও আর মুক্তিযোদ্ধা থাকবেন না। খেতাবপ্রাপ্ত এবং শহীদরাও সনদ হারাতে পারেন
বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ প্রায় চার লাখই ছিল শিশু-কিশোর। যুদ্ধের সময় যে নারীরা সম্ভ্রম হারিয়েছিলেন তাদেরও অর্ধেকের বেশি ছিলেন কিশোরী। জামুকা মুক্তিযোদ্ধাদের যে নতুন সংজ্ঞা প্রস্তাব করেছে, তাতে একাত্তরে সম্ভ্রম হারানো নারীরা মুক্তিযোদ্ধার সম্মানে ভূষিত হতে যাচ্ছেন। এটা পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে।
গত ১৩ অক্টোবর জামুকার বৈঠকে মুক্তিযোদ্ধাদের বয়স একাত্তরের ২৬ মার্চ ১৫ বছর নির্ধারণ করার পর দেশব্যাপী প্রবল আপত্তি উঠে। অথচ এসব আপত্তি উপেক্ষা করে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চে ১৫ বছর বয়স ধরেই মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য গত ৫ নভেম্বর সারসংক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।
মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক অবশ্য সমকালের সঙ্গে আলাপে নিশ্চিত করেছেন, জামুকা নূ্যনতম বয়স নির্ধারণের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এটি একটি মানদণ্ড, এই মানদণ্ড সর্বসাধারণের জন্য প্রযোজ্য হবে। যেসব কিশোর মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য খেতাব পেয়েছেন তাদের খেতাব বহাল থাকবে। খেতাবপ্রাপ্ত এই মুক্তিযোদ্ধাদের নতুন করে যাচাই-বাছাইয়ের আওতায় আসতে হবে না। মন্ত্রী জানান, জামুকার বৈঠকে বীর কিশোর মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। ধারণা করা হয়, সারাদেশে তাদের সংখ্যা মাত্র কয়েকশ' হবে।
একাত্তরের বীর কিশোর মোজাম্মেল হক বীরপ্রতীক এ ব্যাপারে বলেন, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী বলছেন, মুক্তিযোদ্ধার বয়স যদি নূ্যনতম ১৫ বছর নির্ধারণ করা হয়ও, তা খেতাবপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে নয়, সর্বসাধারণের জন্য প্রযোজ্য হবে। এই সর্বসাধারণ বলতে তিনি কি ভুয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বোঝাচ্ছেন? ভুয়াদের জন্য প্রকৃত যোদ্ধারা কেন অসম্মানের মধ্যে পড়বেন? এটা তো ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় করার মতো কাজ হচ্ছে।
মহাজোট সরকারের আগের মেয়াদে মুক্তিযোদ্ধা চাকরিজীবীদের চাকরির মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া এবং সরকারি চাকরিতে নিয়োগ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও পোষ্যদের কোটা আগের তুলনায় বাড়িয়ে দেওয়ার কারণে মুক্তিযোদ্ধার সনদ সংগ্রহে হিড়িক পড়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধে যাননি, এমন অনেকে অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধার সনদ সংগ্রহ করেন। সচিব পর্যায় থেকে শুরু করে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও মিথ্যা তথ্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধা সনদ সংগ্রহ করে বিতর্কের সৃষ্টি করেন। এরই মধ্যে চার সচিবের সনদ বাতিলও হয়েছে। তাদের কারও কারও বয়স একাত্তরে ১৫ বছরের কম ছিল বলেই জামুকা নতুন সংজ্ঞায় মুক্তিযোদ্ধার নূ্যনতম বয়স নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
স্বাধীনতার ৪৩ বছরে বারবার মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা পুনর্নির্ধারণ এবং মুক্তিযোদ্ধার নির্ভুল তালিকা প্রণয়ন করতে গিয়ে সংকট বেড়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। বঙ্গবন্ধুর শাসনকালে ১৯৭২ সালে ঘোষিত 'দি বাংলাদেশ (ফ্রিডম ফাইটারস) ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অর্ডার' অনুযায়ী নির্ধারিত মুক্তিযোদ্ধার প্রথম সংজ্ঞা ১৯৭৫ সালের পর এসে পরিবর্তিত হয়েছে। পরে একেক সময় একেক ধরনের সংজ্ঞা নির্ধারণের কারণে নতুন নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্র্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) হেলাল মোর্শেদ খান বীরবিক্রম বলেন, কারা মুক্তিযোদ্ধা_ সেটি ১৯৭২ সালের আদেশে স্পষ্ট রয়েছে। এটি নিয়ে বারবার বিতর্ক সৃষ্টি করে মুক্তিযোদ্ধাদের হেয় করা হচ্ছে। তার মতে, মুক্তিযোদ্ধার নতুন সংজ্ঞাটি যেভাবে প্রস্তাব করা হয়েছে, তা অনুমোদন পেলে একাত্তরে যারা কিশোর ছিলেন, তাদের জন্য রীতিমতো বিব্রতকর হবে।
একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নির্বাহী সভাপতি শাহরিয়ার কবির বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বয়সে বেঁধে ফেলা ঠিক হবে না। মুক্তিযুদ্ধের যেসব দলিল রয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে ১২-১৩ বছরের কিশোররাও অসাধারণ অবদান রেখেছেন। বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখতে গিয়ে অনেকে শহীদ হয়েছেন। এই যে আমাদের কিশোর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল, তিনি তো বীরপ্রতীক। একাত্তরে তার বয়স কত ছিল, ক্লাস নাইনে পড়তেন। ক্লাস এইট-নাইনের শিক্ষার্থীরাও অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন।
সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজের চেয়ারম্যান ও প্রধান গবেষক মেজর (অব) কামরুল হাসান ভুঁইয়া বীরপ্রতীক ২০১৩ সালে প্রকাশিত তার 'মুক্তিযুদ্ধে শিশু-কিশোরদের অবদান' বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, 'সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রেণী ও বয়সানুযায়ী একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় মোট মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা (যুদ্ধ করতে সক্ষম প্রাক্তন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বাঙালি সৈনিক, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যসহ) ১,২০,০০০। বন্ধনীর মধ্যে সৈনিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪২,০০০। অর্থাৎ গণযোদ্ধা ছিল (১,২০,০০০ _ ৪২,০০০)= ৭৮,০০০। এই ৭৮,০০০ গণযোদ্ধার প্রায় ২৩ শতাংশ ছিল শিশু-কিশোর অর্থাৎ ১৭,৯৪০।'
'মুক্তিযুদ্ধে শিশু-কিশোরদের অবদান' বইয়ে পরিবেশিত এ পরিসংখ্যান সম্পর্কে জানতে চাইলে কামরুল হাসান ভুঁইয়া সমকালকে বলেন, 'শিশু-কিশোর মুক্তিযোদ্ধার এ সংখ্যাটি একটি যুক্তিনির্ভর অনুমান। সংখ্যাটি একটু কমবেশি হতে পারে।'
'একাত্তরের বীরযোদ্ধা : খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা' বইয়ের সংগ্রাহক ও গ্রন্থনাকারী রাশেদুর রহমান সমকালকে বলেন, জামুকার এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে অন্তত চারজন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সনদ বাদ পড়বে। তাদের মধ্যে রয়েছেন শহিদুল ইসলাম লালু, মোজাম্মেল হক, আবু সালেক ও তারামন বিবি।
মুক্তিযুদ্ধে কিশোরদের অবদান নিয়ে গবেষণায় নিযুক্ত মোস্তফা হোসেইন সমকালকে বলেন, শহিদুল ইসলাম লালু, মোজাম্মেল হক, আবু সালেক ও তারামন বিবি ছাড়াও বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্তদের মধ্যে মতিউর রহমান, রফিকুল ইসলাম, বশির আহমেদ, নূর ইসলাম, বাহাউদ্দিন রেজা ছিলেন স্কুলপড়ুয়া। তিনি বলেন, কিশোরের বয়স যদি ১৮ পর্যন্ত ধরা হয় তাহলে খেতাবপ্রাপ্তদের মধ্যে অন্তত ২২জন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন।
তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে মাঠপর্যায়ে গবেষণার অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চিত হয়েছি, মুক্তিযোদ্ধাদের অর্ধেকেরও বেশি ছিলেন ছাত্র এবং তাদের অর্ধেকেরও বেশি ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সী। তবে ১৫ বছরের কম বয়সী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা হবে ২০ হাজারের মতো।
http://www.samakal.net/2014/12/01/102074
- Biplob Rahman | ০৮ ডিসেম্বর ২০১৪ ১৯:২৪582792
- বঙ্গবন্ধুর বীর বিচ্ছু লালু
বঙ্গবন্ধু এক কিশোরকে ভালোবেসে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। সেটা ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারির ঘটনা
রাজীব নূর
বঙ্গবন্ধু এক কিশোরকে ভালোবেসে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। সেটা ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারির ঘটনা। টাঙ্গাইলে বিন্দুবাসিনী স্কুলে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণের এক অনুষ্ঠানে কিশোরটির বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের বিবরণ শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে তাকে কোলে তুলে নিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আদর করে নাম দিলেন 'বীর বিচ্ছু'।বঙ্গবন্ধুর বীর বিচ্ছু লালু
সেই বীর বিচ্ছুর ভালো নাম শহীদুল ইসলাম। অবশ্য যুদ্ধের সময়েই আরও একটি নতুন নাম জুটেছিল তার। ভারতের তুরা ক্যাম্পে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণকালে ভারতীয় বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সমজিৎ সিং আদর করে শহীদুল ইসলামকে ডাকতেন 'লালু' বলে। মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব বিবেচনায় বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্তদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এই লালুর মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়াটা খুব সহজ ছিল না। পিতৃ-মাতৃহীন লালু যুদ্ধে যোগ দিতে গেলে মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন পাহাড়ি ভেবেছিলেন, মাত্র ১২-১৩ বছরের এই ছেলে যুদ্ধ করবে কী করে!
তাই লালুকে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে ফাই-ফরমাশ খাটা ও অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কারের কাজ দেন তিনি। অবশ্য এই কাজের ফাঁকেই তিনি নিজের আগ্রহে শিখে নিয়েছিলেন কীভাবে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয়, অস্ত্র চালাতে হয়, গ্রেনেড ছুড়তে হয়, নিতে হয় শত্রুর গতিবিধির খবর।
এইটুকু অভিজ্ঞতা সম্বল করেই কাদেরিয়া বাহিনীর হয়ে যুদ্ধে নামেন তিনি। যুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতে গ্রুপ কমান্ডার পাহাড়ি তাকে নির্দেশ দেন গোপালপুর থানা রেকি করে আসতে। লালু সেখানে গিয়ে তার দূরসম্পর্কের ভাই সিরাজের দেখা পান। সিরাজ পাকিস্তানি সেনাদের দালালি করছে। সেও লালুকেও একই কাজ করার প্রস্তাব দেয়। নিজের পরিচয় গোপন করে ভাইয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান লালু। কয়েক দিন থানায় কাজ করে পাকিস্তানিদের আস্থা অর্জন করেন।
এর আগে ১৯৭১ সালের ৭ অক্টোবর রাতে মুক্তিযোদ্ধারা হামলা করে পরদিন ৮ অক্টোবর পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়েও থানাটি দখল করতে পারেননি। লালু ওই থানায় কয়েক দিন কাজ করার পর মুক্তিযোদ্ধাদের পরিকল্পনামাফিক একদিন তিনটি গ্রেনেড নিয়ে থানায় হাজির হন। পুরো পুলিশ স্টেশন একবার চক্কর মেরে এসে এক বাংকারে প্রথম গ্রেনেড ছুড়লেন লালু। ভীত ও হতভম্ব পাকিস্তানিরা আন্দাজে গুলি ছুড়তে শুরু করে লক্ষ্যহীনভাবে। শুয়ে পড়েন লালু। শুয়ে থেকেই দ্বিতীয় গ্রেনেডটি ছুড়লেন, কিন্তু সেটা বিস্ফোরিত হলো না। তৃতীয় গ্রেনেডটি সশব্দে অন্য একটি বাংকারে বিস্ফোরিত হলো। ওই দিন লালুর দুঃসাহসিক হামলায় গোপালপুর থানায় পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগীসহ আটজন নিহত হয়। আহত হয় অনেকে।
গোপালপুর থানার জয়ে অবদানের জন্যই বীরপ্রতীক খেতাব পান লালু। গোপালপুরের যুদ্ধ ছাড়াও কয়েকটি গেরিলা যুদ্ধে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, তিনি যে বীরপ্রতীক খেতাব পেয়েছেন- তা তার নিজেরই জানা ছিল না অনেক দিন। জেনেছেন বহু পরে, ১৯৯৮ সালে। ততদিনে তার প্রথম সন্তান মুক্তার জন্ম হয়েছে। অভাব-অনটনকে সঙ্গী করে জীবনের অনেক পথ পাড়ি দিয়েছেন তিনি। লালুর স্ত্রী মালা বেগম বলেন, আগেও লোকটা মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতেন। আমার বিশ্বাস হতো না। ভাবতাম, এত বড় যোদ্ধা হলে কি এমন দরিদ্র অবস্থা হয়?
গত নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে একদিন মালা বেগম ও তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ হলো মিরপুরে চিড়িয়াখানা সংলগ্ন এলাকার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের বাসায়। এ বাসাতেই কেটেছে লালুর জীবনের শেষ দিনগুলো। এখানেই ২০০৯ সালের ২৫ মে মারা যান লালু।
মালা বেগম জানালেন, অভাব তখনও ছিল তার নিত্যসঙ্গী। বীর এ মুক্তিযোদ্ধা সারাজীবনই কাটিয়েছেন চরম দারিদ্র্যের মধ্যে।
মালা বেগম বলেন, শুনেছি, জীবিকার তাগিদে হাসপাতালের ওয়ার্ডবয়ের চাকরি নিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের পরপরই। কখনও রেলস্টেশনে কুলির কাজ করেছেন, হোটেলের বাসন মেজেছেন; আবার কখনও বাবুর্চির কাজ করেছেন। জীবনের শেষদিকে এসে ঠেলাগাড়িতে চা বিক্রি করেছেন। ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশের এ-জেলা ও-জেলা।
ঘুরতে ঘুরতে মুন্সীগঞ্জে গিয়ে পরিচয় হয় মালা বেগমের এক আত্মীয়ের সঙ্গে। ততদিনে লালুর প্রথম স্ত্রী মারা গেছেন। প্রস্তাব পাঠান মালার পরিবারের কাছে। পারিবারিক সম্মতিতে তাদের বিয়ে হয়। তবে মিরপুরের বাসায় এসেছেন ছেলে আকতারের জন্মের পর। বাসা বলতে টিনশেডের লম্বা দুটি ঘর। ঘরগুলো আবার ছোট কয়েকটি খুপড়িতে ভাগ করা। খুপড়িগুলো ভাড়া দিয়ে কোনো রকমে দিন চলে মালা বেগমের। অবশ্য এখন মাসে ছয় হাজার টাকা মুক্তিযোদ্ধা ভাতা পাচ্ছেন।
লালু ও মালার চার ছেলেমেয়ের মধ্যে সবার বড় মুক্তার বিয়ে হয়েছে। দ্বিতীয় সন্তান আকতার পড়েছেন ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত। বাবার মৃত্যুর পর পড়াশোনা চালাতে না পেরে বাসের হেলপারের কাজ নিয়েছিলেন। হেলপারের কাজ করতে করতে ড্রাইভিংটাও শিখে ফেলেছেন। তৃতীয় সন্তান সোহাগ ইন্টারমিডিয়েটে এবং চতুর্থ সন্তান হালিমা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ছে। সোহাগ একজন ভালো ক্রিকেটারও।
মালা বেগম বললেন, বড় ছেলেটার যদি একটা চাকরি হতো তাহলে ছোট ছেলেমেয়ে দুটিকে তিনি আরও ভালোভাবে মানুষ করতে পারতেন। বড় ছেলে আকতার ড্রাইভিং জানলেও ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকায় এখনও হেলপারের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। বিদায় দেওয়ার সময় মালা জানতে চান, সরকার কি বীর মুক্তিযোদ্ধা লালুর ছেলেকে ড্রাইভারের একটা চাকরি দিতে পারে না?
http://www.samakal.net/2014/12/02/102328
- Biplob Rahman | ০৮ ডিসেম্বর ২০১৪ ১৯:২৬582793
- প্রকাশ : ০৩ ডিসেম্বর, ২০১৪ ০০:৩০:০৬
পিতৃহত্যার বদলা নিতে যুদ্ধে গিয়েছিলেন আবু সালেক
রাজীব নূর
খুঁজতে গিয়েছিলাম কিশোর মুক্তিযোদ্ধা আবু সালেককে। তার গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার মনিয়ন্দ ইউনিয়নের টানমান্দাইল গ্রামের ঠিকানা ধরে। ভুল ভাঙল ওই এলাকায় গিয়ে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সেই কিশোর মুক্তিযোদ্ধা আবু সালেকের গ্রামের নাম এখন হাশেমপুর। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত আবু সালেকের বাবা শহীদ আবুল হাশেমের নামানুসারে গ্রামটির নামকরণ করা হয় হাশেমপুর। স্থানীয় ধরখার-আখাউড়া চেকপোস্ট-আগরতলা সড়কের ধরখার মৌজায় অবস্থিত হাশেমপুর গ্রামটির আগের নাম ছিল হাটামাথা।
যুদ্ধের প্রশিক্ষণের সময় কার ক্যামেরায় ধরা পড়েছিলেন তা জানা নেই আবু সালেকেরও সংগৃহীত
যুদ্ধের প্রশিক্ষণের সময় কার ক্যামেরায় ধরা পড়েছিলেন তা জানা নেই আবু সালেকেরও সংগৃহীত
ধরখার-আগরতলা সড়কের আখাউড়া অভিমুখী পথে ডান পাশের পাকা ঘরটি আবু সালেকের। চার কক্ষবিশিষ্ট ঘরটিতে আবু সালেকের স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে থাকেন। ওই ঘরের একটি কক্ষে গিয়ে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে সম্মাননা নেওয়ার বড় একটি ছবি দেয়ালে সাঁটানো। এ ছাড়া আলমারিতে কিছু সম্মাননা স্মারক
সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বাড়িতে গিয়ে আবু সালেককে পাওয়া গেল না।
আবু সালেকের বড় ছেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজের স্নাতক প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী মোস্তাফিজুর রহমান রুবেল জানান, তার বাবা বেশিরভাগ সময় চাকরিস্থল সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় থাকেন।
রুবেলের দেওয়া মোবাইল ফোন নম্বরে যোগাযোগ করা হলে আবু সালেক বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। সেনাবাহিনী ছাড়ার পর থেকে সরকারি পাট ক্রয় কেন্দ্রে সাধারণ একজন কর্মচারী হিসেবে চাকরি করছেন। পাট ক্রয় কেন্দ্রে যোগদানের পর চট্টগ্রামে কাজ করেছেন কিছুদিন। সেখান থেকে বদলি হয়ে চলে যান সিরাজগঞ্জে।
আবু সালেক জানান, আশির দশকের শুরুর দিকে তাদের গ্রামের নাম হাশেমপুর রাখা হয়। তার বাবার হত্যাকারীদের মূল হোতা রাজাকার মোবারকের ফাঁসির আদেশ হয়েছে। সালেক জানান, একাত্তরে এই মোবারক ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর রোকন। পরে মোবারক আওয়ামী লীগে যোগ দিলে তারা ব্যথিত বোধ করেছিলেন। এখন অপেক্ষা করছেন বাবার হত্যাকারীর ফাঁসি দেখবেন বলে।
আবু সালেক তার বাবা হত্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে জানান, যুদ্ধের সময় ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে তার বাবা আবুল হাশিম, চাচা আবদুল খালেক, গোলাম মাওলা, চাচাতো ভাই তারা চানসহ টানমান্দাইল ও জাঙ্গাল গ্রামের ৩৩ জন সাধারণ মানুষকে স্থানীয় গঙ্গাসাগর দীঘির পাড়ে ধরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছিল। এর আগে তাদের দিয়েই গর্ত খোঁড়া হয়। ওই ফায়ারিং স্কোয়াড থেকে তার বড় ভাই আবুল খায়ের মাস্টার ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। আবুল খায়েরকে মৃত ভাবা হয়েছিল। পরে ভাসতে ভাসতে গঙ্গাসাগর দীঘি পাড় হয়ে বাড়িতে ফিরেছিলেন তিনি।
বাবা, চাচাসহ ৩৩ জনের গণহত্যার ঘটনা প্রতিশোধস্পৃহা তৈরি করে আবু সালেকের মনে। সে সময় তিনি ভারত সীমান্তবর্তী উপজেলা কসবা হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তেন।
মুক্তিযুদ্ধে কিশোরদের অবদান নিয়ে গবেষণায় নিযুক্ত মোস্তফা হোসেইন সমকালকে বলেন, তার ধারণা, খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আবু সালেক সর্বকনিষ্ঠ। এতকাল সর্বকনিষ্ঠ বলে প্রচারিত শহীদুল ইসলাম লালু সালেকের চেয়ে খানিকটা বড় হবেন।
আবু সালেক নিজে অবশ্য এ নিয়ে আলোচনার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না। তিনি বলেন, 'আমি যুদ্ধে গিয়েছিলাম বাপ-চাচা ও ভাইদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে। যুদ্ধে যাওয়ার পর অবশ্য অনেক বড় একটা স্বপ্ন জন্ম হয়েছিল মনে। সেই স্বপ্ন এখনও অনর্জিতই রয়ে গেছে।'
আবু সালেক জানান, যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর তিনি আগরতলায় চলে যান। সেখানকার ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে লোক বাছাই চলছিল। বাছাইপর্ব শুরু হলে ভারতীয় এক সেনা কর্মকর্তা তাকে দেখে বলেন, এ তো বাচ্চা ছেলে। এই বাচ্চা ছেলেকে যোদ্ধা হিসেবে নির্বাচন করা যাবে না বলে মত দিলেন বাঙালি কর্মকর্তারাও। যুদ্ধে যেতে পারবেন না জেনে সবার সামনেই কেঁদে ফেললেন সালেক। তার কান্নায় অফিসাররা মত পাল্টান। প্রথমে ওমপিনগরে তার প্রশিক্ষণ হয়। এরপর তাকে পাঠানো হয় মেলাঘরে ২ নম্বর সেক্টরে। সেখানে তিনি চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানিতে অন্তর্ভুক্ত হন।
আবু সালেক কসবা এলাকায় যুদ্ধ করেন। একদিন হাবিলদার আবদুল হালিমের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি গ্রুপ মনিয়ন্দ গ্রামে গিয়ে পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগী রাজাকাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কয়েক দিন পর তারা ১০ জন আবার রাতে পাকিস্তানিদের পাকা বাঙ্কারের কাছে গিয়ে অধিনায়কের নির্দেশে গুলি শুরু করেন। এক সঙ্গে ১০টি অস্ত্র থেকে ক্রমাগত গুলি চলে পাকিস্তানিদের ওপর।
এর ১০ দিন পর আর একটি অপারেশন করে তারা কসবা হাই স্কুলের কাছাকাছি চন্দ্র্রপুর গ্রামে অবস্থান নেন। সেদিনই মধ্যরাত থেকে শুরু হয় প্রচ গোলাগুলি। একপর্যায়ে পাকিস্তানি বাহিনীর মর্টার আক্রমণে বাঙ্কার ত্যাগ করা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু শত্রুপক্ষকে ব্যস্ত রাখা না গেলে কেউ বেরোতে পারবেন না। ছোট্ট কাঁধে বিশাল এই দায়িত্ব তুলে নিলেন আবু সালেক। ক্রমাগত গুলি করতে লাগলেন পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প লক্ষ্য করে। সেই অবসরে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে গেলেন অন্যরা। কিন্তু গুলি করা থামালেন না সালেক। এক সময় পাকিস্তানি সেনারা মনে করল, মুক্তিযোদ্ধারা মনে হয় খুব সংগঠিতভাবে আক্রমণ চালাচ্ছে। ফলে ওরাও পিছু হটে গেল। বাঙ্কারে থেকে গেলেন শুধু আবু সালেক। একসময় রাত শেষ হয়ে সকাল হলো। মুক্তিযোদ্ধারা ভেবেছিলেন, গোলাগুলি যখন থেমেছে, আবু সালেক নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। কিন্তু বাঙ্কারে ফিরে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখেন কিশোর আবু সালেক একা সেখানে বসে আছেন।
২২ নভেম্বর চ ীদ্বারবাজার সংলগ্ন খাতপাড়া গ্রামে এক যুদ্ধে আবু সালেক শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত শেলের টুকরোর আঘাতে আহত হন। তাকে উদ্ধার করে গৌহাটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখান থেকে সুস্থ হয়ে ফেরেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পর।
http://www.samakal.net/2014/12/03/102501
- Biplob Rahman | ০৮ ডিসেম্বর ২০১৪ ১৯:২৮582794
- প্রকাশ : ০৪ ডিসেম্বর, ২০১৪ ০১:০২:০০ | আপডেট : ০৪ ডিসেম্বর, ২০১৪ ১২:৫০:৫৯
সনদ পদক নিয়ে ভাবেন না মৃত্যুঞ্জয়ী মোজাম্মেল
আলাপ করতে চেয়ে ফোন করতেই তিনি জানতে চাইলেন, 'বিষয় কি মুক্তিযোদ্ধার বয়স?' ফোনের অপর প্রান্তের মানুষটি মোজাম্মেল হক বীরপ্রতীক। তার জন্ম ১৯৫৬ সালের ১২ ডিসেম্বর। ঢাকা শহরের অদূরবর্তী ভাটারায় জন্ম নেওয়া এই মানুষটি ১৯৭১ সালে ছিলেন শাহীনবাগের স্টাফ ওয়েলফেয়ার স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র।
রাজীব নূর
আলাপ করতে চেয়ে ফোন করতেই তিনি জানতে চাইলেন, 'বিষয় কি মুক্তিযোদ্ধার বয়স?' ফোনের অপর প্রান্তের মানুষটি মোজাম্মেল হক বীরপ্রতীক। তার জন্ম ১৯৫৬ সালের ১২ ডিসেম্বর। ঢাকা শহরের অদূরবর্তী ভাটারায় জন্ম নেওয়া এই মানুষটি ১৯৭১ সালে ছিলেন শাহীনবাগের স্টাফ ওয়েলফেয়ার স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর দিনগুলোতে তার বয়স ছিল ১৫ বছরেরও কম। সনদ পদক নিয়ে ভাবেন না মৃত্যুঞ্জয়ী মোজাম্মেল
১৯৭১-এর ১৩ অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর মোনায়েম খানের বাড়িতে দুঃসাহসী অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এই কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। বীরত্বপূর্ণ ওই অভিযানের জন্য বীরপ্রতীক উপাধি পেয়েছেন তিনি।ফোনালাপেই মোজাম্মেল হক বললেন, একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধার বয়স সর্বনিম্ন ১৫ বছর নির্ধারণ করাটা ঠিক হয়নি। তবে এ নিয়ে তিনি নিজে মোটেই বিচলিত নন, এটা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী মোজাম্মেল। বললেন, 'সনদ, খেতাব, ভাতা এই সব পাব ভেবে যুদ্ধ করতে যাইনি। মোনায়েম খানকে যখন মারতে গেলাম, সেখান থেকে জীবন নিয়ে ফিরতে পারব, এমনটা ভাবিইনি।'১৯৭১ সালে বাড্ডা, ভাটারা, ছোলমাইদ ছিল পুরোপুরি গ্রাম। মাইলের পর মাইল ধানের ক্ষেত, খাল-বিল-জলাশয়। মোজাম্মেলের বাপ-চাচারা প্রায় সবাই ছিলেন কৃষক। পড়াশোনার ফাঁকে কৃষিকাজে বাপ-চাচাদের সাহায্য করতেন তারা। ২৫ মার্চের কালরাতে মোজাম্মেলের বাবা ধানের জমিতে সেচ দিচ্ছিলেন। মোজাম্মেল তার বাবার জন্য খাবার নিয়ে মাঠে গিয়েছিলেন। হঠাৎ ক্যান্টনমেন্ট থেকে গুলির শব্দ ভেসে আসে। মর্টারের ফায়ার এবং ফ্লেয়ার গানের আলোয় পুরো আকাশ ঝলসে ওঠে। বাবা মোজাম্মেলকে বললেন, যুদ্ধ শুরু হয়েছে। চল বাড়ি যাই।
যুদ্ধ শুরুর আগেই অনেক বঞ্চনাবোধ বিচলিত করত মোজাম্মেলকে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কাছাকাছি বাড়ি হওয়ায় তারা সেনাবাহিনীর অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই যুদ্ধ শুরু হলে নিজেও যুদ্ধে যেতে চাইলেন। প্রথমবার চাচাতো ভাইদের সঙ্গে গোপনে যুদ্ধে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। বড়রা জেনে যাওয়ায় বিফল হলেন। দ্বিতীয়বার অভিভাবকদের সম্মতি আদায় করে গেলেন ত্রিপুরায়। ১৫ দিন পর ভয় পেয়ে পালিয়ে আসেন। বাড়ির লোকজন তো মহাখুশি। ঘরের ছেলে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে এসেছে।একই গ্রামের রহিমুদ্দীন প্রশিক্ষণ নিয়ে গ্রামে ফিরে এলে আবারও যুদ্ধে যাওয়ার ভূত চাপে মাথায়। প্রশিক্ষণ না নিয়েই যুদ্ধে জড়িয়ে যান তিনি। রহিমুদ্দীনের সঙ্গী হয়ে গুলশানের একটি বিদেশি দূতাবাসে হামলা করেন। এর কয়েকদিন পর আবারও ত্রিপুরায় গেলেন যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেবেন বলে। এবার সঙ্গী হলেন রহিমুদ্দীন।
মোজাম্মেল হক বলেন, '২নং সেক্টরের কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফের সেকেন্ড ইন কমান্ড ক্যাপ্টেন এটিএম হায়দার আমাকে দেখেই রহিমুদ্দীনকে দিলেন ধমক, কী সব পোলাপাইন নিয়ে আসছ, এই সব দিয়ে কী যুদ্ধ করা যায়? রহিমুদ্দীন আমার পক্ষে উকালতি করে বলে, স্যার, ও ছোট হলেও খুব সাহসী। ঢাকার বিদেশি দূতাবাসে হ্যান্ড গ্রেনেড চার্জ করেছে।'হায়দারের সম্মতিতে এবার মেলাঘরে পেলেন গেরিলা যোদ্ধার প্রশিক্ষণ। ২১ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে যোগ দিলেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গেরিলা গ্রুপে। ১৫ জনের গ্রুপটির শুরুটা ভালো হলো না। কুমিল্লার সিএনবি রোডে উঠতেই পাকিস্তানি সেনাদের অ্যামবুশের মুখে পড়ে গেরিলা দলটি। পালিয়ে কোনো রকমে মেলাঘরে ফিরে যান তারা। ক্যাপ্টেন হায়দার স্যার বেঁকে বসলেন; বললেন, এদের মরাল ডাউন হয়ে গেছে। এদের দিয়ে আর যুদ্ধ হবে না। তিনি কোনো একটি গেরিলা ইউনিটে এদের গোলা-বারুদ বহনকারীর দায়িত্ব দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।
যুদ্ধ করতে এসে যোদ্ধাদের জোগানদারের ভূমিকায় নিজেকে ভাবতেই পারছিলেন না মোজাম্মেল। তাই তিনি প্রতিদিন রুটিন করে মেজর হায়দারের অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে শুরু করলেন। মোজাম্মেল বলেন, '১৫-২০ দিন পর হায়দার স্যার ডেকে বললেন, এই তোর কী হয়েছে? প্রত্যেক দিন এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস কেন? আমি বলি, স্যার আমাদের যুদ্ধে পাঠান। আমরা মরতে ভয় পাই না।'মোজাম্মেল হকের দৃঢ়প্রত্যয়ে মন গলে হায়দারের। তিনি এবার ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গ্রুপকে দায়িত্ব দেন মোনায়েম খানকে হত্যার।
কাজটা সহজ ছিল না। ঢাকায় এসে মোজাম্মেল হক যোগাযোগ করেন মোনায়েম খানের রাখাল শাহজাহানের সঙ্গে। অক্টোবরের এক সন্ধ্যায় প্রথম শাহজাহানের সহযোগিতায় তিনি মোনায়েম খানের বাড়িতে ঢোকার সুযোগ পান। বাসায় ঢুকে গেটের পাশের কলাবাগানের ঝোঁপে ঘাপটি মেরে বসে থাকেন। একটু পরে শাজাহান এসে জানান, মোনায়েম খান দোতলায় উঠে গেছেন। দু-তিন দিন পর আবারও গেলেন। এবার বাড়ির লোকজন ও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যরা টের পেয়ে যাওয়ায় দেয়াল টপকে পালাতে বাধ্য হন।দ্বিতীয়বারের ব্যর্থতার পর একটু ভয় পান তিনি। মোজাম্মেল বলেন, 'আমার তো মন খুব খারাপ। পর পর দুবার অপারেশনে বাধা পড়ল। আর বুঝি হবে না। এরই মধ্যে একদিন শাজাহান ভাই ভাটারা এসে আমাকে ধরে জানতে চাইলেন, কী ভাই, যুদ্ধ হবে না? তার কথায় আবার মনোবল ফিরে পাই।'
তৃতীয়বার মোজাম্মেলের সঙ্গী হলেন তার রাজনৈতিক গুরু ও চাচাতো ভাই, মুক্তিযুদ্ধের আরেক বীরপ্রতীক আনোয়ার হোসেন। মোজাম্মেল বলেন, অপারেশন শুরুর আগে শাহজাহান ভাইসহ আমাদের সহায়তাকারী মোনায়েম খানের কর্মচারীদের বাড়ি ছেড়ে যেতে বলি। ওরা সরে গেলে আমরা অপারেশন চালাই। মোনায়েম খান ছিলেন তার ড্রইংরুমে। ড্রইংরুম খোলা ছিল। রুমের ভেতর পশ্চিম দিকে মুখ করে সোফায় বসা ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী আমজাদ হোসেন এবং মোনায়েম খানের মেয়ের জামাই জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল। দুই জনের মাঝখানে মোনায়েম খান। সে সময় ইন্ডিয়ান স্টেনগানে আমরা ফায়ার ওপেন করি। অস্ত্র আমাদের সঙ্গে বিট্রে করে। এসএমজি থেকেও মাত্র একটা বুলেট বের হওয়ার পর ফেঁসে যায়। চেম্বারে গিয়ে দ্বিতীয় বুলেট আটকে যায়। বুলেট আর বের হয়নি। পরে জানতে পাই, ওই একটি গুলিতেই প্রাণ হারান মোনায়েম খান।এর পর বনানী কবরস্থানে মোজাম্মেল ও আনোয়ারের পালানোর গল্পটায় রয়েছে টানটান উত্তেজনা।
মোজাম্মেল হক বীরপ্রতীক এখন একজন জনপ্রতিনিধি। ভাটারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তিনি। ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের উল্টো পাশেই ভাটারা ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সর্ব উত্তর-পূর্ব কোণে ফাজিলারটেক শাওড়াতলায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে মোজাম্মেল হকের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা করা ভাস্কর্য 'বীরের প্রত্যাবর্তন'।
http://www.samakal.net/2014/12/04/102758
- Biplob Rahman | ০৮ ডিসেম্বর ২০১৪ ১৯:৩৫582795
- ০৫ ডিসেম্বর, ২০১৪ ০১:২৭:৫৫ | আপডেট : ০৫ ডিসেম্বর, ২০১৪ ০৩:০৬:০৭
তারামন বিবির ভয়
একাত্তরের বীরযোদ্ধা তারামন বিবিকে খুঁজে বের করে এনেছিলেন যে মানুষটি, সেই অধ্যাপক বিমলকান্তি দে বললেন, তারামন ভয় পেলে সে ভয়টা তো হবে বাংলাদেশের।
রাজীব নূর
তারামন বিবি কি ভয় পেয়েছেন? ১৯৯৫ সালে একাত্তরের বীরযোদ্ধা তারামন বিবিকে খুঁজে বের করে এনেছিলেন যে মানুষটি, সেই অধ্যাপক বিমলকান্তি দে বললেন, তারামন ভয় পেলে সে ভয়টা তো হবে বাংলাদেশের।একাত্তরে তারামনের বয়স কত ছিল? এতদিন সবাই জানতেন, ১৩ কি ১৪ বছর। তার জন্ম ১৯৫৭ সালের দিকে। তবে সম্প্রতি তারামন নিজে জানালেন, না, একাত্তরে তার বয়স ছিল ১৬ বছরের বেশি।তারামন বিবির ভয়
ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক বিমলকান্তি দে বলেন, এক দশকের খোঁজাখুঁজি শেষে ১৯৯৫ সালের ২৮ অক্টোবর যখন তারামনকে পেলেন, তখন তাকে তারামন বলেছিলেন, একাত্তরে তার বয়স ১৩-১৪ বছর ছিল। তার অনুমান, একাত্তরের ২৬ মার্চ মুক্তিযোদ্ধার সর্বনিম্ন বয়স হতে হবে ১৫ বছর_ এমন সরকারি সিদ্ধান্ত হতে পারে শুনে তারামন হয়তো ভয় পেয়ে গেছেন।
তারামন অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তরে নীরব থেকেছেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, তার জন্ম ১৯৫৪ সালের ১১ ডিসেম্বর। তারামন বিবি মুক্তিযুদ্ধে অবদানেরজন্য খেতাবপ্রাপ্ত দুই নারীর একজন। অন্যজন হলেন ডা. সিতারা বেগম। তিনি ছিলেন ২ নম্বর সেক্টরে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ হাসপাতালের অন্যতম উদ্যোক্তা।মুক্তিযুদ্ধ গবেষকদের মতে, যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ সরকার যে নীতি নিয়েছিল, তা নারীদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং গেরিলা যুদ্ধের জন্য তৈরি করার অনুকূল ছিল না। নারীরা সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জানানোয় সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর দায়িত্বে ৩০০ তরুণীকে গোবরা ও বিএলএফ ক্যাম্পে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। গোবরা ক্যাম্পের প্রশিক্ষণার্থী গীতা মজুমদার, গীতা কর, শিরীন বানু মিতিল ও লাইলী পারভীন বিভিন্ন সময় সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, অস্ত্র চালনা শিখে যুদ্ধে যাওয়ার অদম্য প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও তারা যুদ্ধে যেতে পারেননি।
অধ্যাপক বিমলকান্তি দে বলেন, তারামন হলেন সেই বিরল সৌভাগ্যবানদের একজন, যিনি সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন এবং বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করে খেতাব পেয়েছেন।অনুশোচনার বিষয় হচ্ছে, ১৯৯৫ সালের আগে তারামন নিজেও জানতেন না তার খেতাবপ্রাপ্তির কথা। সরকার, সমাজ ও রাজনৈতিক দল, এমনকি গবেষক, নারী আন্দোলনের সংগঠক_ কেউই তারামন বিবির খোঁজ করেননি। অধ্যাপক বিমলকান্তি দে সংবাদপত্রে তারামন বিবির খবর প্রকাশ করলে ১৯৯৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তারামন বিবির হাতে বীরপ্রতীকের পদক তুলে দেন।
কীভাবে তারামনের খোঁজ পেয়েছিলেন_ তা জানতে চাইলে বিমলকান্তি দে বলেন, ময়মনসিংহ অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তার মনে হলো, গবেষণাপত্রে ওই অঞ্চলের খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নাম থাকলে ভালো হয়। সেটা আশির দশকের শুরুর দিককার কথা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য খেতাব দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৭৩ সালে খেতাবপ্রাপ্তদের চূড়ান্ত তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশিত হলেও ময়মনসিংহের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করার সময় গেজেটটি বিমলকান্তি দে সংগ্রহ করতে পারেননি। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে শুনে শুনে তিনি ওই অঞ্চলের খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা করেছিলেন, তাতে অনেক ভুল থেকে গিয়েছিল। পরে ১৯৮৬ সালের দিকে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেটটি হাতে পাওয়ার পর দেখেন, গেজেটেও অনেক ভুল রয়ে গেছে।খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেট ঘাঁটতে গিয়ে তারামন বিবির নামটির প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তিনি খুঁজতে শুরু করেন, কে এই নারী। অবশেষে ১৯৯৫ সালের ২৮ অক্টোবর পেঁৗছলেন কুড়িগ্রামের রাজীবপুর উপজেলায়।তারামন এখন বাস করেন রাজীবপুরের কাছারিপাড়ায়। একাত্তরে তাদের বাড়ি ছিল রাজীবপুরের কোদালকাটি ইউনিয়নের শঙ্কর মাধবপুর গ্রামে। ব্রহ্মপুত্রের ভাঙনে হারিয়ে গেছে তাদের সেই বাড়ি। আবদুস সোবাহান ও কুলসুম বেওয়ার মেয়ে তিনি।
যুদ্ধের সময় ১১ নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল তারামনদের গ্রাম শঙ্কর মাধবপুরের কাছে দশঘরিয়ায় ক্যাম্প করেছিল। মুহিফ হালদার নামের একজন হাবিলদার মুক্তিযোদ্ধাদের ওই ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন। তিনিই তারামন বিবিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন।তারামনের নিজের জবানিতেই শোনা যাক :একদিন, দিন-তারিখ মনে নাই, জঙ্গলে কচুরমুখী তুলছিলাম। একজন বয়স্ক মানুষ এসে জানতে চাইলেন, আমি মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে কাজ করব কি-না। জানতে চাইলেন ভাত রাইন্ধা দিতে পারব কি-না। সেদিন কোথা থেকে যেন একটা শক্তি পেলাম। মনে হলো, এই তো সুযোগ। মাথার ওপর রক্ষা করার মতো কেউ নাই, যার ভরসায় বেঁচে থাকব। মরতে তো হবেই। যুদ্ধ করে বাঁচার চেষ্টা করলে দোষের কী। তাকে বললাম, আফনে আমার মায়ের লগে কথা কন। উনি যাইবার দিলে যাইমু।
তারামনের মা কুলসুম বেওয়া প্রথমে এতে রাজি হননি। পরে হাবিলদার মুহিফ তারামনকে ধর্মমেয়ে হিসেবে গ্রহণ করেন। এর পরই তারামনকে মুক্তিযোদ্ধাদের শিবিরে রান্নার কাজে পাঠাতে রাজি হন তার মা। তারামনের সাহস ও শক্তির পরিচয় পেয়ে তাকে অস্ত্র চালনা শেখান হাবিলদার মুহিফ।এভাবে তারামনের একজন যোদ্ধা হয়ে ওঠা। একদিন ঠিক মধ্যদুপুরের ঘটনা। মুক্তিযোদ্ধাদের সবাই খেতে বসেছেন। তারামনকে পাকিস্তানি সেনাদের কেউ আসছে কি-না দেখার জন্য বলা হলো। তারামন সুপারিগাছে উঠে দূরবীন দিয়ে চারদিকে লক্ষ্য রাখছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, পাকিস্তানিদের একটি গানবোট তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। সবাই খাওয়া ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। দ্রুত প্রস্তুতি নিয়ে আক্রমণ করবেন বলে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তারামন তার সহযোদ্ধাদের সঙ্গে ওই যুদ্ধে অংশ নেন। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। সেদিন তারা শত্রুদের পরাস্ত করতে সক্ষম হন। এর পর তারামন পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। অনেকবার তাদের ক্যাম্পে পাকিস্তানিরা হামলা করেছে। তবে ভাগ্যের জোরে প্রতিবার বেঁচে গেছেন তারামন।
শুধু সম্মুখ যুদ্ধই নয়, নানা কৌশলে শত্রুপক্ষের তৎপরতা ও অবস্থান জানতে গুপ্তচরবৃত্তিও করেছেন তারামন। কখনও সারা শরীরে কাদামাটি, কালি, এমনকি মানুষের বিষ্ঠা পর্যন্ত লাগিয়ে পাগল সেজেছেন। চুল এলোমেলো করে বোবা সেজে পাকিস্তানি সেনাদের সামনে দীর্ঘ হাসি কিংবা কান্নার অভিনয় করেছেন। কখনও প্রতিবন্ধী সেজে, কখনও আবার পঙ্গুর অভিনয় করে পেঁৗছে গেছেন শত্রুসেনার শিবির। নদী সাঁতরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসেছেন শত্রুদের অবস্থানের। কলাগাছের ভেলা নিয়ে কখনও পাড়ি দিয়েছেন ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী সোনাভরি। জান-মানের কথা না ভেবেই এসব দুঃসাহসী কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এই বীর কিশোরী।মুক্তিযুদ্ধে সাহস ও বীরত্বের জন্য তারামন বিবিকে বীরপ্রতীক খেতাব দেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালের সরকারি গেজেটে তার নাম ছিল মোছাম্মৎ তারামন বেগম।প্রতিবেদন তৈরিতে সহযোগিতা করেছেন কুড়িগ্রাম থেকে মমিনুল ইসলাম মঞ্জু
http://www.samakal.net/2014/12/05/102971
- Biplob Rahman | ০৮ ডিসেম্বর ২০১৪ ১৯:৩৭582797
- বিচ্ছু জালালের ললাটলিখন
রাজীব নূর
কপালে বাঁধা থাকে বাংলাদেশের পতাকা। পরনেও পতাকার লাল-সবুজ রঙের জামা। তিনি জহির উদ্দিন মোহাম্মদ জালাল। কিন্তু সবার কাছে 'বিচ্ছু জালাল' নামেই পরিচিত। মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার শুরু হওয়ার পর থেকে ঘুরেফিরে বারবার দেখা গেছে লাল-সবুজে সজ্জিত এই মানুষটাকে। কখনও আদালতের বারান্দায়, কখনও গণজাগরণ মঞ্চের সভা-সমাবেশ ও মিছিলে। আবার কখনও টেলিভিশনের পর্দায়। সর্বত্র লাল-সবুজে সজ্জিত বিচ্ছু জালালকে দেখে মনে পড়েছে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের শহীদ নূর হোসেনকে নিয়ে লেখা শামসুর রাহমানের কবিতা 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়'। বাংলাদেশকে
বুকে ধারণ করে ১৯৭১ সালে যুদ্ধে গিয়েছিলেন জহির উদ্দিন মোহাম্মদ জালাল। তিনি অবশ্য বলেন, বাংলাদেশ তার ললাটলিখন। ললাটলিখনের শুরুটা ভালো হয়নি। তাই তো ১৫ আগস্টের পট পরিবর্তনের পর থেকে বহুকাল আত্মগ্গ্নানিতে ভুগতে হয়েছে তাদের। দেখেছেন যে দেশের জন্য জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে গিয়েছিলেন, সে দেশের মন্ত্রী হয়েছে যুদ্ধাপরাধীরা। যুদ্ধাপরাধী নিজামী-মুজাহিদদের গাড়িতে পতপত করে উড়েছে জাতীয় পতাকা। অথচ এই দু'জনের হাতে তিনি নিজেও নির্যাতিত হয়েছিলেন। প্রত্যক্ষ করেছেন শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ছেলে রুমীসহ বদি, জুয়েল, আজাদসহ অন্যদের নির্যাতনের নির্মম দৃশ্য। দেখেছেন নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত অমর একুশের গানের সুরকার আলতাফ মাহমুদকে। পুরনো এমপি হোস্টেলে নিজামী ও মুজাহিদ গং তাদের ধরে এনে নির্যাতন করেছিল। নিজামীর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন জালাল নিজেও। শরীরে এখনও সেই ক্ষত বহন করছেন তিনি। অবরুদ্ধ ঢাকায় গেরিলা অভিযান চালাতে এসে ধরা পড়েছিলেন বিচ্ছু জালাল। তাকে ওই নির্যাতন কেন্দ্র থেকে উদ্ধার করে আনেন পাঞ্জাবি এক কর্মকর্তা।
বিচ্ছু জালাল জানান, আমার রক্ষাকর্তা ওই ভদ্রলোককে আমরা এডিসি বিএম আফজাল বলে জানতাম। জাতিতে পাঞ্জাবি আফজাল সাহেব ছিলেন বাঙালিদের প্রতি সহানুভূতিশীল। যুদ্ধাপরাধী মতিউর রহমান নিজামী ও আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী হিসেবে তিনি এসব কথা জানিয়েছেন।
একাত্তরে কত ছিল তার বয়স? বিচ্ছু জালাল জানালেন, ১৪ বছরের একটু বেশি হবে। ঢাকার আজিমপুর ওয়েস্টএন্ড হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীতে উঠেছেন মাত্র। ওই বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে গিয়েছিলেন যুদ্ধ করতে। যোগ দিয়েছিলেন ২ নম্বর সেক্টরে। সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফ ডানপিটে জালালকে আদর করে ডাকতেন 'বিচ্ছু জালাল' বলে। সেই থেকে নামটির প্রেমে পড়ে গেছেন জালাল নিজেও। তাই তো মুক্তিযুদ্ধের এতকাল পরও নিজের ভিজিটিং কার্ডে নামের পাশে ব্র্যাকেটে বিচ্ছু জালাল লেখেন। কার্ডে ছাপানো আছে এক কিশোর যোদ্ধার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছবি।
ছবিটা সম্পর্কে জানতে চাইলে বিচ্ছু জালাল বললেন, এটা ১৯৭১ সালের ১৯ ডিসেম্বরের ছবি। আজিমপুরের লিটল অ্যাঞ্জেলস স্কুলের সামনে থেকে ছবিটা তুলেছিলেন তার বন্ধু বর্তমানে জার্মানি প্রবাসী নাসিম। স্কুলের ভেতরে আটকে রাখা হয়েছিল রাজাকার মাওলানা মান্নানকে। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ জয় করে স্বাধীন দেশে ফিরেছেন তারা। তখন তো অনেক স্বপ্ন ছিল মনে। অথচ পরে এই রাজাকাররা সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে; বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়েছে।
জালাল জানান, যুদ্ধ শুরুর মাসখানেক আগেও যুদ্ধ নিয়ে তেমন কোনো ভাবনা ছিল না তার। একাত্তরের ১ মার্চের একটি ঘটনা তার কিশোর মনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। জালাল বলেন, আমরা স্কুলের ছেলেরা খেলতে গিয়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসীন হলের মাঠে। ওটা ছিল স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অংশ। মাইকে গান বাজাচ্ছিলাম। দুপুর ১টার দিকে বড়দের কেউ একজন একটা রেডিও নিয়ে এলেন। তারা অপেক্ষা করছেন ইয়াহিয়া খানের ভাষণ শুনবেন বলে। অপেক্ষার এক পর্যায়ে দুপুর ১টা ৫ মিনিটে ঘোষণা এলো_ ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত। এই সংবাদ রেডিওতে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় নেমে আসেন। আমরা স্কুলপড়ূয়ারাও যোগ দিই সেই মিছিলে। মুহূর্তেই এক বিক্ষুব্ধ নগরীতে পরিণত হয় ঢাকা। সবার মুখে মুখে ধ্বনিত হতে থাকে 'জয় বাংলা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর/বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'তোমার আমার ঠিকানা/পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'।
মুক্তিযোদ্ধা জালালের বাবা আলাউদ্দিন আহমেদ ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ বিভাগের ঢাকার গোয়েন্দা শাখার পুলিশ সুপার। সেই সুবাদে জালালরা থাকতেন ইস্কাটন গার্ডেন সার্কিট হাউসের ষষ্ঠ তলার ফ্ল্যাটে। ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইটের কিছুক্ষণ আগেও দুঃসাহসী জালাল তার ভাই ফরিদউদ্দিন আহমেদ মঞ্জু ও ইসরাতউদ্দিন আহমেদ বাবুলসহ ৩০০ থেকে ৪০০ সঙ্গী নিয়ে কাঠের গুঁড়ি, ভ্যানগাড়ি, বাঁশ, পরিত্যক্ত গাড়ি, ড্রাম দিয়ে বাংলামোটরের সামনের রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়েছিলেন। সেই রাতে ঘটল ইতিহাসের নির্মমতম গণহত্যা।
এপ্রিলের মাঝামাঝি মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে জালাল প্রথমে কিশোরগঞ্জের ভৈরবে যান। সেখান থেকে মেঘনা নদী পেরিয়ে যান আশুগঞ্জে। সেখানে দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন মো. গাফফার, ক্যাপ্টেন হেলাল মোর্শেদ, ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ নাসিমকে দেখতে পান। তাদের কাছে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। বয়স কম হওয়ায় কেউ তার ইচ্ছেকে আমল দেননি। তবু ওখানে থেকে যান বিচ্ছু জালাল এবং এর মাত্র একদিন পর ১৪ এপ্রিল হঠাৎ পাকিস্তানি সেনারা আশুগঞ্জে দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর জঙ্গি বিমান ও হেলিকপ্টার নিয়ে আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা আক্রমণ করেন। কিন্তু এই যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী টিকতে পারেনি। আশুগঞ্জের মেঘনা পারের এই যুদ্ধে সাত জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। পরে বাঙালি মুক্তিসেনাদের ওই বাহিনীর সঙ্গে ১৭ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া হয়ে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় পেঁৗছেন। প্রথমবার কিছুদিন থেকে ফিরে আসেন ঢাকায়। এডিসি আফজাল তাকে বললেন, 'তোমার আর ঢাকায় থাকা উচিত হবে না। যুদ্ধে যাও, তোমাদের স্বাধীনতা আসবেই।' পরে এই আফজালই বিচ্ছু জালালকে উদ্ধার করে এনেছিলেন নিজামী-মুজাহিদের নির্যাতন কেন্দ্র থেকে।
বিচ্ছু জালাল দ্বিতীয়বার আগরতলায় গিয়ে যোগ দেন ২ নম্বর সেক্টরের মতিনগর ক্যাম্পে। পরে পাকিস্তানি সেনারা হামলা করলে ক্যাম্প স্থানান্তরিত হয় মেলাঘরে। মেলাঘরে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন। আরও কয়েকজন গেরিলা যোদ্ধার সঙ্গে কমান্ডো ক্যাপ্টেন এটিএম হায়দারের কাছে হিট অ্যান্ড রান টেকনিকের স্পেশাল ট্রেনিং পান তিনি। তারা ওয়াই প্লাটুন 'সজীব গ্রুপ' নামে গেরিলা বাহিনীর সদস্য হয়ে অবরুদ্ধ ঢাকায় কখনও চোরাগোপ্তা, কখনও গেরিলা অপারেশন করে পাকিস্তানি সেনাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। তাদের এই গ্রুপের কমান্ডার ছিলেন কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলার পুরুরা গ্রামের মফিজুর রহমান খান সজীব।
http://www.samakal.net/2014/12/06/103141
- Biplob Rahman | ০৮ ডিসেম্বর ২০১৪ ১৯:৩৮582798
- প্রকাশ : ০৭ ডিসেম্বর, ২০১৪ ০১:৪২:০৮
আবু জাহিদ :পান্থশালায় ক্ষণিকের অতিথি
রাজীব নূর
'আবু একটা গান খুব গাইত।' এই কথা বলেই থামলেন মুক্তিযুদ্ধের কিশোর শহীদ আবু জাহিদের সহযোদ্ধা আবদুল্লা-হিল-বাকী। কোন গানটা মনে করার চেষ্টায় স্মৃতি হাতড়িয়ে বললেন, কেমন যেন একটা বিষাদের গান ছিল! গানে কান্নার কথা ছিল; ছিল পান্থশালায় ক্ষণিকের অতিথির বেদনা। আবদুল্লা-হিল-বাকী বলেন, আবু হয়তো টের পেয়েছিল_ এই পৃথিবীতে আর বেশি দিন থাকবে না সে।
পরে আবু জাহিদের ছোট ভাই মোশাররফ হোসেন নাসিমের কাছ থেকে জানা গেল, গানটা ছিল 'এই পৃথিবীর পান্থশালায় গাইতে গেলে গান/ কান্না হয়ে বাজে_ কেন বাজে আমার প্রাণ...।'
সত্তর সালের দিকে মুক্তি পাওয়া একটি সিনেমার গান এটি। শিল্পী সৈয়দ আবদুল হাদী। যুদ্ধে যাওয়ার আগে থেকেই আবু এই গানটি গাইতে শুরু করেছিলেন।
আবু জাহিদ ও আবদুল্লা-হিল-বাকী, একাত্তরে দু'জনই ছিলেন কুমিল্লা জিলা স্কুলের ছাত্র। জাহিদ পড়তেন নবম শ্রেণীতে আর বাকী দশম শ্রেণীতে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার চারগাছ বাজারের যে যুদ্ধে আবু জাহিদ শহীদ হন, সেই যুদ্ধেও তারা একসঙ্গে ছিলেন।
কিশোর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আবু জাহিদের জন্ম ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে কুমিল্লা শহরের মগবাড়ী চৌমুহনীতে। বাবা আবুল হাসেম দুলা মিয়া ও মা ভেলুয়া বিবির পাঁচ ছেলের একজন আবু। ১৯৬৭ সালে কুমিল্লা জিলা স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন তিনি। শৈশব থেকেই আবু জাহিদ অনেক রাজনীতি সচেতন ছিলেন বলে তার সহপাঠী ও সহযোদ্ধারা জানান। সহপাঠীদের কাছ থেকেই জানা গেল, আবু খুব ডানপিটে ছিলেন। পাখির বাসা খোঁজ করা, গ্রীষ্মের ভরদুপুরে আম পাড়া আর বাড়ির কাছের গোমতী নদীতে সাঁতরে বেড়ানো দারুণ মোহিত করত তাকে।
আবু গান গাইতেন। সাহসী হিসেবে বন্ধুমহলে তার পরিচিতি ছিল। খেলাধুলায় ভীষণ আগ্রহ ছিল তার। বিশেষ করে দৌড়, হকি ও ফুটবল প্রতিযোগিতায় তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো কেউ ছিল না স্কুলে। ফলে সবার কাছে পরিচিতি ছিল তার। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন আবু জাহিদ। শহীদ আসাদের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে মুক্তিকামী জনতার প্রতিবাদ ও সংগ্রামের কথা খবরের কাগজে পড়ে তার মনে বিপ্লবী স্পৃৃহার জন্ম নেয়। ছাত্রলীগের রাজনীতি করতেন। এরই মধ্যে সত্তরের নির্বাচন দেখলেন। ওই সময় স্কুলে, ঘরে-বাইরে সর্বত্র একই আলোচনা। শেষ পর্যন্ত কী হবে? যুদ্ধ অনিবার্য?
৭ মার্চে এলো বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা। আবু জাহিদ দেখলেন, পাড়ার বড় ভাই নাজমুল হাসান পাখী ছোটদের সংগঠিত করছেন। এক সময় যুদ্ধ শুরু হয়। আবু মায়ের কাছে বায়না ধরেন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য। অনুমতি মেলে না তার। মা ভেলুয়া বিবির স্বামীসহ অন্য তিন ছেলে এরই মধ্যে যুদ্ধে গেছেন। তাই এতটুকুন ছেলেকে ভেলুয়া বিবি কিছুতেই যুদ্ধে পাঠাতে রাজি হন না।
একদিন কিশোর আবু ফন্দি করে মাকে বললেন, '১০টা টাকা দাও। সেলুনে যাব, চুল কাটাতে হবে।'
ওই টাকা নিয়ে কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান কিশোর আবু। একাত্তরের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে আবু কুমিল্লা শহরের অদূরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সোনামুড়া টিলার কাছে মুক্তিবাহিনীর শিবিরে গিয়ে উপস্থিত হন। তখন তার পরনের কাপড় ছিল ভেজা। সেখানে অবস্থানরত বড় ভাই আনোয়ার হোসেন কেনু মিয়া ছোট ভাই আবুকে দেখে বিচলিত হন। চেষ্টা করেন ছোট ভাইটিকে বাড়িতে ফেরত পাঠাতে।
আবু তার বড় ভাই কেনু মিয়াকে বলেছিলেন_ প্রত্যেক দিন পাকিস্তানি সৈন্যরা তোমাদের খোঁজে বাড়িতে আসে। বাড়ি তল্লাশি করে। আমরা এখানে-ওখানে পালিয়ে বেড়াই। এভাবে বেঁচে থাকতে ভালো লাগে না। যদি বাঁচতে হয়, তাহলে বীরের মতো যুদ্ধ করে বাঁচব। দেশকে বাঁচাতে পারলে আমরাও ভালো থাকব।
সেখানে উপস্থিত অন্য মুক্তিযোদ্ধারাও বয়স কম বলে আবু জাহিদকে মুক্তিযুদ্ধে যেতে বারণ করেন। আবু নাছোড়বান্দা। অনেক পীড়াপীড়ির পর সেক্টর ইস্টার্ন জোনের কমান্ডার শেখ ফজলুল হক মনি আবুকে প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেন। প্রশিক্ষণ শেষে আবু অবস্থান করছিলেন নিমবাগ বাদামঘাট হেড কোয়ার্টারে।
১২ সেপ্টেম্বর বড় ভাই আনোয়ার হোসেন কেনুর উদ্দেশে একটি চিঠি লেখেন আবু। কারণ সুযোগ এসেছে পাড়ার বড় ভাই নাজমুল হাসান পাখীর সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার। বড় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন কলেজটিলায়। না পেয়ে ভাইয়ের কাছে লেখা চিঠিতে দোয়া চেয়ে জানিয়েছিলেন, 'ভাই... আমি পাখী ভাইয়ের সাথে যুদ্ধে যাচ্ছি... তিনি ছাড়া আর কারো সাথে যুদ্ধে যাব না।'
১২ সেপ্টেম্বর রাতে নাজমুল হাসান পাখীর নেতৃত্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার চারগাছ বাজারে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি ঝটিকা অপারেশনে বের হন। নয়জন মুক্তিযোদ্ধার একটি বহর নৌপথে ওই অপারেশনে রওনা হয়। ওই দলে ছিলেন নৃপেন পোদ্দার, মুমিনুল হক ভূঞা, মোজাম্মেল হক আবু, আবদুল্লা-হিল-বাকী, সাইফুল ইসলাম সাফু, আবু জাহিদসহ আরও কয়েকজন।
রাতের অভিযান, তাই কিছু বুঝে ওঠার আগেই পাকিস্তানি বাহিনী তাদের দোসর এ দেশের আলবদর বাহিনীর সহায়তায় মাঝনদীতে দলটির ওপর গুলি চালায়। তখন পাকিস্তানি বাহিনীর গুলিতে মারা যান মোজাম্মেল হক আবু ও সাইফুল ইসলাম সাফু। কনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা আবুও গুলিবিদ্ধ হয়ে নদীতে ঝাঁপ দেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। কনিষ্ঠ এই যোদ্ধাও শহীদ হন। সঙ্গী এবং মুক্তিকামী জনতা নদী থেকে কিশোর আবুর মরদেহ উদ্ধার করেন। অতঃপর তাকেসহ তিন মুক্তিযোদ্ধাকে চারগাছ উচ্চ বিদ্যালয় এলাকায় কবর দেওয়া হয়। পরে সেখানে তাদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।
ওই যোদ্ধা দলটির নেতা নাজমুল হাসান পাখী এখনও সেই রাতের কথা মনে হলে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তার কাছে শহীদ আবু জাহিদ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, যুদ্ধে যাওয়ার আগে থেকেই আবুকে চিনতাম। আবু দেশকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করত। তেজোদীপ্ত ছেলে ছিল ও। খেলার মাঠ, গানের আসর থেকে মিছিল-সমাবেশ সর্বত্রই ও থাকত সামনের সারিতে।
আবু জাহিদের ছোট ভাই মোশাররফ হোসেন নাসিম জানান, কুমিল্লা শহরের আদালত চৌমুহনী মোড় থেকে ভাটাপাড়া পর্যন্ত সড়কটি 'শহীদ আবু জাহিদ সড়ক' নামকরণ করা হয়েছে। তা ছাড়া কুমিল্লা জিলা স্কুলের ফোরাম '৭৩ উদ্যোগী হয়ে স্কুলের মিলনায়তনটির নামকরণ করেছে 'শহীদ আবু জাহিদ মিলনায়তন'। বেঁচে থাকলে আবু জাহিদও ১৯৭৩ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতেন। তাই জিলা স্কুলের ওই ব্যাচের শিক্ষার্থীরা সব সময়ই শহীদ আবুকে স্মরণ করেন বলে জানালেন মোশাররফ হোসেন নাসিম।
http://www.samakal.net/2014/12/07/103471
- Biplob Rahman | ০৮ ডিসেম্বর ২০১৪ ১৯:৩৯582799
- প্রকাশ : ০৮ ডিসেম্বর, ২০১৪ ০১:৫৩:২৭
আরেক যুদ্ধের কথা বললেন আবদুল্লাহ-হিল-বাকী
রাজীব নূর
মুক্তিযুদ্ধ কি শেষ হয়েছে? আবদুল্লাহ-হিল-বাকী মনে করেন শেষ হয়নি। যুদ্ধটা এখন চেতনাগত। নতুন আঙ্গিকে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করতে হবে। যুক্ত করতে হবে নতুন প্রজন্মকে। আনতে হবে অর্থনৈতিক মুক্তি।
মুক্তিযুদ্ধের পরের সেই যুদ্ধটা করতে চান তিনি। যদিও তিনি তা করতে পারবেন কি-না, তা নিয়ে নিজেরই সংশয় রয়েছে। তাই তিনি চান, নতুন প্রজন্ম নিক নতুন যুদ্ধের দায়।
আবদুল্লাহ-হিল-বাকীর মতে, মুক্তিযোদ্ধাদের দেওয়া সনদ, খেতাব_ এসবের বিনিময়ে মুক্তিযোদ্ধারা যে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন, তা-ই কতিপয় সুবিধাভোগীকে লোভাতুর করে তুলেছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের এতকাল পরে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা শনাক্ত
করতে হচ্ছে। মিথ্যা তথ্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধার সনদ নিয়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তিরা। এখন আবার অপরাধীদের ঠেকাতে যদি মুক্তিযোদ্ধার নতুন সংজ্ঞায় সর্বনিম্ন ১৫ বছর বয়সের বাধ্যবাধকতা আনা হয়, তাহলে অবমাননার মধ্যে পড়বেন একাত্তরের কিশোর যোদ্ধারা।
আবদুল্লাহ-হিল-বাকীর মনে মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়তি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া ঠিক হয়েছে কি-না তা নিয়ে দ্বিধা রয়েছে। তিনি বলেন, 'কে বড় মুক্তিযোদ্ধা? আবদুল্লাহ-হিল-বাকী, নাকি বিপদ হতে পারে জেনেও যে নারী যুদ্ধাহত আবদুল্লাহ-হিল-বাকীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সেবাশুশ্রূষা দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন তিনি?'
চারগাছের যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন তিনি। সেই যুদ্ধের স্মৃতি কোনোদিনই ভুলতে পারবেন না। চারগাছের যুদ্ধে কিশোর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল্লাহ-হিল-বাকী হারিয়েছেন তার সহযোদ্ধা অপর দুই কিশোর সহযোদ্ধা_ আবু জাহিদ আবু ও সাইফুল ইসলাম সাফুকে। অগ্রজপ্রতিম মোজাম্মেল হক আবুও শহীদ হন সেই যুদ্ধে।
মুক্তিযুদ্ধের সময় কুমিল্লা জিলা স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়তেন আবদুল্লাহ-হিল-বাকী। যুদ্ধ শুরুর আগে শুরু হয়েছিল তার যুদ্ধ_ 'পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি' নামের বই পাঠ্যতালিকা থেকে বাতিলের আন্দোলনের মধ্যদিয়ে। যার মূলে ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা। এরপর একাত্তরের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু বললেন, 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম... যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।' তখন তিনিও প্রস্তুত হয়ে গেলেন। প্রস্তুতিপর্বে নেতৃত্ব দিলেন কুমিল্লা শহরের অগ্রজপ্রতিম ছাত্রলীগ নেতারা। বিশেষ করে ছাত্রলীগ নেতা নাজমুল হাসান পাখীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ধাপে ধাপে মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার কাজটি সেরে নিলেন তিনি। তাদের দায়িত্ব দেওয়া হলো_ কসবা, বুড়িচং, ব্রাহ্মণপাড়া, মুরাদনগরের অংশবিশেষে দায়িত্ব পালন করার জন্য। সেই অনুযায়ী তারা যুদ্ধ করলেন বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু চারাগাছের যুদ্ধ নিয়ে এসেছিল তাদের জন্য চরম পরাজয়ের গ্গ্নানি।
আবদুল্লাহ-হিল-বাকী বলেন, সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই জানতে পারেন তাদের যেতে হবে মুরাদনগর এলাকায়। তাদের কমান্ডার ছিলেন নাজমুল হাসান পাখী। সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখ তাদের বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা ছিল। অনিবার্য কারণে দেরি হয়ে যায়। পরে রওনা হলেন ১২ তারিখে। রওনা হওয়ার পর আবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দক্ষিণে উজানিসার ব্রিজ পর্যন্ত আসতে দেরি হয়ে যায় তাদের। একপর্যায়ে গভীর রাতে নৌকায় রওনা হন জামসেদপুরের দিকে। রাজাকারদের উৎকোচ দিয়ে ব্রিজের নিচ দিয়ে বেরিয়ে আসতে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না।
খালের পাড়ঘেঁষে নৌকা চলতে থাকে পশ্চিমে চারগাছের দিকে। নিশ্চিন্ত তখন নৌকার অন্যরাও। কারণ একটু আগেই চলে গেছে ঢাকার মোস্তফা মহসীন মন্টুদের একটি নৌকা। কোনো গুলির শব্দ হয়নি। তার মানে তারাও নিশ্চিন্তেই পাড়ি দিতে পারবেন পথটুকু। নৌকায় ছিলেন নাজমুল হাসান পাখী, মমিনুল হক ভূঁইয়া দানা মিয়া, মোজাম্মেল হক আবু, নৃপেণ পোদ্দার, আবদুল্লা-হিল-বাকী, আবু জাহিদ আবু, সাইফুল ইসলাম সাফু, নাবালক মিয়া, নুরুল ইসলাম, মেহরাব হোসেন ও রকিব হোসেন। ১১ জনকে নিয়ে যেন একটি পরিবার। বয়সে ছোট হওয়ার কারণে আবু ও বাকীর আবার আদর বেশি। কমান্ডার নাজমুল হাসান পাখী থেকে শুরু করে সবাই তাদের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখেন_ কোনোভাবে যেন ছোট এ দু'জনের কোনো অসুবিধা না হয়। তাদের দিকে থাকে বড়দের তীক্ষষ্ট নজর।
নৌকা চারগাছ বাজারের কাছাকাছি পেঁৗছালে হঠাৎ আবদুল্লা-হিল-বাকীর নজরে আসে বাজারে কে যেন সিগারেট টানছে। সহযোদ্ধাদের বললেন, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগছে। ওখানে রাজাকারা পাহারা বসিয়েছে নাকি? দেখতে পেলেন অনুসন্ধানী বাতি জ্বলে উঠেছে। বাতি জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির মতো গুলি আসতে শুরু করে বাজারের দিক থেকে। গুলি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৌকার ভেতরে থাকা সাইফুল ইসলাম সাফু ও মোজাম্মেল হক আবু গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।
কমান্ডার নাজমুল হাসান পাখী সবাইকে নৌকা থেকে পাল্টা গুলি চালানো এবং আত্মরক্ষার জন্য পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেন। কমান্ডারের নির্দেশে আবু জাহিদ হাঁটুপানিতে নেমে পাল্টা গুলি করছিলেন। শত্রুপক্ষের একটি গুলি এসে আবুকে ঘায়েল করে দেয়। তিনি সেখানেই শহীদ হন। আবদুল্লাহ-হিল- বাকী ও মমিনুল হক ভূঁইয়া দানা মিয়া গুরুতর আহত হন।
বাকী জানান, আহত হওয়ার পর ঘটনাস্থল থেকে বেশ খানিকটা সরে গিয়ে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে থাকেন। ফজরের আজানের পর একটি নৌকায় করে যান চারগাছ থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরের এক গ্রামে। তার ধারণা সেটি ছিল শিকারপুর। সেখানে এক গৃহবধূ তাকে আশ্রয় দেন। তিন দিন ছিলেন সেখানে। কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর ওই নারী তাকে আগরতলায় পেঁৗছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।
যে তিন দিন বাকী তার আশ্রয়ে ছিলেন, প্রতিদিন খবর পেতেন পাকিস্তানি সৈন্যরা চারগাছের আশপাশের গ্রামগুলো তছনছ করে মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজছে। আবদুল্লাহ-হিল-বাকী বলেন, আমি যদি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সনদ ও ভাতা পাই, তাহলে আমার আশ্রয়দাতা ওই নারীর কী প্রাপ্য হয়?
সংশোধনী : আবদুল্লাহ-হিল-বাকীর তিন সহযোদ্ধা আবু জাহিদ আবু, সাইফুল ইসলাম সাফু ও মোজাম্মেল হক আবুর কবর চারগাছের পাশের গ্রাম জামসেদপুরে। গতকাল আবু জাহিদকে নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভুলবশত এই তিন শহীদের কবর চারগাছে লেখা হয়েছে। মোজাম্মেল হক আবুর ফুপাতো ভাই ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক মোস্তফা হোসেইন জানান, কবর তিনটি মোজাম্মেল হক আবুর পরিবারের উদ্যোগে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
আগামীকাল :বীরপ্রতীক রফিকুল ইসলাম
http://www.samakal.net/2014/12/08/103729
- Biplob Rahman | ০৮ ডিসেম্বর ২০১৪ ১৯:৪২582800
- অমি রহমান পিয়াল
ভারত না ভুটান: বিতর্কটির নিষ্পত্তি প্রয়োজন
ডিসেম্বর ৬, ২০১৪
সপ্তাহ খানেক ধরে অনলাইনে একটা বিতর্ক চলছে, বাংলাদেশকে কোন দেশ প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিল? কেউ বলছে ভারত, কেউ বলছে ভুটান। যারা ভুটানের পক্ষে, তাদের কারও কারও সোর্স আকাশবাণী; কারও পাঠ্যবই। আবার কেউ কেউ এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে প্রাধান্য দিয়ে হুংকার দিচ্ছেন।
যারা আকাশবাণীর রেফারেন্স দিচ্ছেন তাদের দাবি– তারা নিজেরা ইভা নাগের সুললিত কণ্ঠে শুনেছেন যে, ৩ ডিসেম্বরেই নাকি ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাকিরা কেউ পড়েছেন পাঠ্যবইয়ে, কেউ-বা বিসিএস পরীক্ষা-প্রস্তুতির সাধারণ জ্ঞান বইয়ে। কেউ লিংক দিচ্ছেন কিছু ওয়েবসাইটের, যেখানে ভুটান ৬ ডিসেম্বর এবং ভারত ৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে।
সর্বশেষ, তারা লন্ডন থেকে আবদুল গাফফার চৌধুরীর অডিও বক্তব্য ধারণ করে সম্প্রচার করছে যেখানে তিনিও ভুটান ভারতের আগে স্বীকৃতি দিয়েছে বলে জানাচ্ছেন। আজ (৬ ডিসেম্বর) সকালে একাত্তর টিভির স্ক্রলে যখন একই কথা লেখা দেখলাম, তখন মনে হল এই বিতর্কের নিষ্পত্তি প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, তৃণমূল থেকে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এ ব্যাপারে সংশোধন হওয়া দরকার।
আমি এই বিতর্কে ভারতের পক্ষে আমার মতামত দিয়েছি। এ প্রসঙ্গে আমার যুক্তিগুলো পাঠকদের জন্য তুলে ধরছি।
১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর আকাশবাণীতে ইভা নাগের সেই খবর শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে, ৮ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের বেতার ভাষণের টেক্সট পড়ার ভাগ্য হয়েছে। মুজিবনগর সরকারের দলিলপত্রে, স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র এবং বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, তিন জায়গাতেই এ বক্তৃতার বাংলা ও ইংরেজি টেক্সট রয়েছে। ৮ ডিসেম্বরের সেই বেতার ভাষণে তাজউদ্দিন আহমদ বলেছেন:
‘‘ভারতের জনসাধারণ অনেক আগেই আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছেন তাদের অন্তরে। এখন তাদের সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি জানিয়েছেন। বাংলাদেশের সর্বশ্রেণির জনসাধারণের পক্ষে এ এক বিজয়। বিজয় তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের, আর বিজয় তাদের মুক্তিবাহিনীর। … ভারতের পর ভুটান স্বীকৃতি দিয়েছে বাংলাদেশকে। এর জন্য ভুটানের রাজা ও জনসাধারণের নিকট কৃতজ্ঞ।’’
ইংরেজিতেও একই কথা লেখা:
Bhutan is the second country to accord recognition to the People’s Republic of Bangladesh. We are grateful to the King and the people of Bhutan for this noble act.
[Mujibnagar Government Documents 1971, Page: 419]
সব দলিলই নির্দেশ করছে যে, ৬ ডিসেম্বর ভারতই প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।
কথা হচ্ছে, স্বীকৃতি তো মুখে বললেই হয় না, হাবেভাবে বোঝালেও চলে না। এর একটা আনুষ্ঠানিকতা আছে। ভারত কিংবা ভুটান যে দেশই হোক, অফিসিয়ালি সেই স্বীকৃতির চিঠি পাঠানো হয়েছে তাজউদ্দিন আহমদের বরাবরেই– ইভা নাগ কিংবা আকাশবাণীতে নয়। তাহলে আমরা কার বক্তব্য বিবেচনায় নেব? মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নয় কি? তাজউদ্দিন আহমদের মতো খুঁতখুতে এবং ডিটেল নিয়ে কাজ করা মানুষ এত বড় ভুল করবেন যে, ভুটানের আগে ভারতের নাম বলে দেবেন!
১৯৭২ সালের ৬ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলা পত্রিকায় তাজউদ্দিন আহমদের একটি সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি বলেছেন:
‘‘বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের অনুরোধ জানিয়ে ১৯৭১ সালের ১৫ অক্টোবর প্রথম শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে চিঠি লিখি। এরপর ২৩ নভেম্বর আর একখানা চিঠি দিই। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ঘোষিত যুদ্ধের আগের দিন ২ ডিসেম্বর এবং পরের দিন ৪ ডিসেম্বর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি। ৬ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় ভারতীয় পার্লামেন্ট বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের কথা ঘোষণা করার পর শ্রীমতি ইন্দিরা আমাকে একখানা আনুষ্ঠানিক চিঠি দেন। ৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার বিকেল সোয়া তিনটায় মুজিবনগরে সেই চিঠি আমার হাতে এসে পৌঁছেছে।’’
দলিল আরও আছে। সে সময় মুজিবনগর সরকারের একটি আন্তর্জাতিক প্রকাশনা ছিল, নাম ‘বাংলাদেশ’। মূলত এটি ছিল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও কূটনীতিকদের জন্য। ১৯৭১ সালের ৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের প্রথম বর্ষ ২৪তম সংখ্যাটি। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ছবিসহকারে তার লিড নিউজ ছিল, ‘‘ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে।’’
একই নিউজে ছিল একটি বক্স আইটেম, যাতে লেখা:
‘‘ভারতের পর ভুটান দ্বিতীয় দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে।’’
বার্তা সংস্থা ‘রয়টার্স’ এবং ‘অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস’ এর (এপি) সৌজন্যে সেই সংবাদ বিশ্বব্যাপী প্রচারও হয়েছে।
এ লেখায় ‘রয়টার্স’ এর বরাতে ‘লন্ডন টাইমস’ এ প্রকাশিত খবরটি সংযুক্ত করা হল, যেখানে বলা হয়েছে: ভুটান ৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে।
এবার আসা যাক ৬ ডিসেম্বরের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনায়। ভারত শুরু থেকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার উদার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। দেশান্তরী বাংলাদেশ সরকারকে আশ্রয় ও মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সব ধরনের সুবিধা দিয়েছে। লাখ থেকে কোটিতে পৌছানো আমাদের উদ্বাস্তুদের আশ্রয় ও খাবারদাবারও পেয়েছি ভারতের কল্যাণে। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র ও ট্রেনিংদানের কৃতিত্ব ওদের। কিন্তু আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিপ্রদানে এত দেরি কেন!
১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে যখন বাংলাদেশ সরকার শপথ নিল, সেদিনই স্বীকৃতি দিতে পারত ওরা। তাজউদ্দিন আহমদ চারটা চিঠি দিয়েছেন একই দাবিতে। যে কোনোটির প্রত্যুত্তর হতে পারত এই স্বীকৃতি। তাহলে ৬ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা কেন?
এর উত্তর খুঁজতে আমাদের যেতে হবে আরেকটি ফ্রন্টে। জাতিসংঘ।
‘‘৩ ডিসেম্বর ছয় বছরের মধ্যে দ্বিতীয় বারের মতো সামরিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে ভারত ও পাকিস্তান। সেদিন বিকেলে ভারতের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটিতে বিমান হামলা চালিয়ে এর সূচনা করে ইয়াহিয়া খানের সরকার। হামলার কারণ হিসেবে তার যুক্তি ছিল, ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন বিষয়ে নাক গলাচ্ছে বহুদিন ধরে। তারা ‘দুষ্কৃতিকারী’দের (পড়ুন মুক্তিযোদ্ধা) সামরিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়ে পাকিস্তানের ভেতর অন্তর্ঘাত চালাচ্ছে। বহুবার সতর্ক করার পরও তাদের এই বৈরিতা থামেনি। অতএব পাকিস্তান নাচার। আক্রমণ ছাড়া উপায় নেই তাদের।’’
৫ ডিসেম্বর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন বসে। পাকিস্তানের দুই মিত্র, দুই পরাশক্তি, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন এবং তাদের তাঁবেদার দেশগুলোর প্রস্তাবনা টিকে গেলে বাংলাদেশের সহসা স্বাধীনতা লাভ হত না। দু’পক্ষে যুদ্ধবিরতির আহবান জানিয়ে প্রস্তাবনাটির মূল বার্তা ছিল, দু’পক্ষ যার যার সীমান্তে থাকবে। কেউ কারও ব্যাপারে নাক গলাবে না। প্রয়োজনে শান্তিরক্ষী বাহিনী সীমান্ত প্রহরার দায়িত্ব নেবে। নিশ্চিত করবে যুদ্ধবিরতির কার্যকারিতা।
তার মানে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিতান্তই পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন সমস্যা। ভারতকে এ থেকে হাত গুটিয়ে নিতে হবে। পাশাপাশি, সীমান্ত পাড়ি দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নিজের দেশে ঢোকার সুযোগেরও ইতি। রাশিয়া তার প্রথম ভেটোটি দিয়ে প্রস্তাবনাটি থামাল।
দৈনিক বাংলা এর সেই সাক্ষাতকারে তাজউদ্দিন আহমদ আরও বলেছিলেন:
‘‘১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট সম্পাদিত ঐতিহাসিক ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তিই ছিল স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাকে স্বীকৃতিদানের প্রথম ভিত্তি। এটি ছিল বর্তমান বিশ্বের কূটনীতির ক্ষেত্রে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর অসাধারণ সাফল্য।’’
আসলেই তাই। ৫ তারিখে বাংলাদেশ সরকারকে জানানো হয় যে, পরদিন স্বীকৃতি আসছে। ভারতীয় পার্লামেন্টের এ ঘোষণার পরপরই সেখানে উপস্থিত বিশেষ প্রতিনিধি হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে ইন্দিরা গান্ধীকে ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।
৬ ডিসেম্বরের এই ঘোষণার মাধ্যমেই বিশ্ব মোড়লদের জানান দেওয়া হয় যে, এটা এখন আর পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন সমস্যা নেই, এটা বাংলাদেশ-পাকিস্তানের সমস্যা। ভারত মানবতা ও নৈতিক ঔচিত্যবোধ থেকেই তাদের প্রতিবেশির পাশে দাঁড়িয়েছে। আর তার প্রমাণও দেখা যায় পরদিন ৭ ডিসেম্বর। পূর্ব ফ্রন্টে সীমান্ত পাড়ি দেয় ভারতীয় ট্যাংক। একসঙ্গে মার্চ করে ভারত-বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীর সমন্বয়ে গড়া মিত্র বাহিনী। যশোর মুক্ত হওয়ার মাধ্যমে শুরু হয় তাদের অভিযাত্রা, যা ১৬ ডিসেম্বর শেষ হয় ঢাকায় চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণে।
লিংক:
৬ ডিসেম্বর এবং ভারতের স্বীকৃতির তাৎপর্য বোঝাটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের স্বার্থেই তাই জরুরি। এই স্বীকৃতি একই সঙ্গে ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মতো পরাশক্তিকে জানানো একটি চ্যালেঞ্জ। ভুটানের স্বীকৃতি সম্পূরক হিসেবে কাজে এসেছে। জাতিসংঘ ও পরাশক্তিগুলো তখন ভারতকে একগুঁয়েমির অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারেনি। ৫ তারিখ থেকে বিজয়ের আগ পর্যন্ত সর্বমোট তিনটি ভেটো দিয়ে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ থেকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্তিমলগ্ন রক্ষা করেছে রাশিয়া। সেটির প্রেক্ষাপট হিসেবে, শক্ত ভিত হয়ে কাজ করেছে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি, যেটি ছিল ভারত-প্রদত্ত।
প্রসঙ্গত বলতে হয় যে, ২৯ নভেম্বর ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং টবগে তাঁর ব্যক্তিগত টুইটার অ্যাকাউন্টে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রসঙ্গে একটি বক্তব্য দিয়েছেন; সেটি এ রকম:
December 6th coincides with the day on which Bhutan became the first country after India to recognize Bangladesh’s independence.
যার অর্থ দাঁড়ায়:
১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতের পর ভুটানই প্রথম দেশ যারা বাংলাদেশকে স্বাধীন বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ফার্স্ট কানট্রি আফটার ইন্ডিয়া, ভারতের পর প্রথম। তার মানে ভারতই বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতিদানকারী দেশ।
লিংক:
https://twitter.com/tsheringtobgay/status/538674489802752000
ভুটানের প্রধানমন্ত্রী তাঁর দেশের পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাস জানবেন না এ তো হতে পারে না। যেখানে ভুটান নিজেদের দ্বিতীয় স্থানে রাখছে, সেখানে আমরা জোর করে তাদের প্রথম বানাতে চাইছি কেন? কাদের অপমান ঠেকাতে? কাদের অপমান করতে? যারা এ দেশের স্বাধীনতায় আন্তরিকতার সবটুকু উজাড় করে দিয়েছিল, তাদের? সে সঙ্গে আমরা কাকে ছোট করছি?
মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারকে, মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রকে।
একাত্তরের আকাশবাণীর সেই নিবিষ্ট শ্রোতাদের কাছে জানতে ইচ্ছে করে, যুদ্ধের হালহকিকত জানতেই তো রেডিও শুনতেন, ইভা নাগের সুকণ্ঠ মনে রাখলেন, ভুলেই গেলেন প্রধানমন্ত্রীর কথা! তাঁর বক্তব্য! বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ!
একাত্তরে, গোটা মুক্তিযুদ্ধকালে তাজউদ্দিন আহমদের কান্নায় ভেঙে পড়া একটাই ছবি মেলে। সেটি ৬ ডিসেম্বর আকাশবাণীতে তাঁর প্রতিক্রিয়া রেকর্ড করার সময়ে তোলা। ভারতের এই স্বীকৃতির মূল্য এত হালকা ভাবছেন কেন? কেন বুঝতে পারছেন না ওই একটা ঘোষণার পর বাঙালির গা থেকে ‘রিফিউজি’ শব্দটা মুছে গিয়েছিল? পাকাপাকিভাবে বসে গিয়েছিল মুক্তির জন্য লড়তে থাকা ‘মুক্তিযোদ্ধা’ শব্দটা?
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির ধাক্কায় আমাদের পরপর কয়েকটি প্রজন্ম ক্ষতিগ্রম্ত হয়েছে। তারা মুক্তিযুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত সত্যগুলো নিয়েও বিতর্ক তোলে। কারণ, তারা বইয়ে পড়েছে। ১৯৭৫ সালের পর পাঠ্যপুস্তকে যে অভিসন্ধিমূলক এডিটিং চলেছে, তা যে পুরোপুরি সংশোধন করা যায়নি, তার প্রমাণ এই ভারত-ভুটান বিতর্ক। মুক্তিযুদ্ধের সময়কার দলিল-দস্তাবেজ বিবেচনা করে এ ব্যাপারে সরকারের আশু বক্তব্য দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।
ভুল হতেই পারে। সেটা স্বীকার করে শুধরে নিলে তাতে আমরা ছোট হব না। কিন্তু একটা ছোট ভুল যদি মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়-নির্ধারণী বিষয়গুলোকে বিতর্কিত ও তুচ্ছ করে দেয়, তাহলে নিজেদের বড় অকৃতজ্ঞ মনে হবে।
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ একজন বাঙালি হিসেবে এটা আমার কাছে অপমানজনক।
অমি রহমান পিয়াল: ব্লগার, অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট।
__
http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/22909
 aranya | 154.160.226.93 | ০৮ ডিসেম্বর ২০১৪ ২১:০১582801
aranya | 154.160.226.93 | ০৮ ডিসেম্বর ২০১৪ ২১:০১582801- তাজউদ্দিন আহমদ সম্বন্ধে যেটুকু পড়েছি, এই লোকটি যদি বেঁচে থাকতেন, অনেক উপকার হত বাংলাদেশের।
দেশের সুসন্তান-দের অকালে চলে যেতে হয় :-(
- Biplob Rahman | ৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ ১৯:১৯582802
- Songs Of Freedom
Liverpool folkie who sang for Bangladesh
Zaid Bin Kalam
o me brothers and sisters of Bangladesh
Unite together and stay that way,
And remember the good times
Are coming at last
The freedom fighters are on their way,
These are the words of a song titled “Freedom fighters” by Lee Brennan, a folk singer and poet of Liverpool, England. Following the March 1971 crackdown by Pakistan army on innocent Banglaees, Brennan rushed to the members of the Bangladeshi community living in Liverpool that time to find a way how he can support the victims.
Within a very short period, Brennan produced a collection of four songs, sold the records on his own effort and donated the money to the war torn people of Bangladesh, recalls Mahbubar Rahman Khan who was in Liverpool then. Khan, former chairman of botany and microbiology departments of Dhaka University, contacted The Daily Star on December 19 this year and handed over the vinyl record of Brennan's songs.
Khan met Brennan at a Liverpool restaurant called Kismet, whose owner was from Sylhet.
Brennan asked Khan about what he can do to support the struggle for freedom in Bangladesh.
In reply Khan told him, “You are an artist, you can do many things to support us.”
Hearing Khan's reply, Brennan went silent for a couple of seconds and said, “I got your point” and then he left.
After four days, Brennan drove his Jaguar and went to Khan's flat and took him and his wife to his house.
There the Khan couple met Brennan's wife and three of his band members.
“I have composed four songs on Bangladesh, I will sing them to you and if you think that they are okay then I will record them and share it with you,” Brennan told Khan.
After listening them, Khan provided some feedbacks based on the life and culture in Bangladesh and Brennan quite humbly readjusted his lyrics and music accordingly.
“He accepted, changed and re-composed his songs which amazed me as a famous singer like him listened to such a novice like me,” Khan said.
“The next day, Brennan took one of my colleagues, Mesbahuddin, then a PhD student of chemistry, to a local music studio called CAM Records Ltd and recorded the collection,” Khan recalled.
Khan was one of the members in the city's Action Committee formed under the direct supervision of Justice Abu Sayeed Chowdhury, who became the second president of independent Bangladesh, to organise the Bangladeshi people living in England.
Justice Chowdhury played a leading diplomatic role in building support among the international communities for Bangladesh's Liberation War.
The cover jacket of the vinyl record bears the following message of Justice Chowdhury: “People of Bangladesh will fight unto the last for Truth and Justice. Victory shall be ours. Our grateful thanks are due to Lee Brennan, Dawn, Pete Thomas, John Brown, Jimmy Sefton for their sympathy and support at this hour of our grim struggle.” Abu Sayeed Chowdhury, Special Envoy, Government of Peoples Republic of Bangladesh.
This 45 RPM (rotation per minute) EP (extended play) record disk contains four songs -- two on each side. On Side A are: Freedom fighters (2:26 minutes) and Mr Human (2:03 minutes) and Side B: Fight, fight, fight (2:11 minutes) and We will survive (3:22 minutes).
Brennan himself took the burden of collecting funds for our Liberation War by selling the records, said Khan.
Brennan used to sing the songs he composed on Bangladesh at pubs and restaurants of Liverpool and sold the copies if listeners felt interested.
Published: 12:07 am Tuesday, December 30, 2014
Last modified: 12:36 pm Tuesday, December 30, 2014
__
http://thedailystar.net/backpage/songs-of-freedom-57663
- Biplob Rahman | ১২ জানুয়ারি ২০১৫ ২০:১০582803
- Documents from different local and international sources concerning the 1971 Liberation War
The Document of Surrender
The Document of Surrender
The brutality the Pakistan army showed while trying to crush Banglaees’ resistance to their massacre and struggle for independence in 1971 resulted in the world’s one of the worst genocide. While carrying out the bloodbath in the then East Pakistan, the Pakistan government kept the people of West Pakistan totally in dark about the macabre butchery. As a result, when a judicial commission formed by the Pakistan government after its 93,000 soldiers sent to crush the Bengalis surrendered to the Allied Forces on December 16, 1971 expressed its very critical opinion of the Pakistan's military interference and pointed out the misconduct of the politicians, the Pakistan government had reasons not to make the report public. It is only after an Indian magazine ‘Indian Today’ published the report of Hamoodur Rahman Commission, in 2000, that Pakistani newspaper Dawn reproduced it on August 14 the same year. The Pakistan government apparently declassified the report in December that year letting its people know for the first time ever what brutal role its military played for silence its own people back in 1971 and how heartlessly the politicians who endorsed the genocide.
While India played a very supportive role sheltering the refugees and training Bangladesh’s freedom fighters, the world superpowers aligned themselves in line with their own interests with both the United States and China backing Pakistan.
Archer Blood
Archer Blood
In doing so, the two major powers in a way gave their approval for what Archer Blood, the then US Consulate General in Dhaka, termed as “genocide” in his cables to the US State Department. Blood’s dissent cables later became famously known as "Blood Telegram".
Declassified US government documents and audio clips regarding US policy towards India and Pakistan during Bangladesh’s 1971 Liberation War detail how US policy, directed by Richard Nixon and Henry Kissinger, followed a course that became infamously known as "The Tilt" and show the brutal details of the genocide conducted in the then East Pakistan.
As we keep on enriching this repository on the 1971 Liberation War, we will gather more documents that can give an idea of the events relating to what Bangalees now cherish as their glorious struggle for independence.
If you have any such documents or know about online resources where we can find so, please let us know by emailing us at [email protected].
Hamoodur Rahman Commission Report
The Hamoodur Rahman Commission was a judicial inquiry commission constituted "to prepare a full and complete account of the circumstances surrounding the atrocities and 1971 war", including the "circumstances in which the commander of the Eastern High Command, surrendered the Eastern contingent forces under his command laid down their arms."
The report published by Indian magazine India Today
and reproduced by Pakistan’s Dawn newspaper
Justice Hamoodur Rahman Photo: Wikipedia
Justice Hamoodur Rahman Photo: Wikipedia
Its primary conclusion was very critical of the role of Pakistan's military interference and misconduct of politicians as well as intelligence failure of the Inter-Services Intelligence (ISI) and the Federal Investigation Agency permitted the infiltration of Indian agents all along the borders of East Pakistan.
Originally, there were 12 copies of the report based on extensive interviews and testimonies. Many say all the copies were destroyed, excepting one kept with the then President Zulfikar Ali Bhutto whose government did not allow disclosure of the content. However, Maj-Gen Rao Farman Ali Khan, a former political adviser to the East Pakistan governor, told Pakistan’s Dawn newspaper on August 13, 2000 that it would be wrong to say that all copies of the report had been destroyed.
The report was leaked eventually in 2000 and Indian magazine India Today published it. Dawn, Pakistan oldest English newspaper, reproduced the India Today report on August 14, 2000. In December 2000, the Pakistan government declassified the report, with additional reports concerning the year of 1971.
Justice Hamoodur Rahman handing over the commission's report to President Zulfikar Ali Bhutto. Photo: Wikipedia
Justice Hamoodur Rahman handing over the commission's report to President Zulfikar Ali Bhutto. Photo: Wikipedia
According to Rao Forman Ali, two of the 12 copies of the report had been taken by then president Bhutto and one copy was taken back when the military raided his Larkana residence following the 1977 takeover.
Talking on whether the report was genuine, Rao Farman said the Indian magazine report seems genuine as it contains all what he had said before the Hamoodur Rahman Commission. There was no reason to say that the report was fake, he added.
Meanwhile, in a rare interview in December 2001—two years and three months before his death, disgraced Gen AAK Niazi, who surrendered before the Indian army in Dhaka on December 16, accused ZA of for modifying 35 pages of Hamoodur Rahman Commission report for clearing his name in his capacity as the prime minister.
Related articles:
28/12/2000
Government declassifies Hamoodur Rahman Commission Report
Dawn
Government declassified a controversial report on the dismemberment of the country's eastern province that became Bangladesh in 1971.
10/09/2000
Gen Agha Mohammad Yahya Khan – 3
Dawn
TO the credit of the man, it must be said that Yahya Khan never denied responsibility for the part he played in the dismemberment of Jinnah's Pakistan. He made this admission on many an occasion, as well as to the Hamoodur Rahman Commission. The final sentence of Major-General Rao Farman Ali Khan's book 'How Pakistan Got Divided' reads: "A far as Yahya was concerned, the Commission stated that he had accepted responsibility for everything."
17/09/2000
Gen Agha Mohammad Yahya Khan - 4
Dawn
THIS newspaper of record did us a great service by publishing the full text of the 1974 Supplementary Report of the Hamoodur Rahman Commission the day after it was released in the Indian press. We subsequently read that our government intended to publish the 1972 Main Report of the HR Commission, but this was swiftly denied. End of story.
17/12/2013
ZA Bhutto had changed 35 pages of Hamood Commission report
The News
ISLAMABAD: As fall of Dhaka still haunts the memories of Pakistanis, disgraced Gen AK Niazi, who surrendered before the Indian army accused Zulfikar Ali Bhutto for modifying 35 pages of Hamoodur Rehman Commission report for clearing his name in his capacity as the prime minister.
Declassified US Cables
On the 31st anniversary of the creation of Bangladesh, Washington-based National Security Archive on December 16, 2002 published 46 declassified US government documents and audio clips concerned with US policy towards India and Pakistan during the 1971 Liberation War.
'Our government has failed to denounce the suppression of democracy', the then US Consulate General wrote to Washington expressing his dissent towards US policy regarding Bangladesh and Pakistan.
The documents, declassified and available at the US National Archives and the Presidential Library system detail how US policy, directed by Richard Nixon and Henry Kissinger, followed a course that became infamously known as "The Tilt".
The documents show the brutal details of the genocide conducted in the then East Pakistan in March and April of 1971.
One of the first "dissent cables" questioning US policy and morality at a time when, as the Consulate General in Dhaka Archer Blood writes the State Department, "unfortunately, the overworked term genocide is applicable”. Known as the "Blood Telegram," low classification (Limited official use) of Document 8 led to its high dissemination among government officials.
The role that Nixon's friendship with Yahya Khan and the China iniative played in US policymaking leading to the tilt towards Pakistan, George Bush Senior's view of Henry Kissinger, illegal American military assistance approved by Richard Nixon and Henry Kissinger to Pakistan following a formal aid cutoff by the US and Kissinger's duplicity to the press and towards the Indians vis-à-vis the Chinese.
Click the links below to read the individual cables:
Document 1: March 28, 1971: Selective Genocide (PDF)
Consul General Archer Blood reports of "a reign of terror by the Pak Military" in East Pakistan. Blood indicated that evidence is surfacing suggesting that Awami League supporters and Hindus are being systematically targeted by the Martial Law Administrators.
Document 2: March 28, 1971: Situation in Pakistan
Memorandum for Dr. Kissinger
Source: NPMP, National Security Council Files, Country Files, Middle East, Box 625
NSC official Sam Hoskinson tells Kissinger that events in East Pakistan have taken a turn for the worse. More significantly, this memorandum acknowledges both American recognition of the "reign of terror" conducted by West Pakistan, and the need to address the new policy issues that have been created as a result of the terror.
Document 3: March 29, 1971: Selective Genocide
U.S. Embassy (New Delhi) Cable
>Source: Record Group 59, Subject Numeric File 1970-73, Pol and Def, Box 2530
Ambassador Keating expresses his dismay and concern at repression unleashed by the Martial Law Administrators with the use of American military equipment. He calls for the U.S. to "promptly, publicly, and prominently deplore" the brutality. Washington however, never publicly spoke out against West Pakistan.
Document 4 : March 30, 1971: Killings at University
U.S. Consulate (Dacca) Cable
Source: Record Group 59, Subject Numeric File 1970-73, Pol and Def, Box 2530
Blood reports an American's observation of the atrocities committed at Dacca University. The observer indicates that students had been "shot down in rooms or mowed down when they came out of building in groups." In one instance, the MLA set a girls dormitory on fire and then the girls were "machine-gunned as they fled the building."
Document 5: March 31, 1971: Extent of Casualties in Dacca
US Consulate (Dacca) Cable
Source: Record Group 59, Subject Numeric File 1970-73, Pol and Def, Box 2530
Blood reports that an estimated 4-6,000 people have "lost their lives as a result of military action" since martial law began on March 25. He also indicates that the West Pakistani objective "to hit hard and terrorize the population" has been fairly successful.
Document 6: March 31, 1971: Army Terror Campaign Continues in Dacca; Evidence Military Faces Some Difficulties Elsewhere
U.S. Consulate (Dacca) Cable, Sitrep:, Confidential, 3 pp.
Source: Record Group 59, Subject Numeric File 1970-73, Pol and Def, Box 2530
Blood indicates that Martial Law Administrators are now focusing on predominantly Hindu areas. "Congen officer heard steady firing of approximately 1 shot per ten seconds for 30 minutes." Cable also reports that naked female bodies found "with bits of rope hanging from ceiling fans," after apparently being "raped, shot, and hung by heels" from the fans.
Document 7: April 6, 1971: USG Expression of Concern on East Pakistan
U.S. Department of State Cable
Source: Nixon Presidential Materials Project (NPMP), National Security Council Files, Indo-Pak War, Box 578.
During a conversation with Assistant Secretary Sisco, Pakistani Ambassador Agha Hilaly asks that "due allowance be made for behavior of Pak officials and others during what had amounted to civil war for a few days," because the "army had to kill people in order to keep country together." Expressing concern over the situation and bloodshed as well as use of U.S. arms in repression, Sisco observed that the US is "keenly sensitive to problems and feelings on developments [in East Pakistan]."
Document 8: April 6, 1971: Dissent from US Policy Toward East Pakistan
US Consulate (Dacca) Cable, Confidential, 5 pp. Includes Signatures from the Department of State.
Source: RG 59, SN 70-73 Pol and Def. From: Pol Pak-U.S. To: Pol 17-1 Pak-U.S. Box 2535
In one of the first "Dissent Cables," Blood transmits a message denouncing American policy towards the South Asia crisis. The transmission suggests that the United States is "bending over backwards to placate the West Pak [sic] dominated government and to lessen likely and deservedly negative international public relations impact against them." The cable goes on to question U.S. morality at a time when "unfortunately, the overworked term genocide is applicable."
Document 9: April 28, 1971: Policy Options Toward Pakistan
Memorandum for the President, Includes Nixon's handwritten Nixon note
Source: NPMP, NSC Files, Country Files: Middle East, Box 625
Kissinger presents Nixon with U.S. policy options directed towards the crisis in East Pakistan. Nixon and Kissinger both feel the third is the best as it, as Kissinger writes, "would have the advantage of making the most of the relationship with Yahya, while engaging in a serious effort to move the situation toward conditions less damaging to US and Pakistani interests." At the end of the last page Nixon writes, "To all hands: Don't squeeze Yahya at this time."
Document 10: May 10, 1971: Memorandum of Conversation (Memcon) MM Ahmad, Agha Hilaly, Henry Kissinger and Harold H Saunders
Source: Nixon Presidential Materials Project (NPMP), National Security Council Files, Indo-Pak War, Box 578.
US and Pakistani officials discuss the potential for a political solution in East Pakistan. Kissinger indicates Nixon's "high regard" and "personal affection" for Yahya and that "the last thing one does in this situation is to take advantage of a friend in need." He also offers American assistance so as to not compound "the anguish" that Pakistan "is already suffering," as a result of the repression in East Pakistan.
Document 11: May 10, 1971: Memcon The President, M.M. Ahmad, Agha Hilaly, and Harold H. Saunders
Source: Nixon Presidential Materials Project (NPMP), National Security Council Files, Indo-Pak War, Box 578.
Nixon and Pakistani officials discuss a potential political solution in East Pakistan. Nixon expresses sympathy for Pakistan by indicating that "Yahya is a good friend," and seemingly in response to the genocide like repression in the East, says he "could understand the anguish of the decisions which [Yahya] had to make." Nixon also declares that the U.S. "would not do anything to complicate the situation for President Yahya or to embarrass him."
Document 12: May 26, 1971: Possible India-Pakistan War
Department of State, Memorandum for the President
Source: Nixon Presidential Materials Project (NPMP), National Security Council Files, Indo-Pak War, Box 575.
As early as May 1971 the State Department became aware that a war was possible between India and Pakistan. This memorandum denotes three causes that may lead to an India-Pakistan war: (1)continued military repression in the East, (2) the refugee flow into India, and (3) Indian cross-border support to Bengali guerillas (the Mukti Bahini).
Document 13: June 3, 1971: Memcon Kenneth Keating, Henry Kissinger, and Harold Saunders
Source: Nixon Presidential Materials Project (NPMP), National Security Council Files Country Files: Middle East, Box 596.
Kissinger, Keating, and Saunders discuss the situation in Pakistan and American military assistance. Kissinger indicates that Nixon wants to give Yahya a few months to fix the situation, but that East Pakistan will eventually become independent. Kissinger points out that "the President has a special feeling for President Yahya. One cannot make policy on that basis, but it is a fact of life."
Document 14: July 7, 1971: Memorandum for RADM Daniel J. Murphy, Dr. Kissinger's Reports of Conversations in New Delhi
Top Secret/Sensitive/Eyes Only, 4 pp.
Source: Nixon Presidential Materials Project (NPMP), National Security Council Files, Haig Chron, Box 983.
Relaying his impressions of his visit to India, Kissinger describes the strong feelings about the heavy burden placed upon India by the refugees from East Pakistan. In his meetings with Indian officials, Kissinger discussed the East Pakistan situation, military assistance to Pakistan, and China. He assures the Indians that the U.S. "would take the gravest view of any unprovoked aggression against India."
Document 15: July 7, 1971: Memcon, Dr. Sarabhai, Dr. Haksar, Dr. Kissinger, Mr. Winston Lord
Secret/Sensitive, 4pp.
Source: NPMP, NSC Files, Pres/HAK Memcons, Box 1025
Just days before Kissinger's secret trip to China, Indian and U.S. officials discuss numerous issues, including the Soviet Union, the situation in East Pakistan, arms transfers to Pakistan, and China. During the conversation, Kissinger assures the Indians that "under any conceivable circumstance the U.S. would back India against any Chinese pressures." He also states that "In any dialogue with China, we would of course not encourage her against India."
Document 16: July 15, 1971: Indo-Pakistan Situation
Department of State, Cable, Secret, 7 pp.
Source: Nixon Presidential Materials Project (NPMP), National Security Council Files, Indo-Pak War, Box 578.
Indian Ambassador to the United States L.K. Jha and Acting Secretary John Irwin discuss the East Pakistan situation, a possible political solution, American military assistance to Pakistan, and the role of the UN in refugee camps.
Document 17: July 19, 1971: Memorandum for Dr, Kissinger, Military Assistance to Pakistan and the Trip to Peking
Secret, 2 pp. Includes handwritten Kissinger note on bottom of second page.
Source: NPMP NSC Files, Indo-Pak War, Box 574
Saunders discusses US Aid to South Asia, specifically noting the connections between U.S. military assistance to Pakistan and Pakistan's role in the China initiative. Kissinger writes, "But it is of course clear that we have some special relationship to Pakistan."
Document 18: July 28, 1971: Memorandum for the Presidents File, President's Meeting with Ambassador Joseph Farland
Secret, 5 pp. Attached to Cover Memoranda
Source: NPMP, NSC Files, Country Files: Middle East, Box 626
Nixon expresses his concern over the South Asian conflict to Ambassador Farland, "not only for its intrinsic tragedy and danger, but also because it could disrupt our steady course in our policy toward China."
Document 19: July 30, 1971: NSC Paper, South Asia: Cutting of Military and Economic Assistance
Source: Nixon Presidential Materials Project (NPMP), National Security Council Files, Indo-Pak War, Box 570.
The NSC staff discusses Congressional reaction to the conflict in East Pakistan and American military assistance. The Administration has chosen quiet diplomacy as means to motivate Yahya to avert famine and create conditions in which the refugees may return from India. "We have not openly condemned Yahya. He appreciates this."
Document 20: August 7, 1971: Handwritten Letter from President Nixon to President Yahya
Source: RG 59 PPC S/P, Directors Files (Winston Lord), Box 330.
Nixon writes to personally thank Yahya for his assistance in arranging contacts between the US and China. At a time when West Pakistani troops were engaging in a repression of East Pakistan, Nixon told Yahya that "Those who want a more peaceful world in the generation to come will forever be in your debt."
Document 21: August 11, 1971: Memorandum for the Record: The President, Henry Kissinger, John Irwin, Thomas Moorer, Robert Cushman, Maurice Williams, Joseph Sisco, Armistead Seldon, and Harold Saunders
Source: NPMP NSC Files, Indo-Pak War, Box 578
The NSC Senior Review Group discusses the situation in East Pakistan and increasing tensions between India and Pakistan. The President indicates that "the big story is Pakistan," and he expresses his concern from the standpoint of human suffering. While Nixon suggests that some Indian and Pakistani interest might be served by war, it is not in American interests as "the new China relationship would be imperiled, probably beyond repair." While stating that the Indians are more "devious" than the "sometimes extremely stupid" Pakistanis, the U.S. "must not-cannot-allow" India to use the refugees as a pretext for breaking up Pakistan. Despite the conditions in the East, which Ambassador Blood described as "selective genocide," Nixon states that "We will not measure our relationship with the government in terms of what it has done in East Pakistan. By that criterion, we would cut off relations with every Communist government in the world because of the slaughter that has taken place in the Communist countries."
Document 22: August 14, 1971: Letter from Prime Minister Gandhi
Department of State Cable, Secret, 4 pp.
Source: Nixon Presidential Materials Project (NPMP), National Security Council Files, Indo-Pak War, Box 578.
Indira Gandhi, in a letter to President Nixon, notes that the refugee flow has not slowed, and has reached approximately seven million. She questions U.S. efforts to work towards a political solution in East Pakistan as well as American arms transfers to Pakistan.
Document 23: August 16, 1971: Memorandum for the President, My August 16 Meeting with the Chinese Ambassador in Paris
Top Secret/Sensitive/Eyes Only, 16 pp. Includes Memorandum of Conversation between Huang Chen, Tsao Kuei Sheng, Wei Tung, Henry Kissinger, Vernon Walters, and Winston Lord Dated August 19, 1971.
Source: RG 59, PPC S/P, Directors Files (Winston Lord), Box 330.
Kissinger in a memorandum to Nixon describes his talks with the Chinese Ambassador in Paris. Kissinger explains to the Chinese that the U.S. is prevented from giving any military assistance to Pakistan because of Congress, but supports Chinese assistance by stating that the U.S. would "understand it if other friends of Pakistan will give them the equipment they need." He also declares that the U.S. "will do nothing to embarrass the government of Pakistan by any public statements."
Document 24: August 18, 1971: Memorandum for the President, Implications of the Situation in South Asia
Source: NPMP NSC Files, Indo-Pak War, Box 570
Kissinger discusses the developments in South Asia including Yahya's stand to not grant independence in the East, the serious insurgency movement underway in East Pakistan, and the continued flow of refugees into India. He suggests that American strategy give Yahya a face-saving way of taking the political steps necessary to re-establish normal conditions. While Kissinger wrote in his memoirs, "We had no national interest to prevent self-determination for East Pakistan," the documents show he believed otherwise. In this record, at a time when rapprochement with China was in the national interest, Kissinger suggests that "a U.S. effort to split off part of Pakistan in the name of self-determination would have implications for Taiwan and Tibet in Peking's eyes."
Document 25: September 17, 1971: Arrests of East Pakistan Intellectuals
US Embassy (Islamabad), Cable, Confidential, 3 pp.
Source: Nixon Presidential Materials Project (NPMP), National Security Council Files, Indo-Pak War, Box 576.
Indicates that repression of intellectuals in the East continues, but on a reduced scale. Ambassador Farland advises that the best policy is to continue the current practice of "persistent but quiet pressure on GOP toward better treatment of East Pakistanis in all categories."
Document 26: November 15, 1971: Memorandum for General Haig, Pakistan/India Contingency Planning
Secret/Eyes Only, , 3 pp. Includes JCS Cable.
Source: NPMP, NSC Files, Indo-Pak War, Box 570
The US disguising the movement of the nuclear aircraft carrier, the USS Enterprise into the Bay of Bengal for evacuation purposes, gladly lets the ship movement represent possible American involvement in the conflict, especially if it expanded to a superpower confrontation. Admiral Welander from the NSC Staff indicates that the JCS has approved, for planning purposes only, the CINCPAC concept to ready a USS attack carrier to dissuade "third party" involvement in the South Asia crisis.
Document 27: November 18, 1971: Pakistan Crisis
United States Embassy (Islamabad) Cable, Secret, 9 pp. Attached to Presidents Saturday Briefing and includes United Stated Embassy (New Delhi) Cables Dated November 15 and 16, 1971.
Source: Nixon Presidential Materials Project (NPMP), National Security Council Files, Indo-Pak War, Box 570
Keating suggests that Gandhi is trying to "cool" the political climate in India while continuing to exert pressure on Pakistan. The Presidents Briefing indicates however, that India is stepping up its support for the guerillas fighting in East Pakistan, action that could "goat" the Pakistanis into a full scale war.
Document 28: December 4 and December 16, 1971: White House, Telephone Conversations (Telcon)
Dated 11 pp. Includes Cover Sheet Dated January 19, 1972
Source: NPMP, NSC Files, Country Files: Middle East, Box 643.
These telcons show Nixon and Kissinger's knowledge of third party transfers of military supplies to Pakistan. Haig summarizes the Telcons to Kissinger by writing that the telcons, "confirm the President's knowledge of, approval for and, if you will, directive to provide aircraft to Iran and Jordan," in exchange for providing aircraft to Pakistan. The telcons also show that Kissinger and Nixon, following the advice of Barbara Walters, decide to put out a White House version of the facts involved with the South Asian crisis through John Scali. Nixon express his desire to, "get some PR out on the- - put the blame on India. It will also take some blame off us."
Document 29: December 7, 1971: National Security Council Memorandum for Henry Kissinger, Jordanian Transfer of F-104's to Pakistan
Secret, Includes State Department Cable to Jordan, State Department Memo to Kissinger, and United States Embassy (Amman) cable. First page has handwritten Kissinger note in which he, in reference to the title and secrecy of the issue, suggests "that title should have been omitted."
Source: NPMP, NSC Files, Indo-Pak War, Box 575
Saunders discusses Yahya's request for military equipment from the U.S. and other sources, specifically Jordan. He also observes that "by law," the U.S. "cannot authorize" any military transfers unless the administration was willing "to change our own policy and provide the equipment directly." This would rule out any transfer of American military equipment for Pakistan, supplied by the U.S., or any third party.
Document 30: December 7, 1971: Background Briefing with Henry Kissinger
Source: NPMP, NSC Files, Indo-Pak War, Box 572
As a result of American media criticism towards the U.S. position on the India-Pakistan conflict, Kissinger in an attempt to straighten the record conducts a "background" press briefing. Kissinger presents the U.S. position using many questionable facts.
Document 31: December 8, 1971: US Public Position on Road to War
United States Embassy (New Delhi) Cable, Secret
Source: NPMP, NSC Files, Indo-Pak War, Box 572.
Responding to a news story based on Kissinger's background briefing, Keating argues that many of Kissinger's statements cannot be supported. Specifically, Keating questions Kissinger's reference to Indian requests for a relief program, the Pakistani offer of amnesty to Awami Leaguers, and his claim that Washington has favored autonomy for East Pakistan.
Document 32: December 10, 1971: Event Summary by George H.W. Bush
Source: George Bush Presidential Library. George H.W. Bush Collection. Series: United Nations File, 1971-1972, Box 4.
UN Ambassador Bush describes the December 10 meeting between Kissinger and the Chinese delegation to the United Nations. While discussing the India-Pakistan crisis, Kissinger reveals that the American position on the issue was parallel to that of the Chinese. Kissinger disclosed that the U.S. would be moving some ships into the area, and also that military aid was being sent from Jordan, Turkey, and Iran. Some of this aid was illegally transferred because it was American in origin. Bush also reports that Kissinger gives his tacit approval for China to provide militarily support for Pakistani operations against India. Bush expresses his personal doubts in the administration's "Two State Departments thing," and takes issue with Kissinger's style, in one instance calling him paranoid and arrogant.
Document 33: December 8, 1971: NSC List, Courses of Actions Associated with India/Pakistan Crisis
Top Secret/Sensitive, Source: NPMP, Country Files: Middle East, Box 643.
Possible American courses of action with regards to the India/Pakistan crisis included notification to China that the U.S. would "look with favor on steps taken" by Beijing to "demonstrate its determination to intervene by force if necessary to preserve the territorial integrity of West Pakistan to include subtle assurance the Government of the United States will not stand by should the Soviet Union launch attacks against the PRC."
Document 34: December 9, 1971: Pakistan Request for F-104's
Department of State Cable, Secret, Source: NPMP, NSC Files, Indo-Pak War, Box 573.
The transfer of F-104 planes to Pakistan from both Jordan and Iran is under review at "very high level of USG."
Document 35: December 9, 1971: Defense Intelligence Agency Intelligence Appraisal, Communist China's Capability to Support Pakistan
Source: NPMP, NSC Files, Indo-Pak War, Box 572.
The DIA assesses the limits and possibility of Chinese support to the Pakistanis. It opines that while Chinese support will be limited to political, diplomatic, and propaganda for the time being, the PRC could initiate small attacks in the high mountainous areas in the East, and therefore occupy Indian troops without "provoking Soviet retaliatory moves."
Document 36: December 12, 1971: Memcon, Huang Ha, T'ang Wen-sheng, Shih Yen-hua, Alexander Haig, Winston Lord
Top Secret/Sensitive, Exclusively Eyes Only,
Source: RG 59, PPC S/P, Directors Files (Winston Lord), Box 330.
In a discussion of the India-Pakistan situation, Haig declares that the U.S. is doing everything it can do to facilitate transfers of fighter planes and military supplies from Jordan, Iran, and Saudi Arabia to Pakistan.
Document 37: December 14, 1971: Carrier Deployment in Indian Ocean
Department of State of Cable, Secret
Source: NPMP, NSC Files, Indo-Pak War, Box 578
Indian Ambassador Jha expresses his concern over American deployment of a Nuclear Carrier in the Indian ocean.
Document 38: December 14, 1971: Situation in India-Pakistan as of 0700 hours (EST)
Department of State, Situation Report #41, Secret,, 4 pp.
Source: NPMP, NSC Files, Indo-Pak War, Box 573
The State Department sees the possibility of a ceasefire in the East; Notes that Eleven Jordanian F-104 fighter aircraft have possibly been sent to Pakistan.
Document 39: December 15, 1971: Situation in India-Pakistan as of 0700 hours (EST)
Secret, Department of State, Situation Report #44,
Source: NPMP, NSC Files, Indo-Pak War, Box 573
Heavy fighting is turning in favor of the Indians, while cease-fire plans continue to be in the works. A controversy is brewing with regards over the U.S. decision to send a nuclear carrier into the Bay of Bengal.
Document 40: December 15, 1971: United States Embassy (Islamabad) Cable
Top Secret/ Exclusive Eyes Only
The present trickle of Mig-19's and F-104's will not hold off the Indians. Handwriting next to Mig-19's notes "China" and next to F-104's notes "Jordan."
Document 41: December 15, 1971: Deployment Carrier Task Force in Indian Ocean
United States Embassy (New Delhi), Cable, Secret, 2 pp.
Source: NPMP, NSC Files, Indo-Pak War, Box 573
Keating describes his difficulty in explaining the rationale behind the deployment of a carrier task force. He also suggests that the decision to send the task force into the Indian Ocean has only encouraged Yahya to continue the Pakistani military effort.
Document 42: December 16, 1971: India-Pakistan Situation Report (As of 1200 EST)
Central Intelligence Agency, Intelligence Memorandum, Top Secret,
Source: NPMP, May Release, MDR# 4.
India has ordered a unilateral cease fire upon the unconditional surrender of West Pakistani forces in East Pakistan. Despite the cease-fire, American officials in Dacca report that "no one seems to be in effective control of the situation," and that fighting continues "between Bengalis and scattered "Mujahid/Razakar/West Pakistani elements." Also, in a heavily excised paragraph, the CIA reports that a squadron of American origin, Jordanian F-104's was delivered to Pakistan on 13 December, despite an American embargo on military supplies to both India and Pakistan. This embargo includes third party transfers of American equipment to either of the parties.
Document 43: December 23, 1971: Supply of Third Country US Arms to Pakistan
Department of State, Cable, Secret
Source: NPMP, NSC Files, Indo-Pak War, Box 575
Secretary Rogers suggests that Keating neither confirm nor deny allegations that the U.S. endorsed Jordanian and Iranian transfer of American arms to Pakistan.
Document 44: December 29, 1971: F-5 Aircraft to Pakistan
United States Embassy (Tehran), Cable, Secret, , 3 pp. Includes DOD cable.
Source: NPMP, NSC Files, Indo-Pak War, Box 575
Embassy Iran reports that three F-5A Fighter aircraft, reportedly from the United States, had been flown to Pakistan to assist in the war efforts against India. A Northrop official matches the aircraft to a group of planes originally slated for sale to Libya, but which were then diverted to USG control in California. This information suggests that not only did Washington look the other way when Jordan and Iran supplied U.S. planes to Pakistan, but that despite the embargo placed on Pakistan, it directly supplied Pakistan with fighter planes.
Document 45: January 6, 1972: National Security Council, Notes, Anderson Papers Material
Source: NPMP, NSC Files, Country Files: Middle East, Box 643.
The Nixon administration, during the East Pakistan crisis convened meetings of the Washington Special Action Group (WSAG) to discuss the situation in South Asia. Records of these meetings were kept, and somehow leaked to Syndicated columnist Jack Anderson. Anderson's articles, based on classified WSAG minutes became contentious, not only because they quoted from leaked classified material, but also for their racy content. Kissinger and others in the administration became upset at Anderson's exposure of White House policies because, among other things, it revealed the tilt towards Pakistan, despite the genocidal conditions in the East.
Notes:
Anderson, Jack with George Clifford. The Anderson Papers. (New York: Random House, 1973) 214.
Brown, W. Norman. The United States and India, Pakistan, and Bangladesh. (Cambridge: Harvard University Press, 1972) 217. Other public estimates of the final death toll range from one to three million.
Ganguly, Sumit. Conflict Unending: India-Pakistan Tensions since 1947. (New Delhi: Oxford University Press, 2001) 61.
Anderson: 215.
American military assistance was cutoff to Pakistan following the commencement of violence in East Pakistan. Then in early December 1971, when the conflict grew to an India-Pakistan war, aid to India was also suspended. See documents 23 and 29. In the former, Kissinger acknowledges that American assistance to Pakistan is forbidden by Congress, whereas in the latter Harold Saunders observes that "by law," the U.S. "cannot authorize" any military transfers, including third party transfers, unless the administration was willing "to change our own policy and provide the equipment directly."
Document 8, a cable transmission from Consul General Archer Blood to the State Department has been very controversial. Known as the "Blood Telegram," its low classification (Limited official use) led to its high dissemination among government officials. The day after it was sent, the State Department reclassified the message as secret, in efforts to limit its spread. Blood's role in the transmission of this cable has been blamed for his being transferred out of Dacca by the Administration. Kux, Dennis. The United States and Pakistan, 1947-2000: Disenchanted Allies. (Washington, D.C.: Woodrow Wilson/Johns Hopkins University Press, 2001); Blood, Archer. Oral history interview, Foreign Affairs Oral History Collection. Georgetown University Library, June 1990.
See Note 5.
See Also Burr, William ed. The Kissinger Transcripts. (New York: The New Press, 1998); Ganguly, Sumit. Conflict Unending: India-Pakistan Tensions since 1947. (New Delhi: Oxford University Press, 2001); Hitchens, Christopher. The Trials of Henry Kissinger. (New York: Verso Books, 2001); Sisson, Richard and Leo E. Rose. War and Secession: India, Pakistan, the United States, and the Creation of Bangladesh. (Berkeley: University of California Press, 1990); Kissinger, Henry. The White House Years. (Boston: Little Brown and Co., 1979).
http://www.thedailystar.net/freedom-in-the-air-documents
- Biplob Rahman | ২৫ মার্চ ২০১৫ ১৫:৪৮582804
- 12:00 AM, March 25, 2015 / LAST MODIFIED: 02:49 PM, March 25, 2015
War Crimes Tribunals
Five years, 17 verdicts
Staff Correspondent
The trial of war criminals passed yet another year with two special war crimes tribunals having delivered eight verdicts so far to the satisfaction of the justice seekers.
But delay in initiating trial against Jamaat-e-Islami as an organisation for its alleged crimes committed during the Liberation War frustrates many. Besides, no verdict of the tribunals was executed in the last one year due to legal proceedings at the Supreme Court, further extending people's long wait.
The Awami League-led government formed an International Crimes Tribunal (ICT) on March 25, 2010 in line with the party's electoral pledge to try the war criminals. A second tribunal was formed on March 22, 2012 to expedite the trial.
In last one year, the International Crimes Tribunal-1 delivered verdicts in the cases against Motiur Rahman Nizami, MA Zahid Hossain Khokon, Mobarak Hossain, ATM Azharul Islam and Abdul Jabbar. All but Jabbar were sentenced to death for their wartime crimes. Jabbar was sentenced to imprisonment until death for the same offences.
The International Crimes Tribunal-2 has meanwhile delivered verdicts in the cases against Abdus Subhan, Mir Quasem Ali and Syed Mohammad Quasar. All of them were sentenced to death for their wartime crimes.
Prosecutor Rana Dasgupta said there were many limitations, but the prosecutors tried their best.
“The trial was actually an unfinished task of the Liberation War. We have tried to complete it with honesty and sincerity. We believe we have not failed. But it's the people who will evaluate whether we are successful,” he told The Daily Star last night.
Sanaul Huq, a senior member of the investigation agency, added, “We are satisfied with our performance and believe that we have been able to meet the aspiration of the people to some extent.”
But the prosecution could not initiate trial against Jamaat-e-Islami as the government has yet to take initiatives to bring amendment to the International Crimes (Tribunals) Act, 1971, which is considered as the main obstacle to prosecuting the party.
The investigation agency on March 25 last year completed its probes into the alleged war crimes committed by Jamaat and handed over the report to the prosecution.
Rana Dasgupta said they were waiting for the amendment so that Jamaat could be prosecuted. The matter whether trial of Jamaat could be held at all would be the centre of all discussion next year, he added.
Shyamoli Nasrin Chowdhury, widow of martyr physician Alim Chowdhury, feels relieved that the AL government initiated the trial after four decades of wait. “But it hurts when we see delay in execution of the verdicts and beginning of Jamaat's trial.”
“The trial of Jamaat should be taken seriously. We do not like negligence,” said Shyamoli, also the senior vice-chairperson of Ekattorer Ghatak Dalal Nirmul Committee.
TRIBUNALS GET OWN MANPOWER
For smooth functioning of the special courts, the tribunal authorities have meanwhile begun recruiting their own manpower, a need that was felt since the beginning of the war crimes trial.
The recruitment is going on in phases. The tribunals have so far been functioning with personnel hired from the High Court, Dhaka District and Sessions Judges Courts, Court of Chief Metropolitan Magistrate, Dhaka, and Administrative Tribunals.
http://www.thedailystar.net/frontpage/five-years-17-verdicts-73581
- Biplob Rahman | ২৯ এপ্রিল ২০১৫ ১৭:৪৩582805
- কালরাতের পাতা উল্টে
স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা / শিল্প-সাহিত্য
বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম
২৫ মার্চ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। কার্যত এদিন থেকেই হয়েছিল নয়মাসব্যাপী মহান মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাত। ২৫ মার্চই বাংলার বুকে লাখো মুক্তিযোদ্ধার জন্ম দিয়েছিল।
সময়টা ২৫ মার্চ, ১৯৭১। রাত তখন প্রায় ১টা। রাজধানীজুড়ে সবাই তখন ঘুমে নিমগ্ন। চারদিক সুনসান। হঠাৎ করেই যেন নেমে এলো গুমোট অন্ধকার। চারদিকে শুধু গুলির আওয়াজ। পাকিস্তানি হায়েনাদের অবিরাম তাণ্ডবে কাঁপছে বাংলার মাটি। বর্বর হানাদারের বুটের তলায় কান্নারত নিষ্পাপ শিশু আর নারী-পুরুষের বাঁচার আর্তনাদ। এ কী দুঃস্বপ্ন, নাকি সত্যি!
সেদিন খাকি পোশাকের পাকিস্তানি পিশাচদের একটাই চাওয়া, রক্ত! তারা রক্ত চায়। নিরীহ বাঙালির তাজা রক্তে পিপাসা মেটাতে চায় নিজেদের। নিমিষেই রক্তের জোয়ারে ভেসে গেল ঢাকা। বাতাস ভারি হয়ে এলো শত শত মানুষের তাজা রক্তের গন্ধে। এজন্য ২৫ মার্চের ভয়াল এ রাতের আরেক নাম কালরাত।
১.
স্বাধীন বাংলার ইতিহাসের পাতায় নিষ্ঠুর এ হত্যাযজ্ঞের নাম ‘অপারেশন সার্চলাইট’। কাপুরুষ পাকিস্তানিরা বাঙালির মুখোমুখি হতে না পেরে ঘুমন্ত মানুষের উপরই আক্রমণ চালায়। ভীতুরা দিনের আলো ভয় পায়। আর তাই বুঝি রাতের আঁধাকেই আশ্রয় করে নিল তারা। পশ্চিম পাকিস্তান এ ঘৃণ্য কাজের জন্য ব্যবহার করল ‘বেলুচিস্তানের কসাই’ খ্যাত জেনারেল টিক্কা খানকে।
একটু পেছন থেকে ইতিহাসের পাতা ওল্টালে, দিনটি ১৬ মার্চ, ১৯৭১। পশ্চিম পাকিস্তানের দমন-পীড়নে অতীষ্ট হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। বৈঠকের প্রতিপাদ্য বিষয়, বিগত দিনে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাজারো নিরীহ বাঙালি হত্যার প্রতিবাদ এবং আলোচনার মাধ্যমে সব দাবিদাওয়ার গ্রহণযোগ্য সমাধান করা। তবে কে জানত, এ আলোচনা ছিল শুধুমাত্র বাক্যব্যয় আর ইয়াহিয়ার নিছক ছলনা।
২.
আলোচনার আড়াই ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। সারাদেশের জনগণ আকুল হয়ে রয়েছে, আলোচনার ফলাফল শোনার জন্য। মনে পোষা স্বাধীন পায়রা বাংলার নীল আকাশে ওড়াবে বলে মানুষ যখন স্বপ্ন দেখছে, তখন ইয়াহিয়া তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মৃত্যুফাঁদের নকশা কেটে ঢাকা ছাড়লেন। ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ঘুমন্ত-নিরস্ত্র জনতার উপর পাকিস্তানি সেনার পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ।
তারা বর্তমান ফার্মগেটসহ পিলখানা ইপিআর হেডকোয়ার্টারে আক্রমণ চালায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগ, শাঁখারি বাজারসহ সমগ্র ঢাকাতেই শুরু হয় ব্যাপক জ্বালাও-পোড়াও ও আক্রমণ। ট্যাঙ্ক আর ভারী মেশিনগানের শব্দে ধু-ধু হয়ে যাচ্ছিল বাতাসের প্রতিটি ভাঁজ। শুধু তাই নয়, ঢাকার অলিগলিতে তারা চালায় হত্যা, লুট ও ধর্ষণ।
সে রাতেই হত্যা করা হয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক অধ্যাপক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরদা, ড. ফজলুর রহমান খান, অধ্যাপক এম মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক এম এ মুক্তাদির, অধ্যাপক এম আর খাদেম, ড. মোহাম্মদ সাদেক প্রমুখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের।
জগন্নাথ হলের কয়েকশ নিরীহ ছাত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের লাশ পুঁতে ফেলা হয় মাটিতে। রোকেয়া হলের মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যান্টনমেন্টে। বৃদ্ধ, শিশু, রিকশাওয়ালা, ভিখারি, ফুটপাথবাসী, দিনমজুর থেকে শুরু করে শহরের কোনও শ্রেণির মানুষই সেদিন রেহাই পায়নি তাদের পাশবিক অত্যাচার থেকে।
অন্যায়ভাবে পুড়িয়ে দেওয়া হয় দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, সাপ্তাহিক গণবাংলা ও দৈনিক পিপলের অফিস। মিরপুর, মোহাম্মদপুরের বিহারিরা আশেপাশের বাঙালি প্রতিবেশিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রবল হিংস্র উন্মাদনায়।
একরাতেই চোখের পলকে বদলে গেল নগরীর চিত্র। ঢাকা পরিণত হলো মৃতের শহরে। যখন পাকিস্তানি পিশাচেরা থামল, রাত তখন শেষ। বাংলার আকাশে বিষণ্ণ সূর্য। সেদিনের সূর্যটাও যেন ছিল রক্তাক্ত। এলাকার পর এলাকা জুড়ে শুধু লাশ আর লাশ। পোড়া ছাইয়ের গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে লাশের গন্ধ।
৩.
এরপর ২৬ মার্চের সূর্য, প্রতিবাদের সূর্য। সবুজ বাংলার স্বাধীনতার এ লাল টুকটুকে সূর্যটাকে ছিনিয়ে আনবে বলে বেরিয়ে পড়ে বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা।
পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ রাতেই ঢাকায় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করলেও দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর সংকল্পবদ্ধ প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।
২৫ মার্চের পাকিস্তানি সেনাদের এ আক্রমণ স্বাধীনতা যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়, যা দীর্ঘ নয় মাস দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। আর মুক্তিযোদ্ধাসহ সব শহীদদের দৃঢ় সংকল্প আর আত্মত্যাগের মাধ্যমে আজ স্বাধীন বাংলায় উড়ছে লাল সবুজের পতাকা। তাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।
http://banglanews24.com/fullnews/bn/379994.html
- Biplob Rahman | ২৯ এপ্রিল ২০১৫ ১৭:৪৪582806
- বাংলাদেশ বেতারের শ্রোতাবন্ধুহীনতা | তুষার আবদুল্লাহ
স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা / শিল্প-সাহিত্য
বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম
লেখার প্রতিপাদ্য যদি হয় উজ্জীবিত বা প্রণোদিত শব্দ যুগল, তাহলে আলোচনার ব্যপ্তি ’৭১ থেকে ২০১৫ নাগাদ বিস্তৃত করা সহজ হবে। মনে করি এই বিস্তৃতির অনিবার্যতাও আছে। একাত্তরে রণক্ষেত্রে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য উজ্জীবনী ভূমিকা রেখেছিল বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। যা পরবর্তীতে পরিচিতি পায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে।
বাংলাদেশের প্রথম বেতার কেন্দ্রের কাজই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে। দেশের শিল্পী ও চিন্তক শ্রেণির যারা বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম বাংলায় যেতে পেরেছেন, তাদের একটি বড় অংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। রণাঙ্গন থেকে কোনও কোনও মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সাংবাদিকতাও করেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিকল্প সেনাপতির কাজও করেছে। কারণ যুদ্ধের গতি প্রকৃতি কোন দিকে যাচ্ছে, মুক্তিযোদ্ধাদের কী কৌশল নিতে হবে, সেটা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সূত্রে পেয়ে যেতেন মুক্তিযোদ্ধারা।
অন্যদিকে পাক হানাদার বাহিনীকে হতাশায় নিমজ্জিত করা, মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করার কাজটিও করেছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত উর্দু অনুষ্ঠান। যারা মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ নিতে পারেননি, তারাও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের নয়মাসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র জনমানুষের গণমাধ্যম হিসেবে নিজের স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করতে পেরেছিল। জনগণ এই বেতারকে গ্রহণ করেছিল নিজেদের মত প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে। বলা যায় একাত্তরের এটিও একটি বড় বিজয় বা অর্জন।
মুক্তিযুদ্ধ শেষে দেশ স্বাধীন হবার পর গঠিত হলো বাংলাদেশ বেতার। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রজাতন্ত্রের নাগরিকেরা ভেবেছিলেন, বাংলাদেশ বেতারও তাদের মতপ্রকাশের মাধ্যম হবে। কিন্তু তাদের সেই ধারণা বা বিশ্বাসটি মিথ্যে হয়েছে বা বলা যায় তারা প্রতারিত হয়েছেন। এই গণমাধ্যমটি আর জনমানুষের থাকেনি। বাংলাদেশ বেতার বিভিন্ন তরঙ্গ এবং উপকেন্দ্রে বিস্তৃত হয়েছে, কিন্তু সেই তরঙ্গটি রাষ্ট্র বা ক্ষমতার কাঠামোর প্রচার যন্ত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে বেশি। দেশে টেলিভিশন সহজলভ্য হবার আগ-পর্যন্ত বেতারের ওপরই ছিল শ্রোতাদের নির্ভরশীলতা। খবরের জন্য তারা বেতারের দিকেই কান পেতে থাকতেন। একটা পর্যায় পর্যন্ত মানুষ বেতার যা বলত, তাই বিশ্বাস করত।
ধীরে ধীরে মানুষের সেই বিশ্বাসের ভূমিতে ধস নামতে থাকে। রাজনৈতিক সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে যখন সামরিক সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন থেকেই মূলত বেতার সরকারি যন্ত্রে রূপ নিতে থাকে। স্বৈরাচার সরকারের সময় থেকেই বেতার সাহেব-গোলামের বাকসোতে রূপ নেয়। বেতারের এই রূপবদল ঐ মাধ্যমটির প্রতি সরিয়ে নেয় জনগণের আস্থা। এর যৌক্তিক কারণও ছিল। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময় সাধারণ জনগণের ওপর রাষ্ট্রযন্ত্রের যে নৃশংসতা নেমে এসেছিল, তার খবর কিন্তু বাংলাদেশ বেতারে আসেনি। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের খবরও জায়গা পায়নি সরকারি বেতার যন্ত্রে।
হুম, বাংলাদেশ বেতার আসলে এতদিনে সরকারি বেতার যন্ত্রের পুরো চরিত্রই নিয়ে নিয়েছিল। সেখানে জনগণের কোনও সংবাদ পাওয়ার সুযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জনগণ তখন সত্য খবরের জন্য আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। সেখান থেকেই দিনশেষে দেশের রাজনৈতিক খবরাখবরের হাল নাগাদ অবস্থা জানতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে শ্রোতারা।
নব্বইতে স্বৈরাচার সরকারের পতন ঘটলেও, বাংলাদেশ বেতারকে ব্যবহারের যে অভ্যাসটি রাষ্ট্রযন্ত্র বা ক্ষমতাসীনদের হয়ে উঠেছিল—সেই বলয় থেকে পরবর্তী গণতান্ত্রিক সরকারগুলোও আর বের হতে পারেনি। আজও বাংলাদেশ বেতার সরকারের প্রচার যন্ত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। গণমাধ্যম বিস্ফোরণের ফলে বেসরকারি টেলিভিশন এবং বেতার আসাতে সত্য খবরের জন্য আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের প্রতি শ্রোতাদের এখন আর নির্ভর করতে হচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু বাংলাদেশ বেতার তার শ্রোতাদের আর ফিরিয়ে আনতে পারেনি সত্য খবর জানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে।
কেবল খবরের কথাই বলছি কেন, অনুষ্ঠান তৈরির ক্ষেত্রেও দলীয় বিভাজন বা দলকানা আচরণটি বেতারে স্পষ্ট। অনুষ্ঠানগুলোকেও সরকারের প্রপাগান্ডা এবং সরকারিদল মনষ্কদের পদচারণায় মুখর রাখা হয়েছে। কোনও কোনও গণমাধ্যম বিশ্লেষকদের মতে, এই ভূমিকাটি স্বৈরাচার সরকারের সময়কালের চেয়ে গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর সময়কালে আরও প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এবং ক্রমশ তা ঘনীভূতই হচ্ছে।
বেতার তার পচাঁত্তর বছর পালন করল। বিষয়টি গৌরবের। কিন্তু এই বেতারের গোড়া পত্তন বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালীন সূচনালগ্নে এবং স্বাধীন বাংলা বেকারকেন্দ্রের সঙ্গে যাদের সম্পৃক্ততা ছিল, তারা গৌরবের চেয়ে বরং শ্বাস ছাড়ছেন বড় দীর্ঘ করে। আফসোসের এবং বেদনার জায়গাটি হলো—তাদের প্রত্যক্ষ সময়কালেই বাংলাদেশ বেতার তাদের সাধারণ শ্রোতাদের থেকে দূরের তারা সম দূরত্বে অবস্থান নিয়েছে। বাংলাদেশ বেতারকে এখন আর প্রজাতন্ত্রের নাগরিকেরা তাদের উচ্চারণ ও ভাবনার মাধ্যম মনে করেন না। এই দুঃখবোধের জায়গা থেকে বাংলাদেশ বেতার অদূর সময়ে মুক্তি পাবে, সেই স্বপ্ন দেখারও ভরসা পাচ্ছেন না তারা।
http://banglanews24.com/fullnews/bn/380038.html
- Biplob Rahman | ২৯ এপ্রিল ২০১৫ ১৭:৪৭582808
- যুদ্ধদিনের গদ্য | সালেক খোকন
স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা / শিল্প-সাহিত্য
বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম
তাঁর নাম বাকি মোল্লা। বয়স আটষট্টির মত। একাত্তরে পাকিস্তানি সেনাদের গুলির আঘাতে কেটে ফেলতে হয় তাঁর ডান পা। শরীরের ভারে বাঁ পা-ও এখন বেঁকে গিয়েছে। ফলে হাঁটতে পারেন না, শুধু শরীরে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারেন। জীবনের হিসেব তাঁর মিলে না। তাই বুকে পুষে রাখা কষ্ট এবং কান্না-হাসির মাঝে কেটে যাচ্ছে তাঁর দিনগুলি।
খবর পেয়ে একদিন আমরা পা রাখি বাকি মোল্লার বাড়িতে।
মিরপুর চিড়িয়াখানার পাশেই একটি খুঁপরি ঘরে আমরা খুঁজে পাই মুক্তিযোদ্ধা বাকি মোল্লাকে। টিনে ঘেরা ছোট্ট ঘর। একটি চৌকি, টেবিল ও একটি হুইলচেয়ার ছাড়া তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। যুবক বয়সী একজন পাশের ঘর থেকে নিয়ে এলো একটি কাঠের বেঞ্চ। সেখানে বসেই আমরা চোখ রাখি বাকি মোল্লার চোখে।
পরিচয় দিতেই তিনি প্রশ্ন করেন, ‘কেন আইছেন?
আপনার কথা, মুক্তিযুদ্ধের কথা আর দেশের কথা শুনতে।
তিনি উত্তেজিত হয়ে যান। পরক্ষণেই চোখ ভেজান বুকে পুষে রাখা কষ্টের স্মৃতিগুলো অনুভব করে।
স্বাধীনতার জন্য শুধু অঙ্গ নয়, এই যোদ্ধা হারিয়েছেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকুও। দেশের জন্য আত্মত্যাগের প্রতিদান তিনি চান না। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর অন্যদের সঙ্গে নিজের জীবনের হিসেবটুকুও তিনি মেলাতে পারেন না। তিনি শুধু বললেন, ‘আমরা তো ভিখেরির মত বেঁচে আছি। কর্তব্য ছিল, করে দিছি। এখন যদি হাজারও মাথা ঠুকি, আপনি পারবেন না আমার একটা অঙ্গ ফিরায়া দিতে। শরীরের ভারে বাম পা-ও বেঁকে গেছে। বসতে পরি না। চলতে পারি না। এত কষ্ট লাগে আমার।’
বাকি মোল্লা যুদ্ধ করেন ৭নং সেক্টরের সাব সেক্টর লালগোলা ডাক বাংলা ক্যাম্পের অধীনে। প্রথম অপারেশনেই তিনি গুলিবিদ্ধ হন। সেদিনের আদ্যোপান্ত শুনি মুক্তিযোদ্ধা বাকির জবানিতে:
‘১৯৭১ সালের জুনের প্রথম সপ্তাহের ঘটনা। রাজশাহীর বাসুদেবপুর অপারেশন। খবর ছিল ভিতরবাগ, মইরবাগ থেকে পাকিস্তানি সেনাদের একটি বহর যাবে নন্দনগাছির দিকে। আমরা মাত্র ২৫-৩০জন। কমান্ডে নায়েক সুবেদার কাশেম। আমাদের কাছে ছিল মার্কও রাইফেল। রাতে আমরা পজিশন নিই আড়ানি ব্রিজের পাশে। ভোর হয়-হয়। পাকিস্তানি সেনারা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসছিল। আতঙ্ক তৈরি করে ওরা এভাবেই পথ চলত।
ব্রিজের কাছাকাছি আসতেই আমরা দুইপাশ থেকে আক্রমণ করি। গুলি ছুঁড়ে আমি দৌড়ে সামনে আগাইতে যাই। অমনি একটা গুলি আইসা লাগে আমার ডান পায়ের হাঁটুতে। আমি দুই লাফ গিয়ে ছিটকে পড়ি। শরীরটা তখন দুইটা ঝাড়া দেয়। প্রথম বুঝতে পারি নাই। অসহায়ের মত পড়ে ছিলাম। মৃত্যুভয় তাড়া করছিল। সহযোদ্ধারা আমাকে টেনে পেছনে এক গ্রামের ভেতর নিয়ে যায়। পরে একটা দরজার পাল্লায় শুইয়ে আমাকে নেওয়া হয় আড়আলীর বাজারে। ওইখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সন্ধ্যায় সাগরপাড়া ক্যাম্পে এবং সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় মুর্শিদাবাদের বহরমপুর হাসপাতালে। ওইখানেই অপারেশন করে আমার ডান পা হাঁটুর উপর এক বিঘাত থেকে কেটে ফেলা হয়। জ্ঞান ফিরতেই দেখলাম পা-ডা নাই।’
এক পা হারালেও মুক্তিযোদ্ধা বাকি বেঁচে আছেন, এটাই ছিল তাঁর সান্ত্বনা। স্বাধীন দেশে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখের সংসার করবেন। বাড়িতে রেখে আশা অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর কোলে দেখবেন ফুটফুটে নবজাতক। স্বাধীনতার পর এমন স্বপ্ন নিয়ে বাড়ি ফিরে তিনি দ্বিতীয়বার রক্তাক্ত হন। বাকি মোল্লার ভাষায়:
“আমি স্টেশনে নামি, এক হাজির পোলা মধু আমারে দূর থেকে দেখে ছুটে আসে, ‘কী রে, ভাই বাকি?’ জড়িয়ে ধরে বলে, ‘আহা রে তোর পরিবারডা মারা গেল। পেটের সন্তানডাও মরিছে। তুই দেখতে পারস নাই।’ শুনেই আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। আমার স্ত্রী কুলসুম বড় ভালো মানুষ ছিল। স্বাধীনতার জন্য তারেও হারালাম!”
আরেক যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুল কুদ্দুস মীর। ১১ নং সেক্টেরের অধীনে তিনি গেরিলা অপারেশন করেন নেত্রকোণায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি বাম পায়ের হাঁটুর উপরে মারাত্মকভাবে গুলিবিদ্ধ হন। ফলে তিনি চলছেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। বয়স ষাটোর্ধ্ব। তবুও গুলিবিদ্ধ হওয়ার রক্তাক্ত সে দিনটি আজও তাঁর কাছে জীবন্ত। শুনব তার মুখ থেকে:
‘১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১। রাত তহন ১১ টা। নেত্রকোণার নেতাই নদীর পাড়ে আমরা পুরা প্লাটুন। কমান্ডে নির্মল দত্ত। পাকিস্তানি সেনারা পূর্বধলা থেকে অ্যাডভান্স হইছিল। ওদের ঠেকানোর জন্যই নদীর তীরে আমরা পজিশন লই। আমাদের কাভারিংয়ের জন্য পজিশনে ছিল রজব কোম্পানি ও ১ নম্বর সেকশন। পেছনে ভারতীয় সেনারা। ওরা পূর্বধলা পার হয়েছে খবর পাইয়া আমরা ভারতীয় সেনাদের ম্যাসেজ পাঠাই। তারা টুআইস মটর ছাড়তে থাকে। পাকিস্তানি সেনারা তহন ঘাবড়ে যায়। ধীরে ধীরে পিছু হটে। এ সুযোগে আমরা অ্যাডভান্স করি।
বৃষ্টির মতো গুলি চলছিল। আমি আইলে শুয়ে স্ট্যানগান চালাচ্ছি। পাশেই এলএমজি ম্যান হারুনুর রশিদ। আমার ডান দিকে এবাদত আলী। হঠাৎ একটা গ্রেনেড এসে পড়ে হারুনের সামনে। আমি তাকে পা দিয়া ধাক্কা দিতেই সে দূরে ছিটকে পড়ে। গ্রেনেডের বিস্ফোরণ হলেও সে যাত্রায় সে বাঁইচা যায়। আইলে আমি একটু উঁচুতে ছিলাম। চু করে একটি গুলি এসে লাগে আমার বাম পায়ে। গুলিটি আমার হাঁটুর ওপর দিয়ে বিদ্ধ হয়। প্রথম কিছুই টের পাইনি। মনে হয়েছে সাপে কাটছে। বাম পা টানতে পারছিলাম না। কী হলো পায়ে? হাত দিতেই অনুভব করি পিনপিন করে রক্ত বেরোচ্ছে। রক্ত গেলেও জ্ঞান হারাই নাই। সহযোদ্ধারা আমাকে পেছনে টেনে পাঠিয়ে দেয় মোড়ল বাড়ি ক্যাম্পে। পরে সেখান থেকে পুনা হাসপাতালে। অপারেশন করে সেখানেই গুলি বের করা হয়।’
আমাদের কথা হয় যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ তারা মিয়ার সঙ্গে। তিনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন ২নং সেক্টরে। এছাড়াও বিচ্ছু বাহিনীতে গোয়েন্দার কাজ করতেন। পাকিস্তানি সেনাদের আর্টিলারির আঘাতে জখম হয় তাঁর স্পাইনাল কর্ডে। পরে সেখানে ইনফেকশন হওয়াতে তাঁর দু’পা প্যারালাউজড হয়ে যায়। বর্তমানে হুইল চেয়ারই তাঁর একমাত্র অবলম্বন।
আলাপচারিতার শুরুতেই ভদ্রতাবশত প্রশ্ন করেছিলাম, ‘কেমন আছেন?’
চোখেমুখে কষ্ঠ ছড়িয়ে তিনি বলেন, ‘দেখতেই তো পারতাছেন, এইডা কোনও মাইনসের জীবন! স্বাধীন হইয়া দেশটা তো একাই চলছে। আমি চলছি অন্যের সাহায্যে।’
আহত হওয়ার ঘটনা জানতে চাইলে খানিকক্ষণ নীরব থেকে তারা মিয়া বলেন:
‘আমরা ছিলাম তারাবোতে। পেছনে ভারতীয় আর্মি। মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটি দলও যোগ দিছে। শীতলক্ষ্যা-বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে লতিফ ভবানি জুট মিল। সেখানে ছিল পাকিস্তান সেনাদের শক্তিশালী ক্যাম্প। আমরা ক্যাম্পটা দখল কইরা অ্যাডভান্স হইয়া ঢাকা দখলে নিব, এমন ছিল পরিকল্পনা।
১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১। সকাল তখন ১১ টার মত। আমি ফেরিঘাটের কাছে পজিশনে। সঙ্গে মেশিনগান। ওরা গুলি ছুঁড়লে আমরাও ছুঁড়ি। ওরা ফেরি দিয়ে এই পাড়ে আসতে চাইত। কিন্তু আমরা ওগোরে ঠেকায়া দিতাম। এই ভাবেই চোখের সামনে কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হইল।
হঠাৎ বৃষ্টির মত আর্টিলারি পড়তে থাকে। আমি তখন শরীর লুকাই একটা দেওয়ালের পাশে। কিছু বুইঝা ওঠার আগেই একটা আর্টিলারি আইসা পড়ে দেওয়ালে। পরে তার কিছু অংশ ছিটকা আইসা আঘাত করে আমার পেছনে, মাজার জয়েন্টে। চিৎকার দিয়া আমি উপুড় হইয়া পড়ি। অমনি পুরা দেওয়ালডাও ধইসা পড়ে আমার শরীরের ওপর। সহযোদ্ধারা তুইলা নিয়া পাঠায়া দেয় নরসিংদী হাসপাতালে। চিকিৎসার পর ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাঁটতে পারতাম। কিন্তু স্পাইনাল কর্ডে যে ইনফেকশন হইয়া গেছিল টের পাই নাই। ধীরে ধীরে ব্যথা বাড়তে থাকল। আস্তে আস্তে পঙ্গুই হইয়া গেলাম।’
যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা বীর প্রতীক মতিউর রহমান। বাড়ি তাঁর নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার চর মল্লিকপুর গ্রামে। মতিউর আহত হন ২ নং সেক্টরের এক অপারেশনে। পাকিস্তানি সেনাদের ব্রাশফায়ারে তাঁর ডানহাতের বাহুর হাড় গুঁড়ো হয়ে যায়। কী ঘটেছিল রক্তাক্ত সে দিনটিতে? তাঁর ভাষায়:
‘চন্দ্রপুর গ্রামে ছিল আমাদের সি কোম্পানির ডিফেন্স। কমান্ডে লেফটেন্যান্ট আজিজ। সেখান থেকে দুইশ গজ উত্তরে লতিয়া মোড়ায় ছিল পাকিস্তানিদের শক্তিশালী ঘাঁটি। তারা অস্ত্র সেখানে জমা করে আগরতলার দিকে আর্টিলারি ছুঁড়ত। আমরা দেড়শ মুক্তিযোদ্ধা। অন্য পাশে ছিল ইন্ডিয়ান আর্মির একটি কোম্পানি। তিন দিন ধরে চলে রেইকি ও ব্রিফিং।
২১ নভেম্বর, ১৯৭১। রাত ১২টার পর অপারেশ শুরু হয়। ইন্ডিয়ান আর্মিরা আক্রমণ করে লতিয়া মোড়ার পূর্ব দিকে। রেললাইনের ওপর দিয়ে ক্রলিং করে চন্দ্রপুর গ্রামের পূর্বদিকে আমরা এগোই। পরিকল্পনা ছিল ওদের বাঙ্কারের পেছনে পৌঁছে আমরা ফায়ার ওপেন করব। কিন্তু তা হলো না। একশ গজের ভেতরে প্রবেশ করতেই ওরা ফায়ার ওপেন করে দেয়। বেরি লাইট নিক্ষেপ করে আমাদের অবস্থানটা জেনে যায়। ধানক্ষেতে আমরা তখন পজিশন নিই।
তুমুল গুলি চলছিল। পাশে লেফটেন্যান্ট আজিজ, উত্তরে হাবিলদার আবদুল হালিম বীর বিক্রম। শোঁ শোঁ করে গুলি আসছে। খানিক পরেই দেখি তাদের নিথর দেহ পড়ে আছে। নিজেকে সামলে নিই। ক্রলিং করে দক্ষিণ পাশের একটি বাঙ্কারের নিচে আসি। আমার হাতে একটা থাট্টি সি হ্যান্ড গ্রেনেড। অপেক্ষায় থাকি। ফায়ার বন্ধ হলেই থ্রো করব। তাই করলাম। কিন্তু সে মুহূর্তেই ব্রাশ এসে লাগে আমার ডান হাতে।
প্রথম কিছুই বুঝিনি। মনে হলো কেউ যেন রাইফেল দিয়ে হাতে বাড়ি দিয়েছে। ডান হাত কোথায়? কোনও বোধ নেই। ভাবলাম, হাত কেটে পড়ে গেছে। পরে খেয়াল করে দেখি ডানহাতের বাহুর হাড় গুঁড়ো হয়ে হাতটি পেছনে উল্টো হয়ে উঠে গেছে। প্রচণ্ড ব্যথা। সহযোদ্ধারা ইনজেকশন দিতেই আমার শরীর ঢলে পড়ে। যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলাম আমি আসামের গৌহাটি হাসপাতালে।’
যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ বশির উদ্দিন। বাড়ি সিলেটের গোয়াইন ঘাট উপজেলার ইসলামপুর গ্রামে। তিনি ছিলেন ৫নং সেক্টরের ডালডা কোম্পানির ৩০ জনের একটি প্লাটুনের কমান্ডার। ১৯৭১ সালে এক অপারেশনে পাকিস্তানি সেনাদের গুলি এসে লাগে তাঁর বাঁ পায়ের হাঁটুর উপরে। চিকিৎসার পর হাঁটতে পারলেও তিনি পা ভাঁজ করতে পারেন না। সেদিনকার কথা শুনি তাঁর জবানিতে:
‘পাকিস্তানি সেনাদের হেভি ডিভেন্স ছিল উমাইরগাঁয়ে। ২১ নভেম্বর, ১৯৭১। গৌড়নদী থেকে রাতেই অ্যাডভান্স হয়ে আমরা পজিশন নিই উমারইগাঁওয়ের উত্তর দিকে। পেছনে ইন্ডিয়ান ঘুরকা গ্রুপ। তাদের পেছনে ছিল ইপিআর, পুলিশ, আর্মিসহ আমাদের আরেকটি দল।
২২ নভেম্বর। তখন ফজরের আজান হচ্ছে। পরিকল্পনা মোতাবেক ভারতের তালাব বাজার থেকে মর্টার ছোঁড়া হয়। এর পরপরই আমরা ফায়ার ওপেন করি। সারাদিন চলে গোলাগুলি। বিকেল তখন ৪টা। হঠাৎ খেয়াল করলাম ওদের গুলি বন্ধ। বুঝে গেলাম ওরা পালিয়েছে। আমরা তখন ‘জয় বাংলা’ বলে ওদের ডিফেন্সে ঢুকে বাঙ্কারগুলো চেক করতে থাকি। আমার পাশেই এলএমজির টোআইসি রমিজ উদ্দিন। দুজন মিলে বাম সাইডের শেষ বাঙ্কারটি চেক করছিলাম। ওরা তখন বাম পাশ থেকে কাউন্টার অ্যাটাক চালায়।
আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। হঠাৎ দেখলাম রমিজ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। একটি গুলি বিদ্ধ হয়েছে তার মাথায়। শরীরটা কয়েকবার ঝাঁকি দিয়ে তার দেহখানা নিথর হয়ে গেল। আমি তাকে ধরতে যাব, অমনি আরেকটি গুলি এসে লাগে আমার বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপরে। আমি ছিটকে পড়ি। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি পিনপিনিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। আমাদের পেছনের গ্রুপটি পাল্টা অ্যাটাক করলে ওরা তখন পালিয়ে যায়। সে অপারেশনে শহীদ হয় রমিজ। আহত হই আমি, খাইরুল, নিজামসহ চারজন।’
এরকম প্রান্তিক যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ ও বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার বর্ণনাগুলোই আমাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসকে তুলে ধরে। শত বছর পরেও কেউ যখন এ ইতিহাসের কথা জানবেন, তখন যাঁরা এ স্বাধীনতা এনেছেন, সেই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কথা ভেবে গর্বে তার বুক ভরে উঠবে। এভাবেই যুদ্ধদিনের গদ্যগুলো বেঁচে থাকবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।
http://banglanews24.com/fullnews/bn/380036.html
- Biplob Rahman | ২৯ এপ্রিল ২০১৫ ১৭:৪৯582809
- সেলুলয়েডে মুক্তিযুদ্ধ | সাইফ বরকতুল্লাহ
স্বাধীনতা দিবস / শিল্প-সাহিত্য
বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম
মুক্তিযুদ্ধ—আমাদের গৌরব আমাদের অহঙ্কার। লক্ষ প্রাণের রক্তের বিনিময়ে এসেছে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়। নির্মাতারা আরেক যুদ্ধ করছেন তাদের চলচ্চিত্রে। রক্তস্নাত মুক্তিযুদ্ধকেই বন্দি করছেন সেলুলয়েডে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের দেশে এত চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে যা আমাদের গর্ব। পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে তাদের স্বাধীনতা নিয়ে সম্ভবত এত চলচ্চিত্র নির্মিত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এত বেশিসংখ্যক প্রামাণ্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য এবং পূর্ণদের্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে যে, দেশের বাইরেও তা প্রশংসা কুড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকার ভাষায়, ‘আগামী প্রজন্মের কাছে সবচেয়ে গৌরব, গর্ব আর বেদনাগাথা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরতে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পালন করে যাচ্ছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। দেশটির জন্য সত্যিই এটি আশা ও অহঙ্কারের বিষয়’। ওরা ১১জন থেকে গেরিলা পর্যন্ত যেক’টি ছবি তৈরি হয়েছে সেগুলোতে আমাদের মুক্তির সংগ্রামের ছবি ফুটে উঠেছে। বিজয়ের পর যেক’টি সিনেমা এদেশে মুক্তি পেয়েছে সেগুলোকে খাটো দেখার কোনও উপায় নেই।
১৯৬৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ছিল ৩৩টি। ১৯৭০ সালে সেটা বেড়ে হয়েছিল ৪১। যুদ্ধের আগে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ছাড়া ১৯৭১-এ আর কোনও ছবি নির্মাণ সম্ভব ছিল না। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে যুদ্ধের আগের নির্মীয়মাণ ছবিসহ ৭২ সালেই ২৯টি ছবির মুক্তি পায়। ১৯৭২, ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে মোট দশটি মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক চলচ্চিত্র তৈরি হয়। ২০০৪ সালে আবার একই বছরে তিনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়।
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন চাষী নজরুল ইসলাম। চলচ্চিত্রটির নাম ‘ওরা ১১ জন’। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন মাসুদ পারভেজ, জাগ্রত কথাচিত্রের ব্যানারে। চাষী নজরুল ইসলামের এটিই প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র যার কাহিনীকার আল মাসুদ, চিত্রনাট্যকার কাজী আজিজ, সংলাপে এটিএম শামসুজ্জামান। অভিনয় করেছিলেন খসরু, শাবানা, রাজ্জাক, নূতন, সুমিতা দেবী, রওশন জামিল, এটিএম শামসুজ্জামানসহ আরও অনেকে। ১১ই আগস্ট ১৯৭২ এ মুক্তি পায় এই চলচ্চিত্রটি।
মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র সুভাষ দত্ত পরিচালিত সিনেমা ‘অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী’ মুক্তি পায় ১৯৭২ সালের ৮ই নভেম্বর । কুসুমপুর গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন, নারী ধর্ষণ এবং প্রতিবাদে বাঙালিদের মুক্তি সংগ্রামকে কেন্দ্র করে এই চলচ্চিত্র নির্মিত। শতদল কথাচিত্রের প্রযোজনায় এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন আনোয়ার হোসেন, ববিতা, উজ্জ্বল প্রমুখ।
মুক্তিযুদ্ধের তৃতীয় ও চতুর্থ চলচ্চিত্র ‘রক্তাক্ত বাংলা’ এবং ‘বাঘা বাঙালী’ মুক্তি পায় ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে। ‘রক্তাক্ত বাংলা’ পরিচালনা করেন মমতাজ আলী এবং ‘বাঘা বাঙালী’ পরিচালনা করেন আনন্দ। ১৯৭৩ সালে মুক্তি পায় আলমগীর কবির পরিচালিত ‘ধীরে বহে মেঘনা’, আলমগীর কুমকুম পরিচালিত ‘আমার জন্মভূমি’ এবং খান আতাউর রহমান পরিচালিত ‘আবার তোরা মানুষ হ’। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তরুণ প্রজন্ম কী করছে তা নিয়ে তৈরি হয় ছবিটি।
পরিচালক আলমগীর কবিরের নির্মিত ‘ধীরে বহে মেঘনা’ চলচ্চিত্রটিতে অভিনয় করেছেন বুলবুল আহমেদ, জয়শ্রী কবির, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ। এটি আলমগীর কবিরের প্রথম চলচ্চিত্র। ১৯৭৩ সালে নির্মিত অন্যান্য ছবিগুলো হলো, আলমগীর কুমকুম পরিচালিত ‘আমার জন্মভূমি’। ১৯৭৪ সালে মুক্তি পায় চাষী নজরুল ইসলামের ‘সংগ্রাম’, নারায়ন ঘোষ মিতার ‘আলোর মিছিল’ এবং আনন্দের ‘কার হাসি কে হাসে’।
নারয়ণ ঘোষ মিতা পরিচালিত চলচ্চিত্র ‘আলোর মিছিল’ ছবিতে অভিনয় করেন রাজ্জাক-সুজাতা। পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি এটি।
এ ছবিতে পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেন ববিতা। ’৭৪-এ আরও নির্মিত ছবির মধ্যে রয়েছে, মোহাম্মদ আলী পরিচালিত ‘বাংলার ২৪ বছর’। সত্তর দশকেই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক মোট ১৩টি ছবি নির্মাণ হয়। সত্তর দশকে এতগুলো মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছবি নির্মাণ হলেও আশির দশকে নির্মাণ হয় মাত্র ৩টি ছবি। তাও আবার শুধু ১৯৮১ সালে। ছবিগুলো হলো, এজে মিন্টু পরিচালিত ‘বাধন হারা’, শহীদুল হক খান পরিচালিত ‘কলমীলতা’ এবং মতিন রহমান পরিচালিত ‘চিৎকার’। অবশ্য ’৯০-এর দশকে এসে মুক্তিযুদ্ধের ছবির সংখ্যা আবার বৃদ্ধি পেয়ে মোট ৭-এ দাঁড়ায়।
১৯৯৩ সালে লেখক শাহরিয়ার কবিরের লেখা এবং নাসির উদ্দীন ইউসুফ-এর পরিচালনায় নির্মিত ছবি ‘একাত্তরের যীশু’। ছবির প্রধান চরিত্রগুলোতে অভিনয় করেছেন পীযূষ বন্দোপাধ্যায়, হুমায়ূন ফরীদি, জহির উদ্দিন পিয়াল, আবুল খায়ের, আনওয়ার ফারুক, কামাল বায়েজীদ ও শহীদুজ্জামান সেলিম। এছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইব্রাহীম বিদুৎ, শতদল বড়ুয়া বিলু, সাইফুদ্দিন আহমেদ দুলাল, ফারুক আহমেদ, ইউসুফ খসরু, দেলোয়ার হোসেনসহ আরও অনেকেই। ১৯৯৩ সালে হারুন উর রশীদ পরিচালিত ‘মেঘের অনেক রং’ ও ‘আমরা তোমাদের ভুলব না’ নির্মিত হয়। ১৯৯৪ সালে তানভীর মোকাম্মেল পরিচালিত ‘নদীর নাম মধুমতি’।
১৯৯৫ সালে কথা সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের প্রথম নির্মিত মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র ‘আগুনের পরশমনি’। এ ছবিতে নায়ক হিসেবে মুক্তিযোদ্ধার চরিত্রে অভিনয় করেন আসাদুজ্জামান নূর। ছবির নায়িকা বিপাশা হায়াত। এ ছবিতে আবুল হায়াতই তার বাবার ভূমিকায় অভিনয় করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় একটি পরিবারের বিভিন্ন ঘটনা নিয়েই এ ছবি নির্মিত। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৯৫ সালে। এ বছরের আরও একটি চলচ্চিত্র হলো তারেক মাসুদ পরিচালিত ‘মুক্তির গান’। চলচ্চিত্রটি প্রযোজনা করেন ক্যাথরিন মাসুদ।
১৯৯৭ সালে সেলিনা হোসেনের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত ছবি ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’ মুক্তি পায়। একই বছরে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে তিনটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পায় ছবিটি। তারেক মাসুদ পরিচালিত ও ক্যাথরিন মাসুদ প্রযোজিত ১৯৯৯ সালে নির্মিত ছবি ‘মুক্তির কথা’। ১৯৯৮ সালে নির্মিত হুমায়ূন আহমেদের ‘শ্রাবণ মেঘের দিন’। ২০০২ সালে তারেক মাসুদ নির্মাণ করলেন ‘মাটির ময়না’।
২০০৪ সালে হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নির্মিত চলচ্চিত্রের মধ্যে আরেকটি বিশেষ ছবি ‘শ্যামল ছায়া’। এছাড়া একই বছর তৌকির আহমেদ নির্মাণ করেন জয়যাত্রা, হুমায়ূন আহমেদ পুনরায় নির্মাণ করলেন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র শ্যামল ছায়া। ২০০৪ সালে চাষী নজরুল ইসলামের ‘মেঘের পর মেঘ’।
২০০৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তি পায় চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত ছবি ‘ধ্রুবতারা’। এ ছবির বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করেন মৌসুমী। মৌসুমী অভিনীত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম ছবি এটি। ২০০৬ সালে মোরশেদুল ইসলাম নির্মাণ করেন ‘খেলাঘর’।
সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস ‘নিষিদ্ধ লোবান’ অবলম্বনে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও চলচ্চিত্রকার নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু ২০১১ সালে নির্মাণ করেন ‘গেরিলা’। গেরিলা ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পুরস্কার ও প্রশংসা অর্জন করেছে। এতে অভিনয় করেছেন জয়া আহসান, ফেরদৌস, শতাব্দী ওয়াদুদ প্রমুখ।
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আরও ছবি হলো, শাহজাহান চৌধুরীর ‘আত্মদান’। ছবিতে অভিনয় করেছেন নিরব ও নিপুন। যুদ্ধপরবর্তী সময়ে একজন মুক্তিযোদ্ধা ভিক্ষুকের গল্প নিয়ে খালিদ মাহমুদ মিঠু নির্মাণ করে ‘গহীনে শব্দ’। ছবিতে মুক্তিযোদ্ধার চরিত্রে অভিনয় করেছেন মাসুম আজিজ। সোহেল আরমান পরিচালিত ‘এই তো প্রেম’। ইলাজার ইসলাম পরিচালিত ‘দীপ নেভার আগে’।
এ ছবিটি জাহানারা ইমামের উপন্যাস ‘একাত্তরের দিনগুলি’ অবলম্বনে নির্মিত। মুক্তিযুদ্ধের নির্মিত চলচ্চিত্র ‘কারিগর’। ইমপ্রেস টেলিফিল্ম প্রযোজিত স্বাধীনতা দিবসকে উদ্দেশ্য করে, গত ২৩ মার্চ বলাকা সিনেওয়ার্ল্ডে মুক্তি পেয়েছে এ ছবিটি। এ ছবিতে অভিনয় করেছেন রোকেয়া প্রাচী, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, সুষমা সরকার, রাণী সরকার, হিমা মৃধা, গোলাম মোস্তফা, মাসুদ আলম বাবু, শামীম খান প্রমুখ।
আমাদের চেতনা জুড়ে ছড়িয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধ। আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে গৌরব ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে মর্যাদার সঙ্গেই চলচ্চিত্রে তুলে ধরেছেন আমাদের অভিনয় শিল্পী, নির্মাতারা। যা দিয়ে আমাদের আগামী প্রজন্ম জানতে পারবে আমাদের গৌরব সম্পর্কে।
বাংলাদেশ সময়: ০৮৩৮ ঘণ্টা, মার্চ ২৫, ২০১৫
http://banglanews24.com/fullnews/bn/380034.html
- Biplob Rahman | ২৯ এপ্রিল ২০১৫ ১৭:৫১582810
- মুক্তিযুদ্ধ ও পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের একাল-সেকাল
স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা/ শিল্প-সাহিত্য
বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে কলকাতার সম্পর্কের দিকে নজর রাখলে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার নজির হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতায় আসা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪৪ বছর পর কলকাতার সেই রিফিউজি কলোনিগুলি ঘুরে সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতির খোঁজখবর করল বাংলানিউজ।
প্রধানত পাক বাহিনীর আক্রমণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগের কারণে ছিন্নমূল পূর্ববঙ্গের মানুষেরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাসহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে সব থেকে বেশি মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন।
পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন অংশে আশ্রয় নিয়েছিল এই শরণার্থী পরিবারগুলি। ১৯৭১ সালের আগেও পঞ্চাশের দশক থেকেই কলকাতা পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল মানুষদের বড় অংশের বসবাসের জায়গা হয়ে উঠেছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৫১ সালের ভারতের জনগণনার তথ্যে। দেখা যাচ্ছে ঐ সময় কলকাতার জনসংখ্যার ২৭% মানুষ রিফিউজি।
তবে একসঙ্গে সব থেকে বেশি শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসার ঘটনা ঘটে মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকের কয়েক মাস প্রায় এক কোটি মানুষ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এবং ১৫ লক্ষ মানুষ আর ফিরে যাননি।
সরকারের তরফ থেকে প্রাথমিকভাবে এই শরণার্থীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তী সময়ে বহু বেসরকারি মালিকানাধীন জমিতেও রিফিউজি কলোনি গড়ে ওঠে। এই বেসরকারি কলোনির জমি ‘জবর দখল’ করে এই কলোনিগুলি গড়ে তোলেন এই সব ছিন্নমূল মানুষরা।
সেই সময়ে এই সব জমির মালিকদের সঙ্গে তাদের সরাসরি বিরোধিতা হয়। এই বিরোধিতা অনেক সময়ই সহিংস রূপ নিয়েছিল বলে জানা যায়।
এই সময় পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আবেদন জানান।
১৯৭১ সালে যে এক কোটির মতো শরণার্থী এসেছিলেন বলে জানা যায়, তাদের একটা বড় অংশই বসবাস শুরু করেন কলকাতা এবং তার আশেপাশের এলাকায়। জানতে পারা যায় এই সময়েই আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দিন আহমেদ এবং ব্যারিস্টার আমিনুল ইসলাম লুঙ্গিপরা অবস্থায় ঢাকা থেকে পালিয়ে ভারতে হাজির হন।
শরণার্থীরা ভারতে আসার পরেই ১৯৭১ সালের ১৭ মে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে আসেন। এবং পরিষ্কারভাবে রাজ্য সরকারকে জানান, শরণার্থী বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত রকম সাহায্য করবে।
বনগাঁ সীমান্ত পেরিয়ে বহু মানুষ শিয়ালদা স্টেশনে হাজির হয়েছিলেন বলে জানা যায়। তাদের সম্বল যা ছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা দিয়ে জীবন ধারণ করা কোনওভাবেই সম্ভব ছিল না। পূর্ব রেলের দক্ষিণ শাখার স্টেশনগুলিতে একের পর এক ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে রিফিউজি কলোনি। এর মধ্যে কসবা, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, বাঘাযতীন, গড়িয়া, নরেন্দ্রপুর, টালিগঞ্জ, আজাদগড়, বিজয়গড় ছিল অন্যতম।
অন্যদিকে কলকাতার পূর্ব অংশে বেলেঘাটা, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, মধ্যমগ্রাম এবং কেষ্টপুর খালের পাশের অঞ্চলেও গড়ে উঠেছিল রিফিউজি কলোনি। তবে সব থেকে বেশি সংখ্যক রিফিউজি কলোনি ছিল কলকাতার যাদবপুর-বাঘাযতীন-বিজয়গড়-টালিগঞ্জ অঞ্চলকে ঘিরে।
কেমন ছিল এই শরণার্থী শিবিরগুলি? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৈরি হওয়া এবং তার পর থেকে দীর্ঘকাল খালি পড়ে থাকা সেনা ছাউনিগুলিকে অনেক ক্ষেত্রেই শরণার্থী শিবির হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। বাসস্থানের জায়গা গুলি ছিল মাটির উপরে লম্বা টানেলের মত। টিন দিয়ে তৈরি। সেখানেই একত্রে বহু মানুষ বসবাস করতেন।
কলকাতার যাদবপুর এবং টালিগঞ্জের মধ্যবর্তী অংশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের একটি খালি সেনা ব্যারাক ছিল বলে জানা যায়। সেখানে বসবাস শুরু করেন উদ্বাস্তু মানুষরা। এছাড়াও সামরিক ছাউনির বাইরে তাঁবুতেও থাকতেন বহু পরিবার। একটি তাঁবুতে চারটি পরিবার থাকার কথাও জানতে পারা যায়। এমনই মানবেতর জীবন ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থী হ’য়ে আসা এসব ছিন্নমূল বিপন্ন মানুষের।
পরে এই ছাউনি সংলগ্ন বেসরকারি খালি জমিতেও তারা বসবাস শুরু করেন। যাদবপুর থেকে টালিগঞ্জের দিকের জমিগুলির মালিক ছিল লায়ালকা পরিবার। তাদের নামেই এই অঞ্চলের একাংশের বর্তমান নাম ‘লায়ালকার মাঠ’।
জমির মালিকদের সঙ্গে উদ্বাস্তু মানুষদের লড়াইয়ের ইতিবৃত্ত আজও এসব কলোনিতে গেলে শোনা যায়। জমির মালিকরা অনেক সময় তাদের ভাড়া কড়া গুণ্ডাবাহিনী পাঠাতেন কলোনিগুলির দখল নিজেদের কব্জায় রাখতে। ফলে তাদের সঙ্গে সংঘাত ছিল অনিবার্য। এসব গুণ্ডাবাহিনীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী লড়াই চলতো কলোনিবাসীর।
তবে এই ইতিহাস শুধু যে সংঘাতের এমনও নয়। শরণার্থীদের জন্য কলকাতার আদি বাসিন্দাদের সাহায্যের হাতও ছিল প্রসারিত। অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক কর্মী থেকে সাধারণ মানুষ এই শরণার্থীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।
তবে এই কলোনি বা ক্যাম্পগুলিতে জীবন মোটেও সহজ ছিল না। বেকারত্ব ছিল সব থেকে বড় সমস্যা। এইসব ক্যাম্পে মৃত্যুর হারও ছিল বেশি। তৎকালীন সরকারের তরফে ১৬ রুপি করে মৃতদেহ সৎকার করতে দেওয়া হতো বলে জানিয়েছেন এই ধরনের শিবিরে বাস করা মানুষেরা। কারণ বাস্তবিক ক্ষেত্রে এই মানুষদের সৎকার করার মত আর্থিক ক্ষমতা একেবারেই ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে মৃতদেহ জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হত বলেও জানা গেছে।
সরকারি ক্যাম্পের বাইরে ‘জবর দখল’ করে গড়ে ওঠা কলোনিগুলির অবস্থাও ছিল প্রায় একই। জীবন বা খুব ছোট বয়সে এসব কলোনিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন এমন মানুষেরা জানিয়েছেন, তাদের জীবন তখন ছিল এক নির্মম লড়াইয়ের নাম—একটি বাস্তুচ্যুত, ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর শূন্য থেকে শুরু করবার লড়াই।
কেমন ছিল সেই লড়াই? এক প্রবীণ জানালেন, খাবার জোটেনি এমন দিন কম ছিল না। অনেকদিনই কাঁচা আলু আর কাঁচা লাউ খেয়ে পেট ভরাতে হয়েছে।
জানা যায় দক্ষিণ কলকাতার বাঘাযতীন মোড় থেকে সোজা তাকালে রেল লাইন দেখা যেত ১৯৭০ সাল নাগাদ। এই অঞ্চলগুলিতে প্রচুর শেয়াল এবং সাপের উপদ্রব ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে ছিল শুধু রেলপথ। যাদবপুর, বাঘাযতীন, নাকতলা, টালিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকার কলোনিগুলিতে পানীয় জল, চিকিৎসার অভাব ছিল প্রচণ্ড। কলকাতা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে অন্য কয়েকটি জেলাতেও গড়ে ওঠা কলোনিগুলির চিত্র ছিল একই রকমের।
কিন্তু এখন সময়ের সঙ্গে বদলে গেছে এই অঞ্চলগুলির চেহারা, চরিত্র। কলোনির মাটির টালি, টিনের ছাউনি কিংবা খড়ের চালের দেখা মেলে না আর কলোনিগুলিতে। কলোনির সমস্ত বাসিন্দাদের সরকারের তরফে জমির মালিকানা হস্তান্তর বা পাট্টা প্রদান করা হয়েছে। বদল হয়েছে এই কলোনিগুলির আর্থ-সামাজিক অবস্থা। অর্থনৈতিক অবস্থার বদল ঘটাতে সরকারের তরফে বিভিন্ন বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল কলোনি গড়ে ওঠার প্রথম থেকেই।
যাদবপুর, বাঘাযতীন, টালিগঞ্জ এখন পুরোমাত্রার শহর। বিরাট চওড়া রাস্তার দুইধারে অট্টালিকার সারি। দ্রুতগতির যানবাহন, বাজারঘাট সরকারি, বেসরকারি হাসপাতাল,বাজার, রেস্তোরাঁ, প্রেক্ষাগৃহসহ আধুনিক জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই বিদ্যমান এখানে।
প্রায় প্রতিটি কলোনিতে তৈরি হয়েছে এক বা একাধিক বিদ্যালয় এবং কলেজ। তৈরি হয়েছে কমিউনিটি হল থেকে শুরু করে খেলার মাঠ, পাঠাগারসহ আধুনিক নাগরিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই।
শহরের অন্য অংশের সঙ্গে আজ আর কোনও পার্থক্য নেই কলোনিগুলির। অনেক জায়গাতেই কলোনির জমিতে তৈরি হয়েছে আবাসন। আর এই আবাসনগুলিতে কলকাতা শহরের ‘কসমোপলিটান’ চরিত্র বজায় রেখে বসবাস করছেন বিভিন্ন রাজ্যর মানুষ। তৈরি হয়েছে শপিংমল থেকে মালটিপ্লেক্স।
এই কলোনিতে জন্ম নেওয়া নতুন প্রজন্ম মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে বাকি কলকাতার সঙ্গে। বাংলাদেশ নিয়ে তাদের আবেগ আছে, আছে উৎসাহ। আর প্রবীণরা স্মৃতি হাতড়ে বেড়ান কেবল—চিরদিনের জন্য পেছনে ফেলে আসা জন্মভিটে, প্রিয় নদীতীর, শেকড় স্মৃতির ভেতর থেকে আজও প্রাণে উঁকি দ্যায়। ঢের সময় পেরিয়ে এইভাবেই আজ কলকাতার বাকি অংশের সাথে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে গেছে একসময়ের ছিন্নমূল পরিবারগুলি।
http://banglanews24.com/fullnews/bn/380005.html
- Biplob Rahman | ২৯ এপ্রিল ২০১৫ ১৭:৫৭582811
- মূল নকশা পাশ কাটিয়ে নির্মিত হয়েছিল জাতীয় স্মৃতিসৌধ
স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা / শিল্প-সাহিত্য
বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম
মূল নকশার কথা মাথায় রাখলে জাতীয় স্মৃতিসৌধকে অসম্পূর্ণই বলতে হবে। স্বাধীনতার অনবদ্য স্মারক স্মৃতিসৌধের বর্তমান যে চিত্র তার অনেক কিছুই ছিল না মূল নকশায়। আবার নকশায় যা ছিল তার অনেক কিছুই নেই বাস্তবে—এমনই দাবি করেছেন জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি প্রয়াত সৈয়দ মাইনুল হোসেনের পরিবার।
মূল নকশার সাথে স্মৃতিস্তম্ভের কেবল অসম্পূর্ণতাই নয়, জীবদ্দশায় যথাযথ সম্মান ও মূল্যায়ন পাননি গুণী এই স্থপতি। এই আক্ষেপ মাইনুল হোসেনের পরিবারকে এখনও পোড়ায়। স্মৃতিসৌধের উদ্বোধনী দিনেও আমন্ত্রণ জানানো হয়নি একুশে পদকপ্রাপ্ত এই প্রতিভাবান স্থপতিকে।
বাংলানিউজের সঙ্গে একান্তে আলাপচারিতায় এমনটিই বললেন প্রয়াত মাইনুল হোসেনের স্ত্রী আসমা আকতার।
মুক্তিযুদ্ধে শহীদ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সাভারে নির্মাণ পরিকল্পনা করা হয় জাতীয় স্মৃতিসৌধের। ১৯৭৮ সালে নকশা আহ্বান করা হলে জমা পড়ে ৫৭টি নকশা।
এর মধ্যে বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামে বিজয়ের স্মারক জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্মৃতির মিনারের জন্য নির্বাচিত হয়—সে সময়ে ২৬ বছরের তরুণ স্থপতি মাইনুল হোসেনের নকশাটি।
তার নকশা অনুযায়ী বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধিকার আন্দোলন পর্যন্ত ছিল সাতের প্রভাব। যার প্রমাণ স্মৃতিসৌধের বেদীমূল থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে সাতটি ত্রিকোণ কলাম। সবচেয়ে বড়টি ১৫০ ফুট উঁচু। এই সাতটি কলামে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সাতটি পর্যায়কে তুলে ধরা হয়েছে। আকার আকৃতিতে ভিন্নতা থাকায় একেক দিক থেকে স্মৃতিসৌধকে দেখায় একেক রকম।
দীর্ঘ ২২ বছরের কর্মজীবনে সৈয়দ মাইনুল হোসেন ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ভবন, চট্টগ্রাম ইপিজেড কার্যালয়, জাতীয় যাদুঘর ও উত্তরা মডেল টাউনের মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নকশার কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন।
১৯৫২ সালের ১৭ মার্চ ঢাকায় জন্ম নেওয়া সৈয়দ মাইনুল হোসেনের জীবনাবসান ঘটে ২০১৪ সালের ১০ নভেম্বর। দেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নকশা তৈরির স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৮৮ সালে একুশে পদকে ভূষিত হন এই স্থপতি। তবে বঞ্চনার যাতনাও কম সইতে হয়নি তাকে। যেমনটি বলছিলেন সৈয়দ মাইনুল হোসেনের ছোট মেয়ে সৈয়দা তানজিনা হোসেন।
বাংলানিউজকে তিনি তার খেদ ও বেদনার কথা বলছিলেন এভাবে, ‘জীবদ্দশায় বাবাকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। বাবা এখন নেই। এখন এসব বলেই বা কী লাভ! ২০০৫ সাল পর্যন্ত স্মৃতিসৌধের নামফলকে বাবার নামের বানান ভুল ছিল। বাবার নাম সৈয়দ মাইনুল হোসেন। কিন্তু সবাই বলে ‘মইনুল’ হোসেন। তাঁর জন্ম তারিখ ১৭ মার্চ, কিন্তু অনেকে লেখেন ৫ মে। তাঁর জন্মস্থান ঢাকায় কিন্তু লেখা হয় মুন্সিগঞ্জে।’
প্রয়াত মাইনুল হোসেনের স্ত্রী আসমা আকতার বলেন, ‘আমার কাছে মনে হয় জাতীয় স্মৃতিসৌধের নকশা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নকশা। তবে আমাদের কাছে এই স্মৃতিসৌধ যেমন গর্বের তেমনি বেদনারও। এখনও স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে সেই দিনগুলো। অধীর আগ্রহ আর গভীর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সবাই অপেক্ষা করছিলাম স্মৃতিসৌধের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটির জন্য। তবে দুঃখজনক হলো, সে দিন মাইনুলকে আমন্ত্রণটুকু পর্যন্ত জানানো হয়নি।
মনে পড়ে আমাকে নিয়ে মাইনুল তার প্রাণের নকশার বাস্তবায়ন দেখতে গিয়েছিল সেদিন, যেদিন জনসাধারণের জন্যে খুলে দেয়া হয়েছিল এই স্মৃতিসৌধ।
মাইনুলের মাঝে ছিল সাতের প্রভাব। সেই ভাবনা থেকেই এই নকশা। আমাদের কাছে সেই নকশার ব্লুপ্রিন্ট রয়েছে। তাতে বেদীর সামনে অগ্নিশিখা থাকার কথা ছিল। অথচ তা নেই। স্মৃতিস্তম্ভের যে উচ্চতা নকশায় ছিল তাও অনুসরণ করা হয়নি। এছাড়াও স্মৃতিস্তম্ভ সাদা মার্বেল পাথরে মুড়ে দেবার কথা নকশায় থাকলেও সেটা করা হয়নি। এসব দিক বিবেচনা করা হলে বলাই যায়, মাইনুলের নকশার সাথে স্মৃতিসৌধটির বেশ কিছু অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতা রয়েছে।’
এব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে স্মৃতিসৌধের দায়িত্বপ্রাপ্ত গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী সতীনাথ বসাক বাংলানিউজকে জানান, প্রায় তিন দশক আগে স্মৃতিসৌধের কাজ হয়েছে। সেই সময়ে যারা কাজ করেছেন তারা নকশা ধরেই কাজ করেছেন।
তবে মূল নকশার তুলনায় বর্তমান স্মৃতিসৌধটি যে ‘অসম্পূর্ণ ও অসঙ্গতিপূর্ণ’ সে প্রসঙ্গটি কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে তিনি বলেন, ‘মূল নকশার সাথে নির্মিত সৌধের তফাত থাকার বিষয়ে আমাদের বিভাগের কিছু জানা নেই। স্মৃতিসৌধের বর্তমান আদলে যা রয়েছে তা-ই আমরা রক্ষণাবেক্ষণ করছি। আপাতত স্মৃতিসৌধের কোথায় পরিবর্ধন বা নতুন কিছু সংযোজনের বিষয়ে কোনও পরিকল্পনা নেই।’
তিনি আরও বলেন, ‘এখানে ১০টি প্রতীকী গণকবর রয়েছে। কোনও বীরশ্রেষ্ঠ বা মুক্তিযোদ্ধার কবর অন্য স্থান থেকে এখানে স্থানান্তরেরও কোনও পরিকল্পনা আপাতত নেই।’
http://banglanews24.com/fullnews/bn/380000.html
- Biplob Rahman | ২৯ এপ্রিল ২০১৫ ১৭:৫৯582812
- চরমপত্র ৭১ : ফিরে দেখা
স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা / শিল্প-সাহিত্য
বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম
‘মেজিক কারবার। ঢাকায় অখন মেজিক কারবার চলতাছে। চাইরো মুড়ার থনে গাবুর বাড়ি আর কেচ্কা মাইর খাইয়া ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়া সোলজারগুলা তেজগাঁ-কুর্মিটোলায় আইস্যা—আ-আ-আ দম ফালাইতাছে। আর সমানে হিসাবপত্র তৈয়ার হইতাছে....’
এরকম বহু শ্লেষ, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক মন্তব্যে ভরপুর ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত ‘চরমপত্র’ অনুষ্ঠানটি। সে সময় স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান এটি। অনবদ্য এ অনুষ্ঠানটির প্রতিটি অধ্যায়ের রচয়িতা ও কথক ছিলেন কথাযোদ্ধা এম আর আখতার মুকুল (১৯২৯-২০০৪)।
হালকা ভাঙা-ভাঙা কণ্ঠের অসাধারণ শব্দচয়ন ও অনন্য বাচনভঙ্গিতে এই কথিকা মুক্তিকামী বাঙালিকে কেবল রোমাঞ্চিতই করেনি, ৫৬ হাজার বর্গমাইলের যুদ্ধাক্রান্ত দেশটির মানুষের মধ্যে বিনোদনের একমাত্র খোরাকও হয়ে উঠেছিল। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বর্বর শত্রুকে নিয়ে এমন শ্লেষ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নজিরবিহীনই বটে!
অন্যদিকে চরমপত্রের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষ রাজাকার-আলবদর ও পাকিস্তানপন্থিদের কাছে ছিল দগদগে ঘায়ে নুনের ছিটার মত। নিছক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপই কি ছিল চরমপত্রে? পাকিস্তানি সামরিক জান্তার পৈশাচিক বর্বরতার বিরুদ্ধে এটি হয়ে উঠেছিল মোক্ষম এক রাজনৈতিক হাতিয়ার।
১৯৭১ সালের মে থেকে ডিসেম্বর। এই আট মাস বাংলাদেশের যুদ্ধরত মুক্তিকামী মানুষ স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রের ‘চরমপত্র’ শুনে আলোড়িত, আন্দোলিত উজ্জীবিত হতো। ২৫ মে স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্র চালু হওয়ার দিন থেকে ‘চরমপত্র’ পাঠ শুরু হয়। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয়ের দিনে ‘চরমপত্র’র শেষ পর্ব সম্প্রচারিত হয়।
‘চরমপত্র’ অনুষ্ঠানের নামকরণ করেছিলেন স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রের একনিষ্ঠ কর্মী আশফাকুর রহমান খান।
মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেওয়ার পাশাপাশি এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশের শত্রুকবলিত এলাকার জনগোষ্ঠী ও ভারতে অবস্থানরত বাঙালি শরণার্থীদের মনোবল চাঙ্গা রাখতে রেখেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।
মানসম্মত রেকর্ডিং স্টুডিওর অভাবে টেপ রেকর্ডারে ‘চরমপত্র’ রেকর্ড করা হতো। ৮-১০ মিনিটের এই টেপ নিয়মিতভাবে স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রের ট্রান্সমিটার থেকে সম্প্রচার করা হতো। ‘চরমপত্র’র প্রতি পর্বের রচনা ও ব্রডকাস্টিংয়ের জন্য এম আর আখতার মুকুল পারিশ্রমিক হিসেবে পেতেন মাত্র ৭ টাকা ২৫ পয়সা।
এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিদিন গল্পের ছলে দুরূহ রাজনীতি ও রণনীতি ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রণাঙ্গনের সর্বশেষ খবরাখবর সহজ, সাবলীল ও ব্রাত্যজনের ভাষায় অত্যন্ত নিষ্ঠা ও মুন্সিয়ানায় উপস্থাপন করতেন এম আর আখতার মুকুল।
যখন তিনি অনুধাবন করলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের ৯৫ শতাংশই গ্রাম-বাংলার সন্তান। তখন তিনি ‘চরমপত্র’ পঠনে চমক আনলেন। শহুরে প্রমিত ভাষা ত্যাগ করে ঢাকাইয়া ভাষার ব্যবহার করা শুরু করলেন। একইসঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ঐক্য আনতে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারও শুরু করেন তিনি।
শুধু তাই নয়, নিজের সৃষ্টি নতুন নতুন শব্দ মাঝে মধ্যেই জুড়ে দিতেন চরমপত্রে। ১৯৭১ সালের ২৯ মে ‘চরমপত্র’র পঞ্চম পর্বের অংশবিশেষ ছিল এরকম—‘জেনারেল ইয়াহিয়া খান এখন ঝিম ধরেছেন। এদিকে আগায় খান, পাছায় খান, খান আব্দুল কাইউম খান আবার খুলেছেন, মাফ করবেন ‘মুখ’ খুলেছেন। আয় মেরে জান, পেয়ারে দামান, খান কাইউম খান তোমার ক্যারদানী আর কত দেখাইবা? জেনারেল ইয়াহিয়া, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। হা-ডু-ডু খেলা দেখেছো কখনও? সেই হা-ডু-ডু খেলায় কেচ্কি বলে একটা প্যাঁচ আছে। আর তুমি বুঝি হেই কেচ্কির খবর পাইয়া আউ-কাউ কইরা বেড়াই আছো।’
আর ১৬ ডিসেম্বর শেষ পর্বটি ছিল—‘আইজ থাইক্যা বঙ্গাল মুলুকে মোছুয়াগো রাজত্ব শ্যাস। আট হাজার আটশ চুরাশি দিন আগে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট তারিখে মুছলমান মুছলমান ভাই ভাই কইয়া, করাচি, লাহোর, পিন্ডির মছুয়া মহারাজারা বঙ্গাল মুলুকে যে রাজত্ব কায়েম করছিল, আইজ তার খতম তারাবি হইয়া গেল। বাঙালি পোলাপাইন বিচ্ছুরা দুইশ পঁয়ষট্টি দিন ধইরা বঙ্গাল মুলুকের ক্যাদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট পাইটিং ফোর্সগো পাইয়া, আরে বাড়িরে বাড়ি। টিক্কা মালেক্যা গেল তল, পিঁয়াজী বলে কত জল?
প্রিয় পাঠক স্বাধীনতা খেতাবপ্রাপ্ত বাকযোদ্ধা প্রয়াত এম আর আখতার মুকুলের অনন্য কণ্ঠে শেষ পর্বের ‘চরমপত্র’ শুনেই দেখুন একবার। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিশেষ আয়োজনের অংশ হিসেবে বাংলানিউজ তা ইউটিউব থেকে পাঠকদের জন্য তুলে ধরছে।
http://banglanews24.com/fullnews/bn/380003.html
- Biplob Rahman | ২৯ এপ্রিল ২০১৫ ১৮:০১582813
- ‘আমার সোনার বাংলা’ যেভাবে জাতীয় সংগীত হলো | মুহম্মদ সবুর
স্বাধীনতা দিবস / শিল্প-সাহিত্য
বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম
এই সঞ্চয়িতা-সঙ্গে থাকলে আমি আর কিছুই চাই না। নাটক নয়, উপন্যাস নয়, কবিগুরুর গান ও কবিতাই আমার বেশি প্রিয়। সব মিলিয়ে এগারো বছর কাটিয়েছি জেলে। আমার সব সময়ের সঙ্গী ছিল এই সঞ্চয়িতা। কবিতার পর কবিতা পড়তাম আর মুখস্থ করতাম। এখনও ভুলে যাইনি। এই প্রথম মিয়ানওয়ালি জেলের ন’মাস সঞ্চয়িতা সঙ্গে ছিল না। বড় কষ্ট পেয়েছি। আমার একটি প্রিয় গানকেই “আমার সোনার বাংলা” আমি স্বাধীন দেশের জাতীয় সঙ্গীত করেছি। আর হ্যাঁ, আমার আর একটি প্রিয় গান ডি এল রায়ের “ধন ধান্য পুষ্প ভরা”। দুটি গানই আমি কাজের ফাঁকে গুনগুন করে গেয়ে থাকি।’—নয় মাসের পাকিস্তানি কারাগারে বন্দীদশা শেষে নিজ মাতৃভূমিতে ফিরে আসার বারোদিন পর এই ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উচ্চারণ। যার আন্দোলন-সংগ্রাম এবং জীবন সাধনায় রবীন্দ্রনাথ অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে। তাই শান্তিনিকেতনের এক সময়ের শিক্ষার্থী ও সিলেটে জন্ম সাহিত্যিক-সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরীকে বলেছিলেন, ‘রবীন্দ্রনাথকে আমি ভালোবাসি তার মানবপ্রেম ও দেশপ্রেমের জন্য। বড় হয়ে পড়লাম, “হে মোর দুর্ভাগা দেশ”—আমাদের দেশের দুর্ভাগা মানুষের প্রতি এত দরদ আর কার আছে।’ স্বাধীন দেশে এসেছিলেন সে সময়ের ‘আনন্দবাজার’ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী। ৩২ নম্বরের বাড়িতে সেদিন রাজনীতি নয়, কথা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা যে তিনি গড়ে তুলতে চান, সে চাওয়া ও স্বপ্নের কথাও বলেছিলেন।
পাকিস্তানের উপনিবেশক শাসকরা বাঙালির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকারকে পর্যুদুস্ত করার প্রক্রিয়া চালু করে সেই সাতচল্লিশে দেশভাগের পর। নির্যাতন, নিপীড়ন, জেল, জুলুম, নিষেধাজ্ঞা, বহিষ্কারের মত কঠিন কঠোর পদক্ষেপ যেমন নেয়া হয়েছিল সেই আটচল্লিশ থেকেই, তেমনি রবীন্দ্রনাথকে নিষেধ, বর্জন ও নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে। শেখ মুজিবের কাছে রবীন্দ্রনাথ সাহস হয়ে দেখা দিতেন। আর সেই সাহসে ভর করে তিনি তারুণ্য থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত বারবার জেল খেটেছেন। ফাঁসির আসামীর সেলে কাটিয়েছেন। বিপর্যস্ত হয়ে পড়েননি। জানা ছিল তার, ‘ওদের বাধন যতই শক্ত হবে, তোদের বাঁধন ততই টুটবে।’ কিন্তু শেখ মুজিব সব বাধা বিঘ্ন মাড়িয়েছেন। তাই কণ্ঠে ধ্বনিত হতো, ‘নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার।’
সেই আটচল্লিশেই যখন জেলে গেলেন মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষার জন্য, তখনও রবীন্দ্রনাথ যুগিয়েছেন প্রেরণা। মায়ের ভাষার বিলুপ্তি মানেই জাতি হিসেবে বাঙালির বিলুপ্তি—এমনটা মেনে নিতে পারেননি শেখ মুজিব। তাই ‘বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি বারে বারে হেলিস না’ গেয়ে প্রতি পদক্ষেপেই বাঙালির স্বার্থরক্ষার আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়েছেন, ‘জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য’ বানিয়ে। বাঙালির স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের অগ্রদূত হয়ে জেগেছিলেন জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর সেই সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ছিলেন যিনি পঞ্চাশ, ষাট ও মুক্তিযুদ্ধে—বাঙালির সমগ্র সংগ্রামেরই অংশবিশেষ। যে সম্মিলিত সংগ্রাম শুরু বায়ান্ন সালে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন বাঙালির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে প্রশস্ত করে নিজের দিকে ফিরে তাকানোর পথ দেখায়। বাঙালি নিজের স্বাজাত্যবোধের প্রতি ক্রমশ আগ্রহী হয়ে ওঠে। মা, মাটি, মাতৃভূমির সঙ্গে মাতৃভাষাকে অঙ্গাঙ্গি করে স্বাধিকারকামী হতে থাকে। এই স্বাজাত্যবোধের রাজনৈতিক অগ্রনায়ক হিসেবে অবস্থান পেলেন শেখ মুজিব। আর সাংস্কৃতিক অগ্রদূত হিসেবে আবির্ভূত হন রবীন্দ্রনাথ। হয়ে ওঠেন তিনি বাঙালির চেতনা স্বরূপ। যে চেতনা আপন সাহিত্য-সংস্কৃতির লালনে পুষ্ট হবার পরে বাঙালিকে বিশ্বের দিকে হাত বাড়িয়ে সকল গ্রহণীয় ঐশ্বর্য অধিগত করতে বলে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালির জাতিসত্ত্বা সন্ধানের সহযাত্রী হয়ে ওঠেন। তার গান, কবিতা, নাটকসহ সাহিত্য মুক্তির সংগ্রামে ও যুদ্ধে বাঙালিকে এক অসমতম সংগ্রামে জয়ী হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।
বঙ্গবন্ধুর প্রতি পাকিস্তানের শাসকদের যে ঘাতক মনোভাব এবং প্রতিপক্ষে রূপান্তর করা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথও ছিলেন পাকিস্তানী জান্তাদের প্রতিপক্ষ। তাদের সমর্থনে বাঙালি বংশোদ্ভূত পাকিস্তানী মানসিকতার শিক্ষিতজনরা বঙ্গবন্ধু এবং রবীন্দ্রনাথকে প্রতিপক্ষে পরিণত করেছিল বিশ শতকের পঞ্চাশ-ষাট দশকে। তেমনি স্বাধীনতাত্তোর বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর আবারও বিতর্কিত করা হয়—যেমন বঙ্গবন্ধুকে, তেমনি রবীন্দ্রনাথকেও। আজও যা নিঃশেষ হয়ে যায়নি।
পাকিস্তান যুগে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া যেমন অপরাধ ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশে পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে। কোনও কিছুই রবীন্দ্রনাথকে শরবিদ্ধ করতে পারেনি। ১৯৫৩ সালে ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ ভাষা আন্দোলনের শহীদ স্মরণে ২১ ফেব্রুয়ারি এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তাতে আবদুল লতিফের সুর দেওয়া ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো’ ছাড়াও গাওয়া হয়েছিল ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’। এসব গান গাওয়ার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ উদ্যোক্তা ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছিল। তবে প্রকাশ্য সভায় সে সময়ে দুঃসাহসী কাজ করেছিল ডাকসু। ১৯৫৩-৫৪ সালের ডাকসুর অভিষেক অনুষ্ঠানে গাওয়া হয় ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটি। আর ছাত্রসমাজ হয়ে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই প্রসারিত হতে থাকেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে।
১৯৫৬ সালে ঢাকায় পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন বসেছিল। পাকিস্তানের পশ্চিমাংশ থেকে আসা সংসদ সদস্যদের সম্মানে কার্জন হলে আয়োজন করা হয়েছিল অনুষ্ঠানের। উদ্যোক্তা ছিলেন গণপরিষদ সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান। অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বাঙালি সংস্কৃতিকেই তুলে ধরেছিলেন। তাতে রবীন্দ্রনাথ, ডি এল রায়, নজরুল, লোকগানও ছিল। ডি এল রায়ের ‘ধন ধান্য পুষ্প ভরা’ বঙ্গবন্ধুর প্রিয় গান বলেই গাওয়া হয়েছিল। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞ সনজীদা খাতুনও ছিলেন আমন্ত্রিত শিল্পী। তিনি মঞ্চে আসার আগে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে তাকে বলা হলো ‘আমার সোনার বাংলা’ গাইবার জন্য। কারণ তিনি চাইছেন পাকিস্তানীদের কাছে ‘সোনার বাংলা’র প্রীতি ও ভালোবাসার জানান দিতে। কিন্তু সনজীদা খাতুনের গানটি পুরো মুখস্থ ছিল না। সনজীদা খাতুনের ভাষ্যে, ‘বেকায়দা হলো, কারণ অত লম্বা পাঁচ স্তবকের গানটি যে আমার মুখস্থ নেই। গীতবিতান-এর খোঁজ পড়ল। বই হাতে পেয়ে কোনওমতে অত বড় গানটি গেয়েছিলাম আমি। গানটি বাঙালিকে কতখানি আবেগ তাড়িত করে, সেইটি বোঝাবার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিদেরকে গানটি শোনাতে চেয়েছিলেন শেখ মুজিব। তখনো “বঙ্গবন্ধু” নামটি দেয়া হয়নি তাকে।’
এরপর থেকে সনজীদা খাতুনসহ অন্য শিল্পীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ‘আমার সোনার বাংলা’ গাইতে থাকেন। আর ১৯৬১ সাল থেকে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরীর অন্যতম গান হয়ে ওঠে আমার সোনার বাংলা। এ গানকে যেন বঙ্গবন্ধু আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে দিলেন।
১৯৬৮ সালের ১৯ জুনের ঘটনা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা আনুষ্ঠানিকভাবে ওঠানো হলো ক্যান্টনমেন্টে স্থাপিত বিশেষ আদালতে। সব আসামীকে (মোট ৩৫ জন) একত্রিত করা হলো এই প্রথম। আর তাদেরও জানানো হলো কারা এই মামলার আসামী। ওই দিন সকালে লোহার জাল ঘেরা ভ্যানে ওঠানোর পর পরস্পরকে দেখে আবেগ, উচ্ছ্বাস, চিৎকার, হাসিকান্নায় ভ্যান সরগরম হয়ে উঠেছিল। ছাড়ার অল্প আগে বঙ্গবন্ধুকে ওঠানো হলো ভ্যানে। বসেছিলেন ভ্যানের পেছনের দরজার কাছে। সশস্ত্র প্রহরাযুক্ত ভ্যানটি ট্রাইব্যুনালের পথে যাত্রা করে। মামলার আসামী পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধা নৌকমান্ডার আবদুর রউফ সে মুহূর্তের বর্ণনা করেছেন, ‘ভ্যান চলতে শুরু করার সাথে সাথেই আমাদের কণ্ঠে একটি গানের কলি গুনগুনিয়ে উঠল। দেখতে দেখতে সমস্ত ভ্যানের আরোহীরাই তাতে কণ্ঠ মিলালো। শুধু বাসের ভেতর নয়, পথের দু’পাশেও ধ্বনিত হলো, ‘ধন্য ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা’। সশস্ত্র সেন্ট্রি ভয় পেয়ে আমাদের থামতে বলল। ভ্যানে গান গাওয়া নিষেধ আছে শুনে আমরা গান থামিয়ে দিলাম। গান থেমে গেছে দেখে বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, “গান থামিয়েছিস কেন?’ আমরা বললাম যে, সেন্ট্রি গানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। বঙ্গবন্ধু এবার উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, ‘আমি শেখ মুজিব নির্দেশ দিচ্ছি, তোরা গান গা...”। এরপর আমরা গাইতে শুরু করলাম। পুলিশ এবার আর কিছু বলল না। “ধন ধান্য পুষ্প ভরা” গান গাইতে গাইতে আমরা ট্রাইব্যুনালে হাজির হলাম।’ এই মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়ে বঙ্গবন্ধু জেল থেকে বেরিয়ে এলেন। কারাফটকের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেচিলেন, ‘এই দেশেতে জন্ম আমার যেন এই দেশে মরি’।
তারও আগে সেই পঞ্চাশ দশকে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাভাষায় বক্তৃতা প্রদান, রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে সোচ্চার ছিলেন বঙ্গবন্ধু। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বরাবর বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানতে থাকে। আরবি ও রোমান হরফে বাংলা লেখা শুধু নয়, বাংলা ভাষায় উর্দু, আরবি, ফারসি শব্দের যথেচ্ছাচার ব্যবহার চালানোর অপচেষ্টা চলে। কিন্তু বাঙালির তাতে নিশ্চুপ থাকার নয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পঞ্চাশের দশকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী হবার পর প্রথমেই ঢাকায় গড়ে তুললেন চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা। বাঙালির জীবন ধারায় নতুন সংযোজন ঘটল। পূর্ববঙ্গেও চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হলো। বাঙালি নিজস্ব সংস্কৃতিকে তুলে ধরে চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। এমনকী ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় উর্দু ছবির অত্যাধিক প্রদর্শনের বিরুদ্ধে এবং বাংলা ছবির করুণ অবস্থায় ক্ষোভ প্রকাশও করেছিলেন।
১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনে আসে বাধা। শেখ মুজিব এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। পাকিস্তান সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের মাধ্যমে বাঙালির সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এক বিশাল পরিবর্তন আসে। রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম অবলম্বন। বাঙালির নিজের সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ, মমত্ব এবং ঐতিহ্য ধারণের বোধ জাগ্রত হতে থাকে। গড়ে ওঠে বাঙালির সংস্কৃতিচর্চার পাদপীঠ ‘ছায়ানট’। নববর্ষসহ ঋতুভিত্তিক উৎসব পালনের মাধ্যমে বাঙালি জাতিসত্ত্বার বিকাশে শেখ মুজিবুরের রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলন একাত্ম হয়ে উঠতে থাকে। বঙ্গবন্ধু তার পাশে পেয়েছিলেন কবি সুফিয়া কামালকে।
১৯৬৭ সালের ২৩ জুন পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী ঢাকার নওয়াব বংশোদ্ভূত খাজা শাহাবুদ্দিন বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার নিষিদ্ধ করে ঘোষণা দিল ‘রবীন্দ্র সংগীত আমাদের সংস্কৃতি নয়।’ এর সমর্থনে এগিয়ে এলেন চল্লিশজন বাঙালি বুদ্ধিজীবী নামধারী। যাদের মধ্যে শিক্ষক, কবি, সাংবাদিক, আইনজীবী, গায়কও রয়েছেন। বাইশে শ্রাবণ উপলক্ষে তিনদিন ধরে সকল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের যৌথ অনুষ্ঠান আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। গভর্নর মোনেম খাঁর পুত্র অনুষ্ঠান পণ্ড করার অপচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়। বঙ্গবন্ধু বাঙালির সংস্কৃতি রক্ষায় এগিয়ে আসেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে এগিয়ে নেবার প্রেরণা যোগান। রবীন্দ্র সংগীতকে মর্যাদা দান ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তার প্রসার ঘটানোর জন্য সভা-সমাবেশে রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন চালু করান। যার মধ্যে আমার সোনার বাংলা ছিল প্রধান। সঙ্গীতজ্ঞ ওয়াহিদুল হক, ছিলেন যিনি এই আন্দোলনের মুখ্য সংগঠকের অন্যতম, তার উপলব্ধি ‘সাতষট্টির আন্দোলনের সব চাইতে স্থায়ী ফসল “আমার সোনার বাংলা” গানটির যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠা।’
রবীন্দ্র বিরোধিতা পাকিস্তানি আমলেই এ দেশে রবীন্দ্রনাথকে আরো বেশি শক্তিশালী করেছে। বাঙালির জীবনে ও চেতনায় কবি আরও বেশি অবিভাজ্য হয়ে উঠেছিলেন। বাঙালির প্রেরণা, গরিমা, ঐতিহ্য, বীরত্ব, ভালোবাসা, গণমানসিকতা, সুস্থতা, পরিচ্ছন্নতা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতীক হয়ে ওঠেন ক্রমান্বয়ে। প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ আচার অনুষ্ঠান কিংবা জাতীয় সংকটে সবখানেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। হয়ে ওঠেন তিনি মুক্তির আশ্রয়। তার গান ছড়িয়ে পড়ে জনারণ্যে। মানব মুক্তির হাতিয়ার হলো রবীন্দ্রনাথের গান, রাজনৈতিক সম্মুখ সমরে। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় কেতনে আঁকা হলো রবীন্দ্র আলেখ্য। একাত্তরে পাক হানাদারদের বর্বরতার বিরুদ্ধে বাঙালির রক্তকে ফেনিয়ে তুলতে এবং স্বাধীনতার যুদ্ধে মৃত্যুর প্রতিরোধ ও জীবনের সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের গান ছিল পাথেয় ও প্রেরণা। মুক্তিবাহিনীর প্রতিটি প্লাটুন, সেকশন, লুঙ্গি পরে গেঞ্জি গায়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে যে গান গেয়েছে, সেই ‘আমার সোনার বাংলা’ গ্রহণ করতে, গৌরবদান করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দেরি হয়নি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙালির প্রধান সৈনিক, আদর্শের ধ্রুব। বাঙালি বারবার তার সৃষ্টির কাছে আশ্রয় খুঁজেছে অশেষ আকুলতায়। পেয়েছেও তাকে জীবনের নানা সংকটে, দুঃসময়ে। বাঙালির আনন্দ ও বেদনা, সংগ্রাম ও শান্তিতে রবীন্দ্রনাথ আজো তাই বাঙালির চিরসঙ্গী।
সত্তর সালের গোড়ায় বঙ্গবন্ধু জাহিদুর রহিমকে দায়িত্ব দেন ‘আমার সোনার বাংলা’ গানের রেকর্ড প্রকাশের জন্য। কলিম শরাফী তখন ই এম আই গ্রামোফোন কোম্পানির ঢাকার কর্ণধার। ১৯৬৯ ও ৭০ সালের মধ্যে এই কোম্পানি রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের দুইশ’ গান রেকর্ডে ধারণ করে। প্রথম ১২টি গানের একটা গুচ্ছ গেয়েছিলেন সনজীদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, রাখী চক্রবর্তী, আফসারি খানম, বিলকিস নাসিরউদ্দিন ও কলিম শরাফী। ‘আমার সোনার বাংলা’ গানের রেকর্ড প্রকাশে ছায়ানটের শিল্পীরাও এগিয়ে আসেন। কলিম শরাফীর ব্যবস্থাপনায়, আবদুল আহাদের পরিচালনায়, সনজীদা খাতুনের বাসায় তাঁরই যত্ম-আত্তিতে খাটুনিতে তৈরি হয় গানটি। সম্মেলক কণ্ঠে ছিলেন, জাহিদুর রহিম, অজিত রায়, ইকবাল আহমদ, ফাহমিদা খাতুন, জাহানারা ইসলাম, হামিদা আতিক, নাসরীন আহমদ প্রমুখ। সর্বত্র বাজতে থাকে এই রেকর্ড। অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধকালে বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজের কণ্ঠে এই গান ধ্বনিত হতো। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে শিল্পী কলিম শরাফী রমনা রেসকোর্সে লাখো লাখো জনতার উপস্থিতিতে সোনার বাংলাসহ রবীন্দ্রসংগীতের এক সেট গানের রেকর্ড উপহার দিয়েছিলেন সাড়ে সাতকোটি মানুষের বিজয়ী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে।
৭০ সালে জহির রায়হান তার ‘জীবন থেকে নেয়া’ চলচ্চিত্রে ‘আমার সোনার বাংলা’ গানটি ব্যবহার করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় দিকে দিকে বেজে ওঠে ‘আমার সোনার বাংলা’। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগেই ভবিতব্য বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে জনগণ ‘আমার সোনার বাংলা’কে নির্বাচন করেছিল। আর এই গ্রহণের ক্ষেত্রটি তৈরি করেছিলেন স্বয়ং বঙ্গবন্ধু। কারণ বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন রাজনীতি এবং শিল্প ও সাহিত্য একই জীবনের দু’রকম উৎসারণ। অসহযোগ আন্দোলনকালে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বেতার টিভিতে সোনার বাংলাসহ দেশপ্রেমের গান বেজেছে। সে সময় পুরো পাঁচ স্তবকই গাওয়া হতো অনুষ্ঠানে। রবীন্দ্রনাথ মূর্ত হয়ে ওঠেছিলেন বাঙালির জীবনে গণ-অভ্যূত্থানের সেই উনসত্তর সালে।
[জহির রায়হানের ‘জীবন থেকে নেয়া’ চলচ্চিত্রে ‘আমার সোনার বাংলা’]
সোনার বাংলা গানটি পূর্ববাংলার শিল্পীরা যে সুরে গাইতেন বা এখনও গাওয়া হয়, তা স্বরবিতানে ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর ছাপা স্বরলিপির সুরের অনুসরণ নয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এইচ এম ভি প্রথম ‘আমার সোনার বাংলা (নম্বর-২৭৭৯০) গানের রেকর্ড প্রকাশ করে। রেকর্ডের অপর পিঠে ছিল ‘সার্থক জনম আমার’। গেয়েছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত কন্যা সুচিত্রা মিত্র।
শান্তিদেব ঘোষ ছিলেন এই গানের ট্রেনার। ফলে স্বরবিতানের সুর থেকে এই সুরটি আরও বেশি বাউলাঙ্গ হয়ে পড়ে। এই সুরেই ফাহমিদা খাতুন ষাটের দশকের শেষ দিকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাইতেন। তারা সুচিত্রা মিত্রের রেকর্ড থেকেই গানটি তুলেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় গানটি এতোই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, ‘তখন বহু জায়গায় তা অশুদ্ধ উচ্চারণে ও ভুল সুরে কিন্তু সত্যিকার আবেগ দিয়ে গাইতে শুনেছি।’ মুক্তিযুদ্ধকালীন শিল্পী সংস্থার অন্যতম উদ্যোক্তা সনজীদা খাতুনের উপলব্ধি ছিল তাই। ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পর ‘আমার সোনার বাংলা’র প্রথম দশ চরণ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রূপে আর ডি এল রায়ের ‘ধন ধান্য পুষ্প ভরা’ জাতীয় গীত হিসেবে গৃহীত হয়। আর বঙ্গবন্ধু এভাবেই তার স্বপ্নকে রূপ দিলেন মূর্ততায়।
‘আমার সোনার বাংলা গানে’ রবীন্দ্রনাথ বাউল সুর প্রয়োগ করেছিলেন। স্বদেশের বাণীকে সাধারণের মর্মমূলে প্রবেশ করানোই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যিনি সঙ্গীত নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপ এবং বাহাস করতেন, বলেছেন তিনি, ‘বাংলাদেশের বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালী প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রাদেশিক অর্থাৎ দেশি সুর পদ্ধতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। বাংলাদেশের মাটির সঙ্গে, দেশের প্রাণের সঙ্গে যোগ তার খুবই নিবিড় ছিল। সেজন্য বিদেশি সভ্যতার কল্যাণে পুষ্ট স্বাধীন চিন্তা ও সৃষ্টির ধারা এই দেশের, গ্রামের পলিমাটি কেটেই বইল।’
স্বাধীনতার পর কেবিনেট ডিভিশনের সভায় বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও জাতীয় গীত হিসেবে দু’টি গান অনুমোদন করা হয়। কেবিনেট সচিব হোসেন তৌফিক ইমাম; টেলিভিশনের পক্ষে জামিল চৌধুরী সভায় আলোচনায় অংশ নেন। সভায় বঙ্গবন্ধু শোনেন যে, স্বরবিতানের ছাপানো সুরের সঙ্গে আমাদের শিল্পীদের গাওয়া সুরের মিল নেই। তখন তিনি বলেছিলেন, ‘যে সুর গেয়ে এদেশ স্বাধীন হয়েছে, সে সুরেই আমাদের জাতীয় সংগীত গাওয়া হবে, সেটিই জাতীয় সংগীতের সুর।’ পরবর্তীকালে জামিল চৌধুরী ‘শ্রোতার আসর রেকর্ড ক্লাব’ থেকে জাতীয় সংগীত ও জাতীয় গীতির একটি এক্সটেনডেড প্লে বা ব্যাপ্ত বাদন রেকর্ড বের করেন। দু’টি পিঠে দু’টি গান। যুদ্ধের সময় মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে যে সুরে ‘সোনার বাংলা’ গেয়েছিলেন, সেই সুরেই রেকর্ডে গাওয়া হয়। সুচিত্রা মিত্রের গাওয়া সুরের অনুসরণে মুক্তিযুদ্ধের সময় গাওয়া সুরটি ধরে রাখার জন্য তা রেকর্ডে ধারণ করা হয়।
বঙ্গবন্ধুর নিদের্শে কেবিনেট সচিব এইচ টি ইমাম জাতীয় সংগীতের স্বরলিপি সংগ্রহের উদ্যোগ নেন। দায়িত্ব দেন শান্তিনিকেতনের প্রথম মুসলমান ছাত্র রবীন্দ্র স্নেহধন্য শিল্পী আবদুল আহাদকে। বলেছিলেন, ‘আমার সোনার বাংলা গানটির স্বরলিপি নিয়ে আসার জন্য আপনাকে কলকাতা অথবা শান্তিনিকেতন যেতে হবে।’ আবদুল আহাদ, শিল্পী আতিকুল ইসলাম এবং আফসারী খানমসহ শান্তিনিকেতন যান। বিশ্বভারতীর মিউজিক বোর্ডের সভায় উপস্থিত হয়ে তারা জানালেন, ‘আমার সোনার বাংলা গানটি স্বরলিপি বইয়ে যেভাবে ছাপা আছে, সেটা আমরা গাই না। যে সুরটি প্রথম খুব সম্ভব সুচিত্রা মিত্র শিখেছিল ইন্দিরা দেবীর কাছ থেকে এবং রেকর্ডও করেছিল—বাংলাদেশের দরকার সেই সুরটির স্বরলিপি। শান্তিদেব ঘোষ যিনি রেকর্ডে সুচিত্রা মিত্রের ট্রেনার ছিলেন, সভায় তিনিও ছিলেন। আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত জানালো বিশ্বভারতী যে, তারা স্বরলিপি তৈরি করে বাংলাদেশের সরকারকে কিছুদিনের মধ্যে পাঠিয়ে দেবেন। যথারীতি বিশ্বভারতী স্বরলিপি ছাপিয়ে পাঠিয়েছিলেন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু সে চিঠি খোলা হয়নি। দুঃখ করেন সনজীদা খাতুন, ‘বেশ কিছু পরে জামিল চৌধুরী সরকারি দপ্তরে অনাদরে পড়ে থাকা বিশ্বভারতীর ছাপানো সোনার বাংলা স্বরলিপিপত্র দেখতে পেয়ে আমাকে এনে দেন। পত্র শেষে ছাপা আছে ‘প্রথম মুদ্রণ: ফাল্গুন, ১৩৭৮’ এবং ‘দ্বিতীয় মুদ্রণ: অগ্রহায়ণ ১৩৭৯।’ সুরটির বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ছায়ানটের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার আসর রেকর্ড ক্লাবও এগিয়ে এসেছিল। জাতীয় সংগীতের সুর নিয়ে বিভ্রম ঘোচাতে তারা সচেষ্ট হলেও তা ঘোচেনি। সুর লোকমুখে প্রায় বদলে গেছে। যথাযথ সুর অনুসরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় না।
রবীন্দ্র সংগীত বিশেষজ্ঞ ও সংগঠক সনজীদা খাতুন বলেছেন, ‘বিশ্বভারতীর প্রকাশিত “স্বরবিতান” ষট্চত্বারিংশ খণ্ডের পৌষ ১৩৬২ থেকে শুরু করে ভাদ্র ১৩৭৮ পর্যন্ত “আমার সোনার বাংলা” গানের কেবল ইন্দিরা বেদ চৌধুরাণীর স্বরলিপিটি পাই। তার পরে শ্রাবণ ১৩৮৫ (পুনর্মুদ্রণ) প্রকাশিত স্বরবিতান ৪৬ নম্বরের শেষে ‘সুরভেদ/ছন্দোভেদ’ শিরোনামে ‘আমার সোনার বাংলা’র দ্বিতীয় স্বরলিপিটি পাচ্ছি। শুরুতে বলা আছে ‘শ্রীমতি সুচিত্রা মিত্র—গীত গ্রামফোন রেকর্ড অনুসারে শ্রীশান্তিদেব ঘোষকৃত স্বরলিপি।’
দু’টি শক্তি এখানে মুখোমুখি। একটি শক্তি সাম্প্রদায়িক, ধর্মান্ধ হিংসার দর্শন দ্বারা পরিচালিত। অপরটি ভাষা আন্দোলনের পধ ধরে যে অসাম্প্রদায়িক, মননশীল, উদার মানবিকতার বিকাশ ঘটেছে তার পক্ষে। যদিও বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছে ধর্মীয় জাতীয়তাবোধকে বর্জন করে। বাংলাদেশে প্রকাশ্য রবীন্দ্রবিরোধিতা শুরু হয় ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর। সেই সঙ্গে বিতর্কিত করা হয় বাঙালি জাতীয়তাবোধকে। বঙ্গবন্ধুর জনসভার বাঁধা গায়ক শুধু নয়, জাহিদুর রহিম ছিলেন এদেশের প্রাগ্রসর শিল্পী। স্বাধীনতার পর স্টাফ আর্টিস্ট হিসেবে বাংলাদেশ বেতারে যোগ দেন। ১৯৭৭ সালের ১৬ ডিসেম্বরে তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়। ‘অপমানের দাহ তার পক্ষে দুঃসহ হলো’। ১৯৭৮ সালের জুন মাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চলে গেলেন ষাটের দশক থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রিয় গায়ক জাহিদুর রহিম। যাকে বঙ্গবন্ধু ডাকতেন ‘বাবু’ নামে। আমাদেরও জানা ছিল, তাই ‘বাবুভাই’ সম্বোধন পেতেন।
অমিতাভ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথ নিয়ে অনেক গ্রন্থ লিখেছেন। বাহাত্তরের জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের পর লিখেছিলেন, ‘শেখ মুজিব রবীন্দ্রনাথকে কতটা ভালোবাসতেন তার পরিচয় আমরা পেয়েছি গোড়া থেকেই। মনে আছে, ১৯৭১ সালে তিনি যখন পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি জেলে বন্দী, তখন বারবার আবৃত্তি করতেন, “নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এইদ্বার।” বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাহাত্তর সালের ৮ জানুয়ারি লন্ডনে যান। অমিতাভ চৌধুরী ফোনে বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জানান। বঙ্গবন্ধুর মুখে “জয় বাংলা” কথাটা শুনে আমি শিহরিত হয়েছিলাম এবং তিনি যখন ওই টেলিফোনেই বলতে শুরু করলেন “উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নাই, ওরে ভয় নাই” তখন আমি বাকরুদ্ধ।’
ঢাকায় বঙ্গবন্ধুকে বাহাত্তরের জানুয়ারিতে সাক্ষাৎকালে অমিতাভ চৌধুরী উপহার দিলেন অখণ্ড গীতবিতান, সঞ্চয়িতা এবং সমগ্র রবীন্দ্র রচনাবলী। সঙ্গে সুচিত্রা মিত্রের গাওয়া একাত্তরে প্রকাশিত রেকর্ড ‘আমার সোনার বাংলা’ এবং অংশুমান রায়ের গাওয়া ‘শোন, একটি মুজিবরের থেকে।’ উপহার নিয়ে বঙ্গবন্ধু সঞ্চয়িতার পাতা তখন উল্টে চলেছেন। পরনে হাফশার্ট ও লুঙ্গি। অমিতাভ চৌধুরী সেই মুহূর্তের কথা বর্ণনা করছেন এভাবে, ‘হাসিনা বলেন, আব্বা, মনে আছে তোমার, একটা বই—রবীন্দ্রনাথের—তাতে সব জেলের ছাপ ছিল? শেখ সাহেব সঞ্চয়িতার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মুখ না তুলেই বললেন, “মনে থাকবে না, ও বইখানা তো ওরা পোড়ায়া দিছে।’
বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ২৫ মার্চ রাতে যে গোলাবর্ষণ হয়েছিল, তাতে সঞ্চয়িতাও গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর গ্রন্থের সংগ্রহ পাকবাহিনী লুটপাট করে নিয়ে যায়, এমনকি গ্রামোফোন যন্ত্র। তাই রেকর্ড হাতে আক্ষেপ করে বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব বলেছিলেন অমিতাভ চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে, ‘হায়রে কপাল, ও তো জানেও না যে, বাড়িতে গ্রামোফোন নাই।’ রবীন্দ্রনাথের প্রচুর কবিতা বঙ্গবন্ধুর মুখস্থ ছিল। কবিতা তাকে প্রেরণা যোগাতো। পাকিস্তানী কারাগারে নয়মাসের বন্দীজীবনে রবীন্দ্র কবিতা আওড়াতেন, ছিল যা মুখস্থ।
বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু ও রবীন্দ্রনাথকে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়েছে অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংগ্রাম আন্দোলনের মাধ্যমে। দীর্ঘ পরাধীন একটি পশ্চাৎপদ জাতিকে তারা আত্মবোধনে উদ্বোধন করেছিলেন। আর সেই জাতিকে তার ভাষা, সংস্কৃতিসহ একটি রাষ্ট্র উপহার দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর। ‘বাঙালি’ বলে যে জাতির কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, বঙ্গবন্ধু সেই জাতিকেই আবিষ্কার করেন সোনার বাংলায়। এনে দেন আত্মমর্যাদা, স্বাধীন সত্তা। এই বাংলাকে ভালোবেসে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ‘আমার সোনার বাংলা’। আর বঙ্গবন্ধু তা একটি জাতির জাতীয় সঙ্গীতে রূপান্তর করে, চিরস্থায়ী করে দেন। সেই জাতীয় সংগীতের সঠিক সুর প্রয়োগ যদি না হয়, তবে বঙ্গবন্ধু বা রবীন্দ্রনাথের কাছে দায়বদ্ধতা শুধু নয়, একটি জাতির প্রতি অবহেলার নামান্তর হবে।
তবে আশার কথা যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগ জাতীয় সংগীতের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত শিক্ষা কোর্স চালু করেছে। সেখানে ছায়ানট প্রণীত স্বরলিপি অবলম্বনে জাতীয় সংগীত শেখানো হয়। কিন্তু সাধারণ স্কুল কলেজ বা অনুষ্ঠানগুলোতে জাতীয় সংগীত যে যথাযথভাবে গাওয়া হয় না, সে বলাই বাহুল্য। বেতার টেলিভিশনও পারে যথা সুরে জাতীয় সঙ্গীত শেখানোর আয়োজনে এগিয়ে যেতে। বাংলার স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু ও রবীন্দ্রনাথ দু’জনেই শারীরিক অনুপস্থিত থাকলেও ছিলেন সবসময়ই প্রতিটি মুক্তিকামী বাঙ্গালীর পাশে ও মনে এবং জীবনযাপনে। তারা তাদের দেশকে ভালোবাসতেন বলেই গেয়েছিলেন, ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।’
http://banglanews24.com/fullnews/bn/380027.html
- Biplob Rahman | ২৯ এপ্রিল ২০১৫ ১৮:০২582814
- শৈশবের মুক্তিযুদ্ধ এবং কয়েকজন হিন্দু শরণার্থী | শাকুর মজিদ
স্বাধীনতা দিবস / শিল্প-সাহিত্য
বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম
মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স মাত্র ৬/৭ বছর। এ সময়ের স্মৃতি মানুষের মনে থাকে না। আমারও নাই। যা কিছু আছে, তা খুবই ঝাপসা। খণ্ড খণ্ড। অনেকটা পুরনো স্বপ্নের মত। কখনও জায়গাটি সঠিক মনে হয় না। কখনও মানুষের মুখগুলোও অচেনা লাগে, এমনটি।
জালাল চাচার কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের পাড়াতেই তার বাড়ি। আমার বাড়ি থেকে কয়েক কদম পূর্বদিকে। তিনি আমাদের থেকে ৪/৫ বছরের বড়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি আমাদেরকে নিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতেন। বাঁশ দিয়ে এক ধরনের নকল বন্দুক বানানো হতো। এর কৌশলটি তার নিজের আবিষ্কার ছিল। এই বাঁশের ভেতর বন্দুকের ট্রিগারের মত একটা জিনিস থাকে। সেখানে গুলিও ভরা যেত। গুলি ছিল পাটকাঠি। এই পাটকাঠির গুলি দিয়ে পাঞ্জাবি আর মুক্তিরা যুদ্ধ করত। জালাল চাচা আমাদের কমান্ডার, তিনি আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে লেফট-রাইট করতেন। তার কাছ থেকেই প্রথম শোনা—এটেনশন, স্টেন্ডেট ইজ, ফরোয়ার্ড মার্চ, কুইক মার্চ—এসব শব্দ। আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিল এই খেলায়। সবার নাম মনে নাই। নানাবাড়ির জামাল, তার পাশের বাড়ির হেলাল, তার ছোট ভাই জালাল, ছফর, আছাদ—এরা ছিল আমাদের যোদ্ধাদলের সঙ্গী। আমাদের কাজ ছিল মাঝে মাঝে দল বেঁধে বাড়ির পাশের রাস্তায় শ্লোগান দেয়া।
আমার জীবনে একমাত্র মুক্তিযোদ্ধাকে দেখেছিলাম যুদ্ধের সময়কালে। তিনি আমাদের হান্নান দাদা। আমাদেরই আত্মীয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন। তাঁর মা আমাদের বাড়িতে এসে প্রতিদিন কান্নাকাটি করতেন। ছেলে বেঁচে আছে, না মারা গেছে, এটা তিনি জানতেন না। যুদ্ধের সময়ই তিনি একদিন বাড়ি এলেন। তাঁর গায়ে বাদামি রঙের খাকি পোশাক। কোমরের কাছে বিরাট আকারের একটা বেল্ট। বেল্টের সঙ্গে গুলি লাগানো, আমরা তাঁর পাশে গিয়ে বসি। তার পাশে রাখা বন্দুক ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করি। তিনি বন্দুকে হাত দিতে দেন না। আমি নাম জিজ্ঞেস করি। বলেন, এটা ‘ইস্টেনগান’।
এই স্টেনগান থেকে কী করে গুলি বের হয় আমার খুব জানতে ইচ্ছে হয়েছিল। তিনি আমাদের নিয়ে বাড়ির পুকুরপাড়ে আসেন। তার সঙ্গে আমরাও আসি। কাচ্চাবাচ্চার দল—১৫-২০ জন তো হবেই। আমাদের নিয়ে হান্নানদা বাড়ির বাইরে পুকুরপাড়ে আসেন। বেল্ট থেকে বের করে গুলি লোড করেন, ট্রিগার টিপে টিপে অনেক খোলা ফায়ার করেন উপরের দিকে।
আরেক মুক্তিযোদ্ধাকে দেখেছিলাম, সেটা অবশ্য দেশ স্বাধীন হবার পর। ২৫-২৬ বছর বয়স তার। তরুণই। কিন্তু চুলদাঁড়িগোঁফ কিছুই কাটা নেই। বাউল দরবেশের মত চেহারা, অনেক বড় হবার পর বিপ্লবী নেতা চে গুয়েভারার যে ছবিটা দেখেছিলাম, অনেকটা সেরকম। ঈদগাঁ বাজারে হাঁটতে গিয়েছি। সে-যোদ্ধা তখন বাজারে এসেছেন। তাঁর হাতেও তখন বন্দুক। লোকজন বলল, উনিও আমাদের গ্রামের যোদ্ধা, তবে যুদ্ধ করেছেন খুলনা অঞ্চল থেকে। সেখানেই সে সময় ছিলেন তিনি। তার নাম আতাউর। তিনি নাকি পণ করেছিলেন দেশ স্বাধীন না হলে কোনওদিন চুলদাঁড়ি কাটবেন না। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে। অস্ত্র জমা দেবেন আর চুলদাঁড়িও কাটবেন।
দেশে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এটা খুব ভালো করে বুঝতে পারতাম না। আমার বাবা জাহাজে চাকরি করতেন, তিনি তখন জাহাজে। দাদা হ্বজে। বাড়িতে মা আর দাদী। আমার ছোট একটা বোন আছে। ওর মুখ থেকে একটু একটু কথা ফুটেছে। হঠাৎ শুনি সে বলে—‘জালাললা, জালাললা’—এর কোনও মানে বুঝি না। দু একদিন পর শুনি ও বলছে, ‘হুশিয়া, হুশিয়া...’।
আমরা তখন আমাদের কমান্ডার জালাল চাচার নেতৃত্বে যে স্লোগান পেতাম—‘পাকিস্তানের দালালরা, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার’ আসলে এই কথাগুলোই সে তখন বলত।
বিকেলবেলা আমরা কখনও ‘মুক্তি মুক্তি’ খেলতাম কখনও বা গোল্লাদৌড়। গ্রামে আমাদের বাড়িটি শেষ মাথায়, পশ্চিমপাড়ে। তারপর মাঠ। সেই মাঠে আমরা খেলছি। এমন সময়, দেখি আমাদের বাড়ির উপর দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে। বেশ বড় কুণ্ডলি পাকানো ধোঁয়া। এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। কিছু কিছু বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে। যেসকল পরিবারের লোকজন মুক্তিযুদ্ধে গেছে, তাদের বাড়ি পোড়ানো হচ্ছে। আমি প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেলাম—নিশ্চয়ই হান্নানদার ঘরে আগুন দেয়া হয়েছে। আমরা দৌড়ে আবার বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখি—আগুন আসলে অনেক দূরে। খালেদ ছিল আমাদের সাথে খেলায়, সে বলল আজির উদ্দিনের বাড়িতে আগুন দিয়েছে। আজির উদ্দিন আমার মামা হন, তিনি মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক।
এর কয়েকদিন পর আবার মাঠে খেলছি। আজ খালেদ নাই। ২/৩ দিন ধরে সে খেলতে আসছে না। হঠাৎ দেখি তার বাড়ির উপর আগুনের ধোঁয়া। আমরা দৌড়ে তার বাড়ির দিকে যেতে চাইলাম। গ্রামের লোকজন বলল, রাজকাররা আছে ওখানে, যে আগুন নেভাতে যাবে, তাকেও পিটাবে। আমরা ভয়ে কেউ আর যাইনি।
আরেকদিন বিকেলবেলা। পশ্চিমের মাঠে খেলছি, এমন সময় ২০-২৫ জনের একদল লোক পশ্চিমের হাওড় পেরিয়ে আমাদের গ্রামের দিকে যাচ্ছে। ওদের দলে বুড়াবুড়ি, তরুণী আর কোলে ২-৩টা বাচ্চাও ছিল। ওদের চেহারা দেখে বুঝতে পারছি, ওরা হিন্দু। মহিলাদের কপালে সিঁদুর, লোকগুলোর কারও কারও পরনে ধূতি। মাগরিবের আজান হয়ে গেছে, আমরা খেলা ছেড়ে বাড়ির দিকে রওনা দিই।
বাড়ি এসে দেখি, সেই দল, আমাদের বাড়ির পূর্বপাশে যে টংগি ঘর ছিল, তার বারান্দায় বসে আছে। ঘরের ভেতর গিয়ে শুনি অন্য অবস্থা। আম্মা বলেন, এরা হিন্দু শরণার্থী। সুনামগঞ্জ থেকে হেঁটে এসেছে সারাদিন, কেউ খায়নি। তারা নাকি রাতে আমাদের বাড়িতে থাকতে চায়। সকাল হলেই তারা আবার চলে যাবে। এরা যাবে ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ার বর্ডার আমাদের বাড়ি থেকে আরও ৪-৫ মাইল দূরে।
আমার আম্মা খুব ধর্মপ্রাণ মহিলা। তিনি হিন্দুদের ঘরের ভেতর ঢুকতে দেন না। গগন নামে এক হিন্দু দইয়ালা আমাদের বাড়িতে আসত যখন বাবা থাকতেন। এই দইওয়ালাকে তিনি ঘরে ঢুকতে দিতেন না। কিন্তু এখন দেখি আম্মার অনেক ব্যস্ততা। তিনি বললেন—এসে লোককে খাওয়ানোর মত কিছু নাই। আমাকে পাঠালেন মুদরিছ চাচার দোকানে ডাল আর পেঁয়াজ কেনার জন্য। আমি আমার চাচাত ভাই আলমকে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা দোকানে গেলাম। ডাল এলো, পেঁয়াজ এলো। এক ফাঁকে টংগি ঘরে এসে দেখি, মহিলারা বাচ্চা নিয়ে ঘরের মেঝেতে শুয়ে আছে, পুরুষেরা বারান্দায়। এরা কত রাত এভাবে থাকবে বুঝতে পারি না। ভেতর বাড়িতে তাদের নিয়ে যাবার কোনও পরিকল্পনা আম্মার যে নেই, এটা বুঝতে পারছিলাম।
নিজের ঘরে এসে দেখি, আম্মা রান্নাঘরে ডাল রাধতে ব্যস্ত। গরম ভাত আর ডাল পাঠানো হলো টংগি ঘরে।
পরদিন সকালবেলা মসজিদে যাব মিয়াছাবের কাছে পড়তে। আমি উঁকি মারি টংগি ঘরের ভেতর। গিয়ে দেখি, কেউ নেই।
দিনের আলো ফুটে ওঠার আগেই হিন্দু শরণার্থীরা সবাই চলে গেছে। ২০-২৫ জনের দল কেমন করে একটা ঘরে রাত কাটাল, কিছুই জানতে পারলাম না। ১৯৭১ সালে ৬-৭ বছরের এক শিশুর তখন কতটুকুই বা জানার কথা!
http://banglanews24.com/fullnews/bn/380037.html
 aranya | 83.197.98.233 | ০৩ মে ২০১৫ ১১:৩৩582815
aranya | 83.197.98.233 | ০৩ মে ২০১৫ ১১:৩৩582815- সব কটা জানালা খুলে দাও না
আমি গাইব, গাইব বিজয়ের গান
ওরা আসবে, চুপি চুপি
যারা এই দেশটাকে ভাল বেসে দিয়ে গেছে প্রাণ ..
 aranya | 83.197.98.233 | ০৩ মে ২০১৫ ১১:৩৪582816
aranya | 83.197.98.233 | ০৩ মে ২০১৫ ১১:৩৪582816- কেউ যেন ভুল করে গেও না কো মন ভাঙা গান
- বিপ্লব রহমান | ০৫ মার্চ ২০১৭ ১৪:৪৯582817
- অগ্নিঝরা মার্চ
‘ইয়াহিয়া বললেন, খেলা শেষ’
সোহরাব হাসান
০৫ মার্চ ২০১৭, ০১:৪৭
১
একাত্তরের ঘটনাবলি পাকিস্তানের একেক কুশীলব একেকভাবে দেখেছেন। ব্যাখ্যা করেছেন। সিদ্দিক সালিক ও আরশাদ সামি খান দুজনই ছিলেন পাকিস্তানের সেনা কর্মকর্তা। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়।
মুক্তিযুদ্ধের সময় সিদ্দিক সালিক ছিলেন ঢাকায় আর সামি খান রাওয়ালপিন্ডিতে। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকের বর্ণনা দিতে গিয়ে সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, ‘জেনারেল নিয়াজি ১৪ ডিসেম্বর রাও ফরমান আলীকে সঙ্গে নিয়ে মার্কিন কনসাল জেনারেল স্পিভাকের কাছে যান এবং যুদ্ধবিরতির শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা করার অনুরোধ জানান। কিন্তু স্পিভাক জানিয়ে দেন যে তিনি তাঁদের পক্ষ নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন না, বার্তাটি পাঠিয়ে দিতে পারেন মাত্র।
জেনারেল নিয়াজি চেয়েছিলেন, প্রস্তাবটি ভারতের সেনাপ্রধান স্যাম মানেকশর কাছে পাঠানো হোক। কিন্তু স্পিভাক পাঠিয়েছেন ওয়াশিংটনে। মার্কিন সরকার ভারতের কাছে পাঠানোর আগে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে পরামর্শ করার চেষ্টা করে, কিন্তু ইয়াহিয়া খানকে পাওয়া যাচ্ছিল না। সিদ্দিক সালিক জানাচ্ছেন, ইয়াহিয়া ৩ ডিসেম্বর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন এবং আর অফিসে আসেননি। তাঁর সামরিক সচিব মানচিত্রের মাধ্যমে তাঁকে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতেন। একবার সেই মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, ‘পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আমি কী করতে পারি?’
১৬ ডিসেম্বর লাখ লাখ বাঙালির উপস্থিতিতে তৎকালীন রমনা রেসকোর্স ময়দানে জেনারেল নিয়াজি বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। নিয়াজি প্রথমে যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানালে ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা তাঁর অবস্থানে অনড় থেকে বলেন, ‘এটি আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়।’ তখন নিয়াজি যৌথ বাহিনীর কাছেই আত্মসমর্পণ করেন।
যুদ্ধ আরও কয়েক দিন প্রলম্বিত করতে পারতেন কি না, পরে সিদ্দিক সালিক জিজ্ঞেস করলে নিয়াজি জবাব দেন, ‘তাতে আরও বেশি মানুষের মৃত্যু ও সম্পদ ধ্বংস হতো। নগরজীবন অচল হয়ে যেত। মহামারি ও অন্যান্য ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু পরিণতি একই হতো। এরপর তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন, ‘আমি ৯০ হাজার বিধবা ও ৫০ লাখ এতিমের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে এখন ৯০ হাজার যুদ্ধবন্দী পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাচ্ছি।’
এর আগের একটি ঘটনা। যুদ্ধে পরাজয় এড়ানোর জন্য পাকিস্তান তখন মরিয়া। ইয়াহিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে সহায়তা চেয়ে বার্তা পাঠালেন। পাকিস্তান সময় রাত দুইটায় নিক্সন যখন টেলিফোন করেন, ইয়াহিয়া তখন নিদ্রামগ্ন। তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিলে দুই প্রেসিডেন্টের মধ্যে কথোপকথন হয়। নিক্সন পাকিস্তানের নিরাপত্তা নিয়ে তাঁর উদ্বেগের কথা জানান এবং বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠানোর নির্দেশ দেন। দুই নেতার টেলিফোন সংলাপ শেষ হওয়ার পর উদ্দীপ্ত ইয়াহিয়া জেনারেল হামিদকে টেলিফোনে লাগিয়ে দিতে বলেন। ইয়াহিয়ার মতো সামিও তখন উদ্দীপ্ত।
ইয়াহিয়া বললেন, ‘হামিদ, আমরা এটা করেছি। আমেরিকানরা পথে আছে।’ এরপর সামির মন্তব্য, ‘পূর্ব পাকিস্তানে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও জীবনহানি সত্ত্বেও সেই আমেরিকান নৌবহর আর আসেনি, এমনকি ঢাকা পতনের পরও নয়।’ তাঁর কাছে ঢাকার পতন এবং আত্মসমর্পণ ছিল একটি দুঃখজনক অভিজ্ঞতা। তিনি বলেছেন, ‘আমি কেঁদেছি এবং আমাদের টিমের আরও অনেকেই কেঁদেছে। পরাজিত ও অবমাননার বোধ তাড়িত করেছিল আমাদের। এসব যখন আমাদের সঙ্গে ঘটছে, আমরা তখন তা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সামি ভেবেছেন, সেটি ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন এবং তা একসময় কেটে যাবে।
কিছুক্ষণ পর তাঁর বোধোদয় হলো, এটি কোনো দুঃস্বপ্ন ছিল না। প্রতিদিনের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মতো ধ্রুব সত্য।
ভুট্টো বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে যে কমিশন গঠন করেছিলেন, সেখানে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সামি খান তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। সেটি অবশ্য নিজের জন্য নয়। তিনি যার এডিসি ছিলেন, সেই পদচ্যুত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের জন্য। কমিশনের প্রধান তাঁকে বহু নারীর নাম উল্লেখ করে জানতে চান, ‘স্কোয়াড্রন লিডার, আপনি এঁদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ করে দিয়েছেন, আপনি কি বলতে পারেন, তাঁরা ভেতরে যাওয়ার পর কী হয়েছে? মনে রাখবেন, আপনি শপথ নিয়েছেন।’
এই প্রশ্নে সামি খান বিরক্ত হলেও মাথা ঠান্ডা করে বললেন, ‘এখানে দুটি বিষয় আছে, প্রটোকল ও নিরাপত্তা। এডিসি হিসেবে যাঁরা সাক্ষাতের সময় ঠিক না করে আসেন, তাঁদের বিষয়টি দেখা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আপনি স্মরণ করে দেখতে পারেন, অনুমতি নিয়ে অনেকবার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেছেন। কিন্তু ভেতরে প্রেসিডেন্ট ও আপনার মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছে, সেটি আমার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। প্রেসিডেন্ট ও আপনি যেসব নারীর কথা বললেন, তাঁদের মধ্যে কী হয়েছে, তা–ও আমার জানার কথা নয়।’
দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, জেনারেল ইয়াহিয়া সব সময় মদ খেতেন। আপনি কী বলতে পারেন দিনে কী পরিমাণ মদ তিনি খেতেন?
সামি উত্তর দিলেন, ‘স্যার, আপনি ভুল লোককে প্রশ্ন করেছেন। আমি তাঁর মদ পরিবেশনকারী ছিলাম না। আপনি যদি এই প্রশ্নের উত্তর চান তাহলে বার বয় বা হাউস কম্পট্রোলারের কাছে জিজ্ঞেস করুন।’
নিয়াজির বার্তা পেয়ে ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন এবং ঢাকার পরাজয়কে দুঃখজনক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,
এই বিপর্যয় সাময়িক এবং পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধ অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন। কিন্তু প্রেসিডেন্টের ভাষণের মূল রূপরেখা অনেক দিন আগেই তৈরি করে রাখা হয়েছিল।
এরপর ইয়াহিয়া জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে এই বার্তা পাঠান যে, পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দিয়েছে এবং ভারতকেও এটি মানতে হবে। তিনি এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরও সহযোগিতা চান।
তখনো পশ্চিম পাকিস্তানের ৫ হাজার বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ড এবং ৯০ হাজার যুদ্ধবন্দীর বিষয়টি জনগণকে জানানো হয়নি। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে জয়ী না হয়েও যেভাবে জনগণকে বোঝানো গিয়েছিল, এবার আর সেটি সম্ভব হচ্ছে না। এর অর্থ হলো, জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও তাঁর সহযোগীদের বিদায়। জেনারেলদের সঙ্গে ইয়াহিয়ার বৈঠকের মাঝখানেই জানা গেল সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে।
এই প্রেক্ষাপটে ইয়াহিয়া তাঁর এডিসি সামি খানকে লক্ষ করে বললেন, ‘শোনো, ব্রিগেড বিদ্রোহ করেছে, এ খবর সত্য হোক বা না হোক, খেলা শেষ।
২০ ডিসেম্বর জুলফিকার আলী ভুট্টো দেশে ফিরে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে শপথ নেন।
আগামীকাল: ঢাকায় ইয়াহিয়ার নৈশবিহার
সোহরাব হাসান: কবি, সাংবাদিক।
[email protected]
http://www.prothom-alo.com/opinion/article/1097434/%E2%80%98%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7%E2%80%99
- বিপ্লব রহমান | ০৫ মার্চ ২০১৭ ১৪:৫১582819
- অগ্নিঝরা মার্চ
‘ইয়াহিয়া বললেন, খেলা শেষ’
সোহরাব হাসান
০৫ মার্চ ২০১৭, ০১:৪৭
একাত্তরের ঘটনাবলি পাকিস্তানের একেক কুশীলব একেকভাবে দেখেছেন। ব্যাখ্যা করেছেন। সিদ্দিক সালিক ও আরশাদ সামি খান দুজনই ছিলেন পাকিস্তানের সেনা কর্মকর্তা। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়।
মুক্তিযুদ্ধের সময় সিদ্দিক সালিক ছিলেন ঢাকায় আর সামি খান রাওয়ালপিন্ডিতে। মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকের বর্ণনা দিতে গিয়ে সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, ‘জেনারেল নিয়াজি ১৪ ডিসেম্বর রাও ফরমান আলীকে সঙ্গে নিয়ে মার্কিন কনসাল জেনারেল স্পিভাকের কাছে যান এবং যুদ্ধবিরতির শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা করার অনুরোধ জানান। কিন্তু স্পিভাক জানিয়ে দেন যে তিনি তাঁদের পক্ষ নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন না, বার্তাটি পাঠিয়ে দিতে পারেন মাত্র।
জেনারেল নিয়াজি চেয়েছিলেন, প্রস্তাবটি ভারতের সেনাপ্রধান স্যাম মানেকশর কাছে পাঠানো হোক। কিন্তু স্পিভাক পাঠিয়েছেন ওয়াশিংটনে। মার্কিন সরকার ভারতের কাছে পাঠানোর আগে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে পরামর্শ করার চেষ্টা করে, কিন্তু ইয়াহিয়া খানকে পাওয়া যাচ্ছিল না। সিদ্দিক সালিক জানাচ্ছেন, ইয়াহিয়া ৩ ডিসেম্বর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন এবং আর অফিসে আসেননি। তাঁর সামরিক সচিব মানচিত্রের মাধ্যমে তাঁকে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতেন। একবার সেই মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, ‘পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আমি কী করতে পারি?’
১৬ ডিসেম্বর লাখ লাখ বাঙালির উপস্থিতিতে তৎকালীন রমনা রেসকোর্স ময়দানে জেনারেল নিয়াজি বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। নিয়াজি প্রথমে যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানালে ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা তাঁর অবস্থানে অনড় থেকে বলেন, ‘এটি আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়।’ তখন নিয়াজি যৌথ বাহিনীর কাছেই আত্মসমর্পণ করেন।
যুদ্ধ আরও কয়েক দিন প্রলম্বিত করতে পারতেন কি না, পরে সিদ্দিক সালিক জিজ্ঞেস করলে নিয়াজি জবাব দেন, ‘তাতে আরও বেশি মানুষের মৃত্যু ও সম্পদ ধ্বংস হতো। নগরজীবন অচল হয়ে যেত। মহামারি ও অন্যান্য ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু পরিণতি একই হতো। এরপর তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন, ‘আমি ৯০ হাজার বিধবা ও ৫০ লাখ এতিমের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে এখন ৯০ হাজার যুদ্ধবন্দী পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাচ্ছি।’
এর আগের একটি ঘটনা। যুদ্ধে পরাজয় এড়ানোর জন্য পাকিস্তান তখন মরিয়া। ইয়াহিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে সহায়তা চেয়ে বার্তা পাঠালেন। পাকিস্তান সময় রাত দুইটায় নিক্সন যখন টেলিফোন করেন, ইয়াহিয়া তখন নিদ্রামগ্ন। তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিলে দুই প্রেসিডেন্টের মধ্যে কথোপকথন হয়। নিক্সন পাকিস্তানের নিরাপত্তা নিয়ে তাঁর উদ্বেগের কথা জানান এবং বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠানোর নির্দেশ দেন। দুই নেতার টেলিফোন সংলাপ শেষ হওয়ার পর উদ্দীপ্ত ইয়াহিয়া জেনারেল হামিদকে টেলিফোনে লাগিয়ে দিতে বলেন। ইয়াহিয়ার মতো সামিও তখন উদ্দীপ্ত।
ইয়াহিয়া বললেন, ‘হামিদ, আমরা এটা করেছি। আমেরিকানরা পথে আছে।’ এরপর সামির মন্তব্য, ‘পূর্ব পাকিস্তানে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও জীবনহানি সত্ত্বেও সেই আমেরিকান নৌবহর আর আসেনি, এমনকি ঢাকা পতনের পরও নয়।’ তাঁর কাছে ঢাকার পতন এবং আত্মসমর্পণ ছিল একটি দুঃখজনক অভিজ্ঞতা। তিনি বলেছেন, ‘আমি কেঁদেছি এবং আমাদের টিমের আরও অনেকেই কেঁদেছে। পরাজিত ও অবমাননার বোধ তাড়িত করেছিল আমাদের। এসব যখন আমাদের সঙ্গে ঘটছে, আমরা তখন তা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সামি ভেবেছেন, সেটি ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন এবং তা একসময় কেটে যাবে।
কিছুক্ষণ পর তাঁর বোধোদয় হলো, এটি কোনো দুঃস্বপ্ন ছিল না। প্রতিদিনের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মতো ধ্রুব সত্য।
ভুট্টো বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে যে কমিশন গঠন করেছিলেন, সেখানে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সামি খান তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। সেটি অবশ্য নিজের জন্য নয়। তিনি যার এডিসি ছিলেন, সেই পদচ্যুত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের জন্য। কমিশনের প্রধান তাঁকে বহু নারীর নাম উল্লেখ করে জানতে চান, ‘স্কোয়াড্রন লিডার, আপনি এঁদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ করে দিয়েছেন, আপনি কি বলতে পারেন, তাঁরা ভেতরে যাওয়ার পর কী হয়েছে? মনে রাখবেন, আপনি শপথ নিয়েছেন।’
এই প্রশ্নে সামি খান বিরক্ত হলেও মাথা ঠান্ডা করে বললেন, ‘এখানে দুটি বিষয় আছে, প্রটোকল ও নিরাপত্তা। এডিসি হিসেবে যাঁরা সাক্ষাতের সময় ঠিক না করে আসেন, তাঁদের বিষয়টি দেখা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আপনি স্মরণ করে দেখতে পারেন, অনুমতি নিয়ে অনেকবার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেছেন। কিন্তু ভেতরে প্রেসিডেন্ট ও আপনার মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছে, সেটি আমার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। প্রেসিডেন্ট ও আপনি যেসব নারীর কথা বললেন, তাঁদের মধ্যে কী হয়েছে, তা–ও আমার জানার কথা নয়।’
দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, জেনারেল ইয়াহিয়া সব সময় মদ খেতেন। আপনি কী বলতে পারেন দিনে কী পরিমাণ মদ তিনি খেতেন?
সামি উত্তর দিলেন, ‘স্যার, আপনি ভুল লোককে প্রশ্ন করেছেন। আমি তাঁর মদ পরিবেশনকারী ছিলাম না। আপনি যদি এই প্রশ্নের উত্তর চান তাহলে বার বয় বা হাউস কম্পট্রোলারের কাছে জিজ্ঞেস করুন।’
নিয়াজির বার্তা পেয়ে ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন এবং ঢাকার পরাজয়কে দুঃখজনক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,
এই বিপর্যয় সাময়িক এবং পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধ অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন। কিন্তু প্রেসিডেন্টের ভাষণের মূল রূপরেখা অনেক দিন আগেই তৈরি করে রাখা হয়েছিল।
এরপর ইয়াহিয়া জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে এই বার্তা পাঠান যে, পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দিয়েছে এবং ভারতকেও এটি মানতে হবে। তিনি এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরও সহযোগিতা চান।
তখনো পশ্চিম পাকিস্তানের ৫ হাজার বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ড এবং ৯০ হাজার যুদ্ধবন্দীর বিষয়টি জনগণকে জানানো হয়নি। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে জয়ী না হয়েও যেভাবে জনগণকে বোঝানো গিয়েছিল, এবার আর সেটি সম্ভব হচ্ছে না। এর অর্থ হলো, জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও তাঁর সহযোগীদের বিদায়। জেনারেলদের সঙ্গে ইয়াহিয়ার বৈঠকের মাঝখানেই জানা গেল সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে।
এই প্রেক্ষাপটে ইয়াহিয়া তাঁর এডিসি সামি খানকে লক্ষ করে বললেন, ‘শোনো, ব্রিগেড বিদ্রোহ করেছে, এ খবর সত্য হোক বা না হোক, খেলা শেষ।
২০ ডিসেম্বর জুলফিকার আলী ভুট্টো দেশে ফিরে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে শপথ নেন।
আগামীকাল: ঢাকায় ইয়াহিয়ার নৈশবিহার
সোহরাব হাসান: কবি, সাংবাদিক।
[email protected]
http://www.prothom-alo.com/opinion/article/1097434/%E2%80%98%E0%A6%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%96%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7%E2%80%99
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... জয়ন্ত ঘোষ , অভিজিৎ চক্রবর্তী। , Kuntala)
(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, অঞ্জনা ঘোষাল, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Sara Man, প্যালারাম, যদুবাবু)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... dc)
(লিখছেন... dc)
(লিখছেন... &/, aranya)
(লিখছেন... রং, Kuntala)
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... &/, সিএস, &/)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... রঞ্জন , kk, Ranjan Roy)
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল)
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : [email protected] ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত