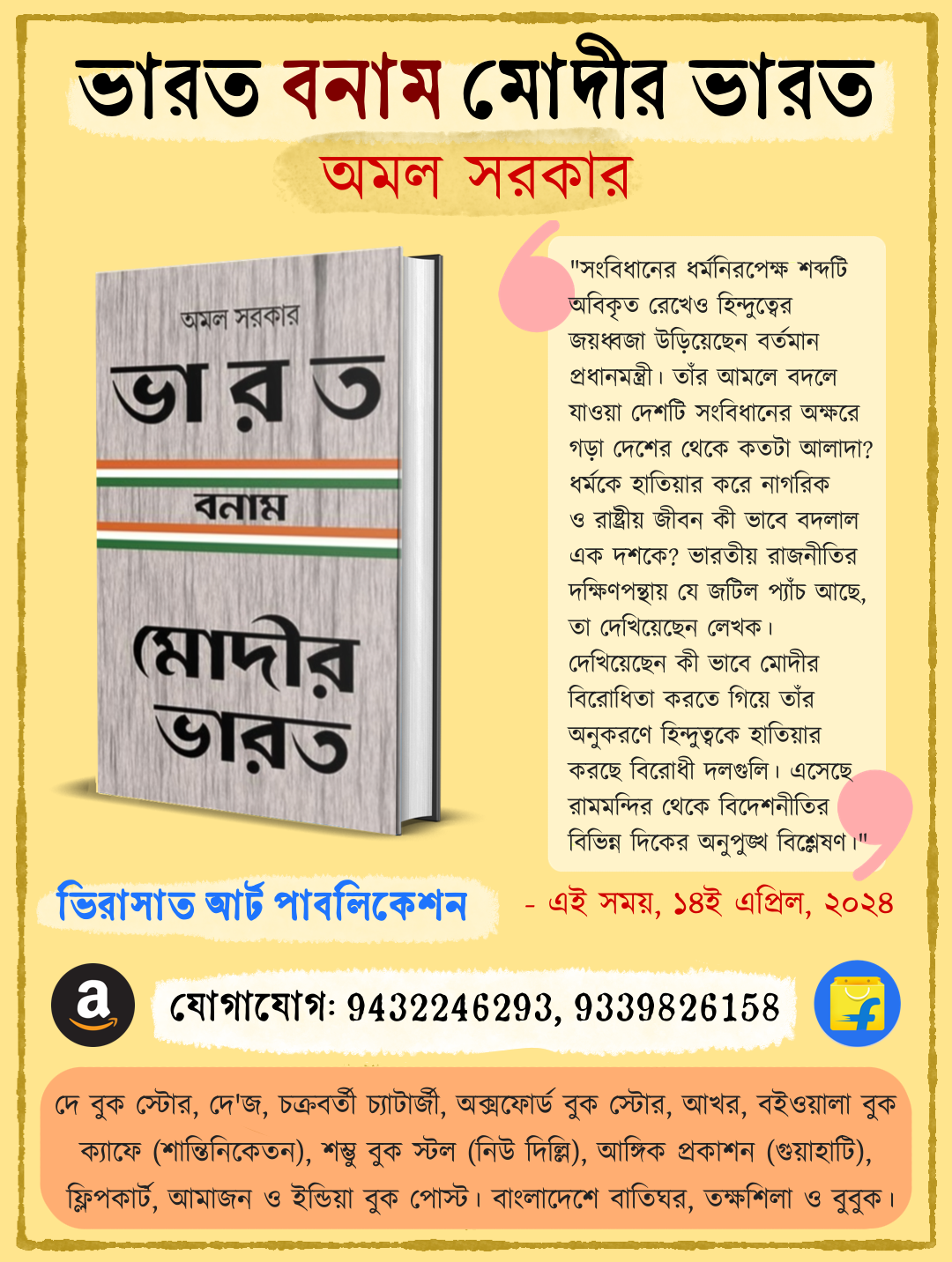- টইপত্তর অন্যান্য

-
১৯৭১ :: মুক্তিযুদ্ধের কথা
বিপ্লব রহমান
অন্যান্য | ০৯ ডিসেম্বর ২০১২ | ৪৯৫১২♦ বার পঠিত
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
- Biplob Rahman | ২১ ডিসেম্বর ২০১৩ ১১:০৩582654
- কাদের মোল্লার ফাঁসির জন্য ইমরান খানের আহাজারি প্রসঙ্গে
লিখেছেন: ফারজানা কবীর খান স্নিগ্ধা
স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ ৪২ বছর পর যখন বাংলাদেশ নিজেদের কলঙ্ক মুক্ত করার প্রথম অধ্যায়ে পা রেখেছে, ঠিক তখনই জাতিসংঘ থেকে শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব, তুরষ্ক, পাকিস্তানের মত দেশগুলো তার বিরোধিতা করে চলছে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের জামাতে ইসলামের শাখা তাদের সহযোদ্ধা কাদের মোল্লার ফাঁসির রায়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। এমনকি তারা পাকিস্তানকে আহ্বান জানাচ্ছে বাংলাদেশের ওপর আক্রমণ করার জন্য। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিসার আলি খান কাদের মোল্লার ফাঁসিতে অত্যন্ত আপত্তিকর বক্তব্য প্রদান করেছেন। পাক-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,- “একাত্তর সালে পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করে কাদের মোল্লা দেশ-প্রেমিকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছেদ হওয়ায় পাকিস্তানিদের মনে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে আবারও ব্যাথা দেওয়া হলো এই ফাঁসির মাধ্যমে।”
এই তালিকায় পিছিয়ে নেই পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ দলের প্রধান ও সাবেক ক্রিকেট তারকা ইমরান খান। ইমরান খান, একজন মানবাধিকার কর্মীর কাছে কাদের মোল্লা সম্পর্কে শুনে তাকে ‘নির্দোষ’ হিসেবে দাবি করেছেন। তিনি দাবি করেন, ওই মানবাধিকারকর্মীই নাকি তাঁকে বলেছেন কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছিল, তা সব মিথ্যা। আর সেগুলোর ব্যাপারে ইমরান খান কিছুই জানতেন না।
এই ব্যাপারে একটু বিশ্লেষণ করা যাক; দেখা যাক বেশির ভাগ পাকিস্তানীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে কি জানে। যেখানে পাকিস্তানের পাঠ্যপুস্তকে এখন পর্যন্ত উল্লেখ আছে,- ”১৯৭১ সালে পাকিস্তান ও মুসলিম ভাইদেরকে বিভাজনের মূল কারণ ছিল ইন্ডিয়ার ষড়যন্ত্র আর শেখ মুজিব ছিল তার মূল নায়ক।” সে সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানী নাগরিকদের কাছ থেকে এই গণহত্যার খবর কিভাবে আড়াল করা হয়েছিল, এই মর্মে প্রভাবশালী পাকিস্তানী দৈনিক “দ্য ডন” এর রিপোর্ট দেখা যাক:
Soon after the military operation ‘Searchlight’ began in former East Pakistan on March 25, 1971, the uprising became the subject of discussion all over the world. Chained by censorship, West Pakistan newspapers did not give a single word to their readers about what was happening in the Eastern wing; hence only foreign news radio was heard and believed. BBC’s were the most popular broadcasts.
পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর এই নৃশংসতা যাতে কোনভাবেই আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় প্রচার হতে না পারে এজন্যও তারা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালায়। ২৫ মার্চের আগেই অধিকাংশ বিদেশী সাংবাদিককে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগে বাধ্য করা হয়। এমনকি এই রাতে যারা ঢাকায় অবস্থান করছিলেন, তাদেরকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল (বর্তমান হোটেল রূপসী বাংলা) এ অবরূদ্ধ রাখা হয়। তবুও একাধিক বিদেশী সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই রাতের রিপোর্ট লিখেন। এদের মাঝে এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস এবং সাইমন ড্রিং এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে আসলে কি ঘটছে সে ব্যাপারে বিশ্বকে জানাতে যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন।
এছাড়া, জুলফিকার আলী ভুট্টোর দৌহিত্র ফাতিমা ভুট্টো ”Songs of Blood and Sword” নামের একটা বই লিখেছেন। সেই বই নিয়ে ”দৈনিক প্রথম আলো” একটা প্রতিবেদনও ছেপেছিলো। বইটিতে লেখা হয়েছে,- ‘পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যুদ্ধের কৌশল হিসেবে চার লাখ নারীকে ধর্ষণ করেছে। বাঙালি জনগোষ্ঠীকে শায়েস্তা করা ও দুর্দশায় ফেলার অংশ হিসেবেই পাকিস্তান সৈনিক বাহিনী এ কাজ করেছে। সেই বইতে ”সুসান ব্রাউনমিলার”কে কোট করা হয়েছে, সঙ্গে এটাও লেখা হয়েছে যে ফাতিমা তার পিতামহ জুলফিকার আলী ভুট্টোকে দেখেছেন, বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য সিন্ধুর জেনারেল গুল হাসানকে খুব এক চোট ধমকে ছিলেন। ফাতিমা তার পিতামহকে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে মহাপুরুষ বানিয়ে দেননি। ফাতিমা আরও লিখেছেন, মুজিব চেয়েছিলেন তাঁর দল এককভাবে সংবিধান রচনা করবে এবং তাঁকে সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়া হবে। সেনাবাহিনী যদিও ভুট্টোকে আওয়ামী লীগের সমপরিমাণ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু তাতে তিনি (ভুট্টো) আশ্বস্ত হতে পারেননি। এরপর ফাতিমার বিশ্লেষণ করেছেন, সেনাবাহিনী এই দুজনকে একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে এবং যাতে শান্তিপূর্ণ কোনো সমাধান না হয় তা নিশ্চিত করেছে। তাঁর ভাষায়, ”এরপর সারা পূর্ব পাকিস্তানে দাঙ্গা ও রক্তের বন্যা বইতে লাগল।”
এবার ফিরে দেখা যাক, সমগ্র পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে কাদের মোল্লা বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া। এক দিকে যখন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চৌধুরী নিসার আলি খান আর তেহরিক-ই-ইনসাফ দলের প্রধান ও সাবেক ক্রিকেট তারকা ইমরান খান স্বাধীনতার ৪২ বছর পরেও যখন বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাদের নাক গলানোর চেষ্টা করছেন। সেই সঙ্গে গতকাল সোমবার পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নিন্দা জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাস করা হচ্ছে ঠিক তখন পাকিস্তানের পিপলস পার্টি আর এমকিউএম সংসদে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। একই সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়েছে, সেখানকার একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির শাখা সেক্যুলার ফোরামও। পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) সাংসদ আবদুল সাত্তার বাচানি পরিষদকে এ ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ না করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, ‘পুরো বিষয়টিই বাংলাদেশের একান্ত অভ্যন্তরীণ বিষয়। আমাদের উচিত হবে না একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে এ ধরনের প্রস্তাব পাস করা।’
যদিও কিছুদিন আগে ”দৈনিক প্রথম আলো”কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ইমরান খান বলেছিলেন,- বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া উচিত। তিনি দাবি করেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানী বাহিনী বাংলাদেশে অভিযান শুরুর আগে তিনি শেষ বিমানে করে ঢাকা ছেড়েছিলেন। ১৯৭১ সালে বাঙালি হত্যায় পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের নির্দেশ প্রদান প্রসঙ্গে ইমরান খান বলেন, ‘আমি নিজ কানে শুনেছি, তারা বলেছে, এই বামন ও কালোদের হত্যা কর। তাদের একটা শিক্ষা দাও।’ ইমরান খানের সাক্ষাৎকারে তিনি আরো বলেছিলেন,’৭১ থেকে শিক্ষা নেয়নি পাকিস্তান। ইমরান জানিয়েছিলেন, তিনি বিশ্বাস করেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী অপরাধীরা শাস্তি পেলে পশতুনরা আজ হয়রানির শিকার হতো না।আজ একজন মানবাধিকার কর্মীর কাছে কাদের মোল্লা সম্পর্কে শুনে তাকে ‘নির্দোষ’ হিসেবে দাবি করাটা ইমরান খানকে জেনারেল নিয়াজীর যোগ্যতম উত্তরসূরী হিসেবে বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করে। আজ ইমরান খান বলছেন,- ‘১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর “ঢাকার পতন” আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে পুরো ব্যাপারটির নিষ্পত্তিই সে সময় গণতান্ত্রিকভাবেই হওয়া উচিত ছিল।’ এর কারন হলো ইমারান খানের চাচা জেনারেল নিয়াজী। তাই আজ চাচা জেনারেল নিয়াজীর পরিচালিত সেনাহত্যা যজ্ঞের সহযোগী কাদের মোল্লাকে নির্দোষ দাবী করে নিজেকে উন্মোচিত করেছেন ইমরান খান। তার এই বক্তব্যের এবং কাদের মোল্লাকে সমর্থন জানানোর মানে এই দাঁড়ায়, ৭১ এর হত্যাযজ্ঞ তার চোখে মানবতা বিরোধী অপরাধই ছিলোনা।
আন্তর্জাতিক বিশ্বের চোখে পাকিস্তান আজ একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র। তারা তাদের নিজের দেশের মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। বছরে আনুমানিক গড়ানুপাতে ৫ হাজারের মতো মানুষ আত্মঘাতি বোমা হামলায় মারা যাচ্ছে। পাকিস্তান সমগ্র বিশ্বের চোখে একটি তালেবানী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত। জুলফিকার আলী ভুট্টো, বেনজীর ভুট্টো, মোহাম্মদ জিয়াউল হকের মতো রাষ্ট্রপ্রধানদের আততায়ীর আক্রমণে মৃত্যু বারে বারে ইতিহাসের পূণরাবৃত্তি করে। তারা মুখে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিলেও এখন পর্যন্ত একটি সরকারও সামরিক শাসনের দখলদারীত্ব ছাড়া স্থাপন করতে পারেনি। ২০০১ টুইনটাওয়ারের ঘটনা থেকে শুরু করে আজমল কাসব ও তার বাহিনীর ভারতের তাজমহল হোটেলের উপর আক্রমণ পাকিস্তানের হিংস্রতাই প্রমাণ করে। যে আমেরিকা এক সময় পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়েছিলো, তাদের দেশেই সবচেয়ে সন্দেহভাজন নাগরিকদের দলে পাকিস্তানীরা। অসংখ্য হলিউড সিনেমা বা সিরিয়ালের দিকে তাকালে দেখা যায়, ইসলামিক রাষ্ট্রের সন্ত্রাসী হিসেবে এক পাকিস্তানী নাগরিকই সেটির ভিলেন চরিত্রের ভূমিকায় রয়েছে। যদিও পাকিস্তানের এই পরিস্থিতির জন্য আমেরিকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি অনস্বীকার্য।
১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে হাত মিলিয়েছিল কিছু সুবিধাবাদি দেশদ্রোহী রাজাকার, আলবদর, আল শামস আর বিহারীদের একটি বিশাল অংশ। এই বিশেষ বাহিনীর একজন ছিল কাদের মোল্লা। সেই কাদের মোল্লার ফাঁসিতে পাকিস্তানের এমন ভূমিকায় বাংলাদেশীরা অবাক হয় না।নিজেদের কৃতকর্মকে বৈধতা দিতেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান। এই পাকিস্তান এক সময় আমাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছিলো। এমনকি গত ৪২ বছরে ৭১ এর গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্যও বাংলাদেশের কাছে রাষ্ট্রীয় ভাবে ক্ষমা চায়নি তাদের সরকার। বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামাতের মতো একটি সংগঠনকে সমর্থন করে বার বার একটি কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় পাকিস্তান, আর তা হলো বাংলাদেশের কাছে নিজেদের পরাজয়কে আজও তারা মেনে নিতে পারেনি। তাই কাদের মোল্লার ফাঁসি তাদের জন্য আরেকটি পরাজয় মাত্র। পরিশেষে ইমরান খানের এই বক্তব্য বিপরীতে স্যার হুমায়ুন আজাদের করা একটি উক্তি মনে পড়ে যায়,- ”পাকিস্তানীদের আমি অবিশ্বাস করি, যখন তারা হাতে গোলাপ নিয়ে আসে- এমন কী তখনো।”
ফারজানা কবীর খান (স্নিগ্ধা)
তথ্যসূত্রঃ
১) উইকিপিডিয়া বাংলা
২) ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস স্ট্র্যাটেজি ফোরাম
৩) বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের অনলাইন আর্কাইভ
৪) বিভিন্ন জাতীয় এবং বিদেশী পত্রিকার অনলাইন আর্কাইভ
৫)
৬) Songs of Blood and Sword -- ফাতিমা ভুট্টো
৭)
http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=38594
- Biplob Rahman | ২১ ডিসেম্বর ২০১৩ ১১:০৮582655
- অল কান্ট্রিজ এক্সসেপ্ট পাকিস্তান
লিখেছেন: ফরিদ আহমেদ
বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশ কোনটি, এই প্রশ্ন করলে বেশির ভাগ লোকই কোনো রকমের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই বলে দেবেন যে ভারত। যাঁরা একটু বেশি খোঁজ খবর রাখেন, মুচকি হেসে বলবেন, ভুটান। হ্যাঁ, এই দ্বিতীয় অংশরাই সঠিক। ভুটানই বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশ। যেদিন বাংলাদেশ-ভারত মিত্রবাহিনী গঠিত হয়, ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, সেই ৩রা ডিসেম্বর ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ভারতই যে ভুটানকে দিয়ে এটা করিয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অজানা খাবার অন্য কাউকে দিয়ে আগে খাইয়ে যেমন স্বাদ পরীক্ষা করা হয়, ভারতও ভুটানকে দিয়ে এই জায়গাটা পরীক্ষা করিয়ে নিয়েছিল।
ভারত করাক বা ভুটান নিজের গরজেই করুক, ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশ, এটাই প্রতিষ্ঠিত সত্য।
এখন আমি যদি বলি যে, এই তথ্যও সঠিক নয়। ভারত বা ভুটান নয়, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী দেশটি হচ্ছে ভিন্নতর একটি দেশ, আমাকে পাগল ঠাওড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে ষোল আনাই। কিন্তু, এটাই আসল সত্যি। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশ ভারত বা ভুটান কেউ-ই নয়। যে দেশটি এই স্বীকৃতি দিয়েছিল, তার নামটি কল্পনায় আনতেও কষ্ট হবে আমাদের।
বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতিদানকারী দেশটির নাম হচ্ছে ইজরায়েল। এটি নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর একটা তথ্য। তবে, আরো বিস্ময়কর তথ্য হচ্ছে ইজরায়েল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে একবার নয়, দুই দুই বার।
ইজরায়েলের প্রথম স্বীকৃতি আসে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরে। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কাছে একাত্তর সালের এপ্রিল মাসের আটাশ তারিখে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির চিঠি পাঠায় তারা। স্বীকৃতির সাথে সাথে ছিল যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য সমরাস্ত্র দেবার অঙ্গীকার। বাংলাদেশ সরকার সেই স্বীকৃতি গ্রহণ করে নি। সমরাস্ত্র সাহায্যের প্রস্তাবও প্রত্যাখান করে।
ইজরায়েলের বদলে ভারতের কাছ থেকে এই স্বীকৃতি প্রথম আসার কথা ছিল। কারণ, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই উদার হস্তে ভারত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে যে, এত সুযোগ থাকার পরেও ভারত কেন বাংলাদেশকে শুরুতেই স্বীকৃতি দেয় নি? কেন ভারতকে অপেক্ষা করতে হলো ডিসেম্বর পর্যন্ত? বরুণ রায় ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে লেখা প্রবন্ধ ‘কেন ভারত ঠিক এই মুহুর্তে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল?’-তে এ প্রসঙ্গে বলেনঃ
“প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী গত ২৬শে জুলাই যখন বাংলাদেশের ব্যাপার নিয়ে সংসদের বিরোধী দলের নেতাদের নিয়ে বৈঠকে মিলিত হন, তখন তাঁরা একবাক্যে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দেবার জন্যে তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন।
তার উত্তরে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, স্বীকৃতির প্রশ্নে ভারত সরকার তাঁদের মন খোলা রেখেছেন। যে মুহুর্তে বোঝা যাবে স্বীকৃতি দিলে বাংলাদেশের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয় স্বার্থেরও সাহায্য হবে, সেই মুহুর্তেই বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।
সেই বিশেষ মুহুর্ত হঠাৎ এই সময় কেন দেখা দিল? ভারত সরকার তাঁদের সিদ্ধান্তের জন্য ডিসেম্বরের ছয় তারিখটিকে কেন বেছে নিলেন? এই সিদ্ধান্ত কেন আরও আগে নেওয়া হলো না, বিশেষত যখন স্বীকৃতি দেবার পক্ষে একাধিক সুযোগ নয়াদিল্লীর সামনে হাজির হয়েছিল, এবং যখন স্বীকৃতি দেবার জন্য দেশের মানুষ দীর্ঘকাল যাবত দাবী জানিয়ে আসছিল?
প্রথম সুযোগ এসেছিল গত মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে, যখন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের সর্বাত্মক আক্রমণের জবাবে বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করেছিল শেখ মুজিবর রহমানকে রাষ্ট্রপ্রধান করে। ঐ সরকারের কোনো আনুষ্ঠানিক ক্যাবিনেট তখনও ছিল না, কিন্তু কার্যত গোটা বাংলাদেশ ছিল মুক্তি সংগ্রামীদের দখলে। নয়াদিল্লী ইচ্ছে করলে তারই ভিত্তিতে স্বীকৃতি দিতে পারত। পিকিং সরকার আরও কম ভিত্তিতে কম্বোডিয়ার নরোদম সিহানুকের নির্বাচিত সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।
কিন্তু ভারত ঐ প্রলোভন গ্রহণ করে নি।
দ্বিতীয়বার সুযোগ এসেছিল যখন গত ১৭ই এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তের কাছে বাংলাদেশের একটি গ্রামে অস্থায়ী সরকারের নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে শপথ গ্রহণ করেন। ঐ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিশ্বের দেশগুলির কাছে স্বীকৃতির জন্য অনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন জানিয়েছিলেন এবং ঐ আবেদনের সূত্র ধরে ভারত সরকারের পক্ষে স্বীকৃতি দেওয়ার কোনো বাধা ছিল না। কেন না তারই চারদন আগে রায় বেরিলীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, বাংলাদেশ সরকার যদি আবেদন জানান তাহলে স্বীকৃতির প্রশ্নটি বিবেচনা করা হবে।
কিন্তু তখনও ভারত কোনো সিদ্ধান্ত নেয় নি।
তৃতীয় একটা সুযোগ হাজির হয়েছিল গত ৯ই আগষ্ট ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে মৈত্রী ও পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরে। ততদিনে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনো মীমাংসা আলোচনায় বসতে রাজি নন। আর এটাও স্পষ্ট ছিল যে, ভারতের মনোভাব যথেষ্ট কঠিন হয়ে উঠেছে। চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পরেই স্বীকৃতির মাধ্যমে ঐ মনোভাব প্রকাশ পেলে অবাক হবার কিছু থাকত না।
কিন্তু নয়াদিল্লী তখনও লাফিয়ে পড়ে নি।
এ ছাড়া জনমতের চাপেরও সুযোগ তো ছিলই। বাংলাদেশের সংগ্রামে সমবেদনা ও একাত্মবোধ প্রকাশ করে গত ৩১শে মার্চ সংসদে সর্ববাদীস্মমত প্রস্তাব গৃহীত হবার পর থেকে গণ-অভিমতের সবগুলি মাধ্যম থেকে স্বীকৃতি দেবার জন্যে সরকারের কাছে প্রবল দাবী জানানো হয়েছে। চাপ ছিল সংসদের শ্রীমতী গান্ধীর নিজের দলের, দুয়েকটি ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক দলের, বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভার, সংবাদপত্রের। জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য বিনোবা ভাবের ও এম সি চাগলার মতো শ্রদ্ধেয়, বিচক্ষণ জননেতারাও ভারতকে সাহস সঞ্চয় করে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। যদি প্রকৃত জাতীয় দাবী বলতে কোনো একটি বিষয় থাকত তবে তা ছিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার দাবী। জনমতের এই প্রবল চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নয়াদিল্লী এই দীর্ঘ আট মাসের মধ্যে আরো আগে যে কোনো সময় স্বীকৃতি দিতে পারত।
কিন্তু দেয় নি।
এর কারণ কি? সাহসের অভাব? দ্বিধা? ঝুঁকি নেবার অনিচ্ছা? বৃহৎ শক্তির ভয়? স্বীকৃতির সমস্ত দাবীকেই ভারত সরকার এতবার এতভাবে এড়িয়ে গেছেন, এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যেভাবে স্বীকৃতির ব্যাপারে তাঁকে চাপ না দেবার জন্য একাধিকবার অনুরোধ জানিয়েছেন যে, ভারতের বাংলাদেশ নীতি সম্পর্কে জনমনে এই প্রশ্নগুলি দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল।
কিন্তু এর কোনোটাই সত্যি ছিল না, কেন না প্রধানমন্ত্রী একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসরণ করে চলেছিলেন, এবং এতগুলি কথায় না বললেও বিভিন্ন সময়ে তিনি এ সম্পর্কে যথেষ্ট ইঙ্গিতও করেছিলেন, যদিও সে সময় তার তাৎপর্য গরম কথার আড়ালে হারিয়ে গিয়েছিল।” (৭১-এর যুদ্ধে পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ – দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়)
বরুণ রায়ের দীর্ঘ বক্তব্য থেকে বোঝা গেল যে, ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার বিষয়ে যে, দীর্ঘসূত্রিতা করেছে তার মূলে ছিল সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা, ভারতের জাতীয় স্বার্থ দেখা এবং একই সময়ে বাংলাদেশের স্বার্থ যাতে ক্ষুন্ন না হয়, সেই বিষয়টাও নিশ্চিত করা। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার বিষয়ে ভারত তার নিজস্ব স্বার্থ দেখবে, এতে দোষণীয় কিছু নেই।
কিন্তু ইজরায়েল এত কিছু চিন্তা-ভাবনা করে আসে নি। বাংলাদেশ তাদের থেকে ভৌগলিকভাবে এত দূরে যে, কোনো স্বার্থে আসার সুযোগও বাংলাদেশের ছিল না। তারপরেও তারা সবার আগে বাংলাদশকে স্বীকৃতি দেবার পত্র পাঠিয়েছে। এর মূল কারণ আবেগগত। নেপালে নিযুক্ত ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত বলেন, “ইজরায়েল বাংলাদেশের জনগনের সংগ্রামের সাথে তাদের মিল খুজে পেয়েছিল।”
দ্বিতীয়বার তারা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয় বাহাত্তর সালের ফেব্রুয়ারী মাসের চার তারিখে। মন্ত্রীপরিষদের নিয়মিত সভার অপেক্ষা না করে সব মন্ত্রীর সাথে টেলিফোনে আলাপ করে, তাদের সম্মতি নিয়ে ইজরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদকে তারবার্তা পাঠান।
Israel Recognizes Bangladesh
February 7, 1972
JERUSALEM (Feb. 6)
Israel has officially recognized the new state of Bangladesh. The announcement said that Foreign Minister Abba Eban informed Bangladesh Foreign Minister Abdus Samad Azad of the recognition in a cable Friday. The recognition decision was taken after telephone consultations with all members of the Cabinet Friday instead of waiting for today’s regular Cabinet meeting.
Source: http://www.jta.org/1972/02/07/archive/israel-recognizes-bangladesh
বাংলাদেশ সরকার ইজরায়েলের এই সদিচ্ছার কোনো উত্তর দেবারও প্রয়োজন বোধ করে নি। কারণটা কী? ইজরায়েল মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের মুসলিম ভাইদের ধরে ধরে আচ্ছামত পিটুনি দেয়। ওদের পিটুনি আমাদের গায়ে এসেও সজোরে লাগে। মুসলমান-মুসলমানতো নাকি ভাই ভাই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই ভাই-রা আবার বাংলাদেশের জন্ম মন থেকে মেনে নিতে পারে নি। রীতিমত গোস্যা করেছিল তারা হুট করে বাংলাদেশ জন্মে যাওয়ায়। কেউ-ই স্বীকৃতি দিতে রাজি ছিল না তখন। অনেক দেন দেরবার করে, বহু বছর সাধ্য সাধনা করে তাদের গোস্যা ভাঙাতে হয়েছে বাংলাদেশকে।
তারা এখন আমাদের মুসলিম উম্মাহ, মুসলিম ভ্রাতৃত্বের অংশ। আর ইজরায়েল? শত্রু রাষ্ট্র!
বাংলাদেশের পাসপোর্টে পরিষ্কার করে লেখা থাকে একটা বাক্য, ALL COUNTRIES OF THE WORLD EXCEPT ISRAEL।
অথচ মিশর, তুরস্কের মতো মধ্যপ্রাচ্যের অনেক মুসলিম দেশেরই কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে ইজরায়েলের সাথে। আমরা পোপের চেয়েও বড় খৃস্টান।
দূরদেশের মুসলমান ভাইদের জন্য আমাদের দরদ কতখানি ভাবেন। এইবার আসেন ঘরের খবর নেই। যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ করতে হয়েছে নয় মাস ধরে, যে পাকিস্তান আমাদের ত্রিশ লাখ মানুষকে মেরেছে কুকুর বিড়ালের মত, যে পাকিস্তান আমাদের দুই লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করেছে, সেই পাকিস্তান আমাদের প্রাণের বন্ধু। আমরা তাদের আদরের ছোট ভাই। ছোট ভাই বলেই হয়তো সব ব্যাপারে ভাইয়াগিরি ফলাতে আসে তারা। এই যেমন কাদের মোল্লার মতো একজন নৃশংস ঘাতককে বিচার করে আমরা ফাঁসিতে ঝোলাতেই মাতম পড়ে গেছে তাদের দেশে। আমরা নাকি ফেরেস্তার মতো একজন মানুষকে জুডিসিয়াল কিলিং করেছি। কেউ গালাগাল করছে আমাদের, কেউ আমাদের আক্রমণ করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে, পার্লামেন্টে আমাদের জন্য নিন্দা প্রস্তাব আনছে।
ওদের সবচেয়ে প্রগতিশীল অংশ, যাদেরকে প্রথম আলো প্রতিনিয়ত প্রমোট করে চলেছে আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলে, সেই তাদের প্রতিনিধি হামিদ মীরও ইনিয়ে বিনিয়ে বলছে যে, কাদের মোল্লাকে ফাঁসি দিয়ে আমরা ভুল করেছি। আমাদের সেই ভুল স্বীকার করতে হবে। সবচেয়ে প্রগতিশীলদেরই যদি এই দুর্গতি হয়, তবে বাকিদের অবস্থা কী তা সহজেই অনুমেয়।
আমি দেশে থাকা অবস্থায় পাকিস্তানিদের সাথে পরিচিত হবার কোনো সুযোগ পাই নি। বিদেশে আসার পরে পড়ালেখা, কাজ বা বাইরে বের হবার কারণে প্রচুর পাকিস্তানির সাথে পরিচিত হবার সুযোগ হয়েছে। আগে এদের প্রতি রাগ ছিল একাত্তরের কারণে। এখন এদের প্রচুর লোককে দেখার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে দ্বিধা নেই যে, পৃথিবীতে খচ্চর লোক দিয়ে পরিপূর্ণ কোনো জাতি যদি থেকে থাকে, তবে তা নিঃসন্দেহে এই পাকিস্তানিরা। হেন কোনো অপকর্ম নেই, যা এরা করতে পারে না। আমি মাঝে মাঝে খুব বিস্মিত হয়ে ভাবি যে, এই অদ্ভুত অসৎ, মিথ্যাবাদী, নাক উঁচু, প্রতারকে পরিপূর্ণ একটা জাতির সাথে এক দেশ হিসাবে আমরা তেইশ বছর ছিলাম কী করে?
এই ইতর দেশটার জন্য কেন আমাদের পাসপোর্টে লেখা নেই ALL COUNTRIES OF THE WORLD EXCEPT PAKISTAN?
লেখা নেই, তাতে কী? এখন সময় এসেছে এই কথাটা লেখার।
http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=38588
- Biplob Rahman | ২২ ডিসেম্বর ২০১৩ ১৫:১৮582656
- Ragib Hasan
বাংলাদেশের ইতিহাসটা কেমন হতে পারতো, যদি মুক্তিযুদ্ধের শেষ প্রহরে রাজাকার-আল বদরের কিলিং স্কোয়াডের হাতে আমাদের সেরা বুদ্ধিজীবীরা শহীদ না হতেন? এই প্রশ্নটা আমাকে প্রায়ই তাড়া করে ফিরে। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের দেশের প্রচুর মানুষ শহীদ হওয়ার পাশাপাশি চিন্তা চেতনার এই ক্ষতিটা বিশাল ও দীর্ঘমেয়াদী। শহীদুল্লাহ কায়সার, মুনীর চৌধুরী, থেকে শুরু করে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী - এই সব অসাধারণ প্রতিভাদের জন্ম প্রতি বছরে, প্রতি দশকে হয় না, অনেক অনেক দিন পর পর হয়।
বাংলা উইকিপিডিয়াতে শহীদ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর জীবনীটা যোগ করেছিলাম। তাঁর মেধার কথা লিখতে গিয়ে প্রতিটি বাক্যেই হয়েছিলাম অভিভূত - নোয়াখালীর গ্রামের একটি স্কুল থেকে অবিভক্ত বাংলায় পুরো প্রদেশের মাঝে মেট্রিক পরীক্ষায় চতুর্থ হন, আর ইন্টারমিডিয়েটে পুরো বাংলায় হন প্রথম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ১০০ বছরের সেরা ছাত্র হিসাবে ১৯৫৮ সালে তিনি নির্বাচিত হন।
আমাদের দূর্ভাগ্য, জামাতের প্রতিষ্ঠিত আল বদর কিলিং স্কোয়াডের হাতে এরকম অসামান্য প্রতিভাদের শহীদ হতে হয়েছিলো। জাতি হিসাবে আমরা রাতারাতি পিছিয়ে গেছিলাম বহু বছর। সে দৈন্য কাটেনি আমাদের, টক-শোতে কাঁপাকাপি গলায় ঝগড়া করতে পারা প্রচুর রাজা-উজির মারা "বুদ্ধি"-জীবীর উদ্ভব হলেও আরেকজন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীকে পাইনি, আরেকজন আলতাফ মাহমুদকে পাইনি।
শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে আমাদের সেই সূর্যসন্তানদের প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম। আর তার পাশাপাশি ইংল্যান্ডে কিংবা নিউইয়র্কে পালিয়ে থাকা আল-বদরের সেই খুনিদের প্রতি রইল ঘৃণা।
শহীদ স্মৃতি অমর হোক।
#শহীদবুদ্ধিজীবীদিবস #১৯৭১ #মুক্তিযুদ্ধ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152036037358670&set=a.10150212635053670.326981.513618669&type=1
- Biplob Rahman | ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ ১২:৩৪582657
- অমি রহমান পিয়াল
মুক্তিযুদ্ধে গোপন তৎপরতা (১): বুদ্ধিজীবী হত্যায় মার্কিন দায়
ডিসেম্বর ১১, ২০১৩
ভূমিকা:
গোপন তৎপরতার আদ্যোপান্তই ‘গোপনীয়’ সিলগালায় মোড়কবন্দী থাকে। এটাই নিয়ম। মাঝেমাঝে ফিসফাস কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছ থেকে কিছু তথ্য বেরোয় বটে, কিন্তু তা দিয়ে এসব তৎপরতায় কাউকে দায়ী করা খুব মুশকিল।
আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ভীষণ রকম সত্যি। এখানে যুযুধান দুই পক্ষ পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর এবং স্বাধীনতাকামী মুক্তিবাহিনী। মুক্তিযোদ্ধাদের পেছনে আশীর্বাদ হয়ে ছিল ভারত ও রাশিয়া; তেমনি পাকিস্তানিদের পক্ষে আমেরিকা ও চীন। প্রতিবেশি ভারত সরাসরি লড়াইয়ে নেমেছে বাংলাদেশের পক্ষে। অন্যদিকে তিন পরাশক্তির লড়াইটা প্রকাশ্যে কূটনৈতিক হলেও আড়ালে তার ছিল ভিন্ন রূপ।
এর মধ্যে আলাদা করে বলতেই হয় মার্কিন সরকারের কথা। গোপনীয় প্রচুর সরকারি দলিল অবমুক্ত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধে তাদের তৎপরতার নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে মার্কিন প্রশাসনের মধ্যেই দুটো ধারা ছিল যারা সে দেশের জনগণের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাংলাদেশের পক্ষ নিয়েছেন। নিক্সন-কিসিঞ্জারের যাবতীয় দুষ্টকীর্তি তাদের মাধ্যমেই হাতে পান জ্যাক অ্যান্ডারসনের মতো সাংবাদিক এবং সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির মতো রাজনীতিবিদরা। এখনকার ‘টক অব দ্য ওয়ার্ল্ড’ উইকিলিকসের প্রাথমিক উদাহরণটাও তখনকারই গড়া।
এসব দলিলের মধ্য দিয়েই আমরা আস্তে আস্তে একটি ছবি পাই, ঝাপসা হলেও যার অবয়বটা বুঝে নিতে খুব একটা কষ্ট হয় না। সময়টা শীতল যুদ্ধের উত্তুঙ্গকাল। কমিউনিস্ট জুজু দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তার সম্প্রসারণবাদী নীতি চালিয়ে যাচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়াজুড়ে। তাদের প্রতিপক্ষ বড় আকারে সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনও। ইন্দোনেশিয়ায় মার্কিনপন্থী জননিরাপত্তা আইনের বাস্তবায়নে নিহত ১০ লাখেরও বেশি মাওবাদী কমিউনিস্ট। নিকারাগুয়া, ব্রাজিল, উরুগুয়েতে সিআইএ তৈরি করেছে গোপন ঘাতক দল। ভিয়েতনামে শুরু হয়ে গেছে ‘ফিনিক্স প্রোগ্রাম’– এখানেও সার কথা একটাই– যে কোনো মূল্যে কমিউনিস্ট ঠেকানো।
সোভিয়েত তাদের একমাত্র প্রতিপক্ষ হলেও বাকিদের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে নীতি বদলে গেছে নিক্সন প্রশাসনের। যেমন বলা যায় চীনের বিরুদ্ধে তিব্বতে যে তৎপরতা তারা চালাত তাতে মাধ্যম ছিল ভারত। তিব্বতিদের স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স সিআই-এর রূপরেখাতেই তৈরি। বাংলাদেশের কুর্মিটোলা বিমানবন্দর ব্যবহার করে তিব্বতি এজেন্টদের বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্টে পাঠাত তারা। মুক্তিযুদ্ধের সময় এই চীনকেই হঠাৎ মিত্র হিসেবে প্রয়োজন মনে হল যুক্তরাষ্ট্রের। দূতিয়ালির কাজটা করলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। বিনিময়ে তার সাত খুন মাফ অবস্থা।
অস্ত্র সরবরাহে সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তা অমান্য করেছে নিক্সন প্রশাসন গোপনে। তাদের একমাত্র অজুহাত ভারত হচ্ছে সোভিয়েত-ঘেঁষা। আর চীন কেন! একটি জবাব হতে পারে ভিয়েতনামে মার্কিনিদের লড়াইয়ে চীনাদের কোনোভাবে নিরপেক্ষ রাখা, বিনিময়ে তাইওয়ান ও হংকং প্রশ্নে নিরব থাকার প্রতিশ্রুতি।
দলিলের সংখ্যা ও মেয়াদকাল (অতীত অর্থে) যত বেড়েছে, ততই আসলে বিভ্রান্তির উপকরণও বেড়েছে। অংকটা জটিল এক সমীকরণে রূপ নিয়েছে। ভাবটা এমন যে মার্কিন সরকার কয়েকটা দলকে ভাগ করে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়েছে যার একটার সঙ্গে আরেকটা সংঘাতপূর্ণ। যে এগিয়ে থাকবে তাকে পরিচর্যা করে বাকিদের নিজেদের মতো চলতে দেওয়া! এই গবেষণায় আমরা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্ম হওয়ার পর থেকে মার্কিন নীতি ও দলিলপত্র নিয়ে কাজ করেছি। বোঝার চেষ্টা করেছি এর ধারাবাহিকতা। আবিষ্কার করেছি একটি প্যাটার্ন।
তাই ১৯৫১ কিংবা ১৯৫৩ সালে গৃহীত নীতির খানিকটা যে ১৯৭১ সালেও আরোপিত হয়েছে– মাথা খাটিয়ে তা উদঘাটন করা গেছে। এজন্য আমাদের অবশ্য ঘুরে আসতে হয়েছে ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম থেকে। বুঝতে হয়েছে কাউন্টার ইনসার্জেন্সি অর্থাৎ সরকারবিরোধী তৎপরতা ঠেকানোর জন্য মার্কিনিরা কী ধরনের উপদেশ, মদত ও সহযোগিতা দিয়েছে। এখানেও সেই কথিত প্যাটার্নের অনেকটাই মিলে গেছে।
হাইপোথিসিস থেকে সত্যিকার থিসিসে উত্তীর্ণ হওয়ার মতো খুব বেশি উপকরণ আমাদের হাতে আসলেই নেই। কারণটা আগেই বলা হয়েছে– কিছু দলিলের গোপনীয়তা যা সংগ্রহ করা অসম্ভব। কিছু নামের, কিছু কাজের একেবারেই হাপিশ হয়ে যাওয়া। তারপরও সম্ভাব্য সব জায়গায় ঢুঁ মারা হয়েছে, ঢুঁ মারা হবে। এখন পর্যন্ত যেটুকু উদঘাটন করা গেছে, তাতে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘের (বর্তমানে ইসলামী ছাত্র শিবির) সদস্যদের সম্পৃক্ততা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের ঘাতক হিসেবে দায়িত্ব পালনের হুকুমদাতা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থা এবং তখনকার গভর্নরের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী।
কিন্তু পরিকল্পিত উপায়ে এই বিদ্রোহ দমনের পরিকল্পনাটা তাদের কাছে পেশ করেছিল আসলে সিআইএ। পাকিস্তানে কমিউনিস্টবিরোধী তৎপরতা চালানোর জন্য ধর্মোন্মাদ দলগুলো নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা শুরুতেই নিয়েছিল তারা। তালিকায় জামায়াতে ইসলামী বরাবরই প্রায়োরিটি পেয়েছে, যেমন পেয়েছে তাদের মুখপাত্র হিসেবে থাকা দৈনিক ‘সংগ্রাম’ নামের পত্রিকাটি। আমরা জেনেছি, যে আনসার বাহিনী বিলুপ্ত করে রাজাকার বাহিনীর সৃষ্টি; তার সম্পর্কে সিআইএ বিশদ খোঁজ-খবর নিয়ে রেখেছিল অনেক আগেই।
আলোচ্য নিবন্ধে ধারাবাহিকভাবে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তার মধ্যে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ও পরবর্তী সময়কালে বিভিন্ন মাধ্যমে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যায় আলোচিত ও অভিযুক্ত সিআইএ এজেন্টদের নাম, তৎপরতা ও তার প্রমাণ যোগাড়ের চেষ্টা। দেশভাগের পর থেকে মার্কিন নানা গোপন নীতির দলিল বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধকালে কিছু তৎপরতার সঙ্গে তার মিল খোঁজার চেষ্টা করেছি আমরা। সবশেষে একটি সার্বিক মূল্যায়নের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করব দুয়ে দুয়ে চার মেলানোর। কিংবা তার কাছাকাছি যাওয়ার।
বুদ্ধিজীবী হত্যার সময়কাল ও যে হত্যাকাণ্ডটি অল্পের জন্য ঘটেনি
প্রথমেই একটি ব্যাপার পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। জাতীয়ভাবে ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস আমরা পালন করি সত্যি, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের গোটা সময়কাল জুড়েই হত্যার শিকার হতে হয়েছে বুদ্ধিজীবীদের। ডিসেম্বরের প্রথম দুই সপ্তাহজুড়ে যা ঘটেছে, তা ছিল এক ধরনের ফিনিশিং টাচের মতো। পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যাওয়ার পর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যখন ঢাকার দিকে পালিয়ে আসছিল পাকিস্তানি সেনারা, তার আগে তারা যে কাজগুলো সেরে আসার ওপর জোর দিচ্ছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল সংশ্লিষ্ট এলাকার বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা। ঢাকাতেও ১৬ ডিসেম্বরের আগের কদিন ধরে রাও ফরমান আলীর নির্দেশে বিভিন্ন সরকারি দলিল ও ব্যাংক নোট পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে; পাশাপাশি মাটিলেপা গাড়ি করে হাতে তালিকা নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের দুয়ারে হানা দিচ্ছিল আলবদর ঘাতকরা।
বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছিল ২৫ মার্চ রাতে গণহত্যা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে। ‘অপারেশন সার্চলাইট’-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাশাপাশি তালিকা ধরে মারা হয় কয়েকজন শিক্ষককে। ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, ড. ফজলুর রহমান খান, এ আর কে খাদেম, ড. আবদুল মোক্তাদির, শরাফত আলী, অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, এম সাদত আলী এবং এম এন মনিরুজ্জামান ছিলেন সে রাতে নিহতদের তালিকায়। (১)
এখানে একটা মিসফায়ারের ঘটনাও ঘটেছে বলে জানিয়েছেন সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী। তাঁর ভাষায়:
‘‘পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে জামায়াতিরা স্বাধীনতার সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের যে নামের তালিকা ধরিয়ে দেয়, তাতে নাম ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের। হানাদাররা ভুল করে পরিসংখ্যানের অধ্যাপক মনিরুজ্জামানকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গিয়ে হত্যা করে। এই মনিরুজ্জামান ছিলেন জামাতপন্থী শিক্ষক।’’ (২)
প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষকদের কথা এলেও বুদ্ধিজীবী বলতে শুধু তাদেরই বোঝায় না। শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, আইনবিদ, শিল্পীসহ নানা পেশার মিশেলে তৈরি বুদ্ধিজীবীদের তালিকা। তবে প্রথম ধাক্কাটা গিয়েছে শিক্ষকদের উপর দিয়েই এবং দেশজুড়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় নিহত শিক্ষাবিদ ও আইনজীবীদের মোট সংখ্যা পাওয়া গেছে ৯৬৮ জন। এদের সঙ্গে যোগ হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ জন শিক্ষক। (৩)
ঘটনার প্রায় এক মাস পর, ২৬ এপ্রিল নরসিংদির কাছে বাস থেকে নামিয়ে হত্যা করা হয়েছিল শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ড. শাহাদত আলীকে। (৪)
তেমনি বিজয়ের ঠিক এক মাস আগে ১৬ নভেম্বর নটর ডেম কলেজের সামনের কালভার্টের নিচে পাওয়া যায় হাত-পা-চোখবাঁধা দুই চিকিৎসক ড. হুমায়ুন কবির ও ড. আজহারের লাশ। (৫)
মুক্তিযুদ্ধের গোটা সময়টাতেই বুদ্ধিজীবীদের গ্রেফতার ও হত্যার তথ্য মিলে মার্কিন দূতাবাসের একটি দলিলেও। সেপ্টেম্বরের শেষদিকে ইসলামাবাদ থেকে রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ড তারবার্তাটি পাঠিয়েছেন সেক্রেটারি অব স্টেট হেনরি কিসিঞ্জারকে। ‘পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের গ্রেফতার’ শিরোনামে এই টেলিগ্রামের ভাবানুবাদটি এ রকম:
১. সারমর্ম:
পূর্ব পাকিস্তানে বুদ্ধিজীবীদের ওপর দমননীতি চলছেই। যদিও সম্ভবত সীমিত মাত্রায়। অবশ্য ইঙ্গিত মিলেছে যে পাকিস্তান সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আরেকটু মৃদুনীতি গ্রহণ করা হয়েছে যা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক করে তোলায় ভূমিকা রাখবে। এ প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সম্ভাব্য সেরা নীতি হবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ অব্যাহত রাখা যাতে তারা বুদ্ধিজীবীসহ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সঙ্গে একটু ভালো আচরণ করে। সারমর্ম শেষ।
টেলিগ্রাম- প্রথম অংশ
২.
পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদদের ওপর পাকিস্তান নতুন করে কোনো দমননীতি আরোপ করেছে বলে আমরা মনে করি না। অন্যদিকে এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই যে মার্চে শুরু হওয়া সেনাবাহিনীর দমন অভিযানে প্রাথমিক লক্ষ্যের মধ্যে ছিল এই অংশটুকু। ইঙ্গিত মিলেছে সে্ই অভিযান এখনও চলছে, তবে আগের মতো ঢালাওভাবে নয়, বরং সীমিত আকারে এবং বেছে বেছে।
৩.
আপনার (স্টেট) পাঠানো টেলিগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব অধ্যাপককে গ্রেফতারের কথা বলা হয়েছে, তার সম্পূরক তথ্য হিসেবে ঢাকার কনসাল জেনারেল (স্পিভাক) সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার বয়ান দিয়েছেন:
ক) পূর্ব পাকিস্তানের বিশিষ্ট আইনজীবী, পণ্ডিত ও লেখক কামরুদ্দিন আহমেদকে ৬ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার একদিন পরই। তবে গ্রেফতারের নির্দেশটি হয়তো ক্ষমা ঘোষণার আগেই অনুমোদিত হয়েছিল।
খ) আগস্টের মধ্যভাগ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১৭ জন ছাত্র-কর্মচারী ও শিক্ষককে গ্রেফতার নয়তো সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার সমন জারি করা হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন বাংলা একাডেমির সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা সরদার ফজলুল করিম এবং চট্টগ্রামের ছাত্রনেতা।
http://www.scribd.com/doc/46430904/‘‘বুদ্ধিজীবী-হত্যার-দলিল-১”
৪.
বেশিরভাগ প্রমাণাদি বলছে, বুদ্ধিজীবীদের এই ক্রমাগত হেনস্থার সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের বর্তমান গৃহীত নীতির কোনো সম্পর্ক নেই। বরং উল্টোটাই, বিশেষ করে ৫ সেপ্টেম্বর ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর পদ থেকে টিক্কা খানকে সরিয়ে ডক্টর মালিককে নিয়োগ এবং ১৪ সেপ্টেম্বর মালিকের বক্তৃতায় তার আপোষকামী সুর– সব মিলিয়ে ইঙ্গিত দিচ্ছে পাকিস্তান সরকারের উচ্চপর্যায় পূর্ব পাকিস্তানে দমননীতির বদলে এখন সমঝোতার পথে এগুচ্ছে।
সমস্যা হচ্ছে তাদের মনোভাবকে মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ কিছু সেনা ইউনিট ও কর্মকর্তা, পুলিশ ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুবাদ করার ক্ষেত্রে। মার্চের পর থেকে যা ঘটছে তার আলোকে অত্যন্ত সুসংগঠিত প্রশাসনিক অবকাঠামোর জন্যও ব্যাপারটা ঘটতে যথেষ্ট সময় লাগবে। আপনার বার্তার জবাবে বড়জোর এটাই বলা যায় যে এখন পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীদের ওপর যে নিপীড়ন চলছে, পাকিস্তান সরকারের নতুন নীতির প্রেক্ষিতে পরিস্থিতি আগামীতে আরেকটু ভালো হবে বলে আশা করা যায়।
৫.
বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের মনোভাব কী হবে সে ব্যাপারে জানাই যে, গত কয়েক মাসে পাকিস্তান সরকারের শীর্ষমহলে বেশ কয়েক বারই সাধারণ এবং বিশেষ সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ হিন্দু) ওপর সরকারি দমননীতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমাদের। গত ১৩ সেপ্টেম্বর ঢাকায় এক আলোচনায় ডিসিএম (ডেপুটি চিফ অব মিশন) সুনির্দিষ্টভাবে সাম্প্রতিক সময়ে গ্রেফতার হওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিষয়টি তুলেছিলেন মেজর জেনারেল ফরমান আলী (গভর্নর মালিকের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার) এবং মেজর জেনারেল রহিম খানের (পূর্ব পাকিস্তানের উপ সামরিক আইন প্রশাসক) কাছে। অনুমান করছি আমাদের মনোভাব কর্তৃপক্ষের কাছে পরিষ্কার। সবচেয়ে ভালো হয় আমরা যদি পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখি যাতে পূর্ব পাকিস্তানের সব ধরনের মানুষের সঙ্গেই আরেকটু সহনশীল আচরণ তারা করে।
টেলিগ্রাম- দ্বিতীয় অংশ
টেলিগ্রাম- দ্বিতীয় অংশ
৬.
ডক্টর আবদুস সাত্তারের ঘটনা পূর্ব পাকিস্তানের অন্য বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে আলাদা। ইসলামাবাদে আগে পাঠানো টেলিগ্রাম অনুযায়ী সাত্তারকে সুনির্দিষ্ট বেআইনি কাজের দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্তত একটি অপরাধ– গোপনে দেশত্যাগের চেষ্টার দায়ে তিনি দোষী। যদিও সাত্তারের মনোভাবের প্রতি সমবেদনা জাগতেই পারে, কিন্তু এ ব্যাপারটিতে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো রকম নাক গলানো উচিত হবে না মনে করি। সবচেয়ে বড় কথা সাত্তারের বন্ধুই আমাদের এ ব্যাপারে নিষেধ করেছে।
— ফারল্যান্ড
http://www.scribd.com/doc/46434835/‘‘বিশ্ববিদ্যালয়-গণহত্যার-পর-পাকিদের-মনোভাব”
টেলিগ্রামে মাঠ পর্যায়ের সেনা কর্মকর্তাদের যে মনোভাবের কথা বলেছেন ফারল্যান্ড, তার একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে। ১৩ মে ‘নিউইয়র্ক টাইমস’-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন লিখেন ম্যালকম ডবলিউ ব্রাউন। পাকিস্তান সরকার যে ৬ জন বিদেশি সাংবাদিককে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখাতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, প্রতিবেদক তাদের একজন। ঢাকার পরিস্থিতির বর্ণনা দেওয়ার পর ম্যালকম কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তা তুলে ধরেছেন। এদের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, যিনি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিদেশে যাওয়ার কথা ভাবছেন।
একজন সেনা কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেছেন যে, ‘অভিভাবকদের আস্কারা পেয়ে এরা গোল্লায় গেছে। না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে মদ খাওয়া আর ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটে? এমন ব্যাপার তো মুসলিম সমাজে বরদাশত করার মতো নয়। এসব লোক স্বভাবতই অস্ত্র হাতে নিয়ে সমাজদ্রোহী হয়ে উঠবে আর আমাদের হাতে মারা পড়বে। …ভবিষ্যত প্রজন্মকে পুরোপুরি ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে।’ প্রতিবেদনটিতে স্পষ্টতই ফুটে উঠেছে বুদ্ধিজীবীদের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রোশের নানা দিক।
নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন
নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন
এই আক্রোশ মেটানোর একটি সুযোগ তারা নিতে চেয়েছিল ১৪ ডিসেম্বর ঢাকায় গভর্নর ভবনে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলগুলোতে সার্কিট হাউজ কিংবা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবনে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশিষ্ট নাগরিকদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে সেনাবাহিনীর রিট্রিটের আগে। (৬)
ব্যাপারটা শুরু হয় নভেম্বরের শেষার্ধ থেকে। ব্রাক্ষণবাড়িয়া, মৌলভীবাজার, সিলেট, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ রকম হত্যাকাণ্ডের খবর পরবর্তীতে প্রকাশ হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়। গভর্নর হাউজের হত্যাকাণ্ডটি হতে পারেনি ভারতীয় বিমান হামলার কারণে। তীব্র হামলায় গভর্নর হাউজ বিধ্বস্ত হওয়ার পর ডক্টর মালেক তার মন্ত্রিসভাসহ ইস্তফা দিয়ে সপরিবারে আশ্রয় নেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে, রেডক্রসের নিউট্রাল জোনে।
হত্যা পরিকল্পনাটি ঘটানোর কথা ১৪ নভেম্বর বিকেলে। সেদিন বিকেলে গভর্নর হাউজে আসার জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন সচিবালয়সহ সকল সরকারি কর্মকর্তা। আমন্ত্রণপত্রটি সবার কাছে পৌছে দেওয়া হয় ১৩ তারিখ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সাবেক রাষ্ট্রপতির সচিব আতাউল হক এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের তখনকার সিনিয়র সহকারী সচিব আবদুল মতিন। পরিকল্পনা ছিল বঙ্গভবনের লনে সকল অফিসারকে বসতে দেওয়া হবে। চারপাশে তাঁবু খাটিয়ে ৪০ টিরও বেশি মেশিনগান প্রস্তুত রাখে সেনাবাহিনী।
মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ গোয়েন্দা প্রতিবেদনে ব্যাপারটি জানতে পেরে মিত্রবাহিনীর সহযোগিতা চান। সুবাদেই গভর্নর হাউজকে গুড়িয়ে দিতে একের পর এক মিগ হামলে পড়ে সেদিন সকালে। রাও ফরমান আলী অবশ্য হাল ছাড়েননি। ১৭ ডিসেম্বর সকালে সভাটি নতুন করে অনুষ্ঠানের কথা জানানো হয় কর্মকর্তাদের। কিন্তু তার আগেই ঢাকা স্বাধীন। (৭)
বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে কোন কোন বিদেশি শক্তি জড়িত ছিল, যথাযথ গবেষণা ছাড়া সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়, তবে এ বিষয়ে ইঙ্গিত দেবার জন্য দুয়েকটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা যেতে পারে।
এ বিষয়ে প্রথম দলিলটি হচ্ছে ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে ভারতের রসাপ্তাহিক ‘দ্য নিউ এইজ’ পত্রিকার একটি প্রতিবেদন। এর অংশবিশেষের বাংলা তরজমা নিম্নরূপ:
গণহত্যা তদন্ত কমিটির সভাপতি চলচ্চিত্র প্রযোজক জনাব জহির রায়হান আমাদের জানিয়েছেন:
‘‘আলবদরদের কার্যকলাপ অনুসন্ধান করতে যেয়ে আমরা একই সঙ্গে অপরাধীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝবার জন্য নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যখন নিহত বাবা ও ভাইদের দেহাবশেষ ঢাকার বধ্যভূমিতে খুঁজে ফিরছিলেন তখন আমাদের ধারণা ছিল যে দখলদার পাকিস্তানি শাসকদের নিশ্চিত পরাজয় উপলব্ধি করে সন্ত্রস্ত গোঁড়া ধর্মধ্বজী পশুরা ক্রোধান্ধ হয়ে কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করেছে। কিন্তু পরে বুঝেছি ঘটনা তা ছিল না। কেননা এই হত্যাকাণ্ডের শিকার যারা হয়েছেন তারা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি স্থানীয় এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবের জন্য সুপরিচিত ছিলেন।’’
আলবদর বাহিনীর ধর্মান্ধ ও মূর্খ লোকদের কাছে সব লেখক ও অধ্যাপকই এক রকম ছিলেন। জহির রায়হান বলছিলেন এরা নির্ভূলভাবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রমনা বুদ্ধিজীবীদের বাছাই করে আঘাত হেনেছে। এ থেকে একটা সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো যায় যে আলবদরদের এই স্বেচ্ছাসেবকরা অপরের ইচ্ছা কার্যকরী করার বাহন ছিল মাত্র। কিন্তু কারা এই খুনিদের পেছনে ছিল?
সংগৃহীত দলিল ও সাক্ষ্যপ্রমাণাদি থেকে জানা যায় শ্রেষ্ঠ বাঙালি সন্তানদের হত্যার কাজে নিয়োজিত অন্ধ ধর্মীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত গুণ্ডাদের আলবদর বাহিনীতে যারা সংগঠিত করে, তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে জড়িত।
p-4
পূর্বে উল্লিখিত পাকিস্তানি জেনারেলের (বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক জেনারেল রাও ফরমান আলী) ডায়েরিতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে দুজন আমেরিকান নাগরিক ঢাকা সফর করে। এরা হল হেইট (Haight) ও ডুসপিক (Dwespic), এদের নামের পাশে ছোট ছোট অক্ষরে ইউএসএ (USA) ও ডিজিআইএস (DGIS) অর্থাৎ ডিরেক্টর জেনারেল অব ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস লেখা ছিল। আর লেখা আছে– ‘‘রাজনৈতিক, ৬০-৬২, ৭০’’। অপর এক জায়গায় লেখা আছে– ‘‘এ দুজন আমেরিকান পিআই-এর একটি বিশেষ বিমানে ব্যাংককের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন’’।
হেইট ও ডুসপিক কে? ঢাকার দৈনিক বাংলার রিপোর্টে দেখা যায়, হেইট ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেছে। সে ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীতে চাকরি করত। ১৯৫৩ সাল থেকে সে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ১৯৫৪ সাল থেকে সে আমেরিকান দূতাবাসের রাজনৈতিক কূটনীতিবিদ হিসেবে বহুদেশ ভ্রমণ করেছে। সে কোলকাতা এবং কায়রোতেও ছিল। সিআইএ এজেন্ট ডুসপিকের সঙ্গে গত বছর সে ঢাকা ফিরে আসে এবং রাও ফরমান আলীর সঙ্গে তিন হাজার বুদ্ধিজীবীর একটি তালিকা তৈরি করে। জেনারেলের শোবার ঘরে এই তালিকা পাওয়া গেছে।
নিহত বুদ্ধিজীবীদের আত্মীয়-স্বজনদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে আলবদরদের পরিকল্পিত হত্যার কাজে বিদেশি মুখোশ, ছদ্মপোশাক ও ছোরা ব্যবহার করা হয়েছে। গণহত্যা তদন্ত কমিটির রিপোর্ট থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়।
স্বভাবতই পাকিস্তানি সেনাপতি ও সিআইএ চরদের মধ্যেকার এই যোগাযোগ গোপন ব্যাপার ছিল। আলবদর বাহিনীর সাধারণ কর্মীরা এ সম্পর্কে কিছুই জানত না। আবার এই সন্ত্রাসবাদী সংস্থার হোতারা এবং জামায়াতে ইসলামী দলের নেতারা অনুগামীদের মনোবল বাড়ানোর আশায় আমেরিকা ও পিকিং নেতাদের সঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক একনায়কের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা প্রচার করত।
১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর ঢাকার জামায়াতে ইসলামীর সম্পাদক প্রকাশিত এক প্রচারপত্রের ভাষা হল: ‘‘বিদেশে আমাদের বন্ধুরা আছেন। চীন ও আমেরিকা আমাদের সমর্থক বন্ধুদেশ।’’
উল্লেখ্য, রাও ফরমান আলীর ডায়েরিতে যে দুজন সিআইএ এজেন্টের নাম পাওয়া গিয়েছিল তারা ইন্দোনেশিয়াতে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করেছিল এবং ইন্দোনেশীয় সরকার সেজন্য তাদের অনুপস্থিতিতে বিচারও করেছিল।
ব্যবহৃত সূত্র:
১. ‘‘মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান’’, এ এস এম সামছুল আরেফিন (পৃ:৫৫০)
২. আবদুল গাফফার চৌধুরীর কলাম, দৈনিক সমকাল: ২৪ ডিসেম্বর ২০১০ সংখ্যা
৩. ‘‘On slaught of intellect and intelligentia/ Nurul Islam Patwari: Bangladesh 1972’’ (page: 87)
৪. ‘‘মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান’’, এ এস এম সামছুল আরেফিন (পৃ:৫৫০)
৫. ‘‘বাংলাদেশ উইনস ফ্রিডম’’, মুসা সাদিক (পৃ:৩৫৮)
৬. ‘‘একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়’’ (পৃ:১১৬)
৭. ‘‘বাংলাদেশ উইনস ফ্রিডম’’, মুসা সাদিক (পৃ:৩৫২)
http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/13725
- Biplob Rahman | ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ ১২:৩৬582658
- অমি রহমান পিয়াল
মুক্তিযুদ্ধে গোপন তৎপরতা (২): বুদ্ধিজীবী হত্যায় মার্কিন দায়
ডিসেম্বর ১৫, ২০১৩
জহির রায়হানের তদন্ত কমিটি ও প্রাথমিক ইঙ্গিত
বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে বিদেশি পরাশক্তি জড়িত থাকার ইঙ্গিতটা প্রথম এসেছিল জহির রায়হানের তরফে। ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১ দৈনিক ‘অবজারভার’-এর প্রতিবেদনে জানা যায় যে, তিনি বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করতে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। বুদ্ধিজীবী হত্যায় অনেক পাকিস্তানি অফিসার জড়িত এবং তাদের যুদ্ধবন্দি হওয়ার বদলে যুদ্ধাপরাধের দায়ে বিচার দাবি করেন জহির রায়হান। কিছু বিদেশি পরাশক্তিও এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত বলে অভিযোগ তাঁর। (১)
এখানে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য যে, তখনও বুদ্ধিজীবীদের একাংশ (যাদের লাশ মেলেনি বা চিহ্নিত করা যায়নি) আলবদরদের হাতে বন্দি বলে বিশ্বাস করতেন অনেকে; জহির রায়হান তাদের উদ্ধারে তৎপর হওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছেন সেই প্রতিবেদনে। ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি সে রকমই এক উদ্ধার অভিযানে নিহত হন জহির রায়হান।
একই প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইঙ্গিত রয়েছে। জহির রায়হান অনেকটা একাই তদন্ত করছিলেন, কিছু দলিলপত্রও জোগাড় করেছিলেন। টিএন্ডটি, বুয়েট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও পুলিশসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বেশ কিছু কর্মকর্তা এসব হত্যাকাণ্ডে পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে সাংবাদিকদের জানান তিনি। আলবদর বাহিনীর কাছ থেকে উদ্ধার করা একটি দলিল এ সময় সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরেন জহির যেখানে ১৪ জনের একটি তালিকা ছিল।
একদম উপরে RM/1 লেখা সে তালিকায় ছাত্র, সাংবাদিক ও ব্যবসায়ীদের নাম ছিল। নামের পাশে লেখা vd (very dangerous), vvd, d, ld ইত্যাদি সাংকেতিক কথা। খুব বিপজ্জনক ট্যাগধারী ৫ সাংবাদিক ছিলেন হলিডের এনায়েতুল্লাহ খান, দ্য সান পত্রিকার আতাউস সামাদ, পূর্বদেশের এরশাদ মজুমদার, দ্য পিপলের চিত্রসাংবাদিক রেনু এবং দৈনিক বাংলার আবদুল হান্নান। তালিকায় নয়া পল্টন, ফকিরাপুল, আরামবাগ, পুরানা পল্টন এ রকম কিছু জায়গার নামও ছিল।
একই দিন বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয় জহির রায়হানের নেতৃত্বে। এই কমিটির অন্য সদস্যরা ছিলেন এহতেশাম হায়দার চৌধুরী, ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, এনায়েতুল্লাহ খান, সৈয়দ হাসান ইমাম ও ড. সিরাজুল ইসলাম। ৩০ জানুয়ারি জহির রায়হান মিরপুরে নিহত হওয়ার পর বুদ্ধিজীবী হত্যা তদন্ত কমিটির উদ্যোগ থেমে যায়। কমিটি ইতোমধ্যে যে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ উদ্ধার করেছিল, কোলকাতার একটি পত্রিকার একজন সাংবাদিক তা ভারতে নিয়ে চলে যান। (২)
কে এই সাংবাদিক, কেন তাকে এসব গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র দিয়ে দেওয়া হল, তার কোনো উল্লেখ নেই সূত্রে। কমিটিতে বেশ ক’টি নাম বেশ সন্দেহজনক চরিত্রের, বাংলাদেশের পরবর্তীকালের রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা ছিল মার্কিনঘেঁষা।
জহির রায়হানের উদ্ধৃতি দিয়ে ভারত থেকে ‘দ্য নিউ এজ’ নামে একটি সাপ্তাহিকে উঠে আসে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য এবং দুজন মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তার নাম। প্রতিবেদনটির আংশিক অনুবাদ ‘একাত্তরের ঘাতক-দালালরা কে কোথায়’ (১২০-১২১) বইটি থেকে তুলে দেওয়া হল–
‘‘বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে কোন কোন বিদেশি শক্তি জড়িত ছিল, যথাযথ গবেষণা ছাড়া সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়, তবে এ বিষয়ে ইঙ্গিত দেবার জন্য দুয়েকটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে প্রথম দলিলটি হচ্ছে ’৭২ সালের জানুয়ারিতে ভারতের সাপ্তাহিক ‘দ্য নিউ এইজ’ পত্রিকার একটি প্রতিবেদন। এর অংশবিশেষের ভাবানুবাদ অনেকটা এ রকম:
গণহত্যা তদন্ত কমিটির সভাপতি চলচ্চিত্র প্রযোজক জনাব জহির রায়হান আমাদের জানিয়েছেন– আলবদরদের কার্যকলাপ অনুসন্ধান করতে যেয়ে আমরা একই সঙ্গে অপরাধীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝবার জন্য নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যখন নিহত বাবা ও ভাইদের দেহাবশেষ ঢাকার বধ্যভূমিতে খুঁজে ফিরছিলেন তখন আমাদের ধারণা ছিল যে দখলদার পাকিস্তানি শাসকদের নিশ্চিত পরাজয় উপলব্ধি করে সন্ত্রস্ত গোঁড়া ধর্মধ্বজী পশুরা ক্রোধান্ধ হয়ে কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করেছে। কিন্তু পরে বুঝেছি ঘটনা তা ছিল না। কেননা এই হত্যাকাণ্ডের শিকার যারা হয়েছেন তারা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধি স্থানীয় এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবের জন্য সুপরিচিত ছিলেন।
আলবদর বাহিনীর ধর্মান্ধ ও মূর্খ লোকদের কাছে সব লেখক ও অধ্যাপকই এক রকম ছিলেন। জহির রায়হান বলছিলেন, এরা নির্ভুলভাবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রমনা বুদ্ধিজীবীদের বাছাই করে আঘাত হেনেছে। এ থেকে একটা সিদ্ধান্তেই পৌছানো যায় যে আলবদরদের এই স্বেচ্ছাসেবকরা অপরের ইচ্ছা কার্যকরী করার বাহন ছিল মাত্র। কিন্তু কারা এই খুনীদের পেছনে ছিল?
সংগৃহীত দলিল ও সাক্ষ্যপ্রমাণাদি থেকে জানা যায় শ্রেষ্ঠ বাঙালি সন্তানদের হত্যার কাজে নিয়োজিত অন্ধ ধর্মীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত গুণ্ডাদের আলবদর বাহিনীতে যারা সংগঠিত করে, তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে জড়িত। পূর্বে উল্রিখিত পাকিস্তানি জেনারেলের (বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক জেনারেল রাও ফরমান আলী) ডায়েরিতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে দুজন আমেরিকান নাগরিক ঢাকা সফর করে। এরা হল হেইট (Haight) ও ডুসপিক (Dwespic)। এদের নামের পাশে ছোট ছোট অক্ষরে ইউএসএ (USA) ও ডিজিআইএস (DGIS) অর্থাৎ ডিরেক্টর জেনারেল অব ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস লেখা ছিল। আরও লেখা আছে, রাজনৈতিক, ৬০-৬২, ৭০’। অপর এক জায়গায় লেখা আছে– এ দুজন আমেরিকান পিআইএর একটি বিশেষ বিমানে ব্যাংককের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।
হেইট ও ডুসপিক কে? ঢাকার দৈনিক বাংলার রিপোর্টে দেখা যায়, হেইট ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেছে। সে ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীতে চাকরি করত। ১৯৫৩ সাল থেকে সে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ১৯৫৪ সাল থেকে সে আমেরিকান দূতাবাসের রাজনৈতিক কূটনীতিবিদ হিসেবে বহুদেশ ভ্রমণ করেছে। সে কলকাতা এবং কায়রোতেও ছিল। সিআইএ এজেন্ট ডুসপিকের সঙ্গে গত বছর সে ঢাকা ফিরে আসে এবং রাও ফরমান আলীর সঙ্গে তিন হাজার বুদ্ধিজীবীর একটি তালিকা তৈরি করে। জেনারেলের শোবার ঘরে এই তালিকা পাওয়া গেছে।
নিহত বুদ্ধিজীবীদের আত্মীয়স্বজনদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে আলবদরদের পরিকল্পিত হত্যার কাজে বিদেশি মুখোশ, ছদ্মপোশাক ও ছোরা ব্যবহার করা হয়েছে। গণহত্যা তদন্ত কমিটির রিপোর্ট থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়। স্বভাবতই পাকিস্তানি সেনাপতি ও সিআইএ চরদের মধ্যেকার এই যোগাযোগ গোপন ব্যাপার ছিল। আলবদর বাহিনীর সাধারণ কর্মীরা এ সম্পর্কে কিছুই জানত না।
বুদ্ধিজীবী হত্যার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ‘নিউইয়র্ক টাইমস’ পত্রিকায় সে সময় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন দেখুন–
দৈনিক ‘অবজারভার’-এর সেই প্রতিবেদন যেটিতে বুদ্ধিজীবী হত্যার ব্যাপারে জহির রায়হানের দাবি তুলে ধরা হয়েছে
দৈনিক ‘অবজারভার’-এর সেই প্রতিবেদন যেটিতে বুদ্ধিজীবী হত্যার ব্যাপারে জহির রায়হানের দাবি তুলে ধরা হয়েছে
আবার এই সন্ত্রাসবাদী সংস্থার হোতারা এবং জামায়াতে ইসলামী দলের নেতারা অনুগামীদের মনোবল বাড়ানোর আশায় আমেরিকা ও পিকিং নেতাদের সঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক একনায়কের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা প্রচার করত। ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর ঢাকার জামায়াতে ইসলামীর সম্পাদক প্রকাশিত এক প্রচারপত্রের ভাষা হল:
‘‘বিদেশে আমাদের বন্ধুরা আছেন। চীন ও আমেরিকা আমাদের সমর্থক বন্ধুদেশ।’’
রাও ফরমান আলীর অফিসকক্ষ থেকে উদ্ধার করা চিরকুট নিয়ে প্রতিবেদন
রাও ফরমান আলীর অফিসকক্ষ থেকে উদ্ধার করা চিরকুট নিয়ে প্রতিবেদন
উল্লেখ্য, রাও ফরমান আলীর ডায়েরিতে যে দুজন সিআইএ এজেন্টের নাম পাওয়া গিয়েছিল তারা ইন্দোনেশিয়াতে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করেছিল এবং ইন্দোনেশীয় সরকার সেজন্য তাদের অনুপস্থিতিতে বিচারও করেছিল।
ফরমান আলীর অফিসকক্ষে প্রাপ্ত চিরকুট
ফরমান আলীর অফিসকক্ষে প্রাপ্ত চিরকুট
এইসব অনুসন্ধানের সূত্র কী, নাকি নেহাতই আন্দাজে তীর ছোঁড়া তা জানার কোনো উপায় নেই।
অনেক ঘাঁটাঘাটি করে ডুসপিক সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। হেইট সম্পর্কে খানিকটা জানা গেছে। জুলিয়াস ম্যাডার ১৯৬৮ সালে একটি বুকলেট বের করেছিলেন ৩ হাজার সিআইএ এজেন্টের নাম ও কর্মস্থল সম্পর্কে জানিয়ে। ধারণা করা হয় কেজিবির ইন্ধনে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং এখন এটি পাওয়া পায় অসম্ভব। ‘হু ইজ হু ইন দ্য সিআইএ’ নামে বইটিতে হেইটের উল্লেখ পাওয়া গেছে।(৩)
http://www.scribd.com/doc/46459438/Who-is-Who-in-the-CIA
তার পুরো নাম হেইট হিউ গ্রিনোউ (Haight Hue Greenough)। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সিআইএর নানা তৎপরতায় যুক্ত ছিলেন তিনি। মাঝে ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত ছিলেন ভারতে। হেইট ও ডুসপিকের উল্লেখ কি আসলেই তাদের সম্পৃক্ততার নির্দেশনা নাকি আর কারও থেকে নজর সরানোর জন্য তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কারণ গোটা মুক্তিযুদ্ধকালে অন্য একজন সিআইএ এজেন্টের সম্ভাব্য তৎপরতা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল প্রবাসী বাংলাদেশ ও ভারত সরকার। সে আলোচনায় একটু পরেই আসছি।
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে বুদ্ধিজীবীদের লাশ আবিষ্কারের পরপরই ভারতীয় বিভিন্ন পত্রিকায় সিআইএর যুক্ত থাকার ব্যাপারটি বারবার উঠে আসে। এ নিয়ে উদ্বেগ জানায় যুক্তরাষ্ট্র, বিশেষ করে তাদের ধারণা হয় কেজিবি এই উস্কানিটা দিচ্ছে।
রহস্যময় রবার্ট জ্যাকসন
একটা প্রশ্ন সবার মনে জাগতেই পারে। মুক্তিযুদ্ধের সময় সিআইএ-র কেউ নিজের হাতে কোনো বাঙালিকে খুন করেনি। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সহযোগিতার, স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের নামের তালিকা সরবরাহের। এখন একটা দেশের জন্য কারা বিপজ্জনক সেটা সেই দেশের গোয়েন্দাদের চেয়ে সিআইএ বেশি জানবে! উত্তর, হ্যাঁ, জানবে। কারণ তারা প্রতিটা দেশের গুরুত্বপূর্ণ লোকজনের (তাদের জন্য উপকারী এবং বিপজ্জনক) ওপর ফাইল সংরক্ষণ করে যাকে বলা হয় বায়োগ্রাফিকাল রিপোর্টিং। নানা গোয়েন্দা সূত্র থেকে তথ্য দিয়ে সাজানো হয় প্রতিটি ফাইল। তাই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্য সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তাদের সরবরাহ করা তালিকা মানা। এটাও চুক্তিরই অংশ। ব্যাপারটা এবং বায়োগ্রাফিকাল রিপোর্টিংয়ের পদ্ধতি দলিলসহ বোঝানো হবে সামনের পর্বগুলোতে।
আসা যাক তালিকা সরবরাহের অভিযোগে। আগের পর্বে হেইট ও ডুসপিকের নাম যে কারণে এসেছে, সেই একই অভিযোগে মুক্তিযুদ্ধের প্রায় গোটা সময়টাতেই আলোচিত ছিলেন রবার্ট জ্যাকসন। মুক্তিযুদ্ধকালীন অনেকগুলো পত্রিকাতেই তার নাম এসেছে। কোথাও ‘জ্যাকশন’, কোথাও বা ‘কিলার জ্যাক’ উপাধি জুড়ে বসেছে নামের পাশে। এসব অভিযোগ যে ভিত্তিহীন ছিল না তার প্রমাণও রয়েছে আমাদের হাতে। তার আগে দেখা যাক কীভাবে আলোচিত ছিলেন এই জ্যাকসন।
মুক্তিযুদ্ধকালীন রুশপন্থী পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র সাপ্তাহিক ‘মুক্তিযুদ্ধ’-তে প্রথম উঠে আসে জ্যাকসনের নাম। একাত্তরের ১ আগস্ট প্রকাশিত সংখ্যায় ‘‘ইয়াহিয়াচক্রকে মদত দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক দল ও মার্কিন বিশেষজ্ঞ’’ শিরোনামে দ্বিতীয় শীর্ষ সংবাদ ছিল এটি। (৪) সেখানে লেখা হয়:
‘‘মার্কিন ষড়যন্ত্রকারীরা কি বাংলাদেশকে ভিয়েতনামে রূপান্তরিত করার ষড়যন্ত্র আঁটিয়াছে? এই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি আজ সকলের মনকে আলোড়িত করিতেছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়াছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ‘জননিরাপত্তামূলক’ কর্মসূচির নামে ঢাকায় পুলিশ ‘বিশেষজ্ঞ’ পাঠাইবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। জননিরাপত্তার নামে এই বিশেষজ্ঞ ও তাহার শিকারি কুকুরের দলের কাজ হইবে, মুক্তিযুদ্ধ দমনের কাজে ইয়াহিয়ার জল্লাদ বাহিনীকে মদত দেওয়া। এই দায়িত্ব দিয়া যে কূটনীতিককে ঢাকায় পাঠানো হইতেছে, এই ধরনের কাজে তাহার নাকি বিশেষ পারদর্শিতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। খবরে প্রকাশ, ইতোপূর্বে এই ব্যক্তি ভিয়েতনামে নিযুক্ত ছিল এবং সেখানেই বিশেষজ্ঞ হিসেবে হাত পাকায়। পাকিস্তানে নিযুক্ত বর্তমান মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড একজন কুখ্যাত সিআইএ এজেন্ট। একসময় তিনিও কূটনৈতিক কার্য উপলক্ষে ভিয়েতনামে ছিলেন। কাজেই পুলিশ বিশেষজ্ঞ হিসেবে রবার্ট জ্যাকসন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের পুরাতন খেলারই পুনরাবৃত্তি হইতে চলিয়াছে মাত্র।’’
‘মুক্তিযুদ্ধ’ পত্রিকায় প্রকাশিত জ্যাকসনকে নিয়ে রিপোর্ট
‘মুক্তিযুদ্ধ’ পত্রিকায় প্রকাশিত জ্যাকসনকে নিয়ে রিপোর্ট
তবে সবচেয়ে ডিটেলে জ্যাকসনকে নিয়ে লিখে আওয়ামী লীগের মুখপাত্র সাপ্তাহিক ‘জয়বাংলা’। (৫) পত্রিকাটির ১৩ আগস্ট সংখ্যায় ‘‘আর এক আইকম্যান রবার্ট জ্যাকসন’’ উপশিরোনাম এবং ‘‘আন্তর্জাতিক গণহত্যা বিশারদ ঢাকায়…’’ শিরোনামে জ্যাকসনকে নিয়ে বিশাল এক প্রতিবেদনের কপি নিচে দেওয়া হল–
‘জয়বাংলা’ পত্রিকায় জ্যাকসনকে নিয়ে প্রতিবেদন
‘জয়বাংলা’ পত্রিকায় জ্যাকসনকে নিয়ে প্রতিবেদন
দেখা যাচ্ছে প্রতিবেদনটিতে লেখা হয়–
‘‘কে এই ব্যক্তিটি? জ্যাকসন নামে যিনি কুখ্যাত? নাজি বাহিনীর হত্যা বিশেষজ্ঞ আইকম্যানের উত্তরসূরী রবার্ট জ্যাকসন? আধুনিক উপনিবেশবাদের প্রধান পাণ্ডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ও সরকারি কর্মচারি রবার্ট জ্যাকসন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে গণহত্যায় সহযোগিতা করেছেন। আন্তর্জাতিক গণহত্যা বিষারদ ‘কিলার জ্যাক’ নামে তাকে উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশে হত্যা, ধ্বংস ও গণহত্যায় তার ভয়াবহ ভুমিকা ছিল। ২৫ মার্চের হত্যাযজ্ঞের পূর্ব থেকেই জ্যাকসন ঢাকায় ছিলেন এবং ইসলামাবাদ ও জেনারেলদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল প্রাত্যহিক। এ সমস্ত তথ্য আজ মার্কিন মুল্লুক থেকেই প্রকাশ পাচ্ছে।
সিনেটর কেনেডি সম্প্রতি নিউইয়র্কে রবার্ট জ্যাকসন সম্পর্কিত তথ্য বিশ্বের নিকট প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে, জ্যাকসনকে পুলিশ বিশেষজ্ঞ রূপে পুনরায় ঢাকায় প্রেরণ করা হচ্ছে। অপর একটি খবর থেকে প্রকাশ, ‘জল্লাদ জ্যাক’ বাংলাদেশে হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পিত সম্প্রসারণের জন্য পুনরায় ঢাকা পৌঁছেছেন।
বাংলাদেশে গণহত্যার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত এবং বাছাই করা ব্যক্তিদের হত্যার পরিকল্পনাকারী রবার্ট জ্যাকসনকে মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার পুলিশ-নীতির বিশেষজ্ঞ রূপে দীর্ঘদিন পূর্বে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছিল। সে সময় তিনি প্রকাশ্যে সামরিক জান্তার পুলিশের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছিলেন বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জ্যাকসন ঢাকাস্থ মার্কিন কনস্যুলেটে একটি গোপন দফতর খুলে চক্রান্তমূলক কাজে লিপ্ত ছিলেন। তিনি কালক্রমে কনস্যুলেটে এতটা শক্তিশালী হয়ে উঠেন যে, কনসাল জেনারেল (আর্চার) ব্লাডের সঙ্গে তার ক্ষমতার লড়াই পর্যন্ত হয়। জ্যাকসনের এই ক্ষমতা পেন্টাগন জুগিয়েছিল বলে আজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।’’
বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে নানা সাহায্য সংস্থা ও সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এভাবে বিশেষজ্ঞদের আচ্ছাদনে গুপ্তচর ও হত্যার পরিকল্পনাকারীরা প্রবেশ করে। রবার্ট জ্যাকসন সে ধরনের একজন ক্রীড়ানক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাধারণ মানুষের রক্তে যার হস্ত রঞ্জিত, সেই জ্যাকসনই বাংলাদেশে নির্বাচিত হত্যার তালিকা প্রস্তুত করে সেনাপতিদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এই জল্লাদ জ্যাকই দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও ব্রাজিল সরকারকে হত্যা ও ধ্বংসের পরিকল্পনা করে দেন। উক্ত দুটি দেশে জ্যাকসন পরিকল্পিত সংস্থা নরহত্যা ও ধ্বংস দীর্ঘদিন অব্যাহত রাখে।
একটি বিদেশি পত্রিকা গণহত্যা বিশেষজ্ঞ জ্যাকসনের ঢাকা অবস্থানকালে যে বিভীষিকাময় কার্যক্রমের সঙ্গে লিপ্ত ছিলেন তা উদঘাটন করেছে। পত্রিকাটিতে বলা হয়েছে: ‘পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে যাদের হত্যা করা হবে তার একটি দীর্ঘ তালিকা তিনি প্রস্তুত করেন। জ্যাকসন আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে ইসলামাবাদকে উপদেশ দিতেন। এই ব্যক্তির পরিকল্পনা উত্তমরূপে কার্যকর হয়। ২৫ মার্চ গণহত্যা আরম্ভ করার সময় পশ্চিম পাকিস্তানি বাহিনী তারই তালিকা বেছে বেছে বিশেষ বিশেষ শ্রেণির ব্যক্তিদের হত্যায় লিপ্ত হয়।’
উল্লেখ্য যে, ১৯৬০ সাল থেকেই ঢাকাস্থ মার্কিন কনসাল জেনারেলের সম্প্রসারিত অফিসের নামে শাহবাগ হোটেলের একটি স্যুটে একটি গোপন অফিস ছিল। উক্ত গুপ্ত অফিসের উচ্চপদস্থ অফিসার জনাব ফরিদউদ্দিন আহমেদ ১৯৬৪ সালের দিকে আকস্মিকভাবে চাকরি ছেড়ে দেন। তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন যে, কতিপয় মার্কিন অফিসার সমস্ত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নেতা, গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আলোকচিত্র, জীবনী ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে রিপোর্ট সংগ্রহ করে গোপন কক্ষে রাখা হয়। জনাব ফরিদ স্থানীয় একটি দৈনিকে সহকারী সম্পাদক রূপে কাজ পান। কিন্তু সমস্ত তথ্যসম্বলিত একটি পুস্তক প্রকাশ করতে তিনি ব্যর্থ হন, কোনো প্রকাশক তা ছাপাতে চাননি।
শাহবাগ হোটেলে গুপ্তচরবৃত্তির কাহিনি বিভিন্ন মহলে ছড়িয়ে পড়ার পর মতিঝিলস্থ আদমজী কোর্টে অবস্থিত কনস্যুলেট অফিসে গুপ্ত অফিসটি সরিয়ে নেওয়া হয়। জ্যাকসন শেষ অবধি এই অফিসের সঙ্গেই সম্পর্কিত ছিলেন। জ্যাকসন একাই নন, তার সঙ্গে আরও তিনজন সহকারী জড়িত।
হত্যার সহায়ক ও গণহত্যায় পরিকল্পনাকারী এই কুখ্যাত ব্যক্তিটি দক্ষিণ ভিয়েতনামে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড অব্যহত রাখার উদ্দেশ্যে ‘অপারেশন ফিনিক্স’ নামক একটি মানবতাবিরোধী প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেন। জনৈক মার্কিন সিনেটর এই ধিকৃত ফিনিক্সকে ‘দক্ষিণ ভিয়েতনামে রাজনৈতিক বিরোধীদের হত্যার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে উচ্ছেদ সাধনের কার্যক্রম’ বলে উল্লেখ করেছেন। সমস্ত বিপ্লবী ঘাঁটি ধ্বংস এবং মুক্তিফ্রন্টের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল ব্যক্তিকে হত্যাই ছিল জ্যাকসনের ‘ফিনিক্স অপারেশনের’ মূল লক্ষ্য। একসময় মার্কিন সিনেট সাব-কমিটির জনৈক সদস্য ভিয়েতনাম সফর করে এসে বলেছিলেন যে, উক্ত অপারেশন ফিনিক্স কার্যকরী করে পনের হাজার সায়গন সরকারবিরোধী রাজনৈতিক নেতাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এবং অনেককে নিক্ষেপ করা হয়েছে ‘কনসেনট্রেশন’ ক্যাম্পে।
জ্যাকসন, যাকে বলা হয় জল্লাদ জ্যাক– ব্রাজিলে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর লোক নিয়ে একটি আধাসামরিক সংস্থা গঠন করেন। উক্ত দেশে পরিকল্পিত হত্যানুষ্ঠানের জন্য দায়ী এই সংস্থাটির নাম ‘ডোপস’। জ্যাকসন প্রতিষ্ঠিত ডোপস, রাতের অন্ধকারে রাজনৈতিক বিরোধীদের নৃশংসভাবে হত্যার অভিযান চালাত। ভাড়াটিয়া হত্যাকারী জ্যাক ব্রাজিলের কর্তৃপক্ষকেও হত্যার জন্য একটি দীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। তদুপরি সত্য উদঘাটনের নামে জ্যাক নির্দেশিত নয়া পদ্ধতিতে রাজনৈতিক কর্মীদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার চালানো হত। এই সমস্ত হত্যার শিহরণমূলক কাহিনি শুনে বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত পোপের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়।
সেই ঘৃণ্য জল্লাদটি পুনরায় ঢাকায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তার নাম ও কার্যক্রম আন্তর্জাতিকভাবে প্রকাশ পাওয়ায় তিনি হয়তো এবার বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে হত্যার পরিকল্পনা ফ্যাক্টরি করবেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রায় সাতলক্ষ্ বৈদেশিক সৈন্য ও ঘাঁটি এবং তাবেদার সরকার ছিল। আর ব্রাজিলে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদলেহী সরকার। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ঢাকা তথা বাংলাদেশের বিদ্রোহী মাটি যে জ্যাকসনদের জন্য আর নিরাপদ নয়, সে কথা উচ্চারণের অপেক্ষা রাখে না।
মুক্তিবাহিনীর সেনারা আজ খুঁজে বেড়াচ্ছে সেইসব রক্তপিপাসু কুকুর ও হায়না– যারা হত্যা করেছে, আর যারা হত্যার সহায়ক।’’
প্রায় একই ধরনের কথা লেখা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ওপর ভারতীয় লেখক ক্যাপ্টেন এস কে গার্গের ‘Spotlight: Freedom Fighters of Bangladesh’ বইয়েও (পৃ: ১৬৯-১৭০)। ভারতীয় স্টেটসম্যান পত্রিকার ২৮ অক্টোবর, ১৯৭১ সংখ্যায় উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন:
‘‘স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরুতেই সিআইএ পাকিস্তানের পক্ষে তাদের গোয়েন্দা সহযোগিতার কার্যক্রম শুরু করে। প্রথমদিকে গেরিলাবিরোধী তৎপরতায় পাকিস্তান সরকারকে সহযোগিতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল তাদের কর্মকাণ্ড। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ২৫ মার্চের রাতেই নিকেশ করে দেওয়া হয়েছিল। আর এই নীলনকশাটি ছিল ঢাকার সাবেক ইউএস এইড কর্মকর্তা ‘কসাই’ জ্যাকসনের তৈরি। কাদের মারা হবে তার তালিকাটি তৈরি করেন কর্ণেল তাজ আর তা বাস্তবায়ন করেন ব্রিগেডিয়ার বশীর, কাদের ও হিজাজী। এরা বন্দিদের জেরাও করতেন।… আত্মসমর্পণের ঠিক আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ জন শিক্ষকসহ ৩ হাজার বুদ্ধিজীবীর একটি তালিকা তৈরি করে সিআইএ যাদের জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সদস্যদের নিয়ে গঠিত আলবদর দিয়ে দ্রুত নির্মূলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।’’ (৬)
দেখুন–
4
রবার্ট জ্যাকসনের ঢাকা আসার খবর লন্ডনের ‘অবজারভার’ পত্রিকা ছাপায় ৭ আগস্ট তাদের মস্কো প্রতিনিধির বরাতে। (৭) ঢাকায় জ্যাকসনের উপস্থিতি নিয়ে ‘সোভিয়েত রাশিয়া উদ্বিগ্ন’ জানিয়ে প্রতিবেদনে লেখা হয়:
Moscow has been even more disturbed than Delhi by reports reaching here that Washington has assigned to Dacca, a Mr. Robert Jackson, a counter-insurgency-expert with wide experience in Vietnam. This suggests to Moscow that Washington is now heading towards the Vietnamisation of East Bengal conflict. Whether or not Mr. Jackson will be anymore successful in East Bengal than in Vietnam, Moscow believes this move foreshadows a prolonged conflict in East Bengal in which China might be tempted to join America in playing a bigger physical role.
রিপোর্টটি নিচে দেখুন–
মস্কোর উদ্বেগ নিয়ে লন্ডনের ‘অবজারভার’ পত্রিকায় প্রকাশিত সেই প্রতিবেদন
মস্কোর উদ্বেগ নিয়ে লন্ডনের ‘অবজারভার’ পত্রিকায় প্রকাশিত সেই প্রতিবেদন
সাপ্তাহিক ‘জয়বাংলা’ পত্রিকায় জ্যাকসনের মুখোশ খোলার কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডিকে। ঘটনা সত্যি। ২৩ জুলাই নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে গোপন দলিলপত্রের দোহাই দিয়ে কেনেডির বরাতে বলা হয়:
‘‘যুক্তরাষ্ট্র সরকার পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহ দমনে পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য পুলিশ বিশেষজ্ঞ রবার্ট জ্যাকসনকে ঢাকায় পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। জ্যাকসনকে ২৫ মার্চের গোলযোগের পর প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কাউন্টার ইনসার্জেন্সিতে বিশেষজ্ঞ জ্যাকসন ঢাকায় দায়িত্ব নেওয়ার আগে ভিয়েতনাম ও ব্রাজিলে কর্মরত ছিলেন। এ নিয়ে বিব্রত সরকারি কর্মকর্তাদের পাশাপাশি গোয়েন্দা বিভাগে অস্বীকার করা হয় যে পূর্ব পাকিস্তানে মার্কিন পুলিশ টিম পাঠানোর কোনো পরিকল্পনা হয়েছে। তবে এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের ডিরেক্টর অব সাউথ এশিয়ান অপারেশনস জন রীস স্বীকার করেছেন যে রবার্ট জ্যাকসনকে ঢাকা পাঠানোর আবেদন করা হয়েছিল।’’ (৮)
জ্যাকসন সম্পর্কে সিনেটর কেনেডির ইঙ্গিত নিয়ে ‘নিউইয়র্ক টাইমস’-এর প্রতিবেদন
জ্যাকসন সম্পর্কে সিনেটর কেনেডির ইঙ্গিত নিয়ে ‘নিউইয়র্ক টাইমস’-এর প্রতিবেদন
(চলবে)
ব্যবহৃত সূত্র:
১. বাংলাদেশ অবজারভার, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১
২. ‘একাত্তরের ঘাতক-দালালরা কে কোথায়’ (পৃ: ১২২-১২৩)
৩. ‘হু ইজ হু ইন দ্য সিআইএ’, জুলিয়াস ম্যাডার
৪. সাপ্তাহিক মুক্তিযুদ্ধ, ১ আগস্ট ১৯৭১
৫. সাপ্তাহিক জয় বাংলা ১৩ আগস্ট ১৯৭১
৬.‘Spotlight: Freedom Fighters of Bangladesh’
(পৃ: ১৬৯-১৭০)
৭. লন্ডন অবজারভার, ৭ আগস্ট, ১৯৭১
৮. নিউইয়র্ক টাইমস, ২৩ জুলাই, ১৯৭১
http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/13791
- Biplob Rahman | ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ ১২:৩৭582659
- অমি রহমান পিয়াল
মুক্তিযুদ্ধের গোপন তৎপরতা (৩): বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে মার্কিন দায়
ডিসেম্বর ২৭, ২০১৩
তার আগে দেখা যাক পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে পাবলিক সেফটি অ্যাডভাইজার বা জননিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে কারা কারা কাজ করেছেন।
অফিস অব পাবলিক সেফটির (ওপিএস) সাবেক কিছু কর্মকর্তা একটা স্মৃতিচারণমূলক প্রকাশনা বের করেছিলেন। মুখবন্ধতেই তারা বলে নিয়েছেন যে, এটা সরকারি কোনো প্রকাশনা নয় এবং ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগের এই স্মৃতি রোমন্থনে সবার নাম কিংবা সব ঘটনা মনে না থাকাটাই স্বাভাবিক।
বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের পাবলিক সেফটি অ্যাডভাইজারদের উল্লেখে পাকিস্তানও ছিল। আর সেখানে হদিস মিলেছে রবার্ট জ্যাকসন ওরফে বব জ্যাকসনেরও (যুক্তরাষ্ট্রে নাম ছোট করে ডাকার প্রথা আছে; অ্যাডওয়ার্ড যেমন ‘অ্যাড’ বা `টেড’, তেমনি রবার্ট হয়ে যায় ‘বব’)।
ছবি-১
তাদের ভাষ্যে–
“পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম দুই প্রান্তেই পাবলিক সেফটি প্রকল্প চালু ছিল। তবে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো ধরনের প্রস্তাবনা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনুমোদিত হতে হত। পাকিস্তানের প্রথম পাবলিক সেফটির স্টেশন চিফ হয়ে আসেন সম্ভবত স্ট্যান শেলডন, ১৯৬০ সালে। করাচিতে ছিল তার সদর দফতর। জোকোর তার উপপ্রধান হলেও পরবর্তীতে পাকিস্তানের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাদের সহকারী হিসেবে বিভিন্ন সময় কাজ করেছেন বব গলিন্স, জন লি, রবার্ট লকহার্ট, হ্যারি উইন এবং চার্লস নেটবিট।
http://www.scribd.com/doc/46576803/পাকিস্তানে-যুক্তরাষ্ট্রের-জননিরাপত্তা-কার্যক্রম
১৯৬৫ সালে ভিয়েতনাম থেকে পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্ব নিয়ে আসেন রবার্ট ন্যাটবুশ। সে সময় এই প্রকল্পে কাজ করছিলেন হ্যারল্ড অস্টিন, জ্যাক জিমিক, লিওন ক্লেমেন্ট, ফ্রান্সিস পেরি ও অ্যাশটন ক্রেইগ। ১৯৬৭ সালে ন্যাটবুশকে ভিয়েতনামে ফেরত পাঠানো হয়। তার জায়গায় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন জোকোর। একই সময় মেরিন অ্যাডভাইজার হয়ে আসেন বব জানুস।
১৯৬৯ সালে ভিয়েতনাম থেকে অরভ্যাল উনারকে পূর্ব পাকিস্তানে ডেকে আনা হয়। তিনি ছিলেন ভিয়েতনামের পিসডি/এমআর-ওয়ান (জহির রায়হানের পাওয়া তালিকায় আরএমওয়ান নামে ইনিশিয়াল ছিল) বিভাগের উপপরিচালক। জোকোর গোটা পাকিস্তানের দায়িত্ব নিয়ে করাচি চলে যান।
অরভালের ওপরওয়ালা (ইমিডিয়েট সুপারভাইজার) ছিলেন বব জানুস। পরে তার জায়গা নেন বব জ্যাকসন। এই অরভালই পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ ডিটেকটিভ ট্রেনিং স্কুল (রাজারবাগ) ও ট্রাফিক ট্রেনিং স্কুলের পাঠ্যসূচি নতুন করে তৈরি করেন। রায়ট পুলিশকেও নতুন করে ট্রেনিং দেন তিনি। একই বইতে লেখা হয়েছে যে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের পাবলিক সেফটি বিভাগের কর্মকর্তাদের তেহরান সরিয়ে নেওয়া হয়।”
উপরের তথ্য সঠিক হলে রবার্ট ওরফে বব জ্যাকসন ২৫ মার্চের আগে ঢাকায় ছিলেন এটা প্রমাণ হয়।
ছবি-২
উপাত্তের ভিত্তিতে আমরা নিশ্চিত এক জ্যাকসনের উপস্থিতি ছিল ঢাকা দূতাবাস অফিসে। পাকিস্তানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষপাতমূলক আচরণে ঘৃণা জানিয়ে কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডের নেতৃত্বে ঐতিহাসিক ‘ডিসেন্ট টেলিগ্রামে’ সাক্ষর করেছিলেন যারা, তাদের মধ্যে রবার্ট জ্যাকসন নামটাও ছিল। তবে তার পদবীর কোনো উল্লেখ সেখানে ছিল না। সেই ঘটনার পর আর্চার ব্লাডকে প্রত্যাহার করে নেয় নিক্সন প্রশাসন। একই ভাগ্য বরণ করতে হয়েছিল সাক্ষরকারী বাকিদেরও।
ছবি-৩
এবার দেখা যাক তার ফিরে আসার কাহিনীতে। সিনেটর অ্যাডওয়ার্ড কেনেডি যে গোপন টেলিগ্রামের সূত্র ধরে কংগ্রেসে বোমা ফাটিয়েছিলেন সেই নির্দিষ্ট টেলিগ্রামটিতে। এটি একাত্তর সালের ২৫ জুন পাঠানো হয়, কেনেডি তা ফাঁস করেন ২২ জুলাই। পাকিস্তানের মার্কিন দূতাবাস এবং ইউএস এইডের যৌথ টেলিগ্রাম এটি যদিও পাঠানো হয়েছে রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের বরাতে সেক্রেটারি অব স্টেট কিসিঞ্জারকে। এটি উদ্দিষ্ট হয়েছে পাবলিক সেফটি বিষয়ক দুই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ইঙ্গল এবং ম্যাকডোনাল্ডের জন্য।
জোকোরের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান পুলিশের আইজিপি এমএকে চৌধুরীর সঙ্গে আলাপচারিতা এবং তার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে লেখা বার্তাটির ভাবানুবাদ তুলে দেওয়া হল:
১.
নিচের বর্ণনা জোকোরের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও পূর্ব পাকিস্তান পুলিশের আইজিপি (উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সাবেক আইজিপি) এমএকে চৌধুরীর সঙ্গে আলাপচারিতার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে।
ক.
পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ এমনিতে মোটামুটি মানের একটি সংগঠন হলেও বর্তমানে এটি ভগ্ন, দীর্ণ, মনোবলহীন একটি বাহিনী যার ৩৩ হাজার সদস্যের ৭৫ ভাগই হয় প্রতিপক্ষে যোগ দিয়েছে, পালিয়েছে, নয়তো মারা গেছে। এই হারটা কোন বিভাগে কেমন সে সম্পর্কে আইজিপি সঠিক বলতে না পারলেও দাবি করেছেন যে, হতাহতের হার যা শোনা যাচ্ছে তার চেয়ে কম এবং অনুমান করছেন ভবিষ্যতে পলাতকদের অনেকেই ফিরে এসে যোগ দেবে যেহেতু নতুন নিয়োগ শুরু হয়েছে। বলেছেন যারা ভয়ভীতি বা কোনঠাসা হয়ে যাবে ভেবে যারা অনুপস্থিত আছে তাদের সবাই নির্ভয়ে ফিরে যোগ দিতে পারবে।
যদিও স্বীকার করেছেন যে বেশ বড় সংখ্যক সদস্যই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এবং তারা ভারত থেকে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। জানিয়েছেন সারদা পুলিশ একাডেমির অধ্যক্ষ ডিআইজি আবদুল খালেক ও রাজশাহী রেঞ্জের মামুন মাহমুদ, রাজশাহীর পুলিশ সুপার এমআর চৌধুরীর সঙ্গে ভারত পাড়ি জমিয়েছেন। যদিও ভিন্ন প্রতিবেদনে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে মামুন এবং চৌধুরীকে সেনাবাহিনী হত্যা করেছে।
কুমিল্লার এসপি এএসএম ওসমান, চট্টগ্রামের এসপি শামসুল হক এবং ফরিদপুরের এসপি নুরুল মোনেম খানকে গ্রেফতার এবং গুলি করে মারা হয়েছে বলে বিশ্বাস। সাবেক আইজিপি টি আহমেদ এবং ঢাকার সাবেক এসপি ইএ চৌধুরীকে বরখাস্ত এবং দৃশ্যত গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে। অন্য অনেক পুলিশ কর্মকর্তাকে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ করতে।
খ.
লোকবল ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ বাহন এবং যোগাযোগের মাধ্যম নিয়ে দারুণ সঙ্কটে ভুগছে যা হয় সেনাবাহিনী ব্যবহার/অধিগ্রহণ করেছে নয়তো প্রতিপক্ষ ধ্বংস/কব্জা করেছে। আইজিপি সম্পূর্ণ তালিকা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন ঢাকায় সেনাবাহিনী ইতোমধ্যে কিছু জিনিসপত্র ফেরত দিয়েছে। তবে প্রতিপক্ষের হাতে রেডিওগুলো (ওয়ারলেস) থাকায় বিপাকে পড়েছে পুলিশের নেটওয়ার্ক। রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধাদি ক্ষতিগ্রস্ত এবং রক্ষণাবেক্ষণে যোগ্য লোকজন হারিয়ে যাওয়াদের দলে।
ছবি-৪
গ.
আইনশৃংখলার বর্তমান পরিস্থিতিকে আইজিপি তুলনা করেছেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঘটনাবলীর সঙ্গে। বলেছেন সীমান্ত এলাকার গ্রাম ও এলাকাগুলোয় প্রতিপক্ষ বাহিনী অসংখ্য হামলা করেছে এবং সেখানে ত্রাসের রাজত্ব চালানো হয়েছে। স্বীকার করেছেন একই ধরনের ঘটনা সীমান্ত ছাড়াও অন্যান্য জায়গায় ঘটেছে। তবে পদ্ধতিটা তার চোখে মামুলি ধরনের, তড়িঘড়ি হামলা চালিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মতো যা এক ধরনের উত্যক্ত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেনাবাহিনীর পক্ষে এসব সামাল দেওয়া সম্ভব এবং তারা দেবে।
ঢাকায় টানা বোমা হামলায় তিনি উদ্বিগ্ন এবং খুব খারাপ পরিস্থিতিতে পড়েছেন। পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ আইনশৃংখলা বজায় রাখার পূর্ণদায়িত্ব একসময় ঠিকই বুঝে নেবে, তবে এজন্য মাস ছয়েক লাগবে বলে আইজিপির অনুমান। কারণ একটি কার্যকর বাহিনী মাঠে নামাতে সময়টা প্রয়োজন।
সরকার সবার আগে গুরুত্ব দিচ্ছে মনোবল ফিরিয়ে আনাকে যা আসলে বিশাল দায়িত্ব বলে স্বীকার করতে হয়। বিহারিদের নিয়োগ এবং আইনশৃংখলা রক্ষায় সেনাবাহিনীকে খানিকটা রেহাই দিতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রেষণে ৫ হাজার পুলিশ আমদানি এই লক্ষ্যে একটা বড় প্রতিবন্ধক। বিহারিদের সঙ্গে বাঙালিদের একসঙ্গে টহল ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। তার চেয়ে বড় কথা পাঞ্জাবি/বিহারি/বাঙালির একত্রে টহলদারি কল্পনারও বাইরে। তারপরও আইজিপি আশাবাদী এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে সফরে ব্যস্ত যাতে অধীনস্থরা আগ্রহী হয়।
http://www.scribd.com/doc/46573984/জ্যাকসনকে-চেয়ে-ফারল্যান্ডের-টেলিগ্রাম
ঘ.
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোর ঘটনাবলী পুলিশের ঘড়ি কয়েক বছর পিছিয়ে দিয়েছে। আইনশৃংখলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান পুলিশের কোনো অস্তিত্ব নেই। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ বাদে এটি বিশেষ কিছু পুলিশি দায়িত্ব পালন করছে। নতুন সদস্য অপ্রতুল এবং ট্রেনিং সেন্টারগুলো অকার্যকর। জননিরাপত্তা কার্যক্রমের মাধ্যমে যা একটু উন্নতি হয়েছিল তার কিছুই নেই; যদিও প্রকল্পের অনুষঙ্গমূহ, যেমন যানবাহন, যোগাযোগের যন্ত্রপাতি এবং অংশগ্রহণকারী সাবেক সদস্যরা বর্তমান।
এহেন পরিস্থিতিতে আইজিপির অনুমিত ছয় মাসের মধ্যে একটি কার্যকর সংস্থা দাঁড় করানো আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র। নিশ্চিতভাবেই এই মুহূর্তে নাগরিকদের জন্য একটি কার্যকর আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী গঠনপ্রক্রিয়ার উত্তরণ অদূর ভবিষ্যতেও খুব একটা আশাজাগানিয়া নয় বরং তা স্থগিত রাখাই ভালো। তবে জননিরাপত্তামূলক সহযোগিতা চালু করা সম্ভব।
ছবি-৫
ঙ.
অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নীতি হল– ১) পাকিস্তানের ঐক্য বজায় রাখার পক্ষে সমর্থন এবং একটি স্থির ও প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে থাকা; এবং ২) পাকিস্তানের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টায় সহায়তা করা।
অবশ্যই এসব নীতির লক্ষ্যমাত্রা বর্তমানে চলতে থাকা একটি অস্থিতিশীল, ভীতিপ্রদ, নৈরাজ্যমূলক ও বহুধা সামাজিক অবস্থার মধ্যে সম্ভব নয়। আর্থসামাজিক উন্নতির জন্য দায়িত্বশীল এবং কার্যকর আইন প্রয়োগকারী সংস্থা জরুরি। অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা আইনের মানবিক, নিরপেক্ষ এবং দক্ষ প্রয়োগ উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয় পরিবেশ গঠনে ও রক্ষণাবেক্ষণে সহায়ক। পূর্ব পাকিস্তান পুলিশের সাহায্য দরকার এবং তারা তা স্বাগত জানাবে।
পাকিস্তান সরকার জননিরাপত্তা প্রকল্প পরিচালকের মাধ্যমে প্রকল্পে সহায়তার অনুরোধ জানিয়েছে। যদিও অনুরোধের তালিকায় বাড়তি কিছু অনুষঙ্গ* চাওয়া হয়েছে (পরে জানা গেছে জেরা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি চাওয়া হয়েছে, যার কিছু পাঠানোও হয়েছিল)। আমরা জানি যে প্রকল্প অব্যাহত রাখার জন্য যৌথ জরিপের ভিত্তিতে পুলিশ কমিশনের সুপারিশ ও প্রমাণাদি প্রয়োজন। পাকিস্তান সরকার এখানে একাই সব করতে চায়।
২.
আমাদের বিশ্বাস পুলিশের সঙ্গে সম্পর্ক অব্যাহত রাখা দূতাবাস এবং ঢাকা কনসুলেটের জন্য ভালোই হবে। তবে পরে বর্ণিত পরিস্থিতির আলোকে ঠিক কতদূর তা বজায় রাখা সম্ভব হবে সেটা অনিশ্চিত। আমাদের বিশ্বাস সেটা নিশ্চিত করার সেরা উপায় হতে পারে সাময়িকভাবে হলেও আমাদের জননিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাকসনকে পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত আনা।
তার প্রাথমিক দায়িত্ব হবে আগের যোগাযোগ পুনঃস্থাপন এবং তার ভিত্তিতে পরবর্তী ৯০ দিনের মূল্যায়ন প্রতিবেদন যাতে অতীতের প্রয়াসের পাশাপাশি একটি সংশোধিত কর্মসূচি চালানোর সম্ভাবনা ও নির্দেশনা থাকবে। পুরো ব্যাপারটা খুব গোপনে করা সম্ভব এবং এমনভাবে করতে হবে যাতে এই স্পর্শকাতর ব্যাপারটি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের জন্য বিব্রতকর হয়ে না দাঁড়াতে পারে।
৩.
যদি এইড/ডব্লু মনে করে ব্যাপারটা প্রয়োজনীয়, তাহলে আজই সবকিছু ওয়াশিংটনে কোরের জন্য প্রস্তুত রাখা হোক।’’
– ফারল্যান্ড
কেনেডি এই পরিকল্পনা ফাঁস করার আগে একটি মাস কেটে গিয়েছিল। অথচ অক্টোবরেও রবার্ট জ্যাকসনকে নিয়ে লেখালেখি চলছিল। তার মানে তিনি ঢাকায় ফিরে এসেছিলেন। আর তার খানিকটা প্রমাণ মিলবে পূর্ব পাকিস্তানে পাবলিক সেফটি প্রজেক্টের পরবর্তী মূল্যায়নে।
[চলবে]
সূত্র:
১. অফিস অব পাবলিক সেফটি
২. মার্কিন দূতাবাসের তারবার্তা।
http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/14140
- Biplob Rahman | ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ ১২:৪০582660
- বৃন্দলেখক
বাংলাদেশ রুখে দাঁড়াও
ডিসেম্বর ২৪, ২০১৩
সাতক্ষীরা
এক
শনিবার দুপুর আড়াইটায় প্রথমে কলারোয়া উপজেলার যুগীখালি গ্রামে পৌঁছালে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের মুখোমুখি হই আমরা। বাজারের সর্বস্ব লুট হয়ে যাওয়া দোকানগুলো দেখতে দেখতে আমরা গ্রামে ঢুকতে থাকি।
১০ ডিসেম্বর রাতে লুটপাট করে ধ্বংস করে দেওয়া নিমাই চন্দ্র হোড়ের দোকানের সামনে মানুষের বিশাল জটলা তখন। জনগণ চিৎকার করে বলছেন, ‘‘সাতক্ষীরাকে জ্বালায়-পুড়ায় ৪ জনকে মেরে ফেলেছে ওসি।’’ ‘‘আমরা কি পাকিস্তানে, আফগানিস্তানে?’’ ওসির পরিবর্তন চেয়ে তখন শ্লোগান দিচ্ছেন অনেকেই।
জানা গেল, ১০ তারিখ রাতে মুখে কাপড় বেঁধে ১৫০/২০০ মানুষ এসে লুটতরাজ চালায় এই বাজারে। হোটেল মালিক আবদুর রশিদ জানালেন, কাদের মোল্লার রায় কার্যকর হবার দু’দিন আগেই রাত এগারোটায় তার হোটেল ভেঙে দেওয়া হয়।
তবে সবচেয়ে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয় কলারোয়া ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আজহারুল ইসলাম আজুর বাড়িতে উপস্থিত হলে। কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় কার্যকর হবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কয়েকশ জামায়াত-শিবির কর্মী তাকে কুপিয়ে হত্যা করে। আজু জামায়াত কর্মীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য পিতার কবরের মধ্যে পালিয়েও রেহাই পাননি, বরং কবর থেকে ধরে এনে স্বজনদের সামনেই কুপিয়ে হত্যা করা হয় তাকে। এমনকি তার কবর দিতেও বাধ সাধে তারা।
দুই
সদর উপজিলার আগরদাড়ির তিন কিলোমিটার দূরে কুচপুকুর এলাকায় রয়েছে জামায়াত পরিচালিত মাদ্রাসা। স্থানীয় জনগণ বলে ‘জামায়াতের ক্যান্টনমেন্ট’। এখানে ১ মার্চ আওয়ামী লীগের স্থানীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলামকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। নজরুল ইসলামের বাড়িতে গেলে সেখানেও কান্নায় ভেঙে পড়েন তার স্বজনরা।
সেখানেই দেখা হয়ে যায় তৃণমূল আওয়ামী নেতাদের সঙ্গে। তাদের সবাই কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। দোকান-পাট ভেঙে দেওয়া হয়েছে অথবা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা মারধোর করা হয়েছে। এই এলাকাতেই নয় বছরের শিশু রিয়াদকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছে ঘাতকরা।
ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকদের বাড়ি। কুচপুকুর এলাকায় আওয়ামী লীগ নামে কোনো সংগঠন থাকবে না মর্মে ঘোষণা দিয়েছে জামাতের চেয়ারম্যান শেখ আনোয়ারুল ইসলাম।
তিন
দেবহাটা উপজিলার কুলিয়া ইউনিয়নের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ইছামতি নদী আর পশ্চিম দিকে ভারত। এ বছর ২৮ ফেব্রুয়ারির পর থেকেই আওয়ামী লীগ আর হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপর নেমে এসেছে চরম নির্যাতন। আওয়ামী লীগ নেতা আসাদুল হকসহ চারজনকে হত্যা করা হয়েছে এ পর্যন্ত।
মুখোশধারী হত্যাকারীরা পিটিয়ে হত্যা করেছে পারুলিয়ার আবু রায়হান, আলমগীর হোসেন, আবদুল আজিজকে। হাত-পা ভাঙা অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন নারাণ সরকার, মো. বেলাল হোসেন, শেখ ফারুক হোসেন রতন, নাজিম হোসেন, আকিনুর, শরিফুল ইসলাম মিন্টু। বসতবাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, দোকানপাট পুড়িয়ে দেওয়ার রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে ৭৫ জনের। কাদের মোল্লার ফাঁসির রায়ের পরেই চেষ্টা করা হয়েছে কুলিয়া শহীদ মিনার ভেঙে ফেলার।
তবে সকল তাণ্ডবের সাক্ষী হয়ে আছে বুঝি দেবহাটা থানার গাজীর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা সুভাষ ঘোষের বাড়িটি। ১৩ তারিখ সকালেই শত শত মানুষ এসে সম্পন্ন মজবুত দোতলা বাড়িটি পেট্রোল ঢেলে আর গান পাউডার দিয়ে পুড়িয়ে সর্বস্বান্ত করে রেখে গেছে মাত্র আধাঘন্টার মধ্যে। কাঠের দরজা-জানালাগুলো কয়লা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
পুরুষেরা কেউ বাড়িতে নেই। শুধু বেশ কয়েকজন নারী মূল বাড়ির পাশে একটা খড়ের চালার নিচে পাশাপাশি আতঙ্কিত দাঁড়িয়ে আছেন। শতাধিক বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে এখানে। দেশত্যাগ করেছেন হিন্দু-মুসলিম অনেকেই।
চার
কালীগঞ্জে জামায়াত-শিবিরের তাণ্ডবে নিহত হয়েছেন বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোসলেম আলী, মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগের কর্মী শেখ আলাউদ্দিন। বাড়িঘর ভাঙচুর আর লুটপাট করা হয়েছে কৃষ্ণনগর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল মাজেদ আর সাধারণ সম্পাদক অমল কুমার ঘোষের। এই এক উপজেলাতেই ভাঙচুর আর অগ্নিসংযোগের শিকার হয়েছেন আওয়ামী লীগের ৪৫ নেতা-কর্মী।
কালীগঞ্জের নলতায় যখন আমরা জনসভা করি, তখন সন্ধ্যা নেমে গেছে। অনেক মাসের মধ্যে এই প্রথম একটি জনসমাবেশ পেয়ে মানুষের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। তৃণমূল নেতাদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার বোধ এবং এলাকায় অনুপস্থিত সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় নেতাদের ব্যাপারে চরম অভিযোগে পাল্টাপাল্টি অবস্থান চোখ এড়ায় না।
পাঁচ
আশাশুনির বুধহাটা বাজারে প্রথমেই সহিংসতার সাক্ষ্য হিসেবে দেখা গেল চন্দন দেবনাথের ‘সুলভ বস্ত্রবিতান’টি আর নেই। ১২ তারিখ রাতেই লুট করে আর আগুন জ্বালিয়ে শেষ করে দেওয়া হয়েছে সব। পাশেই তরুণ ঘোষের ক্ষতিগ্রস্ত স্টুডেন্ট টেইলার্স। তিনি কোনো কথাই বলতে পারলেন না। সম্পন্ন ব্যবসায়ী রাজ্যেশ্বর দাসের বাগদা চিংড়ির ঘের লুট হয়ে গেছে; তার দাবি মোট ৩০ লক্ষ টাকার সম্পদ হানি হয়েছে তার।
ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি এ টি এম আখতারুজ্জামানের আনিসুল আক্তার ট্রেডার্স গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে গোবিন্দ ব্যানার্জীর কম্পিউটার দোকান, আওয়ামী লীগের ইউনিয়ন যুগ্ম সম্পাদক সাজউদ্দিন সাজুর ঘড়ির দোকান। আগুন দেওয়া হয়েছে রাসেল স্মৃতি এবং শ্রমিক লীগের অফিসে। আমরা পথসভা করেছি ভাঙা শহীদ মিনারের পাদদেশে।
বিএনপি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আবদুল হান্নানের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানোর অভিযোগ উঠেছে। জানা গেল, এই থানার আওয়ামী লীগের সভাপতি বা সিনিয়র কোনো নেতা কেউ-ই দেখতে আসেননি ক্ষতিগ্রস্ত জনপদকে অভয় দিতে।
ছয়
জনজীবন স্বাভাবিক হয়নি তখনও। তবে সকলেই বলেছেন, যৌথবাহিনীর অপারেশনের আগে যে অবস্থা ছিল সেখান থেকে উত্তরণ হচ্ছে। পথে পথে আমরা শত শত গাছের গুঁড়ি দেখেছি। এইসব গাছ ফেলে অভাবনীয় কায়দায় রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করে, রাস্তা কেটে আসলে পুরো এলাকার জীবন বিপর্যস্ত করে ফেলা হয়েছিল।
প্রশাসনিক এবং সাধারণ নাগরিকদের অনেক পর্যায়ে কথা বলেই জানা গেল যে, ওই অঞ্চলটিকে রাষ্ট্রের মধ্যে আরেকটি রাষ্ট্র বানিয়ে ফেলারই প্রচেষ্টা ছিল বলে তারা মনে করেন।
যৌথবাহিনীর অপারেশনের বেশ কয়েকদিন পার হয়ে গেলেও পথেঘাটে লোক চলাচল সীমিত ছিল। আতঙ্ক কাটছে না। চলতি পথে বিজিবি আর পুলিশের জোর প্রহরা। কিন্তু পুলিশ প্রহরায় যে জীবন সে জীবনকে আর যাই হোক স্বাভাবিক বলা যায় না।
সবচেয়ে বড় কথা, আতঙ্কের যে অভয়ারণ্যের ভেতর তারা ছিলেন, সেটি সমূলে উৎপাটিত না হওয়া পর্যন্ত এই আতঙ্ক কাটার কারণ নেই। আমাদের প্রতিনিধি দল কলারোয়া থেকে ফিরে আসার পরেই মৃত আজহারুল ইসলামের পরিবারে গিয়ে হুমকি দিয়ে আসা হয়েছে।
কীভাবে কাটবে এই অবরুদ্ধ দশা
আমাদের সামনে নির্যাতন ও তাণ্ডবের যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে, তা প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি এবং তাণ্ডবের তুলনায় খুবই সামান্য এবং উপরিভাসা একটি অংশ বলে দাবি করেছেন প্রায় সবাই। গণমাধ্যমে সহিংসতা ও নির্যাতনের খবর যতটুকু প্রকাশিত হয়েছে বাস্তবে এর ভয়াবহতা অনেক বেশি।
প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রকৃত চিত্র উঠে আসা তো দূরে থাক, প্রচারিত হয়নি, অনেক স্থানের কথা এমনকি গণমাধ্যমে পৌঁছায়নি। ভয়াবহ এই সহিংসতায় এবং নিরাপত্তার অভাবে সাতক্ষীরার গ্রামাঞ্চল থেকে অনেকেই গোপনে দেশ ছেড়ে চলে গেছে। আওয়ামী রাজনীতি করার অপরাধে জামায়াত-শিবির তাদের উপর ক্রমাগত সহিংসতা চালালেও তাদের পাশে কেউ দাঁড়ায়নি।
সীমান্তের পাশ্ববর্তী এলাকা বলে চোরাচালানের অর্থনীতিও এই হামলাকারী শক্তিরই হাতে। তাদের অর্থনৈতিক শক্তি কত বেশি সেটি বোঝা যায় একটিমাত্র উদাহরণে যে, আন্তঃনগর বাস চলাচল চালু করা যাচ্ছে না, কারণ বাসগুলোর মালিকরা জামায়াত-শিবিরের। আমাদের প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, সাতক্ষীরায় যে জঙ্গি কার্যক্রম চলছে তার পেছনে আছে ইসলামী ব্যাংকসহ বিভিন্ন ইসলামি বাণিজ্যিক এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন ও সক্রিয় সহযোগিতা।
সীমান্তের পাশে অবস্থিত সাতক্ষীরায় জামায়েতের রাজনীতি বরাবরই শক্তিশালী। ভারতবিরোধী ও আওয়ামীবিরোধী মনোভঙ্গি রয়েছে প্রবল। গত পাঁচ বছরে এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ তো করা তো দূরে থাক, বহুধাবিভক্ত জেলা আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। তৃণমূল নেতা-কর্মীদের পাশে আস্থা হয়ে দাঁড়াননি তারা।
সব মিলিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেবার কোনো তাৎক্ষণিক উপায় বাতলানো খুবই মুশকিল। যৌথবাহিনীর অপারেশন যে পর্যন্ত করেছে, সেগুলো ছিল প্রশাসনিক পদক্ষেপ। কিন্তু রাষ্ট্র ও জনগণের সেখানে থেমে গেলে চলবে না। প্রহরা থাকার পাশাপাশি কতগুলো কাজ আন্তরিকভাবে করা দরকার, নয়তো এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি থামানো যাবে না। একই সহিংসতা আমরা দেখতে পাচ্ছি লালমনিরহাটসহ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতেও।
এই মুহূর্তের প্রয়োজন হল আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ানো। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা প্রতিরোধ করা। সরকারকে শক্ত হতে হবে। একই সঙ্গে আহবান জানাই গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দলগুলোর প্রতি, তারা যেন দলীয় নেতা-কর্মীদের ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করে।
গণমাধ্যমের বর্তমান দায়িত্বশীল ভূমিকা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি প্রত্যন্ত অঞ্চলের ঘটনাগুলো তুলে আনার ক্ষেত্রে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। এসব সংবাদ ‘ব্ল্যাক-আউট’ করা যাবে না।
এসব আশু কর্তব্য পালনের পাশাপাশি মূল যুদ্ধাপরাধী এবং সহিংস দল হিসেবে জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কোনো বিকল্প নেই। সাতক্ষীরার সহিংসতার ধরন প্রমাণ করে এসব সহিংসতা মোটেই নির্বাচনকেন্দ্রিক নয়, বরং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করা ও জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার যে দাবি উঠেছে তারই প্রতিক্রিয়া। এমনকি বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে অস্বীকার করতেও তাদের দ্বিধা নেই।
যারা একাত্তরে শুধু বাংলাদেশ রাষ্ট্র চায়নি এমন নয় বরং এদেশের মানুষের বিরুদ্ধে, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটন করেছে– সেইসব যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ত্বরান্বিত করে রায় দ্রুত কার্যকর করতে হবে। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে দলীয় নেতা-কর্মীদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। দেশকে তালেবানি রাষ্ট্র বানানোর যে পাঁয়তারা চলছে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তির ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ গঠন করে এই ফ্যাসিস্ট শক্তিকে পরাভূত করার কোনো বিকল্প নেই।
বাংলাদেশ রুখে দাঁড়াও।
লেখকবৃন্দ:
আবেদ খান, জিয়াউদ্দিন তারেক আলী, সাদেকা হালিম, সানজিদা আখতার, জিয়াউর রহমান, রোকেয়া প্রাচী ও কাবেরী গায়েন।
(লেখকরা সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও সাংস্কৃতিক কর্মী)
(সাতক্ষীরা থেকে ফিরে)
http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/14107
- Biplob Rahman | ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ ১২:৪৩582661
- অভিজিৎ রায় ও আরিফ রহমান
কাদের মোল্লার আসল নকল: একটি নির্মোহ অনুসন্ধান
ডিসেম্বর ২৩, ২০১৩
একাত্তরের কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী ও ‘মিরপুরের কসাই’ খ্যাত আবদুল কাদের মোল্লা
একাত্তরের কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী ও ‘মিরপুরের কসাই’ খ্যাত আবদুল কাদের মোল্লা
যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার ফাঁসি হয়েছে। এটা আমাদের জন্য একটা বিরাট অর্জন, বলাই বাহুল্য। এবারের বিজয় দিবস এবং সেই সঙ্গে নতুন বছরের আগমনটাই যেন ভিন্নমাত্রায় পৌঁছে গেছে এই অর্জনের ফলে। যুদ্ধাপরাধী রাজাকার-আলবদরদের বিচারের যে আকাঙ্ক্ষা একটা সময় আমাদের রক্তে শিহরণ তুলত, একটা অপ্রাপ্তির বেদনা গ্রাস করে ফেলত বছর খানেক আগেও, সেটা থেকে যেন আমরা মুক্তি পেয়েছি।
অন্তত একজন যুদ্ধাপরাধীর বিচারের কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি নানা ধরনের বিতর্ক, প্রতিবন্ধকতা, বিশ্বমোড়লদের তরফ থেকে দেওয়া আন্তর্জাতিক চাপ সবকিছু অগ্রাহ্য করে। এটা যে কত বড় অর্জন তা বোধহয় আমরা কেউ বুঝতে পারছি না। এই দিনটা দেখার স্বপ্ন আমরা বুকের মধ্যে লালন করেছিলাম বহুদিন ধরে।
কিন্তু আমরা কী দেখলাম? কাদের মোল্লার ফাঁসির পর বাংলাদেশের আপামর জনগণ যখন আনন্দোচ্ছ্বাস করছে, ঠিক তখনই এক মুখচেনা মহল সারা দেশে শুরু করেছিল সহিংসতা আর নৈরাজ্যের বিস্তার। জ্বালাও-পোড়াও, সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর আক্রমণ, বিচারকদের বাসায় বোমাবাজি সবই শুরু হল পুরোদমে। পাশাপাশি আরেকটা কাজও জামাতিদের তরফ থেকে করার প্রচেষ্টা চালানো হল– যেটা তারা সবসময়ই করে থাকে– বিভ্রান্তি ছড়ানো।
সত্য যখন উন্মোচিত আর দিনের আলোর মতো উদ্ভাসিত, বিভ্রান্তি আর মিথ্যে প্রচারণা– এটাই বোধহয় একমাত্র অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায় তখন। সাঈদীর ফাঁসির রায়ের পর চাঁদে সাঈদীর মুখচ্ছবি দেখা নিয়ে কী প্রচারণাটাই না চালানো হয়েছিল। অথচ পুরোটাই ছিল ফটোশপে এডিট করা খুব কাঁচা হাতের কাজ। যারা নিজেদের ধর্মের একনিষ্ঠ সেবক মনে করেন, তাদের সাচ্চা সৈনিকেরা এভাবে ফটোশপে ছবি এডিট করে যাচ্ছেতাই প্রচারণা চালায়-– ভাবতেও হয়তো অনেকের অবাক লাগবে।
কিন্তু যারা এই গোত্রটির কাজকর্মের নাড়ি-নক্ষত্রের হদিস জানেন, তারা অবাক হন না। শাহবাগ আন্দোলন শুরুর সময় একে কলঙ্কিত করতে নানা ধরনের রগরগে ছবি জোড়াতালি দিয়ে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল-– ‘প্রজন্ম চত্বর’ নাকি আসলে ‘প্রজনন চত্বর’। ওখানে নাকি রাত্রিবেলা গাঁজা খাওয়া হয়, ফ্রি সেক্স হয়, তরুণীরা সেখানে গেলেই ধর্ষিত হতে হয়, আরও কত কী।
কী না করেছিল তারা! মুম্বাই মেডিকেলের স্ক্যান্ডালের ছবির সঙ্গে ইমরান এইচ সরকারের চেহারা জোড়া দেওয়া, শাহবাগের জমায়েতে নাইট ক্লাবের নগ্নবক্ষা নারীর ছবি কাট অ্যান্ড পেস্ট করে লাগিয়ে দিয়ে ফেসবুকে ছড়ানো, নামাজরত এক পাকিস্তানি পুলিশকে শিবিরের কর্মী হিসেবে চালিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে প্রতীকী রশি নিয়ে কাদের মোল্লার ফাঁসির দাবি সম্বলিত ছবির শিরোনাম বদলে ‘ফাঁসির অভিনয় করতে গিয়ে শাহবাগে যুবক প্রাণ হারাল’ টাইপ মিথ্যে নিউজ তৈরি করা-– কোনো কিছুই বাদ যায়নি।
মুক্তমনা ব্লগে আমাদের সতীর্থ দিগন্ত বাহার ‘কথিত ইসলামি দল জামায়াতে ইসলামীর মিথ্যাচার সমগ্র’ শিরোনামের পোস্টে খুলে দিয়েছিলেন তাদের মিথ্যের মুখোশ; লিঙ্কটি পাঠকদের উদ্দেশ্যে দেওয়া গেল:
http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=33825
কাদের মোল্লার ফাঁসির পরেও নানা ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ানো হবে তা আগেই বোঝা গিয়েছিল। ফাঁসির আগে থেকেই কাদেরের তথাকথিত ‘অ্যালিবাই’ উপজীব্য করে ছড়ানো হয়েছিল মিথ্যে। কাদের ট্রাইব্যুনালকে বলেছিল:
“আজ এই কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, ১৯৭১ সালে মিরপুরে কসাই কাদের কর্তৃক যেইসব হত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল তার একটি অপরাধের সঙ্গেও আমার দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। কাদের মোল্লা বলেন, আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি আমি ১৯৭৩ সালের আগে কোনোদিন মিরপুরেই যাইনি।”
এই অ্যালিবাইকেই সত্য ধরে নিয়ে অনেকে জল ঘোলা করছেন। কিন্তু এটাই কি স্বাভাবিক নয় যে কাদের মোল্লার মতো এত বড় একটা পাষণ্ড এবং ঠাণ্ডা মাথার খুনি এ ধরনের অ্যালিবাই হাজির করেই নিজেকে আত্মরক্ষা করতে চাইবে? তার তো এটাই বলার কথা যে ঘটনার সময় সে ঘটনাস্থলে ছিল না।
এ নিয়ে সম্প্রতি ব্লগার নিঝুম মজুমদার কিছু গবেষণা করেছেন। মুক্তমনায় প্রকাশিত তার দি কিউরিয়াস কেইস অব কাদের মোল্লা এবং সাক্ষী মোমেনা শিরোনামের লেখাটি থেকে জানা যায়, এই কাদের মোল্লার একসময়ের সবচাইতে বড় ইয়ার দোস্ত ‘আক্তার গুণ্ডা’ ছিল কাদের মোল্লার মতোই এক ভয়াবহ খুনি। কাদের মোল্লা এই আক্তার গুণ্ডার সঙ্গে মিলেই মূলত ১৯৭১ সালে মিরপুরে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল।
১৯৭২ সালের দালাল আইনে এই আক্তার গুণ্ডার বিচার হয় এবং বিচারে তার ফাঁসিও হয়। মজার ব্যাপার হল, এই আক্তার গুণ্ডাও আজ থেকে ৪০ বছর আগে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে সেই একই ধরনের অ্যালিবাই হাজির করেছিল যে, সে ঘটনাস্থলে ছিল না, ছিল পাকিস্তানে। গণহত্যার সে কিছুই জানে না [‘আক্তার গুণ্ডা ভার্সেস বাংলাদেশ রায়’ দ্র:]।
রায়ের ফটোকপি দ্রষ্টব্য
রায়ের ফটোকপি দ্রষ্টব্য
কিন্তু কেউ এ ধরনের ‘ভেজা বিড়াল’ সাজতে চাইলেই যে সেটা ঠিক তা তো নয়। বহু চাক্ষুষ সাক্ষীই আক্তার গুণ্ডার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল এবং সে দোষী প্রমাণিত হয়েছিল।
কাদের মোল্লাও বিয়াল্লিশ বছর পরে তার প্রিয় গুণ্ডা বন্ধুর মতোই অ্যালিবাই হাজির করতে গিয়ে বলেছে, সে কস্মিনকালেও মিরপুরে যায়নি, গণহত্যা তো কোন ছাড়! এমন একটা ভাব যে, কাদের মোল্লা ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না। সহজ সরল এক ভালো মানুষকে যেন ‘কসাই কাদের’ ভেবে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।
একই কাজ তারা অন্য আসামির বেলায়ও করেছে। এই ‘সাকাচৌ’ সেই সাকা চৌধুরী নয়, সে ছিল পাকিস্তানে। এই দেলু রাজাকার সেই ‘দেইল্যা’ নয়। একই ধারাবাহিকতায় এখন বলছে, এই কাদের মোল্লা সেই কসাই কাদের নয়। কিন্তু তাদের এই কথা ঠিক কতটুকু যৌক্তিক– এই প্রবন্ধে আমরা সেটা পুংখানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখব।
একাত্তরে কাদের মোল্লার মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার ব্যাপারটা বহুভাবেই আসলে প্রমাণ করা যায়। শুরু করা যাক ইন্টারনেটে পাওয়া একটি বহুল প্রচারিত ছবি দিয়ে, যেখানে নিয়াজীর পেছনে আশরাফুজ্জামান এবং কাদের মোল্লাকে দেখা যাচ্ছে। আশরাফুজ্জামান বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে মূল ভূমিকা পালন করেছিল, বর্তমানে ব্রিটেনে পলাতক আলবদর নেতা মুঈনুদ্দীনের সঙ্গে মিলে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান খ্যাত ১৮ জন বুদ্ধিজীবীকে ঘর থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করে তারা। মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মুঈনুদ্দীনের সঙ্গে আশরাফুজ্জামান খানেরও ফাঁসির আদেশ হয়েছে সম্প্রতি। সেখানেই বীরদর্পে কাদের মোল্লা দণ্ডায়মান। মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত ‘মুক্তিযুদ্ধ কোষ’ বইয়ে ছবিটির হদিস পাওয়া যায়। ইউটিউবেও এর একটি ভিডিও আছে।
সেই ঐতিহাসিক ছবি, নিয়াজীর পাশে কাদের মোল্লা
সেই ঐতিহাসিক ছবি, নিয়াজীর পাশে কাদের মোল্লা
সেই বিয়াল্লিশ বছর আগের ছবিটির কথা যদি আমরা বাদও দিই, আজকের দিনের প্রসঙ্গ গোণায় ধরলেও, কাদের মোল্লার পরিচয় গোপন থাকে না। তার ফাঁসির পর পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চৌধুরী নিসার আলী খান বলেছেন–
“১৯৭১ সালের ঘটনার বিয়াল্লিশ বছর পর কাদের মোল্লার ফাঁসি একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বস্ততা ও সংহতির জন্য কাদের মোল্লাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। তার মৃত্যুতে সকল পাকিস্তানি মর্মাহত এবং শোকাহত।’’
তিনি আরও বলেন, “এ ঘটনার মাধ্যমে পুরনো ক্ষত আবারও জাগিয়ে তোলা হয়েছে।”
জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের প্রধান মুনাওয়ার হাসান কাদের মোল্লাকে তাদের ‘বাংলাদেশি সহচর’ এবং ‘পাকিস্তানের মুক্তিযোদ্ধা’ আখ্যায়িত করে তার ফাঁসিকে ‘শোচনীয়’ বলে মন্তব্য করেন। শুধু তাই নয়, কাদেরের ফাঁসি দেওয়ায় বাংলাদেশ আক্রমণের জন্য নিজেদের সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল জামায়াত-ই-ইসলামী। ‘কসাই কাদের’ আর ‘কাদের মোল্লা’ এক ব্যক্তি না হলে পাকিস্তানি জামাতের এত শখ হল কেন এই বিবৃতি দেবার?
বারবারই বাংলাদেশের জামাত দাবি করে এসেছে কসাই কাদের আর কাদের মোল্লা এক ব্যক্তি নয়, তারা হাজির করে কাদেরের জবানবন্দি, যেখানে কাদেরের অ্যালিবাই ছিল:
“১৯৭১ সালের ১২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরের আমিরাবাদ চলে যান এবং মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়ই তিনি গ্রামের বাড়িতে অবস্থান করেন। গ্রামে অবস্থানকালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও হাইস্কুলের প্রায় ৩০ জন ছাত্রের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ থেকে ১ মে পর্যন্ত (পাকিস্তান সেনাবাহিনী ফরিদপুরে পৌঁছার দিন পর্যন্ত) অন্যদের সঙ্গে তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ চালিয়ে যান। সেনাবাহিনীর জুনিয়র কমিশনড অফিসার (জেসিও) মফিজুর রহমান ডামি রাইফেল দিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দেন।” (ইত্তেফাক)
কাদের এবং তার দলবলের দাবি অনুযায়ী সে একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধা ছিল; অথচ পাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু স্পষ্ট করেই বলেছেন–
‘‘কাদের মোল্লা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অখণ্ড পাকিস্তানের সমর্থক ছিলেন এবং তা তিনি নিজের মুখেই বলেছিলেন।’’
নিজের মুখে কাকে এ কথা বলেছেন কাদের? তিনি বিরাট মুক্তিযোদ্ধা হয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে তো নিজেকে ‘অখণ্ড পাকিস্তানের সমর্থক ছিলেন’ সেটা বলার কথা নয়। যেভাবে নিউজগুলো পত্রিকায় এসেছে তাতে মনে হয় নিসার সাহেবের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল এবং তিনি কাদেরের পরিচয় সম্বন্ধে যথেষ্টই ওয়াকিবহাল। না হলে নিসার সাহেব বলবেন কেন যে, পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বস্ততা ও সংহতির জন্য কাদের মোল্লাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই?
এগুলো থেকে কী প্রমাণিত হয়? কসাই কাদের আর কাদের মোল্লা দুই ব্যক্তি? সেই হিন্দি সিনেমার মতো আসল কাদেরকে জীবিত রেখে তার ‘জরুয়া’ ভাইকে ঝোলানো হয়েছে? মোটেও তা নয়। বরং সম্প্রতি একটি পত্রিকায় ড. জিনিয়া জাহিদ যে কথাগুলো তার ‘কাদের মোল্লা মরিয়া প্রমাণ করিল’ শিরোনামের লেখায় উল্লেখ করেছেন সেটাই সত্য হিসেবে প্রকট হয়ে উঠেছে–
‘‘সেই যে রবীন্দ্রনাথের কাদম্বিনী গল্পে পড়েছিলাম, ‘কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে, সে মরে নাই’, ঠিক তেমনি কাদের মোল্লার ফাঁসিতে মৃত্যুর পর তাদের সমগোত্রীয় পাকি-জামায়াতের স্বীকারোক্তিতে এটাই প্রমাণ হল যে, এই কাদের মোল্লাই একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লা এবং এই কাদের মোল্লাই আমৃত্যু পাকি-সমর্থক ছিলেন। এই কাদের মোল্লা একাত্তরেও যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী ছিলেন, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি স্বাধীনতাবিরোধী ছিলেন।’’
মিথ্যাচারী এবং মিথ্যার বেসাতি করা জামাত-শিবির কেবল কাদের মোল্লাকে কসাই কাদের থেকে পৃথক করার মিশন নিয়েই মাঠে নামেনি, তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পর্যন্ত প্রমাণ করতে চেয়েছে। সে নাকি একাত্তরের যুদ্ধে গ্রামে বসে কলেজ ও হাইস্কুলের প্রায় ৩০ জন ছাত্রের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ থেকে ১ মে পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ চালিয়ে গেছে। মিথ্যাচারের একটা সীমা থাকে! অথচ এই কাদের মোল্লাই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে করেছিল চরম বিদ্রূপাত্মক উক্তি, যেটা ২০০৭ সালে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়েছিল:
“কেউ সুন্দরী নারীর লোভে, কেউ হিন্দুর সম্পদ লুণ্ঠন, কেউ ভারতীয় স্বার্থরক্ষায় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। কেউই আন্তরিকতা কিংবা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেননি।” (কাদের মোল্লা, সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ৩১ অক্টোবর, ২০০৭)
এর বাইরেও বহুবারই কাদের মোল্লার বাংলাদেশ বিরোধিতা এবং বাংলাদেশের প্রতি অবজ্ঞার ব্যাপারটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যেমন এ বছরের নভেম্বর মাসে বিডিনিউজ টোয়েন্টি ফোর ডটকমে প্রকাশিত এই নিউজটি দ্রষ্টব্য:
কাদের মোল্লার দম্ভোক্তি
কাদের মোল্লার দম্ভোক্তি
এই লোক ‘কসাই কাদের’না হয়ে মুক্তিযোদ্ধা হবে, সেটা কি কোনো পাগলেও বিশ্বাস করবে?
এবার কিছু চাক্ষুষ সাক্ষীর বয়ান শোনা যাক।
এক: ফজর আলী
“মিরপুর ১১ নম্বর বি ব্লকের বাসিন্দা ফজর আলী গণতদন্ত কমিশনকে দেওয়া সাক্ষ্যে তার ছোট ভাই মিরপুর বাংলা কলেজের ছাত্র পল্লবকে নৃশংসভাবে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন কাদের মোল্লাকে। ২৯ মার্চ নবাবপুর থেকে পল্লবকে তুলে নিয়ে আসে কাদের মোল্লার সাঙ্গপাঙ্গরা। এরপর তার নির্দেশে ১২ নম্বর থেকে ১ নম্বর সেকশনের শাহ আলী মাজার পর্যন্ত হাতে দড়ি বেঁধে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ছাত্রলীগ কর্মী পল্লবকে। এরপর আবার ১ নম্বর থেকে ১২ নম্বর সেকশনের ঈদগাহ মাঠে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে টানা দু’দিন একটি গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয় পল্লবকে। ঘাতকরা এরপর তার দু’হাতের সবকটি আঙুল কেটে ফেলে।
৫ এপ্রিল একটি মজার খেলা খেলে কাদের মোল্লা। সঙ্গীদের নির্দেশ দেওয়া হয় গাছে ঝোলানো পল্লবকে গুলি করতে, যার গুলি লাগবে তাকে পুরষ্কার দেওয়া হবে। পরে কাদের মোল্লার সঙ্গী আক্তার পল্লবের বুকে পাঁচটি গুলি করে পরপর। পল্লবের লাশ আরও দু’দিন ওই গাছে ঝুলিয়ে রাখে কাদের মোল্লা, যাতে মানুষ বোঝে ভারতের দালালদের জন্য কী পরিণাম অপেক্ষা করছে। ১২ নম্বর সেকশনে কালাপানি ঝিলের পাশে আরও ৭ জন হতভাগার সঙ্গে মাটিচাপা দেওয়া হয় পল্লবকে।
অক্টোবরে মিরপুর ৬ নম্বর সেকশনে একজন মহিলা কবি মেহরুন্নেসাকে প্রকাশ্যে নিজের হাতে নির্মমভাবে হত্যা করে কাদের মো্ল্লা। প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন সিরাজ এই নৃশংসতায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। মূলত বিহারিদের নিয়ে একটি খুনে দল তৈরি করেছিল কাদের মোল্লা। আর বুলেট বাঁচাতে জবাই করা ছিল তার কাছে বেশি প্রিয়।”
দুই: ফিরোজ আলী
“ফিরোজ আলী তখন মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তি, একাত্তর সালে সপরিবারে মিরপুরে থাকতেন। ২৫ মার্চের পর তার ভাই পল্লবকে শুধু ‘জয় বাংলা’র অনুসারী হওয়ার অপরাধে কাদের মোল্লার নির্দেশে অবাঙলি গুণ্ডারা অকথ্য নির্যাতন করে নির্মমভাবে হত্যা করে। তখন সমগ্র মিরপুরে হত্যা আর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে কাদের মোল্লা ও তার অনুসারী অবাঙালিরা। জবাই করে বাঙালি হত্যা ছিল তাদের প্রতিদিনের রুটিনমাফিক কাজ। একেকটি জবাই’র আগে ঘোষণা দিত যারা বাংলাদেশ তথা ‘জয় বাংলা’র অনুসারী, তারা বিধর্মী-নাস্তিক-ভারতের দালাল, এদের হত্যা করা সওয়াবের কাজ!
এমন জবাই’র নেশা বেড়ে যাওয়ায় কাদের মোল্লার নাম তখন এ তল্লাটে আতঙ্কের সমার্থক শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্থানীয়রা আবদুল কাদের মোল্লাকে ‘কসাই কাদের’নামকরণ করে। গরু জবাই-এর মতো মানুষ জবাই-এ দক্ষতার নামডাকে (!) কসাই কাদের ‘মিরপুরের কসাই’ নামেও পরিচিতি লাভ করে ব্যাপক।
কসাই কাদের মোল্লার প্রতিহিংসার শিকার শহীদ পল্লবের ডাক নাম ছিল ‘টুনটুনি’। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে বেশ কিছু চলচ্চিত্রে পার্শ্ব অভিনেতা হিসেবে অভিনয় করে সুখ্যাতি অর্জন করে প্রতিপক্ষের চক্ষুশূল হন পল্লব। এ কথা জানান ফিরোজ আলীর স্ত্রী।
পল্লব ছাড়াও কবি মেহেরুন্নেছা নামের এলাকায় খুবই শান্ত-নিরীহ প্রকৃতির বাঙালি গৃহবধূ কসাই কাদের মোল্লার প্রতিহিংসার বলি হন। মিরপুর ৬ নং সেকশন, ডি ব্লক মুকুল ফৌজের মাঠের কাছাকাছি একটি বাড়িতে থাকতেন কবি মেহেরুন্নেছা। তিনি ছিলেন কবি কাজী রোজীর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী।
কসাই কাদের মোল্লার নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে লেখালেখির অপরাধে মেহেরুন্নেছাসহ তার পুরো পরিবারকে বটি দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল! এরপর টুকরো করা মাংসখণ্ডগুলো নিয়ে ফুটবলও খেলা হয়েছিল ৬ নং মুকুল ফৌজের মাঠে! কসাই কাদেরের নির্দেশে ৩০/৩৫ জনের একটি অবাঙালি ঘাতকের দল, মাথায় লাল ফিতা বেঁধে, ধারালো তলোয়ারে সজ্জিত হয়ে অংশ নেয় কবি মেহেরুন্নেছা ও তার পরিবারের হত্যাযজ্ঞে!”
তিন: কাদের মোল্লার বন্ধু মোজাম্মেল এইচ খান
ড. মোজাম্মেল এইচ খান ছিলেন রাজেন্দ্র কলেজে কাদের মোল্লার সহপাঠী। তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন কাদের মোল্লার কাজকর্ম, একাত্তরে এবং তার পরবর্তী সময়। তিনি ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ দৈনিক জনকণ্ঠে একটি চমৎকার লেখা লিখেছিলেন, ‘‘কাদের মোল্লাকে নিয়ে ‘আমার দেশ’ পত্রিকার আষাঢ়ে কাহিনী’’ শিরোনামে:
“কাদের মোল্লা হলেন আমাদের রাজেন্দ্র কলেজের ১৯৬৪-১৯৬৬ এইচএসসি ব্যাচের সবচেয়ে পরিচিত মুখ এবং তিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমধিক পরিচিত ব্যক্তি, তা সে যে কারণেই হোক না কেন। এমনকি তিনি আমাদের সে সময়ের আরেক সহপাঠী বেগম জিয়ার বিগত শাসনামলের মন্ত্রী আলী আহসান মুজাহিদকেও পরিচিতির দিক দিয়ে ছাড়িয়ে গেছেন; যদিও মুজাহিদও একইভাবে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলার অপেক্ষায় রয়েছেন, যদি না সুপ্রীম কোর্ট তার দণ্ডকে উল্টে দেয়।’’
ড. মোজাম্মেল খান তাঁর প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, এমনকি কাদেরের পরিবারের দেওয়া বিবরণেও তিনি ১৯৭২ সালে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে ‘তার ডিপার্টমেন্টে তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন’ এ ধরনের কোনো দাবি নেই; বরং তিনি যে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন সে কথাই বলা হয়েছে। এমনকি তিনি যে কোনো ডিগ্রি পেয়েছেন সেটার কোনো উল্লেখ নেই।
তেমনিভাবে ‘যুদ্ধের পুরো সময় তিনি গ্রামেই অবস্থান করেন’ সে কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তিনি যে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন সেটার কোনো উল্লেখ নেই। ‘শেখ মুজিবুর রহমান তাকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে চাকরিও দিয়েছিলেন’ সেটাও কাদেরের পরিবার উল্লেখ করেনি; অথচ ‘আমার দেশ’ এবং ‘বাঁশের কেল্লা’রা চাঁদে সাঈদীর মুখচ্ছবি দর্শনের মতো করে ঠিকই ‘সত্যের সন্ধান’ পেয়ে গেছে!
জামাতিদের পক্ষ থেকে আরও ছড়ানো হয়েছে যে, কাদের মোল্লা নাকি ‘ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট’ হওয়া ‘গোল্ড মেডেলিস্ট’ ছাত্র ছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা মোটেই সে রকমের নয়। মোল্লার ‘ভালো ছাত্রত্বের’ গুমোর ফাঁস করে দিয়েছেন মোজাম্মেল খান তাঁর কলামে:
‘‘এইচএসসির ফলাফলে কাদের গড়পড়তা ছাত্রের থেকে নিচে ছিল যার ফলে সরাসরি সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়ার যোগ্যতা অর্জন করেনি। সে রাজেন্দ্র কলেজেই বিএসসি পড়ে (১৯৬৬-১৯৬৮) এবং ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস কোর্সে এমএসসিতে ভর্তি হয় যেটা তার পরিবারের দেওয়া সময়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যাচ্ছে; যদিও তার পরিবারের ভাষ্য অনুযায়ী সে এসএসসি পাস করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে। অথচ কাদের আমাদের সঙ্গে এইচএসসি পাস করেছে ১৯৬৬ সালে।
তাহলে এর মাঝে দুই বছরের বেশি সময় সে কী করেছে? তার পরিবার বলেছে সে স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসে এবং ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সেখানে অধ্যয়ন করে। এ বক্তব্যের প্রথম অংশটুকু সত্য নয় এবং যে কোনো পাঠকই বুঝতে পারবেন দুই বছরের এমএসসি ডিগ্রির জন্য ৮ বছর (১৯৬৯-১৯৭১, ১৯৭২-১৯৭৭) বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করার হিসেব মেলানো যায় না।’’
বর্তমানে কানাডাপ্রবাসী অধ্যাপক মোজাম্মেল খান সেই একই প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন যখন তিনি ১৯৭৯ সালে দেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন, কীভাবে কাদের মোল্লার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়েছিল এবং কীভাবে সে উল্লসিত হয়ে মোজাম্মেল সাহেবকে বলেছিল ‘জয় বাংলা’কে সরিয়ে ‘জিন্দাবাদ’ রাজত্ব করে চলেছে:
“১৯৭৩ সালের প্রথমার্ধ্বে আমি যখন উচ্চশিক্ষার জন্য দেশের বাইরে আসি তখন জানতাম না কাদের কোথায় আছে। ১৯৭৯ সালে আমি দেশে বেড়াতে গেলে একদিন যখন ঢাকার মগবাজারের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি তখন পেছন থেকে একজন আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘তুই কি মোজাম্মেল? আমি কাদের।’ আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল, ‘কাদের, তুই বেঁচে আছিস?’ কাদেরের উত্তর ছিল, ‘হ্যাঁ, আমি ভালোভাবে বেঁচে আছি এবং এখন আমি দৈনিক সংগ্রামের নির্বাহী সম্পাদক। তোর জয় বাংলা এখন এদেশ থেকে নির্বাসিত; ফিরে এসেছে আমাদের জিন্দাবাদ এবং এটা এখন প্রচণ্ডভাবে জাগ্রত।’ যেহেতু কাদের সত্য কথাই বলেছিল, সেহেতু আমি ওর কথার কোনো জবাব দিতে পারিনি।
কয়েক সপ্তাহ পরে আমি যখন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাই তখন সংবাদপত্রে পড়লাম প্রেসক্লাবে একটি বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিল কাদের মোল্লা; একেই বলে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস!”
মোজাম্মেল এইচ খান ইংরেজিতেও এ নিয়ে একটি লেখা লিখেছেন Quader Mollah: fact versus fiction শিরোনামে যেটা মুক্তমনা সাইটের ইংরেজি ব্লগে প্রকাশিত হয়েছে।
ড. মোজাম্মেল এইচ খান কাদের মোল্লার ফাঁসির পর স্ট্যাটাসও দিয়েছিলেন, ‘‘বিদায় এককালের সহপাঠী কাদের মোল্লা। তোমার এ পরিণতিতে আমি শোক করতে পারছি না’’ বলে:
মোজাম্মেল খানের ফেসবুক স্ট্যাটাস
মোজাম্মেল খানের ফেসবুক স্ট্যাটাস
পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আমরা এ লেখায় এখন পর্যন্ত মোমেনা বেগমের কথা আনিনি। এই নারী কাদের মোল্লার দ্বারা ধর্ষিত হয়েছিলেন। তাঁর পরিবারের সব সদস্যকে চোখের সামনে মরতে দেখেছেন। বিডিনিউজ টোয়েন্টি ফোর ডটকমে প্রকাশিত তাঁর ভাষ্য থেকে জানা যায়, বেলা ডোবার আগে কাদের মোল্লার নেতৃত্বে মোমেনাদের বাড়িতে হামলা হয়। “আব্বা দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া আসে এবং বলতে থাকে ‘কাদের মোল্লা, মেরে ফেলবে’। আক্তার গুণ্ডা, বিহারিরা তারা ও পাক বাহিনীরা দৌড়াইয়া আসছিল। আব্বা ঘরে এসে দরজার খিল লাগায়ে দেয়।”
হযরত দরজা এঁটে সন্তানদের খাটের নিচে লুকাতে বলেন। মোমেনার সঙ্গে তার বোন আমেনা বেগমও খাটের নিচে ঢোকে। তখন দরজায় শোনেন কাদের মোল্লাসহ বিহারিদের কণ্ঠস্বর, ‘এই হারামি বাচ্চা, দরজা খোল, বোম মার দেঙ্গা।’ শুরুতে দরজা না খোলায় বাড়ির দরজার সামনে একটি বোমা ফাটানো হয়। এক পর্যায়ে হযরতের স্ত্রী একটি দা হাতে নিয়ে দরজা খোলেন। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করা হয়।
“আব্বা তখন আম্মাকে ধরতে যায়। কাদের মোল্লা পেছন থেকে শার্টের কলার টেনে ধরে বলে, ‘এই শুয়ারের বাচ্চা, এখন আর আওয়ামী লীগ করবি না? বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যাবি না? মিছিল করবি না? জয় বাংলা বলবি না?’ আব্বা হাতজোড় করে বলে, ‘কাদের ভাই, আমাকে ছেড়ে দাও’। আক্তার গুন্ডাকে বলল, ‘আক্তার ভাই, আমাকে ছেড়ে দাও’।” তবু না ছেড়ে হযরত আলীকে টেনে-হিঁচড়ে ঘরের বাইরে নিয়ে যায় বিহারিরা।
সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এরপর কাঁদতে কাঁদতে চোখের সামনে ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দেন মোমেনা। “দাও দিয়ে আমার মাকে তারা জবাই করে। চাপাতি দিয়ে খোদেজাকে (বোন) জবাই করে। তাসলিমাকেও (বোন) জবাই করে। আমার একটি ভাই ছিল বাবু, বয়স ছিল দুই বছর, তাকে আছড়িয়ে মারে। বাবু মা মা করে চিৎকার করছিল,” বলতে গিয়ে অঝোরে কাঁদেন মোমেনা।
বাবুর চিৎকার শুনে খাটের তলায় লুকানো আমেনা চিৎকার দিলে তার অবস্থান জেনে যায় হামলাকারীরা। মোমেনা বলেন, “আমেনাকে তারা টেনে বের করে, সব কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে ফেলে। এরপর তাকে নির্যাতন করতে থাকে। আমেনা অনেক চিৎকার করছিল, একসময় চিৎকার থেমে যায়।”
কাঁদতে কাঁদতে প্রায় অজ্ঞান মোমেনা এরপর শোনান নিজের ওপর নির্যাতনের বর্ণনা।
মোমেনার সাক্ষ্য নিয়ে কম জল ঘোলা করেনি জামাতিরা। বলা হচ্ছে মোমেনা নাকি তিনবার সাক্ষ্য দিয়েছেন। একেক জায়গায় নাকি তার একেক রকম বক্তব্য। তিনি নাকি মিরপুরের জল্লাদখানার জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাতে কাদের মোল্লার নাম ছিল না। তিনি নাকি বোরকা ও নেকাবে মুখ আবৃত করে ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত হয়েছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।
এগুলো আসলে একেবারেই বানোয়াট প্রোপাগাণ্ডা। ব্লগার নিঝুম মজুমদার মুক্তমনায় প্রকাশিত দি কিউরিয়াস কেইস অব কাদের মোল্লা এবং সাক্ষী মোমেনা প্রবন্ধে প্রতিটি কুযুক্তিই খণ্ডন করেছেন। পাঠকেরা প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে পারেন।
আসলে মোমেনা মূলত তার জীবনে একবারই সাক্ষ্য দিয়েছেন তাঁর পিতা-মাতা আর ভাই-বোন হত্যা মামলায়। আর সারাজীবন যদি অন্য কোনো বক্তব্য দিয়ে থাকেন তবে সেটি আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি, হবার কথাও নয়।
মোমেনার যে জবানবন্দির কথা বলে জল ঘোলা করার চেষ্টা করা হয়– যেটি তিনি মিরপুরের জল্লাদখানার জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে দিয়েছেন বলে ‘বাঁশের কেল্লা’রা ক্রমাগতভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে, সেটি কিন্তু মাননীয় আদালতের চোখে সম্পূর্ণভাবে অসাড় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। যে অভিযোগ আদালতে ধোপে টেকেনি, সেটা যদি ‘কন্সপিরেসি থিওরি’ হিসেবে কেউ ছড়িয়ে বেড়ায় তখন তার ঘাড়েই দায় বর্তায় সেটা প্রমাণ করার, আমাদের ওপর নয়।
নিঝুম মজুমদারের অনুসন্ধানী পোস্ট থেকে জানা যায়, ‘‘কাদেরের আইনজীবী একটা কাগজ নিয়ে এসেছে ছবি ফরম্যাটে [ফটোস্ট্যাট] যাতে কোনো কর্তৃপক্ষের সাক্ষর নেই, সাক্ষ্যদাতার সাক্ষর নেই, এটি কীভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে সেটির ব্যাখ্যা নেই কিংবা বলতে পারেনি, এই বিচারের আইনের ধারা ৯, সাব সেকশন ৫-এর নিয়ম ফলো করা হয়নি, এটা কোনো সাক্ষ্য নয়।’’ [ট্রাইব্যুনাল-২ এর মামলার রায়, পৃষ্ঠা ১১৯, প্যারা ৩৯১-৩৯২ দ্র:]
আর কোনো জাদুঘরের সাক্ষাতকারে যদি মোমেনা কাদের মোল্লার নাম উল্লেখ না করে থাকেন কিংবা আদালতে যদি বোরকা পরে সাক্ষ্য দিতে এসে থাকেন তাতেই-বা কী সমস্যা ছিল? যে মানুষটি তাঁর পরিবারের প্রত্যেককে চোখের সামনে নৃশংসভাবে খুন হতে দেখেছেন, যে ব্যক্তি গত বিয়াল্লিশটি বছর শোক-দুঃখ-হাহাকার নিয়ে বড় হয়েছেন, কাতর হয়েছেন অমানুষিক যন্ত্রণায়, তিনি কি নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে প্রয়োজনমাফিক ব্যবস্থা নেবেন না? মোমেনা বেগম নিজ মুখেই তো বলেছেন যে, আদালতে সাক্ষ্যের আগে তিনি ভয় এবং নিরাপত্তার কারণে অনেক সময়ই নাম গোপন করে গেছেন:
“অনেক মানুষ আমার কাছে এসেছিল ও আমার ছবি নিয়েছিল; কিন্তু ভয়ের কারণে আমি কাউকে কাদের মোল্লা এবং আক্তার গুণ্ডার নাম বলি নাই।”
তাঁর ভয়ের ব্যাপারটা তো অমূলক নয়। জামাত-শিবিরের সন্ত্রাস সম্বন্ধে কেউ তো অজ্ঞ নয়। সাঈদীর মামলায় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী গোলাম মোস্তফা নিহত হননি? তারা বোধহয় একই পরিণতি মোমেনা বেগমের জন্যও চেয়েছিল। সেটা বাস্তবায়িত না হওয়াতেই কি এত ক্ষোভ আর মিথ্যাচার?
আর এই মামলায় তো কেবল মোমেনা বেগম নয়, অনেক সাক্ষীই ‘ক্যামেরা ট্রায়ালে’ সাক্ষ্য দিয়েছেন। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে এই জাতীয় ট্রায়ালের ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলো প্রচলিত রয়েছে, সে ধরনের নিয়ম মেনেই সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। অথচ হঠাৎ করেই মোমেনা বেগমের সাক্ষ্য কেন্দ্র করে গোয়েবলসীয় প্রচারণায় মেতে উঠেছেন মুক্তিযুদ্ধবিরোধী মহল।
মজার ব্যাপার হচ্ছে, অনেকেরই হয়তো জানা নেই– সাক্ষী নিয়ে বরং ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়েছিলেন কাদের মোল্লার পক্ষের আইনজীবীরাই। মোল্লার এক ভিকটিম পল্লবের ভাইয়ের স্ত্রী মোসাম্মৎ সায়েরাকে তারা হাত করতে চেষ্টা করেন, তাকে দিয়ে মিথ্যে সাক্ষ্য দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু মিথ্যে কথা বলতে গিয়ে লেজেগোবরে করে ফেলেছেন তিনি। (ট্রাইব্যুনালের রায়ের প্যারা ১৮২-১৮৯ দ্রঃ)। মজা হচ্ছে এগুলো নিয়ে গোয়েবলস বাবাজি আর তার সাগরেদরা সব নিশ্চুপ।
পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই, কেবল মোমেনা বেগম নয়, অনেকের সাক্ষ্য থেকেই জানা গেছে এই কাদের মোল্লাই– আক্তার গুণ্ডা, নেহাল, হাক্কা গুণ্ডা যারা মীরপুরে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল একাত্তরে– তাদের সহচর ছিল। এদের অনেকেই সরাসরি কাদেরকে নিজ চোখে শনাক্ত করেছিল। সেই চাক্ষুষ সাক্ষীর মধ্য থেকেই দু’জনের বয়ান উপরে এই লেখাতেই উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আছেন প্রধান সাক্ষী মুক্তিযোদ্ধা শহিদুল হক মামা, যিনি আদালতে দাঁড়িয়ে কাদের মোল্লাকে শনাক্ত করেছিলেন। কাদের মোল্লার আসল-নকল নিয়ে প্রধান সাক্ষী শহিদুল হক মামা ‘একাত্তর’ টিভিতে ১৩.১২.২০১৩, ইউটিউব ভিডিও:
তারপরও বেশিরভাগ মুক্তিযুদ্ধবিরোধী, জামাত-সমর্থক গোষ্ঠীর ধারণা কাদের নির্দোষ ভালো মানুষ। কিছু “বিকৃত তথ্য”এবং তার সঙ্গে একগাদা নির্জলা ‘মিথ্যাচার’ জড়িয়ে সারাদিন এরা করে যাচ্ছে ধর্মব্যবসা। গোয়েবলসীয় কায়দায় তারা বলেই চলেছে কাদের মোল্লা আর কসাই কাদের নাকি এক নয়। যারা এখনও বলে, কসাই কাদের আর মোল্লা কাদের এক নয়, তাদের কাছে আমাদের একটাই প্রশ্ন–
‘কসাই কাদের’টা তাইলে গেল কোথায়? রাতারাতি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নাকি?
আমরা মনে করি, কাদের আর কসাই একই লোক সেটা আদালতেই প্রমাণিত হয়ে গেছে আর শাস্তিও দেওয়া হয়েছে, আমাদের নতুন করে আর কিছু প্রমাণের নেই। ‘বার্ডেন অব প্রুফ’টা তাদের কাঁধেই যারা মনে করেন দুই কাদের ভিন্ন ব্যক্তি। আমরা মনে করি, তারা সেটা প্রমাণ করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। অন্যদিকে মোমেনার মতো চাক্ষুষ সাক্ষীরাই যথেষ্ট যাদের পরিবার কাদের মোল্লার হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন। তাকে চিনতেন তার বন্ধু এবং সহপাঠীরাও, যেমন ড. মোজাম্মেল এইচ খানের মতো ব্যক্তিরা।
বিপরীত পক্ষ বরাবরই সেগুলো অস্বীকার করে ‘বাঁশের কেল্লা’ আর গোলাম মওলা রনির মতো লোকজনের কথাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। আসুন দেখি কতটা নির্ভরযোগ্য এই গোলাম মাওলা রনি, যে সরকারদলীয় সাংসদ অতীতে সাংবাদিক পেটানোসহ বহু কারণেই বিতর্কিত হয়ে সংবাদের শিরোনাম হয়েছিলেন।
কাদের মোল্লার ফাঁসির আগ মুহূর্তে তিনি একটি চিরকুট প্রকাশ করেন ফেসবুকে এবং দাবি করলেন রনির সঙ্গে মোল্লা সাহেবের কারাগারে সাক্ষাত হয়েছিল এবং সেই সুবাদে মোল্লা রনিকে একটা চিঠি দেন, সেখানে ইনিয়ে বিনিয়ে কাদের মোল্লার ‘একটু উস্তাভাজি খাওয়ার’ বাসনা ছিল আর মোল্লা নাকি রনিকে এও অনুরোধ করে বলেছিলেন, ‘আমার ফাঁসির পর একবার হলেও বল বা লিখ যে, কাদের মোল্লা আর কসাই কাদের এক ব্যক্তি নয়’। এই সেই চিঠি:
রনিকে লেখা মোল্লার তথাকথিত চিরকুট
রনিকে লেখা মোল্লার তথাকথিত চিরকুট
এই চিঠি পুঁজি করেই সহানুভূতির বাণিজ্য শুরু করেছিলেন গোলাম মওলা রনি ফেসবুকে। গোলাম শুরু করেছিলেন কাদেরের গোলামী।
কিন্তু আমরা যখন এ নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করলাম তখন বেরিয়ে এল অন্য তথ্য, বিশেষ করে যখন কাদের মোল্লার স্ত্রীকে লেখা একটি চিঠি অনলাইনে প্রকাশিত হয়ে যায়:
স্ত্রীকে লেখা মোল্লার চিঠি
স্ত্রীকে লেখা মোল্লার চিঠি
ব্যাপারটা কি লক্ষ্য করেছেন পাঠক???
পাঠকদের সুবিধার জন্য দুটো ছবি একসঙ্গে দেওয়া গেল। একটু ভালো করে খেয়াল করলেই বোঝা যাবে যে ‘ডাল মে কুছ কালা হ্যায়’:
দুটো চিঠিতে হাতের লেখার পার্থক্য স্পষ্ট
দুটো চিঠিতে হাতের লেখার পার্থক্য স্পষ্ট
গোলাম মওলা রনি সাহেবের যে ফেসবুক স্ট্যাটাসটা নিয়ে এত চেঁচামেচি, এখন তো থলের বেড়াল বেরিয়ে এসেছে; সেই চিরকুটের সিগনেচার আর কাদের মোল্লার পরিবারের কাছে লেখা চিঠির সিগনেচার ভিন্ন!
লেখাটি শেষ করার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারও পাঠকদের মনে করিয়ে দিতে চাই। এই ট্রাইব্যুনাল যদি স্বচ্ছ না হয়, যদি কাদের সত্যই মনে করে যে তাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে, তাহলে ট্রাইব্যুনালের প্রথম রায়ের পর কসাই কাদের কেন দুই আঙুল দিয়ে জয়সূচক ‘ভিক্টরি চিহ্ন’ দেখিয়েছিল? যে ট্রাইব্যুনাল স্বচ্ছ নয়, নিরপেক্ষ নয়, আন্তর্জাতিক নয়– সেই ট্রাইব্যুনালে প্রথম রায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পাওয়ার পরেও কেন কাদের নিজেকে জয়ী মনে করল?
‘নিরপরাধ’ মোল্লা যাবজ্জীবন দণ্ড পেয়েও ভি-চিহ্ন দেখিয়েছিল, মনে পড়ে সে কথা?
‘নিরপরাধ’ মোল্লা যাবজ্জীবন দণ্ড পেয়েও ভি-চিহ্ন দেখিয়েছিল, মনে পড়ে সে কথা?
যদি সে সত্যিই কসাই কাদের না হয়, কস্মিনকালেও যদি মিরপুরে না গিয়ে থাকে, একটি মানুষও হত্যা না করে থাকে, তবে কতবড় পাগল হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পাবার পরেও হাত তুলে নিজেকে জয়ী ঘোষণা করে? হিসেবটা কি মেলে?
আশা করি আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটি বিভ্রান্তি দূর করে হিসেবগুলো মেলাতে কিছুটা হলেও সাহায্য করবে।
আরিফ রহমান: বস্ত্রপ্রকৌশলে অধ্যয়নরত ব্লগার, অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট।
ড. অভিজিৎ রায়: মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, বিজ্ঞান লেখক ও গবেষক।
http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/14020
- Biplob Rahman | ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ ১২:৫৩582662
- শারমিন আহমদ
জেলহত্যাকাণ্ড: আবদুস সামাদ আজাদের সাক্ষাৎকার (পর্ব-১)
ডিসেম্বর ২১, ২০১৩
জেলহত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে ভূমিকা:
১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম. মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামরুজ্জামানের নির্মম হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যখন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯৭২-৭৩) আবদুস সামাদ আজাদের সাক্ষাৎকারটি পত্রিকায় পাঠাচ্ছি, তখন সারা বাংলাদেশে বইছে চরম অস্থিরতার ঝড়।
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার নিরীহ মানুষের রক্তে প্লাবিত হচ্ছে মাঠ-ঘাট-রাজপথ, হিন্দুদের বাড়িঘর জ্বলছে, ধ্বংস হচ্ছে জাতীয় সম্পদ, ধসে পড়ছে আশা ও স্বপ্ন। শিশু, কিশোর ও তরুণ যারা এই জাতির ভবিষ্যৎ, তাদের মধ্যকার সব সম্ভাবনা শ্বাসরুদ্ধ হচ্ছে এই নৈরাজ্যপূর্ণ ও কলুষিত রাজনৈতিক আবহাওয়ায়। হরতালে কিশোর মনিরের ভস্মীভূত দেহখানি আমাদের মৌন বিবেকের ওপর আর্তনাদ করে প্রশ্ন করেছে কেন আমরা জাতিগতভাবে মেনে নিচ্ছি এমন অন্যায়-অপরাধ?
হরতালকারীদের হিংস্রতার আরেক বলি, মাথার খুলি বিদীর্ণ হয়ে নিহত (২৭ নভেম্বর) মনোয়ারা বেগমের কন্যা শোকাহত নাসিমা ধিক্কার দিয়ে বলছে, “একজন রাজনীতিবিদের নাম দাও, যে এই হরতালের সহিংসতায় মৃত্যুবরণ করেছে?” আসলেই তাই, রাজনীতিবিদ যারা এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে তারা কিন্তু নিরাপদেই রয়েছে। তাদের নিয়োজিত কর্মীবাহিনী দেশকে জিম্মি করে ঘটিয়ে যাচ্ছে এইসব নারকীয় কার্যকলাপ।
সবই হচ্ছে জনগণের স্বার্থরক্ষার নামে। জনগণের স্বার্থরক্ষার নাম করে যখন জনগণকেই জিম্মি করে তাদেরকে হত্যা ও তাদের জান-মাল ভস্মীভূত করা হয় তখন সেই রাজনৈতিক দল/দলসমূহ হারায় জনগণের প্রতিনিধি হবার বৈধতা ও যোগ্যতা। কিন্তু বাংলাদেশের ভাগ্যেই ঘটছে ব্যতিক্রম। যুগ থেকে যুগে। সে যেই দলই হোক না কেন, পেশীবলে, অর্থবলে, প্রতারণা ও মিথ্যাচার বলে কোনো প্রকার রাজনীতিবিদের সিলটি যদি একবার গায়ে এঁটে যায় তখন তাকে সেই পদ থেকে হটানো হয় মুশকিল।
জনগণের অর্থ ও সম্পদ ডাকাতি করে,আত্মসাৎ করে (যাকে বলা হয় দুর্নীতি), রাহাজানি, খুন, গুম খুন ও সকল প্রকার অমানবিক কাজ ও অসভ্য আচরণ করেও এই পেশাদার রাজনীতিবিদ ও তাদের অনুসারীরা ভালোমতোই বেঁচে থাকে। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, কিন্তু যেখানে পুরো রাষ্ট্রপরিচালনা পদ্ধতিটিই কলুষিত সেখানে মুষ্টিমেয়র সততা ও ন্যায়নীতি কতটুকুই-বা পরিবর্তন আনতে পারে অথবা তাদেরকে কতদূরই-বা সত্যিকারের কাজ করতে দেওয়া হয়!
আজ বাংলাদেশে যে চরম নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার মূল কারণ হল এই আষ্টেপৃষ্ঠে দুর্নীতিগ্রস্ত মানসিকতাসম্পন্ন রাজনৈতিক দল, প্রশাসন ও রাষ্ট্রপরিচালনা পদ্ধতি। তারা জনগণের সেবক হবার বদলে পরিণত হয়েছে ভক্ষকে। স্বাধীনতার মহান আদর্শকে অপমানিত করে ব্যক্তি,পরিবার-স্বজন ও দলীয় স্বার্থে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া ও লালন করা দুর্নীতি, অনাচার ও আইনের শাসনের গতিপথ রুদ্ধ করার প্রবণতা– এই কারণগুলির শিকড় বেয়েই আজ উঠে এসেছে গণহত্যাকারী রাজাকার-আলবদর ও তাদের নির্লজ্জ সমর্থকরা।
আওয়ামী লীগ উন্নয়ন ক্ষেত্রে (বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি) বিএনপির চাইতে অনেক ভালো করেও জনগণের আস্থা এবং জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে উল্লেখিত কারণগুলির জন্য। আর উল্লিখিত কারণগুলিসহ বিএনপির দুঃশাসনের চরম নমুনা সৃষ্টির প্রতিবাদে এক-এগারোই শুধু ঘটেনি এবং গত নির্বাচনে বিএনপি পরাজিত হয়নি, তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিজেদেরকে নিক্ষিপ্ত করার আয়োজন করেছে একাত্তরের পরাজিত, পাকিস্তান-সৌদিপালিত সাম্প্রদায়িক ও গণহত্যাকারী দলের বাহন হয়ে।
তাদের এই অশুভ অ্যালায়েন্স লক্ষ শহীদের রক্তে অর্জিত বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্যই আজ হুমকিস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিএনপি এবং জামায়াত-এ-ইসলামসহ পবিত্র ধর্মের নাম বিক্রি করে চরম অধর্মপূর্ণ কর্মকাণ্ডের হোতা দলগুলির মধ্যকার আদর্শগত পার্থক্য আজ বিলীন হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের ভাগ্য হয়ে উঠছে জটিল থেকে জটিলতর। আর এমনি একটি অনিশ্চিত সময়ের প্রেক্ষাপটে আমি জেলহত্যার সাক্ষাৎকারের অবতারণা করছি।
ওই নির্মম হত্যাকাণ্ডগুলি এমন এক সময়ের ইতিহাস যাকে দল-মতের উর্ধ্বে উঠে বস্তুনিষ্ঠভাবে গবেষণা-বিশ্লেষণ না করা ও তার থেকে শিক্ষা না নেবার বিষয়টিও ছিল অন্যতম এক কারণ, যে জন্যে আমরা আজও পরিগণিত হতে পারিনি সভ্য এক রাষ্ট্ররূপে। যে কারণে আজও বাংলাদেশ লাভ করেনি মানসিক স্বস্তি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। এই বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের দেশে মৌলিক গবেষণা হয়নি বললেই চলে।
আজকে জেল হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত সাক্ষাৎকারটি উল্লেখ করার আগে এক ঝলক চোখ বুলানো যাক সেই সময়টিতে। আজকের প্রজন্ম যারা সেই সময়টি সমন্ধে জানে না বা তাদেরকে আমরা সঠিকভাবে জানাতে ব্যর্থ হয়েছি, বিশেষত তাদের জন্যই সেই ইতিহাসের অতিসংক্ষিপ্ত এই বর্ণনা।
দেশ যখন স্বাধীন হল তখন যদি সদ্যস্বাধীন দেশটির প্রশাসনে মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য অনুযায়ী, আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ন্যায়বিচার সমুন্নত রাখা হত এবং নিজ দলের ভেতর লুকিয়ে থাকা স্বাধীনতাবিরোধী ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী প্রথম বাংলাদেশ সরকারবিরোধী মূল ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হত, তাহলে ভেতরের ও বাইরের কোনো চক্রই তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করতে পারত না। আজকের দুঃখজনক এই প্রসঙ্গেরও অবতারণা হত না।
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর পরিবারসহ নির্মমভাবে নিহত হন। বঙ্গবন্ধুর আস্থাভাজন, তাঁর মন্ত্রিসভা ও বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য খন্দকার মোশতাক আহমেদ এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী জুনিয়র আর্মি অফিসাররা ক্ষমতা দখল করে। অবৈধভাবে রাষ্ট্রপতির পদ দখলকারী মোশতাক অর্ডিন্যান্স জারি করে যে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার করা যাবে না।
মুক্তিযুদ্ধের সেনাপতি জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী যিনি বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত একদলীয় বাকশালের প্রতিবাদ করে তাতে যোগদান করেননি, তিনি নির্দ্বিধায় বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পদে যিনি ছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুসহ নারী-শিশুর হত্যাকারীদের অন্যতম মোশতাকের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার পদে নিয়োজিত হন। চিফ অব আর্মি স্টাফ মেজর জেনারেল শফিউল্লাহকে সরিয়ে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান তার স্থলভূক্ত হন।
তিনিও হত্যাকারীদের বিরদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেন না; বরং হত্যাকারীদের বিচার করা যাবে না এই অর্ডিন্যান্সকে পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হবার পর সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনীর (৬ এপ্রিল, ১৯৭৯) মাধ্যমে বৈধতা দেন (বলাবাহুল্য, কোনো অন্যায় কখনওই আইনত বৈধ হতে পারে না, তা একদিন বাতিল হতে বাধ্য)।
১৫ আগস্টে হত্যাকাণ্ডের দুইমাস বিশ দিন পর ৩ নভেম্বর দিবাগত রাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে (লেখার শুরুতেউল্লেখিত) মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী বঙ্গবন্ধুর চার সহকর্মী নিহত হন। ওই একই রাতে অবৈধ মোশতাক সরকার ও বঙ্গভবন দখলকারী হত্যাকারী সেনা অফিসারদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং জিয়াকে গৃহবন্দী করে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এক রক্তপাতহীন অভ্যুথানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন।
তার মাত্র চার দিন পরে, ৭ নভেম্বর সিপাহী বিদ্রোহে (এই দিনটিকে সিপাহী-জনতার অভ্যূত্থান বলা হলেও, আসলে এই বিদ্রোহটি ছিল বামপন্থী জাসদ সংগঠিত এবং জনতার অংশগ্রহণ এতে ছিল না) নেতৃত্বদানকারী কর্নেল তাহের জিয়াকে মুক্ত করেন। ওই একই দিন খালেদ মোশাররফ ও তাঁর দুই সহকর্মী কর্নেল নাজমুল হুদা ও কর্নেল এ টি এম হায়দার নিহত হন।
তাদের বিরুদ্ধে অভ্যূথানকারীরা এই অপবাদ ছড়ায় যে খালেদ ও তার অনুগামীরা ভারতের দালাল। যারা খালেদ মোশাররফ সমন্ধে কিছুটা ধারণা রাখেন তারা জানেন যে এই অকুতোভয় স্বাধীনচেতা বীর মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে ওই কথাটি ছিল অপপ্রচার মাত্র।
পরবর্তীতে জিয়াকে মুক্তকারী, কর্নেল তাহেরকেই এক প্রহসনমূলক গুপ্ত বিচারের মাধ্যমে জিয়া ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেন এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে একাত্তরের পরাজিত ঘাতক-দালালদের পুনর্বাসিত করেন। জিয়াউর রহমান পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার পর মেজর জেনারেল মঞ্জুর নির্দেশিত আরেক ব্যর্থ সেনা অভ্যূথানে নিহত হন। জিয়ার বিএনপি সরকারকে এক রক্তপাতহীন ক্যু-এর মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় আসেন ১৯৮২ সালে।
এই এতগুলো বছরেও জাতির জনক ও স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী চার নেতা, যারা গোটা জাতিরই নেতা, তাদের হত্যার কোনো বিচার হয় না। তার জন্য অপেক্ষা করতে হয় আরও চৌদ্দ বছর; আওয়ামী লীগ সরকার দীর্ঘ একুশ বছর পর পুনরায় ক্ষমতায় আসার সময় পর্যন্ত।
১৯৮৭ সালে আমি যখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে এসে জেল হত্যাকাণ্ডের ওপর তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করি তখন অবাক হয়ে লক্ষ্য করি যে এই সম্পর্কে হত্যাকাণ্ডের সুদীর্ঘ বার বছর পরেও তথ্য, উপাত্ত এবং প্রমাণসহ গবেষণামূলক কোনো লেখনী প্রকাশিত হয়নি। জেল হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী ব্যক্তিবর্গ এবং এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার, ইতিহাসের উপাদান হিসেবে যার গুরুত্ব অনেক, তা সংগ্রহ করে জাতিকে জানাবারও কোনো প্রচেষ্টা নেওয়া হয়নি।
জাতির বিবেককে যারা নাড়া দেবেন বলে আশা করা যায় সেই বুদ্ধিজীবী সমাজ এই বিষয়টি সমন্ধে জানতে এবং জানাতে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেননি। আমাদের এমনিতর ইতিহাস সংরক্ষণ চেতনার অভাবের কারণেই তো ঘটে যায় আরও নির্মমতা এবং জাতি ঘুরপাক খায় বিভ্রান্তিতে। বৈহাসিকের পার্শ্বচিন্তা কলামে, প্রখ্যাত কলামিস্ট আবু জাফর শামসুদ্দীন, জাতীয় ইতিহাসের মর্মান্তিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের এই সম্মিলিত উদাসীনতা ও অবহেলাকে চিহ্নিত করে জাতির কাছে কিছু প্রশ্ন রেখেছিলেন। জেলহত্যা দিবসে তিনি লিখেছিলেন–
“কী দোষ করেছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ ও তাঁর তিন সহকর্মী এ প্রশ্নের জবাব এ পর্যন্ত কোনো সরকার দেয়নি। আমরা দেশবাসীও সোচ্চার হয়ে এ প্রশ্ন করিনি এবং তার জবাব চাইনি। এই যে প্রশ্ন করিনি এবং তার জবাব চাইনি এটাও আমাদের লজ্জার বিষয়– গণতন্ত্রের সমর্থকরূপে প্রশংসিত নাগরিকদের কর্তব্যকর্মে চরম ঔদাসীন্য ও অবহেলার প্রমাণ।” (সংবাদ , ৫ নভেম্বর, ১৯৮৪)
ঢাকায় পৌঁছে আমি যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগহ করি ও সাক্ষাৎকার নিই তারা হলেন স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯৭২-৭৩) আবদুস সামাদ আজাদ, জেলহত্যা তদন্ত কমিশনের সদস্য, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি কে এম সোবহান (৭ নভেম্বর জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণের পর তদন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়) স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এ এস মহসীন বুলবুল, ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক (ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নির্দেশে তিনি জেল হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ডিআইজি প্রিজনস আবদুল আউয়ালের রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকার নেন) ও প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী আবদুল মোমিন।
উল্লিখিত প্রথম ও তৃতীয় সাক্ষাৎকারদাতা ১৯৭৫ সালে চার নেতার সঙ্গে জেলে বন্দি ছিলেন। এছাড়াও তাজউদ্দীন আহমদের শৈশব ও ছাত্রজীবন সম্পর্কে ওনার শিক্ষক ও ভাই-বোনদের সাক্ষাৎকার নিই। পঁচাত্তরে জেলে কর্মরত কর্তৃপক্ষর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। আরও যাদের সঙ্গে দেখা হয় তারা সে সময় আমাকে সাক্ষাৎকার দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন।
বঙ্গবন্ধু ও জেল হত্যাকারী লে. কর্নেল ফারুক ও রশীদ তখন দেশে ফিরে ফ্রিডম পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা প্রকাশ্যেই শেখ মুজিবের মরণোত্তর বিচার করবে বলে হুমকি দিচ্ছে। লে. কর্নেল ফারুক জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে ১৯৮৬ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছে। মোশতাক দুর্নীতির দায়ে জেল খেটে বেরিয়ে তার আগা মসীহ লেনের বাড়িতে বহাল তবিয়তেই আছে (তাকে হত্যাকাণ্ডের জন্য বিচারের মুখোমুখি কখনওই দাঁড়াতে হয়নি, তার আগেই সে মৃত্যুবরণ করে)।
সুতরাং এই পরিস্থিতিতে, অনেকেই যে কোনো তথ্য বা সাক্ষাৎকার দিতে অপারগতা প্রকাশ করবে সেটাই হয়তো স্বাভাবিক। তারপরেও সেদিনের সাক্ষাৎকার হতে জেলহত্যা সম্পর্কে যে চিত্রটা মনে অস্পষ্ট ছিল তা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জেল থেকে চিরতরে ও রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যাওয়া তাজউদ্দীন আহমদের মহামূল্যবান ও ঐতিহাসিক ডায়েরিটি কে নিয়েছিল সে সমন্ধেও জানতে পারি।
১৯৮৭ তে সংগ্রহকৃত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে রচনা করি “৩ নভেম্বরের জেলহত্যা ও বিবেকের আত্মাহুতি” প্রবন্ধ যা ১৯৮৮ সালে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত প্রথম নিয়মিত সাপ্তাহিক ‘প্রবাসী’ পত্রিকা এবং পরে বাংলাদেশের অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিন বছর পরে, ১৯৯১ সালে আমার ছোটবোন সিমিন হোসেন রিমি বহু কষ্টে অবসরপ্রাপ্ত ডিআইজি প্রিজনসের ঠিকানা যোগাড় করে তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। ডিআইজিসহ অবসরপ্রাপ্ত আইজি প্রিজনস নুরুজ্জামান, জেলর আমিনুর রহমান ও সুবেদার ওহায়েদ মৃধার সাক্ষাৎকার সে ‘ভোরের কাগজ’ পত্রিকায় এবং তার লেখা “আমার ছোটবেলা, ১৯৭১ এবং বাবা তাজউদ্দীন আহমদ” বইয়ে প্রকাশ করে।
বলাবাহুল্য যে, নিজ পিতা ও তাঁর তিন সহকর্মীর নির্মম ও অন্যায় হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজটি মনের দিক থেকেও সহজসাধ্য ছিল না। তারপরেও করতে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের কাণ্ডারি অন্যন্য সংগঠক এক অসাধারণ চরিত্রের বাবার প্রতি অসীম ভালোবাসা থেকে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ের তাঁর তিন সহযোদ্ধার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা হতে। রক্তস্নাত নির্মম অতীতের উত্তরসূরী, দিশাহীন এই বর্তমানের অন্ধকারাচ্ছন পথটিতে, নতুন প্রজন্ম একদিন আশা ও শান্তির আলো ছড়াবে সেই পরম প্রত্যাশা হতে।
আবদুস সামাদ আজাদের রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকার (প্রথম অংশ)
এই সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয় উনার কলাবাগানের বাসায়, ১৯৮৭ সালের ৫ জুলাই। সে সময় আমার সঙ্গে ছিলেন আমার মা সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন।
শারমিন আহমদ: ১৯৭৫ সালের কোন সময় আপনি জেলে যান?
আবদুস সামাদ আজাদ: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর আমাকে ইন্টার্ন করে রাখল। তার বোধহয় ৭ দিন পর, যতদূর মনে হয় শবেবরাতের রাত ছিল, নামাজ পড়েছি সারারাত, রোজাও রেখেছি। সকালবেলা সূর্য তখনও উদয় হয়নি, হঠাৎ পিয়ন এসে বলল, ‘একজন অফিসার এসেছে’। সঙ্গে দেখি আরও অফিসার এসেছে। তারাও ঘুম থেকে উঠে এসেছে। তারাও ঘটনা উপলব্ধি করতে পারছে না।
তারা বলল, ‘স্যার আপনাকে আমাদের নিয়ে যেতে হবে’। আমার সন্দেহ হল। এর আগেও ঘটনা হয়েছে দুই একটা। আমি বললাম, ‘আমি কাপড়-চোপড় চেঞ্জ করে আসি’। তারা বলল যে, ‘আরও নেতাদের নেওয়া হবে তো, সেইভাবেই আসেন’। আমি তখন একটা ব্যাগে কাপড়-চোপড় ভরে এলাম। আমাদের বাড়ির কাছেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তারা একটি কন্ট্রোল রুম করেছে। সেখানেই তারা নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান সাহেব—ও আরও কিছু লোক অন্য রুমে আছেন। আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। মোট ২৬ জন লোক। ১০ মিনিট পর দেখি তাজউদ্দীন সাহেব এলেন।’
শারমিন আহমেদ: দিনটি ২২ আগস্ট ছিল?
আ সা আ: হ্যাঁ, ২২ আগস্ট। তো তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে আমরা দুজন আলাপ করলাম। কেন এনেছে, কী ব্যাপার– উনি তো কেবিনেটেও ছিলেন না। (দল ও সরকার পরিচালনা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মতবিরোধের কারণে তাজউদ্দীন আহমদ ২৬ অক্টোবর, ১৯৭৪ অর্থমন্ত্রীর পদ হতে ইস্তফা দেন) একটু পরেই (মেজর শরিফুল হক ডালিম) ডালিম এল। কামরুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে কথা বলে গেল। তখন কামরুজ্জামানকে জিজ্ঞেস করলাম– ‘এ কে?’ বললেন, ‘এ-ই ডালিম’।
তখনও জানি না কী করবে না করবে, মেরে ফেলার জন্য এনেছে না কী করবে। একটু পরে (মেজর আবদুর রশীদ) রশীদ এল। সে ইলেকট্রিক কানেকশন আছে কিনা লোক লাগিয়ে পরীক্ষা করল। এরপর সৈয়দ হোসেন সাহেব এলেন। উনি আগেই অ্যারেস্টেড ছিলেন।
শা আ: সৈয়দ হোসেন কে?
সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন: বঙ্গবন্ধুর—-
আ সা আ: বঙ্গবন্ধুর ভগ্নীপতি। তো ওনার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রশীদ বলছিল, “আপনাকে আমরা এনেছি, আপনি তো কারাগারেই আছেন–”(টেপের এই অংশটি অস্পষ্ট)। পরে আমরা জানতে পারলাম, রশীদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল আমাদের মেরে ফেলবে। এমন ভাবসাব। কারণ ইলেকট্রিক ওয়্যারিং-টয়্যারিং করছে। একটু পর দেখি ফটোগ্রাফার এল।
একজন ফটোগ্রাফার আমার সঙ্গে অ্যাটাচড ছিল (বঙ্গবন্ধু প্রশাসনে মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে) সে বলল, ‘স্যার, আমাদেরকে ঘুম থেকে উঠিয়ে এনেছে’। তারপর দেখি টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যানও আছে। তারপর রশীদও চলে গেল। আমরা ভাবছি কীসের জন্য আনল না আনল-–এর মধ্যেই আরেকজন এসে বলল, ‘আপনারা চলেন’। বললাম, ‘কোথায়?’ সে বলল, ‘ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে?’
শা আ: কে এসে বলল?
আ সা আ: কোনো এক অফিসার। মিলিটারি অফিসার। বলল, ‘সেন্ট্রাল জেলে চলেন।’ তারপর আমাদেরকে কারে নিল। এই পাঁচ জনকে কারে নিল।
শা আ: আব্বুর সঙ্গে কি আপনি ছিলেন?
আ সা আ: হ্যাঁ, আমি, তাজউদ্দীন সাহেব, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামান সাহেব।
সৈ জো তা: আহহা! (দুঃখ প্রকাশ)
আ সা আ: আমরা তো সেন্ট্রাল জেলে ঢুকলাম ওইদিনই এগারোটা সাড়ে এগারোটায়। দিনের বেলা।
শা আ: বেলা এগারোটা সাড়ে এগারোটা?
আ সা আ: মনে হয় ওই রকমই সময়।
শা আ: আব্বুকে ধরে নিয়েছিল ২২ আগস্ট বেলা–
সৈ জো তা: ৮ টায়।
আ সা আ: মনে হয় তখন রোদ উঠে গিয়েছিল। সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে ঢুকলাম। কী সিচুয়েশন! সমস্ত জেলখানায় কয়েদীদের তালা বন্ধ করে রেখেছে। আমরা সলেম্ন অবস্থায়– কী হবে না হবে। আমি, তাজউদ্দীন সাহেব তো আগে থেকে জেলখাটা লোক। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। কয়েদিরা হৈচৈ করছে জানালা দিয়ে। জাসদ আছে, নকশাল আছে, তারা নাম ধরে ধরে ডাকছে। এরপরে আমাদের অ্যাপ্রুভার সেলে রাখল।
শা আ: কী সেল?
আ সা আ: অ্যাপ্রুভার। ওই যে রাজসাক্ষী হয়। খুব খারাপ সেল। ২০ নম্বর ওয়ার্ড। আমি প্রটেস্ট করলাম। এখানে থাকব না। আমরা তো জেল খেটেছি। সব ওয়ার্ড জানা আছে। জেলর বলল, “স্যার, জায়গা তো নাই। আপনাদের তো আলাদা রাখতে হচ্ছে।” জেনারেলি এইসব হৈচৈ-এর মধ্যে সৈয়দ সাহেবেরা বাহির হতে চান না। আমরা তো জেল খেটেছি।
শা আ: সৈয়দ নজরুল কি এর আগে জেল খাটেননি?
আ সা আ: সৈয়দ সাহেব তো জেল খাটেননি। এই অবস্থায় আমাদেরকে নিল পরে।(অন্য জায়গায়) আইজির অফিস ছিল একটা এরিয়ায়। সেটা তখন অফিস নাই। সেই বিল্ডিংটাকে (অফিস) খালি করে করে আমাদেরকে নিয়ে গেল বিকালবেলায়। সেটার নাম নিউ জেল। সেই জেলে রাস্তাও ছিল না, বাগানও ছিল না। তাজউদ্দীন সাহেব নিজেই বাগান করেছেন।
শা আ: যে সময় (ওখানে) ছিলেন তখুনি আব্বু বাগান করেছিলেন?
আ সা আ: হ্যাঁ। দুই মাস পর্যন্ত, বড় বাগান। কয়েদীদের নিয়ে নিজেই মাটি খুঁড়তেন। সুন্দর বাগান করেছিলেন। এরিয়াটাকে খুব সুন্দর করা আরকি। নিট এন্ড ক্লিন করা। ওটা বাজে জায়গা ছিল। ড্রেনগুলি পচা ছিল। সেগুলিকে সুন্দর করেন। এইভাবে জেলখানার জীবন চলছে। নানা রকমের রিউমার ডেইলি যায়। প্রথমদিকে ইন্টারভিউ দিচ্ছিল না। পরে ইন্টারভিউ দেওয়া শুরু হল। আমাদের সকলেরই।
শা আ: কে ইন্টারভিউ দেওয়া শুরু করল?
আ সা আ: আমাদের ফ্যামিলির সঙ্গে ইন্টারভিউ। আমাদের সঙ্গে ফ্যামিলি মেম্বাররা দেখা করা আরম্ভ করল।
সৈ জো তা: আমাদেরকে প্রথমদিকে দেখা করতে দেয়নি (অন্যদের সাক্ষাতের অনুমতি আগে মিললেও একমাস পরে তাজউদ্দীন আহমদের পরিবারকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়)।
আ সা আ: হ্যাঁ, প্রথমদিকে দেয়নি। পরে ইন্টারভিউ দেয়। তারপরে ফ্যামিলি মেম্বারদের সঙ্গে যতটুকু সময় কাটাই, ফ্যামিলির সমস্যা ছাড়াও, বাইরের খবর-টবর কী অবস্থা এই সব জানি। ওরা তখনও আছে বঙ্গভবনে– মোশতাক, রশীদ, ফারুক (তদানীন্তন মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান)। এরা আছে এই খবর-টবর পাই। তার কিছুদিন পরে, প্রায় দুই মাস (তখন) হয়ে গিয়েছে, কোনো পরিবর্তন কি হবে? আমরা কি ছাড়া পাব? (এই চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়)
(অস্পষ্ট) —–ইনভেসটিগেশন শুরু করেছে স্পেশালি আমাদের এই কজনের। এখানে (ইনভেস্টিগেশনে) মিলিটারি অফিসারসহ চার-পাঁচজন বসেছে। তারা আমাদেরকে প্রশ্ন করে।
শা আ: তারা কী ধরনের প্রশ্ন করে?
আ সা আ: এই সমস্ত পার্সোনাল (বিষয়)– কার কোথায় কী আছে, না আছে। আমাদের বাড়ি-ঘর-প্রপার্টি ইত্যাদি সমন্ধে স্টেটমেন্ট দিতে হয়। ইনভেস্টিগেশন আর কি। পুলিশের লোক দুইজন আছে। বাকি মিলিটারি। জেলগেটেই।
সৈ জো তা: রাজনৈতিক অবস্থার ওপর তাজউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে কী বলতেন?
আ সা আ: এটা পরে আলাপ করব। পলিটিক্যাল আলাপটি পরে করব। তোমার সঙ্গে (শারমিন আহমদকে লক্ষ্য করে) আলাপ করব আরেক সিটিংয়ে।
শা আ: আমি পুরো ঘটনাটি টেপ করে রাখতে চাচ্ছি। সে সময় কী পরিস্থিতি ছিল? হয়তো একদিন আমি বেঁচে থাকি কি আপনি বেঁচে থাকেন, কিন্তু ইতিহাস বেঁচে থাকবে।
আ সা আ: তারপরে আমাদেরকে প্রথমে ডিভিশন দেয়নি। প্রথম রাতে আমরা সাধারণ ঘরে—
শা আ: প্রথম কতদিন ডিভিশন দেয়নি?
আ সা আ: প্রথম দিন ও রাতটা ডিভিশন দেয়নি। পরদিন, বোধহয় একদিন পরেই আমাদেরকে ডিভিশন দিয়ে দিল। ক্লাস ওয়ান। প্রথম রুমটা ছিল ছোট। সবাই এই রুমে প্রথমে উঠেছিল। এরপরেই ওই বিল্ডিঙে আরেকটা রুম। তারপরে বড় রুমটা। ওই রুমটায় আমি চলে গেলাম। আমার সঙ্গে মনসুর আলী সাহেব ছিলেন (নিউ জেল বিল্ডিং)।
শা আ: আপনি কত নং রুমে ছিলেন?
আ সা আ: তিন নাম্বার রুমে।
শা আ: তিন নাম্বার রাজবন্দিদের?
আ সা আ: এই বিল্ডিঙটা আইজির অফিস ছিল। জেলের ভিতরেই। পরে নিউ জেল নাম দেয়। এটা, ফাঁসি দেয় যে এরিয়ায়, সেটা পার হয়ে– আরেকটা ওয়াল আছে, তারপরে এটা। সেটাতেই আমাদের জন্য জেল বানায়।
শা আ: আইজির অফিসের তিন নাম্বার রুমে ছিলেন?
আ সা আ: না। একটা বিল্ডিং আছে আইজি অফিসের। সেই বিল্ডিঙের তিনটা রুম। প্রথম রুম হল— আমরা নিজেরাই (নাম্বার) বলতাম আর কি। প্রথম রুমটায় গিয়ে বসলাম। সবাই ওই রুমে গিয়ে বসলাম। সন্ধ্যার দিকে দেখলাম ওই রুমে তো থাকা যাবে না। মাঝের রুমে গেলেন কামরুজ্জামান ও আরও কিছু লোক। লাস্ট রুমটায় আমি গেলাম। মনসুর আলী বললেন, ‘আমি সেখানে থাকব’।
শা আ: আব্বু কোন রুমে থাকতেন?
আ সা আ: এই প্রথম রুমটায়। এই রুমটা ইতিহাস!
(বড় মর্মান্তিক ইতিহাস। এই এক নম্বর রুমটিতে অন্যান্যদের সঙ্গে থাকতেন তাজউদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম। বঙ্গভবন থেকে মোশতাক-রশীদের নির্দেশপ্রাপ্ত হত্যাকারীদের আদেশে দুই নম্বর অর্থাৎ মধ্যের রুম থেকে কামরুজ্জামান সাহেব এবং তিন নাম্বার বা শেষ রুম থেকে মনসুর আলী সাহেবকে প্রথম রুমে নিয়ে যায় জেল কর্তৃপক্ষ। বাকি নেতৃবৃন্দদের ওই রুম থেকে সরিয়ে রাতের গভীরে মুক্তিযুদ্ধের চার নেতাকে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়।)
শা আ: আব্বুর সঙ্গে কেউ ছিলেন?
আ সা আ: হ্যাঁ, কিছু গেলেন এখানে (প্রথম রুমে) আর সবাই রইলেন তিন নম্বর রুমে। বিল্ডিঙটা এভাবে লম্বা। এই রুমটা পয়লা পাওয়া যায়। এরপর দুই নম্বর সেখানে কামরুজ্জামান ও সঙ্গে আরও কিছু লোক– সঙ্গে যারা ছিল– মায়া (শ্রমিক লীগের নেতা মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী) ও আরও কয়জন। আর লাস্ট রুমে– এটা বড় রুম– তিন নম্বর– আমরা বলি আর কি। জেলের নম্বর কী আছে আমরা জানি না। তারপর সেই রুমে প্রথমে আমি আর মনসুর আলী পরে আরও বহু লোক (গেলেন)।
শা আ: আর সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব কোথায় থাকতেন?
আ সা আ: ওই এক নম্বর রুমে। সৈয়দ সাহেব, তাজউদ্দীন সাহেব, শেখ আবদুল আজীজ, মাখন (ছাত্রনেতা আবদুল কুদ্দুস মাখন), কোরবান আলী, শেষ পর্যন্ত যারা ছিল আর কি। মোট ৮ জন ছিল।
শা আ: দ্বিতীয় রুমে কামরুজ্জামান —
আ সা আ: কামরুজ্জামান ও আদার্স, প্রায় ১২ জন। তৃতীয়টায় যারা আসত (জেলে) তারা ওখানে যেত। কারণ বড় রুম তো। যেমন জোহা সাহেব–
সৈ জো তা: জোহা সাহেব তো অনেক পরে গেলেন।
আ সা আ: হ্যাঁ, পরে গেলেন। তিন নম্বর রুমে জায়গা বেশি ছিল। তারপর ১ তারিখে আমাদের ইন্টারভিউ হচ্ছে– বিভিন্ন খবরাখবর পাই—
শা আ: ১ তারিখ কোন মাসের?
আ সা আ: নভেম্বর মাসের। পয়লা নভেম্বর। জেলার–
শা আ: জেলরের নাম কী?
আ সা আ: মনে হয় মোখলেসুর রহমান। গোপালগঞ্জ বাড়ি। (সঠিক নাম আমিনুর রহমান যা পরে জানতে পারি) এখনও আছে।
শা আ: এখন উনি কোথায় আছেন?
আ সা আ: —-(অস্পষ্ট) সুপারিটেনডেনট ছিল। এখন কোথায় আছে জানি না।
শা আ: আর ডিআইজি প্রিজনের নাম জানেন?
আ সা আ: আউয়াল সাহেব (আবদুল আউয়াল), আর আইজি (প্রিজনস) ছিলেন নুরুজ্জামান।
শা আ: তারপর কী হল? পয়লা নভেম্বর?
আ সা আ: পয়লা নভেম্বর তাজউদ্দীন সাহেবের ইন্টারভিউ ছিল (বেগম জোহরা তাজউদ্দীনের সঙ্গে)। উনি ডায়েরি লিখতেন। তো বিকালবেলায় আমি ও ইনি একটু বেড়াতাম। সকালেও বেড়াতাম, বিকালেও ওই এরিয়ার ভেতরে। বেড়াবার সময় যা কথাবার্তা হত। মাঝে মাঝে মিলাদ পড়াতাম, খতম পড়তাম। এই সব সময় বসতাম। পার্সোনাল আলাপ-টালাপ হত বেড়াবার সময়। তো ওই দিন বিকালবেলা (১ নভেম্বর) তাজউদ্দীন সাহেব আমাকে প্রথম বললেন যে, ‘‘জেলটা আমার যেন মনে হচ্ছে যে রেডক্রসে নিলে ভালো হয়। রেডক্রসের হাতে না নিলে জেলটা মনে হচ্ছে ডেঞ্জারাস—-”
শা আ: মাই গড! আব্বু এটা বললেন যে জেলটা–
আ সা আ: এটা পুরা একটা ইমপ্রেশন। ওনার ইমপ্রেশনটা বললেন। তারপর আমাকে বললেন, “আপনি দেখেন একটা কিছু করা যায় কিনা। আমিও চেষ্টায় আছি। আপনিও চেষ্টা করেন।”
সৈ জো তা: ইশশ! কী আতঙ্ক ঢুকে গিয়েছিল! বুঝে গিয়েছিলেন–
শা আ: ওহ! তখুনি আব্বু বুঝতে পেরেছিলেন—
সৈ জো তা: উনি বুঝে গিয়েছিলেন যে জেলে সিকিউরিটি নেই–
আ সা আ: তখন তো উল্টা আমাদেরকে খবর দেওয়া হয়েছে যে চার পাঁচ দিনের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে। তাজউদ্দীন সাহেব তো সেদিন কথায় কথায় ওনার ইমপ্রেশন বললেন যে, “আপনিও চেষ্টা করেন আমিও চেষ্টা করি যে কোনোভাবে রেডক্রসে খবর পৌঁছানো যায় কিনা।”
তারপর সন্ধ্যার পর মনসুর আলী সাহেব আমার পাশের সিটে ছিলেন (৩ নম্বর রুমে পাশাপাশি বিছানায়)। উনিও একটু আনমনা। আমাকে বললেন, “সামাদ সাহেব, কী যে এরা খবর-টবর বলে। এমনি কথায় কথায় শোনা যায় যে মনে হয় ছেড়ে দেবে– কোনো কেইস তো (দোষী সাব্যস্ত করে কেইস) দাঁড় করাতে পারছে না”। কিছুটা প্রাইভেটলি ওই জেলের ভেতর থেকে খবর যায়।
শা আ: মনসুর আলী সাহেবের সঙ্গে কথা হয় সেদিন সন্ধ্যায়?
আ সা আ: হ্যাঁ। সে তো আমরা এক রুমে থাকি। মনসুর আলী সাহেব ও আমি পাশাপাশি। মনসুর আলী সাহেব বললেন “সামাদ সাহেব আমাদের জেলখানাটা– মিলিটারির লোকরা আসে যায়—”।
একদিন রাতে আমাদের সবাইকে (জেল কর্তৃপক্ষ) এসে জানিয়ে গেল যে কিছু মিলিটারির লোকরা যাবে তো– এখানে গান বাজনা— বাচ্চারা তো গান-টান গায়– ছেলেরা (তরুণ রাজবন্দিরা সময় কাটানোর জন্য কখনও একত্রে গান গাইতেন), একটু হৈচৈ কম হলে ভালো হয়– এইসব বলছিল। দুইদিন আগে দেখেছিলাম যে রাতে কিছু মিলিটারির লোক ওইসব (নিউ জেল) এরিয়া দেখেছিল।
শা আ: ওইসব এরিয়া টহল দেয়?
আ সা আ: না, না– দেখতে গিয়েছিল। তখন তো কোনো গভরমেন্ট নাই। জেল কর্তৃপক্ষ জানে না তারা কী করছে। তারা এসে জানাল, “আজ রাতে মিলিটারির লোক এসে এরিয়াটা প্রদর্শন করবে।” আমরা তো তখন মিলিটারির রাজত্বে। খুব কড়া রাজত্ব। মোশতাকের গভরমেন্ট (নামে মাত্র সিভিলিয়ান গভরমেন্ট)– তারপর আনফরচুনেটলি মোশতাক ছিল আওয়ামী লীগের। মোশতাকের কেবিনেটও আওয়ামী লীগেরই। তার মানে আগে যারা মেম্বার (ছিল) তারাই মেম্বার ছিল কেবিনেটে।
তারপর মনসুর আলী সাহেব আমাকে বললেন রেডক্রসে খবর দিতে। আমি বললাম– “হ্যাঁ, তাজউদ্দীন সাহেবও আমাকে বলেছেন। দেখি আমি পারি কিনা।”
[চলবে]
কোস্তারিকা, ৫ ডিসেম্বর, ২০১৩
শারমিন আহমেদ: শিক্ষাবিদ ও বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের জ্যেষ্ঠ কন্যা।
http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/13989
- Biplob Rahman | ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ ১৩:০৯582664
- ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল
গ্লানিমুক্তির বাংলাদেশ
ডিসেম্বর ১৯, ২০১৩
১.
গত সপ্তাহটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সপ্তাহ। একাত্তরের এই সপ্তাহে বাংলাদেশকে মুক্ত করার যুদ্ধটি শুরু হয়েছিল। আকাশে যুদ্ধবিমান, বোমা পড়ছে, শেলিং হচ্ছে, গুলির শব্দ। আকাশ থেকে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর উদ্দেশে হ্যান্ডবিল বিলি করা হচ্ছে, ভারতীয় বাহিনী সেখানে লিখেছে, ‘‘মুক্তিবাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ কর।’’
আমরা বুঝতে পারছি আমাদের বিজয়ের মূহুর্তটি চলে আসছে; তারপরেও বুকের ভেতর শঙ্কা, আমেরিকার সপ্তম নৌবহর পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে বঙ্গোপসাগর দিয়ে এগিয়ে আসছে। গত নয় মাসে এই দেশে কত মায়ের বুক খালি হয়েছে তার হিসাব নেই। মানুষের প্রাণের কোনো মূল্য নেই, যখন খুশি যাকে ইচ্ছা তাকে নির্যাতন করা যায়, হত্যা করা যায়। চারিদিকে শুধু মৃতদেহ আর মৃতদেহ, আগুনে পোড়া ঘরবাড়ি, বিধ্বস্ত জনপদ, মানুষের হাহাকার।
তার মাঝে জামায়াতে ইসলামীর তৈরি করা বদর বাহিনী খুঁজে খুঁজে এই দেশের কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারদের বাড়ি থেকে তুলে নিচ্ছে। তাদের অত্যাচার করছে, চোখের ডাক্তারের চোখ তুলে নিচ্ছে, হৃদরোগের ডাক্তারদের হৃৎপিন্ড বের করে আনছে, তারপর হত্যা করে মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলছে। দেশটি যেন কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তারা সেটি নিশ্চিত করতে চায়।
সেই হত্যাকারীদের বিচার করে বিচারের রায় হয়েছে। প্রথম রায় কার্যকর হয়েছে সেই একই সপ্তাহে, ডিসেম্বরের ১২ তারিখে। আমি বিয়াল্লিশ বছর ধরে এই দিনটির জন্যে অপেক্ষা করেছিলাম। শুধু আমি নই, আমার মতো স্বজনহারানো অসংখ্য মানুষ অপেক্ষা করেছিল। মুক্তিযোদ্ধারা আপেক্ষা করেছিল, নির্যাতিতেরা অপেক্ষা করেছিল, আর অপেক্ষা করছিল এই দেশের নূতন প্রজন্ম।
আমাদের প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম, আমরা মুক্তিযুদ্ধকে তীব্র আবেগ দিয়ে অনুভব করি। আমি কখনও কল্পনা করিনি এই দেশের নূতন প্রজন্মও মুক্তিযুদ্ধকে ঠিক আমাদের মতোই তীব্রভাবে অনুভব করবে। তাদের জন্মের আগে ঘটে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধের সেই অবর্ণনীয় কষ্ট আর অকল্পনীয় আনন্দ তারা এত তীব্রভাবে অনুভব করতে পারে সেটি আমাদের জন্যে এক অবিশ্বাস্য স্বপ্নপূরণ।
গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কথা দিয়েছিল তাদেরকে নির্বাচিত করলে তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবে। এই দেশের মানুষ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম তাদের কথা বিশ্বাস করে বিপুল ভোটে তাদের নির্বাচিত করে এনেছিল। সরকার তাদের কথা রেখেছে, ট্রাইব্যুনাল তৈরি করে বিচার করে বিচারের রায় দিয়ে রায় কার্যকর করতে শুরু করেছে। এই সরকারের কাছে আমার আর কিছু চাওয়ার নেই, তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা এই দেশকে গ্লানিমুক্ত করার জন্য।
এতদিন যখন এই দেশের শিশুরা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করত, ‘‘যারা এই দেশ চায়নি, যারা এই দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছে, তারা কেমন করে এই দেশে এখনও স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়? কেমন করে রাজনীতি করে, মন্ত্রী হয়? যে পতাকাটি ধ্বংস করার জন্যে হত্যাকাণ্ড করেছে সেই পতাকা গাড়িতে লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়?’’
আমি কখনও তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। মাথা নিচু করে থেকেছি।
আর আমার মাথা নিচু করে থাকতে হবে না, কেউ আর আমাকে এই প্রশ্ন করবে না। সেই প্রশ্নের উত্তর তারা পেয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কী, সেই প্রশ্নের উত্তরটি তারাই আমাদের উপহার দিয়েছে।
২.
আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে এই বিচারের কাজটি যতটুকু সহজ ছিল, এতদিন পর সেটি আর সহজ থাকেনি। যুদ্ধাপরাধীর দল ক্যান্সারের মতো সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, মিলিটারি শাসনের আড়ালে শক্তি সঞ্চয় করেছে, অর্থ উপার্জন করেছে, সেই অর্থ দিয়ে অপপ্রচার করেছে, দেশে-বিদেশে বন্ধু খুঁজে বের করেছে। হুবহু তাদের মুখের কথাগুলো আমরা বিদেশি গণমাধ্যমে শুনতে পেয়েছি। জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিধর দেশগুলো আমাদের সরকারকে শুধু মুখের কথা বলে বাধা দেয়নি, চোখরাঙানি দিয়েছে। ১৯৭১ সালে যারা পাকিস্তানের পক্ষে ছিল এত বছর পরও তারা আবার সেই পাকিস্তানের পদলেহীদের পক্ষে।
আমাদের অনেক সৌভাগ্য এই প্রচণ্ড চাপেও আমাদের সরকার দিশেহারা হয়নি, এক যুদ্ধাপরাধীর বিচারের রায় কার্যকর করেছে। নির্বাচন নিয়ে আমাদের দেশের সব পেশাদার বুদ্ধিজীবীর এখন প্রথম কাজ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এক হাত নিয়ে নেওয়া। সেটা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু যখন হরতাল-অবরোধ কার্যকর করার জন্য পেট্রোল বোমা দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মারা হয়, ট্রেনের লাইন উপড়ে ট্রেন লাইনচ্যুত করা হয়, যাত্রীসহ বাস-ট্রাক পুড়িয়ে দেওয়া হয়, রাস্তা কেটে এলাকা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়– তখনও এই বুদ্ধিজীবী, পত্রিকার সম্পাদকেরা তার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর ‘অদূরদর্শিতা’কে দায়ী করেন– তখন আমি একটা ধন্দের মাঝে পড়ে যাই।
এই কাজটি করে এই দেশের বড় বড় পত্রিকার বড় বড় সম্পাদকেরা যে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডগুলোকে এক ধরনের নৈতিক সমর্থন দিয়ে ফেলছেন সেটি কি তারা একবারও বুঝতে পারছেন না? যে ভয়ংকর তাণ্ডব দেখে তাদের আতঙ্কিত হওয়ার কথা সেটা দেখে তারা এই সরকারের ব্যর্থতার ‘অকাট্য প্রমাণ’ পেয়ে উল্লসিত হচ্ছেন এটি কেমন করে সম্ভব?
আমি পেশাদার বুদ্ধিজীবী নই, বড় পত্রিকার সম্পাদক নই, বাজারে সত্য এবং মিথ্যার মাঝখানে কিংবা ন্যায় এবং অন্যায়ের মাঝখানে নিরপেক্ষ থাকার আমার কোনো চাপ নেই। তাই আমার যে কথাটি বলার ইচ্ছা করে সোজাসুজি বলতে পারি। নির্বাচন নিয়ে কী হবে সেটা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো নিষ্পত্তি করুক। কিন্তু যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর না করার জন্যে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরির হুমকিকে তোয়াক্কা না করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রায় কার্যকর করার জন্যে দেশের মানুষের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই প্রতিজ্ঞটি বাস্তবায়ন করেছেন, সে জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা, তাঁর প্রতি অভিনন্দন। তাঁর বাবা বঙ্গবন্ধু আজ যদি বেঁচে থাকতেন নিশ্চয়ই তার মেয়ের বুকের পাটা দেখে খুশি হতেন।
৩.
১৯৭১ সালের পর আমি কখনও পাকিস্তানের কোনো জিনিস হাত দিয়ে স্পর্শ করিনি। অনেক টাকা বেঁচে যাবে জানার পরও যে প্লেন পাকিস্তানের ভূমি স্পর্শ করে যায় আমি কোনোদিন সেই প্লেনে উঠিনি। পাকিস্তানের উপর দিয়ে যখন কোনো প্লেনে উড়ে যাই, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই দেশটির ভূমি সীমার বাইরে না যাই ততক্ষণ নিজেকে অশুচি মনে হয়। পাকিস্তান দল যত ভালো ক্রিকেট খেলুক না কেন আমি তাদের কোনো খেলা দেখি না (ষাটের দশকে টোকিও অলিম্পিকে স্বর্ণবিজয়ী পাকিস্তান হকি টিমের একজন প্রাক্তন খেলোয়াড় পাকিস্তান মিলিটারির অফিসার হিসেবে আমার বাবাকে একাত্তরে হত্যা করেছিল বলে আমি জানি)।
কেউ কেউ আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে ইতিহাসের একটা বিশেষ সময়ে একটা বিশেষ গোষ্ঠীর একটা সামরিক কাজকর্মের জন্যে সারাজীবন একটা দেশের সকল প্রজন্মকে দায়ী করা যায় না। কথাটি নিশ্চয়ই সত্যি, কিন্তু আমার কিছু করার নেই। একাত্তরে আমি আমার নিজের চোখে পাকিস্তান নামের এই দেশটির মিলিটারির যে নৃশংস বর্বরতা দেখেছি সেটি থেকে আমার কোনো মুক্তি নেই।
দেশটি যদি নিজের এই নৃশংসতার দোষ স্বীকার করে নতজানু হয়ে বাংলাদেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চাইত তাহলে হয়তো আমার বুকের মাঝে ধিকি ধিকি করে জ্বলতে থাকা আগুনের উত্তাপ একটু কমানো যেত। তারা সেটি করেনি, আমার বুকের ভেতর জ্বলতে থাকা আগুনের উত্তাপও কমেনি।
আমি যে রূপ দেখে অভ্যস্ত, দীর্ঘদিন পর এই দেশটির রূপ আমাদের নূতন প্রজন্ম নূতন করে দেখার সুযোগ পেয়েছে। যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার বিচারের রায় কার্যকর করার পর প্রথমে তাদের একজন মন্ত্রী প্রতিবাদ করেছে; তারপর তাদের পার্লামেন্ট থেকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব নিয়েছে। নিন্দা প্রস্তাবের সময় আলোচনার বিষয়বস্তু অত্যন্ত চমকপ্রদ। তারা জোর গলায় বলেছে, কাদের মোল্লা হচ্ছে একজন “সাচ্চা পাকিস্তানি, একাত্তরে সাচ্চা পাকিস্তানি থাকার জন্যেই তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।’’
শাহবাগের তরুণ ছেলেমেয়েরা দিনের পর দিন এই কথাটি বলে শ্লোগান দিয়েছে– ‘‘জামায়াতে ইসলাম মেড ইন পাকিস্তান।’’ যাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল জামায়াতে ইসলামী একাত্তরে এই দেশে কী করেছিল, এখন তাদের কারও ভেতরে কি আর কোনো সন্দেহ আছে?
পাকিস্তান থেকে বক্তব্য দেওয়ার সময় তারা ইনিয়ে বিনিয়ে বলেছে একাত্তরে ‘ঢাকা পতন’ হওয়ার এতদিন পর সেই পুরানো ‘ক্ষত’ নূতন করে উম্মোচন করার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার ‘ঢাকা পতন’ কথাটি নিয়ে আপত্তি আছে। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর মোটেও ঢাকার পতন হয়নি, পাকিস্তানের পতন হয়েছিল। ঢাকা কিংবা বাংলাদেশের সেদিন উত্থান হয়েছিল। ‘ক্ষত’ কথাটি নিয়েও আমার গুরুতর আপত্তি আছে; এটি আমাদের জন্যে ক্ষত নয়, এটি পাকিস্তানের জন্যে ‘ক্ষত’। শুধু ক্ষত নয়, এটি হচ্ছে দগদগে ঘা। চল্লিশ বছরেও সেই ঘা শুকায়নি, শত বছরেও সেই ঘা শুকাবে না।
পৃথিবীর ইতিহাসে পাকিস্তানকে পরাজয়ের এই দগদগে ঘা নিয়ে আজীবন বেঁচে থাকতে হবে। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, গণহত্যা এবং সবশেষে পরাজয়ের এই দগদগে ঘা তাদের অবশ্যই লুকিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু আমাদের কেন সেটি লুকিয়ে রাখতে হবে? ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের সেই বিজয় দিবস আমাদের ক্ষত নয়, সেটি আমাদের গৌরব, আমাদের অহংকার, আমরা শত সহস্রবার সেটি দেখতে চাই। তাই প্রত্যেক বছর এই বিজয় দিবস আমাদের কাছে আগের চাইতেও বেশি উদ্দীপনা নিয়ে আসে।
পাকিস্তানের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। যদি থাকত তাহলে অবশ্যই আমি তাদের কিছু উপদেশ দিতাম। আমি তাদের বলতাম– ‘‘তোমরা তোমাদের দগদগে ক্ষত দেখতে চাও না, খুব ভালো কথা, তোমরা চোখ বন্ধ করে থেকো। কিন্তু আমরা কী করব সেটি নিয়ে ধৃষ্টতা দেখাতে এসো না। ১৯৭১ সালে এই দেশ থেকে তোমাদের বিতাড়ন করে আমরা অনেকদূর এগিয়ে এসেছি, অনেক বিষয়ে আমরা সারা পৃথিবীর মডেল। একটু ধৈর্য ধর, যখন দেখবে আমরা ঠিক ঠিকভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে রায় কার্যকর করে সারা পৃথিবীকে দেখাব কীভাবে সেটি করা যায়, তখন সেটিও সারা পৃথিবীর একটা মডেল হয়ে যাবে। আপাতত তোমরা নিজেদের নিয়ে মাথা ঘামাও। মিলিটারির দাস হয়ে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো যা করছে সেখান থেকে বের হতে পার কিনা দেখো। লেখাপড়া করতে চাইলে মেয়েদের মাথায় গুলি যেন করতে না পারে সেটা খেয়াল করো। সারা পৃথিবীতে সন্ত্রাস রপ্তানি করার যে সুনামটুকু কুড়িয়েছ সেই সুনাম থেকে মুক্ত হতে পার কিনা দেখো।’’
পাকিস্তানের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই; যদি থাকত তাহলে এই তালিকাটি আমি আরও দীর্ঘ করে দিতাম!
কাদের মোল্লার পক্ষে বাংলাদেশের বিপক্ষে পাকিস্তান রাষ্ট্রীয়ভাবে যে নিন্দা প্রস্তাবটি নিয়েছে সেটি আমার কাছে এই রাষ্ট্রটির সঙ্গে মানানসই একটি কাজ বলে মনে হয়েছে। এই দেশে তাদের যে অনুচরেরা আছে তাদের চেহারাটি মনে হয় বেশ ভালোভাবে উম্মোচন করা হয়েছে।
আমাদের নূতন প্রজন্ম এর মাঝে ভয়ানকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। আমি ঠিক এ ধরনের প্রতিক্রিয়াই আশা করেছিলাম। তারা আমাকে নিরাশ করেনি।
৪.
১৬ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষ মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে আমি বিকাল ৪টা ৩১ মিনিটে জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছিলাম। সৃষ্টিকর্তা আমার গলায় কোনো সুর দেননি, আমার মাঝে মাঝে সেজন্যে খুব দুঃখ হয়। আমার মনে হয়, যদি আমার গলায় একটু সুর থাকত তাহলে “আমার সোনার বাংলা” গানটি আমি না জানি কত সুন্দর করে গাইতে পারতাম।
যত বেসুরো গলাতেই গাই না কেন এই গানের চরণগুলো উচ্চারণ করার সময় প্রতিবার আমার চোখ ভিজে আসে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বেসুরো গলায় আমি যখন গানটি গাইছিলাম, যখন একটি একটি করে চরণ গাওয়া হচ্ছিল আর আমার মনে হচ্ছিল, আহা, আরও একটি লাইন শেষ হয়ে গেল! আমার মনে হচ্ছিল, আহা, যদি অনন্তকাল এই গানটি গাওয়া যেত! যদি কোনোদিন এই গানটি শেষ না হত!
জাতীয় সঙ্গীত শেষ হবার পর সাবধানে আমি আমার চোখ মুছেছি। আমাদের প্রজন্মের কাছে এটি তো শুধু কষ্ট, বেদনা। আমাদের আনন্দ, আমাদের উল্লাস।
আমার পাশে কমবয়সী একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল, জাতীয় সঙ্গীত শেষ হবার পর আমাকে বলল, “স্যার, জানেন, যতবার আমি আমার সোনার বাংলা গান গাই আমার চোখে পানি চলে আসে!”
আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম, আমাদের নূতন প্রজন্ম কেমন করে আমাদের সকল স্বপ্ন, আমাদের সকল ভালোবাসা, সকল মমতাকে এমনভাবে গ্রহণ করতে পারল?
ডিসেম্বর ২০১৩
মুহম্মদ জাফর ইকবাল: লেখক ও অধ্যাপক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/13958
- Biplob Rahman | ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ ১৩:১১582665
- যোতির্ময় বড়ুয়া
পাকিস্তানের এখন যা করা উচিত
ডিসেম্বর ১৮, ২০১৩
একাত্তরে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার চলছে। তখন যা ঘটেছিল তা কোনোভাবেই মীমাংসিত বিষয় নয়। নব্বইয়ের দশকে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে দেশ যখন সংগঠিত হচ্ছিল তখন অনেক প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবীই এর স্বপক্ষে অবস্থান নিতে দ্বিধা করেছেন এই ভেবে যে, এটি একটি মীমাংসিত বিষয়, একে প্রশ্নবিদ্ধ করার প্রয়োজন নেই।
এটি কোন বিচারে মীমাংসিত বিষয় তা আমার কাছে বোধগম্য নয়। যারা এই অবস্থান নিয়েছিলেন তারা এখনও তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেননি। তাদের প্রকাশ্য রাজনৈতিক অবস্থান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারীদের পক্ষে না হলেও, তাদের আমরা সঙ্গে পাইনি। সবাই রাস্তায় নেমে আন্দোলনে শরিক হন না, কিন্তু ব্যক্তির অবস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব নয়, কথায়-কাজে বের হয়ে আসে।
শঙ্কাটা অন্য জায়গায়– এই তথাকথিত প্রথিতযশা ব্যক্তিদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে যখন আমাদের বিদেশি বন্ধুরা কথা বলেন, মতান্তরে চাপ দেন, কিংবা পাকিস্তানের ক্ষমতাসীনরা একে মীমাংসিত বিষয় বলেন– তখন আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না, এসব বুদ্ধিজীবীরা স্বদেশে না হলেও বিদেশে তাদের মতপ্রকাশে বেশ সক্রিয়! তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে আমাদের কাছে সংবাদ পৌঁছুতেও সময় লাগে না।
একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য যে বিচারপ্রক্রিয়া চলমান তা নিয়ে আমাদের দেশের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন ছাড়াও চিন্তাবিদদের মধ্যে এক ধরনের বিভাজন বিদ্যমান। রাজনৈতিক বিভাজনটি রাজনৈতিক কারণে হলেও চিন্তাবিদদের মধ্যে বিভক্তি মূলত এর বিচারপ্রক্রিয়া, আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও স্বাধীনভাবে বিচার বিভাগকে তার কাজ করতে দেওয়া নিয়ে।
বিভিন্ন মহল থেকে স্পষ্ট অভিযোগ আছে ক্ষমতাসীন সরকার একে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন বা করতে চেয়েছেন– ৫ ফেব্রুয়ারি শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চের সৃষ্টিও এই অভিযোগ থেকে। কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান থেকে শুরু। ক্রমে বিষয়টি ভিন্ন খাতে গড়িয়েছে। সে সময় সত্যিকারের যে গণবিস্ফোরণ ঘটেছিল তা সময়ের ব্যবধানে প্রশ্নের মুখে পড়ে।
গণজাগরণ মঞ্চের দাবির সঙ্গে সাধারণ মানুষের একাত্মতা থাকার কারণে, ট্রাইব্যুনালের রায়ে অপরাধীর সাজার পরিমাণ কম হলে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করতে না পারার যে বিধান ছিল তা সংসদে আইন করে পরিবর্তন করে। যার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপক্ষ কাদের মোল্লার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে; সেই রায়ে আপিল বিভাগ তার ফাঁসির আদেশ দেয়। ফাঁসির আদেশ হওয়ার পর বিতর্ক চলতে থাকে– আসামি আপিলের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ করতে পারবে কিনা? রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চাইবেন কিনা?
রাষ্ট্রপক্ষে বলা হল, সংবিধানের ৪৭-ক (১) অনুচ্ছেদ মোতাবেক যদি সংবিধানের ৪৭ (৩) অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোনো আইন প্রযোজ্য হয়, সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংবিধানের ৩১, ৩৫ (১) ও (৩) এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের বিধান প্রযোজ্য হবে না। ৪৭ (৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোনো সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য বা অন্য কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিসমষ্টি বা সংগঠন কিংবা যুদ্ধবন্দিকে আটক, ফৌজদারিতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করবার বিধান-সংবলিত কোনো আইন বা আইনের বিধান সংবিধানের সঙ্গে অসমঞ্জস বা পরিপন্থী হলেও, সেই আইন বাতিল বা বেআইনি বলে গণ্য হবে না বা কখনও বাতিল বা বেআইনি হয়েছে বলে গণ্য হবে না।
অনুচ্ছেদ ৪৭-ক (২) অনুসারে যদি কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে সংবিধানের ৪৭ (৩) অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোনো আইন প্রযোজ্য হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির সংবিধানের অধীনে প্রদত্ত কোনো প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করার অধিকার থাকবে না। অর্থাৎ সংবিধানের ১০৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগকে স্বীয় রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনার যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, তা মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত কোনো অপরাধী প্রয়োগ করার সুযোগ পাবেন না। সংবিধানের ৪৭-ক অনুচ্ছেদটি ১৯৭৩ সালে সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে সন্নিবেশিত। এই অনুচ্ছেদটি সংবিধানের মূলধারার পরিপন্থী কিনা, মৌলিক অধিকারের হেফাজত যৌক্তিক কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে।
১৯৭৩ সনের আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনে, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত সাজা কম হলে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের আপিল করার সুযোগ ছিল না, পরবর্তীতে সেটি আইন পরিবর্তনের মাধ্যমে সংযোজন করা হয়। রাষ্ট্রপক্ষ যদি আইনের সমতা আনয়নের জন্য আইন পরিবর্তন করতে পারেন তাহলে অভিযুক্ত পক্ষকে সে সুযোগ দেওয়া হবে না কেন– এই প্রশ্নও অনেকে তুলছেন। এসব নিয়ে আলোচনা চলতে পারে। রাষ্ট্রের বিধি-বিধান সমতাভিত্তিক কিনা তা নিয়ে বিতর্ক নিতান্তই আমাদের দেশের অন্তর্গত বিষয়। তা নিয়ে অন্যের পরামর্শ আমরা নিতে পারি, কিন্তু অন্যের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত খবরদারি মেনে নেওয়া যায় না।
আমাদের মনে রাখা দরকার বিচার একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। যে কোনো রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপরিচালনার নীতির পাশাপাশি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ইছার প্রতিফলন বিচার ব্যবস্থায় থাকবে এটাই স্বাভাবিক। যেখানে রাষ্ট্রের বৃহত্তর অংশ চায় একাত্তরে সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার হোক, সেখানে একটি ক্ষুদ্র অংশ বরাবরই চেয়েছে এই বিচার যেন না হয়। এটি ভিন্নমাত্রা পেয়েছে যখন অভিযুক্তপক্ষ আন্তর্জাতিক লবিস্ট নিয়োগের মাধ্যমে বিদেশি বিভিন্ন রাষ্ট্রকে নিয়ে নানাপ্রকার হস্তক্ষেপ করাতে সফল হয়েছে।
৩১ জানুয়ারি, ২০১২ ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালের পক্ষ থেকে প্রসিকিউটর এডভোকেট জেয়াদ আল মালুম বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিচারে অভিযুক্তের অধিকার কতটুকু সংরক্ষিত হচ্ছে তা নিয়ে রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এই বিষয়ে আমাদের উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন জানতে চাইলে এক ধরনের প্রশ্ন ছিল, কিন্তু পুরো বিষয়টি যখন আসামিপক্ষের লবিস্ট টোবি ক্যাডম্যানের প্রচেষ্টার ফসল– তখন এর উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা সন্দিহান হয়ে পড়ি।
আমাদের দেশে ফৌজদারি আইনে সাধারণ নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে কিনা তা নিয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কেন, বিশ্বের কোনো দেশই মাথা ঘামায়নি। তাহলে আজ মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে অভিযুক্তের অধিকার সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা তা নিয়ে তাদের এই অতিরিক্ত মাথাব্যথার কারণ সহজেই অনুমেয়।
এই মাত্রাহীন সীমালঙ্ঘন ও কূটনৈতিক শিষ্টাচার-বহির্ভূত আচরণ আমরা জাস্টিফাই করেছি তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে আমাদের মতামত উপস্থাপন করে। আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী কীভাবে আমাদের বিচার ব্যবস্থা চলবে তা নিতান্তই আমাদের নিজেদের ব্যাপার। এতে বিদেশিদের নাকগলানো এখন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।
প্রসঙ্গান্তরে বলা প্রয়োজন, আমাদের দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ড একটি স্বীকৃত বিষয়। বিশ্বের অনেক দেশ তাদের বিচার ব্যবস্থা থেকে এই দণ্ড বাদ দিলেও, আমাদের দেশের মতো অনেক দেশেই এটি প্রচলিত আছে। তাছাড়া আমাদের দেশে হত্যা, ধর্ষণ করে মৃত্যু ঘটানো, এসিড নিক্ষেপসহ অন্যান্য অনেক অপরাধের জন্য এটি প্রচলিত একটি শাস্তির বিধান।
আর তাই মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করার জন্যে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ‘ডেথ রেফারেন্স’-এর জন্য আলাদা একটি বেঞ্চ রয়েছে। তার মানে, আমাদের দেশের প্রচলিত আইনে প্রতিনিয়তই কারও না কারও মৃত্যুদণ্ড হচ্ছে। আলোচিত মামলাগুলির কথাই যদি ধরি তাহলে দেখা যায়– মনির হোসেন, এরশাদ শিকদার কিংবা বাংলা ভাইকে আমরা ফাঁসি দিয়েছি।
তাদের সময় এসব বিদেশি মোড়লদের খবরদারি দেখা যায়নি। অর্থাৎ সে সময় ফাঁসি নিয়ে তাদের কোনো উচবাচ্য শোনা যায়নি, তবে এখন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পূর্বের আলোচনা থেকে পাওয়া যাবে। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা দেখি, ১০ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় কার্যকর করা নিয়ে যে ধুম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে তাতেও অনেকে ভাবছেন বিদেশি হস্তক্ষেপ ছিল। সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা জেনেছি আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করে কাদের মোল্লার রায় কার্যকর না করার অনুরোধ করেন।
পরবর্তীতে ১২ ডিসেম্বর কাদের মোল্লার ফাঁসির রায় কার্যকর করার পর, ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে একটি নিন্দা প্রস্তাব পাস করা হয় যা যে কোনো বিচারে কূটনৈতিক শিষ্টাচারের পরিপন্থী। আমরা জেনেছি, জামায়াতে ইসলামীর এমপি শের আকবর খান এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ এবং ইমরান খানের দল তেহরিক-এ-ইনসাফ এই প্রস্তাবে সমর্থন করে। পিপিপি এবং এমকিউএম পার্টি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে।
কাদের মোল্লার রায়ের প্রেক্ষিতে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের এহেন আচরণ আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ। দলমতনির্বিশেষে এর প্রতিবাদ হওয়া দরকার। দেশের বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু জাতীয় স্বার্থে আমাদের এক হতে শিখতে হবে। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৭ ডিসেম্বর এই নিন্দা প্রস্তাব পাসের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের হাইকমিশনারকে মন্ত্রণালয়ে ডেকে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।
প্রধান বিরোধী দল বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব নজরুল ইসলাম খান এক সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানের নিন্দা প্রস্তাব পাসের বিরুদ্ধে দলের অবস্থান পরিস্কার না করে সরকারের উপর দোষ চাপিয়ে বলেন– ‘‘সরকারের আগেই এর প্রতিবাদ জানানো উচিত ছিল। প্রতিবাদ বা ব্যবস্থা সরকারকেই নিতে হবে।’’
এ প্রেক্ষিতে সবাইকে বলব, যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় কূটনীতিক দেবযানী খোবরাগাড়েকে গ্রেপ্তারের প্রেক্ষিতে ভারতের প্রতিক্রিয়ার দিকে নজর দেওয়ার জন্য। দলমতনির্বিশেষে সে দেশের সকল রাজনৈতিক দল এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। আমরাই কেবল পারি না। ভারত এর জবাবে দিল্লিতে মার্কিন দূতাবাসের সামনে থেকে নিরাপত্তা বেষ্টনী তুলে নিয়েছে। আশা করা যায় তাদের এই প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেবযানী খোবরাগাড়েকে অশালীনভাবে দেহতল্লাশি করার প্রতিবাদ জানালে, যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, এটি ভিয়েনা চুক্তি অনুযায়ী কূটনৈতিক শিষ্টাচারের মধ্যে পড়ে না। বোঝা যায়, দুটি শক্তিশালী পক্ষের দৃঢ় অবস্থান আরও গড়াবে।
পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের তেমন উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই। একটি বিশেষ ভাবধারার নাগরিক ছাড়া কেউ পাকিস্তানে বেড়াতে যান বলেও মনে হয় না। তারা আমাদের উন্নয়ন সহযোগীও নন। বরং তারা আমাদের পশ্চাৎপদতার সহযোগী। তাই পাকিস্তানের হাইকমিশনারকে ডেকে প্রতিবাদ জানানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। এটি নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে অভিযোগ দায়ের করে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশীয় বিষয়ে অন্যের হস্তক্ষেপ প্রতিহত করাটাই হবে এই মুহূর্তে সবচেয়ে উপযুক্ত জবাব।
কখনও কখনও উদাহরণ সৃষ্টি করতে হয়– যেমনটি আমরা করেছিলাম একাত্তরে। যদিও আমাদের উচিত ছিল আরও অনেক আগেই পাকিস্তানের ইতোপূর্বের আচরণগুলোর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিস্তারিত তুলে ধরা। একাত্তরের গণহত্যার জন্য, ৯৩ হাজার সেনা ও ১৯৮ জন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী যাদের বিচার করার অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল অথচ তা করা হয়নি, আমাদের প্রাণ ও সম্পদের যে হানি হয়েছিল তার জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের ন্যায্য দাবি তোলা– এসব বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে আবেদন করা– এখন সময়ের দাবি।
এ সমস্ত বিষয় এখনও অমীমাংসিতই রয়ে গেছে এবং এসব মীমাংসার ঐতিহাসিক দায় আছে। তাহলে পাকিস্তানের নতুন প্রজন্মও জানতে পারত– একাত্তরে ‘ঢাকার পতন’ হয়নি বরং ‘বাংলাদেশ’ নামের একটি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়েছিল অনেক রক্তের বিনিময়ে। যে দেশ এখন অনেক ক্ষেত্রেই বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের চেয়ে অনেক অনেক বেশি এগিয়ে, যেখানে তারা একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রের চরিত্র নিয়ে আরও বেশি ব্যর্থতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। পাকিস্তানের এই মুহূর্তে উচিত আমাদের নিয়ে চিন্তা না করে আমেরিকার হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া।
আমরা অপেক্ষায় থাকলাম সেদিনের জন্য যেদিন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সে দেশের নাগরিকের বিয়ের অনুষ্ঠানে, মসজিদে প্রার্থনার সময় বা জানাজা পড়ার প্রাক্কালে ড্রোন হামলা ঠেকাতে নিন্দা প্রস্তাব পাস করবে। বন্ধ করতে পারবে মার্কিন আগ্রাসন।
ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া: আইনজীবী, সুপ্রীম কোর্ট।
http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/13884
- Biplob Rahman | ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ ১৩:১৩582666
- একে খন্দকার
স্মৃতিতে ১৬ ডিসেম্বর: ঐতিহাসিক সেই বিকেল
ডিসেম্বর ১৬, ২০১৩
১৬ ডিসেম্বর এলেই স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসতে হয়, মনে পড়ে যুদ্ধদিনগুলোর কথা। কী গভীর দেশপ্রেম নিয়ে যুদ্ধটি চালিয়ে নিয়ে গেছি আমরা। গুটিকয়েক দেশদ্রোহী ছাড়া গোটা দেশের মানুষ তাদের সর্বস্ব উজাড় করে যুদ্ধ করেছে নয়তো তাতে সহযোগিতা করেছে।
যুদ্ধদিনের প্রতিটি দিনই তো বিশেষ। তবে আমার কাছে সবচেয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে ১৬ ডিসেম্বর বিকেল ৪.৩১ মিনিটে তখনকার রেসকোর্স ময়দানে, এখনকার রমনা মাঠে, যৌথবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের ঘটনাটি। কীভাবে এই ঘটনাটি ঘটল তা যেন এখনও মনের চোখে দেখতে পাই।
আমি তখন কোলকাতায়। ১৬ ডিসেম্বর সকালের দিকে কিছু কাজে বাইরে গেছিলাম। ফিরলাম বেলা দশটার দিকে। ফিরে দেখি আমার জন্য কিছু লোক অপেক্ষা করছেন। তাদের কাছেই জানলাম পাকিস্তানি বাহিনী সেদিন বিকেলে যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করবে। সেজন্য ঢাকার রেসকোর্সে একটি ছোট্ট অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান হবে। আর আমাকে সে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ও মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করতে হবে।
প্রবাসী সরকারে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন জেনারেল এম এ জি ওসমানী। তাঁকে বাদ দিয়ে আমাকে প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে বেছে নেওয়ার কারণ ছিল তখন জেনারেল এম এ জি ওসমানী ছিলেন সিলেটে। মনে রাখতে হবে তখন তো এত মোবাইল বা এ জাতীয় কোনো মাধ্যম ছিল না যে তাঁর সঙ্গে খুব দ্রুত যোগাযোগ করা যেত। তাই আমাকে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ডেকে নেওয়া হয়েছিল।
যাহোক, আমাদের তখনই আগরতলা হয়ে ঢাকায় রওনা দেবার কথা ছিল। আমাদের জন্য তখন কোলকাতার দমদম এয়ারপোর্টে বিশেষ বিমান অপেক্ষা করছিল। আমরা তাই চলে গেলাম দমদমে। আমার সঙ্গে ছিলেন জেনারেল শিশু ও আরও দুজন এখন যাদের নাম আর মনে করতে পারছি না।
দমদমে পৌঁছে বিমানের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম; উঠব—এমন সময় দেখি ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্বকারী জেনারেল অরোরা সস্ত্রীক এসেছেন একটি জিপে করে। তিনি বয়সে আমার অনেক সিনিয়র। তাই তাঁকে সম্মান দেখিয়ে আমি বিমানের দরজা থেকে সরে দাঁড়ালাম। তাঁকে আগে যেতে অনুরোধ করলাম।
কিন্তু জেনারেল অরোরা বিমানে উঠলেন না; তিনি আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, ‘‘আপনি মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার, আপনিই আগে উঠুন।’’ আমি অরোরার এ ব্যবহারে সত্যিই মুগ্ধ হলাম। আমাকেই আগে উঠতে হল, এরপর উনার স্ত্রী ও সবশেষে উনি নিজে। বিমানের দরজা বন্ধ হল। আমরা রওনা দিলাম আগরতলা বিমানবন্দরের উদ্দেশে।
ঢাকার ওপর দিয়েই উড়ে গেলাম আমরা। কেন ঢাকা বিমানবন্দরে না গিয়ে আমরা আগরতলায় গেলাম সে প্রশ্ন থাকতে পারে। ঢাকা বিমানবন্দরের রানওয়ে তখন এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যে কোনো বিমান সেখানে অবতরণ করার মতো অবস্থা ছিল না। তাই আমরা আগরতলা পৌঁছে সেখান থেকে হেলিকপ্টারে ঢাকায় যাব—এমনই পরিকল্পনা।
আগরতলা বিমানবন্দরে পৌঁছে দেখলাম, সাতটি হেলিকপ্টার আমাদের জন্য প্রস্তুত, আমাদের ঢাকায় নিয়ে যেতে। আমরা রওনা দিলাম। ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছে দেখি লোকে লোকারণ্য। আমাদের আসার খবরে সাধারণ মানুষ সেখানে অপেক্ষা করছেন। কোনো রকমে ভিড় ঠেলে আমাদের যেতে হল। জিপে উঠে রেসকোর্সে পৌঁছুতে পৌঁছুতে দেখি পথে পথে হাজারও মানুষ নেমে এসেছেন। ময়দানেও তেমনই, হাজার হাজার লোকের ভিড়। সবার মধ্যে বিরাট আনন্দ আর কৌতূহল।
ঐতিহাসিক সেই মুহূর্ত, আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করলেন দুই সেনাপতি
ঐতিহাসিক সেই মুহূর্ত, আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করলেন দুই সেনাপতি
এত ভিড়ের মাঝে সামান্য একটু জায়গা ফাঁকা রাখা ছিল, সেখানে একটি টেবিল পাতা। সামনেই ঢাকা ক্লাব, সেখান থেকে দুটো চেয়ার এনে বসার ব্যবস্থা করা গেল। বসলেন ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে জেনালে অরোরা এবং পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে জেনালে নিয়াজী। তারপর আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করলেন দুজনে।
স্বাক্ষরের পরপরই সিনিয়র পাকিস্তানি অফিসারদের ওখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হল। কারণ আত্মসমর্পণ করেছে বলে পাক সেনা অফিসারদের নিরাপত্তার দায়িত্বভার আমাদের ওপরই বর্তে গেছে। ওদিকে আশেপাশে ঘিরে থাকা হাজার মানুষ উল্লাসে মুখর হয়ে ঊঠলেন। অনেকেই এগিয়ে এসে আমাদের জড়িয়ে ধরলেন। কাঁদছিলেন প্রায় সবাই। কাঁদতে কাঁদতে তারা বললেন, ‘‘আজ থেকে আমরা শান্তিতে ঘুমাব।’’
সত্যিই তো, কী নিদারুণ কষ্ট, দুঃসহ ব্যথা আর উদ্বেগ নিয়ে তারা এতগুলো মাস কাটিয়েছেন। আজ তাদের তাই কান্নার দিন, সুখের কান্না সেটা, ভারহীন মুক্ত জীবনের স্বপ্ন দেখার দিন।
আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান শেষেই আমাদের রওনা দিতে হল। আবার সেই হেলিকপ্টারে আগরতলা এবং আগরতলা থেকে বিমানে করে কোলকাতায় ফিরে যাওয়া।
প্রেতি বছর ১৬ ডিসেম্বর এলেই আমার সে মানুষগুলোর কথা মনে পড়ে যারা আমাকে বলেছিলেন, ‘‘আজ থেকে আমরা শান্তিতে ঘুমাব।’’ একাত্তরে যে ছবি দেখেছি, যেটি অনুভব করেছি সেটি মনের মধ্যে গেঁথে আছে। সেটা আমি কোনোদিন ভুলব না, ভুলব না সেই অশ্রুজলে মাখা আকুতি।
সেদিনও একটি কথা আমার বেশ মনে হয়েছিল, আজও মনে হয়— যে লাখ লাখ মানুষ এই স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিলেন, যাদের ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের এত আনন্দ– তাদের কথা কতটা মনে রেখেছি আমরা? মনে করছি আমরা?
যে দেশের মানুষ রক্ত দিয়ে দেশটিকে স্বাধীন করেছে সে দেশেরই আরও কিছু লোক মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তানের পক্ষে উল্লাস করতে পারে– এটা যে কত বড় লজ্জার তা বলে বোঝানো যাবে না।
এখন তো এদেশে দু ধরনের লোক বাস করে। এক ধরনের মানুষরা হলেন দেশপ্রেমিক; আরেক ধরনের মানুষরা প্রকাশ্যে আমাদের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে। এ ধরনের মানুষদের চরম শাস্তি দিতে হবে– তরুণরা সে শপথ নিক সেটাই চাইব।
এবারের বিজয় দিবসের ঠিক চারদিন আগেই কাদের মোল্লা নামের এক কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসির রায় কার্যকর হল। এতে যতই খুশি হই না কেন আমরা, আমি বলব এটা বিরাট এক কর্মযজ্ঞের শুরু মাত্র। আরও অনেকদূর যেতে হবে। যে ক্ষতি, যে অপমান, যে দুঃসহ ব্যথা সইতে হয়েছে আমাদের জাতিকে— একজন দুজন নয়, হাজারও যুদ্ধাপরাধীর জন্য— তাদের প্রাপ্য শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
আমার বিশ্বাস নতুন প্রজন্ম সে কাজে এগিয়ে নেবে। ওদের ওপর আস্থা রাখাই যায়।
এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) একে খন্দকার: মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান সেনাপতি।
http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/13840
- Biplob Rahman | ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ ১৩:২১582667
- কায়সার হক
যুদ্ধদিনের স্মৃতি: হামজাপুরের টাইগারদের সঙ্গী
ডিসেম্বর ১৬, ২০১৩
১৯৭১ সালের মে মাস। মুক্তিফৌজে যোগ দেবার জন্যে সীমান্তের ধার দিয়ে এগুনোর সময় ঘটনাচক্রে আমি গিয়ে ঠেকলাম পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সদর দপ্তর বালুরঘাটের কাছাকাছি এক ইয়ুথ ক্যাম্পে। সেখানে দেখা হয়ে যায় আমার হাফ ডজন হুল্লোড়বাজ ঢাকাইয়া বন্ধুর সঙ্গে, যার মধ্যে একজন গ্রেগরিয়ান স্কুলের সহপাঠী তান্না, ঢাকা ক্লাবের বর্তমান প্রেসিডেন্ট, দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে উন্নত করার শপথ নেবার কিছুদিন পরই যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য যে ঘর ছাড়ে। সেই ক্যাম্পে কয়েক হাজার কিশোর ৩ দিনের বিশেষ মিলিটারি প্রশিক্ষণের জন্য অপেক্ষা করছিল যারা, তার পরপরই প্রশিক্ষিত গেরিলা হিসেবে ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে দেশের অধিকৃত এলাকাগুলোতে আক্রমণ চালাবে। অপেক্ষার এই সময়টুকুতে ওরা সেখানে বয় স্কাউটের মতো ড্রিল চালিয়ে যাচ্ছিল।
এ রকম সময়ে ৭নং সেক্টর হেডকোয়ার্টার লাগোয়া এই ক্যাম্পটিতে এল একটি দল যারা অফিসার্স ট্রেনিং ক্যাম্পের জন্য যুবকদের বাছাই করতে বিভিন্ন ক্যাম্পে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। আমি আর আমার বন্ধুরা সাক্ষাৎকারের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম। লেফেটেন্যান্ট কর্ণেল কাজী নুরুজ্জামানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের নির্বাচক দলে ছিলেন কর্ণেল সাফায়াত জামীল আর সেক্টর ৭ এর ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার মেজর নাজমুল হক (শহীদ)। নির্বাচিত হয়ে (ক্লাব মেম্বার?) কাইয়ুম খান আর আমি রওয়ানা হলাম ভুটান বর্ডারের কাছাকাছি জঙ্গলঘেরা পাহাড় আর চা-বাগানের মধ্যে অবস্থিত ছবির মতো মিলিটারি স্টেশন ‘মুরতি’তে।
চলচ্চিত্র প্রেমিকদের জন্য জানাচ্ছি, ‘মি. অ্যান্ড মিসেস আইয়ার’ যে জঙ্গলবাড়িতে রাত কাটিয়েছিল তা এই ‘মুরতি’তেই। এই ক্যাম্পে আমার অভিজ্ঞতা নিয়ে Strike a Heroic Pose শিরোনামে ইংরেজি এক দৈনিকের সাহিত্য পাতায় বিস্তারিত লিখেছি (আগ্রহী পাঠকরা পড়ে দেখতে পারেন), তাই আর এখানে এ নিয়ে কিছু লিখছি না।
অক্টোবরের ৯ তারিখ, ৬১ জন ক্যাডেটের আমাদের এই ব্যাচকে নির্বাসিত বাংলাদেশ সরকার সেনাবাহিনীতে অর্ন্তভুক্ত করে আর এক সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের পোস্টিং দেওয়া হয়। এর মধ্যে শেখ কামাল কর্নেল ওসমানির এডিসি হয়ে কোলকাতা যান। আমাদের বাকি ৬০ জনকে পাঠানো হয় ১১ নং সেক্টর আর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিভিন্ন ইউনিটে। অর্থাৎ বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী ৬০ জন সদ্যপ্রশিক্ষিত কোম্পানি কমান্ডার পেল যারা চলমান যুদ্ধকে তীব্র রূপ দিতে পুরোপুরি প্রস্তুত।
আমিসহ ৫ জনকে পাঠানো হল ৭ নং সেক্টরে, যার দায়িত্বে ছিলেন কর্নেল জামান। ক্যাম্পে গিয়ে কর্নেলের তাঁবুতে ঢুকেই আমরা দেখলাম, সবুজ পোশাক পরা গোলগাল ছোটখাট উৎসাহে টগবগ করা একজন অফিসার খুব উত্তেজিতভাবে কোনো একটা ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি সাব-সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন ইদ্রিস যার সঙ্গে বালুরঘাট ক্যাম্পে থাকার সময় আমার আর কাইয়ুমের একবার দেখা হয়েছিল। এক সকালে আমরা তার ক্যাম্পে গিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম তিনি বিশৃঙ্খল একটা দলকে কিছু একটা বোঝাচ্ছিলেন যারা এরপর বাংলাদেশের ভিতর টহল দিতে যাবে।
পেশাগত জীবনে ক্যাপ্টেন ইদ্রিস ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার যিনি কিছুদিনের জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কাজ করেছিলেন। বাঙালিদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক কিছু একটা বলায় পাঞ্জাবি সিইও’র গায়ে হাত তোলার অপরাধে তাকে কোর্ট মার্শালের মাধ্যমে বরখাস্ত করা হয়। যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন তিনি জয়পুরহাট চিনিকলে কাজ করতেন। সে সময় তিনি একদল স্বেচ্ছাসেবক একত্র করে যথাসম্ভব অস্ত্রসস্ত্র জোগাড় করে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। তিনিই ছিলেন হামজাপুর সাব-সেক্টরের দায়িত্বে, যে ক্যাম্পের নামকরণ হয় এর সদর দপ্তর লাগোয়া এক গ্রামের নামে।
“স্যার, আপনি যদি ভারতীয় কামানের ব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা দিনাজপুর আক্রমণ করব।” তার বাহিনী যেখানে অবস্থান নিয়েছে মানচিত্রে সেই জায়গাটা দেখাতে দেখাতে কর্নেলকে বলছিলেন। প্রস্তাবটি নিঃসন্দেহে উত্তেজনাকর। কর্ণেল তার সাধ্যমতো সাহায্য করার আশ্বাস দিয়ে আমিন আর আমাকে ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের সঙ্গে দিলেন। অস্ত্রসস্ত্র ও অন্যান্য দরকারি জিনিস বোঝাই দুটি জিপ নিয়ে আমরা সেই সন্ধ্যাতেই হামজাপুরের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম।
সেখানে পৌঁছে প্রচণ্ড বিষ্ময়ে আবিষ্কার করলাম যে ক্যাম্প লোকে লোকারণ্য। ক্যাপ্টেন সেক্টর হেডকোয়ার্টারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পরই আকষ্মিক আক্রমণ শুরু হয় এখানে, আর লোকজন যে যেদিকে পারে ছুটে নিজেদের রক্ষা করতে চেষ্টা করে। একজন মারা গেছে, কয়েকজন আহত। প্রচণ্ড রাগে ক্যাপ্টেনের মুখ দিয়ে মেশিনগানের মতো তুবড়ি ছুটতে লাগল। বিশেষ করে এক ভিতু এক্স ইপিআর এনসিও-কে উদ্দেশ্য করে বলতে বলতে একটা ভারি কাঠের চেয়ার তুলে নিয়ে বসে পড়লেন। আমিন আর আমি ভীষণ হতাশ হয়ে পড়লাম; বিষণ্নমুখে আমাদের জন্য নির্ধারিত ক্যাম্পে চলে গেলাম।
পরের দিন সকালে ক্যাপ্টেন অনেকটা শান্ত হয়ে এলেন। তার মতো যুদ্ধাভিজ্ঞ একজন কমান্ডার যিনি অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে এসেছেন, জানেন যে কীভাবে খারাপ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। পুরো বাহিনীকে বেরিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হতে আদেশ দিলেন তিনি। নাস্তা শেষ করেই আমরা ৩ ইঞ্চি মর্টার নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ২ ইঞ্চি মর্টারের মতোই বহুল প্রচলিত এই অস্ত্রটি দিয়েও নিশানা ছাড়াই তাক করতে হয়। কিন্তু আমাদের মর্টারম্যান রহমানের সঙ্গে এই অস্ত্রের এতই সখ্যতা যে একজনের পক্ষে যতটা সম্ভব প্রায় ততটাই অব্যর্থ হয় এর নিশানা।
পুনর্ভবা নদীর দক্ষিণভাগ পার হয়ে আমরা কয়েক কিলোমিটার দূরের সীমান্তের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হতাশা, দুঃখ, আতঙ্ক নিয়ে দেখলাম পাকিস্তানিদের তাড়া খেয়ে ধেয়ে আসা বাংলাদেশি শরণার্থীদের ঢল। ক্যাপ্টেন ইদ্রিস কোথায় যেন উধাও হয়ে গেলেন। আমাদের এখন আাবার সবকিছু নতুন করে শুরু করতে হবে। কামদেবপুর হাই স্কুলের খেলার মাঠের কাছাকাছি পৌঁছুতেই আমাদের লক্ষ্য করে বিশৃঙ্খলভাবে গোলাগুলি শুরু হয়। একটা নির্দিষ্ট এলাকা নিরাপদ করে আমরা সারা এলাকা ঘোরাঘুরি করে আর বিচ্ছিন্ন ছোটখাট কিছু যুদ্ধ করে দিন কাটিয়ে দিলাম। অন্ধকার নেমে এলে মৃত সতীর্থদের লাশ নিয়ে আমরা হামজাপুর ফেরত এলাম।
প্রায় এক সপ্তাহ পর, সেক্টর হেডকোয়ার্টারে আমার আর ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের ডাক পড়ে। ২০০ জন গেরিলা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নতুন যোদ্ধাদের নিয়ে দল গঠন করার দায়িত্ব পড়ে আমাদের উপর। পিএমএ থেকে পালিয়ে আসা সাইফুল্লাহ আর বজলুর রশিদ নামের তার এক বন্ধুর যোগ দেয় আমার সঙ্গে। দেরি করে আসায় তাদের পরের ব্যাচের সঙ্গে যোগ দিতে বলা হলেও তারা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে মরিয়া হয়ে পড়েছিল।
আমরা দিনরাত আমাদের প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছিলাম আর অপেক্ষা করছিলাম প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সরঞ্জামের। এর মধ্যে একদিন কর্নেল আমাকে আর সফিউল্লাহকে তার সঙ্গে এক মিশনে যোগ দিতে ডাকলেন। মাঝরাতের দিকে রওনা হয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা হামজাপুর পৌঁছুলাম। দেখা গেল সেক্টর কমান্ডার দলের হয়ে আমাদের এক যুদ্ধে যোগ দিতে হবে। গন্তব্য, পাকিস্তানি সৈন্য অধিকৃত খানপুর বিওপি। আলো নিভিয়ে আস্তে আস্তে ভারতীয় গোপন অস্ত্রের স্তূপ, ট্যাংক বহর, জিপ পেরিয়ে আমরা মিলিত হলাম হামরাপুর দলের সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসা এলএমজিগুলো তাদের হাতে হস্তান্তর করলাম।
ছোট্ট একটা পুকুরের পাড় ঘেঁষা গাছের আড়ালকে অবজারভেশন পোস্ট হিসেবে বাছাই করেছিল কর্নেল যেখান থেকে হামজাপুরের কয়েকজন এলাকাটা পাহারা দিচ্ছিল। চারপাশ সুনসান, ঘন কুয়াশা পড়েছে ক্ষেতের ফসলে। তখন রমজান মাস। শহরে এ রকম সময় সাইরেন বেজে উঠে সেহরির সময় জানাতে।
এখানে তার বদলে আর্টিলারি শেলের বারুদ ঢেকে দিল সমস্ত বাতাস। শত্রুপক্ষ তাদের হাতে থাকা সব ছোট অস্ত্র দিয়ে জবাব দিতে লাগল আমাদের। আর্টিলারির বজ্রগম্ভীর আওয়াজ, গোলাগুলির একঘেয়ে উন্মত্ততা, উত্তেজনায় আমাদের দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগল। সাইফুল্লাহ আর আমার কাজ হল ছোট ছোট অস্ত্রের শব্দ দিয়ে ওদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করা। কিন্তু এই ভয়ংকর শব্দে তা নিতান্তই অর্থহীন।
একসময় আমরা ধানক্ষেতের ভিতর দিয়ে আক্রমণকারীদের পালিয়ে যাওয়ার শব্দ বুঝতে পারলাম। আমার কোর্সমেট আমিন ছিল সেদিনকার হামলার নেতৃত্বে। গোলাগুলি আস্তে আস্তে দূর থেকে দূরতর হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেল। ফিকে হয়ে আসা অন্ধকারের মধ্যে থেকে কুয়াশা ভেদ করে ৪ নং মাদ্রাজ রেজিমেন্টের ভারতীয় সৈন্যরা এগিয়ে এসে হামজাপুর দলের সঙ্গে যোগ দেয়। কর্নেলকে সঙ্গে নিয়ে আমরা তাদের সঙ্গে কমান্ড পোস্টের দিকে এগুতে এগুতে দেখতে পাই মাদ্রাজ সিও আর ক্যাপ্টেন ইদ্রিসকে।
পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধ তখনও চলছিল। হঠাৎ করে কেউ একজন সাঁজোয়া বাহিনী কালো পোশাক পরা কাউকে লক্ষ্য করল। শত্রুপক্ষের কামান হতে পারে ভেবে ভারতীয় সিও তৎক্ষণাৎ সহায়ক দল চেয়ে রেডিও বার্তা পাঠাল। মূহুর্তের মধ্যেই একটা দল এসে দাঁড়াল আমাদের পেছনে। “এবার কিছুটা ঝামেলা হতে পারে”, সিও বলল। সম্পূর্ণ নতুন মোড় নিল যুদ্ধ। ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সমন্বিত আক্রমণের সময় এখন। সফিউল্লাহ আর আমার স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্ত বাহিনী সঙ্গে নিয়ে স্বল্পচেনা পুনর্ভবার পশ্চিম পাড়ে যুদ্ধের মুখোমুখি আমরা।
যুদ্ধের পরিস্থিতি দাঁড়াল এ রকম: পুনর্ভবার পূর্বপ্রান্তে হামজাপুরের মূল বাহিনী ক্যাপ্টেন ইদ্রিস আর আমিন, সেই সঙ্গে মাদ্রাজ বাহিনী লে. কর্নেল মালহোত্রার নেতৃত্বে। পুনর্ভবার পশ্চিম পাড়ে নবপ্রশিক্ষিত আলফা বাহিনী নিয়ে আমি আর সফিউল্লাহ। দিনাজপুর শহর আর সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত বিখ্যাত ঢিবি রামসাগর ঘিরে পাকিস্তানি রক্ষণভাগ। সাবসেক্টরের পুরোনো বাসিন্দারা ইতোমধ্যেই খাঁটি বাঙালি ভঙ্গিতে তরুণ যোদ্ধাদের নাম দিয়েছে ‘হামজাপুর টাইগার’। যাদুর মতো কাজ করে যখন বলি “তোমরা হামজাপুর টাইগার দলের সদস্য।” শেষবার যখন আমি এখানে এসেছিলাম নদীর পশ্চিম প্রান্তে তার থেকে কিছু পরিবর্তন হয়েছে।
ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের বাহিনী পিছু হটলে আশেপাশের গ্রামের বাংকার থেকে পাকিস্তানি বাহিনী যোগ দিতে থাকে ওই এলাকা দখল করতে। দক্ষিণ দিনাজপুরের দুপাশের সীমান্ত এলাকাজুড়ে শালবন যেখানে রয়েছে সাঁওতাল বসতি। বনের উত্তর পাশ ঘেঁষে পাকিস্তানি বাংকার সীমাবদ্ধ। আমার ধারণা তারা ভয় এই ভেবে যে গেরিলা বাহিনী বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ঝটিকা যুদ্ধ চালিয়ে আবার বনের ভিতরেই পালিয়ে যেতে পারে। (এ পর্যায়ে এসে এখন আমার মনে হচ্ছে আমার গল্প সংক্ষেপ করতে হবে। কিন্তু আমি আর আমার বন্ধু আমিন আরও কিছু জানাতে চায়।)
সামনে আমরা দুটো লক্ষ্য ঠিক করেছিলাম: পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে ওই গ্রামগুলো মুক্ত করা আর তাদের বাংকারগুলো সরাতে বাধ্য করা। আমরা গ্রামগুলো ঘেরাও করে এলাকাগুলো রীতিমতো চষে ফেলি। শত্রুর শক্তিক্ষয়ের জন্যই এ যুদ্ধ। অস্ত্রের অভাব সত্ত্বেও (রাইফেল, স্টেনগান, এলএমজি, ২ ইঞ্চি মর্টার, একটা ৮১ মিমি মর্টার, গ্রেনেড কিন্তু নেই কোনো রকেট লাঞ্চার, এমনকি গ্রেনেড ছোঁড়ার রাইফেল পর্যন্ত ছিল না; ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরের সঙ্গে থাকা কাইয়ুমের কাছে অবশ্য কিছু ছিল)। আমার মূল শক্তি ছিল লোকবল। অন্যদিকে পাকিস্তানি বাহিনীর সেখানেই দুর্বলতা।
শত্রুপক্ষের বেশ কিছু মরিয়া চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এক সকালে তারা নদীর পার দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করে ধাওয়া খায়। অন্য এক রাতে বনের দক্ষিণ পাশে শুরু হয় প্রচণ্ড গোলাগুলি। আমাদের একটা দল শালবনের প্রান্তে ঘাঁটি গেড়েছিল। সারারাত সজাগ থেকে পরের দিন সেখানে ছুটে গিয়ে দেখি, গোলাগুলি এতই বেশি হয়েছিল যে আমাদের লোকজন বনের ভিতর পালিয়ে গেছে।
অবাক ব্যাপার হল, শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্যই মনে হচ্ছিল কেবল ভয় দেখানো। হঠাৎ আমাদের একজন চেঁচিয়ে উঠে আলগা মাটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমার। উপরের মাটিটা সরাতেই প্লাস্টিক বেরিয়ে আসতে দেখে খুব সাবধানে আরেকটু মাটি খুঁড়ে বের করি প্লাস্টিক অ্যান্টি-পার্সোনাল মাইন যেটা একটা বিশাল অ্যান্টি-ট্যাংক মাইনের সঙ্গে জোড়া ছিল। সেদিন ও রকম চারটা মাইন আমি নিষ্ক্রিয় করেছিলাম। আমাদের একজন নির্মম রসিকতা করে বলেছিল, ‘‘একটা ভুল পদক্ষেপ আমাকে কিমা বানিয়ে ছেড়ে দিত।’’
মাইন সব যুদ্ধেই একটা বড় সমস্যা। একটা ট্রিপ-ওয়্যার মাইনের আঘাতে আমাদের বেশ কয়েকজন ছেলে আহত হয়েছিল। যুদ্ধশেষে দিনাজপুর এলাকার সবগুলো মাইন সংগ্রহ করে একটা স্কুলে রাখা হয়েছিল যেখানে আবার মুক্তিবাহিনীর লোকজনও থাকত। এদের মধ্যে অন্তত থেকে গিয়েছিল যেটা নিস্ক্রিয় হয়নি যার ফলে পুরো বিল্ডিংটাই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে উড়ে যায়, মারা যায় প্রায় ৩০০জন। সুদূর বগুড়া থেকে এ শব্দ শোনা গিয়েছিল। বদলি সুবাদে আমরা তখন সেখানেই ছিলাম। লোকজন আমাদের কাছে ছুটে এসে জানতে চাইছিল কী হয়েছে। একজন তো ভেবেছিল আমেরিকা ভয় দেখাতে দেখাতে সরাসরি আঘাত হেনেছে।
শত্রুপক্ষের আকষ্মিক হামলায় ৪নং মাদ্রাজ বাহিনীর একজন অফিসার এবং কয়েকজন জওয়ান তাদের হাতে আটক হওয়ার পর তাদের জায়গায় আসে ১২ নং গাড়ওয়াল রাইফেলস বাহিনী। আমাদের তখন ফিল্ড টেলিফোন আছে। একদিন আর্টলারি ওপি এসে আমার সঙ্গে টহল দিতে বেরিয়ে শত্রুবাহিনীর বাংকারে আঘাত হানে।
আরেকদিন খুব সকালে আমরা শত্রুপক্ষের দক্ষিণপ্রান্তের বাংকার নেটওয়ার্ক ছারখার করে দেয়। অন্য আরেকটা গ্রাম ঘেরাও করতেই শত্রু কোনো রকম প্রতিরোধের চেষ্টা না করেই পালিয়ে যায়। একটি নতুন গেরিলা দল আমাদের সাথে যোগ দেয় যার ফলে আমাদের পক্ষে গ্রামগুলোর আরও গভীরে যাওয়া তখন সম্ভব হচ্ছিল। এক গ্রামে একদিন একটা ছেলে আমাদের কাছে কেঁদে কেঁদে বলছিল কীভাবে তার আর বোনের উপর অত্যাচার হয়েছিল। সেই যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি আমি জীবনে কখনও ভুলব না।
আমাদের সঙ্গে দুটো বাহিনী থাকায় আমরা তখন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করি। তখন আমাদের কাছে ওয়াকিটকি পর্যন্ত এসে গেছে (এগুলো মর্টার ছুঁড়তে বলার জন্য খুব কাজের)। কয়েকটা মোটরবাইকও জোগাড় হয়েছে যার ফলে আমরা অনেক সহজে আমাদের ঘাঁটিগুলো পরিদর্শনে যেতে পারি। তখন সাইফুল্লাহ থাকে একটা দলের সঙ্গে এক গ্রামে আর আমি অন্য একদল নিয়ে অন্য গ্রামে। মাঝখানে বিস্তৃত ধানী জমি। প্রতিদিন আমরা দুজন দিনের কর্মসূচি ঠিক করার জন্য দেখা করতাম।
একদিন সাইফুল্লাহ ঠিক করল মাঠ পেরিয়ে আমার ওখানে আসবে, ভেবেছিল কুয়াশা তাকে শত্রুদের চোখ থেকে আড়াল করে রাখবে। হঠাৎ করেই গোলাগুলি শুরু হয়। একটা ছেলে এসে আমাকে খবর দেয় যে সাইফুল্লাহ আহত হয়েছে। বেরিয়ে যেতেই দেখি ও প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে। আমি দৌড়ে গিয়ে পড়ে থাকা গাছের আড়ালে তাকে টেনে আনি। গুলি তখনও চলছিল। মূহুর্মুহু গুলির ঘা লাগছিল পড়ে থাকা গাছগুলোর গায়ে। চিৎকার করে আমি একটা এলএমজি চাইলাম। তারপর গাছের গুঁড়ির উপর সাবধানে রেখে গুলি যেখান থেকে সেখানটা তাক করে গুলি ছুঁড়ি। পাল্টা গুলি বন্ধ হয়ে যায়। সাবধানে সাইফুল্লাহকে সেখান থেকে নিয়ে এসে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করি। ভাগ্যক্রমে গুলি হাড় ভেদ করেনি।
দুঃসাহসী সাইফুল্লাহকে অবশ্য হাসপাতাল বেশিদিন আটকে রাখতে পারেনি। ঝোলানো হাত নিয়ে হাসপাতাল পালিয়ে রণক্ষেত্রে হাজির হয় ও, মুখে হাসি নিয়ে। ততদিনে যুদ্ধের চূড়ান্ত সময় ঘনিয়ে আসছে। এর মধ্যে একবার রামসাগর আক্রান্ত হল। ১২ নং গাড়োওয়াল্যান্ডকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দিনাজপুর জিতে নিতে পারতাম কিন্তু ভারতীয় সিও কৌশলগত কারণে আমাদের থেমে থাকতে বললেন। তা অবশ্য আমাদের মারমুখো প্যাট্রোলিং কিংবা ক্যাপ্টেন ইদ্রিসকে তার শেষ মরিয়া চেষ্টা থেকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। তাঁর এবং আমাদের ২ প্লাটুন করে সৈন্য, সঙ্গে আমার মর্টার আর সাইফুল্লাহকে সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসেবে সঙ্গী করে তিনি ঠিক করলেন জেলার পশ্চিম সীমান্তের বিরলের দিকে এগুবেন।
ডিসেম্বরের ১৪ তারিখ হঠাৎ শত্রুর এক ফাঁদে পড়ে ক্যাপ্টেনের শরীরের নিচের অংশে আঘাত লাগে। পরবর্তীতে তাঁকে ‘বীরপ্রতীক’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়, যদিও যুদ্ধ শেষে তাঁকে অনাড়ম্বরভাবেই দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। এই ১৪ তারিখেই বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর মোহদিপুর যুদ্ধে নিহত হয়। পরের দিন শত্রুপক্ষ দিনাজপুর ছাড়ে।
এবার শেষ করার পালা। ১৯৭১ সালের সেইসব অকথিত হিরোদের শ্রদ্ধা জানাতে চায় যারা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ হয়েও দেশের জন্য তাদের সর্বস্ব বাজি রেখেছিল। আমার দলের ছেলেদের মধ্যে কেউ বিশ্ববিদ্যলায়ের ছাত্র ছিল না। এর মধ্যে একজন ছিল পনের বছর বয়সী ক্লাস নাইনের একজন– হাসিখুশি ও সাহসী ছেলে। কিছু কলেজপড়ুয়া ছাত্র যারা প্লাটুন কমান্ডার হয়েছিল; এদের মধ্যে একজন ছিল খুব সাহসী এক্স ইপিআর জেসিও। বাকিরা গ্রামের সাধারণ যুবক, কৃষক যারা স্বপ্ন দেখত স্বাধীন দেশ হবে শান্তিময় আর সমৃদ্ধশালী।
আমি তাদের বুঝানোর চেষ্টা করতাম ও রকম আকাশ কুসুম না ভাবতে যদিও আমার মনে হয় না তারা আমার এ কথায় পাত্তা দিত। উন্নত এক দেশ গড়তে তারা উৎসুক ছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুর্নগঠনের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কথা ভাবা হলেও পরে তা বাতিল করা হয়। আমাদেরকে বলা হয় প্রত্যেককে ৫০ টাকা করে দিয়ে নিজ নিজ জায়গায় ফেরত পাঠিয়ে দিতে।
সে সময় দুঃখ আর অপরাধবোধে আমার ভিতরটা গ্রাস করেছিল। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার লেখাপড়া শুরু করতে চাইছিলাম। অন্তত তিনবার আবেদনের প্রেক্ষিতে অবশেষে ১৯৭২ সালে আমি ছাড়পত্র পাই। কিন্তু তারপরও আমার দলের সবার মতোই আমিও ভাবি যে, আবার যদি একই জীবন যাপন করতে হত, আবার আমি এদের সঙ্গেই কাটাতে চাইতাম।
হামজাপুরের বাঘ পরিবারের একজন হিসেবে আমার গর্বের শেষ নেই।
অনুবাদ: রেশমী নন্দী।
কায়সার হক: কবি, অনুবাদক, প্রাবন্ধিক, সাহিত্যসমালোচক ও শিক্ষক।
http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/13832
- Biplob Rahman | ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ ১৩:২৩582668
- আবেদ খান
ভিন্ন প্রেক্ষিতে এবারের বিজয় দিবস
ডিসেম্বর ১৫, ২০১৩
আবেদ খানবিয়াল্লিশ বছরের ভেতরে বাঙালি জাতি এই প্রথম একটি অন্যরকম বিজয় দিবস পালন করছে। একাত্তরের বিজয় দিবস ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের বিরুদ্ধে বাঙালির চূড়ান্ত বিজয়। সেই বিজয়ের ভেতর দিয়ে বাঙালি জাতি তার আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং সেই সময়ের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ।
এরপর বুড়িগঙ্গায় অনেক পানি গড়িয়েছে, আমাদের রাজনীতিতে যে টানাপড়েন চলেছে তার প্রতিফলন ঘটেছে এই বিজয় দিবসের ওপরও। দিবস দিবসের চেহারা পাল্টেছে একটু একটু করে। যুদ্ধের যে চেতনা, সেটা ক্রমশ দূর থেকে সুদূরপরাহত হয়ে উঠেছে। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির ক্রমান্বয়ে অনুপ্রবেশ ঘটেছে রাষ্ট্রপরিচলনার অন্দরে। এ সময় থেকে বিজয় দিবসটি খণ্ডিত ও বিপর্যস্ত হতে শুরু করে। আজ এই বিয়াল্লিশ বছর পর বিজয় দিবসটি অন্য মাত্রা পেয়েছে, ভিন্ন এক শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। আমাদের এক বৃহৎ সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে এই বিজয় দিবসের আগমন।
আক্ষরিকভাবে দেখতে গেলে এটা সত্য বটে যে, একাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। যেহেতু পাকিস্তানি বাহিনী একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালে আমাদের শত্রু হিসেবে পরিগণিত, সেহেতু আমরা ধরে নিতে পারি যে ওইদিন আমাদের চিহ্নিত শত্রুরা অস্ত্রসমর্পণের মাধ্যমে পরাজয় মেনে নিয়েছিল।
ব্যাপারটি সর্বাংশেই যুদ্ধক্ষেত্রের। যুদ্ধে এক পক্ষের জয় হয়েছে এবং অন্য পক্ষ পরাজিত হয়েছে। কিন্তু এ থেকে কি এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে যে বাংলাদেশ একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত হয়েছে? তা-ই যদি হবে তাহলে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ কেন সংঘটিত হল? কেন তেসরা নভেম্বর জেলহত্যা হল?
পুরো পঁচাত্তরেই তো চলেছে নির্মম হত্যাযজ্ঞ এবং হত্যাকারীদের পুনর্বাসনের কার্যক্রম। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রায় সপরিবারে হত্যা করা হল। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা সরকারের যে চার নেতা ছিলেন, তাদের হত্যা করা হল, হত্যা করা হল প্রতিশ্রুতিশীল রাজনীতিক শেখ ফজলুল হক মণি ও তার সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে। রক্ষা পেলেন না বঙ্গবন্ধুর ভাই কিংবা ভগ্নিপতিও। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর পরিবারের কোনো চিহ্ন যেন না থাকে তার চেষ্টা করা হল এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাদেরও অনেকে রেহাই পেলেন না। হয়তো কোনোমতে প্রাণরক্ষা করতে পেরেছেন কেউ কেউ, কিন্তু কেউ কি পেরেছিলেন ওদের প্রতিহত করতে? কেন ঘটল এতসব ঘটনা?
দেশ যদি একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর শত্রুমুক্তই হয়ে থাকে তাহলে শাহ আজিজুর রহমান নামের একজন মুসলিম লীগার, যিনি পাকিস্তানের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ অবস্থান নিয়েছিলেন, কী করে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন? কী করে গোলাম আযমকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার ছাড়পত্র দেওয়া হয় এবং একসময় দিয়ে দেওয়া হয় নাগরিকত্বও? কী করে শর্ষিনার পীরকে দেওয়া হয় স্বাধীনতা পদক?
দেশ যদি বিয়াল্লিশ বছর আগের ষোলোই ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত হয়েই থাকে, তাহলে চিহ্নিত স্বাধীনতাবিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী কী করে দেশে রাজনীতি করতে পারে, নির্বাচন করতে পারে, একটা সময়ে সরকারের অংশীদার হতে পারে? কিংবা নিজামী-মুজাহিদের মতো আলবদর বাহিনীর নেতারা কী করে পাঁচ বছর মন্ত্রিত্ব করতে পারেন?
একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বরের পরদিন থেকেই আসলে স্বাধীনতার শত্রুদের তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। মুক্তির উৎসবে আমরা এতই আপ্লুত হয়েছিলাম যে স্বাধীনতার শত্রুদের অস্তিত্ব অনুভব করতে তো পারিই-নি, বরং তাদের ক্ষমতা তুচ্ছ জ্ঞান করেছি। অথচ স্বাধীনতার শত্রুরা কখনও অপ্রস্তুত ছিল না। একাত্তরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকেই তারা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের পরাজিত হতেই হচ্ছে সামরিকভাবে; তাই তারা আলবদর-আলশামস বাহিনী তৈরি করেছিল বাংলাদেশকে বুদ্ধিজীবীশূন্য করার লক্ষ্যে।
পোড়ামাটি নীতি গ্রহণের মাধ্যমে তারা ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল একাত্তরের শেষ দিনগুলোতে। প্রশাসনে যারা ছিল, তারা আত্মরক্ষার জন্য একদিকে যেমন নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছিল, অন্যদিকে তেমনি সুযোগমতো গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান বাছাই করার চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছিল। মাত্রাতিরিক্ত আবেগ আমাদের বাস্তবতা থেকে ক্রমাগত দূরে ঠেলে দিচ্ছিল আর ওরা দুর্বল মুহূর্তগুলোর পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করে চলেছিল এবং সুবিধামতো জায়গায় অবস্থান নিয়ে নিচ্ছিল।
এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় হল, মুক্তিযুদ্ধের পর যখন আওয়ামী লীগ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্তরের নেতার মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির প্রশাসক হওয়ার প্রতিযোগিতা শুরু হয়, তখন ঘাপটি মেরে থাকা প্রতিপক্ষ সুকৌশলে ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল ক্ষেত্রগুলো সঙ্গোপনে কব্জা করে ফেলে। আমদানিই হোক আর গ্র্যান্ট কিংবা কোনো ধরনের বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ– যা-ই হোক না কেন, সবকিছুরই নিয়ন্ত্রক হয়ে বসে তারাই। এর কুফল ফলতে যে দেরি হয়নি সেটা সে সময়কার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে চোখ রাখলেই বোঝা যাবে।
বাহাত্তর সাল থেকেই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের প্রশ্নে সিন্ডিকেট সক্রিয় হয়ে ওঠে। যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে ঘিরে সিন্ডিকেট শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন তৎকালীন সেই মন্ত্রী, যিনি পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট এবং তার পরবর্তী দিনগুলোর কর্মকাণ্ডের নেপথ্যের মূল নায়ক। তিনি সেই মানুষ, যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগারে রেখে পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। চুয়াত্তরে মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ এরই ফসল।
পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনার পরের সুদীর্ঘকালের ইতিহাস তো একচেটিয়াভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী শক্তির আস্ফালনের ইতিহাস। আমরা শুধু দেখেছি কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তি পশ্চাদপসরণ করতে করতে ক্রমাগত কোনঠাসা হয়ে পড়ছে; কীভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি নানা কৌশলে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করছে।
স্বাধীনতার পর বাহাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনার আলোকে আমাদের যে সংবিধান রচিত হয়েছিল, সেই সংবিধানটিকে নানা সময়ে বার বার কাটাছেঁড়া করে বিপন্ন করা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এই চেতনার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ মূল চার নীতি কাটছাঁট করা হয়েছিল, সম্প্রতি সেই অসাম্প্রদায়িক ও কল্যাণকর রাষ্ট্রনীতি নতুন করে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হয়েছে, যদিও সে চেষ্টা সামগ্রিক ও সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি।
তারপরও এক এক করে আমাদের সংবিধানকে কলঙ্কমুক্ত করা গেছে। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে পঁচাত্তরের ঘাতকদের চিহ্নিত করে বিচার করা হয়েছে এবং বিচারের মাধ্যমে চূড়ান্ত শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। এরই মধ্যে জাতির কাছে এক নতুন অঙ্গীকার এসে দাঁড়িয়েছিল, তা হল– একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য দায়ী অপরাধীদের বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা।
আমরা দেখেছি, ছিয়ানব্বইয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসায় তারা সামান্য সময়ের জন্য থমকে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তাদের চক্রান্তকারী তৎপরতায় এতটুকু ঘাটতি পড়েনি। ২০০১ সালের নির্বাচনে তাদের উত্থান ও নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণতা থেকে বোঝা যায় তারা কী পরিমাণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। জোট সরকারের আমল জুড়ে তারা জঙ্গিবাদ ও স্বাধীনতাবিরোধী মানসিকতার চাষাবাদ করেছে।
২০০৮-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটের জয় আবার তাদের থমকে দিয়েছে, কিন্তু দমাতে পারেনি। পূর্ণোদ্যমে তারা চালিয়ে যাচ্ছে ষড়যন্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তির সরকারের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছে বটে, কিন্তু বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়নি এবং নানামুখী ষড়যন্ত্রের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এই দেশ। স্বাধীনতার শত্রুরা এখন অনেক বেশি শক্তিশালী, অনেক বেশি সংগঠিত। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ।
২০১৩ সাল জুড়েই, বিশেষ করে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত অপরাধীদের এক একটি রায় ঘোষণার পর পর, আমরা দেখেছি কীভাবে অরাজকতা পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে। কীভাবে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছে, নাশকতা করা হয়েছে রাষ্ট্রের ও সাধারণ মানুষের সম্পদের ওপর। আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে মানবতাকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে। তা এখনও চলছে। বিশেষ করে একজন মানবতাবিরোধী অপরাধীর ফাঁসির রায় কার্যকরের পর এই অশুভ শক্তি নৃশংসতার সব উপায় নিয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।
২০১৪ সালে বাংলাদেশের নির্বাচনের মূল শক্তি হবে একটি নতুন প্রজন্ম। তারাই ২০০৮ সালে স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তিকে বিপুল ম্যান্ডেট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছিল। তারা পরিপূর্ণভাবে বাংলাদেশেরই প্রজন্ম। তাদের কাছে মুক্তিসংগ্রামের সুদীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছরের ইতিহাস অজানা– অজানা মুক্তিযুদ্ধের বিশাল পটভূমি কিংবা ঘটনাবলিও। তারা কীভাবে দেখবে দেশকে, কীভাবে দেখবে মুক্তিসংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে? এই নতুন প্রজন্মের কাছে দেশ এবং দেশের ইতিহাস যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য যে কাজ করার কথা ছিল পূর্বসূরিদের, তা কি তারা ঠিকমতো করতে পেরেছেন? কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে নতুন প্রজন্মের হাতেই চলে যাবে দেশটা।
প্রকৃতপক্ষে এবারের বিজয় দিবস হচ্ছে বাঙালির অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ের দিবস এবং সেই অস্তিত্বের লড়াইয়ে নতুন প্রজন্মই নেতৃত্ব দেবে, যুদ্ধ করবে। এ এক ভিন্ন যুদ্ধ, কিন্তু এর আদর্শ ও চেতনা সেই একাত্তরের। একাত্তরের ঘাতকেরা দীর্ঘদিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ছত্রচ্ছায়ায় থেকে তারা লাখো শহীদের রক্তে রাঙা লালসবুজ পতাকাকে তাদের শকটে এবং বাসভূমিতে ওড়ানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল যারা, আজকে তারাই আবার এই বিজয় দিবস এবং এই বিজয়ের মাস কলঙ্কিত করার জন্য নানা চক্রান্তের ফাঁদ পেতেছে।
এরই মধ্যে সমস্ত সংশয় দূর করে একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য গঠিক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল বিচারকার্য সম্পন্ন করেছে কতিপয় শীর্ষ মানবতাবিরোধী অপরাধীর। তাদের একজনের চূড়ান্ত বিচারের রায় কার্যকরও সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমাদের আশার জায়গা এখানেই। সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে আমরা এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে। সেই সামনে এগোনোর পথে যত বাধা আছে, তা সাময়িকভাবে যতই জঙ্গিশক্তিতে অরাজকতা সৃষ্টি করুক, নৈরাজ্য আনুক বাংলার প্রত্যন্ত জনপদেও, শেষ জয় আমাদের হবেই।
অর্থনৈতিকভাবে আমাদের উত্থান আগামীতে বাংলাদেশকে প্রভাবশালী রাষ্ট্রে পরিণত করবে। এমন ‘স্বপ্নের বাংলাদেশ’ অদূর ভবিষ্যতে বাস্তব রূপ পাবে, শুধু ‘স্বপ্নের জগতে’ আটকে থাকবে না। আমি নিশ্চিত।
আবেদ খান: সাংবাদিক, প্রকাশিতব্য দৈনিক জাগরণ-এর সম্পাদক।
http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/13819
- Biplob Rahman | ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ ১৩:২৫582669
- ডা. নুজহাত চৌধুরী
জয় বাংলা
ডিসেম্বর ১৩, ২০১৩
সবিনয় অনুরোধ করি, প্রথমেই ধরে নেবেন না আমি দলীয় শ্লোগান দিচ্ছি। না, তা নয়। এ আমার হৃদয়-নিঃসৃত বর্ণমালা। জাতির এ মাহেন্দ্রক্ষণে ‘জয় বাংলা’-ই আমার গর্বিত উচ্চারণ। কেন তাই বলছি।
কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকর হবার পর থেকে রাতভর আমার মোবাইলে একের এক ম্যাসেজ আসতে থাকল। ফেইস বুকের ইনবক্সে ম্যাসেজের পর ম্যাসেজ। অবাক হয়ে দেখলাম সব ম্যাসেজে একই কথা লেখা, খুবই সংক্ষিপ্ত একটি ম্যাসেজ ‘জয় বাংলা’। অথচ আমার পরিচিতজনের বেশিরভাগই স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তি হলেও রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। আমি ডাক্তার, তাই বন্ধু-বান্ধব বেশিরভাগই ডাক্তার, রোগী বা এমন মানুষজন যারা সাধারণ জনগণের অংশ, যাদের বেশিরভাগই প্রচলিত রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ।
কিন্তু কাল রাতে যেন এক ’৭১ ফিরে এসেছিল। সবার মুখে মুখে শুনলাম একই শ্লোগান ‘জয় বাংলা’। কেউ উল্লাস নিয়ে বলছে, কেউ যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ঘৃণা নিয়ে বলছে, কেউ কেউ প্রত্যয় নিয়ে বলছে, কেউ কেউ আশা নিয়ে বলছে। তাই আমিও তখন চোখের জলে বুক ভিজিয়ে উচ্চারণ করলাম– ‘জয় বাংলা’।
পাকিস্তান আমলে নিপীড়িত ও শোষণের যাঁতাকলে পড়ে বাঙালি বুঝতে পারল তার আত্মপরিচয় কী, তার জাতিগত পরিচয় কী। বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ সুস্পষ্ট দাবি হয়ে উদ্ভাসিত হল ‘জয় বাংলা’ শ্লোগানে। এরপর বহু নির্যাতন, বহু আত্মত্যাগ। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দলমত নির্বিশেষে সবাই এ শ্লোগান নিয়েই স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখেছিল। তরুণ, নবীন প্রাণ সামনে পড়ে থাকা একটি দীর্ঘ জীবনের মায়া তুচ্ছ করে ট্যাংকের নিচে আত্মবলি দিয়েছে এই শ্লোগান বুকে ধারণ করে। একথা বহুবার বলা হয়েছে। তাও আবার বলতে হবে, কারণ এই বিশাল আত্মত্যাগের যোগ্য মর্যাদা তাদের উত্তরসূরী হিসেবে আমাদের দিতেই হবে। এ আমাদের জন্মগত দায়বদ্ধতা, দেশের প্রতি, দেশের সূর্যসন্তানদের প্রতি।
আজ ‘জয় বাংলা’ শ্লোগান একটি দলীয় শ্লোগান বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু শহীদ সন্তান হিসেবে আমি আজ তীব্র চিৎকারে বলতে চাই যে এ আমাদের পুরো জাতির শ্লোগান। আওয়ামী লীগ এটি ধরে রেখেছে। সেটা তাদের সাফল্য। আমরা সাধারণ মানুষ কেন ধরে রাখতে পারলাম না এ আমাদের ব্যর্থতা। এমনকি স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি বলে পরিচয় দেন এমন মানুষগুলোর তথাকথিত ‘নিরপেক্ষতা’ ভ্রান্তির কারণে ও দলীয় সিল পড়ার ভীতির কারণে এ ‘শ্লোগান’ প্রাণে ধারণ করলেও মুখে উচ্চারণ করেননি। এ আমাদের ব্যর্থতা, এ আমাদের ক্ষুদ্রতা, এ আমাদের ভীরুতার পরিচায়ক।
যারা ‘বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ’-এর প্রবক্তা তারা আমার জাতিসত্তার চেতনাকে বিভ্রান্ত করার জন্য এ জাতির বিরুদ্ধে এক নিগূঢ় ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ‘বাঙালি জাতীয়তাবাদের’ বিপরীতে ‘বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ’ তৈরি করেন। কিন্তু জাতিসত্তার পরিচয় তৈরি করার কোনো বিষয় নয়। এটা রক্তের উত্তরাধিকারের বিষয়, হাজার বছরের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মাধ্যমে গড়ে ওঠা রক্তের পরিচয়।
কিন্তু ‘ন্যাশনালিটি’ আর ‘সিটিজেনশিপ’ অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ ও নাগরিকত্ব এ দুটোর পার্থক্য বোঝা এমন কোনো কঠিন কাজ নয়। আমার বাবা-মা একবার ছিলেন ব্রিটিশ, একবার পাকিস্তানি। বাবা বাংলাদেশি হবার সুযোগ পাননি, স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি শহীদ হয়েছেন। মা এখন বাংলাদেশি। তবে কি জাতীয় পরিচয় একটি পোশাকি বিষয় যা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যাবে? এই শিশুসুলভ যুক্তি বিশ্বাস করার পিছনে নির্বুদ্ধিতা কাজ করে, নাকি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা?
সুতরাং স্পষ্ট করে বলছি, বাংলাদেশের নাগরিক হবার সুযোগ না পেলেও আমার বাবা ছিলেন একজন বাঙালি। মা তখন ছিলেন বাঙালি, আজও বাঙালি। আমি বাঙালি। আমার প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর যে দেশেই থাকুক সে হবে বাঙালি। যদি পরবর্তী প্রজন্ম বিদেশে থাকে তবে তার নাগরিকত্ব হবে দেশের কিন্তু জাতিপরিচয় হবে চিরকালই বাঙালি।
তবে সে বির্তক আজ নয়, দুটো রাজনৈতিক ধারার তুলনামূলক বিষয়ে কথা বলার দিনও আজ নয়। আজ দিন জয়গানের, আজ দিন সন্তুষ্টি আর কৃতজ্ঞতার বাঁধভাঙ্গা অশ্রুর। তাই আজ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি চারিদিকে সবাই বলছে ‘জয় বাংলা’। আমাদের যে কোনো জয়গানের উচ্চারণ যে ‘জয় বাংলা’, কাদের মোল্লার ফাঁসির পর আজ আবার আমি স্পষ্ট করে বুঝতে পারলাম।
কাল রাতে একজন সাধারণ নাগরিক আমাকে ম্যাসেজে লিখেছেন, ‘‘বিয়াল্লিশ বছর বঞ্চনার পর একজন যুদ্ধাপরাধীর শাস্তি দেখলাম। এত আনন্দ, এত বেদনা, এত প্রশান্তি, এত অনুভূতি হচ্ছে যা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। মনে হচ্ছে শুধু দুটি শব্দই আমার অনুভূতির ধারণ করতে পেরেছে। তা হল ‘জয় বাংলা’, তাই শুধু সেটাই বারবার উচ্চারণ করছি।”
সেই ক্ষণে আমারও তাই মনে হল। এই তীব্র কষ্ট, আনন্দপ্রাপ্তির বিশালতা ধারণ করতে পারে তাহলে আজ বুঝি শুধু ওই দুটি শব্দেই সেই বিশালতা আছে। শহীদ সন্তান হওয়ার সাধারণ মানুষ, সাংবাদিক সবাই জানতে চাচ্ছেন স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে এই প্রথম একজন যুদ্ধাপরাধীর মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য শাস্তি কার্যকর হল। শহীদ সন্তান হিসেবে আমার কেমন লাগছে? যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবির এ দীর্ঘ সংগ্রামের ক্লান্ত অবসন্ন, অভিমানী বুক থেকে যে তীব্র দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে, সে কি অনুভূতির সমন্বিত ফসল তা আমি কীভাবে বুঝাই?
আমার মনে পড়ে যায় এই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উচ্চারণও একসময় ছিল দুঃসাহসের পরিচয়। এদেশে আমার মতো হাজার হাজার অভাগা পিতৃহীন সন্তান আছে যারা পিতৃহন্তারককে শাসনক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করতে দেখেছে– যখন তারা ও তাদের মায়েরা রাস্তায় সংগ্রাম করছে টিকে থাকার। আমরা যারা আপনাদের সামনে কথা বলি তারা তাও হয়তো কিছুটা শক্ত মাটি পায়ের নিচে তৈরি করতে পেরেছি এতদিনে। কিন্তু জীবনসংগ্রামে পর্যুদস্ত লক্ষ লক্ষ শহীদ পরিবার আজও রাস্তায়– নিগৃহীত, অবহেলিত এবং প্রতিটি মুহূর্তে অপমানিত।
এ অপমান শুধু তাদের নয়, আমার নয়, আমার আপনার সকলের। সে অপমানের, সে অবহেলার, সে গঞ্জনার ক্রোধ আজও বুকে দাউ দাউ করে জ্বলছে। অন্তত একজন যুদ্ধাপরাধীর বিচারের রায় কার্যকর হতে দেখে তারুণ্য উল্লসিত, সমগ্র দেশ উল্লসিত। অনেক অপেক্ষার পরে এর বিচার যা একসময় মনে হত স্বপ্নাতীত। হাতে দুর্লভ হীরকখণ্ড পাওয়ার মতো অবস্থা সবার।
দুর্লভ হীরকখণ্ডই বটে। কিন্তু কেন? এ বিচার তো অনেক আগেই প্রাপ্য ছিল। স্বাভাবিক মানবাধিকারের কারণে সহজাতভাবে এ বিচার হবার কথা ছিল। যে অপরাধ ছিল সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে তার বিচার করার কথা ছিল রাষ্ট্রের। এ তো কারও ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার হিসেব-নিকেশ নয়। আমার বাবা মারা গেছেন দেশের জন্য, তবে আমার কেন বিয়াল্লিশটি বছর চাইতে হল এ বিচার?
শুধু তাই নয় বিচার কেন করা উচিত তা নিয়ে আমাদেরকে অর্থাৎ শহীদ স্বজনদেরকে বারবার সকলের কাছে জবাবদিহি করতে হয়েছে। আমরা যারা অন্যায়ের শিকার আমাদেরকেই বারবার উত্তর দিতে হয়েছে কেন এত বড় একটি অন্যায়ের বিচার প্রয়োজন, কেন বিচার চাচ্ছি। শুধু তাই নয় এর উপরি পাওনা হিসেবে জুটেছিল টিটকারী, লঞ্চনা, গঞ্জনা। এগুলো সব অতীত ঘটনা। কেন অতীত নিয়ে টানাটানি করছি তার জন্য ব্যঙ্গ শুনতে হয়েছে। তারা ভুলে যেতে চেয়েছে যে, অন্যায় কখনও তামাদি হয় না। এটা আমার কথা নয়, এটা আইনের কথা।
যা ছিল আমাদের মৌলিক অধিকার তার জন্য এত কষ্ট কেন করতে হল, কেন দীর্ঘ সংগ্রাম, কেন এত অপেক্ষা, কেন এত অশ্রু? বিয়াল্লিশ বছর দীর্ঘ সময়। শহীদজায়া, মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা কয়জন জীবিত আছেন? কয়জন দেখে যেতে পারলেন? এতবড় হত্যাকাণ্ড, এত ধর্ষণ যা বিশ্ববাসীর সামনে সংগঠিত হল তাকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। তাকে অস্বীকার পর্যন্ত করার আস্পর্ধা দেখিয়েছে স্বাধীনতাবিরোধীরা। শুধু তাই নয়, শহীদদের হত্যাকারীদের গাড়িতে শহীদের রক্তমাখা পতাকা তুলে দিয়েছে এদেশের শাসকগোষ্ঠী। তাই বুকের ভিতরে আছে অনেক ক্ষোভ, অনেক অভিমান, অনেক বেদনা।
এ বিচার নিয়েও কত বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কত ‘কিন্তু’ ‘তবে’ জাতীয় পানি ঘোলা করার প্রচেষ্টা। শুধু রাজনৈতিক স্বার্থে কত বিরোধিতা। শুধু বিরোধীদের কাছ থেকে নয়, সরকারকে এমনকি আমাদের থেকেও কত প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। তাদের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আজ সরকার ও সরকারপ্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কথায় নয় কাজে প্রমাণ করে দিলেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে তাদের আন্তরিকতা। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁর কাছে।
কৃতজ্ঞতা জানাই বাঙালি জাতির কাছে। এদেশের প্রতিটি মানুষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, আমাদের দুঃখের সমব্যথী হয়েছেন। এক সময় দেশটি এমন ছিল, মনে হত আমরা শহীদস্বজনরা বোধহয় একা। কেউ স্বাধীনতা নিয়ে ভাবে না, যুদ্ধাপরাধের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয় না, আমাদের অবহেলা করে। আজ বুঝতে পারছি বাঙালি আসলেই বীর জাতি। সহজ-সরল বাঙালি সময়ের প্রয়োজনে সর্বদা মাথা উঁচু করেই দাঁড়িয়েছে। তারা তাদের ইতিহাস স্বীকার করে, শহীদদের সম্মান জানাতে পারে, বীরাঙ্গনাদের সম্ভ্রমহানির প্রতিশোধ নিতে জানে।
আজ কাদের মোল্লার ফাঁসির পরে তাই বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে সেই ধর্ষিত নারীর কথা যাকে কসাই কাদের নিজে ধর্ষণ করেছিল। তার সামনে তার মা ও বাবাকে হত্যার পরে বোনকে ধর্ষণ ও হত্যার পরে তাকেও সে হত্যা করে। আমাদের সেই বীরাঙ্গনা মা এত বছর পরেও সাহসের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে সেই অমানুষিক নির্যাতানের বর্ণনা দিয়েছেন ক্যামেরা ট্রায়ালে।
আজ বুকের রক্ত চোখের পানি হয়ে ঝরছে অঝোর ধারায় সেই বীরাঙ্গনা মায়ের জন্য। বার বার মনে হচ্ছে, আর কিছু না হোক এ স্বাধীন বাংলাদেশে অন্তত একজন বীরাঙ্গনা বেঁচে থেকে এই জীবনে দেখে যেতে পারলেন যে, তার প্রতি যে অত্যাচার করা হয়েছে, অন্যায় করা হয়েছে সেজন্য তার ধর্ষককে তার দেশ সর্বোচ্চ শাস্তি দিয়েছে।
মনে হচ্ছে দেশ নয়, জাতি নয়, শহীদস্বজন নয়, মুক্তিযোদ্ধা নয়– আমাদের এই বিজয় বীরাঙ্গনাদের জন্য। বীরাঙ্গনা মা, তোমরা দেখ, তোমাদের দেশ, তোমাদের সন্তানরা, তোমাদের আত্মত্যাগ ভুলে যায়নি। তোমাদের প্রতি কৃত অন্যায়ের বিচার তারা শুরু করেছে। এ বিজয় তোমাদের। আমাদের এ সংগ্রাম তোমাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন। মা তোমরা বেঁচে আছ, নাকি নেই জানি না। প্রকাশ্যে আছ, নাকি লুকিয়ে রেখেছ এ দুঃখগাথা। মা, তোমরা যে যেখানেই আছ, তাকিয়ে দেখ আজ তোমাদের সম্ভ্রমহানির প্রতিশোধ নিয়েছি আমরা।
মা, এবার শান্তিতে ঘুমাও, আমি কাঁদি। কাঁদি তোমার জন্য, কাঁদি আমার জন্য, এ অভাগা দেশের জন্য, এ বীর জাতির জন্য, এই দায়মুক্তির সুযোগের জন্য।
তারুণ্য আজ উল্লাস করছে, এটা তাদের বিজয়। এ বিজয়ের উল্লাসে আমিও উল্লসিত। আমিও হাসছি, অথচ দুচোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরে পড়ছে। অনন্য এক অনুভূতি। ’৭১-এর বিজয়ের অনুভূতি এমনই ছিল, যখন ১৬ ডিসেম্বর জাতি বিজয় লাভ করল ৩০ লাখ প্রাণের বিনিময়ে, ৪ লাখ নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে। আনন্দ-বেদনার এ কী অপূর্ব মিলন।
আজ কি বাতাসে অক্সিজেন একটু বেশি? বুকের ভিতর এত হালকা লাগছে কেন? কাঁধের উপর থেকে দায়বদ্ধতার বোঝো নেমে গেল কিছুটা। আহ, কী শান্তি। এত আবেগ আমি প্রকাশ করি কীভাবে? শব্দরাশির রাজ্যে শব্দ খুঁজে পাই না আজ আমার অশ্রুকে ব্যাখ্যা করার। কোনো শব্দই যেন যথেষ্ট বিশাল নয় আমার দীর্ঘশ্বাসের কথা বুঝিয়ে বলার জন্য। দীর্ঘ সংগ্রামের পরে এ বিজয়ের উল্লাসের যে তীব্রতা তাকে প্রকাশ করি কীভাবে? কী দিয়ে এ জাতির জয়গান করি? কী দিলে আমার কৃতজ্ঞচিত্তের আকুল নিবেদন আমি প্রতিটি মানুষকে বোঝাতে পারি যে, তোমাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। কোন শব্দে আছে সেই বিশালতা আর ব্যাপকতা?
যেন শুধু একটি শ্লোগানই এই বিচিত্র, বিশাল অনুভূতিকে ধারণ করতে পারে। তা আমার পিতার শ্লোগান, তা আমার দেশের শ্লোগান। উচ্চকণ্ঠে বার বার বলে উঠি– ‘জয় বাংলা’।
ডা. নুজহাত চৌধুরী: সহকারী অধ্যাপক, অপথালমোলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও শহীদ ডা. আলীম চেীধুরীর সন্তান।
http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/13752
- Biplob Rahman | ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ ১৩:২৮582670
- শওগাত আলী সাগর
মোল্লার ফাঁসি ও অনৈতিক ভূমিকায় নাভি পিল্লাই
ডিসেম্বর ১৩, ২০১৩
এক.
ঘটনাটা ২০১০ সালের। সেবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন চীনের লেখক ও মানবাধিকারকর্মী লিও সিয়াওবো। চীনের রাজনৈতিক সংস্কার এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতির পক্ষে আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে কারারুদ্ধ হন তিনি। কারারুদ্ধ অবস্থাতেই তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান।
ডিসেম্বরে যখন আনুষ্ঠানিকভাবে নোবেল বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়, তখনও লিও চীনের কারাগারে আটক। আর তাঁর স্ত্রী গৃহবন্দি। নোবেল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার নাভি পিল্লাইকে। মিজ পিল্লাই সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে অসম্মতি জানান। তাঁর পক্ষ থেকে অবশ্য তখন জানানো হয় যে, জাতিসংঘ ভবনে তাঁর মানবাধিকার বিষয়ক একটি কর্মসূচি পূর্বনির্ধারিত থাকায় তিনি নোবেল পুরষ্কার প্রদান অনুষ্ঠানে যেতে পারবেন না।
তাঁকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তাঁর পক্ষে বা জাতিসংঘের পক্ষে যে কোনো পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা যেন ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। অন্তত জাতিসংঘের কোনো একজন কর্মকর্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হয়েছিল বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষ থেকেও। কিন্তু নাভি পিল্লাই তাতেও সম্মতি দেননি। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁর বা জাতিসংঘের কোনো প্রতিনিধি ওই অনুষ্ঠানে যাবেন না।
কারারুদ্ধ একজন মানবাধিকারকর্মী, নোবেলের মতো আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত একটি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, আর জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ওই অনুষ্ঠানে নিজে তো যাবেন-ই না, তাঁর কোনো প্রতিনিধিকেও সেখানে যেতে দিবেন না, এ কেমন কথা!
জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষযক হাইকমিশনার কাদের মোল্রার ফাঁসি কার্যকর না করতে সরকারকে কার্যত চাপ দিতে চেয়েছেন
জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষযক হাইকমিশনার কাদের মোল্রার ফাঁসি কার্যকর না করতে সরকারকে কার্যত চাপ দিতে চেয়েছেন
লিও’র শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়া আর জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনের চীন সফরের ঘটনাটা ঘটেছিল কাকতালীয়ভাবে একই সময়ে। সদ্য নোবেল পুরস্কার পাওয়া একজন মানবাধিকারকর্মীর প্রতি জাতিসংঘের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব সহানুভূতিশীল হবেন– এমনটাই প্রত্যাশা করেছিলেন দেশ-বিদেশের মানবাধিকারকর্মীরা। বান কি মুনকে তাঁরা অনুরোধ জানান, চীনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি যেন লিও’র মুক্তির বিষয়টা তাঁর কাছে তুলে ধরেন। বান কি মুন সেই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। এমনকি নোবেল পুরস্কার বিজয়ের জন্য লিও-কে অভিনন্দন জানাতেও রাজি হননি তিনি।
চীনের নিপীড়িত মানুষের মানবাধিকার রক্ষায় লড়াই করতে গিয়ে একজন মানবাধিকারকর্মী যখন বিপন্ন, জাতিসংঘ কিংবা জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার তাঁর পাশে দাঁড়াতে সরাসরি অসম্মতি জানিয়েছেন! তাহলে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশন কাদের জন্য কাজ করে? যে নাভি পিল্লাই মানবতার বিরুদ্ধে পৈশাচিক অপরাধের দায়ে সর্বোচ্চ দণ্ডপ্রাপ্ত একজন অপরাধীর পক্ষে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে দেনদরবারে নেমেছেন, সেই ব্যক্তিই কিনা নোবেল পুরস্কার পাওয়া একজন মানবাধিকারকর্মীর পক্ষে দাঁড়াতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন!
দুই.
চলতি বছরের জুলাই কী আগস্ট মাসের ঘটনা। তামিল গেরিলাদের সঙ্গে চলমান দীর্ঘদিনের সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত শ্রীলঙ্কার মানবাধিকার পরিস্থিতি দেখতে সে দেশ সফরে যান নাভি পিল্লাই। তিনি কোথায় যাবেন, কী করবেন সবকিছুই জানানো হয় শ্রীলঙ্কা সরকারকে। কিন্তু একটি কর্মসূচি সম্পর্কে সরকারকে কিছুই জানানো হয়নি জাতিসংঘের স্থানীয় অফিস থেকে। শ্রীলঙ্কান সেনাবাহিনীর হাতে নিহত লিবারেশন টাইগার অব তামিল ইলম (এলটিটিই) সদস্যদের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর কর্মসূচি নেন তিনি। কলম্বো সরকারকে না জানালেও ঘটনাটা মিডিয়া ফাঁস করে দেয়। তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় পররাষ্ট্র এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। সরকার এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করে।
সরকারের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, নাভি পিল্লাই-র সফরকে শ্রীলঙ্কা সরকার স্বাগত জানাবে। কিন্তু নিহত তামিল গেরিলাদের সমাধিতে ফুল দেওয়ার মতো কোনো কর্মসূচি নেওয়া হলে তার পরিণাম হবে খুবই খারাপ। কিন্ত ভারতীয় তামিল বংশোদ্ভূত মিজ পিল্লাই তাঁর কর্মসূচিতে অটল থাকেন এবং তা চূড়ান্ত করার নির্দেশ দেন। শ্রীলঙ্কান সরকারও স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়, তিনি তাদের অনুমোদিত কর্মসূচির বাইরে কোনো কিছু নিতে চাইলে পুরো সফরটিই বাতিল করে দেওয়া হবে। বাধ্য হয়ে পিল্লাই তার কর্মসূচি বাদ দেন।
শ্রীলঙ্কায় অবস্থানকালেই মিজ পিল্লাই-এর তৎপরতা সমালোচনার মুখে পড়ে। কলম্বোর প্রায় সব ধরনের মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম, ব্লগ সর্বত্রই তাকে নিয়ে সমালোচনার ঝড় শুরু হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ফিরে যাওয়ার পথে সিঙ্গাপুরে তিনি সংবাদ সম্মেলন করে শ্রীলঙ্কান মিডিয়ার সমালোচনার জবাব দেন এবং নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন।
সফর শেষে ফিরে গিয়ে তিনি শ্রীলঙ্কার মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং সরকার সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করে বিবৃতি দেন। আর তাঁর এ বিবৃতির পর শ্রীলঙ্কান মিডিয়া তাকে আরেক দফা তুলোধুনা করে ছাড়ে।
তিন
গত বছরের ঘটনা। টিউশন ফি বাড়ানোকে কেন্দ্র করে কানাডার কুইবেকের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা লাগাতার বিক্ষোভ শুরু করে। এক পর্যায়ে কুইবেক প্রাদেশিক সরকার ছাত্র বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেয়। কুইবেকের ক্ষমতাসীন দল ‘ছাত্রদের কোনো ধরনের বিক্ষোভ আয়োজনের অন্তত ৮ ঘন্টা আগে কর্তৃপক্ষকে জানানো এবং বিক্ষোভের এলাকাসমূহ সম্পর্কে জানানোর নিয়ম বাধ্যতামূলক করে’ সংসদে একটি বিল উত্থাপন করে।
কুইবেক প্রাদেশিক সরকারের এই বিলটিতে সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল সবকটি রাজনৈতিক দলই সমর্থন করে। কিন্তু নাভি পিল্লাই জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বক্তৃতায় অভিযোগ করেন, কুইবেক জনসমাবেশ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করে দিচ্ছে। তিনি কুইবেককে কালো তালিকাভূক্ত করারও হুমকি দেন।
জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে নাভি পিল্লাই-র এই বক্তৃতার তীব্র প্রতিক্রিয়া হয় কানাডায়। কুইবেক প্রাদেশিক সরকার তো বটেই, ফেডারেল সরকার পর্যন্ত তাঁর বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করে। সেই সমালোচনায় যোগ দেয় কানাডার মিডিয়াও। শীর্ষস্থানীয় মিডিয়াগুলো অভিযোগ করে, নাভি পিল্লাই জাতিসংঘের মানবাধিকারের সংজ্ঞাকেই ‘টুইস্ট’ করছেন। কোনো কোনো পত্রিকা এমনও মন্তব্য করে যে তাঁর বর্ণাঢ্য পেশাদার জীবন থাকলেও, কানাডার সংবিধান এবং চার্টার অব রাইটস সম্পর্কে কোনো পড়াশুনা নেই। আর কোনো দেশের আইন কানুন সম্পর্কে না জেনে, পড়াশুনা না করে দায়িত্বশীল পদ থেকে কোনো ধরনের মন্তব্য করা সমীচীন নয় বলেও মন্তব্য করে সেদেশের মিডিয়া।
টরন্টো, মন্ট্রিয়লসহ কানাডার বড় বড় শহরে বিক্ষোভ বা সভা সমাবেশ করতে হলে অন্তত ৩০ ঘন্টা আগে লিখিতভাবে জানিয়ে অনুমোদন নিতে হয়। এমনকি জাতিসংঘের সামনে সমাবেশ করতেও ৩০ ঘন্টা আগে জানাতে হয়। সেখানে শিক্ষার্থীদের জন্য ৮ ঘন্টা আগে জানানোর নিয়মকেই মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন নাভি পিল্লাই।
চার
এশিয়ার দেশ শ্রীলঙ্কা কিংবা পশ্চিমের দেশ কানাডা– যেখানেই ভুল পথে পা রেখেছেন সেখানেই তীব্র সমালোচিত হয়েছেন জাতিসংঘের এই হাইকমিশনার। ব্যতিক্রম শুধু বাংলাদেশ। ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, রাজাকর-আলবদরদের নৃশংসতা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর কোনো ধারণা থাকবে না– সেটি বিশ্বাস করলে ভুল করা হবে। যুদ্ধাপরাধীদের চলমান বিচার সম্পর্কেও তাঁর ধারণা আছে বলেই আমরা মনে করি।
তবু তিনি শেষ মুহূর্তে বিবৃতি দিয়ে কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকর না করতে সরকারকে কার্যত চাপ দিয়েছেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, সেই চাপের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে যতটা প্রতিক্রিয়া হয়েছে, ক্ষোভ দেখা গেছে, মূলধারার মিডিয়াতে তার ছিটেফোঁটাও নেই। ঢাকার কোনো একটি মিডিয়া কি নাভি পিল্লাই-র বিবৃতির সমালোচনা করে সম্পাদকীয় লিখেছে? বিশিষ্টজনের প্রতিক্রিয়া্ নিয়ে কোনো প্রতিবেদন করেছে? কিংবা কোনো সংগঠন বিবৃতি দিয়ে বা কোনোভাবে তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে কি?
৯ ডিসেম্বর রাতে কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকরের উদ্যোগ নিয়েও অকস্মাৎ তা স্থগিত হয়ে যাওয়ায় পুরো দেশ যেভাবে ফুঁসে উঠেছিল, নাভি পিল্লাই-র বিবৃতির বিরুদ্ধেও সেভাবেই প্রতিবাদ হওয়ার কথা। কিন্তু সেটি হয়নি। এমনকি শ্রীলঙ্কার মিডিয়া যে কাজটি করতে পেরেছে, বাংলাদেশের মিডিয়া তার সামান্য কিছুও করতে পারেনি।
কানাডার অন্যতম প্রভাবশালী পত্রিকা ‘দ্য মেট্টোপলিটন’-এর কলামিস্ট ব্যারিল ওয়াজসম্যান একটি কলাম থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দিই–
“And what of Pillay herself? As Adrien Pouliot has pointed out, did she bother to talk about the Chinese repression of Tibet where a monk recently set himself on fire in protest? He was the thirtieth such suicide since 2009. Did she protest the jailing and torture of a Cuban dissident after he had testified in front of an American Senate Committee? Did she express concern over the 13 year prison sentence meted out to Iranian dissident leader Addolfattah Soltani? No! Her reaction, and that of the UN, has been total silence on China, on Iran, on North Korea on Zimbabwe, and the list goes on. But somehow Pillay found the time for Quebec.
Pillay is the perfect ethically bankrupt mouthpiece for a morally bankrupt organization.
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নে কেউ কোনো নেতিবাচক কথা বলতে এলে আমাদেরও এভাবেই রুখে দাঁড়ানো উচিত। সে ব্যক্তি জন কেরিই হোন আর জাতিসংঘের কোনো কেউকেটা হোন। কানাডার ‘দ্য মেট্টোপলিটন’ পত্রিকার মতো আসুন আমরাও উচ্চকণ্ঠে বলে দিই– ‘ইথিক্যালি ব্যাংকক্রাপ্ট’ মানুষের আর যাই হোক, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নে কোনো মন্তব্য করার অধিকার নেই।
শওগাত আলী সাগর: দৈনিক প্রথম আলোর সাবেক বিজনেস এডিটর, টরন্টো থেকে প্রকাশিত নতুনদেশ ডটকম এর প্রধান সম্পাদক।
http://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/13739
- Biplob Rahman | ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ ১৮:২৪582671
- Created on December 22, 2013 at 00:07
Pakistan should apologise for 1971
Tribune Editorial
For a real and lasting normalisation to occur, Pakistan’s leaders should go further than their foreign ministry’s statement
Pakistan’s failure to apologise for the atrocities of 1971, in spite of being asked to, is poor diplomacy and reflects their nationally instituted denial about the war. But the resolution that followed Quader Molla’s execution goes much further, and hints at a total lack of remorse.
By applauding East Pakistani loyalists who actively resisted liberation, the Pakistani Interior Minister effectively endorsed their actions during the war, which are war crimes by any other name.
He then suggested Bangladesh follow a policy of “forgive and forget” and display “magnanimity.”
It’s a bit absurd to expect Bangladesh to forgive when no forgiveness, by way of an apology, has ever been sought. Nor is it sound to say Bangladesh lacks magnanimity when we have maintained good relations with Pakistan even without the apology, and showed grace by forgoing reparations and releasing Pakistani officers after the war.
Pakistan’s foreign ministry statement that it is not its policy to interfere in the affairs of any other country is welcome as a return to diplomatic norms. However, given last week’s resolution, its clear that Bangladesh should not forgo the apology it is entitled to.
Many Pakistani commentators and individuals have remarked unfavourably on their parliament’s resolution. We believe that the debate on this resolution should be used as an opportunity to increase understanding of the shared history between the peoples of Bangladesh and Pakistan. It is in our countries’ mutual interest to build better relations and improve co-operation as partners within SAARC.
Equally while Bangladeshis should have every right to protest the controversial resolution, the sanctity and inviolability of Pakistan’s High Commission must be protected according to the law.
However for a real and lasting normalisation to occur, Pakistan’s leaders should go further than their foreign ministry’s statement and have an open debate on accountability for the 1971 war. This should include making a clear apology for crimes committed.
- See more at: http://www.dhakatribune.com/editorial/2013/dec/22/pakistan-should-apologise-1971#sthash.YQmMY6RD.dpuf
- Biplob Rahman | ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ ১৮:২৬582672
- Created on December 16, 2013 at 00:32
Looking forward on Victory Day
Tribune Editorial
We have cause for optimism. Over half the population is under the age of 24 and the vast majority were not yet born on the first Victory Day in 1971
On Victory Day 42 years ago, the nation was released from a great struggle.
Independence was achieved through the sacrifice and suffering of millions.
The brave men and women who fought for freedom justly deserve the nation’s thanks and solidarity today.
As we celebrate their memory and accomplishment, we can pause to reflect that Bangladeshis have achieved many successes in the past four decades.
Many challenges remain, however. The nation has its independence, but is not free of want or political strife.
The true potential of a free Bangladesh is not yet being achieved. The people have time and again shown much creativity, endurance and resilience in building the country. Think how much more could be accomplished if they were not held back by complacency, corruption and political dysfunction?
We must earn new victories each year over these seemingly intractable problems.
We have cause for optimism. Over half the population is under the age of 24 and the vast majority were not yet born on the first Victory Day in 1971.
It is these generations who will be taking the nation forward. It is they who can overcome past obstacles and reach forward for a better future. It is they who will make a better nation in the years ahead and make us all glad to be Bangladeshi.
- See more at: http://www.dhakatribune.com/editorial/2013/dec/16/looking-forward-victory-day#sthash.4Mr0IIoc.dpuf
- Biplob Rahman | ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ ১৮:২৭582673
- Created on December 14, 2013 at 00:36
Remembering our martyred intellectuals
Tribune Editorial
If we are to truly move forward and develop into the democracy we have dreamt of, we need to take our intellectuals’ ideals and teachings to heart, and practice them diligently
Today marks Martyred Intellectuals Day, when our brightest minds were kidnapped from their homes in the dead of night and shot dead, in an effort to cripple Bangladesh. This is a dark day in our nation’s history, and one we cannot afford to forget.
Throughout our liberation war, many intellectuals had been systematically dragged away and executed by Pakistani soldiers and their cohorts, but on this night 42 years ago, over 200 intellectuals were executed, marking a great blow to our nation’s intellectual development.
These academicians, artists, journalists, writers and lawyers were our nation’s conscience. They planted the seed of nationalism and democracy in the people’s minds, so that they became aware of their rights, and fought for those rights.
Our intellectuals were a beacon who showed us how to be citizens who would care for and work for our nation’s growth.
We have come far in these 42 years, and achieved much, but we have a long way to go. Our nation remains caught in a web of corruption and political violence, and, so far, the human rights of all Bangladeshis have not yet been acknowledged, at least not in practice.
If we are to truly move forward and develop into the democracy we have dreamt of, we need to take our intellectuals’ ideals and teachings to heart, and practice them diligently. We must not let their deaths be in vain.
- See more at: http://www.dhakatribune.com/editorial/2013/dec/14/remembering-our-martyred-intellectuals#sthash.KStu7mDS.dpuf
- Biplob Rahman | ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ ১৮:৩৪582675
- Victory Day Today
Minds without fear, heads held high
Syed Badrul Ahsan
The year 2013 is not the year 1971. The middle-aged citizen of today is no more the youth of yesterday. The freedom we enjoy in these times is far removed from the tortuous struggle we waged for liberty in those times.
And yet there is something called history that connects the dots and links the linear lines of matters generational. That is the reason why we remember 16 December 1971 in winter 2013.
History is forever a matter of remembering what has been. And forty two years ago, in this land, history took shape and form and substance, through reinventing itself on a declining December day. It was the winter of ecstasy for the people of Bangladesh, for they had just succeeded in beating back an enemy which should have had no business running riot through their hearths and homes. All across the streets and alleys of this city was heard a continuum of Joi Bangla, the militant nationalistic slogan which had over the years turned into an articulation of the collective Bengali demand for democratic rights. The demand had, to be sure, changed course through the exigencies of the times — from that of autonomy for a people long suppressed to that of freedom for a nation convinced that Bangladesh needed to be born if decency was to survive and thrive.
On the afternoon of December 16 four plus decades ago, it was freedom which stepped gingerly into our homes. Liberty, for long the stuff that dreams were made of, was suddenly and yet expectedly ours to savour. The ‘brave’ soldiers of the marauding Pakistan army, having put an end to the lives of three million Bengalis and dishonoured as many as two hundred thousand Bengali women, had finally caved in. Note that there were 93,000 of them, all men who had been taught to believe that the Bengali did not matter, that indeed it was ‘East Pakistan’ which had to be reclaimed, that nothing else was. The dramatic nature of the Bengali victory was as compelling as it was inevitable, for only days before his men bit the dust, General Amir Abdullah Khan Niazi had served the eerie warning that Dhaka would be taken over his live body. It was a living, breathing Niazi who had just capitulated before the rolling bandwagon of the nationalistic Bengali spirit.
Forty two years on, it is time to reflect on what was. On 16 December 1971, it was a cheerful rendering of ‘aaj srishti shukher ullaashe’ wafting along, per courtesy of a newly reopened and rejuvenated Dhaka Radio. The joy of creation was all, as was the painful happiness of a return home. Abdul Jabbar, having with so many others kept the spirit of triumph alive in the months preceding the end of the war, now sang ‘hajar bochhor pore abar eshechhi phire . . . Bangla’r buuke achhi darhiye’. In a few days, the Mujibnagar government would be coming home from exile. Within weeks, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman — father of the nation, liberator, our friend and our window to the world — would be back in our midst. There would be a constitution within a year, with a general election to follow. The secular, sovereign Bengali state, fashioned out of the crucible of a twilight struggle, would be on the road to a consolidation of life and liberty.
The rest is, surely, history. Forks in the road would take us down paths we did not need to take. And foul conspiracy would stand triumphant, through a wholesale murder of the men who had steered the nation to freedom. The brave soldiers who would not rest until liberty was at hand would disappear, one after the other, in the land they had caused to be born. These are realities that ought not to have been. This is history which fundamentally owes its reality to the elemental nature of those who have never tolerated the rise of truth. Anti-history was around, right from the moment of our rebirth as a proud, free nation. Precious years were lost through democratic politics being pushed into exile and unconstitutional rule taking over. Bangabandhu enlightened us, even as the euphoria of freedom kept us in thrall, on how Bangladesh could graduate to being the Switzerland of the east. Those who came after him, in predatory fashion, simply jostled us back into the dark.
It was not, as Humayun Azad was to proclaim loudly, the Bangladesh we had bargained for back in the terrifying as also terrific months of the war. Our collective imagination and objective reality, as we serenaded a liberated land, did not envision an ambience of untruth, a political canvas where coups d’etat and a rapid decline in values would undermine our ethos before a horrified world. Bloodletting had never been our prediction; and yet blood streamed into the lives of people who had not forgotten the blood shed by their compatriots in all the years leading up to the arrival of liberty. A free nation does not relish the spectacle of blood. And yet blood has flowed.
Forty two years on, there is that compulsion in the heart, that tug at the soul, for new promises to be made in the interest of generations of Bengalis to be. Those promises come touched with necessary emotion. Now that we are forty two, it is time to restore the ideals we have lost along the way. Our democracy must be made stronger, through a strengthening of the institutions which underpin governance. Our political classes must inform themselves that politics is never combative or adversarial but is always cooperative; that Parliament, being the fountainhead of freedom and justice, ought not to be spurned by those elected to be part of it. Having arrived at adulthood that ought to be of a mature sort, we cannot afford to go on playing young any longer. Good governance is now the aspiration; and visionary politics is what defines the future.
As dawn breaks today, with memories as profound as they are painful, with the wheels of justice finally turning — to inform ageing agents of the Pakistan army that they must finally pay for their sins — this nation proudly recalls those who paved the way to freedom forty two years ago. Their minds were without fear. Their heads were held high. And we celebrate liberty in a Tagorean heaven of freedom.
http://www.thedailystar.net/minds-without-fear-heads-held-high-2634#.Ur15qtIW1GY
- Biplob Rahman | ০১ জানুয়ারি ২০১৪ ১৫:৫৮582676
- আ লো চি ত পাঁ চ জা তী য় ঘ ট না ২ ০ ১ ৩
শাহবাগে বাংলাদেশের গণজাগরণ
আপডেট: ০০:১৭, জানুয়ারী ০১, ২০১৪ | প্রিন্ট সংস্করণ
মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার ও অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে সংগঠিত এবং ঢাকার শাহবাগ চত্বরে সূচিত তরুণ প্রজন্মের এক আন্দোলন ২০১৩ সালের অধিকাংশ সময়জুড়ে দেশি-বিদেশি সংবাদমাধ্যমে আলোচিত হয়।
গত ৫ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল কাদের মোল্লার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় ঘোষিত হলে তার প্রতিবাদে বিকেলেই ‘বাংলাদেশ অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট নেটওয়ার্ক’ (বোয়ান) নামের একটি সংগঠনের ব্যানারে এবং কিছু সচেতন মানুষ শাহবাগের জাদুঘরের সামনে জড়ো হন। সন্ধ্যার পর থেকে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শাহবাগ চত্বরে প্রতিবাদী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত জমায়েত বাড়তে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীরাও যোগ দেন। সবার দাবি, কাদের মোল্লাসহ সব যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসি চাই।
বিক্ষোভকারীরা শাহবাগ চত্বরে অবিরাম অবস্থান করতে থাকেন। তাঁদের মনে একটি সংশয় ছিল যে কাদের মোল্লার সর্বোচ্চ শাস্তি না হওয়ার পেছনে সরকারের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর গোপন বোঝাপড়া কাজ করে থাকতে পারে। ৮ ফেব্রুয়ারি ডাকা হয় প্রথম মহাসমাবেশ। সেখানে কাদের মোল্লাসহ সব যুদ্ধাপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি পুনরুচ্চাতি হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে তিন মিনিটের নীরবতা কর্মসূচি পালিত হয় শাহবাগে। ১৫ ফেব্রুয়ারি দাবি তোলা হয় জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধ করার।
ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত শাহবাগে অবিরাম অবস্থান চলে। এই আন্দোলনের ফলে যুদ্ধাপরাধের বিচারের পক্ষে বিপুল জনমত সঞ্চারিত হয়। আন্দোলনকারীদের চাপের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইন সংশোধন করে রায়ের বিরুদ্ধে বাদীপক্ষের আপিল করার বিধান করা হয়। সংশোধিত আইনটি ফেব্রুয়ারি মাসেই সংসদে পাস হলে মার্চের প্রথম সপ্তাহে রাষ্ট্রপক্ষ কাদের মোল্লার সর্বোচ্চ শাস্তি চেয়ে আপিল করে।
শাহবাগ আন্দোলনের প্রতি বিএনপি প্রথম দিকে সমর্থন জানালেও পরে এটিকে সরকারদলীয় আন্দোলন আখ্যা দেয়। জামায়াত গোড়া থেকেই এর বিরোধিতা করে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের তরুণ প্রজন্মের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আবেগের প্রবল বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং তা সমাজের বৃহত্তর অংশকেও বেশ আলোড়িত করে। একপর্যায়ে শাহবাগ চত্বরে বিপুলসংখ্যক মানুষের সপরিবারে উপস্থিতি লক্ষ করা যায়; নারী ও শিশুদের উপস্থিতিও ছিল ব্যাপক। আন্দোলন ছিল শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল; গানে, কবিতায়, স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত। এই আন্দোলনের ফলে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার-প্রক্রিয়াকে আরও বেগবান করার পক্ষে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি হয় এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যালে একের পর এক মামলার রায় ঘোষিত হতে থাকে। কাদের মোল্লার রায়ের পর ট্রাইবুন্যাল আরও সাতটি মামলার রায় ঘোষণা করেন।
l শরিফুল হাসান
http://www.prothom-alo.com/special_supplement/article/112405/%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87_%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%A3
- Biplob Rahman | ০১ জানুয়ারি ২০১৪ ১৫:৫৯582677
- মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার: ১২ মাসে ৯টি রায়
আপডেট: ০০:১৬, জানুয়ারী ০১, ২০১৪ | প্রিন্ট সংস্করণ
৪৩তম বিজয় দিবসের প্রাক্কালে গত ১৫ ডিসেম্বর রাত ১০টা এক মিনিটে আবদুল কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকর করা হয়। মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার-প্রক্রিয়ায় এটি প্রথম কার্যকর হওয়া দণ্ড।
২০১৩ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মানুষ চার দশকের বিচারহীনতা থেকে মুক্তির দিন হিসেবে মনে রাখবে। সেই সঙ্গে ইতিহাসের পাতায় দিনটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের নাম। একাত্তরে নৃশংসতার জন্য কসাই কাদের নামে পরিচিতি পাওয়া কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হলে তরুণ প্রজন্ম বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। তাদের আন্দোলনের চাপে দুই পক্ষকে আপিলের সমান সুযোগ দিয়ে আইন সংশোধন করা হয়, তারপর সর্বোচ্চ আদালতে আপিল এবং সেখানে ফাঁসির রায়।
একাত্তরে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার করার লক্ষ্যে গঠিত দুটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ২০১৩ সালজুড়ে মোট নয়টি রায় ঘোষিত হয়েছে। ২১ জানুয়ারি জামায়াতের সাবেক সদস্য পলাতক আবুল কালাম আযাদকে মৃত্যুদণ্ড দেন ট্রাইব্যুনাল-২। ৫ ফেব্রুয়ারি কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন ট্রাইব্যুনাল-২, আর ২৮ ফেব্রুয়ারি জামায়াতের নায়েবে আমির দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে মৃত্যুদণ্ড দেন ট্রাইব্যুনাল-১। সাঈদীর রায় ঘোষণার পর সহিংস হয়ে ওঠে জামায়াত, এক সপ্তাহের সহিংসতায় সারা দেশে ৭৭ জন প্রাণ হারান।
গত ৯ মে ট্রাইব্যুনাল-২ জামায়াতের আরেক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামানকে মৃত্যুদণ্ড দেন। জুলাই মাসে এক দিনের ব্যবধানে দুটি রায় হয়। মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য অপরাধ করেও বয়সের কারণে ৯০ বছরের কারাদণ্ডের সাজা পান জামায়াতের সাবেক আমির গোলাম আযম। গত ১৫ জুলাই ট্রাইব্যুনাল-১-এর এই রায়ের এক দিন পর ১৭ জুলাই জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেন ট্রাইব্যুনাল-২। গত ১ অক্টোবর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাংসদ সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে ফাঁসির আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল-১। ৯ অক্টোবর ট্রাইব্যুনাল-২ সাবেক মন্ত্রী ও বিএনপির নেতা আবদুল আলীমকে আমৃত্যু কারাদণ্ডের আদেশ দেন। অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় তিনিও মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য হলেও শারীরিক অসুস্থতা বিবেচনায় তিনি আমৃত্যু কারাদণ্ডের সাজা পান।
গত ৩ নভেম্বর ট্রাইব্যুনাল-২ যুক্তরাজ্যপ্রবাসী চৌধুরী মুঈনুদ্দীন ও যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী আশরাফুজ্জামান চৌধুরীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন। আলবদর নেতা হিসেবে পরিচিত এই দুজনের দণ্ড হয় বুদ্ধিজীবীদের পরিকল্পিতভাবে হত্যার দায়ে। বিচার-প্রক্রিয়ার পুরো সময় তাঁরা উভয়ে আদালতে অনুপস্থিতি ছিলেন।
পলাতক আযাদ ও মুঈনুদ্দীন-আশরাফুজ্জামান ছাড়া দুই ট্রাইব্যুনালে সাজাপ্রাপ্ত প্রত্যেকেই সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করেছেন। এর মধ্যে শুধু কাদের মোল্লার আপিল নিষ্পত্তি শেষে সাজা কার্যকর হয়েছে। ছয়জনের আপিল এখনো বিচারাধীন।
বিচার-প্রক্রিয়ার গুণগত মান নিয়ে দেশে ও বিদেশে নানা প্রশ্ন ওঠে; বিশেষত স্কাইপ কেলেংকারির ফলে বিচার-প্রক্রিয়ায় সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগ ওঠে।
কুন্তল রায়
http://www.prothom-alo.com/special_supplement/article/112402/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%80_%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A7%A7%E0%A7%A8_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%87_%E0%A7%AF%E0%A6%9F%E0%A6%BF_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F
- Biplob Rahman | ০১ জানুয়ারি ২০১৪ ১৬:১৩582678
- মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম, একজন এনায়েত মওলা ও ’কাকলী’ নামের বাড়িটি
আলম খোরশেদ | ২৬ december ২০১৩ ১২:৩২ পূর্বাহ্ন
মহান মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের গৌরবময় ভূমিকার কথা সবারই কমবেশি জানা। কিন্তু এই যুদ্ধে বেসামরিক জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও অপরিমেয় অবদানের সঠিক মূল্যায়নটি আজো ঠিক সেইভাবে করা হয়নি। অখ্যাত অনেক সাধারণ মানুষের অজস্র বীরত্বগাথা ও আত্মত্যাগের কথা চাপা পড়ে গেছে আমাদের নির্মম উপেক্ষা ও উদাসীনতার বলি হয়ে। সেই দীর্ঘ উদাসীনতার ধুলো সরিয়ে মুক্তিযুদ্ধের এক অবিশ্বাস্য, প্রায় মহাকাব্যিক আখ্যানের বয়ান উপস্থাপনের জন্যই এই নাতিদীর্ঘ নিবন্ধের অবতারণা, যার কেন্দ্রে রয়েছে এই চট্টগ্রামেরই একজন অসমসাহসী, নিভৃতচারী, প্রচারবিমুখ মানুষ ও তাঁর ’কাকলী’ নামের বাড়িটি।
অকুতোভয় এই মানুষটির নাম এনায়েত মওলা (জন্ম. ১৯২৯)। দেশভাগের পর তিনি ভারত থেকে ঢাকায় এসে প্রথমে রেডিয়ো পাকিস্তানে এবং পরে চট্টগ্রামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসাবে যোগদান করেন। ক্রমান্বয়ে স্থায়ী বসতি গড়ার লক্ষ্যে একটি বাড়িও নির্মাণ করেন নাসিরাবাদ অঞ্চলে, বর্তমান জিইসি মোড়ের কাছাকাছি, নাম রাখেন তার ’কাকলী’। সেই উত্তাল, উদ্বেল নয় মাসে চট্টগ্রাম শহরের মুক্তিযুদ্ধের একটি ছোটখাটো, প্রায় অঘোষিত নিয়ন্ত্রণকক্ষের ভূমিকা পালন-করা এই বাড়িটিকে ঘিরে সংঘটিত হয় নানা নাটকীয় আর রুদ্ধশ্বাস ঘটনা-পরম্পরা। সেইসব গায়ে কাঁটা দেয়া, রোমাঞ্চকর ঘটনাপুঞ্জের বিশ্বস্ত ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দেন এনায়েত মওলা তাঁর লেখা ’মুক্তিযুদ্ধের ভিন্ন ছবি: চট্টগ্রামের কাকলী’ নামক মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থটিতে। সাহিত্যপ্রকাশ থেকে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত এই ক্ষীণতনু গ্রন্থপাঠে আমরা ফিরে যাই মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন শহর চট্টগ্রামের দমবন্ধকরা, বারুদের গন্ধে ভরা এক অধিকৃত ভূখণ্ডে, যেখানে তখন এক বীর সেনানীর নেতৃত্বে প্রাণ বাজি রেখে যুদ্ধ করে চলেছে একদল টগবগে তরুণ, দেশমাতৃকার মুক্তির লক্ষ্যে।
এনায়েত মওলা যে খুব সজ্ঞানে ও সচেতন সিদ্ধান্তে এই যুদ্ধে যুক্ত হয়েছিলেন তা কিন্তু নয়, বরং বলা চলে অনেকটা ঘটনাচক্রেই তিনি এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সখের শিকারী, সেই সুবাদে বন্দুকচালনায় বিশেষ পারঙ্গম। একদিন ক’টি তরুণ, কোত্থেকে কিছু বন্দুক যোগাড় করে তাঁর বাড়িতে এসে হাজির। বন্দুকগুলো চালাতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়ে তারা কার কাছ থেকে যেন খবর পেয়ে এই সৌখিন শিকারীর কাছে ছুটে এসেছিল বন্দুক চালানো বিষয়ে জ্ঞান নিতে। তিনি যখন দেখলেন যে তারা নিতান্তই আনাড়ি অথচ দেশের জন্য যুদ্ধ করতে এক পায়ে খাড়া, তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তাদেরকে হাতে ধরে, যত্ন করে বন্দুক চালনা শিক্ষা দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেবেন। যেমন ভাবা তেমন কাজ। তিনি তার পাড়ার গুরুজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে বর্তমান জাকির হোসেন রোডের পাশ্ববর্তী পাহাড়ে, এবং পরবর্তী সময়ে শহরের অদূববর্তী কুমিরার দুর্গম অরণ্যে, নিয়ম করে তাদের অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিতে শুরু করেন। এনায়েত মওলার লেখা থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, সেইসময় তরুণদের দেখাদেখি এলাকার বেশ কিছু নারীও অস্ত্রশিক্ষায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি তাদেরকেও নিরাশ করেননি।
এভাবে তরুণ যোদ্ধাদের অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে তিনি নিজেই এই ন্যায়যুদ্ধের সঙ্গে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেলেন দেহে ও মনে। মুক্তিকামী বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্নখানি তাঁর চেতনাতেও ঢেউ তুললো প্রবল আবেগে। এরই ধারাবাহিকতায় তাঁর বসতবাড়িটি হয়ে ওঠে একাধারে একটি ছোটখাটো অস্ত্রাগার, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্থায়ী ক্যাম্প ও যুদ্ধ পরিচালনার মূল মন্ত্রণাকক্ষ বিশেষ। এর জন্য অবশ্য তাঁকে কম মূল্য দিতে হয়নি। নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ চালাতে গিয়ে আর্থিক ক্লেশ স্বীকারের পাশাপাশি শারীরিক-মানসিক যন্ত্রণাভোগ, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতার বেদনা, এমনকি পদে পদে মৃত্যুঝুঁকি নিয়ে পথ চলা কোন কিছুই অবশ্য দমাতে পারেনি তাঁকে। একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছে তাঁর এই বাড়ি, নির্মম হত্যাকাণ্ডও ঘটেছে তাঁর চোখের সামনে, তারপরও অদম্য প্রাণশক্তিতে চালিয়ে গেছেন তিনি তাঁর এই ব্যক্তিগত মুক্তিযুদ্ধ।
চট্টগ্রামের মুক্তিযুদ্ধের অদ্যাবধি অজ্ঞাত, অসংখ্য অবিশ্বাস্য ঘটনাবলির বর্ণনায় পূর্ণ এই অভূতপূর্ব গ্রন্থটি থেকে অন্তত একটি নাটকীয় আখ্যানের উল্লেখ না করা হলে তার প্রতি অবিচার করা হবে। চট্টগ্রামের মুক্তিযুদ্ধের খোঁজখবর যারা রাখেন তাদের কাছে চট্টগ্রাম বন্দরকে অচল করে দেয়ার লক্ষ্যে সংঘটিত অপারেশন জ্যাকপট-এর কথা অজানা থাকার কথা নয়। তবে ফ্রান্স প্রত্যাগত ক’জন বাঙালি নৌকমান্ডো দ্বারা পরিচালিত সেই বীরোচিত অভিযান পরিকল্পনায় যে খোদ একজন পাকিস্তানী নৌসেনার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই কথাটি সম্ভবত খুব কম লোকেরই জানা। বাঙালিপ্রেমী সেই বীর যোদ্ধার নাম লেঃ কমান্ডার আনোয়ার। তিনি ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তান নৌবাহিনীর একজন ঊর্ধতন কর্মকর্তা। কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দরে সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের সময় নির্বিচারে শ্রমিকহত্যা এবং পরে দামপাড়া অঞ্চলে নির্মমভাবে অসংখ্য বাঙালি নৌসেনার হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে তিনি বিবেকের তাড়নায় পাকিস্তানী পক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেন এবং প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি এনায়েত মওলার সংস্পর্শে এসে নৌকমান্ডোদের দ্বারা চট্টগ্রাম বন্দরে সেই ঐতিহাসিক অপারেশন চালানোর কাজে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রাখেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অবশ্য তাঁকে যুদ্ধপরবর্তী নৈরাজ্যময় পরিবেশে প্রতিহিংসার কোপানল থেকে বাঁচার জন্য অশ্রুসজল চোখে দেশত্যাগ করতে হয়। বেশ কয়েক বছর পরে প্রায় একই পরিণতি বরণ করতে হয় এই গ্রন্থের লেখক খোদ এনায়েত মওলাকেও। তিনিও অর্থকষ্টে পড়ে মুক্তিযুদ্ধের সেই সুবর্ণ স্মারক ’কাকলী’ নামের বাড়িটি অবশেষে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন এবং নানাবিধ সামাজিক-রাজনৈতিক বিরুদ্ধতার মুখে দেশত্যাগ করে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান।
তবে আজন্ম লড়াকু চরিত্রের এই নিখাঁদ দেশপ্রেমিক মানুষটি অবশ্য সেখানেও একেবারে হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি। প্রবাসে বেড়ে ওঠা ইতিহাসবিমুখ প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের গৌরবময় জন্মগাথাকে তুলে ধরতে এবং তাদের মনে দেশপ্রেমের অনুরণন জাগিয়ে তুলতে তাঁর এই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি গল্প বলার ভঙ্গিতে, খুবই সুখপাঠ্য ইংরেজিতে রচনা করেন আরো একটি অসাধারণ গ্রন্থ, The Birth of a Nation। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার সুমহান যজ্ঞের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই বীরযোদ্ধা এনায়েত মওলা-কে তাঁর প্রাপ্য যথাযথ স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদান এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সেই ঐতিহাসিক বাড়িটিকে সংরক্ষণ করার মাধ্যমেই কেবল তাঁর কাছে আমাদের অপরিমেয় ঋণভার কিছুটা হলেও লাঘব হতে পারে।
http://arts.bdnews24.com/?p=5571#more-5571
- Biplob Rahman | ০১ জানুয়ারি ২০১৪ ১৬:১৭582679
- বীরের ভঙ্গি:ক্যাম্প জীবনের গল্প
কায়সার হক | ১৫ december ২০১৩ ১১:৫৬ অপরাহ্ন
বলা চলে যুদ্ধের সময় ঘটনাচক্রে আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অফিসার হিসেবে যোগ দেই। ১৯৭১ সালের মে মাসের শেষের দিকে আমি আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা হই। অসাধারণ এক ট্রেন ভ্রমন শেষে কলকাতা পৌঁছে কয়েকজন ঢাকার বন্ধুর দেখা পেয়ে যায় সেখানে। ওরা সেক্টর ৭-এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে জেনে ওদের সঙ্গেই সেখানেই যাব মনস্থির করি। জুনের শুরুর দিকে একদিন সকালে ভারতের পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ সদরদপ্তরে গিয়ে শুনি যে সেই সন্ধ্যাতেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অফিসার পদের নিয়োগপরীক্ষা হবে সেখানে। নির্বাচিত ক্যাডেটরা প্রশিক্ষণ শেষে নিয়োগপ্রাপ্ত সেনা হিসেবে যুদ্ধে যোগ দেবে।
আমার বন্ধুদের সাথে আমার তর্ক শুরু হলো এ সুযোগ আমাদের নেয়া উচিৎ কিনা সেটা নিয়ে। কেই-বা পেশাদার সৈন্য হতে চায়? শেষমেষ আমরা ইন্টারভিউ দেয়া মনস্থির করি। লে কর্ণেল নুরুজ্জামান আমাদের আশ্বস্ত করেন যে যুদ্ধ শেষ হলেই আমরা দায়িত্ব থেকে ছাড় পাবো। দেখা গেলো, তিনিই বোর্ডের শীর্ষ ব্যক্তি এবং আমাকে সব প্রশ্ন তিনিই করছিলেন। আমার বুদ্ধি যাচাই করার জন্য কিছু প্রশ্ন করেই তিনি আমার কাছ থেকে বার্টান্ড রাসেল আর লিয়ার প্যারাডোক্স শুনলেন আর শুনলেন সার্ত্রের টিকে থাকার মূলসুত্র।
নির্বাচিত হয়েছি কিনা জানা যাবে কিছুদিন পর। ততদিন সেক্টর কমান্ডারের বাংলোর একটা রুমে আমদের থাকার অনুমতি দেয়া হলো। কিন্তু সেক্টর সদরদপ্তর সেখান থেকে সরে যাবে, সেজন্য আমরা পাশের একটা ইয়ুথ ক্যাম্পে অবস্থান নেয়।
এ ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা প্রায়- তরুণ এই দুজন ব্যক্তি শিক্ষিত মানুষের সঙ্গ পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। আমরা তাই বিশেষ অতিথির মর্যাদায় বড় একটা রুমে জায়গা পেয়ে যাই যার পুরোটাই কেবল আমাদের থাকার জন্যই বরাদ্দ। পরদিন সকালে অনুশীলনের শব্দে ঘুম ভাঙ্গে আমাদের। তারপর ধীরে-সুস্থে সকালের নাস্তা। এ ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা দু’জনের একজন যৌনতা বিষয়ে অপার জ্ঞানী। আর আমরা চাই বা না চাই আমাদের সেসব শুনিয়েই যাচ্ছিলেন। তারপরই ঠিক একই রকম বিজ্ঞের ভঙ্গীতে শুরু করলেন হ্যারল্ড রবীন’স আওড়ানো আর নারী আকর্ষনের বর্ণনা। আমাদের দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ালো বিদ্ঘুটে এক অভিজ্ঞতা।
এদিকে দেশে গেরিলা যুদ্ধ চলছে। মুক্তিবাহিনীর একজন অফিসারের কথা শুনলাম যিনি তাঁর অপরিসীম দক্ষতা আর সাংঘাতিক রণকৌশলের জন্য জীবন্ত কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন। লে: ইদ্রিস খান পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় বাঙালিদের সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করায় তার একজন উর্ধ্বতনকে আঘাত করেছিলেন। সেই অপরাধে তাকে সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। যুদ্ধ যখন শুরু হয় তিনি তখন জয়পুর চিনি কলে ইজ্ঞিনিয়ার হিসেবে কাজ করতেন। সেই সময় তিনি কয়েকজন যুবককে সাথে নিয়ে অস্ত্র যোগাড় করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এক যুদ্ধ শেষে জয়পুরহাটে ফেরত আসার সময় তিনি জানতে পারেন যে পাকিস্তানি সৈন্য জয়পুরহাটে ঢুকে পড়েছে। তখনই তিনি তার লোকদের সাথে নিয়ে সীমান্তের কাছাকাছি আশ্রয় নেন এবং সেখান থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকেন। নিজের পরিবার থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ছিলেন তিনি। প্রায় এক মাসেরও বেশি সময় পর, এক শরনার্থী শিবিরে তিনি তার পরিবারের লোকজনদের আবিষ্কার করেন। এক সকালে আমরা লে: ইদ্রিসের ক্যাম্পের দিকে রওনা হই। ক্যাম্পে আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা জানান তিনি। তখন তিনি বাংলাদেশের ভিতরে যাওয়ার ব্যাপারে একটা বিশৃঙ্খল দলকে প্রস্তুত করছিলেন। ছোটখাট হলেও মানুষটি শক্তপোক্ত গড়নের। তিনি তার লোকদের কঠিন পরিস্থিতিতেও খুব সাধারণ যুদ্ধকৌশল দিয়ে শত্রুদের প্রায়ই হতচকিত করে দিতেন। একবার তার কানে আসলো যে এক কুখ্যাত ডাকাত, পাকিস্তানি দোসর তার সম্পর্কে খুব খারাপ কোন একটা মন্তব্য করেছে। তিনি তার দলবল নিয়ে সাধারণ গ্রামবাসীর ছদ্মবেশে সরাসরি সেই ডাকাতের আস্তানায় হাজির হন আর সেই বিশ্বাসঘাতকের গালে এমন এক চড় মারলেন যে মরার সময়েও সে স্বীকার করলো যে এত জোরে চড় সে জীবনে আর কখনো খায়নি।
ইন্টারভিউর প্রায় দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেলো, অথচ তখনো কোন খবর আসছিলো না। আমরা তাই ঠিক করলাম কলকাতা গিয়ে কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের চলে যাবার সিদ্ধান্তে ইয়ুথ ক্যাম্পের কর্তা দুজন মুষড়ে পড়লেন। তবে পথের খরচ হিসেবে ক্যাম্পের ফান্ড থেকে আমাদের প্রত্যেকের হাতে ১০০রুপি করে দেয়া হয়। সেখান থেকে আমরা ৮নং থিয়েটার রোডের (সেক্সপিয়ার সরণী) নির্বাসিত বাংলাদেশ সরকারের দপ্তরে গিয়ে শেখ কামালের সাথে দেখা করি। আনন্দের সাথে আবিষ্কার করলাম যে শেখ কামালের সাথে সাথে আমার আর দিপু’র (কাইয়ুম খান) নামও নির্বাচিতের তালিকায় আছে। অলীক গুপ্ত নামে দক্ষিণপশ্চিম প্রান্তের আরেকজনকেও সেখানে দেখলাম। আমাদের চারজনকেই তক্ষুণি সেনাবাহিনীর হাসপাতালে পাঠানো হলো প্রয়োজনীয় পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য। তারপর সেখান থেকে সোজা প্রশিক্ষণ স্কুল। যদি ইয়ুথ ক্যাম্পে বসেই আরো কিছু অশ্লীল গল্প শুনতে থাকতাম তাহলে পুরো সুযোগটাই আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যেত।
মেডিকেল চেকআপ শেষে রেলষ্টেশনে যাবার পথে ভয়াবহ এক দুর্ঘটনার সাক্ষী হয়েছিলাম। গাড়ি চাপায় মৃত একটা শিশু পথের উপর এমনভাবে পড়েছিল যেন সে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে। কেবল তার মাথার খুলিটা বিচ্ছিন্ন হয়ে বাটির মতো উল্টে পড়ে আছে।
শিলিগুড়ির ট্রেন ধরে তারপর অন্য এক রেললাইন দিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম নিউ মাল নামের পাহাড়ঘেঁষা ছোট্ট এক ষ্টেশনে। সেই প্লাটফর্মে নামতেই দেখা হয়ে গেল কিছু পরিচিত মানুষের সাথে - সামাদ ভাই, যিনি সেন্ট গ্রেগরিতে আমার দুই ব্যাচ সিনিয়র ছিলেন, আর ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের দু’বছর সময়ের মধ্যে জোগাড় হয়ে যাওয়া বন্ধুদের হাফ ডজন। সেখান থেকে ভারতীয় সেনা ট্রাকে করে পাহাড়ি পথ বেয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম মুরতিতে। এই সেনা ক্যাম্পে মুক্তিফৌজের জন্য বসানো হয়েছিলো প্রশিক্ষণ ক্যাম্প। শতশত গেরিলা যোদ্ধা তখন সেখানে প্রশিক্ষন নিচ্ছিল। দুই সপ্তাহের নিবিড় প্রশিক্ষণ শেষে তাদের পাঠানো হবে নিজনিজ সেক্টরে। আমাদের অফিসারদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প একদম শেষে, আমি যেমন কল্পনা করেছিলাম তার থেকে একদম আলাদা। সেখানকার বাঁশের কিছু ছাউনিই আমাদের ৬১ জনের পরবর্তী ১৫ সপ্তাহের আবাস। আমাদের সাথে পরবর্তীকালে পাকিস্তানি মিলিটারি একাডেমি থেকে আসা আরো তিনজন যোগ দিয়েছিল।
আমাদের জন্য বরাদ্দ হলো বিছানা, পুরোনো ডিজাইনের সস্তার সুতি পোশাক যার কেবল অর্ধেকটাতে বোতাম আছে, নিজের দিকটা ঢেউ খেলানো, দু’পাশে কুর্তার মতো পকেট, আর সেই সাথে ঢোলাঢালা লম্বা ধরনের সর্ট প্যান্ট। আলো নিভে গেলে আমরা খালি সিমেন্টের মেঝেতে আমাদের বিছানা পেতে হ্যারিকেনের আলো নিভিয়ে বাচ্চাদের মতো ঘুমিয়ে পড়তাম সেখানেই। একসময় খাকি পোশাক বদলে আমরা স্বাভাবিক পোশাক পরা শুরু করলাম। আমাদের অবস্থার উন্নতির অংশ হিসেবে আমাদের জন্য বাঁশের খাট বরাদ্দ হলো যেটার সরু কঞ্চি গায়ে ফুটতো।
এখানে আমাদের সকাল শুরু হয় অর্ধেক মগ দুধ-মিষ্টি দেয়া চা-এর জন্য লাইন ধরে। তারপর বিয়ারের ক্যান দিয়ে ড্রাম থেকে পানি নিয়ে দূরের মাঠে কাঁচা বাথরুমের দিকে ধাওয়া করতাম। এরপর পিটি শেষে পুরি-ভাজি আর চা দিয়ে নাস্তা। পোশাক পাল্টে রাইফেল নিয়ে মিলিটারি ড্রিল আর অস্ত্র প্রশিক্ষণ। এর মাঝেই চলতো যুদ্ধ কৌশল নিয়ে লেকচার। বিকেলে খেলাধুলা। সপ্তাহের কয়েকবার রাতের প্রশিক্ষণ। কয়েক সপ্তাহ ধরে আমাদের কেবল দৌঁড়ে বেড়াতে হলো।
তার ফলও ফললো। আমাদের কয়েকজন পায়ের ব্যাথায় খোঁড়াতে লাগলো, কিন্তু কিছুতেই নিস্তার পাবার জো নেই। রাতের বেলায় আমরা মাটিতে ছেঁচড়ে ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে যুদ্ধ প্রশিক্ষন শেষে রক্তচোষা জোঁক গায়ে নিয়ে ক্যাম্পে ফেরত আসতাম। এ কঠিন সময়ের মধ্যেও থেমে থাকতো না মজা, একজন অন্যজনের পিছনে লাগালাগি এমনকি সামান্য পড়াশুনাও। বাসা থেকে পালিয়ে আসার সময় খুব ভেবেচিন্তে তিনটা বই নিয়ে এসেছিলাম আমি। জন ওয়েন এর An Anthology of Modern Poetry, The Age of the Guerilla নামে একটা বই আর Concise Oxford Dictionary । বইগুলো সে সময়কার অত্যাচারে ছিন্নভিন্ন কিন্তু এখনো অমুল্য সম্পদ। কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাত থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর একটা সংকলন আর ইংরেজী কবিতার উপর ১৯৩৩ সালের একটা ম্যাগাজিন কিনেছিলাম।
আমার দুই কোর্সমেটের কাছ থেকে ধার নিয়েছিলাম ভালোবাসার গল্প আর ড: জিভাগো।
আরেকটা বই যেটা আমাকে যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলো তা হলো ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল সংঘাতের উপর লিখিত মোসে দেয়ান-এর স্মৃতিকথা। বইটা আমার কোর্সমেট সায়েদকে (এখন মেজর জেনারেল) দিয়েছিল চিফ ইনস্ট্রাকটর মেজর থাপা। সায়েদ আমাদের উয়ং লিডার ছিলো। মেজর থাপা ওকে বলেছিলো বইটা পড়ে উনাকে মৌখিক একটা রিপোর্ট দিতে। সায়েদ বইটা পড়ার সময় পাবে না বলে আমাকে বললো পড়ে ব্যাপাটা বুঝে নিতে। আমি খুশি হয়েই রাজী হয়েছিলাম। এই বইটার ব্যাপারে সেনা আগ্রহের মূল কারণ ছিলো রণকৌশল, যেখানে উল্লেখ ছিলো শত্রুর কিছু কিছু বাধা উপেক্ষা করে মোক্ষম জায়গায় আঘাত করা, যাতে পরাজয় নিশ্চিত করা যায়। আমি আমার বন্ধুকে বলেছিলাম, যুদ্ধের সময় ভারতীয় রণকৌশল এমনটিই হবে। আমার আন্দাজ ছিল ওরা শীতকালে চীন সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করবে। সময়ে আমার আন্দাজ ঠিক প্রমাণিত হয়েছিল।
বিচিত্র মানুষের সমাহার আমাদের ঐ ক্যাম্পে, এরকম অ-সাধারণ যুদ্ধেই কেবল এমনটা দেখা যায়। আমাদের মধ্যে বেশিরভাগই শিক্ষার্থী। আমিন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ক্যাডেট ছিলো পরে আমাদের সাথেই অফিসার হয়ে ৭ নং সেক্টরের হামজাপুর সাব সেক্টরে ক্যাপ্টেন ইদ্রিসের নেতৃত্বে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। আর ছিলো ইআরপি সিগন্যাল থেকে আসা আওয়াল চৌধুরী যার বিশাল ব্যাগে ছিলো মশারি, বদনা, বাংলা-ইংরেজী ডিকশনারী। আওয়াল তার অদ্ভুত আচরনের জন্য সারা ক্যাম্পে মজার খোরাক ছিলো।
আওয়ালের অভ্যাস ছিলো বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে ছন্দ মিলিয়ে ছড়া তৈরি। যখন দিপু তাকে তার বদনা নিয়ে ক্ষেপাতো , তখন ও বলতো “Mr Dipu, you are not only rotten but also pungent.” আরেকদিন যখন আমাদের নিয়মিত খাবারের চেয়ে একটু ভালো খাবার দেয়ার দিন ছিলো, ও বললো, “The nomenclature of this food is good.”
শুধু এসবই নয়, বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষে ইংরেজীতে ছড়া রচনা করতো ও। যখন আমরা দলের নেতা ক্যাপ্টেন সাজান সিং কে ওর এই অভ্যাসের ব্যাপারে জানাই, তখন তিনি ওকে কিছু একটা আবৃত্তি করতে বলেন। অবিচলিত আওয়াল উঠে দাঁড়িয়ে পুরো দলের দিকে তাকিয়ে সুর করে বলতে শুরু করলো ………
What a thunder!
Yahya has committed a blunder!
Now he will wonder.
O brave Mukti Fouj,
Strike a heroic pose….
আরো বেশ কিছুটা ছিলো, বাকিটা ভুলে গেছি। আওয়াল দুই লাইনের অর্থপূর্ণ শ্লোক লেখায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলো। একবার ও আমাকে বললো “You must study art, To learn about the human heart.” আরেকদিন দিপু ওকে বাথরুমে বলতে শুনেছিল “It is tight!” একটু পর আনন্দিত গলায় “Now it is right!”
বিনোদনের তেমন কিছু ছিলো না আমাদের ক্যাম্পে। এরই মধ্যে কোন কোন সপ্তাহে হাতখরচ বাঁচিয়ে কাছের বাজারে ‘রাম’ খেতে যেতাম আমরা। বর্ষার শেষে মাঠগুলো শুকনো খটখটে হয়ে গেছে। একদিন রাতে আমাদের ক্যাম্পের পিছনে পাকা শস্যের ক্ষেতে হাতির পাল নেমে এসে আমাদের তাড়া করে। সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল দাশগুপ্ত (যার আদি বাড়ি ছিলো ময়মনসিংহ) ঐ বিশাল প্রাণীগুলোর মাথার উপরে গুলি ছুঁড়েন। ক্যাপ্টেন যাদব নামের আরেকজন সৈন্য, যার প্রিয় শব্দ ছিলো সবাইকে জোকার ডাকা। (এমনকি আমাদের মধ্যে সাহসী যারা তারাও তার কাছে জোকার, সবচেয়ে বড় জোকার আমাদের নেতারা) । হাতি দেখে আমাদের ডেকে বললো, ” একমাত্র এ্যান্টি ট্যাংক মাইন হাতিকে থামাতে পারে। আমাদের সাথে যেহেতু তা নেই, কাজেই, জোকাররা, হাতির পায়ের নিচে না পড়তে চাইলে সবাই দৌঁড়ে গিয়ে পিছনের উঁচু জায়গায় চলে যাও।”
হাতিগুলো অবশ্য সেদিন শেষ পর্যন্ত আমাদের উপর হামলা করেনি। দ্বিতীয়বার তাদের দেখা পাওয়ার আগেই আমরা সফলভাবে ট্রেনিং শেষে পাসিং আউট প্যারেডে অংশ নিলাম। সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন নির্বাসিত বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীপরিষদের কয়েকজন সদস্য এবং কর্ণেল ওসমানি যার চোখে পড়ার মতো গোঁফ আর কথাবার্তা শুনে ভারতীয় সৈন্যরা বলাবলি করছিল, “তিনি কর্ণেল হতে পারেন না, তাঁর তো জেনারেল হওয়া উচিৎ”। খুব বেশিদিন যেতে না যেতেই তিনি অবশ্য জেনারেল হয়েছিলেন। আর সেদিন আমরা হলাম সেকেন্ড লেফট্যানেন্ট যারা দেশের জন্য যুদ্ধ করতে পুরোপুরি প্রস্তুত। এর কিছুদিনের মধ্যেই আমরা রওনা হই আমাদের নির্ধারিত গন্তব্যের দিকে। তার পর? তার পরের গল্প তোলা রইলো আরেক দিনের জন্য।
ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন রেশমী নন্দী
http://arts.bdnews24.com/?p=5555
- Biplob Rahman | ০১ জানুয়ারি ২০১৪ ১৬:৩৮582680
- করোটিতে বিজয়ের ফুল
শামস হক | ১৫ december ২০১৩ ১১:৫০ অপরাহ্ন
বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ একটা চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে গেলে দখলদার বাহিনী এবং তার দোসররা মরিয়া হয়ে ওঠে। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনে তারা তাদের নীলনক্সা অনুযায়ী বাংলাদেশকে চিরতরে বন্ধ্যা করে রেখে যাবার উদ্দেশ্যে সকল অন্যায়, মানবতার চরম অবমাননায়, মরনকামড় শুরু করে।
সারা বাংলাদেশের হাজারও গ্রাম-শহরে নির্বিচারে নিরাপরাধ বাঙালি তথা মুক্তিযোদ্ধাদের নিধন তো চলছিলই; সেই সাথে ঠাণ্ডা মাথায় বেছে বেছে শিক্ষক, সাংবাদিক, ডাক্তার, আইনজীবী, সংস্কৃতিকর্মী, ছাত্র-নেতা যাঁরা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের হাল ধরতে পারতো, তাঁদের হত্যাযজ্ঞ শুরু হয় সেই ২৫ মার্চ থেকেই। পাকিস্তানি জল্লাদ এবং তাদের দোসর রাজাকার-আলবদর-আলশাম্স বাহিনীর খুনীরা দেশের বড় বড় বিদ্বান-পণ্ডিত-মেধাবী মানুষগুলোকে নিশ্চিহ্ন করবার নারকীয় হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। একাত্তুরের ২৫ মার্চ থেকেই শুরু হওয়া ধ্বংসের গতি ও পরিধি জ্যামিতিক হারে বাড়িয়ে দেয়া হয় ডিসেম্বর মাসে। জেনারেল রাও ফরমান আলীর নেতৃত্বে প্রস্তুত সেই নীলনক্সা বাস্তবায়নে বিশেষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত পাকিস্তানি শাসক এবং আলবদর বাহিনী পরিকল্পনা অনুযায়ী পৈশাচিক নিধনযজ্ঞ সম্পন্ন করে। বাংলাদেশের মেধা ও নেতৃত্বের জগতটাকে শূন্য করবার কাজটি শেষ করে। ঢাকার মীরপুর, মোহাম্মদপুর, নাখালপাড়া, রাজারবাগ, রায়েরবাজারসহ হাজারও গ্রাম-শহরের জানা-অজানা বধ্যভূমিগুলোতে জাতির মেধা ও অভিভাবকদের শহিদী আত্মা চিরকাল বাঙালির জাতি-বেদনার সুর তুলবে অনন্ত-বেহাগে। সেই সুরের রেশ ধরে, একদিন বাঙালি তার উপর পরিকল্পিতভাবে আরোপিত বন্ধ্যাত্ব কাটিয়ে জেগে উঠবে আপন বিভায় ও বৈভবে। সে আশায় বুক বেঁধে আজও জেগে আছে আবহমান বাঙালি সত্তা। ২০১৩’র বিজয়দিবসের প্রাক্কালে ঐ আশাবাদ আরো পোক্তভাবে ধ্বনিত হতে পারে পূর্বাপর ঘটনা বলির প্রেক্ষাপটে।
একাত্তুরের পরাজিত শক্তির নব উত্থান একাত্তরের পর অনেক রাজনৈতিক চড়াই উৎড়াই পার করেছে বাংলাদেশ, তার কারণ পাকিস্তানি দখলদার ও তাদের দোসরদের কার্যক্রম থেমে থাকেনি একাত্তরে তাদের পরাজয়ের পরও। একাত্তুরে মেধাশূন্য বাঙালি একাত্তুর-পরবর্তী সময়ে নিজ পায়ের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়ানোর আগেই জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। উদ্দেশ্য, জাতিকে শেষ আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করা। ’৭৫-এর আগষ্ট-ট্রাজেডির তিনমাসের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর জাতীয় চার নেতা, যাঁরা বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে জাতির হাল ধরতে পারতেন, তাঁদেরও জেলের ভেতরেই শেষ করে দেয়া হয় নভেম্বরের ৩ তারিখে।
সেই যে শুরু হলো মহান মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য-আদর্শের বিপর্যয়, তার কি শেষ আছে? মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য-আদর্শ তো বড় কথা। বাংলাদেশের জনগণের যে সাংবিধানিক অধিকার তা’ও কেড়ে নেয়া হয়েছে কতবার। কখনও সামরিক ছাউনি থেকে বন্দুক উঁচিয়ে ক্ষমতা দখল করে, কখনও স্বাধীনতা বিরোধী, মানবতার শত্রুদের ক্ষমতায় বসিয়ে ৩০ লাখ শহীদ দু লাখ মা-বোনের ত্যাগের মহিমাকে ম্লান করে। এরই মাঝে ৭১-এর নীলনক্সার বাস্তবায়ন পর্দার আড়ালেই চলছিল। একজন বাংলাদেশের ঘোষিত শত্রু পাকিস্তানী চামচা শাহ আজিজুর রহমান, তাকে প্রধানমন্ত্রী বানালেন বিখ্যাত এক মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের চরম দুশমন জামায়াত-ই ইসলামের তাত্ত্বিক নেতা পাকিস্তানে স্বেচ্ছানির্বাসিত যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হলো, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, সেই একজন বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধাই অপকর্মটি করলেন। পরে গোলাম আযম বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামের আমীর নির্বাচিত হন। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, একাত্তুরের পাকিস্তানি-নীলনক্শার বাস্তবায়ন; বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানানোর পাঁয়তারা।
মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অবর্তীণ অনেকেই, যেমন মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুজাইিদ, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, আব্দুল আলীম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক পবিত্র পতাকাকে গাড়িতে উড়িয়েছেন মন্ত্রীত্বের পাওনা হিসেবে। বলা বাহুল্য, এইসব দুর্ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে তখনও মুক্তিযোদ্ধাদের বিরাট একটা অংশ জীবিত থাকা অবস্থায়, যদিও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী প্রায় সবাইকে খতম করা হয়েছিল। আক্ষেপ তখন অনেকেই করেছি আমরা, কিন্তু উপায় ছিল না। সেই যে নীলনক্শার বাস্তবায়ন, তার ফলে নেতাশূন্য দেশে নেতৃত্বের অভাবে সংকট সময়ে জাতিকে যুৎসই দিক্নির্দেশনা দেবার কেউ ছিল না। নেতৃত্ব দেবার যদিও বা দু’চার জন ব্যক্তির উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না, তবুও একটা দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই স্বাধীনতার শত্রুরা মরিয়া হয়ে সক্রিয় থাকে। অর্থ-অস্ত্র-আসমানী টোপ বিতরণ করে জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে তারা ঢুকে পড়ে। শুরুতেই দরকার ছিল বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে জাতির ভবিষ্যৎ প্রজম্মকে প্রস্তুত করা। গত ৪২ বছরে সেই কাজটি করতে ব্যর্থ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি। এরই ফাঁকে জামাতীরা তাঁদের নিজস্ব ঘরানার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। দেশের বাকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে লোভ-লাভের খয়রাতি বিতরণ করে নিজেদের আদর্শে অসংখ্য অনুসারী তৈরী করে। কার্য্যতঃ একটা সময়ে তারা সরকার গঠন করে কিংবা সরকারে বড় ভাগ বসিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য আদর্শকে চিরতরে স্তব্ধ করবে এই প্রত্যাশায়। এ পরিকল্পনায় তাঁরা এগিয়েছেনও অনেক। কিন্তু তাদের ইচ্ছাপূরণ শেষ পর্যন্ত আশানুরূপ হয়নি। যুদ্ধপরাধীদের বিচার নিয়ে সাম্প্রতিক ঘটনাবলিই তার সাক্ষ্য।
বাঙালি জাতিসত্তার ফল্গুধারা নীরবে জন্ম দিচ্ছে আর এক অর্নিবাণ শিখার। সম্প্রতি গণজাগরণ মঞ্চে উচ্চারিত মাত্র কয়েকটি শব্দই ঝাঁকুনি দিল জাতির শিকড়মূলে। কলংকিত ইতিহাস খানিকটা হলেও কালিমামুক্ত হলো। অনেক অভ্যন্তরীণ আন্তর্জাতিক চক্রান্ত এড়িয়ে বাংলাদেশের যুদ্ধপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যেখান থেকে বধ্যভূমির করোটি ভেদ করে বিজয়ের ফুল জেগে উঠছে, দেখা যায়। জাতীয়-আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষেণের মধ্যে এ-বিচার প্রক্রিয়াকে অস্বচ্ছ বলার কিংবা প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে অথবা হতে থাকবে, কিন্তু সেসব চেষ্টাকে অংকুরেই নষ্ট করে দেয়ার একটি পরিকল্পিত কর্মসূচি থাকতে হবে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষীয় সরকারের। এ-দিকটা হালকা করে দেখার অবকাশ নেই। হালকা করে দেখলে বুমেরাং হবে, যার পরিণতি ভয়ংকর। সেই ভয়ংকরের ভয়ংকরী মূর্তি জাতিকে অবাক বিস্ময়ে দেখতে হয়েছে পঁচাত্তুরের অগাষ্ট-নভেম্বরে এবং ২০০১ পরবর্তী দিনগুলোতে। দ্বন্দ্বের জায়গাটি যে যুদ্ধেরও জায়গা, এবং সে যুদ্ধের পরাজিত পক্ষ যে বহুমুখী ও বহুমাত্রিক হাইড্রাদৈত্য, তা মনে রেখে পরিকল্পিত ও হারকুলিয়াসতুল্য ব্যুহ রচনা করতে হবে। টিকে থাকা নয়তো বিপন্ন কিংবা বিধ্বস্ত হওয়া। এই ভূ-খণ্ডের এথ্নিক অস্তিত্ব রক্ষায় যে অনিবার্য তাগিদ, তা থেকে পিছু হটা কিংবা আপোস করা হবে অপমৃত্যু মেনে নেয়া। দোহাই, সেইপথের একটিতেও না যেতে। Antagonist পক্ষ বিশেষত অর্থবলে খুবই বলীয়ান, বিদেশি সাহযোগিতার ভাগ্যেও ভাগ্যবান। জনমত গড়াপেটাতে তারা ব্যবহার করতে জানে চিরাচরিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। সুতরাং টিকে থাকা ও যুদ্ধ করে যাওয়ার লড়াই বুঝে সুঝে চালিয়ে যেতে হবে প্রোটাগোনিস্টকে। আন্তর্জাতিক মানের লরেটধারী ব্রুটাস প্রতিদিন বক্তৃতা করে যাচ্ছে প্রলুব্ধকরণ পরিকল্পনায়, কিন্তু গ্রাম-বাংলার সাতকোটি নারীকে জানিয়ে দিতে হবে যে ব্রুটাস অতি ভয়ংকর ব্যক্তি। তথাকথিত ‘সম্মানিত’ হওয়া সত্ত্বেও ভয়ংকর! বাতিল।
মুক্তিযুদ্ধের প্রতিপক্ষ সবচেয়ে বেশি ভয় পায় বিচার প্রক্রিয়া। বিচার প্রক্রিয়া যারা সচল রাখতে চায়, ওরা তাদের চিহ্নিত শত্রু ধরে নিয়ে মধ্যপন্থী একটি সহায়ক শক্তির ওভারকোটের আড়ালে অবস্থান নিতে চায়। ওভারকোট ওয়ালারা সবুজ ও কালো- দু’রঙের ওভারকোটেই মাননসই । ওরা আবহাওয়ার পূর্বাভাস বিবেচনা করে এবং কোটের রঙ বদলায়; সুযোগ বুঝে কালো কোটের আড়ালে আশ্রয় দেয় ঘাতকদের। সুতরাং ঘাতক ভয়ংকর– ওভারকোট অধিকতর ভয়ংকর, সে ক্যামোফ্লেইজ করতে জানে।
বিজয় দিবসের প্রাক্কালে অযুত নিযুত বেদনার কাহিনী বাঙালি জাতিকে আবারো কাঁদাবে। গত ২৪ বৎসর সে কান্নার আহাজারী খানিকটা হলেও স্বস্তি ফেলছে। শাহবাগ চত্বরের গণজাগরণ মঞ্চ রহস্যময় এক রাজনৈতিক তমিস্রা থেকে জাতিকে কিছুক্ষণ আলোর পথ দেখিয়েছে।
শাহবাগই প্রমাণ করে, মাঝে মধ্যে বাংলায় চিল-শকুনের ছোবল দানা বাঁধলেও পরিশেষে বাঙালি জেগে ওঠে। জাতি আবারো পায়ে শক্তি নিয়ে এগোয়। পলাশী থেকে মুজিবনগর, মাঝখানে নীলক্ষেতে একুশ, দেশময় উনসত্তুর–এভাবেই তো বাঙালি, বাংলাদেশ। সে বয়ান যাক্ আপাততঃ।
বরং বলি অন্য কথা, গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রসঙ্গে। ঐ যে -বিলম্ব হলো বিচারে, কেন? কার দোষে এ-শাস্তি ৪২ বছর? তার উত্তর না হয় খুঁজবো পরে।
এই মুহূর্তে শ্যালুট জানাতে হয় শহীদ জননী জাহানারা ইমামের জজ আদালতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। সকৃতজ্ঞ কুর্নিশ জানাতে হয় আর এক বিদেশী, অষ্ট্রেলিয়ান, মি: সোলায়মানকে, যিনি বাদী হয়ে একাত্তুরের যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে ২০০৬ সালে ২০ সেপ্টেম্বর ফেডারেল কোর্ট অষ্ট্রেলিয়ায় একাত্তুরের যুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী ও তাদের কোলাবোরেটরদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছিলেন (যার প্রসিডিং নং SyG 2672 of 2006) এবং তা নথিভুক্ত হয় এভাবে: “On October 25, 2006, a direction hearing will take place in the Federal Magistrates Court of Australia, Sydney registry before Federal Magistrate His Honour Nicholls.” ” কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় অধূনা বাংলাদেশের সরকারকে, নানা চ্যুতি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও জাতি তাকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাবেই, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে বিশেষ পদক্ষেপের জন্য। জানি, দেশ বিদেশের অনেকেই, পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তুরষ্কের প্রেসিডেন্ট, যুক্তরাষ্ট্রে জামায়াত লবি ইত্যাদি অনেকেই এই বিচারকে প্রশ্নবিদ্ধ করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু একথাও তো সত্যি, অনেক অনেক বিশেষজ্ঞ, দেশবিদেশের প্রাজ্ঞজন, এই বিচারের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে নির্বিবাদ, নিশ্চিত, নিশ্চিন্ত। কিন্তু কারা ঐ বিরুদ্ধবাদী? একটু ঘাটলেই দেখা যাবে এরা সকলেই হয় একাত্তুরের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি বিরোধিতা করেছিল, নয় জামায়াতের টাকায় পরবর্তীতে তাদের জন্য সাফাই গাইছে। সেই বিরোধিতাগুলো, সেই ষড়যন্ত্রের হুঙ্কার কানে নেয়নি বর্তমান সরকার, বিশেষ করে সরকার প্রধান শেখ হাসিনা। সে কারণে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র আপাতত: মুখ থুবড়ে আছে। থাকুক। আমাদের এখন কতগুলো সত্য এবং যুক্তিযুক্ত দাবীর প্রতিষ্ঠা দরকার।
জানি, তখনকার সরকার পাকিস্তানে প্রায় ৪,০০,০০০ আটকে পড়া বাঙালি উদ্ধারের জন্য ভারতে বন্দী ৯৩,০০০ সাধারণ সেনাসহ চিহ্নিত ও অভিযুক্ত ১৮৫ জন পাকিস্তানী সেনাকর্মকর্তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। তাই বলে কি বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদবে? তা হতে দেয়া যায় না। নানা বাধা বিপত্তি এবং দুর্যোগের মোকাবিলা করে, আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাত করে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত যে হবে, তা এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। হীন মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষদাঁত ভেঙে গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িকতার পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে কাজে লাগিয়ে; নারীর ক্ষমতায়ন শিশু-বয়স্ক কল্যাণ, শিক্ষা-কৃষি-স্বাস্থ্য উন্নয়ন তথা ‘মিলেনিয়াম ডিভেলপমেন্ট গোল’ অর্জনে বাংলাদেশের রেকর্ডকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব বিবেকের সামনে বাংলাদেশকে শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে দাঁড়াতে হবে। দাঁড়াতে হবে পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের অর্থ-সম্পদের ন্যায্য হিস্সা আদায়ের জন্য। গতকাল এবং আজকের একটি দৈনিক পত্রিকায় জনাব মিজানুর রহমান খান জানান দিয়েছেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোরতর শত্রু, বাংলাদেশে মানবতা বিরোধী শক্তি জামাত এবং তাদের দোসররা শুরু থেকে মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন। একাত্তুরের ঢাকায় নিয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রের-প্রতিনিধি জনাব স্পিভাক কর্তৃক স্টেট ডিপার্টমেন্টে প্রেরিত তাবৎ টেলিগ্রামের বরাত দিয়ে, রাও ফরমান আলীর ফেলে যাওয়া কাগজপত্রের বরাত দিয়ে, তৎকালীন পাকিস্তানের আমলা আলতাফ গহরের বরাত দিয়ে, নানা তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন জামাতের রাষ্ট্রদ্রোহাত্মক এবং মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের নোংরা ইতিহাস। আর জুজুর ভয় নয়, প্রমাণিত অপরাধীদের জারিজুরি নয়, এবারে বিশ্বের দরবারে ন্যায় বিচারের আবেদন; একাত্তুরে বিদেশ থেকে আসা বাংলাদেশের জন্য সাহায্যের ২২০ মিলিয়ন ডলার ফেরতের দাবী; রাষ্ট্রীয় ব্যাংক সহ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় লগ্মীকৃত বাংলাদেশের যাবতীয় অর্থ সম্পদ ফেরত পাওয়ার দাবী; শতাব্দীর নৃশংসতম গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত পাক সেনা এবং তৎকালীন পাকিস্তানের নেতৃত্বের বিচার দাবী; এবং নিদেন পক্ষে পাকিস্তানের বর্তমান প্রশাসন থেকে ঐ যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্যে বাংলাদেশের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবী। বিশ্ব দরবারে এই সব দাবী পুনরুত্থাপন এবং দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ চেষ্টা চালিয়ে যাবে– এই প্রতিজ্ঞা আজকের বাংলাদেশের আপামর মানুষের। এ সব দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বধ্যভূমিতে আটকে পড়া শহীদদের আত্মাই শুধু নয়, এ দাবী শাশ্বত বাংলার, আবহমান বাঙালির এবং এ গ্রহের ন্যায়বিচারপ্রার্থী, শান্তিকামী সকল সুস্থ মানবিকতার।
http://arts.bdnews24.com/?p=5554
- Biplob Rahman | ০১ জানুয়ারি ২০১৪ ১৬:৪৩582681
- বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা প্রসঙ্গে
ফরিদ আহমদ দুলাল | ১৫ december ২০১৩ ১১:৩৯ অপরাহ্ন
‘উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই/নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।’ যাদের স্মরণে বাংলাদেশের মানুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার এ পংক্তিটি উচ্চারণ করে, তাঁরা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবনোৎসর্গকারী অসংখ্য সূর্যসন্তান, বাঙালি যাঁদের ‘শহীদ বুদ্ধিজীবী’ অভিধায় চিহ্নিত করেছে । স্বাধীনতার সূর্যটা ছিনিয়ে আনতে যেসব সূর্যসন্তান নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছিলেন, তাঁদের জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করা হলেই জানা যাবে কেন তাঁরা বাঙালির শ্রেষ্ঠসন্তান ছিলেন। কেন তাঁদের জীবন আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে আত্মোৎসর্গকারী সেই সূর্যসন্তানদের চোখের দ্যুতির দিকে তাকিয়ে বারবার আমরা নিজেদের জীবনের ব্যর্থতাগুলো আবিষ্কার করে নিতে পারি; তাঁদের স্মরণ করে আমরা নিজেদের গ্লানিমুক্ত করে নতুন উদ্যোমে পথ চলার প্রেরণা পেতে পারি। সম্ভবত সে কারণেই তাঁদের নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত আজকের প্রেক্ষাপটে সহজ নয়। ১৯৭১-এর বাংলাদেশ, বাংলাদেশের জনপদ আর আজকের জনপদ অভিন্ন নয় । ১৯৭১-এ বাঙালি এক তর্জনীর নির্দেশে ঐক্যবদ্ধ ছিলো, বাংলাদেশের কতিপয় কুলাঙ্গার ছাড়া সমগ্র বাঙালি জাতি ছিলো স্বাধীনতা পেতে উন্মুখ; আর আজ বাঙালিজাতি দ্বিধাবিভক্ত-ত্রিধাবিভক্ত। বাঙালি জাতির এই বিভক্তিকে যদি স্বাধীনতা বিরোধীচক্রের সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই, তাহলে স্বীকার করতেই হয় এটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারীদের ব্যর্থতা । আজকের প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শহীদ বুদ্ধিজীবী, এমনকি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে কথা বললেও তাকে ভিন্নমাত্রায় উপস্থাপনের জন্য প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এমন কী যাঁর তর্জনীর ইশারায় বাঙালি জাতি উদ্বেল হয়ে উঠেছিলো, যাঁর স্বপ্নের সাথে গোটা জাতির স্বপ্ন একাকার হয়ে গিয়েছিলো, যাঁর নির্দেশে গোটা জাতি নিরস্ত্র হয়েও জীবন হাতে নিয়ে সুশিক্ষিত-দুর্ধর্ষ এক বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঁশের লাঠি নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলো; তাঁর বিরুদ্ধেও ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাবার অবকাশ পাচ্ছে অনেকেই। এমন বাস্তবতায় অনেকেই কৌশলী বাক্যবিন্যাসে নিজেদের কথাটি এমনভাবে উচ্চারণ করছেন, যাতে জাতি, বিশেষ করে জাতির নতুন প্রজন্ম বিভ্রান্ত হবার সুযোগ আছে । যদিও ২০১৩-এর ফেব্রুয়ারি নতুন প্রজন্ম সম্পর্কে নতুন করে ভাববার অবকাশ তৈরি করে দিয়ে সচেতন মানুষের দুর্ভাবনাকে অনেকাংশেই দূর করে দিয়েছে নতুন প্রজন্মের সহসী সন্তানেরা । কবি শামসুর রাহমান শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, ‘আজ এই ঘোর রক্ত গোধুলিতে দাঁড়িয়ে/ আমি অভিশাপ দিচ্ছি তাদের/ যারা আমার কলিজায় সেঁটে দিয়েছে/ একখানা ভয়ানক কৃষ্ণপক্ষ।’ পাকিস্তানী দুঃশাসন চেয়েছিলো বাঙালিকে মেধাশূন্য করে দিতে । আর বাঙালিকে মেধাশূন্য করে ফেলার মূল পরিকল্পনার সাথে যারা যুক্ত ছিলো, যারা যুদ্ধের নয় মাস ধরে হানাদার বাহিনীর দোসর হয়ে গোটা বাংলায় তাণ্ডব-নৈরাজ্য-নৃশংসতা-বর্বর পৈশাচিকতার অসহনীয় অবস্থা সৃষ্টি করেছিলো অগ্নিসংযোগ-গণহত্যা-নারীনির্যাতন-ধর্ষণ আর ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের মাধ্যমে; সেই কুখ্যাত আলবদর বাহিনীর কর্তাব্যক্তিদের ক্ষমা করা বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে অসম্ভব বলেই কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী ‘কসাই কাদের মোল্লার’ মৃত্যুদ- না হওয়ায় নতুন প্রজন্ম প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলো শাহবাগের ‘প্রজন্ম-চত্বরে’ ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০১৩-তে । যে কথা কবি শামসুর রাহমান উচ্চারণ করেছিলেন তাঁর কবিতায়–‘একঝাঁক ঝাঁ ঝাঁ বুলেট তাদের বক্ষ বিদীর্ণ করুক/ এমন সহজ শাস্তি আমি কামনা করি না তাদের জন্য….।’ একই ভাষায় উচ্চকিত হয়েছিলো নতুন প্রজন্ম ঘাতকের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবীতে শাহবাগে । এর পর দীর্ঘদিন ধরে বাংলার মানুষ দেখছে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে গোলাম আযম-কাদের মোল্লা গংদের অনুসারীরা কী তা-ব চালাচ্ছে! কী ভাবে পুড়িয়ে মারছে অসহায় ঘুমন্ত মানুষ, কী ভাবে বৃক্ষ নিধন করে প্রকৃতিকে বিপন্ন করছে, কী ভাবে জ্বালিয়ে দিচ্ছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়ি-ঘর-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান; কী ভাবে রেলপথ-সড়ক অবরোধের নামে মারছে মানুষ–মারছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনির সদস্যদের । এসব নব্য রাজাকার-আলবদরদের নৃশংসতায় বাঙালি জাতি যেন আরেকবার প্রত্যক্ষ করছে ১৯৭১-এর নৃশংসতা । তারপরও আজকের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে তাদের পক্ষ অবলম্বন করে কথা বলছেন কেউ কেউ; এবং তারাও নাকি বুদ্ধিজীবী !
এমন বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে ‘বুদ্ধিজীবী’র সংজ্ঞায়ন নিয়ে সংকটে পড়ে যাচ্ছে জাতি । সঙ্গত কারণেই এমন প্রেক্ষাপটে ‘শহীদ বুদ্ধিজীবী’ দিবসের আলোচনা সহজ নয় । শহীদ বুদ্ধিজীবীদের কথা মনে হলেই যেসব উজ্জ্বল মুখ চোখে ভেসে ওঠে সেই মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার, ড. জি. সি. দেব, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডা. আবদুল আলীম চৌধুরী, ডা. মো: ফজলে রাব্বি, আলতাফ মাহমুদ, সিরাজুদ্দীন হোসেন, নিজাম উদ্দিন আহমেদ, সেলিনা পারভীন, খন্দকার আবু তালেবসহ অসংখ্য গুণী মানুষের জীবনদর্শনের কথা, মনে জাগে তাঁদের জীবনের মূল্যবোধ আর দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা, নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে তাঁরা কতটা আপোষহীন ছিলেন সেসব কথা, তাঁদের চরিত্রের নির্লোভ-নিরহংকার বৈশিষ্ট্য, তাঁদের দেশপ্রেম-ত্যাগ-বিজ্ঞানমনস্কতা এবং সর্বোপরি প্রতিমুহূর্তে সংস্কৃতিমান থাকার অহংকার যে কাউকে প্রাণিত করবে (যে কাউকে বলতে ধর্মান্ধ-কূপমণ্ডুকদের নিশ্চয়ই নয়) । আজকের এই ক্রান্তিকালে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালনের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের বুদ্ধিজীবীদের বিষয়েও সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে বৈকি । নিজের মেধা-মনীষা ও বিবেচনা দিয়ে বুঝে নিতে হবে মিডিয়ার অসংখ্য কাদা ছোড়াছুড়ি করা মেধাবীদের মধ্যে কে প্রকৃত বুদ্ধিজীবী আর কারা জ্ঞানপাপী ? ভিড়ের মধ্য থেকে প্রকৃত বুদ্ধিজীবী চিনে নেবার কী কৌশল ? এসব প্রশ্ন আসতেই পারে । যার উত্তর আমার জানা না থাকলেও আমি নিজে যে ভাবে বুদ্ধিজীবী আর জ্ঞানপাপীদের আলাদা করি, সে কৌশলটি নিশ্চয়ই জানিয়ে দিতে পারি পাঠকের জন্য ।
‘বুদ্ধি’কে যারা জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তারাই ‘বুদ্ধিজীবী’ নন । ‘বুদ্ধিজীবী’ শব্দটি একটা কনসেপ্ট । বুদ্ধিজীবী হবেন সমাজের আদর্শ, সমাজের বিবেক; বুদ্ধিজীবী হবেন সৎ-উদার-নির্লোভ-নিরহংকার, সহিষ্ণু-পরোপকারী-দেশপ্রেমিক-ধর্মীয় সংকীর্ণতামুক্ত-বিজ্ঞানমনস্ক এবং সর্বোপরি সংস্কৃতিবান; সংস্কৃতিবান মানেই প্রগতিবাদী । আর জ্ঞানপাপীদের মধ্যে আর সব গুণের উপস্থিতি থাকলেও তারা কিছুতেই সংস্কৃতিবান হতে পারেন না । তাদের চারিত্র্যের কূপ-ুকতা এবং পশ্চাদপদতার বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পাবেই তাদের আচরণে-কথায় এবং জীবনাচারে । যিনি পশ্চাদপদ এবং কূপ-ুক তিনি কখনো ‘বুদ্ধিজীবী’ হবার গৌরব অর্জন করতে পারেন না, তার চিন্তা-চেতনা-দিকনির্দেশনায় কখনো সমাজ ও জাতির কল্যাণ সাধিত হতে পারে না । কেন না সংস্কৃতিহীন সমাজ আর অনাব্য নদীর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না; অনাব্য নদীর জল যেমন দুষিত হতে বাধ্য, সংস্কৃতিহীন সমাজও তেমনি মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য । নতুন প্রজন্ম নিশ্চয়ই অন্ধতার দিকে-স্থবিরতার দিকে- কূপমণ্ডুকতার দিকে থাকবেন না; নিশ্চয়ই তারা এগিয়ে যাবেন আলোর দিকে-প্রগতি ও কল্যাণের দিকে, সর্বোপরি সভ্যতা এবং অগ্রগতির দিকে । ক্রান্তিকালের এই বুদ্ধিজীবী দিবসে এই হলো আমাদের বিনীত প্রত্যাশা । আমার বিশ্বাস নতুন প্রজন্ম তাদের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে চিনে নেবেন কে প্রকৃত বুদ্ধিজীবী আর কে জ্ঞানপাপী। অতঃপর যাকে মস্তকে ধারণ করার তাকে মস্তকে ধারণ করে জ্ঞানপাপীকে নিক্ষেপ করা হবে আস্তাকুঁড়ে ।
ডিসেম্বর ২০১৩
http://arts.bdnews24.com/?p=5553
- Biplob Rahman | ০১ জানুয়ারি ২০১৪ ১৬:৫০582682
- মুক্তিযুদ্ধের কবিতা
কামরুল হাসান | ১৫ december ২০১৩ ১১:৩৪ অপরাহ্ন
১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক ঘটনা, কেননা এর মাধ্যমেই জাতি হিসেবে হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা বাঙালিরা একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের অধিকারী হলো। ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্বে তারা মুক্তির আস্বাদ পেলেও সেসব স্থায়ী হয়নি, বেশিরভাগ সময় কেটেছে পরাধীনতার শৃঙ্খলে। ইতিহাস-কাঁপানো মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলিত করেছে এ দেশের আপামর জনসাধারণকে, যারা শত্র“কে মোকাবিলা করার জন্য বাধ্য হয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল, চালিয়েছিল অসীম সাহসী অসম লড়াই। গেরিলার যেমন অস্ত্র, কবির তেমনি কলম। কবিতায়, চিত্রে, গানে, নাটকে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করার মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন সৃজনশীল মানুষেরা, যারা জনগোষ্ঠির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল। তাদের অনেকেই সরাসরি অংশ নিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে, অস্ত্র, কলম ও কন্ঠে রক্ত ঝরিয়েছেন।
আমাদের সকল প্রধান কবিই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কালজয়ী কবিতা লিখেছেন। মুক্তিযুদ্ধ ঘিরে রচিত হয়েছে অজস্র আবেগী কবিতা, সংখ্যায় তারা অগণিত। এসব কবিতার ভেতরে জসিমউদ্দিনের ‘দগ্ধগ্রাম’, সুফিয়া কামালের ‘আজকের বাংলাদেশ’, আহসান হাবীবের ‘মুক্তিযোদ্ধারা দেখতে কেমন’, সিকান্দার আবু জাফরের ’বাংলা ছাড়ো’, শামসুর রাহমানের ’স্বাধীনতা তুমি’, হাসান হাফিজুর রহমানের ‘যখন উদ্যত সঙ্গীন’, সৈয়দ শামসুল হকের ‘গেরিলা’, শহীদ কাদরীর ‘নিষিদ্ধ জার্নাল’, রফিক আজাদের ‘একজন মুক্তিযোদ্ধার আত্মসমর্পণ’, নির্মলেন্দু গুণের ’স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো’, আবুল হাসানের ‘উচ্চারণগুলি শোকের’, মুহম্মদ নূরুল হুদার ‘আমরা তামাটে জাতি’, সানাউল হক খানের ‘সাতই মার্চ একাত্তর’ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের ‘শহীদ স্মরণে’, অসীম সাহার ‘পৃথিবীর সবচেয়ে মর্মঘাতী রক্তপাত’, হুমাযুন কবিরের ‘বাংলার কারবালা’, আসাদ চৌধুরীর ‘রিপোর্ট ১৯৭১’, হেলাল হাফিজের ‘নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়’, খোন্দকার আশরাফ হোসেনের ‘বাউসী ব্রিজ ’৭১’, মহাদেব সাহার ’ফারুকের মুখ’, আবিদ আজাদের ‘এখন যে কবিতাটি লিখব আমি’, ফারুক মাহমুদের ‘রাহেলা ফুফু’, দাউদ হায়দারের ’বাংলাদেশ’, আবিদ আনোয়ারের ‘আমার মায়ের নামে তোপধ্বনি চাই’, মিনার মনসুরের ‘কী জবাব দেব’, মারুফ রায়হানের ‘সবুজ শাড়িতে লাল রক্তের ছোপ’ প্রভৃতি সহজেই স্মরণে আসে। এসব কবিতায় পাই বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা, মানবিক আবেগ, স্বদেশপ্রেম, সাম্যচেতনা, ক্ষোভ ও মুক্তির তীব্র আকাক্সক্ষা। স্মরণযোগ্য উল্লেখিত কবিরা প্রত্যেকেই মুক্তিযুদ্ধকে বিষয় করে একাধিক কবিতা লিখেছেন, এ তালিকার বাইরেও রয়েছে অনেক আবৃত্তিযোগ্য কবিতা।
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ যে আন্দোলনমুখর ঘটনাবলীর চূড়ান্ত পরিণতি সেসব আন্দোলনের বিশ্বস্ত বর্ণনা উঠে এসেছে তাঁদের কবিতায়। শামসুর রাহমানের ‘আসাদের শার্ট’,-এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়’ উনসত্তরের গণআন্দোলনের সুমহান কাব্যিক দলিল। স্বাধীনতার প্রত্যাশায় উন্মুখ একটি জাতির চেতনাকে তিনি ধারণ করেছেন ‘স্বাধীনতা তুমি’ কবিতায়। কবির আর্তি, ‘তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা/ তোমাকে পাওয়ার জন্য/আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়? আর কতবার দেখতে হবে খা-বদাহন?’ স্বাধানতাকামী বাঙালি জাতির রক্তঝরা ইতিহাস আর তা পাওয়ার দুর্দমনীয় আকাক্সক্ষারই প্রতিধ্বনি। সিকান্দার আবু জাফরের ‘বাংলা ছাড়ো’ কবিতাটি সবুজ বাংলাকে দখলে নেয়া পশ্চিম পাবিস্তানী দানবের প্রতি গণহুঙ্কারের প্রতিধ্বনি; কবির সাথে আমরাও গর্জে উঠি, ‘তুমি আমার আকাশ থেকে/সরাও তোমার ছায়া/তুমি বাংলা ছাড়ো।’ বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে ঢেউ উঠেছিল তা ক্রমশ উত্তুঙ্গ হয়ে ওঠে। একুশের প্রথম প্রহরে লেখা মাহবুবুল আলম চৌধুরীর কবিতা গোটা বাংলাদেশের কন্ঠস্বর হিসেবে গর্জে উঠল ‘কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি।’ আবদুল গাফফার চৌধুরীর কবিতা ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো’ রূপ নিল কালজয়ী গানে। আলাউদ্দিন আল আজাদের কবিতা ‘স্মৃতির মিনার’ সেই অভয়ের বাণীই আমাদের শুনিয়েছিল যা মুক্তিযুদ্ধে অমিত সাহসে রূপান্তরিত হয়েছিল। আহসান হাবীবের ‘মুক্তিযোদ্ধারা দেখতে কেমন’ একটি আলাদা স্বাদের কবিতা যেখানে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে ঘিরে সাধারণ মানুষের ঔৎসুক্যের আড়ালে প্রকাশ পেয়েছে সহমর্মিতা ও মাহাত্ম্যকে তুলে ধরার প্রয়াস।
২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর এই নয় মাস গোটা বাংলাদেশে নৃশংস তাণ্ডব চালিয়েছিল বর্বর পাকবাহিনী। জসিমউদ্দিনের ‘দগ্ধগ্রাম’ কবিতায় তাঁর কাব্যভাষার স্বভাবজাত সারল্যে ফুঠে উঠেছে এক অমানুষিক নিষ্ঠুরতার ছবি-
‘কীসে কী হইল, পশ্চিম হইতে নরঘাতকরা আসি
সারা গাঁও ভরি আগুনে জ্বালায়ে হাসিল অট্টহাসি
মার কোল থেকে শিশুরে কাড়িয়া কাটিল সে খান খান
পিতার সামনে মেয়েকে কাটিয়া করিল রক্তস্নান’
মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস গোটা বাংলাদেশ ছিল অবরুদ্ধ, জনপদের পর জনপদ আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়েছে, অস্ত্র আর বেয়নেটের মুখে ছিল সাত কোটি মানুষ, নিরস্ত্র মানুষ আক্রান্ত হয়েছে, মা-বোনেরা হয়েছে ধর্ষিত। শহীদ কাদরীর ‘নিষিদ্ধ জার্নাল’ কবিতায় শত্র“ বুলেটে নিহত কিশোরের বর্ণনায় সেই অবরুদ্ধ সময়ের চিত্র ফুটে উঠেছে:
‘ধ্বংসস্তূপের পাশে, ভোরের আলোয়
একটা বিকলাঙ্গ ভায়োলিনের মতো দেখলাম তে-রাস্তার মোড়ে
সমস্ত বাংলাদেশ পড়ে আছে আর সেই কিশোর, যে তাকে
ইচ্ছের ছড় দিয়ে নিজের মতো করে বাজাবে বলে বেড়ে উঠেছিল
সেও শুয়ে আছে পাশে, রক্তাপ্লুত শার্ট পরে।’
সৈয়দ শামসুল হকের অনবদ্য পঙক্তি, ‘আমি যেখানে যাই এ শহরের অবেলায় ক্রমাগত বেলা পড়ে যায়’ অবরুদ্ধ ঢাকার ছবি তুলে ধরে। তাঁর ‘গেরিলা’ কবিতাটি কেবল বিষয়ে নয়, শব্দ-কোলাজে একজন লড়াকু গেরিলাকে ফুটিয়ে তুলেছে। একই শিরোনামে হাসান হাফিজুর রহমান লিখেন, ‘সবুজ মানুষেরা আচম্বিতে আজ প্রত্যেকেই গেরিলা’ এ কথাই বলে যে নিরস্ত্র বাঙালিকে পঁচিশে মার্চের কালোরাতের অন্ধকারে আক্রমণ করে বর্বর পাকবাহিনী ঠেলে দিয়েছে সেই প্রান্তে যেখানে প্রত্যেকেই একেকজন মুক্তিকামী গেরিলা। কবির অন্য কবিতা ‘তোমার আপন পতাকা’য় স্বাধীন পতাকার দুঃখনিবারণী শক্তির কথা বলা হয়েছে: ‘হাজার বছরের বেদনা থেকে জন্ম নিল/রক্তিম সূর্যের অধিকারী যে শ্যামকান্ত ফুল/নিঃশঙ্ক হাওয়ায় আজ ওড়ে, দুঃখ ভোলানিয়া গান গায়।/মোছাব তোমার মুখ সেই পতাকায়।’
আবুল হাসানের ‘উচ্চারণগুলি শোকের’ মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির একটি। মুক্তিযুদ্ধের অনেক কবিতাই স্বভাবজ কারণেই রাগী ও শ্লোগানধর্মী; সেই ভীড়ে এ কবিতাটি ব্যতিক্রমী শৈল্পিক।
‘হাঁটি হাঁটি শিশুটিকে আমি আর আজ
কোথাও দেখি না
নরম নোলক পড়া বৌটিকে আমি আর আজ
কোথাও দেখি না
কেবল পতাকা দেখি,
স্বাধীনতা দেখি!
তবে কি আমার ভাই আজ ওই স্বাধীন পতাকা?
তবে কি আমার বোন তিমিরের বেদীতে উৎসব?’
মুহম্মদ নূরুল হুদার ‘বাঙালির জন্মতিথি’ কবিতাটি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য উৎসর্গীত পঙক্তিমালার এক অপূর্ব সন্নিবেশ। কবি বিজয়ের প্রত্যুষে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি উচ্চারণ করেন গভীর শোকজড়িত অভিবাদন-
‘তোমাদের হাড়গুলো জ্যোৎস্নারাতে উড়ে যাওয়া সাদা কবুতর
সুদূর ঝর্ণার জলে স্বপ্ন-ছাওয়া ঘাসের সবুজ;
তোমাদের হাড়গুলো অন্তহীন স্রোতস্বিনী, সুরের নির্ঝর
একতারা হাতে এক বাউলের মনোজ গম্বুজ;
তোমাদের হাড়গুলো বাংলার সীমানা ডিঙ্গানো
ক্রমশঃ বর্ধিষ্ণু এক হরিৎ বাগান
কারবাইন তাক করা-বেপরোয়া সৈনিকের গান;
তোমাদের হাড়গুলো বাংলার হৃদপিণ্ডে অবিনাশী ঝড়,
বাঙালির জন্মতিথি, রক্ত লেখা ষোল ডিসেম্বর।’
খোন্দকার আশরাফ হোসেনের ‘বাউসী ব্রিজ ’৭১’ মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত একটি অন্যতম উজ্জ্বল কবিতা। কবি নিজে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, তাই তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কাব্যিক বুনটে অসামান্য সংবেদনে ধরা পড়েছে।
‘কাঠবিড়ালির মতো ত্রস্ত নৈপুণ্যে আমরা নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়েছিলাম,
তখন কৃষ্ণা একাদশীর ডাইনী রাত ছিলো গর্ভবতী, আর তার কিছুক্ষণ পর
ষাঁড়ের বাঁকানো শিঙ নিয়ে চাঁদ তার হাইডআউট থেকে বেরিয়ে এসেছিলো,
আকাশ-এরিনার অন্য কোণায় তখন মেঘ নামক এক যোদ্ধা অপেক্ষমাণ’
শহীদ মুক্তিযোদ্ধারা এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান, কেননা তারা দেশের জন্য সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করেছেন। যুদ্ধে নিহত এমনি এক মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে লেখা ‘নোটনের জন্য শোক’ খোন্দকার আশরাফ হোসেনের আরেকটি অনবদ্য কবিতা।
মুক্তিযুদ্ধের রূপকার বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ নিয়ে রচিত নির্মলেন্দেু গুণের ‘স্বাধীনতা, এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো’ এক অনন্য কাব্যদলিল। নির্মলেন্দু গুণের ভাষায় শেখ মুজিব হলেন সেই অমর কবি যার কবিতার প্রথম দুটি পঙক্তি, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম/এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম’। রেসকোর্সের ময়দানে সমবেত লাখো মানুষের কালো মাথার আন্দোলনে যে অনবদ্য মাঠ সেই মাঠকে কাব্যের পৃষ্ঠা বানিয়ে স্বাধীনতার কবি লিখছেন তাঁর কালজয়ী কবিতা। সমবেত জনতার অপেক্ষা, ‘কখন আসবেন কবি?’ মার্চের ঐ ঘোষণাই স্বাধীনতার ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ যাকে রূপদান করেছে বাস্তবতায়। বঙ্গবন্ধুর স্মরণে মুহম্মদ নূরুল হুদা একটি কাব্যের নামকরণ করেছেন যিসাস মুজিব’, কেননা যিশু খ্রীষ্টের মতো মুজিবকেও তাঁর জাতির জন্য আত্মোৎসর্গের ক্রুশকাঠে জীবন দিতে হয়েছে।
মুক্তিযোদ্ধারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমমূলক, নজরুলের বিদ্রোহ জাগানিয়া, জীবনানন্দের বাঙলার রূপমুগ্ধতাসমৃদ্ধ কবিতাসমূহের দ্বারা। তাদের প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল দেশপ্রেমের গানসমুহ, যেসব গান মূলতঃ সুরারোপিত কবিতা। ফ্রন্টে, বাঙ্কারে, রাতের অন্ধকারে তাদের বুকের ভেতর দীপ্যমান আলো হয়ে জ্বলেছে কবিতা, শ্র“তিতে বেজেছে দেশমাতৃকার প্রতি নিবেদিত গানের সুরধ্বনি। কেবল বাঙালি কবিরা নন, মুক্তিযুদ্ধ অনুপ্রাণিত করেছিল ভিনদেশী কবিদের। প্রখ্যাত মার্কিন বীট কবি এ্যালেন গীন্সবার্গের সুবিখ্যাত কবিতা ‘সেপ্টেম্বর যশোর রোড’, একাত্তরে এক কোটি বাঙালি শরণার্থীর অবর্ণনীয় দুর্ভোগকে দারুণ চিত্রিত করেছে।
মুক্তিযুদ্ধ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল সত্তর দশকের কবিদের কেননা সে সময়ে তারা সকলেই টগবগে যুবক। সত্তরের কবিতায় যে উচ্চকিত মেজাজ, রাগ ও দ্রোহ দেখা যায় তার প্রধান প্রভাবক মুক্তিযুদ্ধ। আশির দশকের কোনো কোনো কবির কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ অঙ্কিত হলেও বেশির ভাগ কবির কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের জোরালো উপস্থিতি নেই। নব্বই দশকে তা আরও ক্ষীয়মাণ হয়ে আসে। তবে নতুন প্রজন্মের কবিদের, যারা স্বচক্ষে মুক্তিযুদ্ধ দেখেননি, কবিতার মাঝে ফিরে আসছে মুক্তিযুদ্ধ, এর অনুষঙ্গ, নব নব আবিষ্কারে। যেহেতু তাদের কবিতা এখনো দানা বাঁধছে, মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে রচিত পঙক্তির খোঁজে আমাদের জ্যেষ্ঠ কবিদের কাছেই যেতে হয়। সেসব কবিতাই মুক্তিযুদ্ধের কবিতার বিভিন্ন সংকলনে ঠাঁই পেয়েছে যেসব কবিতা থিমেটিক্যালি পুরোপুরি মুক্তিযুদ্ধ ঘিরেই আবর্তিত। সেটাই স্বাভাবিক। সংকলকদের ঘুরে ফিরে যেতে হয়েছে কিছু সুবিখ্যাত কবিতার কাছে। এসবের বাইরে বিপুল সংখ্যক কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ এসেছে খ-িত অবয়বে, অনুষঙ্গ হয়ে।
মুক্তিযুদ্ধের কবিতায় আমরা যেসব উপাদান দেখি তার ভেতরে পাকবাহিনীর ধ্বংসলীলা, বাংলার মানুষের দুর্ভোগ, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার প্রত্যাশা ইত্যাদি ঘুরে ফিরে এসেছে। অসংখ্য কবি তাদের রচনায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আবেগ ও চিত্রকে ধারণ করেছেন। হতাশা, ঘৃণা, ক্রোধ, আশাবাদ, স্বদেশপ্রেম, মুক্তিআকাক্সক্ষা এসব কবিতার প্রধান আবেগ। তীব্রতম আবেগের কারণে অনেক কবিতাই উচ্চকিত। প্রচুর কবিতা বিবৃতিমূলক, যা কবিতা হিসেবে রচনাকে দুর্বল করেছে। বর্ণনামূলক পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে কবিরা একটি দ্যোতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। এসবকে পাশ কাটিয়ে এসব কবিতায় যে শুদ্ধতম আবেগ ফুটে উঠেছে তা সাধুবাদ পাবে। মুক্তিপ্রত্যাশী একটি জাতির আশা-আআক্সক্ষাকে ধারণ করেছে অজস্র জানা-অজানা কবির কলম, তাঁদের মস্তিস্কে মুক্তিযুদ্ধ অজস্র পঙক্তির ফুল ফুটিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের চিরগর্বের সম্পদ, তেমনি সম্পদ একে ঘিরে রচিত সাহিত্য, কবিতা যার সুন্দরতম প্রকাশ!
http://arts.bdnews24.com/?p=5552
- Biplob Rahman | ০১ জানুয়ারি ২০১৪ ১৬:৫৬582683
- ৯৭১-এর দুর্লভ স্মৃতিময় চিঠি
শামিমা নাসরিন চৌধুরী লিলি | ১ এপ্রিল ২০১৩ ১২:৫৬ অপরাহ্ন
একাত্তুরের উন্মাতাল দিনগুলিতে লেখকের এই স্মৃতিচারণামূলক রচনাটি বিডিনিউজ২৪.কম-এর সমাজ বিষয়ক সম্পাদক ও মাননীয় সংসদ সদস্য বেবী মওদুদ-এর কাছ থেকে পাওয়া। লেখক শামিমা নাসরিন চৌধুরী লিলি আইসিডিডিআরবি-র প্রাক্তন কর্মকর্তা। রচনাটি প্রামাণ্য তথ্যে সমৃদ্ধ ও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। তথ্য ও মতামতের সকল দায়-দায়িত্ব লেখকের। পত্রের ভাষা যথাসম্ভব অবিকৃত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। একাত্তর সম্পর্কে এ-ধরনের আরো প্রামাণ্য চিঠি বা উপাত্ত পেলে আমরা তা আপলোড করতে আগ্রহী। - বিভাগীয় সম্পাদক
৩১শে জানুয়ারি ২০১২ সালে আইসিডিডিআরবি-র চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছি। বাসা বদলের সময় পুরনো কাগজপত্র বাছাই করতে বসেছি। পঁয়ত্রিশ বছরের কাগজপত্র বাছাই করা কি চাট্টি খানি কথা! কুড়ি বছরের বেশী হয় ঐ বাড়ীতে ছিলাম। আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। পুরানো কাগজ ফাইল গুছাতে যেয়ে বেশ কটি মূল্যবান তথ্যপূর্ণ চিঠি ও কাগজ পাই। দেখি লাল রং-এর একটি এরোগ্রাম। আমরা পাকিস্তান আমলে চিঠি লিখতাম। আমি অবাক হয়ে গেলাম। চিঠিটি আমি ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সনে আমার বড়বোন সুরাইয়া কাজী ও দুলাভাই আজিজুল হক কাজীকে লিখেছিলাম। লেখা পড়তে গিয়ে আরো বিস্মিত হলাম, এটি যেন এক ছোট দলিল! যেখানে ঐ সময়ের অর্থাৎ ৭ই মার্চ ১৯৭১- এর আগে ও পরের ঘটনার বিবরণী আছে। চিঠিটি লেখা ছিলো ঠিকই, কিন্তু পরদিন পোস্ট করা হয় নি। ১৯৭১ থেকে ২০১২ পর্যন্ত বহুবার আমার বড় বোনের সাথে দেখা হয়েছে- এ চিঠির কথা মনেই ছিলো না।একচল্লিশ বছর এক মাস লাগলো ওদের কাছে এ চিঠি পৌঁছাতে । এখানে বলে রাখা প্রয়োজন আমার বড়ো বোনের বিয়ে হয় ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর দুলাভাইয়ের সাথে আমেরিকাতে পাড়ি জমায় - সংসার জীবন শুরু হয় ওর ওখানেই।
cover.jpg
চিঠিটা নীচে তুলে দিলাম:
“বড়াপু, দুলাভাই
অনেকদিন তোমদেরকে লিখিনি। পরীক্ষা ছিল তাই লেখা হয় নি। শুরু হয়েছিল ১৮ই জানুয়ারি ’৭১। দেশের অবস্থা তোমরা নিশ্চয়ই voice of America থেকে শুনেছে। তাই পরীক্ষা বন্ধ হয়। এখনও7th & 8th paper এবং Viva বাদ আছে। 1st March-এ যখন ইয়াহিয়া ১টা ৫মিনিটে রেডিওতে ঘোষণা করলেন 3rd of March G National Assembly বসবে না এবং এটা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হল। তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না - কেমন করে, কোথা থেকে এত তাড়াতাড়ি ঢাকার পথে সব লোক জন বেরিয়ে এল। নানা ধরনের slogan দিতে লাগল। মনে হলো যেন within a second সব লোকজন বেরিয়ে পড়ল। ওরা সবাই বিক্ষুব্ধ। সারা প্রদেশের মানুষ কিভাবে এমন জেগে উঠল সেটা এক কথায় শেষ করা যাবে না। তোমাকে বলবো কি করে এ অবস্থার কথা। তারপর শুরু হলো ঢাকায় লুটতরাজ খুনোখুনি। সামরিক বাহিনী এল। তাদের গুলিতে মরলো অনেক। তারপর ৭ই মার্চ শেখ মুজিব রেস কোর্সের ময়দানে ঘোষণা করলেন আমাদের (পূর্ব পাকিস্তান, এখন এটাকে বলা হয় বাংলাদেশ) দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্তু আমরা Next কোন National যোগ দেব না। বড়াপু, দুলাভাই, এরমধ্যে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পোড়ানো হোলো। তার পরিবর্তে বাংলাদেশের তৈরী করা হলো। সেটা হলো ঘন সবুজের মাঝে লাল গোলক। তার মধ্যে বাংলাদেশের মানচিত্র। লালটা সংগ্রামের প্রতীক। মানচিত্রটার রং সোনালী। কল্পনা করে নিয়ে জানাবে তোমাদের কেমন লাগলো। ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবস ছিল। শেখ মুজিবের কথামত এটা ছুটির দিন ছিল। সমস্ত বাংলা দেশে বাংলাদেশের পতাকা উঠানো হয়। ৭ই মার্চের পরে থেকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (Non-violent, Non cooperation Movement) চলছে। হরতাল চলেছে অনেকদিন। স্কুল, কলেজ অফিস আদালত সব বন্ধ। আজকে National Assembly বসবাস কথা ছিল। সেটা স্থগিত রাখা হলো। শেখ মুজিব বললেন, আমাদের দাবী না হওয়া পর্যন্ত N.A. তে উনি যোগ দেবেন না। এটা তো জানোই Mujib Single Majority ভোট পেয়েছেন। ও হো, ৭ই মার্চের পরে থেকে আজও আমরা বাংলাদেশের সবাই কালো পতাকা তুলে বসে আছি। এর মধ্যে Governor Ahsanকে সরিয়ে দিয়ে আরেক জনকে এই পদে নিযুক্ত করা হলো। জনাব আহসান কিন্তু খুব ভালো লোক ছিলেন। যাক Tikka Khanকে পাঠানো হলো। আমাদের বিচারপতি ওনার oath নিলেন না। কত বড় অপমান টিককা খানের ভেবে দেখ। যাক অনেক দেশের কথা লিখলাম। আমি মলি ৯ই মার্চে বাড়ী এসেছি। জানি না কবে ঢাকা যাব। তোমরা এর মধ্যে আমাকে এখানের ঠিকানায় চিঠি লিখবে। রবিন, ম্যাকাইনকে আমার চুমু দিও। তোমরা সালাম জেন।
আমরা বাসার সবাই ভালো, লিলি।”
page-1.jpg
আজও ভেবে পাই না কি করে ঐ চিঠি একচল্লিশ বছর লুকিয়ে থাকলো। এতদিন কেন আমার মনে পড়ে নি? ঐ চিঠিটা এবং মেজর জিয়াউর রহমানের নিজ হাতে “জয় বাংলা” লেখা স্বাক্ষর করা একটা কপি আমার কাছে কি করে পড়েছিল। হারিয়ে যেতে বা ছিড়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারতো। এ দুটো হাতে পাবার পর মনে হলো টাইম মেশিনের আলোর গতিকে ছাড়িয়ে ঐ উত্তাল দিনে চলে গেলাম।
page-2.jpg
৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ শুনলাম রোকেয়া হলের প্রধান ভবনের পাঁচ তলা বারান্দার কোণা থেকে। রেস কোর্স মাঠ লোকে লোকারণ্য। সাহস পেলাম না সবার সাথে মাঠে যেতে। আমি পাঁচতলার ৬৩ নম্বর রুমে থাকতাম। ভাষণ শোনার পর আমরা সবাই আঁচ করতে পারলাম ভয়াবহ কঠিন কিছু আমাদের সামনে অপেক্ষা করছে।
আমাদের বি.কম অনার্স পরীক্ষা চলছিলো তখন। ছয় পেপার পরীক্ষা শেষ, আরো দুটি বাদ রয়েছে! উত্তাল সময়। পরীক্ষা স্থগিত হয়ে গেল। আমার ছোট বোন মলি (সামিনা চৌধুরী) তখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। ও হোস্টেলে থাকে।আমরা দু’বোন ৮ই মার্চ সকালে ট্রেনে করে সিরাজগঞ্জ চলে এলাম। এসে দেখি মা-বাবা অস্থির হয়ে আছেন। আমরা যারা বাইরে আছি তারা সময় মত ফিরলাম কিনা, ফিরবো কিনা।
৯ই মার্চ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলো, সমস্ত যাতায়াত ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হলো। দিন দিন সিরাজগঞ্জ শহর উত্তপ্ত হতে শুরু হলো। জেল থেকে সব কয়েদিকে ছেড়ে দেওয়া হলো। লোকজন সব মিছিল করতে শুরু করলো, দেখলাম বড় বড় রামদা তাদের হাতে। বিহারী, বাঙ্গালী, হিন্দু, মুসলমান, পাকিস্তানী নানা ধরনের বিরোধ। সামলানো কঠিন। রেডিওতে খবর শুনতাম। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা খবর শোনার জন্য। খুব তাড়াতাড়ি সিরাজগঞ্জের অবস্থার অবনতি হতে লাগলো। আব্বা প্রমাদ গুণলেন। ভাবলেন আমাদের বোনদেরকে ‘ভারতে’ পাঠাবেন। কিভাবে? ভেয়ে পেলেন না। ছোট মামা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিলেন। বাসায় আমরা একটু প্রশিক্ষণও নিলাম বন্দুক চালানোর। এখানে উল্লেখ্য, আমরা বাড়ীর সবাই ভালো ভাবেই রাইফেল শুটিং পারতাম।
শহরের অবস্থার ভীষণ অবনতি দেখে আব্বা সিদ্ধান্ত নিলেন আমাদেরকে গ্রামে নানা বাড়ী ও দাদাবাড়ী পাঠিয়ে দেবেন। শহরের অনেক পরিবার বাড়ী ছেড়ে গেছে। ২রা এপ্রিল ১৯৭১ শেষ রাতের দিকে আমরা গরুগাড়ী করে গ্রামের যাব। আব্বাকে এত অসহায় কখনো দেখিনি। তার অভিভাবকত্বে তখন ছিলো চাচা, ফুফু, মামা আর আমরা ছয় ভাইবোন। শেষ রাতের আলোয় আব্বা আমাদের সবাইকে ৩০০ করে টাকা দিলেন আর বললেন, “জানিনা তোমরা আমরা কে কোথায় থাকবো! যেখানে থাকো বেঁচে থাকার চেষ্টা করো!” সে যে কি এক অসহায় চেহারা!! আমরা সবাই যার যার মত ছোট ছোট কাপড়ের ব্যাগে দু’তিনটা শাড়ি শালোয়ার কামিজ ও নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস নিলাম। অবস্থা ভালো হলে তো সবাই ফিরবো।
নানা বাড়ী ছেড়ে আরো ভিতরে লক্ষ্মীকোলা দাদাবাড়ী গেলাম। গেলাম বললে ভুল হবে; আমরা পালালাম। দাদাবাড়ীতে পূর্ব পুকুর ধারে মসজিদ ছোট্ট মক্তব, পশ্চিমে পুকুর, মাঝ খানে দাদাবাড়ী।
আমরা ভালো সাঁতার জানিনা। সাঁতার প্রশিক্ষণ নিলাম। পুকুরের মাঝখানে কয়েকটা বাঁশ পুঁতে দেওয়া হলো। যদি পাক আর্মি আসে তখন বিশেষ করে মেয়েরা পুকুরের মাঝখানে যাব; যাবার আগে পুকুর পাড়ের পেঁপে গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে মুখে করে পানিতে ডুব দেব। পেঁপে ডাল পাইনের মত কাজ করে। সাঁতার শেখা ও গোসল করতে করতে আমাদের প্রায় সবারই কানে অসুখ হলো। পুকুরে গোসল করার পর প্রায়শ:ই ৩০০টাকা ভিজে যেতো। তা আবার লুকিয়ে লুকিয়ে শুকাতে হতো।
আমাদের সাথে থাকতেন কওমী জুট মিলের ম্যানেজার সাহেবের পরিবার, তার মা, আর এক জন অফিসার জাফর সাহেব ও লোটাস কামাল। সে অনেক কথা। কিভাবে খাওয়া দাওয়া চলছে। বাড়িতে আরো অনেকে আশ্রয় নিয়েছেন। যুদ্ধ লেগেছে। মরে যাব ভেবে অনেকে প্রতিদিন ঘরের পালা মুরগী খেতে থাকলো। এক মামা বললেন, “মরবু বলে সব খাবু বাঁচলে পরে কি খাবু?” কথাটা কত মূল্যবান।
page-3.jpg
যুদ্ধ চলাকালীন সেপ্টেম্বর মাসে আমরা আবার সিরাজগঞ্জ শহরে ফিরে এলাম। দেখলাম সমস্ত সিরাজগঞ্জ আগুনে পুড়ে ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। আমরা চলে গেলাম কওমী জুট মিলে ম্যানেজার সাহেবের কোয়ার্টারে। জানতে পারলাম ঢাকা এখন স্বাভাবিক হয়েছে, স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় খোলা। বিশ্বাস হয়নি। সিরাজগঞ্জে থাকাও নিরাপদ নয়। চলে এলাম আমরা দু-বোনে ঢাকায়। উঠলাম ফুফুর বাড়ীতে ডিআইটি কোয়ার্টারে। হলে গিয়ে দেখলাম সমস্ত রুম ভরা ছড়ানো ছিটানো জিনিসপত্র। তালা দেওয়া স্যুটকেস ও ট্রাংক ভাঙ্গা। কাপড় চোপড় লুট হয়ে গেছে। ভীষণ অস্বাভাবিক সে দৃশ্য।
ডিসেম্বর ১৯৭১ এগিয়ে এলো। ডিআইটির কোয়ার্টারে থাকি পাকিস্তান আর্মির সমর্পণের দিন এগিয়ে এলো। মুক্তিযোদ্ধারা ও ভারতের আর্মি বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে। এরপর ঢাকায় এলো। মর্টারের শব্দ শুনলাম। ১৬ই ডিসেম্বর সমর্পণের দিন। পাকবাহিনী অস্ত্র হাতে লাইন ধরে রেসকোর্স ময়দানে যাচ্ছে। দেখলাম যাবার পথে এলোপাথাড়ি গুলি করতে করতে তারা গেলো।
সেই যুদ্ধদিনের এক আতঙ্কভরা জীবন থেকে বিজয়ের দিনে এলাম। বিজয়ের আনন্দ যে কত বড় সেদিন বুঝতে পারলাম। আজ শুধু উপলব্ধি করি অনেক বেশি।
http://arts.bdnews24.com/?p=4981
- Biplob Rahman | ০১ জানুয়ারি ২০১৪ ১৭:০৩582684
- ৭১’-এর সেই জনযুদ্ধ যেমনটা দেখেছি
সাজ্জাদ আলী | ১৫ december ২০১২ ৬:৩৯ অপরাহ্ন
১৯৭১ এর মে মাসের প্রথম সপ্তাহের কোন একটা দিন, দুপুরের দিকে, আমার দাদীর বাড়ীতে অন্যদের নিয়ে খেলায় মত্ত আমি। তৃতীয় শ্রেনীর ছাত্র, তবে স্কুলে যাওয়ার বালাই নেই, কারন যুদ্ধ লেগেছে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে, স্কুলের স্যাররা সবাই যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, দু একজন নাকি চলেও গেছে। সারাদিনই শুধু খেলা আর খেলা। হঠাৎ বড়দের মধ্যে ভিশন হৈ চৈ, আমার চাচারা ও তাদের বন্ধুরা যাঁরা ভেতরের বাড়ীতে জটলা করছিল, সবাই দৌড়াচ্ছে বাইরের বাড়ীর কাঁচারী ঘরের দিকে। সেখানে আমার আব্বা অনেক লোকজন নিয়ে প্রতিদিনের মতই সেদিনও সলা-পরামর্শ করছিলেন, বোধকরি দেশের যুদ্ধ নিয়েই। আমাদের বাড়ী সংলগ্ন খেলার মাঠ থেকে আমিও দৌড়ালাম কাঁচারী ঘরের দিকে। যেতে যেতে দেখলাম আশেপাশের বাড়ীগুলো থেকেও পরিচিতরা সবাই আমাদের বাড়ীর দিকেই ছুটে আসছে। গিয়ে দেখলাম একজন লোক একটা ঘোড়ার পিঠে বসা (সেই সময়ে আমাদের এলাকায় দ্রুততার সাথে সংবাদ প্রেরণের একমাত্র অবলম্বন ছিল ঘোড়সওয়ার হওয়া), উচ্চস্বরে আব্বাকে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে এতই উত্তেজিত যে কেউই তার কথার কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। এক পর্যায়ে তার পরনের লুঙ্গির গিট খুলে একটা চিরকুট বের করে আব্বার হাতে দিল। মুহুর্তেই তিনি কাগজের ভাজ খুলে চিঠিটি পড়ে ফেললেন। তাঁর মুখের ফ্যাকাসে অবস্থা দেখে ছোট্র আমারও বুঝতে বাকী রইল না যে ঐ চিরকুটে কোন একটা মহা বিপদের বার্তা আছে। আব্বা সম্প্রতি যুদ্ধ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ‘বাংলা বাহিনী’ নামে একটা দল গঠন করেছেন, ২৫/৩০ জনের এই দলটি গত কয়েক মাস হল মোটামুটিভাবে আমাদের বাড়ীতেই থাকে, খায়। এদের কাজ এলাকার যুবকদের সংগঠিত করা, মিটিং মিছিলের আয়োজন করা, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কেউ কোন শব্দ উচ্চারণ করলে তাকে শয়েস্তা করা ইত্যাদি। তারা আব্বার অত্যন্ত অনুগত, বিনা বাক্য ব্যায়ে যে কোন নির্দেশ বাস্থবায়নে জীবন দিতেও প্রস্তুত। বড়দের বলাবলি করতে শুনেছি ওরা সবাই খুব তাড়াতাড়ি যুদ্ধে চলে যাবে এবং দেশ স্বাধীন করে তবেই ফিরবে। আব্বা হুঙ্কার দিয়ে এই বাংলা বাহিনীকে হুকুম দিলেন,- ‘তোরা এক্ষুনি বেরিয়ে যা, আশেপাশের সব গ্রামে খবর দে, সবাই যেন ঢাল, সড়কি, লাঠি, বল্লম যার যা কিছু অস্ত্র আছে সব নিয়ে এক্ষুনি চলে আসে’। ‘মোক্তার সাহেব’ (আমাদের এলাকার নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য) খবর পাঠিয়েছেন, ভাটিয়াপাড়া ওয়ারলেস স্টেশনে পাকিস্তানি মিলিটারীর ৪০/৫০ জনের একটি দল আজ সকালেই এসে ঘাঁটি গেড়েছে। মোক্তার সাহেবের নির্দেশ, আশপাশের পঞ্চাশ গ্রাম থেকে হাজার হাজার লোক নিয়ে মিলিটারীদের ঘিরে ফেলতে হবে এবং একজন একজন করে পিশে মারতে হবে।
তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহাকুমার কাশিয়ানি থানার এক প্রত্যন্ত গ্রামে আমার দাদির বাড়ী। বংশানুক্রমে আব্বা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং থানা আওয়ামী লীগের সম্পাদক, অঞ্চলের মানুষ তাঁকে ভালবাসে, সমীহ করে, শ্রদ্ধা করে, দুষ্টু লোকেরা ভয়ও করে। আক্তার উদ্দিন মিয়া, পেশায় গোপালগঞ্জ মহাকুমা ফৌজদারী আদালতের মোক্তার, কাশিয়ানী থানা আওয়ামী লিগের সভাপতি। এলাকার সাধারন মানুষ সন্মান করে তাঁকে ‘মোক্তার সাহেব’ বলে ডাকে। ১৯৭০ এর সাধারন নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যাবধানে মুসলিম লিগের ডাকসাইটে প্রার্থির জামানত বাজেয়াপ্ত করে দিয়ে প্রাদেশিক সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। আক্তার কাকাকে আমাদের পরিবারের একজনই মনে হত আমার কাছে, আমার আব্বার থেকে বয়সে বেশ বড়, তাঁর নাম ধরে ‘টিপু মিয়া’ বলে ডাকেন, তবে দীর্ঘ দিনের নিবীড় বন্ধুত্ব ও বোঝাপড়া দুজনার মধ্যে। ‘দল চালাবার টাকা’ এবং স্থানীয় আওয়ামী লিগের যে কোন নীতিগত সিদ্ধান্তের জন্য মোক্তার সাহেব আব্বার উপরেই নির্ভরশীল ছিলেন।
দু তিন ঘন্টার মধ্যেই আমাদের বাড়ীর সামনের মাঠ হাজারো মানুষে পরিপুর্ন। সবাই উত্তেজিত, প্রত্যেকের হাতেই দেশী অস্ত্র। কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ, কেউই বাদ যায় না, লাঠী/সড়কীর শির্শে স্বাধীন বাংলার পতাকা। শ্লোগানে শ্লোগানে মুখর সারা গ্রামের আকাশ বাতাস। মুক্তিকামি হাজারো মানুষের গগন বিদারী চিৎকার,- ‘বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর’, ‘পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা’, ‘তোমার নেতা আমার নেতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব’, ‘ইয়াহিয়ার চামড়া, তুলে নেব আমরা’, ‘শেখ মুজিবের কিছু হলে, জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে’ ইত্যাদি। এ যেন হাজারো মানুষের সম্মিলিত শক্তির মহাবিষ্ফোরণ, কি তার তেজ, কি বিক্রম ! কে রুখবে এদের স্বাধীনতা ? নিরীহ, নিরন্ন মানুষদের এমন প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, পৃথিবী আর দেখেছে বলে আমার জানা নেই, এ অহংকার কেবল বাঙালীরই সাজে।
আমাদের ভেতরের বাড়ীতে দৃশ্যটা অন্যরকম। আমার দাদী বসে আছেন উঠনের মাঝখানে তাঁর সেই চেয়ারখানায়, মাঝে মধ্যেই হাকডাক করে সবাইকে তটস্থ রাখছেন, আমার আম্মা আর মেঝচাচী রান্নার তদারকীতে ব্যস্ত। অন্তত দশটা চুলায়, বড় বড় ড্যাগে (বিশাল সাইজের রান্নার পাত্র) ভাত ও খেসাড়ীর ডাল রান্না হচ্ছে। কোন একটা ড্যাগের রান্না শেষ হওয়ার সাথে সাথেই বাংলা বাহিনীর লোকেরা সেটা বাইরের বাড়ীর উঠোনে নিয়ে লম্বা লাইনে বসা ক্ষুধার্থ মানুষদের কলাপাতার থালায় খাবার বেড়ে দিচ্ছে। মাঝেমধ্যেই আমার দাদী তদারকী করতে বাইরের উঠোনে আসছেন আর বলছেন সবাইকে ‘পেট ভরে খাও, যুদ্ধে যাচ্ছ তোমরা, আবার কখন খেতে পাবে সেতো আল্লাহই জানে’!
বাঙলা বাহিনীর ছেলেরা আমাদের মাঠে ইতিমধ্যেই একটা কাঠের চৌকির উপরে আরো একটা চৌকি দিয়ে ষ্টেজ বানিয়ে ফেলেছে। বেলা দুইটার দিকে আব্বা সেই ষ্টেজে উঠলেন, হাতে নিলেন তাঁর প্রিয় হ্যান্ড মাইকটি। হাজার হাজার মানুষ, মাঠে তিলধরাবার জায়গাও নেই, কেউ কোন শব্দ করছে না, সবাই অপেক্ষায় নির্দেশের! উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি হুঙ্কার দিয়ে বললেন,- আজ রাতেই ভাটিয়াপাড়া মিলিটারী ঘাটি ঘেরাও করে ৫০/১০০জন পাঞ্জাবী যাই থাকুক সবাইকে জীবিত বা মৃত ধরে এনে এলাকা শত্রুমুক্ত করতে হবে। ‘জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে হাজারো জনতা এ প্রস্তাবে সমর্থন জানালো, এ যেন তাদের সকলেরই মনের চাওয়া! নিজেদের শক্তি সামর্থের একটা ছোটখাট বর্ণনাও দিলেন আব্বা। প্রধান শক্তি হল দেশী অস্ত্রে সজ্জিত কয়েক হাজার সসস্ত্র মানুষ এবং তাঁদের তাদের অদম্য সাহস আর মাত্র দুটো বন্দুক। আমাদের বন্দুকটা দোনলা, উপস্থিত সাধারন মানুষদের ধারনা অনেকটা এরকম যে, ঐ দোনলা বন্দুকটা পৃথিবীর সর্ব শ্রেষ্ট মারণাস্ত্র, ওটা যাঁদের সাথে আছে, জয় তাদের সুনিশ্চিত ! যাই হোক, শক্তি বর্ণনার শেষ পর্যায়ে আব্বা চাইলেন জনতাকে সেই শক্তির প্রদর্শনীর ব্যাবস্থা করে চাঙা করতে। তিনি স্টেজে ডাকলেন তাঁর ইউনিয়ন পরিষদের দফাদারকে, সে আব্বার নিত্য সহচর ও বিস্বস্ত, ছায়ার মত তাঁকে অনুসরণ করে সব সময়, ২৬শে মার্চ থেকে, অর্থাৎ যুদ্ধ শুরুর পরপরই এই দফাদার ভদ্রলোক নিজে থেকেই আব্বার দেহরক্ষিতে পরিনত হয়েছে। সব সময়ই সে বন্দুকটা নিয়ে তাঁর সাথে। আব্বার ইসারায় দফাদার ভাই স্টেজের উপর উঠে বিশেষ কৌশলে দোনলা বন্দুকের দুটো গুলি পরপর এমনভাবে ছুড়লো যেন উপস্থিত জনতার মনে হল ’ব্রাস ফায়ার করা যায় এ বন্দুক দিয়ে’। গুলির শব্দের পরে জনতার যে উল্লাস, তেজ ও বিক্রম সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলাম, সেকি লিখে প্রকাশ করা যায় ?
পরিকল্পনামত যাত্রা শুরু করলো ৩/৪ হাজার জনতার এক বিশাল মুক্তিযোদ্ধার দল, গন্তব্য ভাটিয়াপাড়া ওয়ারলেস স্টেশন মিলিটারী ক্যাম্প। রাতের কোন একটা সুবিধাজনক সময়ে বিশাল এ যোদ্ধার দল একযোগে ঝাপিয়ে পড়বে হানাদারদের উপর, ওরা কিছু বুঝে উঠার আগেই সব শেষ করে দেবে।। শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে জনতা এগিয়ে চলছে ফসলের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে। আমিও চলেছি সাথে। কিছুদুর যেতেই বদর ভাই (আমার ফুফাত ভাই) পেছন থেকে আমাকে ধরে ফেললো, বললো তোকে মামী ডাকে। আমি দৌড় দেবার চেষ্টা করতেই সে আমাকে চ্যাংদলা করে ঘাড়ে তুলে সোজা বাড়ীতে এনে আম্মার সামনে হাজির করলো। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, দেখি সেখানে আমার দাদী আছেন ! দাদীকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না আমার, বায়না একটাই, ‘সবাই যুদ্ধে যাচ্ছে, আমিও যাব’। আমার ইংলিস প্যান্টের পকেট থেকে কাঠের ছোট্র পিস্তলটা বারে বারে বের করছি, দাদীকে দেখাচ্ছি, আর আমার শক্তির উৎসটা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করছি (আমাদের পশ্চিম পাড়ার কাঠমিস্ত্রী খগেন দাদু পিস্তলটা সম্প্রতি আমাকে বানিয়ে দিয়েছেন)। আমার আব্দার না করার ক্ষমতা, আমার ক্ষমতাশালিণী দাদীর কোনদিনই ছিলনা, আর আমার মায়েরও জানা ছিল যে দাদীর ইচ্ছাই চুড়ান্ত। দাদী তাঁর গোমস্তাকে ডেকে বললেন, একে নিয়ে যা যুদ্ধ করাতে, ঘাড়ে করে রাখবি সব সময়, মাটিতে ছাড়বি না, আধা মাইল দুরে থাকবি এবং সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরিয়ে আনবি। দাদীর প্রশ্রয়ে, মায়ের রক্তচক্ষু অতিক্রম করে এই শিশুযোদ্ধা তার কাঠের পিস্তল নিয়ে ঈমান দাদার ঘাড়ে চড়ে জনযোদ্ধাদের মিছিলে সামিল হল।
আমাদের গ্রাম থেকে ভাটিয়াপাড়া ৭/৮ কিলোমিটার দুর। শুকনা মৌসুমে হাটা আর বর্ষায় নৌকা ছাড়া অন্য কোন যাতায়াত ব্যাবস্থা নেই। হাজারো মানুষের কাফেলা এগিয়ে চলেছে দৃপ্ত পদক্ষেপে, এদের কোন ধারনাই নেই শত্রুর সম্পর্কে বা তাদের মারনাস্ত্রের মানুষ মারার সামর্থ সম্পর্কে। বিশাল এই জনযোদ্ধার কাফেলা একটির পর একটি গ্রাম পার হচ্ছে, আসপাশের গ্রামগুলো থেকে আরো শত শত মানুষ সসস্ত্র অবস্থায় যোগ দিচ্ছে এই দলে, কাফেলা বড় হচ্ছে প্রতি মুহুর্তেই, এতক্ষনে বোধকরি ৫/৭ হাজার ছাড়িয়ে যাবে। প্রতিটি গ্রামেই কিছুক্ষনের জন্য এ গণমিছিল থামছে, হ্যান্ড মাইকে আব্বা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/অনুরোধ রাখছেন, কখনও বা সেই গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁদের একাত্বতা প্রকাশ করে বক্তব্য রাখছেন, আবার এগিয়ে চলছে এই জনযোদ্ধার দল।
গ্রামগুলো যখন পেরুচ্ছে এই বিশাল মিছিলটি, তখন আশপাশের বাড়ীগুলো থেকে মহিলারা মুড়ি, চিড়া, গুড়, পানি, যাঁর বাড়ীতে যা কিছু শুকনো খাবার আছে সব জড় করে পথের পাশে দাড়িয়ে থাকছে, যদি কেউ ক্ষুদার্থ থাকে? সেদিনের একটি ছোট্র ঘটনা আমার শিশু মনকে স্পর্শ করেছিল যা আজো আমি স্পষ্ট মনে করতে পারি। যোদ্ধাদের এই বিশাল কাফেলা ‘ঘোনাপাড়া’ নামক গ্রামের বাজারে কিছুক্ষনের জন্য থামলো। বৃত্তাকারে প্রায় এক মাইল, শুধু মানুষ আর মানুষ, ঈমান দাদার ঘাড়ে আমি। অসতিপর এক বৃদ্ধা ঐ ভিড়ের মধ্যে লাঠি ভর দিয়ে আমার আব্বাকে খুজছে, তাঁর কাছে যেতে চাইছে। ‘বাঙলা বাহিনীর’ ছেলেরা বৃদ্ধাকে পথ করে দিল, তিনি আমার আব্বাকে তাঁর হাতের লাঠিখানা দিয়ে বললেন, ‘ বাবা আমিতো তোমার সাথে যেতে পারবো না, তুমি আমার লাঠিখানা নাও, অন্তত একজন খানকে এই লাঠি দিয়ে মারা চাই।’ অত্যন্ত আবেগ ও শ্রদ্ধার সাথে আব্বা সেই লাঠিখানা নিলেন এবং তাঁর কৌসুলি অবস্থান থেকে বৃদ্ধাকে ঐ কথাগুলো আবারো বলতে অনুরোধ করে মাইকটি তাঁর মুখের কাছে এগিয়ে দিলেন। কাঁপা কাঁপা কন্ঠে তাঁর সে নির্দেশ ‘আমার লাঠি দিয়ে পিটিয়ে খান সেনাদের খতম করবা’, যেন বারুদের মত বিস্ফোরিত হল জনতার মধ্যে। ‘বীর বাংগালী অস্ত্র ধর, খান সেনাদের থতম কর’ ধ্বনিতুলে আবার এগিয়ে চললো কাফেলা।
মাঝে আর কোন বাড়ীঘর নেই, আনুমানিক দুই কিলোমিটার লম্বা একটা বিল পেরুলেই ভাটিয়াপাড়া মিলিটারী ক্যাম্প, । সন্ধ্যা প্রায় ৬টা, জনযোদ্ধাদের এই কাফেলা এগুচ্ছে, শুধু ঐ বিলটাই পেরুতে হবে। হঠাৎ গুলির শব্দ, প্রচন্ড শব্দ, বিরামহীন একটানা, শব্দের উৎপত্তিস্থল বোঝাই যাচ্ছে ভাটিয়াপাড়া। পরিস্থিতি অনুধাবনে জনযোদ্ধাদের মিছিল থমকে দাড়ালো। কিছুক্ষনের মধ্যে ঐ দুর থেকেই আমরা দেখতে পেলাম ধোয়ার কুন্ডলী আকাশে, মাঝেমধ্যে আগুনের শিখা, গুলির শব্দ আরো বাড়ছে, কিছুক্ষণ পরপর ভারী গোলার শব্দে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে। ২৫/৩০ মিনিটের মধ্যেই দেখতে পেলাম শত শত নারী, পুরুষ, শিশু দৌড়ে বিল পার হয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। নেতৃবৃন্দের নির্দেশে হাজার হাজার মানুষের কাফেলা বিলের মধ্যে বসে পড়লো। জানা গেল, খান সেনাদের ৫/৭জনের একটি দল বিকেলে টহলে বের হয়েছিল ভাটিয়াপাড়া বাজারে। গ্রামের যুবক ছেলেরা দল বেধে ঝাপিয়ে পড়ে ঐ টহল দলের উপরে, সড়কি ছুড়ে একজন খান সেনার গলা ফুটো করে দেয়। এরপর থেকেই সেনারা দল বেধে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিতে ঝাঝরা করতে থাকে, যাকে সামনে পায় তাকেই। পুরো বাজারে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, গ্রামের মধ্যে ঢুকে নির্বিচারে চালাচ্ছে গুলি। প্রত্যক্ষদর্শিদের বর্ণনায়, শত শত লাশ পড়ে আছে বাজারে ও গ্রামের পথে পথে।
সন্ধ্যা লেগেছে, তবে তখনও কিছু আলো আছে, কাছাকাছি সবই দেখা যায়। খবর এলো ‘মোক্তার সাহেব’ (এ.এল.এ সাহেব) আসছেন। সবার মধ্যেই যেন নতুন প্রানের সঞ্চার হল। মোক্তার সাহেবের সাথে আরো দুজন, তাঁরা বয়সে তরুন, দেখতে শহুরে, পরে জেনেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা তাঁরা (তাঁদের নাম আজ আর মনে নেই)। মোক্তার সাহেব বিলের মধ্যে এসেই আব্বাকে কাছে ডাকলেন, দুজনে কি যেন সলা পরামর্শ করলেন (!), ‘বাংলা বাহিনীর’ ছেলেরা জনতাকে তাঁদের কাছে ঘেসতে দিচ্ছে না। কিছুক্ষন পরে সেই দুই ছাত্রনেতাসহ চারজনে মিলে কথাবার্তা বলে মোক্তার সাহেব মাইক হাতে নিলেন। সবাইকে সেই রাতেরমত বাড়ী ফিরতে অনুরোধ করলেন তিনি। হাজারো জনতা সমস্বরে নেতার এ নির্দেশ অমান্য করে বসলো, তাঁরা সেই রাতেই খান সেনাদের ক্যাম্প আক্রমন করবে,- এই তাদের সংকল্প! নেতা অসহায়ের মত মাইক হাতে দাড়িয়ে। ছাত্র নেতাদের একজন মাইক হাতে নিলেন, সুবক্তা তিনি, সেই রাতে আক্রমন করলে হানাদারদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কতটা এবং পরিস্থিতি কেমন ভয়ংঙ্কর হতে পারে তা বুঝালেন সবাইকে, একে একে বর্ণনা করলেন পাক সেনাদের ব্যবহৃত মারনাস্ত্রগুলোর কর্মক্ষমতা। আমরা হাজার হাজার মানুষ সেদিনই তাঁর মুখে প্রথম শুনলাম টমিগান, ষ্টেনগান, সাব-মেশিন গান, চাইনিজ অটোমেটিক রাইফেল, এ.এল.আর, মেশিন গান, রকেট লান্সার, গ্রেনেড, ডিনামাইট ইত্যাদি সব মারনাস্ত্রের নাম এবং আরো জানলাম এ অস্ত্রগুলোর মানুষ মারার ক্ষমতা সম্পর্কে। উপস্থিত হাজারো জনযোদ্ধার ধারনা ছিল খান সেনা মানেই হাতে ৩০৩ রাইফেল, এদের কাবু করা কঠিন হবে না। কিন্তু ঐ ছাত্র নেতার বর্ণনার পরে জনতা যেন বুঝতে পারলো যে এই হাজার হাজার যোদ্ধাকে পাখির মত মেরে ফেলতে হানাদারদের ১০ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না এবং তারা তা করতে দ্বিধাও করবে না।
জনযোদ্ধারা একটু শান্ত হতেই মোক্তার সাহেব আবার মাইক নিলেন, সবাইকে অনুরোধ করলেন সে রাতের মত বাড়ী ফিরতে। এরপর তিনি বললেন একেবারে নতুন সব কথা! আশার কথা! বললেন, ‘কিছুক্ষনের মধ্যেই আমি ইন্ডিয়া রওনা হচ্ছি, আপনাদের জন্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ আনতে। দেশের মধ্যেই আপনারা অস্ত্র চালনার ট্রেনিং করবেন, প্রয়োজনে আপনাদের ইন্ডিয়া পাঠাবো ট্রেনিং নিতে। এরপর শুরু করবেন গেরিলাযুদ্ধ। গেরিলাযুদ্ধ! সেটা আবার কি? জনতার অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা ? গেরিলাযুদ্ধের সাদামাটা একটা ব্যাখ্যা দিলেন মোক্তার সাহেব, বললেন, ‘হানাদারদের চলার পথে পথে ওৎ পেতে থেকে, তাদের খতম করে, দ্রুত ঐ স্থান ত্যাগ,- এই হল গেরিলাযুদ্ধ।’
‘গেরিলাযুদ্ধ’, ‘স্টেনগান’, ‘গ্রেনেড’, ‘ডিনামাইট’,- কথাগুলো সেই প্রথম শোনা। এই শব্দগুলো যেন কোন এক যাদুর ছোয়ায় উপস্থিত হাজারো মানুষের মনে এক নতুন আশার সঞ্চার করলো। মুহুর্তেই যেন সবাই বুঝে ফেললো এভাবে হবে না, যুদ্ধের কৌশল বদলাতে হবে। কিছুটা অপেক্ষা, অস্ত্রহাতে ট্রেনিং, তারপরেই মরণ আঘাত। আপাততুষ্ট জনতা ততক্ষনে বাড়ী ফিরতে শুরু করেছে। মোক্তার সাহেব আমার আব্বাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষন কাঁদলেন, তারপর বললেন, ‘টিপু মিয়া, আমি যাই, যদি বেঁচে থাকি আবার দেখা হবে। হাজার হাজার অসহায় এবং নিরস্ত্র যোদ্ধাদের আপনার হেফাজতে রেখে গেলাম, এঁদের দেখে রাখবেন’।
http://arts.bdnews24.com/?p=4821
- Biplob Rahman | ০১ জানুয়ারি ২০১৪ ১৭:১২582686
- আবদুল হামিদ রায়হান:
যুদ্ধদিনের আলোকচিত্রীর বিরল অবদান
মফিদুল হক | ৬ অক্টোবর ২০১২ ৮:৫৬ অপরাহ্ন
আলোকচিত্রী আব্দুল হামিদ রায়হান আমাদের যুদ্ধদিনের এক অনন্য শিল্পী। ঢাকা আর্ট সেন্টার তার একটি একক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। ‘রায়হানের ৭১’ শিরোনামে এ প্রদর্শনীর কিউরেটর চিত্রশিল্পী ও তার পুত্র আব্দুল হালিম চঞ্চল। এ প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে আব্দুল হামিদ রায়হানকে নিয়ে লিখেছেন মফিদুল হক। তার লেখাটিসহ নির্বাচিত কিছু আলোকচিত্র দিয়ে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের পাঠকদের জন্য প্রদর্শনীটির একটি অনলাইন সংস্করণ প্রকাশ করা হল। রাজধানীর ঢাকা আর্ট সেন্টার গ্যালারিতে (বাড়ী-৬০, সড়ক-০৭/এ, ধানমন্ডি) এ প্রদর্শনী চলেছে ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত । বি.স. 71-a.jpg
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দ্বার উদ্ঘাটন হয়েছিল ১৯৯৬ সালের ২২ মার্চের বৃষ্টিস্নাত বিকেলে। সেগুন বাগিচার সাবেকি এক দ্বিতল গৃহ ভাড়া নিয়ে জাদুঘরের যাত্রা শুরুর তোড়জোড় শুরু হয়েছিল এর প্রায় বছরকাল আগে। কাঠখড় পুড়িয়ে যে যজ্ঞের আয়োজন তার উপকরণ সংগ্রহ কঠিন হলেও অসাধ্য নয়, জাদুঘর প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক আয়োজন সেভাবেই সম্পন্ন হচ্ছিল; কিন্তু বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের উপকরণ পাওয়া নিয়ে। ইতিহাসের অমূল্য সব উপাদান গচ্ছিত রয়েছে বিভিন্ন মানুষের কাছে, তাঁদের অনেক গর্ভ ও দুঃখের সেইসব ধন তাঁরা কি নিয়ে আসবেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে, যার প্রতিষ্ঠা তখনো ঘটে নি, যে-জাদুঘর তখন কেবল প্রতিশ্রুতি হয়ে রয়েছে।
কিন্তু আমাদের এই শঙ্কা মোচনে বিশেষ বিলম্ব ঘটে নি, বহু মানুষের বহু অবদানে এমনভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে জাদুঘর যে তা অচিরেই হয়ে উঠলো জনগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সর্বজনের প্রতিষ্ঠান। শুরুর সেই শুরুতে একাত্তরের বিপুলসংখ্যক আলোকচিত্র প্রদান করে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সজীব করে তুলতে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিন গুণীর কথা বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয়। এঁরা হলেন ঢাকার রশীদ তালুকদার, যশোরের এস. এম. শফী এবং কুষ্টিয়ার আবদুল হামিদ রায়হান। রশীদ তালুকদার ঢাকার রাজপথের বহু মিছিলের শরিক সেই ষাটের দশক থেকে। পেশাদারি দায়িত্ব পালনকালে তিনি হয়ে উঠেছিলেন মিছিলেরই একজন। বঙ্গবন্ধুর বিশেষ স্নেহ তিনি পেয়েছিলেন। ঢাকার এক প্রধান দৈনিকের আলোকচিত্রগ্রাহক হিসেবে সেটা তাঁর যেন ছিল সহজাত প্রাপ্য। কিন্তু এস. এম. শফী ও আবদুল হামিদ রায়হান সত্যিকার অর্থে মুক্তিযুদ্ধের ফসল, মুক্তিযুদ্ধ যেমন বহু অজানা-অচেনা মানুষকে জাতীয় গুরুত্ব অর্জনকারী হিসেবে চিহ্নিত ও সম্মানিত করেছে, তেমনি বিরল ভূষণ আমরা অনায়াসে প্রদান করতে পারি শফী ভাই ও রায়হান ভাইয়ের প্রতি। একাত্তরে এক বিরল ভূমিকা তাঁরা পালন করেছিলেন, যাঁর যা কিছু আছে তাই নিয়ে যে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মানুষ, সেই যুদ্ধে মফস্বলের এই দুই পেশাদার আলোকচিত্রগ্রাহক রাতারাতি পরিণত হয়েছিলেন যুদ্ধ-আলোকচিত্রী। এঁদের রত্নভান্ডার ছিল লোকচক্ষুর আড়ালে, স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের রক্তাক্ত অধ্যায় ইতিহাসের অস্বীকৃতি ও বিস্মৃতির যে ধারা তৈরি হয়েছিল সেখানে এসব আলোকচিত্রের কোনো কদর ছিল না, মূল্য দেয়ার মতো সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল না। যখন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার বার্তা প্রচারিত হলো তখন উভয়েই বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সহযোগিতার হাত এবং আজ আমরা বিশেষভাবে বলবো আবদুল হামিদ রায়হানের কথা।
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে যেতে হয় নি জনাব আবদুল হামিদ রায়হানের কাছে, তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এসেছিলেন জাদুঘরে এবং ভান্ডারে জমা দিয়েছেন তাঁর কাজের বিশাল সম্ভার। প্রায় দুইশ’ ছবি বড় আকারে ম্যাট পেপারে প্রিন্ট করে তিনি দান করেছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। সব ছবি প্রদর্শিত হতে পারে নি গ্যালারিসমূহে। যে-ক’টি ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা গেছে, তার বিষয়-মাহাত্ম নিমেষে একজন দর্শককে ফিরিয়ে নিয়ে যায় একাত্তরের দিনগুলোতে। এসব ছবি একত্র করে দেখবার অবকাশ তৈরি হলে তা মানুষের জন্য হবে বড় পাওয়া এবং এটা আনন্দবহ যে অনেক বিলম্ব হলেও দৃক গ্যালারির উদ্যোগে সেই কাজ সম্পাদিত হচ্ছে।
আমি যতবারই দেখি আবদুল হামিদ রায়হানের ছবি ততবারই মুগ্ধ হই এর আটপৌরে আন্তরিকতার স্পর্শে। তিনি পেশাদার সংবাদচিত্রী ছিলেন না, ফলে নাটকীয় মুহূর্তের খোঁজে তিনি প্রাণপাত করেন নি, ক্যামেরায় তিনি বন্দি করতে চেয়েছিলেন জীবনকে। আর তাই এমন অনেক ছবি তিনি তুলেছেন যার সংবাদ গুরুত্ব হয়তো কম; কিন্তু মানবিক মাত্রা অনেক বেশি। ফলে মুক্তিযুদ্ধের আরেক মাত্রা আমরা খুঁজে পাই আবদুল হামিদ রায়হানের স্ন্যাপশটে।
একাত্তর সালে আমাদের সমাজে ক্যামেরা বিশেষ সুলভ ছিল না। ঢাকার বাইরে ভালো ক্যামেরার অধিকারী মানুষ তো ছিল প্রায় হাতেগোনা। মফস্বল শহরে একটি-দুটি পেশাদারি যেসব স্টুডিও ছিল তার অনেকগুলো পাকবাহিনীর আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, অনেক ক্ষেত্রে স্টুডিও ফেলে পালাতে হয়েছিল মালিককে, ব্যবসার আর কোনো সুযোগ তো ছিলই না, উপরন্তু ছিল ধনে-প্রাণে মরবার আশঙ্কা। সেই দুঃসহ দিনে পরিবার সহ সরে পড়তে হয়েছিল আবদুল হামিদ রায়হানকে, কিন্তু সরে গিয়ে তিনি কী করেছিলেন তাঁর দলিল হয়ে আছে সেইসব আলোকচিত্র। তিনি শরণার্থী শিবিরের জীবন দেখেছেন, প্রশিক্ষণ শিবিরের তরুণ যোদ্ধাদের ছবি ধারণ করেছেন পরম মমত্বে, গ্রামীণ পটভূমি থেকে আসা সাধারণ সেইসব যুবার প্রত্যয়ী চেহারা তো মুক্তিযুদ্ধের অনেক কথাই বলে যায়। তিনি প্রবাসী সরকারের নেতাদের মুক্তাঞ্চল সফরের ছবি তুলেছেন, জনসংযোগ কর্মকর্তার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং সেসব ছবি দেখিয়ে দেয় সেই রণদীপ্ত দিনে কীভাবে ঘুচে গিয়েছিল নেতা ও জনতার ফারাক। পাটগ্রামের মুক্ত এলাকায় ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য এবং ওয়ার অন ওয়ান্টের প্রধান ডোনাল্ড চেসওয়ার্থের ছবি তুলেছেন আবদুল হামিদ রায়হান এবং এই ছবি হয়ে আছে ইতিহাসের মূল্যবান দলিল।
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আবদুল হামিদ রায়হানের তোলা একটি ছবি দর্শকদের বিশেষভাবে টানে। তা হলো যুদ্ধাবসানে কুষ্টিয়ার মুক্তির পর পাকবাহিনীর ক্যাম্পের সামনে ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তাজা গোলাবারুদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা অর্ধ-উলঙ্গ বিস্ফারিত দৃষ্টির দুই বালকের আলোকচিত্র, ছবি দেখে মনে হবে যুদ্ধের প্রবল মৃত্যুলীলার মাঝখানে এভাবেই বুঝি ফুটে ওঠে জীবনের ফুল, মনে পড়বে এ-বিশ্বকে এই শিশুর বাসযোগ্য করে যাওয়ার অঙ্গীকার।
কোনো প্রাপ্তি নয়, নিবিড় এক অঙ্গীকার থেকে একাত্তরের চিত্রধারণ করেছিলেন আবদুল হামিদ রায়হান এবং তাঁর সেই চিত্রসম্ভার দান করে গেছেন জাতিকে। এমন মানুষের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান জানানোটাও এক দুরূহ কাজ। কামনা করি তাঁর শতায়ু, তাঁর অক্ষয় অবদান সত্যরূপে স্নাত করুক প্রজন্মের পর প্রজন্ম। জয় হোক আলোকচিত্রী আবদুল হামিদ রায়হানের।
আবদুল হামিদ রায়হান : সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত
আবদুল হামিদ রায়হানের জন্ম ১৯৩২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর, ৪ আশ্বিন ১৩৩৯, বৃহস্পতিবার;কুষ্টিয়ার জগতি ইউনিয়নের বড়িয়া গ্রামে, খালার বাড়িতে। তার পৈতৃক ভিটেবাড়ি গড়াই নদীর ওপারে শালদা গ্রামে। বাবার নাম চয়েন উদ্দিন, মা জোবেদা খাতুন।
তার পড়ালেখা শুরু হয় আড়–য়াপাড়ায় এক মক্তবে। পরবর্তীকালে মুসলিম হাই স্কুলে পড়ালেখা করেছেন ক্লাশ নাইন পর্যন্ত। অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ও পারিবারিক চাপে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার ইতি ঘটে এবং এরপর জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন নানা পেশা।
চল্লিশের দশকে খুব অল্প বয়স থেকেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তার পরিচয় ও সম্পর্ক গড়ে উঠে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় কুষ্টিয়ার সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালেও তার এই সম্পৃক্ততা বজায় ছিল।
আলোকচিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ততা তৈরি হয় ১৯৪৫ সাল নাগাদ। কিন্তু অর্থনৈতিক ও পারিবারিক দায়িত্বের চাপে আলোকচিত্রে মনোযোগী হওয়ার সুযোগ পাননি তিনি। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর তিনি আলোকচিত্রে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং নিয়মিত চর্চা শুরু করেন। ১৯৬৬ সালে লুবিডর ক্যামেরা দিয়ে এই যাত্রা শুরু, পরে ইয়াসিকা সহ বিভিন্ন ক্যামেরা ব্যবহার করেছেন।
১৯৬৯ এর গণআন্দোলন যখন তুঙ্গে তিনি ক্যামেরা হাতে এর ডকুমেন্টেশন করতে শুরু করেন এবং ১৯৭০ এবং ১৯৭১ সালে তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোকচিত্র ধারণ করেন। এর মধ্যে ১৯৭০ এর নির্বাচনের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিববর রহমানের কুষ্টিয়া সফর এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বিভিন্ন আলোকচিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে করিমপুর ইয়ুথ ক্যাম্পের সঙ্গে সহকারী ইন্সট্রাক্টর হিসেবে যুক্ত ছিলেন। তবে, এ সময়টাতে তিনি ফটোগ্রাফির সুযোগ পাননি। পরে বাল্যবন্ধু ব্যারিষ্টার আমীরুল ইসলামের সহায়তায় বাংলাদেশ ভলান্টারি সার্ভিসেস কোর (বি.ভি.এস.সি.) -এ আলোকচিত্রী হিসেবে যোগ দেন সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখ এবং এরপর থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ও ঘটনা তিনি তার ক্যামেরায় ধরে রেখেছেন। বিশেষ করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদসহ সেসময়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেশি-বিদেশি ব্যক্তিত্বদের কর্মকান্ড, মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের ক্যাম্প- জীবন, মুক্তাঞ্চলের কর্মকান্ড, পাকিস্তান বাহিনীর অত্যাচারের নানা উদাহরন, রাজাকার ও আল বদর বাহিনীর নির্যাতন এবং ধরা পড়ার পর তাদের শাস্তি ও পরিণতি, মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন কলকাতাসহ বিভিন্ন সীমান্ত-অঞ্চলে স্বাধীনতার সপক্ষে নানা কার্যক্রম তিনি তাঁর ক্যামেরায় বন্দি করেছেন।
মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে তিনি কুষ্টিয়ায় ‘রূপান্তর’ নামে একটি বাণিজ্যিক ফটোগ্রাফির প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন যা এখনো বিদ্যমান ও সক্রিয়।
http://arts.bdnews24.com/?p=4685
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... জয়ন্ত ঘোষ , অভিজিৎ চক্রবর্তী। , Kuntala)
(লিখছেন... রমিত চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, অঞ্জনা ঘোষাল)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Sara Man, প্যালারাম, যদুবাবু)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... )
(লিখছেন... রং, Kuntala)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... &/, dc, &/)
(লিখছেন... বিপ্লব রহমান, Maria’s Creation, Maria’s Creation)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... &/, সিএস, &/)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... রঞ্জন , kk, Ranjan Roy)
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল)
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : [email protected] ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত