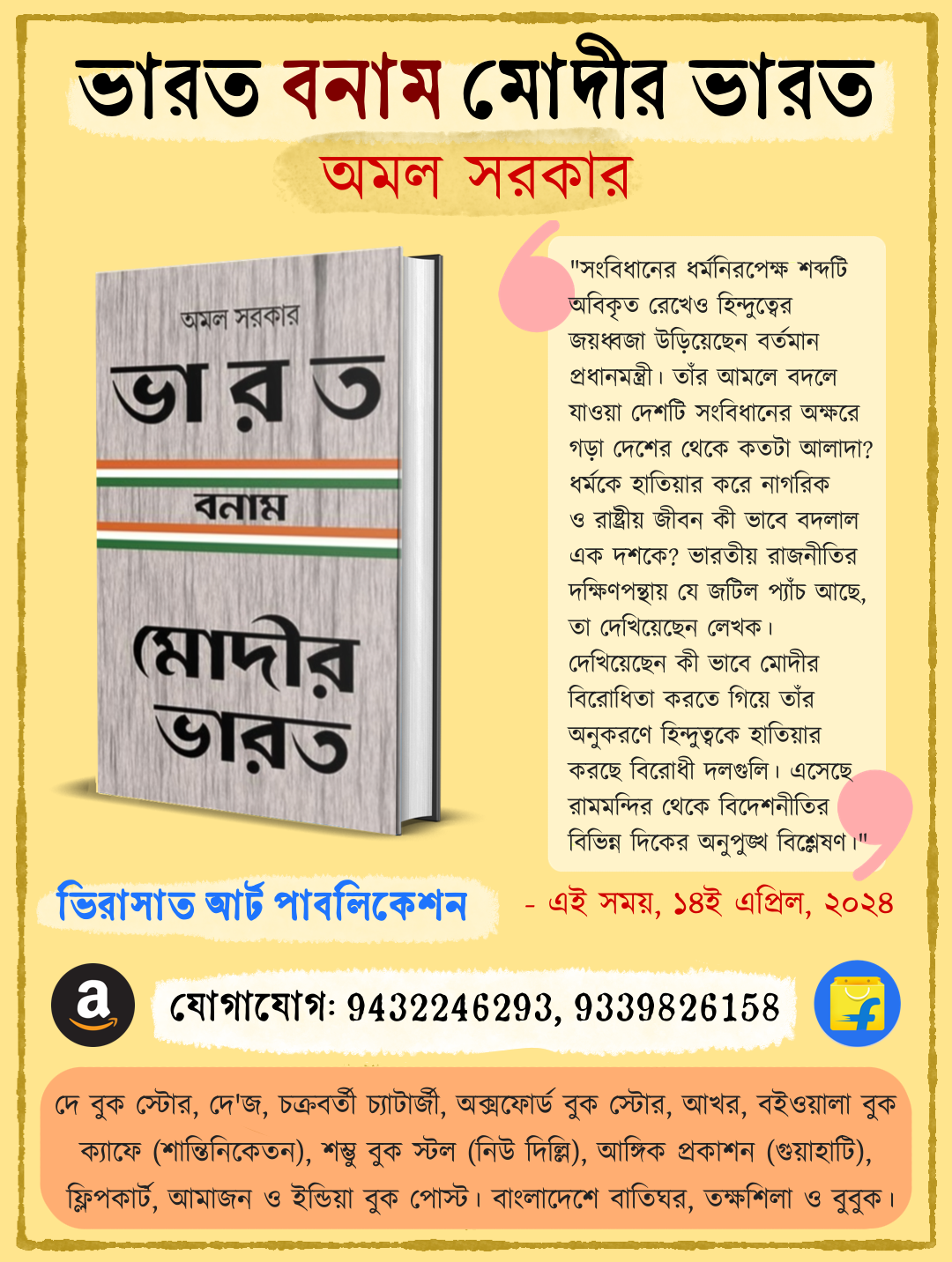- টইপত্তর অন্যান্য

-
১৯৭১ :: মুক্তিযুদ্ধের কথা
বিপ্লব রহমান
অন্যান্য | ০৯ ডিসেম্বর ২০১২ | ৪৯৫২৮♦ বার পঠিত
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 বিপ্লব রহমান | 127.18.231.63 | ২৬ মার্চ ২০১৩ ০৮:৪৭582554
বিপ্লব রহমান | 127.18.231.63 | ২৬ মার্চ ২০১৩ ০৮:৪৭582554- মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখযোদ্ধাদের কলমে একাত্তরের গৌরবময় যুদ্ধগাথা
মুক্তির লড়াই
এ কে খন্দকার | তারিখ: ২৬-০৩-২০১৩
দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও সংগ্রাম শেষে ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে শুরু হয় স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ আগে কখনো এভাবে যুদ্ধ করেনি। তাই যুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না বললেই চলে। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য উদ্গ্রীব এ দেশের মানুষের কাছে সে যুদ্ধ কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।
মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশ নিয়েছিল তাদের পেছনে ছিল ব্যাপক জনসমর্থন। এ দেশের ভূখণ্ড ছিল তাদের চেনা। অসীম সাহস সম্বল করে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত যুদ্ধবাজ পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে। পাকিস্তানি বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে অপ্রস্তুত জাতি শুরুর কিছুদিন সীমিত অস্ত্র আর শক্তি নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু করে। সে অবস্থাটি ছিল সাময়িক। প্রাথমিক দুর্বলতা কাটিয়ে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ বাহিনী সংগঠিত হতে থাকে। বাংলাদেশ বাহিনী, যা তত দিন মুক্তিবাহিনী নামে সাধারণ মানুষের কাছে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, ছড়িয়ে পড়ে দেশের সর্বত্র। স্থানীয় জনগণের একান্ত সহযোগিতায় হাট, বাজার, শহর, বন্দর, গ্রাম সব জায়গায় তারা শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। বন্ধুরাষ্ট্র থেকে পাওয়া এবং শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্র ও অন্যান্য সমরাস্ত্রের সাহায্যে প্রতিরোধযুদ্ধ ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয় গেরিলা যুদ্ধে।
আমাদের মুক্তিবাহিনীর সামরিক তৎপরতা শুধু ভূমিযুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তারা নৌপথ ও আকাশপথেও আক্রমণ করতে শুরু করে। অবশেষে মিত্রবাহিনীর সহায়তায় সেটি পরিণত হয় সর্বাত্মক যুদ্ধে। সে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আসে বিজয়। জন্ম নেয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের।
নভেম্বর মাসে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে চলে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ। এসব যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন সে সময়ের মাঠপর্যায়ের নেতারা। সেই নেতাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থাকলেও তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন একেবারে অনভিক্ত বা স্বল্প অভিজ্ঞ। যুদ্ধের মধ্য দিয়েই তাঁরা অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং তা শত্রুর ওপর প্রয়োগ করেন। কোনো কোনো খণ্ডযুদ্ধের বিজয় বাঙালির মনোবল অনেক গুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের করে তুলেছিল আরও দুর্দমনীয় ও সংকল্পবদ্ধ। কোনো কোনোটির বিজয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তার সফল পরিণতির দিকে। সব যুদ্ধেই যে মুক্তিযোদ্ধারা সফল হয়েছিলেন, তা নয়। তবে কোথাও কখনো ব্যর্থ হয়ে থাকলে পরের অভিযানে তাঁরা তা শুধরে নিয়েছেন। প্রতিটি খণ্ডযুদ্ধ তাঁদের আরও সাহসী করেছে, করেছে আরও কৌশলী ও দক্ষ। দিয়েছে চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা।
মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে প্রায় ৪২ বছর আগে। অথচ যুদ্ধের বর্ণনাগুলো এখনো যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের বীরদের যুদ্ধগাথা এখনো অনেকের ভালো করে জানা নেই। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত প্রথম আলোর এই বিশেষ ক্রোড়পত্রে মাঠপর্যায়ের কয়েকজন সমরনেতা তাঁদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। খণ্ডযুদ্ধে অংশ নেওয়া এই মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধবর্ণনার মধ্য দিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলোকে অনুভব করতে পারব, জানতে পারব তাঁদের বীরত্বগাথা।
এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার, বীর উত্তম: মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান, বর্তমানে পরিকল্পনামন্ত্রী
http://www.prothom-alo.com/detail/date/2013-03-25/news/339548
 বিপ্লব রহমান | 127.18.231.63 | ২৬ মার্চ ২০১৩ ০৮:৫৩582555
বিপ্লব রহমান | 127.18.231.63 | ২৬ মার্চ ২০১৩ ০৮:৫৩582555- সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রাহীদ এজাজ
পাকিস্তানের অবশ্যই ক্ষমা চাওয়া উচিত
হামিদ মির | তারিখ: ২৬-০৩-২০১৩
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নেতাদের নিয়ে বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন অধ্যাপক ওয়ারিস মির। দেশে ফিরে পাকিস্তানি নিধনযজ্ঞ নিয়ে লেখালেখি করেন। তিনি লাহোরে এক জনবক্তৃতায় পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যাপক সমালোচনাও করেছিলেন। এ ভূমিকার জন্য জীবদ্দশায় পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে সমালোচিত ও নিন্দিত হয়েছিলেন সাংবাদিকতা বিভাগের এ অধ্যাপক। তাঁর পক্ষে মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা নিতে ২৩ মার্চ ঢাকায় এসেছেন তাঁর ছেলে সাংবাদিক হামিদ মির।
প্রথম আলোকে দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরা হলো:
প্র. আ.: আপনার বাবা একাত্তরে কেন বাংলাদেশ সফর করেছিলেন?
হা. মি.: একাত্তরের অক্টোবরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্রকে নিয়ে তিনি বাংলাদেশে শিক্ষাসফরে এসেছিলেন। ওই সফরের সময় বাবা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগের প্রধান। তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র সংসদের নেতাদের ইউরোপ নেওয়ার জন্য বলেছিল।
প্র. আ.: তবে কি তিনি বাংলাদেশ সফরে প্রভাবিত করেছিলেন?
হা. মি.: তা বলতে পারেন। তাঁকে যদিও ছাত্রদের ইউরোপ নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তিনি তাঁদের বাংলাদেশ সফরে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ওই সফরে তিনি ও তাঁর শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে পৌঁছে নিজেদের চোখে দেখলেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হত্যা, নির্যাতন আর ধর্ষণের ভয়াবহ চিত্র। পাকিস্তানি সেনারা কেন বাংলাদেশে এ নিধনযজ্ঞ চালাচ্ছে, তা জানতে দেশে ফিরে তিনি সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। কিন্তু কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করল না। দেশে ফিরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের প্রতিনিধিদলটি একটি সংবাদ সম্মেলন করেছিল। সেখানে তারা তুলে ধরেছিল কী নৃশংসতা পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশে চালাচ্ছে। সে সময় গণমাধ্যমের ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ছিল সেনাবাহিনীর। স্বভাবতই ওই সংবাদ সম্মেলনের খবর শেষ পর্যন্ত কোথাও প্রকাশ পেল না। এরপর বাবা তাঁর বাংলাদেশ সফর নিয়ে বেশ কিছু নিবন্ধ লিখলেন। সেগুলোও কোনো পত্রিকা প্রকাশ করল না। এরপর একাত্তরের নভেম্বরে তিনি লাহোরে একটি গণবক্তৃতা দিলেন। ওই বক্তৃতার পর তাঁকে সরকার কারণ দর্শানোর নোটিশ দিল। তখনকার সেনাশাসক তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল। কিন্তু কোনো কিছুই প্রমাণ হলো না।
প্র. আ.: মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনাদের পরিবারের বিশেষ কোনো আবেগঘন মুহূর্তের কথা কি মনে পড়ে?
হা. মি.: এক রাতের কথা বলতে পারি। আমার মা কাঁদছিলেন, সঙ্গে বাবাও। আমি দ্বিধায় পড়ে গেলাম। প্রশ্ন করে কোনো উত্তর পেলাম না। পরদিন সকালে মাকে প্রশ্ন করলাম। এবারও এড়িয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত আমার জেদের কাছে হার মানলেন। তাঁর মুখেই শোনা বাংলাদেশের হত্যা আর ধ্বংসের বর্ণনা দিতে গিয়ে বাবা কেঁদেছেন। মা বললেন, সাতচল্লিশের উপমহাদেশ বিভক্তির সময় তাঁর অবস্থাও আমার মতো হয়েছিল। মা জানালেন, ওই সময় আমার নানিকে অপহরণ করা হয়েছিল। অনেক মুসলিম নারী হিন্দুদের হাতে ধর্ষিত হয়েছিলেন। সাতচল্লিশে হিন্দুরা মুসলিম নারীদের ধর্ষণ ও হত্যা করেছিল। আর একাত্তরে এসে মুসলমানরাই মুসলিম নারীদের ধর্ষণ ও হত্যা করছে। তাই কাল রাতে কেঁদেছি।
প্র. আ.: বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সমর্থনের জন্য আপনার বাবা সমালোচিত হয়েছিলেন। এ জন্য কি আপনাকে কোনো বিড়ম্বনার মুখে পড়তে হয়েছিল?
হা. মি.: সালটা ১৯৮২। আমি তখন সবে কলেজে ভর্তি হয়েছি। আমার এক সহপাঠী বলল, তুমি বিশ্বাসঘাতকের ছেলে। তোমার সঙ্গে আমি হাত মেলাব না। অপমান আর রাগ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। বাবাকে ঘটনার বর্ণনা দিলাম। বাবা হেসে বললেন, ‘আমি বাংলাদেশের পক্ষে ছিলাম। তাই তারা আমাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করে।’ এ নিয়ে তিনি আমাকে তর্ক না করার পরামর্শ দিলেন। অভয় দিলেন, এমন দিন আসবে যেদিন বলবে তোমার বাবা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক।
প্র. আ.: সে সময় কি এসেছে?
হা. মি.: সে সময় সত্য বলাটা পাকিস্তানে দুরূহ ছিল। আর আজ আমি পাকিস্তানের কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে টিভিতে কথা বলছি, কলাম লিখছি। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন জায়গায় আলোচনাতে উচ্চকণ্ঠ থেকেছি। কই এখন তো কেউ আর আমাকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলছে না।
প্র. আ.: কিন্তু আপনার এ বক্তব্য নিয়ে তো লোকজন প্রশ্নও করছেন।
হা. মি.: তা করছেন। আমিও জবাব দিচ্ছি। দিনের শেষে তাঁরা আমার যুক্তি মেনে নিচ্ছেন। আমি মনে করি, একাত্তর নিয়ে পাকিস্তানে দৃষ্টিভঙ্গির একটা পরিবর্তন এসেছে।
প্র. আ.: এ পরিবর্তন তো বেসরকারি পর্যায়ে হচ্ছে। সরকার কিংবা রাজনীতিবিদ তাঁরা কি একাত্তর নিয়ে পুনর্মূল্যায়নের কথা ভাবছেন?
হা. মি.: তাঁদের মাঝেও এ ভাবনা শুরু হয়েছে। পাকিস্তানের এ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যম বড় ভূমিকা রেখেছে। একাত্তর নিয়ে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গে বেশ কয়েকজন রাজনীতিবিদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তাঁরা আমাকে আশ্বস্ত করেছেন শিগগিরই পাকিস্তানের পার্লামেন্টে একটি বিল আনা হবে। ওই বিলে বলা হবে, একাত্তরের ভূমিকার জন্য বাংলাদেশের জনগণের কাছে পাকিস্তানের অবশ্যই ক্ষমা চাওয়া উচিত। আমি তো আশা করি, পাকিস্তানের আগামী পার্লামেন্টেই বিলটি উঠবে আর আমরা দেখব একাত্তরের জন্য প্রকাশ্যে বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাইছে পাকিস্তান। আর এর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হবে বাবার অবস্থানটাই সঠিক ছিল।
প্র. আ.: একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অপকর্মের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টি পাকিস্তানের সরকার কীভাবে দেখছে?
হা. মি.: পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিনা রাব্বানি খারকে এ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। নীতিগতভাবে তিনিও বাংলাদেশের দাবিকে যৌক্তিক মনে করেন। তবে তিনি এটিও উল্লেখ করেছিলেন, ক্ষমা চাওয়ার প্রক্রিয়ায় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সমস্যা রয়েছে। কারণ, পিপিপি সরকারের পার্লামেন্টে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। শরিকদের নিয়ে আমাদের সরকার চালাতে হয়েছে। শরিকদের মধ্যে ডানপন্থী দলও রয়েছে। তাই ক্ষমা চাওয়ার প্রসঙ্গটিতে আমরা কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে চাইনি।
প্র. আ.: তার মানে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের দাবিটি যৌক্তিক বলে পাকিস্তানও মানছে?
হা. মি.: আমি তো তা-ই মনে করি। বাংলাদেশের দাবিটি যথেষ্ট যৌক্তিক। একাত্তরে বাংলাদেশে এবং পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন এমন সামরিক কর্মকর্তা, বেসামরিক কর্মকর্তা ও গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখেছি। এসব আলাপচারিতা থেকে জেনেছি, একাত্তরের সব অপকর্মের সঠিক চিত্র কিংবা প্রমাণ বাংলাদেশের কাছেও নেই। তাই নষ্ট অতীত পেছনে ফেলে একটি উজ্জ্বল অতীতের জন্যই পাকিস্তানের ক্ষমা চাওয়া উচিত।
প্র. আ.: পাকিস্তানের আসন্ন নির্বাচনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন। পাকিস্তান কোন পথে এগোচ্ছে?
হা. মি.: সঠিক পথেই আছি। এ নির্বাচন অনেক পরিবর্তন আনবে। এটি হবে পাকিস্তানের ইতিহাসের সবচেয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন।
প্র. আ.: পরিবর্তনের সূচনা বলতে কী বোঝাতে চাইছেন?
হা. মি.: পরিবর্তন তো বটেই। এবার আর সেনাবাহিনী কিংবা গোয়েন্দা সংস্থা নির্বাচনে নাক গলানোর যথেষ্ট সুযোগ পাচ্ছে না। নির্বাচনকে প্রভাবিত করার সুযোগও তাদের নেই। কারণ, বিচার বিভাগ বিশেষ করে সুপ্রিম কোর্ট, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও সক্রিয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে মতপার্থক্য থাকলেও একটি বিষয়ে তারা একমত পোষণ করেছে, নির্বাচনে সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার ভূমিকা রাখার কোনো সুযোগ নেই।
আমার মনে হয়, পাকিস্তানে ভবিষ্যতে একটি কোয়ালিশন সরকার হবে। আর নওয়াজ শরিফকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হলে তিনি কোয়ালিশন সরকারের নেতৃত্ব দেবেন।
http://www.prothom-alo.com/detail/date/2013-03-26/news/339674
 বিপ্লব রহমান | 127.18.231.63 | ২৬ মার্চ ২০১৩ ০৮:৫৫582556
বিপ্লব রহমান | 127.18.231.63 | ২৬ মার্চ ২০১৩ ০৮:৫৫582556- সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রাহীদ এজাজ
ইতিহাস লুকিয়ে রাখা যায় না
আসমা জাহাঙ্গীর | তারিখ: ২৬-০৩-২০১৩
একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তারের পর তাঁর মুক্তির দাবিতে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে চিঠি লিখেছিলেন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মালিক গোলাম জিলানি। বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার প্রতিবাদে তিনি সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন। কোনো পত্রিকা সে খবর ছাপেনি। পাকিস্তানিদের নিধনযজ্ঞের নিন্দা জানিয়ে তিনি অনেক চিঠি ও কলাম লিখলেও সেগুলো ছাপেনি সেনানিয়ন্ত্রিত তৎকালীন গণমাধ্যম। উল্টো দিন কাটিয়েছিলেন কারাগার আর গৃহবন্দী অবস্থায়। বাবার এ অবদানের স্বীকৃতি নিতে ঢাকায় এসেছেন পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও মানবাধিকারকর্মী আসমা জাহাঙ্গীর। গত রোববার রাতে প্রথম আলোকে দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত তুলে ধরা হলো:
প্রথম আলো: একাত্তরের দিনগুলোর বিশেষ স্মৃতি কি মনে পড়ে?
আসমা জাহাঙ্গীর: আমার বাবা স্বতন্ত্র সাংসদ ছিলেন। এ কারণে তিনি ঘন ঘন ঢাকায় আসতেন। ফলে বাংলাদেশে তাঁর অনেক বন্ধু ছিলেন। তিনি সব সময় বলতেন, পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঞ্জাবের প্রভাব অত্যন্ত আগ্রাসী। পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বৈষম্যের তিনি বিরোধী ছিলেন। পার্লামেন্টের বিরোধীদলীয় অনেক সাংসদ ছিলেন তাঁর বন্ধু। তাঁদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং তাঁদের সঙ্গে মেলামেশায় তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। আমার মনে আছে, একাত্তরে গৃহবন্দী হওয়ার পর তিনি নিয়মিত রেডিও শুনতেন, খোঁজ রাখার চেষ্টা করতেন, কী হচ্ছে বাংলাদেশে। প্রথমে তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিধনযজ্ঞের পর তিনি বলতেন, দুই পাকিস্তান আর থাকছে না। তাদের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে, এরপর তাদের আর একসঙ্গে থাকার জন্য বলা যায় না। লক্ষ করেছি, প্রায় নিয়মিতভাবে বন্ধুদের মৃত্যুর কথা তাঁর কানে আসত। আর অসহায় মানুষটিকে দেখেছি দুই চোখ তাঁর পানিতে ভরে গেছে।
পশ্চিম পাকিস্তানের পরিস্থিতি এতটাই অসহনীয় ছিল, যা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। একদিকে সেনাবাহিনী, যারা ন্যূনতম ভিন্নমত গ্রহণ করবে না; অন্যদিকে রাজনৈতিক শক্তি, যারা জনগণের মাঝে এ ধারণা ছড়িয়ে দিয়েছে যে, পাকিস্তানের বিরোধীদের শায়েস্তার জন্য হত্যা আর নিধনযজ্ঞ চলছে। যে কেউ এ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেই তাকে বিশ্বাসঘাতক বলা হচ্ছে। সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়। কিন্তু জনগণের মাঝে উন্মত্ততা ছড়িয়ে দিলে তার মোকাবিলা করা দুরূহ। জনগণের এ উন্মত্ততা তো যেকোনো সমাজের জন্য আতঙ্কের বটে! অনেকেই বলতেন, তাঁরা এসব জানতেন না। প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি না জেনে তো থাকার কথা নয়। আসলে তাঁরা তো জানতে চাইতেন না। এই যে না জানার কথা তাঁরা বলেন, আসলে এড়িয়ে যাওয়ার এটি খুবই কুৎসিত এক প্রবণতা।
প্র. আ.: বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরও কি আপনারা একই ধরনের দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছেন?
আ. জা.: বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর তিনি এক দিনের জন্য মুক্তি পেয়েছিলেন। পরে তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর ওই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করি। মামলাটি আমাকে ‘আসমা জিলানির মামলা’ হিসেবে পরিচিতি এনে দেয়। ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সেনাশাসক ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করা হয়। তাঁর সরকারের নেওয়া সব পদক্ষেপ অবৈধ ঘোষণা করা হয়। ওই সময়ে হামুদুর রহমান কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনে বাবা যা বলেছিলেন, ওই ভাষ্য আর ইয়াহিয়ার কাছে লেখা চিঠির বক্তব্য একই। তবে একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, অনেকেই একাত্তরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে মুখ খুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি ভয়াবহ থাকায় ইচ্ছা থাকলেও অনেকেই এগিয়ে আসেননি।
প্র. আ.: আপনি বলতে চাইছেন, পাকিস্তানের লোকজন ধীরে ধীরে একাত্তর নিয়ে আত্মসমালোচনা শুরু করেছেন?
আ. জা.: ইতিহাসকে মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা যায় না। যখন রাষ্ট্রব্যবস্থা আর পরিবেশ বদলাবে, লোকজন সত্য কথাটা বলতে উৎসাহিত হবে। যাঁরা এত দিন চুপ করে ছিলেন, তাঁরাই সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হবেন। কাজেই প্রকাশ্যে এখন আর কেউ গণহত্যাকে অস্বীকার করছেন না। তবে এখনো এমন কাউকে কাউকে পাওয়া যাবে, যাঁরা বলবেন হত্যা দুই পক্ষেই ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত এটাই বলব, সত্যকে অস্বীকার করার প্রবণতা অতীতের তুলনায় এখন একেবারে নেই বললেই চলে।
প্র. আ.: একজন মানবাধিকারকর্মী ও আইনজীবী হিসেবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?
আ. জা.: ক্রান্তিকালীন বিচার (ট্রানজিশনাল জাস্টিস) সমর্থন করি। কারণ, দায়মুক্তির সংস্কৃতির অবশ্যই অবসান হওয়া উচিত। অপরাধ করে লোকজন পার পেয়ে যাবে, এটা হতে পারে না। তবে এ বিচার-প্রক্রিয়ায় সফল হতে হলে যথাযথ পন্থা অনুসরণের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করতে হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, যোগ্য আইনজীবী পাওয়া ও আপিলের সুযোগ—সবকিছুই দিতে হবে। আর আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় না। আমিও মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী। তবে বাংলাদেশের জনগণ এটি ঠিক করবে। এ বিচার-প্রক্রিয়া যাতে বিজয়ী পক্ষের বিচার হয়ে না যায়, সেটিও সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ রাখতে হবে।
প্র. আ.: একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের জন্য পাকিস্তানের আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে মনে করে বাংলাদেশ। বিষয়টি আপনার কাছে কতটা যৌক্তিক বলে মনে হয়?
আ. জা.: এ ধরনের হত্যা আর নিধনযজ্ঞের যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেটি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। শুধু আমাদের কিংবা আপনাদের জন্যই নয়, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের জনগণের ভাগ্যে যেন এ পরিণতি না ঘটে। এটি নিশ্চিত করার স্বার্থে যদি ক্ষমা চাওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকে, তবে তো অবশ্যই পাকিস্তানের ক্ষমা চাইতে হবে।
প্র. আ.: পাকিস্তানে আগামী মে মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন বলে আপনার মত?
আ. জা.: নির্বাচন সামনে রেখে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ কেমন হতে যাচ্ছে, সেটা বলা মুশকিল। নির্বাচন মানে ‘অপেক্ষাকৃত কম খারাপকে’ বেছে নেওয়া। নির্বাচনে কেউ ‘সাধুকে’ খুঁজে নিতে যায় না। এ ক্ষেত্রে জনগণ রাজনৈতিকভাবে কতটা পরিপক্ব হয়ে উঠেছে, সেটির ওপরও অনেক কিছু নির্ভর করে। এটি বলতে দ্বিধা নেই, জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি পিপিপি (পাকিস্তান পিপলস পার্টি)। তার মানে এটা নয়, ভয়াবহ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে পিপিপি। বিশেষ করে, দেশের অর্থনীতি চাঙা রাখতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। যদি সফল হতো, তাদের অবস্থান ভালো হতো। যেকোনোভাবেই হোক, জনগণ মনে করে, গভর্নরদের ওপর পিএমএলের (পাকিস্তান মুসলিম লিগ) প্রভাব পিপিপির তুলনায় ভালো। নতুন করে মাঠে নেমেছেন ইমরান খান। তিনি সব ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। জেনারেল পারভেজ মোশাররফের মতোই তিনি ৯০ দিনের মধ্যে সব সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। তিনি রাজনীতিবিদদের বিষোদ্গারের অস্ত্র বেছে নিয়েছেন, যা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে বিষিয়ে তুলছে। ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে নিয়েও তো অনেক প্রশ্ন রয়েছে। আপনি কারও প্রতি ইট ছুড়লে আপনাকে কিন্তু পাটকেল খেতেই হবে। এমন পরিস্থিতি তো নির্বাচনী পরিবেশকে নষ্ট করবে।
প্র. আ.: আপনি বলতে চাইছেন, ইমরান খান নির্বাচনের পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছেন?
আ. জা.: অবশ্যই। তিনি সব সময় বলছেন, রাজনীতি খারাপ আর রাজনীতিবিদেরা নষ্ট। অথচ তিনি নিজেই রাজনীতি করতে এসেছেন। তাঁর জীবনাচরণেই স্ববিরোধিতা স্পষ্ট। তবে এটা ঠিক, জনগণ পরিবর্তন চায়। জনগণ দুই দলকেই বেশ কিছুদিন ধরে দেখেছে। এখন অন্য কাউকে দেখতে চায়। আর তাদের কাছে সে বিকল্প ইমরানের তেহরিক-ই ইনসাফ। এতেই তিনি বিপুল বিজয়ের সম্ভাবনা দেখছেন। যদিও আমি মনে করি, সেটি ঘটবে না।
প্র. আ.: তার মানে কি কোয়ালিশন সরকার আগামী দিনে পাকিস্তান শাসন করতে যাচ্ছে?
আ. জা.: আমার সেটাই মনে হয়। রাজনৈতিক দলগুলোকে একসঙ্গে কাজ করাটা শিখতে হবে।
http://www.prothom-alo.com/detail/date/2013-03-26/news/339673
 বিপ্লব রহমান | 127.18.231.63 | ২৬ মার্চ ২০১৩ ০৯:০৪582557
বিপ্লব রহমান | 127.18.231.63 | ২৬ মার্চ ২০১৩ ০৯:০৪582557- ৪ দশক পর নিজভূমে ঘুমাবেন তাঁরা
আশরাফুল হক রাজীব
তুমুল যুদ্ধ যখন শেষ, দেখা গেল ময়মনসিংহ সীমান্তসংলগ্ন রণাঙ্গনে পড়ে আছেন নিথর নাসিরউদ্দিন। তাঁর চোখ দুটি খোলা, দৃষ্টি প্রিয় মাতৃভূমির সুনীল আকাশের দিকে। পাকিস্তানি সেনারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়ার পর শুধু নাসির নন, পাওয়া গেল আরো ১১ শহীদের লাশ। সহযোদ্ধারা কাঁধে করে তাঁদের বয়ে নিয়ে গেলেন ওপারে- ভারতে। মেঘালয়ের শালবনে তাঁরা সমাহিত হলেন। কোনো রকমে গোসল-জানাজা হলেও তাঁদের জন্য ছিটানো যায়নি গোলাপজল, বাজেনি বিউগলের করুণ সুর, হয়নি গানস্যালুটও। একটু বসে তাঁদের জন্য বিলাপ করারও সময় মেলেনি সহযোদ্ধাদের। কারণ কোনো রকমে কবর দিয়ে তাঁদের ফিরতে হয়েছিল রণাঙ্গনে। এটাই একাত্তরের বাস্তবতা।
শুধু নাসির নন, ভারতে চিরনিদ্রায় শুয়ে থাকা এসব বীর সেনানীর 'শেষ ঠিকানা' খুঁজে বের করার কঠিন এবং অনন্য কাজটি করেছেন কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক। ১০ বছর ধরে তিনি আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কবরস্থানে হন্যে হয়ে ঘুরেছেন। শেষ পর্যন্ত তিন হাজার মুক্তিযোদ্ধার কবর চিহ্নিত করতে পেরেছেন তিনি। এ অভাবনীয় কাজের জন্য তাঁকে সরকার গতকাল স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করেছে। পরদেশের মাটিতে শেষ ঠাঁই নেওয়া সেসব বীর এবার ফিরবেন প্রিয় মাতৃভূমিতে। চুপি চুপি নয়, তাঁরা ফিরবেন বীরের বেশে। দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জনকারী এসব শহীদকে সমাহিত করা হবে নতুন করে দেশের মাটিতে। একই সঙ্গে বর্ণিল আলোকচ্ছটায় সমাধিস্থলে এসব বীর সেনার জীবন উৎসর্গের বীরত্বগাথা উপস্থাপন করা হবে। রাষ্ট্রীয় বিশেষ দিনগুলোয় ফুলে ফুলে শোভিত হবে তাঁদের সমাধি। এর জন্য কসবায় তিন একর জমি অধিগ্রহণ করেছে সরকার।
কাজী সাজ্জাদ জহীর এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি আমার দায়িত্ববোধ থেকেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সমাহিত শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবর চিহ্নিত করার কাজ শুরু করি। পরে সরকার এগিয়ে এসেছে। কাজটিকে একটি ছাঁচে ফেলে এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কারণ এখানে দুটি দেশ জড়িত। ভারতের একাধিক প্রদেশ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মুক্তিযোদ্ধাদের কবর চিহ্নিত করার কাজ শেষ পর্যায়ে। এখন তাঁদের দেহাবশেষ কিভাবে ফিরিয়ে আনা হবে সেই কৌশল ঠিক করা হচ্ছে। আমি যেসব কবর চিহ্নিত করেছি সেগুলো প্রকৃতই মুক্তিযোদ্ধাদের কি না, তা ভারত সরকার পরীক্ষা করেছে। এতে দেখা গেছে, আমার চিহ্নিত ৯৫ ভাগ কবরই বাংলাদেশি মুক্তিযোদ্ধাদের। আরো নতুন নতুন কবর চিহ্নিত হচ্ছে।'
সেনাবাহিনীর সাবেক এ কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত সাজ্জাদ আলী জহীর জানিয়েছেন, একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধারা ভারতের মিত্র বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন। তাঁদের অধিকাংশ ক্যাম্পই ছিল ভারতের মাটিতে। তাই মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশের লাশ নিয়ে যাওয়া হয়েছে ক্যাম্পে। তারপর ক্যাম্পের আশপাশেই তাঁদের কবর দেওয়া হয়েছে। এখন এসব কবরেরই সন্ধান করা হচ্ছে। শিলং, গৌহাটি, ডাউকি, কুচবিহার, আমপালি, কুকিতলাসহ আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গে একশর বেশি স্পট এখন পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের কবর আছে। ডাউকিতে ২৫১টি কবরের সন্ধান মিলেছে। শিলংয়ের মিলিটারি হসপিটালের কাছে ৫১টি কবর আছে। স্থানীয়ভাবে মপ্রেম কবরস্থান হিসেবে জায়গাটি পরিচিত। মপ্রেম আদীবাসী শব্দ। এর অর্থ পাথর। এটি পাথরবেষ্টিত কবরস্থান। শিলংয়ের বেওয়ারিশ লাশ দাফন-কাফন কমিটির প্রধান আহমদ হোসেন এবং তাঁর ভাই আফজাল হোসেন এসব কবরের তত্ত্বাবধান করছেন। পরিবারটি ১৯৭১ সাল থেকেই নিষ্ঠার সঙ্গে এ কাজটি করছে।
সাজ্জাদ জহীর বলেন, 'কুমিল্লার কাছাকাছি বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের নো ম্যান্স ল্যান্ডের ভারতীয় অংশে ২৮২টি কবর চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০০৯ সালে জেনারেল হারুন আল রশীদের সহায়তায় এই কবরগুলো চিহ্নিত করি। এ কাজে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ও বাংলাদেশ বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি) দারুণভাবে সহায়তা করেছে। মেঘালয়ের পশ্চিম গারো পর্বতের কাছে আমপালি গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের চার থেকে পাঁচ শ কবর আছে। সিলেট সীমান্তের তামাবিল চেকপোস্টের কাছে নো-ম্যান্স ল্যান্ডে ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে সমাহিত করা হয়েছে।'
গত জুনে ভারতে সমাহিত মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধি চিহ্নিত করতে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি কমিটি গঠন করে। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব গোলাম মোস্তফার নেতৃত্বে কমিটিতে রয়েছেন সাজ্জাদ জহীর, একই মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ইনামুল কাদের খান এবং উপসচিব সাইফুল হাসান বাদল। এ কমিটি ভারতের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে বৈঠক করেছে। এ কমিটি গঠনের কারণ হচ্ছে, কাজী সাজ্জাদ জহীর ব্যক্তিগতভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের কবর খোঁজার কাজটি করেছেন। তাঁর এ চেষ্টাকে সহায়তা দিতেই সরকার কমিটি করেছে। ভারত সরকারও এ কমিটিকে সহায়তা দিতে নোডাল অফিসার নিয়োগ করেছে। প্রাদেশিক সরকারের যুগ্মসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তারা নোডাল অফিসার হিসেবে কাজ করছেন।
মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বাংলাদেশে অবস্থানরত শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবার যদি তাঁদের স্বজনদের দেহাবশেষ আনতে না চান, তাহলে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের মরদেহ আনা হবে। ভারতে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সমাহিত এবং স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য ব্রাক্ষ্মণবাড়িয়ার কসবায় তিন একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। সিআইডির ফরেনসিক বিভাগের সহায়তায় ভারতে সমাহিত মুক্তিযোদ্ধাদের হাড়গোড় পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁদের পরিচয় শনাক্ত করা হবে। এ ব্যাপারে কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। ডিএনএ টেস্টের কাজটি সহজ নয় জানিয়ে সাজ্জাদ জহীর বলেন, কার কবর সেটা চিহ্নিত করতে অবশ্যই ডিএনএ টেস্ট করতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যদের সহায়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন সহযোগী ডানিডা ডিএনএ টেস্টে সহায়তা দিতে আগ্রহী।
শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের মরদেহ ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধিনিষেধ আমলে নিয়েছেন কি না, জানতে চাইলে সাজ্জাদ জহীর বলেন, ইসলামী ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের মতামত নেওয়া হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, যেখানে কবর রয়েছে, সেই কবরটার যদি অমর্যাদা না হয়, তাহলে সেটি স্থানান্তর করা যাবে। পানিতে ভেসে যাওয়ার ঝুঁকি থাকলে বা কেউ যদি কবরের পাশে গিয়ে দোয়া করতে চান এবং সেখানে বাধা দেওয়া হয় তাহলে কবর স্থানান্তর করা যাবে। এ ছাড়াও কবর স্থানান্তর করার আরো কিছু উপযুক্ত কারণ আছে। এসব কারণ আমলে নিয়েই কবর স্থানান্তর করা হবে। কিভাবে কবরগুলো চিহ্নিত করেছেন জানতে চাইলে সাজ্জাদ জহীর বলেন, 'ভারতে গিয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় যেখানে কবর দেওয়া হয়েছে সেই জায়গাগুলো চিহ্নিত করি। পরে স্থানীয় মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষক যাঁরা জানাজা পড়িয়েছেন, তাঁদের খুজে বের করি। তাঁরাই বলতে পারেন সঠিক খবর। এ ছাড়া স্থানীয় পুলিশে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরাও সহায়তা দিয়েছেন। এলাকার মুরব্বিরা তো রয়েছেনই। সেই সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসন, পঞ্চায়েত আমাকে সহায়তা করেছে।'
শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের দেহাবশেষ ফিরিয়ে আনার বিষয়ে এরই মধ্যে দুই দেশের সরকারপ্রধানের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। ২০০১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং যখন বাংলাদেশ সফর করেন তখন বিষয়টি তোলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা কমিটি শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের মরদেহ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়। এর আগে ২০০৬ সালের ২৫ জুন চারদলীয় জোট সরকার পাকিস্তানের করাচি থেকে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ ফিরিয়ে আনে। ২০০৭ সালের ১০ ডিসেম্বর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভারত থেকে ফিরিয়ে আনে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের মরদেহ। তাদের দেহাবশেষ নতুন করে মিরপুরের বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয়।
আজ থেকে ১০ বছর আগে সাজ্জাদ জহীর এ কাজটি শুরু করলে জাপানের নজরে আসে। পরে তাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত ১১ জনের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। আর যুক্তরাষ্ট্রের একটি দল তাদের একদল সৈনিকের সমাধিক্ষেত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে বলে জানা গেছে।
ভারত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের কবর স্থানান্তর প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শাহরিয়ার কবীর বলেন, সেখানে কবর সংরক্ষণ করা হয় না। তাই তাঁদের ফিরিয়ে এনে সমাহিত করতে পারলে সেটা জাতির জন্য অনেক বড় কাজ হবে। দেশবাসী শ্রদ্ধা জানাতে পারবে। পরিবারের সদস্যরা কবরের পাশে যেতে পারবেন।
http://www.kalerkantho.com/?view=details&type=gold&data=news&pub_no=1193&cat_id=1&menu_id=13&news_type_id=1&index=0
 বিপ্লব রহমান | 127.18.231.63 | ২৬ মার্চ ২০১৩ ০৯:০৭582558
বিপ্লব রহমান | 127.18.231.63 | ২৬ মার্চ ২০১৩ ০৯:০৭582558- সাজ্জাদ আলী জহির
শহীদ সমাধির খোঁজে নিরলস ১০ বছর
পার্থ সারথি দাস
তিনি হাঁটছেন। হাঁটছেন বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামে। কখনো বা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের শিলং বা আগরতলার পথে পথে ঘুরছেন। খুঁজে ফিরছেন একাত্তরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধি। বিরামহীন চলছে এই সন্ধান, এই ক্লান্তিহীন পথচলা। এই মানুষটি হলেন কাজী সাজ্জাদ আলী জহির। একাত্তরে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে 'বীরপ্রতীক' খেতাব লাভের পরও লড়াই তাঁর থামেনি। দেশের জন্য অসামান্য এ ভূমিকার জন্য সাজ্জাদ জহির এবার লাভ করলেন স্বাধীনতা পদক।
মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয়, সাজ্জাদ আলী জহির পাকিস্তানে। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য জম্মু-কাশ্মীর সীমান্ত পার হয়ে এসে যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। সেনাবাহিনী ছেড়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ায় পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী কোর্ট মার্শাল করে তাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করে।
৬৩ বছরে এসেও সাজ্জাদ চিরসবুজ। গত রবিবার রাতে রাজধানীর গুলশানের বাসায় তিনি তুলে ধরেন তাঁর ছুটে চলার এই অনন্ত উৎসাহের কথা। মহান একটি কাজ নিয়ে সদা ব্যস্ত সাজ্জাদ কাজের ফাঁকেই সেদিন কালের কণ্ঠের সঙ্গে কথা বলছিলেন।
ভারতের বিভিন্ন রাজ্য, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত, নো ম্যান্স ল্যান্ড- সবখানেই তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন একাত্তরে যুদ্ধে নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তিদের। সন্ধান করছেন শহীদদের কবর। প্রায় ১০ বছর ধরে এ অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকার কথা জানিয়ে সাজ্জাদ বলেন, 'এটা আমার দায়িত্ব। অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা পরিবার শহীদের দেহাবশেষের কোনো হদিস পায়নি। এর চেয়ে বড় দুঃখজনক আর কী হতে পারে?'
কাজী সাজ্জাদ আলী জহিরের লেখা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অগুনতি বইয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধ। এর মধ্যে শুধু বাংলা একাডেমী থেকেই প্রকাশিত হয়েছে ২৬টি গ্রন্থ। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে দেশের গ্রাম থেকে গ্রামে ছুটে চলেছেন তিনি। এ যাবৎ দেড় হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরেছেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। দিয়েছেন টানা বক্তৃতা। মসজিদের হাজার হাজার ইমাম ও মুয়াজ্জিনের সামনেও তিনি পাঠ করছেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।
সাজ্জাদ বললেন, 'গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় গিয়েছি। ইমামদের সামনেও পাঠ করছি ইতিহাস।' তিনি আরো বলেন, 'বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করার সুবাদে অনেকে আমাকে চিনতে পারে। আমি তৃণমূলে গিয়ে এ-ও বুঝতে পারি, অনেক মুক্তিযোদ্ধা পরিবার এখনো শহীদদের কবর কোথায় জানে না। তারা দেহাবশেষটা অন্তত পেতে চায়। তাদের ভেতরে বছরের পর বছর এ প্রত্যাশা কেঁদে মরে।'
সাজ্জাদ জহির কালের কণ্ঠকে বলেন, '১০ বছর ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি। ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তে দিনের পর দিন হেঁটেছি। মুক্তিযুদ্ধের সময় অসংখ্য সহযোদ্ধা শহীদ হয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের লাশ পেলে পাক সেনারা সেগুলো নিশ্চিহ্ন করে দিত। কিন্তু আমাদের ওপরের নির্দেশ ছিল- শহীদ যোদ্ধাদের লাশগুলো যেকোনোভাবে যেন আমরা নিয়ে আসি।'
সাজ্জাদ জহিরের কাছ থেকে জানা গেল, ভারতের মিজোরাম ছাড়া অন্য সব রাজ্য থেকে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। ভারতের আসাম, মেঘালয়সহ বিভিন্ন রাজ্যে পরিভ্রমণ করে সেখানে স্থানে স্থানে শহীদদের শেষ স্মৃতিচিহ্ন আবিষ্কার করেছেন সাজ্জাদ। তিনি বলেন, 'কোথাও হাজারখানেক কবর পাওয়া গেছে, কোথাও বা ২০০ কবর। মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে শরণার্থীদের কবরও আছে। ভারতের নদী-নালার পাশে অনেক ক্যাম্প গড়ে উঠেছিল। কারণ পানি পাওয়া যায়, এমন স্থানেই ক্যাম্পগুলো ছিল। ক্যাম্পগুলোর পাশেই কবর দেওয়া হতো শহীদদের।'
নদীভাঙনের কারণে অনেক কবর আবার চিহ্নহীন জানিয়ে সাজ্জাদ বলেন, 'আমি মনে করি, এসব চিহ্নহীন কবরস্থান আমরা চিহ্নিত করতে পারি। সমাধিসৌধ নির্মাণ করতে পারি। এ লক্ষ্য সামনে রেখেই এগোচ্ছি।'
অনুসন্ধানের সূচনা কিভাবে হলো জানিয়ে সাজ্জাদ জহির বলেন, 'বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের কবর খুঁজতে গিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম। ভারতের হাসপাতালগুলো থেকে আমরা এখনো তালিকা পাইনি। ভারতের সব সীমান্ত এলাকায় হেঁটেছি।' কাজটি যে বড় সমস্যাসংকুল এ কথাও উল্লেখ করেন তিনি। বলেন, 'যেসব এলাকায় শহীদের কবর আছে সেগুলোর বিষয়ে বিভিন্ন কারণে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। কবর নিয়ে বেশি কথা বলা যায় না। বেশি নড়াচড়া করা যায় না। তথ্য পাওয়ার কাজটিও করতে হয় সতর্কতার সঙ্গে। ভারতের কোথাও শহীদদের কবর দেওয়ার স্থানটি ইট দিয়ে ঘিরে রেখেছে এলাকাবাসী। ভারতে অনেক এলাকার লোকজন আমাকে কবর খুঁজতে দেখে খুশি হয়ে বলেছে- এত বছর কেউ এলো না, আপনি এলেন।'
মুক্তিযোদ্ধা লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার চৌসই গ্রামের সন্তান। জন্ম ১৯৫১ সালের ১১ এপ্রিল। বাবা কাজী আবদুল মুত্তালিব। মা কাজী নুরুন্নাহার বেগম। ১৯৭১ সালে তাঁর বয়স ছিল বিশের ঘরে। পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি থেকে স্নাতক ডিগ্রি ও সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেছিলেন। একাত্তরে ৪ নম্বর সেক্টরের অধীনে দ্বিতীয় গোলন্দাজ বাহিনীকে সংগঠিত করেন তিনি সিলেট অঞ্চলে।
http://www.kalerkantho.com/?view=details&type=gold&data=news&pub_no=1193&cat_id=1&menu_id=13&news_type_id=1&index=1
 বিপ্লব রহমান | 127.18.231.63 | ২৬ মার্চ ২০১৩ ০৯:১০582559
বিপ্লব রহমান | 127.18.231.63 | ২৬ মার্চ ২০১৩ ০৯:১০582559- বিশেষ লেখা
স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের দায়িত্ব
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
১০ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করে এই অঙ্গীকার করেন যে জাতিসংঘের এক সদস্য হিসেবে তাঁদের ওপর যে কর্তব্য ও দায়িত্ব বর্তেছে, তা তাঁরা পালন করবেন এবং জাতিসংঘ সনদ মেনে চলবেন। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে একটা স্বতোৎসারিত ও স্বাভাবিক রণধ্বনি।
মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভের পর স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় দায়ভার ছিল আত্মশাসনের দলিল রচনা করা। অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এক বছরের মধ্যে সংবিধান প্রবর্তন করা হয়। প্রবর্তনকালে সংবিধানের প্রস্তাবনায় বাংলাদেশের জনগণ এই অঙ্গীকার করেন যে, 'যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;
'আমরা আরো অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে;
'আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সংগতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেই জন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য।'
সংবিধান প্রবর্তনের সময় আমাদের সমাজপতিদের মধ্যে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সব দায়িত্ব পালনের ও রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের দেখভাল করার লোকের বড় অভাব ছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটি লক্ষ করে হেনরি কিসিঞ্জার নাম দিয়েছিল 'একটি তলাহীন ভিক্ষাপাত্র'। সুখের বিষয়, দেশটি নিজের পায়ে দাঁড়াতে তেমন সময় নেয়নি। দাতাদের অর্থে দেশ চলেনি, দেশ চলে নিজের সম্পদেই। বার্ষিক কর্মসূচির মাত্র ১০ শতাংশ অর্থের জোগান দেয় দাতাগোষ্ঠী। বাংলাদেশ কোনো দিন ঋণ পরিশোধে খেলাপ করেনি। আমাদের অবস্থা গ্রিস, সাইপ্রাস, স্পেন বা ইতালির মতো হয়নি। আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিচ্ছিন্নভাবে ঘটলেও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়নি। বাংলাদেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনকে ব্যাপৃত হতে হয়নি। আমাদের কোনো নেতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের কেউ অভিযোগ আনেনি।
এই পরিস্থিতিতে আমাদের রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্বগুলো সম্পর্কে আমাদের অনুক্ষণ সজাগ থাকতে হবে। প্রতিটি সভ্য রাষ্ট্রের দেশের অভ্যন্তরে নাগরিক-অনাগরিক, দেশি-বিদেশি সকল মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আইনের সম্মুখে প্রত্যেকে যে নিরাপত্তা পেতে অধিকারী, তা ধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে রাষ্ট্রকে সংরক্ষণ করতে হবে। রাষ্ট্রকে শুধু মানুষ নয়, পরিযায়ী যেসব পশুপাখি আশ্রয় নেয়, তাদেরও নিরাপত্তা বিধান করতে হবে- বললে চলবে না, আমরা তো তাদের জিয়াফত করে নিয়ে আসিনি। রাজনৈতিক কারণে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে কেউ এ দেশে আশ্রয় চাইলে শরণার্থীদের প্রতি আমাদের কর্তব্য তাদের সাধ্যমতো দেখভাল করা।
১৮০০ সালে পৃথিবীতে ২৯টি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল, ইউরোপে ১০টি এবং এশিয়ায় ৯টি। এখন জাতিসংঘে স্বাধীন রাষ্ট্র সদস্যের সংখ্যা ১৯৪। এসব রাষ্ট্রের কর্তব্য কেবল পুরনো আমলের রেওয়াজমতো মাত্র দ্বিকর্মে সীমিত নয়, কেবল দেশের অভ্যন্তরে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং বহিরাক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করলেও দায়িত্ব শেষ হবে না। আজ রাষ্ট্রের দায়িত্ব বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলের কারণে এবং মানবাধিকার মানুষের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বড় প্রসারিত হয়েছে। শুধু জীবন, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সুখের অন্বেষণে প্রত্যেক নাগরিক যেন স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী আরাধ্য করতে পারেন, তার জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র যে নিরাপত্তা বিধান করবে তা আজ অপরিহার্য প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আগের আমলে রাষ্ট্রের অর্থ, শিক্ষা, সংস্কৃতি বা পরিবেশবিষয়ক মন্ত্রীদের তেমন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় ছিল না। এখন শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা বিশ্বের দায়িত্ব সমবেতভাবে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো নিজেদের স্কন্ধে তুলে নিয়েছে।
আমি স্বাধীনতার দায়ভার প্রবন্ধে বলি, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রচিন্তায় আজ সার্বভৌম রাষ্ট্রের দ্বিবিধ দায়িত্বের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। দেশের বাইরে অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দেশের অভ্যন্তরে নাগরিকের মর্যাদা ও মানবিক অধিকারের প্রতি যথার্থ ও কার্যকরভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। যেসব রাষ্ট্র এই দায়িত্ব পালন করতে পারবে না, সেখানে 'ন্যায্য কারণে' অন্য রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারবে কি না সে প্রশ্ন আজ সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে আলোচিত হচ্ছে। সামরিক হস্তক্ষেপ নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ ব্যাপার। রাষ্ট্রের স্বেচ্ছা-কৃতকর্মে, অকারণে, গাফিলতিতে ও অসামর্থ্যের কারণে যে দেশে সাধারণ মানুষ মারাত্মক ক্ষতি, ব্যাপক প্রাণহানি ও গণহত্যাসম পরিস্থিতির সম্মুখীন, সেখানে সামরিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারটা বিবেচিত হতে পারে। বসনিয়া, রুয়ান্ডা ও কসোভোতে এমন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। গৃহযুদ্ধজনিত দুর্ভিক্ষের জন্য সোমালিয়ায় যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সে পরিপ্রেক্ষিতও আলোচিত হতে পারে। তবে সাধারণ মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্বাচিত সরকারকে অভ্যুত্থানে অপসারণ করা হলে সামরিক হস্তক্ষেপের ওপর সহসা নির্ভর করা অসমীচীন হতে পারে। হস্তক্ষেপের ফলে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না এবং তা আয়ত্ত বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে কি না, সেই সম্ভাবনার কথা সর্বদা স্মরণে ও বিবেচনায় রাখতে হবে। এ ব্যাপারে এটাও স্মর্তব্য যে জাতিসংঘ একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যা এই অসাধারণ পরিস্থিতিতে যখন একটা রাষ্ট্র তার দায়ভার বহন করতে ব্যর্থ হচ্ছে, তখন আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। যেকোনো শক্তিধর রাষ্ট্রের একক হস্তক্ষেপে আন্তর্জাতিক সমাজব্যবস্থা দারুণভাবে বিঘ্নিত হতে পারে।
আজকের দুনিয়ায় 'ন্যায্য যুদ্ধ', 'হস্তক্ষেপের অধিকার', 'শান্তির সড়কের নকশা', 'প্রশাসন পরিবর্তন' ইত্যাকার গালভরা কথা স্বাধীনতার দায়ভার সম্পর্কিত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর না দিয়ে নতুন নতুন প্রশ্নের অবতারণা করছে।
দরিদ্র, দুস্থ ও দুর্বল বাংলাদেশ আজ আমাদের এক টানাটানির সংসার। নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে শুধু বাঁচা বা জীবনধারণ নয়, মেধা ও বুদ্ধি খাটিয়ে নিজেদের মানসম্মানও বজায় রাখতে হবে। স্বাধীনতার দায় মেটাতে সংকল্পবদ্ধ ও বদ্ধপরিকর হলে তার দায়ভার তেমন অসহনীয় ও দুর্বহ নাও মনে হতে পারে। নাই নাই করেও দেশে নানা সুলক্ষণ বিরাজ করছে। হতাশায় মুহ্যমান হওয়ার কোনো কারণ নেই।
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত ২৪ দিনে দেশের ৩২টি জেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলায় অন্তত ৩১৯টি মন্দির, বাড়ি, দোকানঘরে ভাঙচুর ও অগি্নসংযোগ করা হয়। এর মধ্যে ৭১টি মন্দির, ১৫২টি দোকান, ৯৬টি বসতবাড়ি ছিল। অধিকাংশ ঘটনা ঘটেছে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে, যেখানে স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়নি। মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের হিসাবে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দেড় হাজারের বেশি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ নিয়ে আমাদের জাতীয় সংসদ ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশকে যাঁরা মডারেট মুসলিম দেশ হিসেবে পিঠ চাপড়ান, তাঁরাও বিব্রত। গত ২৪ দিনের ঘটনায় সংখ্যালঘু ব্যক্তিরা ২৬টি মামলা করেছেন। পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেছে ১৭টি। এসব মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন ১৮৯ জন। এসব হামলায় জামায়াত জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছে। বিরোধী দলের অভিযোগ, সরকারি দলের লোক এসব কাজ করেছে তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী। সরকার নিজের সুনাম নষ্ট হয়, এমন কাজ করবে বলে মনে হয় না, তবে, শান্তিরক্ষার দায়িত্ব পালনে সরকার দক্ষতার পরিচয় দেয়নি। হতে পারে এসব ঘটনা অভাবিত ও আকস্মিক এবং দৈনন্দিন দায়িত্ব-দুশ্চিন্তার বহির্ভূত ছিল।
দেশের লোক আশা করে, গত ৪২ বছরে বাংলাদেশ যে কয়বার সমূহ বিপর্যয়ের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে, সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমান রাজনৈতিক দুর্যোগাবস্থা কাটিয়ে সে আবার দৃপ্তপদে সম্মুখে এগিয়ে যাবে। জয় বাংলা!
লেখক : তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা
http://www.kalerkantho.com/?view=details&type=gold&data=news&pub_no=1193&cat_id=1&menu_id=13&news_type_id=1&index=2
 বিপ্লব রহমান | 127.18.231.63 | ২৬ মার্চ ২০১৩ ০৯:১৩582560
বিপ্লব রহমান | 127.18.231.63 | ২৬ মার্চ ২০১৩ ০৯:১৩582560- মুক্তিযুদ্ধ
একাত্তরে সংবাদপত্রের ভূমিকা এক মলাটে
নিজস্ব প্রতিবেদক
যুদ্ধ ও গণমাধ্যমের সম্পর্ক সব সময়ই সাংঘর্ষিক। যেকোনো যুদ্ধে প্রথম মৃত্যু হয় সত্যের। সত্যের প্রতীক ধরা হয় সংবাদপত্রকে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রথম শহীদদের অন্যতম এ দেশের সংবাদপত্রগুলো। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশের সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল দ্বিধান্বিত। কোনো কোনো সংবাদপত্র যেমন সামরিক বিধিনিষেধ এবং শাসকের বন্দুকের নলের মুখে সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশে হয়ে উঠেছিল কৌশলী, তেমনি কিছু সংবাদপত্র এসবের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। আর কিছু সংবাদপত্র ছিল মতাদর্শিকভাবেই মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাবিরোধী। সে সময় মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এসব সংবাদপত্রের ভূমিকা কী ছিল, কিভাবে তারা মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিরোধিতা করেছিল মূলত তা নিয়েই একটি বিশাল বই প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট। দুলাল চন্দ্র বিশ্বাসের সম্পাদনায় বইটির শিরোনাম করা হয়েছে 'সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা : একাত্তরের ঘাতকদের জবান জুলুম ষড়যন্ত্র চিত্র'।
বইটিতে রয়েছে ১১টি অধ্যায়- 'রিপোর্ট ও সম্পাদকীয় বিষয়বস্তু', 'রিপোর্ট : দৈনিক সংগ্রাম', 'রিপোর্ট : দৈনিক পাকিস্তান/দৈনিক বাংলা', 'রিপোর্ট : ইত্তেফাক', 'রিপোর্ট : পূর্বদেশ', 'সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় : দৈনিক সংগ্রাম', 'চিঠি, বেতার কথিকা, সাক্ষাৎকার ও টিভি ভাষণ : দৈনিক সংগ্রাম', 'সম্পাদকীয় : দৈনিক পাকিস্তান', 'সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় : দৈনিক পূর্বদেশ', 'চিঠি : দৈনিক পূর্বদেশ' ও 'সম্পাদকীয় : ইত্তেফাক'। বইটিতে বলা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধকালীন দৈনিক ইত্তেফাক ছিল বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রধান কণ্ঠস্বর। দৈনিক পাকিস্তান পরিবেশন করে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ। অন্যদিকে দৈনিক সংগ্রাম ছিল স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র। তাই বইটির প্রায় অর্ধেক পৃষ্ঠাজুড়েই রয়েছে এ পত্রিকার রিপোর্ট, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, চিঠি, বেতার কথিকা, সাক্ষাৎকার ও টিভি ভাষণ। যুদ্ধকালীন হানাদারদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, লুটপাট, ধর্ষণ, অগি্নসংযোগের কোনো খবরই ছাপা হয়নি এ পত্রিকায়। বরং এতে হানাদার বাহিনীর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে নিয়মিত খবর প্রকাশ করা হতো। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর কোনো পত্রিকা বের হতে না পারলেও বেরিয়েছিল সংগ্রাম। পত্রিকাটি সব সময় প্রমাণের চেষ্টায় থাকত, দেশে কোনো গোলযোগ নেই, পরিস্থিতি স্বাভাবিক। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসী ভূমিকার কথা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হতো। মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতাকামীদের আখ্যায়িত করা হতো রাষ্ট্রবিরোধী, ভারতের দালাল, বিচ্ছিন্নতাবাদী দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারী হিসেবে।
দৈনিক পূর্বদেশও ছিল স্বাধীনতাবিরোধী স্রোতের মতাদর্শে বিশ্বাসী। মালিক পক্ষের প্রচণ্ড বিরোধিতা ও চূড়ান্ত অসহযোগিতার মুখে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সাংবাদিকরা স্বাধীনভাবে নিজেদের প্রকৃত চিন্তা-চেতনা প্রকাশ করতে পারেননি। ফলে পত্রিকাটি আদ্যোপান্ত পাকিস্তানি হানাদারদের তোষামোদকারী ন্যক্কারজনক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।
দৈনিক সংগ্রামের কয়েকটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল এ রকম- 'পূর্ব পাক জামায়াতের মজলিসে আমলার দ্বিতীয় দিনের প্রস্তাব : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমেই পাকিস্তান শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হবে' (১২ জানুয়ারি ১৯৭১)। 'মওলানা মওদুদীর ঘোষণা : কোন শক্তিই ইসলামী বিপ্লব রোধ করতে পারবে না' (১৩ জানুয়ারি ১৯৭১)। "শেখ সাহেব কি 'গান্ধী' সাজবেন" (২০ জানুয়ারি ১৯৭১)। 'পূর্ব পাকিস্তানের শহর ও পল্লী এলাকায় শান্তি অব্যাহত রয়েছে' (৩ এপ্রিল ১৯৭১)। অধ্যাপক গোলাম আযমের বেতার ভাষণ : '৭ কোটি পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্য নিয়ে জঘন্য খেলা বন্ধ কর' (১২ এপ্রিল ১৯৭১)। এ পত্রিকাটির কয়েকটি সম্পাদকীয়র শিরোনাম ছিল- 'জনতা পাকিস্তান চায়' (১৫ এপ্রিল ১৯৭১)। 'স্বাভাবিক জীবনযাত্রা' (৭ এপ্রিল ১৯৭১)। 'ভারতীয় অপপ্রচারের ব্যর্থতা' (৮ এপ্রিল ১৯৭১)। 'দুষ্কৃতকারীদের ধরিয়ে দিন' (৪ মে ১৯৭১)
দৈনিক পূর্বদেশের কয়েকটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল- 'ছ'দফা ছিল জনগণকে প্রতারণার আবরণ মাত্র- খান এ সবুর' (৬ এপ্রিল ১৯৭১)। 'বিশ্ব জানে ভারতই পাকিস্তানের একমাত্র শত্রু : জামায়াতে ইসলামী' (৮ এপ্রিল ১৯৭১)। 'বিচ্ছিন্নতাই ছিল মুজিবের লক্ষ্য- কাসুরী (১৯ এপ্রিল ১৯৭১)
দৈনিক পাকিস্তানের কয়েকটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল এমন- 'শান্তি ও সংহতি কমিটির সভা : দেশদ্রোহীদের প্রতি কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান' (১৮ মে ১৯৭১)। 'জামায়াত নেতৃবৃন্দের আহ্বান : দেশের মাটি থেকে পাকিস্তানবিরোধীদের উৎখাত করুন' (২০ মে ১৯৭১)। 'জনগণের প্রতি জামায়াত নেতৃবৃন্দ : ভারতীয় চক্রান্ত থেকে দেশকে রক্ষা করুন' (২১ মে ১৯৭১)।
৬৪৭ পৃষ্ঠার এ বইটির মূল্য ৫০০ টাকা। প্রেস ইনস্টিটিউটের সেমিনার কক্ষে গত শনিবার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু।
http://www.kalerkantho.com/index.php?view=details&type=gold&data=news&pub_no=1193&cat_id=1&menu_id=14&news_type_id=1&index=1#.UVEW-RdHLVwhttp://www.kalerkantho.com/index.php?view=details&type=gold&data=news&pub_no=1193&cat_id=1&menu_id=14&news_type_id=1&index=1#.UVEW-RdHLVw
 বিপ্লব রহমান | 127.18.231.53 | ২৬ মার্চ ২০১৩ ২০:২৮582561
বিপ্লব রহমান | 127.18.231.53 | ২৬ মার্চ ২০১৩ ২০:২৮582561- মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দাবি বীরাঙ্গনাদের
মামুনুর রশীদ ও গোলাম মুজতবা ধ্রুব বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম
Published: 2013-03-26 13:09:06.0 Updated: 2013-03-26 13:14:01.0
একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নির্যাতিত নারীরা মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি চেয়েছেন সরকারের কাছে।
সিরাজগঞ্জ থেকে আসা ১০ জন বীরাঙ্গনা মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৫টায় শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানান।
দেশের স্বাধীনতার জন্য যেসব নারী নিজেদের সম্ভ্রম হারিয়েছেন, তাদের ‘বীরাঙ্গনা’ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত সেইসব নারীদের পক্ষে প্রজন্ম চত্বরের সমাবেশে দেয়া বক্তব্যে বীরাঙ্গনা সূর্য বেগম একাত্তরের সব যুদ্ধাপরাধীর ফাঁসির দাবি জানান।
সেইসঙ্গে তিনি নিজেদের [মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের] মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানিয়ে বলেন, “আমরাও মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে স্বীকৃতি চাই। আমার ছেলে যেন বলতে পারে যে, সে একজন নারী মুক্তিযোদ্ধার ছেলে।”
সমবেত জনতা তখন স্লোগান দিতে থাকে, ‘বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি- দিতে হবে, দিতে হবে’।
বীরাঙ্গনা সূর্য বেগম আরো বলেন, “আমার বঙ্গবন্ধু থাকলে আজ আমাদের কোনো কষ্ট থাকত না। একাত্তরে তিনিই আমাদের সবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।
“আমাদের মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, মা-আপনারা চিন্তা করবেন না। আমি বেঁচে থাকতে আপনাদের কোনো বিপদ হবে না।”
একথা বলতে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেলেন।
সমাবেশে আসা বীরাঙ্গনা রাহেলা বাওয়া বলেন, “যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি ছাড়া কোনো বিচার আমরা মানি না। বাংলাদেশে আমরা ওদের দেখতে চাই না, আমরা মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি চাই।”
সিরাজগঞ্জ থেকে আসা অন্য বীরাঙ্গনারা হলেন-রাহেলা বেগম, করিমন বেগম, নূরজাহান, রাজু বালা, আয়েশা বেগম, শামসুন্নাহার, রহিমা এবং জোসনা।
সাদা শাড়ি পরে সমাবেশ মঞ্চের সামনেই অবস্থান নেন বীরাঙ্গনারা।
বিকালে সমাবেশ শুরুর কিছুক্ষণ পরেই সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু মঞ্চে বীরঙ্গনাদের পরিচয় করিয়ে দেন।
এর আগে মঞ্চে গণসংগীত পরিবেশন করে ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠী।
http://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article606590.bdnews
 বিপ্লব রহমান | 127.18.231.63 | ২৮ মার্চ ২০১৩ ১০:২৮582562
বিপ্লব রহমান | 127.18.231.63 | ২৮ মার্চ ২০১৩ ১০:২৮582562- কালরাত্রি
মেঘনাগুহ ঠাকুরতা
_________________________________________
১৯৭১ সালে আমি হলিক্রস স্কুলের ক্লাস টেনের ছাত্রী। আমার বাবা জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ছিলেন জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট এবং ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক। মা বাসন্তী গুহঠাকুরতা ছিলেন গেণ্ডারিয়া হাইস্কুলের হেড মিস্ট্রেস। আমরা থাকতাম জগন্নাথ হলের পূর্ব পাশের কম্পাউন্ডের নিচতলায়। মার্চের প্রথমেই ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা এলো_ সংসদ অধিবেশন বসবে না। তখনই ঢাকার মানুষজন রাস্তায় নেমে আসে। আমাদের বাসা ছিল হলের পূর্ব পাশে, সেখান থেকে শহীদ মিনারের পুরোটাই দেখা যেত। মার্চের ১ তারিখ থেকেই দেখেছিলাম ছাত্র-জনতা প্রতিদিনই শহীদ মিনারে একত্রিত হতো, মিছিল করত। ইয়াহিয়া খানের বক্তব্যের প্রতিবাদে তারা জোর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিতে লাগল। এবং ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণার পর অবস্থার আরও পরিবর্তন ঘটল। সবাই বন্দুক, লাঠি, দাসহ যার যার সহায় নিয়ে রাস্তায় এসে মিছিল করত। এককথায় বলা যায়_ মার্চ মাসজুড়েই রাজনৈতিক এবং জনগণের অবস্থা ছিল অত্যন্ত অশান্ত এবং অস্থির। এর মাঝে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। সবাই যে যার মতো ঢাকা ছাড়তে লাগল। ইউনিভার্সিটিতে প্রায় প্রতিটি আবাসিক হলের ছাত্ররা হল ত্যাগ করতে লাগল। বাবার অনেক সহকর্মীকেও দেখেছি ঢাকা ছেড়ে নিরাপদ অবস্থানে চলে যেতে। বাবাকেও অনেকে বলতেন_ ঢাকায় থেকে লাভ নেই। স্ত্রী এবং মেয়ে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যান। আমাদের কম্পাউন্ডে যেসব শিক্ষক থাকতেন তাদের অনেকেই চলে গিয়েছিলেন। অনেকে আবার দরজায় তালা লাগিয়ে ভেতরে অবস্থান করতেন। বাবা মাকে বলতেন আমাকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার জন্য। কিন্তু মা তাতে রাজি হননি।
২৫ মার্চ রাত ১২টা নাগাদ গোলাগুলির আওয়াজ পাওয়া গেল। ধীরে ধীরে এর মাত্রা বাড়তে লাগল। গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দে আমরা কিছুটা ভড়কে গিয়েছিলাম। আমরা সবাই এক জায়গায় রুমের ফ্লোরে শুয়ে পড়ি। মা এক সময় জানালার পর্দা সরিয়ে দেখতে পেলেন এক বহর সেনা জিপ আমাদের কম্পাউন্ডের সামনে এসে দাঁড়াল। তারা পেছন দিক থেকে আমাদের বাসার দরজায় জোরে জোরে কড়া নাড়তে লাগল। এ ছাড়াও অন্য বাসার লোকজনকেও ডেকে তোলা হলো। এক পাকিস্তানি সৈন্য এসে বাবা সম্পর্কে জানতে চাইল। বাবা বেরিয়ে আসার পর সৈন্যটি জানতে চাইল- 'আপ প্রফেসর সাহাব হ্যায়?' বাবা উত্তর করলেন_ হ্যাঁ। তখন সৈন্যটি বলল, 'আপকো হাম লে জায়েঙ্গে।' বাবা এর কারণ জানতে চাইলেন। কিন্তু সৈন্যটি বাবাকে কোনো সদুত্তর না দিয়ে তার হাত ধরে বাইরে নিয়ে গেলেন। আমরা সর্বোচ্চ আশঙ্কা করেছিলাম, বাবাকে হয়তো অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে।
পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান মনিরুজ্জামান স্যার আামাদের উপরের তলায় থাকতেন তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে। তার বাসা থেকে তাকে, তার ছেলে, তার ভাই এবং বোনের ছেলেসহ বেশ কয়েকজনকে তারা নিচে নামিয়ে আনতে থাকে। এর পরই বিকট গুলির আওয়াজ পাই। বাইরে বেরিয়ে দেখি মনিরুজ্জামান স্যারসহ তার সঙ্গের সবাইকে সিঁড়ির নিচে এনে গুলি করা হয়েছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চারপাশ। অনেকেই মারা গেছেন। অনেকেই মৃত্যুযন্ত্রণায় পানি-পানি বলে কাতরাচ্ছেন। আমরা তখন তাড়াতাড়ি জগ-কলসি নিয়ে বের হয়ে এলাম। এ সময় প্রফেসর সাহেবের স্ত্রী কিংবা তার বোন কেউ একজন মাকে বললেন, আপনার স্বামীকেও গুলি করা হয়েছে।
আমরা বাবাকে তারপর ধরাধরি করে মনিরুজ্জামান স্যারদের লাশগুলোর উপর দিয়ে ভেতরে নিয়ে আসি। সেই রাতে চারদিক থেকে গুলির আওয়াজ শুনতে পাই। মাঝে একবার থেমে যায় আবার শুরু হয় গোলাগুলি। বাইরে কারফিউ চলছিল বিধায় বাবাকে নিয়ে হাসপাতালেও যেতে পারছিলাম না। কোনো ওষুধপত্র কিংবা ডাক্তার নেই। এর মাঝে দিনের বেলা পাকিস্তানি সৈন্যরা আবার এসেছিল মনিরুজ্জামান স্যারদের লাশগুলো নিয়ে যাওয়ার জন্য। ততক্ষণে তাদের বাসার লোকজন লাশগুলো তিন তলায় তাদের বাসায় নিয়ে গিয়েছিল। তারা আবার লাশগুলো টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে নিয়ে গেল জগন্নাথ হলে যে গণকবর খোঁড়া হয়েছিল সেখানে কবর দেওয়ার জন্য। ২৭ তারিখ সকালে কারফিউ ভাঙার পর রাস্তার কিছু সাধারণ মানুষের দ্বারা বাবাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাই। তখনও বাবা সচেতন এবং জীবিত। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তাররা জানান যে, 'ক্রিটিকাল ইনজুরি'র কারণে আর কিছুই করা সম্ভব নয়। বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কোনো সিটে তুলতে পারিনি। কারণ এত আহত মানুষ ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি হয়েছিল যে, কোনো আসনই ফাঁকা ছিল না। বাবাকে প্রথমে নিচে রাখা হয়। এর পর তার শিক্ষক পরিচয় পেয়ে তাকে আলাদা একটি বেডে স্থানান্তর করা হয়। বাবা সুচিকিৎসা পান, তিনি সুস্থ হয়ে উঠুন_ তখন সেটাই ছিল আমার একমাত্র চিন্তা। দেখতে পাচ্ছিলাম চারদিক থেকে অসংখ্য লাশ নিয়ে আসা হচ্ছিল রিকশা ভর্তি করে। লাশের মিছিলে ঢাকা মেডিকেলের পরিবেশ ভারি হয়ে গিয়েছিল। আমরা বাবার সঙ্গে হাসপাতালেই অবস্থান করতে লাগলাম। এর মাঝে ২৮ তারিখে ডিনামাইট দিয়ে শহীদ মিনার উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। হাসপাতালে আক্রমণ হবে_ এই আশঙ্কায় অনেক রোগীই হাসপাতাল ছেড়ে যেতে লাগল। ডাক্তাররাও জীবনের ভয়ে পালিয়ে গেলেন। শুধু আমরা থেকে গেলাম। চিকিৎসার অভাবে বাবা মারা যান ৩০ মার্চ তারিখে। তার পরেই আমাদের বেরিয়ে আসতে হয় বাবাকে ওভাবে রেখেই। আর্মি হাসপাতাল আক্রমণ করার ফলে তার মৃতদেহের সৎকার আমরা করতে পারিনি। পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলে মা গিয়েছিলেন মর্গে বাবার লাশ খোঁজ করতে। কিন্তু তিনি তার লাশ খুঁজে পাননি। পরে একজন থেকে শুনেছিলাম, বাবাকে মেডিকেল প্রাঙ্গণেই সমাহিত করা হয়েছে। কিন্তু এর কোনো ভিত্তি নেই।
সময় গড়াতে লাগল। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ জোরদার হতে শুরু করল। ধীরে ধীরে দেশ স্বাধীনতার দিকে এগুতে লাগল। অজস্র জীবন, ত্যাগ আর স্বজন হারানোর বেদনা নিয়ে একটা সময় দেশ স্বাধীনও হলো। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া মানুষরা আর ফিরে এলো না। তারা জানতে পারল না_ তাদের জীবনের বিনিময়েই এই দেশ আজ স্বাধীন। স্বাধীনতার অজর্নকে রক্ষায় সবাইকে একাত্ম হয়ে কাজ করার সময় এসেছে বর্তমানে।
http://www.samakal.com.bd/print_edition/details.php?news=29&action=main&menu_type=crorpathro&option=single&news_id=335295&pub_no=1355&type=
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ০৭ এপ্রিল ২০১৩ ২০:৩৪582564
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ০৭ এপ্রিল ২০১৩ ২০:৩৪582564- শেখ মুজিব গ্রেফতার এবং কথিত টেলিগ্রাম
হায়দার আকবর খান রনো
_________________________________
৫. উত্তাল মার্চ : ১৯৭১ সাল
১৯৭১ সালের পহেলা মার্চ ঢাকায় নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা। এই পরিষদই পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করবে। সেখানে শেখ মুজিবুর রহমান একাই সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করতে পারেন। জনগণের কাছে তিনি ওয়াদাবদ্ধ, ৬ দফা ভিত্তিক হবে সংবিধান। পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। ভুট্টো ৬ দফা মানতে রাজি নন। রাজি নয় পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী ও সেনাবাহিনী। তাই সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখলেন। এতে বিদ্রোহ করে উঠলো গোটা বাংলাদেশ। এমন বিদ্রোহ এই দেশে আমরা আগে কখনো দেখিনি। প্রশাসন সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়লো। শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশেই সব কিছু চলতে লাগলো। তিনি নিজ বাসভবন থেকে যেভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন, সেনাবাহিনী বাদে রাষ্ট্রের সকল প্রশাসন, ব্যাংক, অফিস-আদালত এবং জনগণ তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছে।
১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তিনি যে ভাষণ দিলেন তা ছিল ঐতিহাসিক এবং অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত। এই ভাষণের রেকর্ড এখন প্রায়ই শোনা যায়। এই বক্তৃতায় তিনি একদিকে সরকারকে কয়েকটি শর্ত দিলেন, অপরদিকে, শেষ বাক্যে তিনি বললেন, ‘এবারের সংগ্রামের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রামের মুক্তির সংগ্রাম।’ একদিকে, স্বাধীনতার ডাক, অপরদিকে, শাসনতান্ত্রিক উপায়ে আলোচনার পথ খোলা রাখলেন। বস্তুত, আলোচনা চললো। এদিকে, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের কয়েকজন তরুণ র্যাডিকাল নেতা স্বাধীনতার স্লোগান প্রকাশ্যেই দিচ্ছেন। স্বাধীনতার পতাকা পর্যন্ত উড়লো, এমনকি শেখ মুজিবের বাসভবনেও।
১১ মার্চ মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইলে এক বিশাল সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ মেনে চলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান রেখেছিলেন। আরো আগে, তিনি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের আওয়াজ তুলেছিলেন।
সেই সময় একটি কমিউনিস্ট সংগঠন ‘‘কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি’’ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। আমি নিজে এই সংগঠনের নেতৃত্বের একজন ছিলাম। টঙ্গি শিল্প এলাকায় আমাদের ভালো সাংগঠনিক ভিত্তি ছিল। টঙ্গির শ্রমিকদের ব্যাপক সমর্থনের কারণে, আমরা টঙ্গির কারখানাগুলোকে ব্যবহার করে বোমা বানাতাম। গ্রামাঞ্চলে আমাদের কৃষকের ঘাটি অঞ্চল সমূহে সেই সকল বোমা সরবরাহ করা হতো। শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীর এটাও এক চমৎকার দৃষ্টান্ত ছিল। ফেব্র“য়ারি মাসেই আমরা পার্টি কর্মীদের সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য প্রসস্তুত হতে বলি এবং গেরিলা যুদ্ধের কৌশলল সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি। আমাদের তৈরি হাতবোমা ঢাকায় মিলিটারি গাড়ির ওপরও নিক্ষেপ করা হয়। বিকট আওয়াজ হতো। কিন্তু কার্যকারিতা তেমন ছিল না। আমরা বিভিন্নভাবে কিছু বন্দুকও সংগ্রহ করি। তবে প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হলেই কেবল বোঝা গেল আমাদের সামরিক প্রস্তুতি কতো অপ্রতুল ছিল।
১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বিকেলে ‘কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির’ নামেই পল্টনে এক সভা আহ্বান করা হয়েছিল এবং এতে দুই লক্ষাধিক মানুষ জমায়েত হয়েছিল। আমাদের সাংগঠনিক শক্তি কিন্তু এতোটা ছিল না। পরিস্থিতির কারণেই সেদিন মানুষ জমায়েত হয়েছিল। ওই সভায় কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আনোয়ার খান জুনো, আতিকুর রহমান সালু ও আমি বক্তৃতা করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম, মুজিব-ইয়াহিয়া যে আলোচনা চলছে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমরা গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানকে পরাজিত করে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান রেখেছিলাম। সেই রাতেই পাকিস্তান আর্মি অতর্কিতে ঝাপিয়ে পড়েছিল নিরস্ত্র জনগণের ওপর। শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হলেন।
মার্চ মাসে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সেনাকর্মকর্তা শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। সামরিকভাবে কি করা উচিত, সেই নির্দেশ চেয়েছিলেন নেতার কাছ থেকে। কিন্তু নির্দেশ তারা পাননি। বস্তুত জাতিও কোন নির্দেশ পায়নি। মার্চ মাসে তিনি একবার বলেছিলেন যে, ‘সেই শ্রেষ্ঠ সিপাহসালার যে বিনা রক্তপাতে যুদ্ধ জয় করতে পারে।’ এই একই কারণে ২৫ মার্চ রাতে আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীদের পালিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেও নিজে গ্রেফতার হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকলেন। কারণ, তার নিজের ভাষ্যমতে, তিনি পালিয়ে গেলে ব্যাপক রক্তপাত হবে। আমরা জানি যে, তিনি ধরা পড়া সত্ত্বেও কম রক্তপাত হয়নি। বস্তুত, শেখ মুজিব ইতিহাসের এক বিশাল মাপের নেতা হওয়া সত্ত্বেও আত্মগোপনে গিয়ে বিপ্লবী রাজনীতি করা তার অভ্যাসে ছিল না। সামরিক বিষয়েও তার কোন ধারণা ছিল না। ’৭১-এর সশস্ত্র যুদ্ধে তিনি যদি সরাসরি উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব প্রদান করতেন, যেমন করেছিলেন আমাদের দেশেরই ইতিহাসের আরেক মহান নেতা সুভাস চন্দ্র বসু, তাহলে হয়তো স্বাধীনতা পরবর্তী ইতিহাসের গতিধারা ভিন্নরূপ হতে পারতো।
সেই মুজিবুর রহমান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জানতে পারেননি, কিভাবে নয় মাস যুদ্ধ হয়েছে, কতো মানুষের প্রাণ গেল, কারা যুদ্ধ করেছে, কী বিভৎস ছিল পাক হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা অথবা সুনির্দিষ্ট কতকগুলো প্রশ্নে ভারত সরকারের কি ভূমিকা ছিল ইত্যাদি।
২৫ মার্চ সকাল পর্যন্ত আলোচনা চলেছিল। তিনি কি বন্দী হওয়ার আগে স্বাধীনতার কোন ঘোষণা দিয়েছিলেন? পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে ঢাকায় ফিরে এসে তিনি জানালেন যে, স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে তিনি চট্টগ্রামে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্র“মুক্ত হওয়ার পর প্রায় এক মাস পর্যন্ত জহুর আহমেদ চৌধুরী (যার কাছে তিনি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন)সহ চট্টগ্রামের কোন নেতাই এই সংবাদ জানাননি। অর্থাৎ তারা কোনো টেলিগ্রাম পাননি। পাবার কথাও নয়। কারণ, যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সেই সময়ে যদি ঢাকা থেকে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েও থাকে, তা চট্টগ্রামে পৌঁছাতে পারে না। কারণ, ওই সময়ের আগেই যুদ্ধ জাহাজ থেকে ছোড়া বোমার আঘাতে চট্টগ্রাম টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।
এক রকম অপ্রস্তুত অবস্থায় কোন দিকনির্দেশনা ছাড়াই জনগণ সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লো। প্রথমে যুদ্ধ শুরু করলেন বাঙালি সেনারা। তবে এর আগেই ১৯ মার্চ জয়দেবপুরে মেজর সফিউল্লাহর নেতৃত্বে বাঙালি সৈন্যরা বিদ্রোহ করে পূর্বদিকে সরে যাচ্ছিলেন। (১ ও ২ এপ্রিল রাশেদ খান মেনন ও আমি কিশোরগঞ্জে এই বিদ্রোহী সৈন্যদের দেখেছিলাম।) তবু তখনো স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়নি। কারণ, তখনো ঢাকা দুই পক্ষের মধ্যে সংবিধান নিয়ে আলোচনা চলছে।
২৬ মার্চ মেজর জিয়া চট্টগ্রামের রেডিও থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উল্লেখ করে স্বাধীনতার ঘোষণা শোনালেন। ঐতিহাসিক তাৎপর্য দিন এবং তিনি ডাক দিয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমানের নাম নিয়েই।
মোটকথা এইভাবে অপ্রস্তুত অবস্থায় বাঙালি স্বাধীনতা যুদ্ধে নেমেছিল। তবে, ইতোমধ্যে যে মানসিক প্রস্তুতি তৈরি হয়েছিল এবং স্বাধীনতার জন্য উদগ্র আকাঙ্খা ছিল, সেটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ।
৬. মুক্তিযুদ্ধ : বহুমুখী সশস্ত্র তৎপরতা
মুক্তিযুদ্ধ একক কমান্ডে হয়নি। প্রবাসী সরকারের অধীনস্থ যে অফিসিয়াল মুক্তিফৌজ ছিল, তার কমান্ড স্টাকচার বা সেনাপতিমন্ডলী গঠিত হয়েছিল, পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত (অথবা সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত) সেনা অফিসারদের দ্বারা, যারা ভারতে অবস্থান করতেন। তারাই ছিলেন সেক্টর কমান্ডার, সাব সেক্টর কমান্ডার ইত্যাদি। এদের অধীনে পাকবাহিনীর বাঙালি সিপাহী, পুলিশ ইত্যাদি ছাড়াও ছিলেন স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণ, যাদেরকে বলা হতো এফএফ (অর্থাৎ ফ্রিডম ফাইটার)। এই অফিসিয়াল আর্মিতে যাতে এফএফ হিসেবে কোনো বামপন্থী ঢুকে না পরতে পারে, সেই ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ও ভারত সরকার খুব সতর্ক ছিলো।
অফিসিয়াল আর্মি প্রধানতঃ সীমান্তের ওপার থেকে আক্রমণ চালিয়ে দ্রুত নিরাপদে ভারত ভূমিতে ফিরে যেতো। দেশের মধ্যে থেকেও বরিশাল সুন্দরবন অঞ্চলে কেউ কেউ যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা কম।
এছাড়াও ভারত সরকার স্বীকৃত আরেকটি স্বতন্ত্র মুক্তিফৌজ ছিল কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে, যা কাদেরিয়া বাহিনী নামে পরিচিত। টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহের উত্তরাঞ্চলে তাদের তৎপরতা ছিল। কাদেরিয়া বাহিনীর উপর প্রবাসী সরকারের বা সরকারি বাহিনীর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না।
সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর সোভিয়েত সরকারের চাপে ইন্দিরা সরকার বাধ্য হয়েছিল, তথাকথিত মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি-ন্যাপ-ছাত্র ইউনিয়নের তরুণদের আলাদা করে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে ও অস্ত্র সরবরাহ করতে। তারা প্রবাসী সরকারের অধীনস্থ অফিসিয়াল মুক্তিফৌজের কমান্ডের বাইরে ছিল। এমনকি উভয়ের মধ্যে কোন সমন্বয়ও ছিল না। অবশ্য সকলেই ভারতের সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। সিপিবি-ন্যাপ-ছাত্র ইউনিয়নের বাহিনীর একটি দল মনজুরুল আহসান খানের নেতৃত্বাধীনে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে সীমান্ত অতিক্রমকালে, বাংলাদেশে প্রবেশের মুখে, কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার বেতিয়ারা নামক স্থানে পাক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাদের নয়জন শহীদ হন।
ভারত সরকারের বিশেষ তত্ত্বাবধানে ছিল আরও একটি বিশেষ বাহিনী, যারা বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের কমান্ডের বাইরে ছিল। আওয়ামী লীগের বাছাই করা কর্মীদের দ্বারা, এই বাহিনী গঠিত হয়েছিল। শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ প্রমুখ এই বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। এই বাহিনীর নাম ছিল বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স। বাহিনীর একটা ডাক নাম ছিল মুজিব বাহিনী। এই বাহিনী সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।
বাম কমিউনিস্টদের মধ্যেও তখন অনেক বিভক্তি ছিল। ফলে, একেক অংশ একেকভাবে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। পরস্পরের মধ্যে কোন যোগাযোগ পর্যন্ত ছিল না। আবার বামপন্থীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ ‘দুই কুকুরের কামড়াকামড়ি’র চরম বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব উপস্থিত করে, কার্যত এই মহান যুদ্ধের বিরোধিতাই করেছিল। এই ক্ষুদ্র অংশের এই ভূমিকার কারণে বুর্জোয়ারা বাম কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের সুযোগ পেয়েছিল।
বাম শিবিরের মধ্যে সর্বাধিক যুদ্ধ করার রেকর্ড ছিল ‘কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি’র - যার নেতৃত্বে ছিলেন কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন, আবদুল মান্নান ভূইয়া, হায়দার আকবর খান রনো, হায়দার আনোয়ার খান জুনো, মোস্তফা জামাল হায়দার প্রমুখ। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীন সারাদেশে ছোট বড় ১৪টি গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠেছিল এবং সারাদেশে সহযোগী যোদ্ধা মিলিয়ে বিশ হাজার গেরিলার এক বিশাল বাহিনী, যার মধ্যে শতাধিক শহীদ হয়েছিলেন। এই সংগঠনটির গেরিলা তৎপরতার সামান্য কিছু বিবরণ এখানে তুলে ধরা হবে। তবে পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা সম্ভব নয়, প্রথমত. রচনার সীমাবদ্ধ পরিসরের কারণে এবং দ্বিতীয়ত. সামগ্রিক তথ্যের অভাবে। চার দশকের সময়ের ব্যবধানে অনেক ঘটনা স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে এবং যাদের কাছ থেকে জানা যেত, তাদেরও অনেকে আজ পৃথিবীতেই নেই।
(চলবে)
http://amaderbudhbar.com/?p=552
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ১০ এপ্রিল ২০১৩ ১৬:১৬582565
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ১০ এপ্রিল ২০১৩ ১৬:১৬582565- ভারতে গৃহবন্দী মওলানা ভাসানী
হায়দার আকবর খান রনো
_____________________________________
৭. জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি
১৯৭১ সালের ১ ও ২ জুন কলকাতার বেলেঘাটার এক স্কুলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি বাম ও কমিউনিস্ট দল ও গণসংগঠন এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে, গঠন করেছিল, ‘বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি।’ ভাসানী ন্যাপ, কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি, বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (দেবেন শিকদার) প্রমুখ দলের নেতারা এতে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেছিলেন বরদা চক্রবর্তী। বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ঘোষণাপত্র রচনা ও পেশ করেছিলেন এই লেখক। এই সমন্বয় কমিটির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছিল, মওলানা ভাসানীকে, তাঁর অনুপস্থিতিতেই।
‘বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি’র ঘোষণাপত্রটি তখন দেশী-বিদেশী পত্রপত্রিকায় বহুল প্রচারিত হয়েছিল। ঘোষণাপত্রের একটি কপি হাতে নিয়ে কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেমন ও আমি প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে দেখা করি। ঘোষণাপত্রে আমরা বলেছিলাম, আমরা স্বতন্ত্রভাবে সশস্ত্র যুদ্ধ চালালেও প্রবাসী সরকার ও সরকারি মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করবো। এই ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধরত অন্যান্য বাম-কমিউনিস্ট পার্টি ও সংগঠনের পার্থক্য ছিল। যথা সুখেন্দু দস্তিদার-তোয়াহার নেতৃত্বাধীন ইপিসিপি (এমএল) অথবা সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বাধীন সর্বহারা পার্টি (তখন নাম ছিল পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন)। তারা প্রবাসী সরকারকে স্বীকৃতি দিতে চাননি। আমরা প্রবাসী সরকারকে মেনে নিয়েছিলাম। এমনকি সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল, তারা আমাদের সহযোগিতা নিতে আগ্রহী নন। তাজউদ্দিন আহমেদ খুবই ভদ্র লোক ছিলেন। আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলেও, জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গঠন করাকে যে পছন্দ করেননি, তা বোঝা গেল।
আমরা প্রধানতঃ দুই ভাবে যুদ্ধ করেছি। এক. দেশের অভ্যন্তরে ঘাটি করে, দুই. সরকারি মুক্তিবাহিনীর মধ্যে আমাদের দলের কর্মীদের ঢুকিয়ে দিয়ে। এই ব্যাপারে কয়েকজন সেক্টর কমান্ডার আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, কর্নেল (অব.) কাজী নুরুজ্জামান, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর মনজুর আহমেদ, মেজর এম এ জলিল। তারা আমাদেরকে অস্ত্র দিয়েও সাহায্য করেছিলেন।
৮. মুক্তিযুদ্ধ ও মওলানা ভাসানী
আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মওলানা ভাসানীকে প্রধান করে তাঁর অনুপস্থিতিতেই ‘বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি’ গঠিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতেও স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়কালে ভাসানীর দেখা আমরা পাইনি। কারণ, তিনি ভারতে গৃহবন্দী ছিলেন।
এখানে কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বললে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ৩ এপ্রিল রাশেদ খান মেনন ও আমি অনেক পথ ঘুরে (শিবপুর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ হয়ে) টাঙ্গাইলে পৌঁছাই। তখন মির্জাপুরের কাছে বাঙালি ইপিআর সদস্যদের সঙ্গে পাকবাহিনীর তুমুল যুদ্ধ চলছিল। আমরা দুপুরের দিকে বিন্নাফুর গ্রামে চলে যাই। কবি বুলবুল খান মাহবুব আমাদের জানালেন, ‘হুজুর এখন বিন্নাফুরে আছেন, রিকশা নিয়ে চলে যান, কাউকে বলবেন না।’ বিন্নাফুরে মওলানা ভাসানীর দেখা পেলাম। সেই রাত তাঁর বাড়িতেই ছিলাম। এদিকে, বিকেলের আগেই টাঙ্গাইলে পাকবাহিনী ঢুকে পড়েছে। শুরু হয়েছে হত্যা, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি। মানুষ পালাচ্ছে শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে। বিকাল বেলায় পাকবাহিনী ভাসানীর সন্তোষের বাড়িতে আগুন দিল। সেই খবর পেলেন ভাসানী বিন্নাফুর গ্রামে বসেই।
রাতে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আমার ও মেননের কথা হলো। তিনি একটা নির্দিষ্ট তারিখ বললেন। সপ্তাহ খানেক পরের তারিখ। বললেন, ‘‘জাফর, মতিন, তোয়াহা, হক সবাইকে ডাকো।’’ বিন্নাফুরেই একত্রে মিলিত হওয়া যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন। আমার কাছে প্রস্তাবটি অবাস্তব মনে হয়েছিল। কারণ, এই রকম যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সকলকে খবর দেয়াও সম্ভব নয়. তাছাড়া বিন্নাফুর গ্রামও যে নিরাপদ, সেটাই বা ভাবি কি করে?
আমরা বরং তাকে বললাম, ‘আপনি ভারত চলে যান, সেখানে আমরা একত্রে বসতে পারবো।’ তিনি রাজী হলেন না। বললেন, ‘ইন্দিরার পিতা জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল। আমি যখন আসামের জেলে ছিলাম, তখন তিনি আমার স্বাস্থ্যের খবর নিতেন। ভারতে গেলে ডজন খানেক কামান তো আনতেই পারবো। কিন্তু মন চায় না। তোমরা তো ওদের সঙ্গে রাজনীতি করোনি। জানো না। আমি ভারত যাবো না।’
তিনি অবশ্য ভারতে গিয়েছিলেন। প্রথমে পাকবাহিনী বিন্নাফুরের খবর না পেলেও পরে জানতে পেরেছিল এবং বিন্নাফুর অভিমুখে তাদের আসার খবর পেয়ে তিনি একাকী বাড়ি ত্যাগ করে পাশের গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মাথায় টুপি ছিল না। গায়ে পাঞ্জাবি ছিল না। একাকী মাঠ অতিক্রম করে কোথায় গেলেন, আমরা কেউ জানতে পারলাম না। কারণ, তিনি কাউকে সঙ্গে নেননি।
পরে জানা গিয়েছিল যে, তিনি একটি ছোট নৌকা করে যমুনা পার হয়ে সিরাজগঞ্জে পৌঁছান এবং সেখান থেকে ন্যাপ নেতা সাইফুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে যমুনা নদী ধরে উত্তরমুখে রওনা হন এবং আসামে পৌঁছান। ভারতে তিনি গৃহবন্দী ছিলেন। আমরা অনেক চেষ্টা করেও তার দেখা পাইনি। একমাত্র সাইফুল ইসলাম তার সঙ্গে ছিলেন। ভারতের পার্লামেন্টে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা প্রশ্ন তুলেছিলেন, ‘ভাসানী কোথায়?’ কংগ্রেস সরকার কোন উত্তর দেয়নি।
তবে একবার একটি ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। মওলানা ভাসানী প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টামন্ডলীর সভায় বক্তৃতা করছেন। পরবর্তীকালে এর গোপন তথ্য প্রকাশ করেছিলেন, প্রয়াত সাংবাদিক, কমিউনিস্ট রাজনীতিবিদ ও ছড়াকার সাহিত্যিক ফয়েজ আহমদ। ফয়েজ আহমদ যা লিখেছিলেন, তার মর্মকথা হলো এই রকম : জাতিসংঘের বিতর্কের সময় ভারত এটা প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, পাকিস্তান সরকার শুধু আওয়ামী লীগই নয়, সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বিরুদ্ধেই যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে (কথাটা তো সত্যই ছিল)। সেটা প্রমাণ করার জন্যে তারা তাড়াহুড়ো করে একটি উপদেষ্টামন্ডলীর সভার আয়োজন করেন (ভাসানী, মোজাফফর আহমদ, মনিসিংহ, মনোরঞ্জন ধর - দুই ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেসের প্রতিনিধি) এবং তার সভার একটি ছবি ছাপা হয়েছিল, যা সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। সাংবাদিক ফয়েজ আহমদের মতে, এই উপদেষ্টামন্ডলীর আর কোন সভাও হয়নি, তার কোন কার্যকারিতাও ছিল না।
আগস্ট মাসের দিকে মওলানা ভাসানী আমাদের তিনজনকে (কাজী জাফর আহমদ, রাশেদ খান মেনন ও আমি) উদ্দেশ্য করে ছোট একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এটি বহন করেছিলেন সাইফুল ইসলাম। তিনি সিপিআই(এম)-এর কাছ থেকে আমাদের সন্ধান পান এবং আমাদেরকে হস্তান্তর করেন। চিঠিতে লেখা ছিল, (যতোদূর মনে পড়ে), ‘পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশনের ষড়যন্ত্র চলিতেছে। তোমরা ইহা মানিয়া লইবে না। তোমরা যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে।’ শেষ লাইনটি ছিল একটি পরিচিত গানের লাইন, ‘যদি তো ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।’
(চলবে)
http://amaderbudhbar.com/?p=590
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ১০ এপ্রিল ২০১৩ ১৬:১৭582566
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ১০ এপ্রিল ২০১৩ ১৬:১৭582566- মুক্তিযুদ্ধের শহীদ চিকিৎসক ডা. শামসুদ্দিন
সাব্বির আহমদ, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট
বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম
_________________________________
সিলেট: ‘কোথায় যাবেন আপনারা? আমরা ডাক্তার। আহত মানুষ ফেলে আমরা তো কোথাও যেতে পারি না’। সহকর্মী চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলেছিলেন শহীদ ডা. শামসুদ্দিন।
১৯৭১ সালের ৯ এপ্রিল। পাকিস্তানি বর্বর হানাদার বাহিনীর ছোড়া গুলিতে সিলেটের শত শত মানুষ আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসকের দ্বারস্থ হন। অার তখন নিজের জীবন তুচ্ছ করে তাদের পাশে দাঁড়ান মানবসেবায় নিবেদিত প্রাণ ডা. শামসুদ্দিন।
সেদিন ভোররাতে সিলেট শহরের একাংশের দখল নিয়ে হানাদাররা স্বাধিকার আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক ডা. শামসুদ্দিনকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু হাসপাতাল ছেড়ে সরে যাননি কর্তব্য পালনে অবিচল ডা.শামসুদ্দিন। হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় সার্জারি ওয়ার্ডের বারান্দায় তাকে গুলি করে হত্যা করে ঘাতকরা। একই সঙ্গে অপর চিকিৎসক ডা. শ্যামল কান্তি লালা ও হাসপাতালের আরও ছয়-সাতজন কর্মচারীকেও গুলি করে হত্যা করে মানুষরূপী হায়েনারা।
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর নির্মমতার শিকার হয় একের পর এক শহর-নগর-বন্দর। দেশব্যাপী প্রতিদিনই চলে তাদের বর্বরোচিত ও নৃশংস গণহত্যা। তবে ৩ থেকে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত সিলেট শহর ছিলো মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে। সিলেট শহর পুনর্দখলের জন্য ঢাকা থেকে অতিরিক্ত সেনা এনে ৭ ও ৮ এপ্রিল বিমান ও সেনাবাহিনী দিয়ে আক্রমণ চালায় পাকবাহিনী।
অবশেষে ৯ এপ্রিল সিলেট শহরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে পাকবাহিনী। আর তখনই হানাদার বাহিনীর কালো থাবার শিকারে পরিণত হন এ মহান চিকিৎসক। পৈশাচিক কায়দায় হত্যা করা হয় তাঁকে। তিনি তখন সিলেট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের শৈল্য চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
শহর ছেড়ে যখন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাচ্ছে সবাই, ডা. শামসুদ্দিনও নিজের পরিবার পরিজনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন গ্রামের বাড়িতে। ছুটি দিয়ে দেন হাসপাতালের মহিলা নার্সদের। কিন্তু জনমানবশূন্য সিলেট শহরে সেবাব্রত ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাননি ডা. শামসুদ্দিন। একের পর এক আহত মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা করে গেছেন তিনি। তাঁকে সাহায্য করার জন্য থেকে যান হাতে গোনা আরও কয়েকজন।
পানি, বিদ্যুৎ, ঔষধ সব যখন শেষ, তখনও সেবাদান শেষ করেননি ডা. শামসুদ্দিন। জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে মানব সেবার কালজয়ী দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তিনি।
শহরে ভয়াবহ যুদ্ধচলাকালীন সময়ে হাসপাতাল অভিমুখ যাওয়ার পথে পরিচিত একজনের সঙ্গে দেখা ডা. শামসুদ্দিনের। ‘একি আপনি এই পরিস্থিতিতে হাসপাতালে যাচ্ছেন কেন?’ শুরুতেই প্রশ্ন পরিচিতজনের। ‘ভাই, কিছু রোগী হাসপাতালে রয়ে গেছে। তাদের ফেলে কোথায় যাই বলুন। আমার শিক্ষাই যে মানবতার সেবা।’ হাসি মুখে উত্তর দিয়েছিলেন ডা. শামসুদ্দিন।
৯ এপ্রিল ১৯৭১। আকাশে হিংস্র শকুনের চাইতেও শহরে পাক হানাদার বাহিনীর অধিক আনাগোনা। হাসপাতালের পূর্বপাশে সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ। পাকবাহিনীর ক্যাম্প। উত্তর পাশে টিলার উপর সিভিল সার্জনের বাংলো আর টিলার নিচে সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা।
সকাল ৯ টায় মুক্তিবাহিনী সেই বাংলো ও মাদ্রাসা থেকে আক্রমণ চালায় পাকিস্তানি বাহিনীর একটি কনভয়ের উপর। মারা যায় তিন পাকসেনা। বেপরোয়া পাকবাহিনী তখন পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে। তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে মুক্তিযোদ্ধাদের।
ডা. শামসুদ্দিন তখন অপারেশন থিয়েটারে বসে আছেন। রক্তের অভাবে অপারেশন করা যাচ্ছে না আহত মানুষগুলোর। নিজের অসহায়ত্ব তাকে যেন মৃত্যুর চেয়েও বেশি পীড়া দিচ্ছে। হঠাৎ করেই মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজে হাসপাতালে এসে উপস্থিত হয় মেজর রিয়াজসহ সশস্ত্র কয়েকজন পাকসেনা।
মুক্তিযোদ্ধাদের না পেয়ে ডা. শামসুদ্দিনসহ পাঁচজনকে লাইন করে দাঁড় করানো হলো। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে নিজের ব্যক্তিত্বে তখনো অনড় ডা. শামসুদ্দিন। নিজের জীবন ভিক্ষা চাননি তিনি। চেয়েছিলেন অপারেশন থিয়েটারে রেখে আসা মুমূর্ষু রোগীদের অপারেশন শেষ করে আসতে।
কিন্তু বর্বর পাকিস্তানি সেনারা প্রথম গুলি তাকেই করে। প্রথম গুলিটি লেগেছিলো তার বাম উরুতে, দ্বিতীয়টি পেটের বাম পাশে। তিনি তখনও দাঁড়িয়ে। একচোখ বিস্ময় নিয়ে দেখছিলেন কর্তব্যরত ডাক্তার কারো শত্রু হয় কিভাবে। তৃতীয় গুলিটি লাগে তার বুকের বাম পাশে, হৃৎপিণ্ডে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ডা. শামসুদ্দিন।
এরপর একে একে হত্যা করা হয় ডা. শ্যামল কান্তি লালা, ডা. জিয়াউর রহমান, বয় মাহমুদুর রহমান, অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার কোরবান আলীকে। তারপর শুধুই নীরবতা।
মানবতাবাদী ডাক্তার শামসুদ্দিন আহমদ ও তার প্রিয় ছাত্র ডাক্তার শ্যামল কান্তি লালাকে যখন হত্যা করা হয় তখন তাদের বাহুতে ছিলো রেডক্রস ব্যাজ। ঘাতক সেনারা রেডক্রসের ব্যাজ দেখেও তাদের রেহাই দেয়নি।
শহরে এরপর থেকে টানা কারফিউ। ১৩ তারিখ মাত্র এক ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হলে ডা. শামসুদ্দিনের পায়ের জুতো দেখে তাকে শনাক্ত করা হয়। হাসপাতালের ভিতর একফুট গর্ত করে দ্রুত তার দাফন করা হয়।
ডা. শামসুদ্দিনের জীবন ও কর্ম:
ছাত্রজীবনে ডাক্তার শামসুদ্দিন আহমদ প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আসাম মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের নেতা ছিলেন তিনি। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন তৎকালীন যুব ও ছাত্রনেতা পীর হবিবুর রহমান ও তাসাদ্দুক আহমদ।
১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে শামসুদ্দিন আহমদ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তার হয়ে বের হন। প্রথম দিকে তিনি সরকারি চাকরিতে যোগ দেননি, যদিও চাকরির সুযোগ ছিলো।
কিন্তু ভারত বিভক্তির কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ের ডাক্তাররা ভারতে চলে গেলে সিলেট মেডিকেল কলেজে চিকিৎসক শূন্যতা দেখা দেয়। এ সময় মানবতার সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারি ডাক্তার হিসেবে তিনি চাকরিতে যোগ দেন।
ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় ডা. শামসুদ্দিন রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের সার্জারির অধ্যাপক ছিলেন। তীব্র গণআন্দোলনে ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করে। মিছিলে ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণী শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা। ক্যাম্পাসে মোতায়েন জল্লাদ সেনারা মিছিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ড. শামসুজ্জোহাকে গুলি এবং বেয়োনেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে তারা।
ঘাতকরা সার্জারির প্রফেসর ডা. শামসুদ্দিনকে একটি ভুয়া পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তৈরির জন্য হুকুম করে। কিন্তু দেশপ্রেমিক ডা. শামসুদ্দিন তাদের আদেশ পালন না করে রিপোর্টে ড. শামসুজ্জোহার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ তুলে ধরেছিলেন। রাজশাহীতে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পায়নি ঘাতকরা। পরে সিলেটে প্রথম সুযোগেই তার ওপর আঘাত হানে তারা।
সিলেটে যে স্থানটিতে তাদের হত্যা করা হয়েছিলো সেখানে এই বীর শহীদদের স্মরণে স্মৃতির মিনার গড়ে উঠেছে। চৌহাট্টা সড়কের পাশেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন অধ্যাপক ডা. শামসুদ্দিন আহমদ, ডা. শ্যামলকান্তি লালা, মেইল নার্স মাহমুদুর রহমান, অ্যাম্বুলেন্স চালক কুরবান আলী এবং অন্য শহীদেরা।
সেই হাসপাতালটি এখন শহীদ ডা. শামসুদ্দিন হাসপাতাল নামকরণ করা হয়েছে। তার পাশে আছে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীদের আবাসন ডা. শহীদ শামসুদ্দিন ছাত্রাবাস।
http://www.banglanews24.com/detailsnews.php?nssl=bea609a0ba26c4114517fdd68f251852&nttl=10042013188024
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ১৫:২০582567
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ১৫:২০582567- গণহত্যা :শব্দ ভাবনা
সৈয়দ শামসুল হক
________________________________
ভাষা-ইতিহাসের কবে সেই দূর-ধূসরকালে সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসেছিলো এই শব্দটি_ গণ। আর, ওই শব্দের সহযোগে_ বাঙালির কণ্ঠে কতকাল থেকে কতই না ব্যবহৃত_ গণতন্ত্র, গণশক্তি, গণজাগরণ, গণনায়ক। আর, একদিন এই বাংলাদেশের আমরাই ঊনসত্তরের উত্তাল ইতিহাসের জন্যে নতুন রচনা করে উঠি_ গণঅভ্যুত্থান, যা আগে আর ছিলো না। গণ আর হত্যা_ এই শব্দ দুটির সহযোগেই কেবল যে নির্মিত এটি, তা নয়; এর ভেতরে পূরিত হয়ে আছে একটি ইতিহাস_ একাত্তরে বাঙালির ওপরে পরিচালিত পাকিস্তানিদের হত্যাযজ্ঞ। গণহত্যা! এই প্রথম এই শব্দটি উচ্চারিত হলো বাংলা ভাষায়, এবং তার নির্মাণ ও উচ্চারণ এই বাংলাদেশের এই বাঙালিরই।
ভারতীয় যে বাঙালিজন, তাঁদের কাছে গণহত্যা শব্দটি বোধগম্য হলেও, তাঁদের উচ্চারণ-রক্তে নয় তা তাঁদের হৃৎপিণ্ড থেকে ধাবিত বা নিষ্ক্রান্ত; বাংলাদেশের বাঙালির কাছে গণহত্যা যতটা অর্থবহ, তার একবিন্দুও তাঁদের কাছে নয়, কারণ তাঁরা ভাগ্যবান যে গণহত্যার অভিজ্ঞতা তাঁদের পোহাতে হয়নি। ঐতিহাসিক কোনো বৃহৎ অভিজ্ঞতার ভেতরেই থাকে তাকে ধারণ করবার এমন তুমুল একটি চাপ যার অন্তর্গত চিৎকারটি চায় শব্দধ্বনি, আর তখনি জন্ম হয় নতুন শব্দের। বাংলাদেশের মানুষ তিরিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে যা জেনেছে, তারই নামকরণের জন্যে বাংলাদেশকেই শব্দটি তৈরি করে নিতে হয়েছে; বাংলাদেশের বাঙালির উচ্চারণেই প্রথম উঠে এসেছে শব্দটি_ গণহত্যা!
জাতিসংঘের বর্ণনায়, গণহত্যা মানেই এমন এক হত্যাযজ্ঞ যার লক্ষ্য একটি জাতি বা জাতিসত্তা, কিংবা কোনো বিশেষ বর্ণের বা ধর্মবিশ্বাসের মানুষদের নাম নিশানা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। বাংলাদেশের মাটিতে একাত্তরে এটাই করতে চেয়েছিলো পাকিস্তান।
গণহত্যা যারা ঘটায় তারা মানব জীবনের প্রতি নয় শ্রদ্ধাশীল, তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি একনায়কত্ব, তারা মনে করে তাদের সংস্কৃতিই অনন্য শ্রেষ্ঠ। যাদের ওপরে তারা গণহত্যা পরিচালনা করে তাদের তারা মনে করে আধা-মানুষ বা না-মানুষ, মনে করে বর্বর, পতিত, নাস্তিক ও পশুপ্রায়। এই বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় একাত্তরের বাংলাদেশে গণহত্যাকারী পাকিস্তান ও তাদের দোসর গোলাম আযম গংদের সঙ্গে।
গণহত্যার ইংরেজি জেনোসাইড। বাংলাভাষায় গণহত্যার মতোই ইংরেজিতেও জেনোসাইড শব্দটি ছিলো না। ওই ভাষার দীর্ঘ ইতিহাসে মাত্রই সেদিন, ১৯৪৪ সালে, শব্দটি প্রথম আমরা পাই রাফায়েল লেমকিন নামে এক লেখকের রচনায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জার্মানিতে হিটলার পরিচালিত হত্যাযজ্ঞ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি গ্রিক শব্দ জেনোস যার মানে জাতি বা মানুষ, আর লাতিন শব্দ সিডের যার মানে হত্যা করা, এই দুটি শব্দ মিলিয়ে নির্মাণ করেন নতুন শব্দ_ জেনোসাইড, বাংলায় যার দর্পণপ্রায় প্রতিরূপ_ গণহত্যা।
দশই জানুয়ারি উনিশ শ' বাহাত্তর, স্বদেশে ফিরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশে উচ্চারিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কথাগুলো আজও তো আমরা মর্মের ভেতরে শুনতে পাই। 'ভাইয়েরা আমার, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ দানের পর আজ আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে।... তিরিশ লক্ষ লোক মারা গেছে।... তারা আমার মানুষকে হত্যা করেছে। হাজার হাজার মা-বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে।... মানব ইতিহাসের জঘন্যতম কুকীর্তির তদন্ত অবশ্যই করতে হবে।'
আর, একাত্তরে পাকিস্তানিদের সেই কুকীর্তির দোসর যারা ছিলো কুলাঙ্গার সেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যখন বাংলার মাটিতে চলছে, একের পর এক রায় ও দণ্ডদান যখন ঘোষিত হচ্ছে, এবং আরো হবার অপেক্ষায় রয়েছে, তখন যারা সেই বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলে, ঘোষিত রায়ের বিরুদ্ধে হরতাল ডাকে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালায়, হত্যার পর হত্যা করতে থাকে মানুষকে, ভাংচুর জ্বালাও পোড়াও চালাতে থাকে, তখন যে জেগে ওঠে একালের প্রজন্ম, তাদেরও সেই শপথ আমরা মর্মে ধারণ করে উঠি যে, বাংলায় আবার ফিরে এসেছে নতুন এক মুক্তিযুদ্ধ, আর এবারের এই যুদ্ধের লক্ষ্য গণহত্যার সহযোগী যারা বাংলার রাজনীতিকে বারবার বিপর্যস্ত করছে, সেই তাদের বিচার করে, সভ্যতার দায় মিটিয়ে, তিরিশ লক্ষ মানুষের ঋণ শোধ করে, তবেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাকে নিখাদ করে তুলতে হবে।
বিচার তো হতেই হবে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের। লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগি্নসংযোগসহ গণহত্যার তাণ্ডবে মেতে উঠে গোলাম আযম গংদের অপরাধ কখনোই ক্ষমা পেতে পারে না। আজ তাদের বিচার যখন চলছে, নতুন প্রজন্ম যখন জাতিকে আবার গ্রথিত করছে বাঙালির সেই জিয়নমন্ত্র জয় বাংলায়, যখন তারা যুদ্ধাপরাধীদের জন্যে দাবি করছে সর্বোচ্চ শাস্তি, তখন যে জামায়াতে ইসলাম আর বিএনপি এই প্রজন্ম আর এই বিচার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে, আর তার মোকাবেলা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী করছে, তখন সেই পদক্ষেপকে যখন গণহত্যা বলে আখ্যা দিচ্ছেন বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া, তখন স্তম্ভিত হতে হয় তাঁর ইতিহাস ও ভাষা মূর্খতা দেখে নয়, স্তম্ভিত হতে হয় এই ভেবে যে, কোথায় ছিলেন তিনি একাত্তরে? এবং বিস্মিত হয়ে যেতে হয় এটা আবিষ্কার করে যে, তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের কোনো একটি ভাষণে একটিবারের জন্যেও গণহত্যা কথাটি উচ্চারিত হতে আমি অন্তত শুনিনি! শুনলাম এই প্রথম_ শুনলাম জেগে ওঠা বাঙালি ও বাংলাদেশের চেতনায় প্রাণিত সরকারের বিরুদ্ধেই উচ্চারিত হতে! ইতিহাসলব্ধ একটি শব্দের এমন দূষণা আমি আর দেখিনি।
যে-বাঙালি একাত্তর দেখেছে, যে-বাঙালি একাত্তরে লড়েছে, যে-বাঙালি একাত্তরের যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্যে জেগে উঠেছে, এবং যে-বাঙালি গণহত্যা নামে একটি শব্দ তার ইতিহাস থেকেই পেয়েছে, তারা দেখতে পাচ্ছে গণহত্যা শব্দটির এমন দূষিত উচ্চারণ যারা করে বস্তুত তারা তিরিশ লক্ষ মানুষের প্রাণ কোরবানিকেই অস্বীকার করে_ ফলত বাংলার চেতনা ও স্বাধীনতাকেই তারা পদাঘাত করে হ
লেখক
কবি
কথাসাহিত্যিক
http://www.samakal.net/print_edition/details.php?news=257&view=archiev&y=2013&m=03&d=26&action=main&menu_type=&option=single&news_id=336114&pub_no=1359&type=
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ১৫:২২582568
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ১৫:২২582568- ইতিহাসের নিস্তব্ধতা
বিনায়ক সেন
____________________________________
১. দেশভাগ ও গণহত্যা
কোনো কাকতালীয় কারণে দক্ষিণ এশিয়ার তিনটি দেশই_ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় গণহত্যা এড়াতে পারেনি। ১৯৪৭ সালের ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টির আগে ও অব্যবহিত পর সংঘটিত দাঙ্গাগুলোর বিস্তৃতি এমন পর্যায়ে
পেঁৗছেছিল যে, একে গবেষকদের এক বড় অংশ দেখেছিলেন 'গণহত্যামূলক দেশভাগ' (বা জেনোসাইডাল পার্টিশন) হিসেবে। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন_ শহীদ আমিন, বীণা দাস ও বোন পান্ডে স্বাধীনতার আনন্দকে মলিন হয়ে যেতে দেখেছিলেন পার্টিশন-দাঙ্গার বিষয় পরিণামে। আশিষ নন্দী, উর্বশী বুটালিয়া প্রমুখ যারা প্রথাগত অর্থে নিম্নবর্গের ইতিহাস-প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত নন তারাই প্রথম 'গণহত্যামূলক দেশভাগ'-এর শব্দবন্ধটি প্রয়োগ করেন। একই ধারায়, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, গোয়ানিজ বংশোদ্ভূত খ্রিস্টান পাকিস্তানের সাংবাদিক নেভিল এন্থনি ম্যাসকারেনহাস তার 'সানডে টাইমস'-এর ১৯৭১ সালের জুন মাসের প্রচ্ছদ নিবন্ধের শিরোনাম করেন 'জেনোসাইড'। তবে তারও আগে আমাদের স্মরণ করতে হবে আদি-চিন্তক সাদত হাসান মান্টোকে, যিনি দেশভাগের সময়কালীন গণহত্যা নিয়ে তার অবিস্মরণীয় (কিন্তু সহজপাঠ্য নয়) 'স্কেচগুলো' রেখে গেছেন। এতই ব্যাপক ছিল গণহত্যামূলক দাঙ্গা যে, তার পরিণাম দেখে শিউরে উঠেছিলেন নেহরু ও জিন্নাহ উভয়েই। মান্টো তার অতি ক্ষুদ্র 'বিনয়' গল্পটি এভাবে বর্ণনা করেছেন :
'দাঙ্গাকারীরা ট্রেনটাকে থামালো। যারা অন্য ধর্মের ছিল তাদেরকে খুঁজে খুঁজে বার করল ও হত্যা করল। এসব কাজ যখন শেষ হলো তখন ট্রেনের বাদবাকি যাত্রীদের তারা আপ্যায়িত করল দুধ, কাস্টার্ড আর টাটকা ফল দিয়ে।'
ট্রেনটা ছাড়ার আগে আতিথেয়তা দানকারীদের নেতা সমবেত যাত্রীদের উদ্দেশে একটি বক্তৃতা দিলেন : 'ভায়েরা ও বোনেরা, যেহেতু আপনাদের ট্রেন আসার সংবাদটি আমরা দেরিতে পেয়েছি তাই আমাদের যা ইচ্ছে ছিল সে রকম কোনো আপ্যায়ন আপনাদেরকে প্রদান করতে পারিনি।'
যারা গোবিন্দ নিহালনীর সিনেমা 'তামস' দেখেছেন বা কুশওয়ান্ত সিংয়ের 'ট্রেন টু পাকিস্তান' পড়েছেন তাদের এ নিয়ে বাড়তি কিছু বলার নেই। ইয়াসমিন খান তার 'দ্য গ্রেট পার্টিশন : দ্য মেকিং অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান' বইয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, এ রকম নির্মম দেশভাগই কি ছিল ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের কাঙ্ক্ষিত 'চূড়ান্ত মুহূর্ত'? একেই কি নেহরু তার ১৫ আগস্টের মধ্যরাতের বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'ট্রিস্ট উইথ ডেসটিনি'_ নিয়তির সঙ্গে আমাদের অচ্ছেদ্য বন্ধন?
পাঠক নিশ্চয়ই বলবেন, কথা হচ্ছে ২৫ মার্চের ও তার পরের ৯ মাসের গণহত্যা, যেটা বাংলাদেশে ঘটেছিল তা নিয়ে। এর মধ্যে ভারত-পাকিস্তানের দেশভাগ (হোক তা গণহত্যামূলক দেশভাগ) টেনে আনা কেন? দুই কারণে। এক. বাংলাদেশেও ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা হয়েছিল ২৫ মার্চের গণহত্যাময় 'কালরাত্রির' পরই, দুই. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে জাতীয়তাবাদী ঘরানার ইতিহাসবিদরা যত বই লিখেছেন, গণহত্যা নিয়ে লিখেছেন খুবই কম সে তুলনায়। একই কথা প্রযোজ্য ভারত ও পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদদের ক্ষেত্রে। তারাও জাতীয় আন্দোলন লিখতে গিয়ে দেশভাগের দাঙ্গাকে কার্যত এড়িয়ে গেছেন। ২৫ মার্চের গণহত্যার অভিজ্ঞতাই এক রাতের মধ্যে 'পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন নাকি স্বাধীনতা' এর মধ্যে যারা তখনও দোলাচলে ভুগছিলেন তাদের এক নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার সামনে দাঁড় করায়। এরপর আর থাকা চলে না পাকিস্তানের সঙ্গে_ এ রকম একটি সর্বজনীন বোধে মিলিত হয় বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ। অভিজ্ঞতাটা চুন্নু ডোমের চোখে এ রকম :
'আমরা ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ শাঁখারীবাজার থেকে প্রতিবারে একশত লাশ উঠিয়ে তৃতীয়বার ট্রাকবোঝাই করে তিনশত লাশ ধলপুর ময়লা ডিপোতে ফেলেছি। ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ সকাল থেকে আমরা মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশঘর ও প্রবেশপথের দু'পাশ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিববাড়ী, রমনা কালীবাড়ি, রোকেয়া হল, মুসলিম হল, ঢাকা হল থেকে লাশ উঠিয়েছি। ... আমাদের ইন্সপেক্টর পঞ্চম আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এরপর আমরা লাশঘরে প্রবেশ করে বহু যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-কিশোর ও শিশুর স্তূপ করা লাশ দেখলাম। আমি এবং বদলু ডোম লাশঘর থেকে লাশের পা ধরে টেনে ট্রাকের সামনে জমা করেছি। আর গণেশ, রঞ্জিত (লাল বাহাদুর) এবং কানাই লোহার কাঁটা দিয়ে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে পচা, গলিত লাশ ট্রাকে তুলেছে। লাশগুলো ঝাঁঝরা দেখেছি, মেয়েদের লাশের কারও স্তন পাইনি, যোনিপথ ক্ষত-বিক্ষত এবং পেছনের মাংস কাটা দেখেছি। ... প্রত্যেক যুবতীর মাথায় খোঁপা খোঁপা চুল দেখলাম।'
হুমায়ূন আহমেদের মতো শক্তিশালী লেখক ২৫ মার্চের গণহত্যার বিবরণ দিতে গিয়ে তার 'জোছনা ও জননীর গল্প' বইয়ে ন্যারেটিভ থামিয়ে দিয়ে গণহত্যার এসব প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য পাতার পর পাতাজুড়ে তুলে দিয়েছেন। মার্চের রাজনৈতিক সংলাপের এক পর্যায়ে এ রকম একটি গণহত্যা ঘটানোর পরিকল্পনা পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রশক্তি করল কী করে? এটা করলে অখণ্ড পাকিস্তানের সমর্থক যারা এ দেশে তখন পর্যন্ত রয়ে গিয়েছিলেন তারাও যে বিরুদ্ধ-পক্ষে চলে যাবেন এবং তার পরিণতি তো আরও অনিবার্য হয়ে উঠবে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়_ কিছু আগে বা কিছু পরে সে সম্ভাবনাটুকু তারা কি আদৌ বিবেচনায় নিয়েছিলেন? 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে খ্যাত ২৫ মার্চের গণহত্যার অন্যতম পরিকল্পনাকারী মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেছেন, 'আমি আর্মির এ পদক্ষেপের বিরোধী ছিলাম। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের জেনারেলরা এর পক্ষে ছিলেন। তিন দিন ধরে আলোচনা চলছিল মুজিবকে নিয়ে কী করা হবে_ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা হবে নাকি মেরে ফেলা হবে, তা নিয়ে। একাংশ চেয়েছিল তাঁকে মেরে ফেলতে। ২১ মার্চ পর্যন্ত আমরা জানতাম না আর্মি কোনো অ্যাকশনে যাবে কি-না। ২২ মার্চ টিক্কা (খান) আমাদের জানালেন_ তৈরি থাকতে।' এই উদৃব্দতিটি যেখান থেকে নেওয়া সেটি হচ্ছে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত পাকিস্তানের সিএসপি আমলা হাসান জাহিরের বই 'দ্য সেপারেশন অব ইস্ট পাকিস্তান'। তার বইয়ে অনেক নেপথ্যে বলা ঘটনার উল্লেখ আছে, শুধু বর্ণনা নেই ২৫ মার্চের গণহত্যার। এক জায়গায় তিনি বলছেন, মে-জুন মাসের দিকে তিনি গেছেন তার কিছু বাঙালি বন্ধুর বাসায়। সেসব বাসায় ভীত, বিচলিত, আতঙ্কিত দেখেছেন তাদের পরিবারকে : 'সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে, তাদের স্ত্রী-সন্তানদের মধ্যে ভীতি ও নৈতিক মনোবল হারিয়ে ফেলার যে চিত্র আমি দেখেছি তা আমাকে ধাক্কা দিয়েছে। এদের প্রতিটি পরিবার ভয়াবহ কাহিনী শুনিয়েছে আমাদের, এর মধ্যে ছিল মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা নিয়ে নিরাপত্তাহীনতা আর এসবের পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ছিল আর্মি অপারেশন।' এর বেশি আর কিছু সেখানে পাওয়া যায় না। শুধু এক জায়গায়, তিনি বাঙালি নিধন-পরিকল্পনাকে চিহ্নিত করেছেন 'ফাইনাল সল্যুশন' হিসেবে। বলা বাহুল্য, এই শব্দবন্ধটি হিটলারের জার্মানিতে নাজিরা ব্যবহার করেছিল ইহুদিদের সমূলে সংহারের মাধ্যমে জাতি-নিধন পরিকল্পনাকে বোঝাতে গিয়ে। এই নীতি এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রেও নেওয়া হয়েছিল_ এটা হাসান জাহির হিসাবে নেননি। ২৫ মার্চের গণহত্যার শিকার হয়েছিল প্রথমে রেললাইনের ধারের বস্তিবাসী ও তার পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়_ এটিও তার নজর এড়িয়ে গেছে।
২. ইতিহাসের 'উচ্চকণ্ঠ' বনাম ইতিহাসের 'নিস্তব্ধতা'
ইতিহাস অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলে, অনেক বেশি বলে, কিন্তু অনেক বিষয় নিয়ে আবার কোনো উচ্চবাচ্যই করে না, এড়িয়ে যায় বা 'নিস্তব্ধ' থাকে। ইতিহাস যেহেতু আমাদের কাছে 'অতীত'কে বিনির্মাণ করে, উপস্থাপনা করে, সেহেতু কোন ঘটনাটা কতটা প্রাধান্য পায় তার ওপরে ভিত্তি করে আমাদের লিখিত-পড়িত 'ইতিহাসবোধ' (টেক্সট) তৈরি হয়। ইতিহাসের জন্য যা অস্বস্তিকর, সেসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার ফলে শেষাবধি আমরা যা পাই তা হলো সময়ের এক খণ্ডিত চিত্র কেবল। এই খণ্ডিত চিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে যে সমাজ-রাজনীতি-রাষ্ট্র গড়ে ওঠে তাও খণ্ডিত হতে থাকে 'ভেতর থেকে'। নিটশে একে বলেছিলেন, এ রকম ইতিহাসে 'মৃতরা জীবিতদের মাটিচাপা দিয়ে কবর দেয়'।
বিসমার্ক জার্মানিতে একনায়ক হিসেবে ক্ষমতা নেওয়ার দু'বছর পরে, ১৮৭৩ সালে, জার্মান দার্শনিক নিটশে কিছু 'অসময়ের ভাবনা' লিখতে শুরু করেন। তারই অংশ হিসেবে তিনি লেখেন_ 'দ্য ইউজ অ্যান্ড এবিউস অব হিস্টরি ফর লাইফ'। এই ছোট্ট পুস্তিকাটি প্রথাগত ইতিহাসবিদ্যার মৌলিক পদ্ধতিগত সমালোচনা হিসেবে আজ স্বীকৃত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইতিহাস চর্চার নানা খুঁটিনাটি তথ্য পেশ করে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে, অথচ অনেক জরুরি বিষয় নিয়ে কোনো উল্লেখ নেই, বিচার-বিশ্লেষণ তো আরও পরের কথা। এই ছিল নিটশের মূল কথা। নিটশের এই কথার সূত্র ধরে নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহ তার একটি লেখায় বলেছেন, কোনো কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে 'অতিরিক্ত ইতিহাসপনা_ অতিরিক্ত স্মৃতিশক্তির মতো_ কোনো দেশের সংস্কৃতির অবক্ষয়মান স্বাস্থ্যকে নির্দেশ করে'। এক্ষেত্রে তিনি বিখ্যাত স্নায়ু মনস্তত্ত্ববিদ এআর লুবিয়ার একটি গল্প উদৃব্দত করেন। এই মনস্তত্ত্ববিদের কাছে সমস্যা নিয়ে এক রোগী এসেছেন। তার সমস্যা হলো_ তার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি : সে কোনো কিছুই ভুলতে পারে না, সমস্ত খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ খণ্ড খণ্ড চিত্র হিসেবে তার মনের মধ্যে রয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত এত অসংখ্য খুঁটিনাটির মধ্যে তালগোল পাকিয়ে গিয়ে কোনো কিছুরই অর্থ উদ্ধার করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। রণজিৎ গুহ ঔপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা উভয় ধারার মধ্যেই অনেক অনাবশ্যক খুঁটিনাটি তথ্যের জড়ো হওয়াকে একটি বড় মানসিক সমস্যা হিসেবে তুলে ধরেছেন।
আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও কোনো কোনো বিষয়ে আমাদের 'প্রখর স্মৃতিশক্তির' পরিচয় পাই। বস্তুত ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ_ এই তিনটি দেশেই জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার একটি বড় অংশজুড়েই রয়েছে অনাবশ্যক নানা তথ্যের বিপুল আয়োজন, যা পাঠককে (ও নাগরিককে) 'ক্লান্ত, ক্লান্ত' করে। বাহান্না, বাষট্টি, ছেষট্টি, ঊনসত্তর, একাত্তরের ৭ মার্চ ও ২৬ মার্চ_ জাতীয় রাজনৈতিক জীবনের এসব গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক নিয়ে বলতে গিয়ে আবেগ-উচ্ছ্বাসে যেটা হারিয়ে যায় তা হলো সাধারণ জনচৈতন্যের ও জনজীবনের ক্রমবিবর্তনশীল নিত্যদিনের সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পুরো গল্পটা আবর্তিত হতে থাকে 'আগে থেকে গল্পের সমাপ্তি কী জেনে নিয়ে' গল্প বলার মধ্যে (অর্থাৎ 'টেলিওলজিক্যাল' চরিত্রসম্পন্ন) এবং সে গল্পও আবর্তিত হতে থাকে 'নায়ককে' ঘিরে_ সেটা হতে পারে দল হিসেবে আওয়ামী লীগ, ব্যক্তিনায়ক হিসেবে মুজিব, ২৬ মার্চ, ১৭ এপ্রিল ও ১৬ ডিসেম্বরের বীরগাথা আর এসবের 'অতিরিক্ত' আয়োজনে চাপা পড়ে যায় ২৫ মার্চ_ যার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা হচ্ছে কেবল 'একটি কালরাত্রি'। এমনকি 'মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস' যেন নয়-নয়টি মাসের বিবরণ নয়, এটি যেন পূর্ব-নির্মিত রাজনৈতিক ভাবাদর্শের একটি অধীনস্থ প্রত্যয়, যেন একটি দ্রুত ঘটে যাওয়া পর্ব, যার প্রতিটি দিনের কোনো বিবরণ নেই বা যা হারিয়ে যায় শেষ পর্যন্ত ডিসেম্বরের সামরিক যুদ্ধের খাতওয়ারি দিনলিপির মধ্যে। যদি ইতিহাসকে 'ক্রম-প্রকাশ্য' (আগে থেকে অনুমান সম্ভব নয় এমন) কাহিনী হিসেবে বর্ণনা করা যেত তাহলে আমরা অন্যরকম ইতিহাসের বয়ান পেতাম। সে ক্ষেত্রে আরও বেশি জীবন্ত, সত্যাশ্রয়ী ও মানবিক দেখাত ওপরের বর্ণিত জাতীয় মাইলফলকগুলো। সেখানেও স্বাধীনতার ইচ্ছা কীভাবে দানা বেঁধে উঠছিল তাকে ধরার চেষ্টা থাকত; কিন্তু সেটা হতো সরলীকৃত জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের চেয়ে আরও জটিল, বহু-সম্ভাবনাময় এবং বহু-ইঙ্গিতময় বয়ান। সেখানে উত্থান-পতন, সংশয়-দোলাচল, অস্থিরতা ও গণজাগরণ থাকত সব মানবিক বাস্তবতা নিয়ে। সেটি হতো না কেবল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা সমরকৌশলের বিবরণ মাত্র। এ কারণেই 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' (বা চেতনাগুলো) এসব কথাকে কখনোই আমরা ঘটনাপরম্পরায় শনাক্ত করতে পারিনি এবং এ জন্যই (আমার ধারণা) আমাদের মৌলিক সাংবিধানিক প্রত্যয়গুলোতে যেমন : বাঙালি জাতীয়তাবাদের 'বাঙালিত্ব', সমাজতন্ত্রের 'অভিপ্রায়', গণতন্ত্রের 'বৈশিষ্ট্য' বা ধর্মনিরপেক্ষতার 'মানে কী'_ এ নিয়ে আজ পর্যন্ত আমাদের ইতিহাসের ভেতর থেকে উঠে আসা কোনো 'সংজ্ঞাকে' আমরা আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক ডিসকোর্সে তুলে ধরতে পারিনি বা তা নিয়ে সুস্থ বিতর্ক করতে পারিনি। এটা সম্ভব হতো যদি আমরা বাংলাদেশের 'জনগণের ইতিহাসকে' (পিপলস হিস্ট্রি অব বাংলাদেশ) আমাদের ইতিহাস চর্চার প্রধান বিষয় হিসেবে শনাক্ত করতাম। তা না করে আমরা যা করেছি (কিছু স্মরণীয় ব্যতিক্রম বাদ দিলে, যেমন বদরুদ্দীন উমরের 'ভাষা আন্দোলন' বিষয়ক গবেষণা) তা হলো একটি (নতুন) রাষ্ট্রের জন্মবৃত্তান্ত লেখার চেষ্টা। 'রাষ্ট্র' অবশ্যই জনগণের ইতিহাস লেখার একটি অংশ; কিন্তু সেটিই একমাত্র ও প্রধান অংশ নয়।
৩. গণহত্যা নিয়ে পাঠ ও অপাঠ
'রাষ্ট্রীয় ইতিহাস' বনাম 'জনগণের ইতিহাস' এই প্রতিস্থাপনাটি সবচেয়ে বেশি করে প্রকট হয়ে ওঠে যখন আমরা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বা তার পরের ৯ মাসের ক্রমাগত গণহত্যা ও গণসন্ত্রাসের বিবরণী পাঠ করি। আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রের অষ্টম খণ্ড, যেখানে সংকলিত হয়েছে 'গণহত্যা, শরণার্থী শিবির ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা'। এর ভূমিকায় সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান জানিয়েছেন, 'বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে প্রায় সাড়ে তিন লাখ পৃষ্ঠার দলিল ও তথ্য জমা হয়েছে। এর ভেতর ১৫ হাজার পৃষ্ঠা ছাপা হচ্ছে। বাকি দলিল ও তথ্যাদি ছাপার বাইরে রয়ে যাবে'। দুঃখের বিষয়, বাদবাকি দলিল ও তথ্যাদি গ্রন্থিত আকারে আমরা এখনও পাইনি বা পেলেও হয়তো অত্যন্ত আংশিকভাবে পেয়েছি। সবচেয়ে বড় কথা, এ অষ্টম খণ্ডটির কোনো ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থও (আমার জানা মতে) এখন পর্যন্ত বাজারে আসেনি। অষ্টম খণ্ডটিতে ২৬২টি মূল্যবান সাক্ষাৎকার রয়েছে, যার মধ্যে অধিকাংশই হলো সাধারণ মানুষের বয়ান। এ সাক্ষাৎকারগুলো সংগৃহীত আলাপের অতি সামান্য অংশ; কিন্তু এতে করেই একাত্তরের গণহত্যার যে চিত্র আমাদের সামনে ফুটে ওঠে তাতে করে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক প্রায় বিস্মৃত অধ্যায়কে প্রামাণ্যতার ভিত্তিতে আমাদের নিজেদের ও বিশ্ববাসীর জন্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে উপস্থাপন করা সম্ভব।
কী আছে এসব সাক্ষাৎকারে? প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে তা হলো, এক বৈরী রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে সংঘবদ্ধভাবে পরিচালিত সামরিক-রাজনৈতিক অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে অসহায় এক নিরপরাধ সাধারণ জনগোষ্ঠীর ভয়ার্ত দিনযাপন। একাত্তরের ৯ মাসে কীভাবে আক্ষরিক অর্থেই পুরো দেশটা এক বন্দিশিবিরে পরিণত হয়েছিল তার প্রামাণ্যতা মেলে এখানে। আমি বলেছি, প্রথম অনুভূতিটা ছিল 'ভয়ের'_ এক ভীতিবহ রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয়েছিল ওই নয় মাসে। একটি উদাহরণ নাজিমুদ্দিন মানিক বলছেন, ২৬ মার্চের ভোরবেলার কথা :
'বায়তুল মোকাররমের মোড়ে রাস্তার ওপর আরও দুটি নাম না জানা বাঙালি বীরের নশ্বর দেহ চোখে পড়ল, চোখে পড়ল জিপিওর পেছনের গেটে এক ঝুড়ি রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড আর নাড়িভুঁড়ি। তবুও আমি হেঁটে চলেছি, হেঁটে চলেছেন আমার চারপাশের মানুষজন। কেননা আমি এবং আমার চারপাশের মানুষ_ আমরা সবাই তখন বাঁচতে চাই এবং সে জন্যই আমাদের কারও প্রতি কারও কোনো খেয়াল নেই, কারও সঙ্গে কারও কোনো কথা নেই। সবার চোখেই একটা সন্ত্রস্ত ভাব। সবাই ভীতি বিহ্বল'।
প্রাথমিকভাবে যেটা ছিল ভয়ের অনুভূতি, সেটা সময়ের সঙ্গে নীরব অসহযোগিতা ও ক্রমেই সক্রিয় প্রতিবাদ প্রতিরোধে রূপ নেয়। অনেকগুলো সাক্ষাৎকারে বর্ণিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক কর্মী, সাধারণ ছাত্র, নারী, বৃদ্ধ, সাধারণ কৃষক, মেহনতি মানুষ, আলেম, ধর্মপ্রাণ মানুষের ওপর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, শারীরিক নির্যাতন, অগি্নসংযোগ ও হত্যার বিবরণ। বিশেষভাবে এসেছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের 'জাতিগতভাবে' ধ্বংস ও তাদের হত্যা করার বর্ণনা। এসব সাক্ষাৎকার একনাগাড়ে পড়াও সম্ভব নয়, এমনই সব নির্যাতনের বিবরণ দেয়া হয়েছে। যত ধরনের নারী-নির্যাতন সম্ভব, যত ধরনের হত্যা সম্ভব, যত ধরনের আক্রমণ ও লুণ্ঠন সম্ভব_ সব কিছুর নমুনা সংকলিত হয়েছে এসব গণহত্যা ও গণসন্ত্রাসের ডকুমেন্টেশনের মধ্যে।
এসব সাক্ষাৎকারে বেরিয়ে এসেছে যে, অনেক ক্ষেত্রে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অফিসার বা জওয়ানদের চেয়েও পাশবিক ভূমিকা পালন করেছে এ দেশের একটি গোষ্ঠী_ যারা রাজাকার বাহিনী, শান্তি কমিটি প্রভৃতি সাংগঠনিক আয়োজনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে মফস্বল শহরে ও গ্রামাঞ্চলে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে। ব্যক্তিগতভাবে এদের মধ্যেও কেউ কেউ কদাচিৎ সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন এমনও দৃষ্টান্ত মেলে এসব সাক্ষাৎকারে। তবে সাধারণ চিত্রটা ছিল এদের সম্পর্কে এটাই। অকাট্য সব প্রমাণ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপতৎপরতা ও সরাসরিভাবে নিরীহ-নির্দোষ মানবতার বিরুদ্ধে ক্রমাগত অপরাধে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে। ১৯৭১ সালের জুন মাসের পরের সময়ের বিবরণ যেসব সাক্ষাৎকারে দেয়া হয়েছে তাতে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে দখলদার বাহিনী ও তার সহযোগী শক্তিদের মধ্যে ক্রমাগত ভীতি সঞ্চারের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সাধারণ অবাঙালিদের ওপর বাঙালির আক্রমণেরও কিন্তু সাক্ষ্য পাওয়া যায় এসব সাক্ষাৎকারে। এ সময়ের বেশিরভাগ অত্যাচার-নির্যাতনের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা। যারা অত্যাচারিত হয়েছে তারা খুব কম উদাহরণেই সেসব তথ্য দিয়েছেন শত অত্যাচার-নির্যাতনের মুখেও। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে তারা তথ্য গোপন করেছেন বা ভুল তথ্য দিয়েছেন। এদের অনেকেই বলেছেন যে, তারা এখন শারীরিকভাবে পঙ্গু বা চলৎশক্তিহীন বা ক্রনিক কোনো ব্যাধিতে ভুগছেন বা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি দিন কাটাচ্ছেন কোনোভাবে। এসব বীরত্বময় ব্যক্তিরা প্রতিরোধের কাহিনী পড়তে গিয়ে আপনার মনে হবে_ এরাও তো ছিলেন সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা, তা তাদের সনদপত্র থাকুক বা না থাকুক। আমার প্রশ্ন, মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় কি এদেরকে অষ্টম খণ্ড থেকে শনাক্ত করে কোনো সম্মান প্রদানের ব্যবস্থা কখনো নিয়েছে? বা কোনো নিতান্ত বৈষয়িক সহায়তার হাত বাড়িয়েছে রাষ্ট্রের তরফ থেকে? আছে কি এদের নামে প্রতিটি গ্রামে কোনো স্মৃতিফলক? এ জন্যই এই লেখার শুরুর দিকে উচ্চকণ্ঠ জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ইতিহাসের বিপরীতে জন-ইতিহাসের নিস্তব্ধতার কথা বলেছি।
তবে এতসব সাক্ষ্য-প্রমাণের ধারেকাছেও যাননি এখনো যারা দেশে-বিদেশে ১৯৭১-এর গণহত্যা অস্বীকার করেন_ তারা। হার্ভার্ড গবেষক শর্মিলা বোস এদের একজন। তিনি অনায়াসে তাই লিখতে পারেন যে, নারী নির্যাতন, হত্যা, লুণ্ঠন এ জাতীয় কাজ দখলদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী করেনি বা করলেও এসবে তাদের অংশগ্রহণ ছিল সামান্যই। এ দেশের জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যারা ভেতর থেকে স্বাধীনতার বিপক্ষে কাজ করেছিল নয় মাস ধরে, তারাই বেশিরভাগ আক্রমণ-নির্যাতন করে থাকবে। এ জন্যই তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধ বলার পরিবর্তে 'গৃহযুদ্ধ' শব্দটি পছন্দ করেছেন। ক্ষেত্রবিশেষে তা সঠিক হলেও সাধারণভাবে এটি একটি অতি অসত্য পর্যবেক্ষণ। শর্মিলা বোস তার 'ফিল্ড-ওয়ার্ক'-এর ভিত্তিতে যে বইটি লিখেছেন তার নাম 'দ্য ডেড রেকনিং'। সে বইয়ে তিনি অষ্টম খণ্ডের একটি কেস স্টাডিকেও আবার নতুন করে বিচার করার প্রয়াস নেননি স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার জন্য। তিনি ব্যাপক হারের গণহত্যাকে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু অষ্টম খণ্ডের যে কোনো সাক্ষাৎকারই তার মতের বিপক্ষে যায়। তিনি ব্যাপকভাবে 'নারী ধর্ষণ'-এর বিষয়টিকেও 'অতিরঞ্জিত' বলে মনে করেছেন। আমার সামান্য হিসেবে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, শতকরা ৭০ ভাগ সাক্ষাৎকারেই সরাসরিভাবে নারী ধর্ষণের উল্লেখ রয়েছে এবং বিশেষ করে যেখানে নারীরা নিজেরা বয়ান দিয়েছেন তার প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রেই পাশবিক নারী নির্যাতনের উল্লেখ রয়েছে। এসব নারীর কারো ঠিকানা সংগ্রহ করে মুখোমুখি হতে চেষ্টা করেননি শর্মিলা বোস। গণহত্যা অস্বীকারকারী হলোকাস্ট ডিনায়ার হিসেবে তিনি পরিচিতি পেয়েছেন তার বইয়ের জন্য, বিশেষভাবে যা সমাদৃত হয়েছিল জেনারেল পারভেজ মোশাররফের পাকিস্তানে, যেখানে তিনি প্রায় সেলিব্রেটি। পারিবারিক সূত্রে তিনি নেতাজী সুভাষ বোসের ভাই শিশির কুমার বোসের মেয়ে_ ফলে তিনি বাড়তি কিছুটা মনোযোগও পেয়েছেন। আমি নির্মোহভাবে বিচার করেই এ সিদ্ধান্তে এসেছি যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রের অষ্টম খণ্ডটি অস্বীকার করে, বিশেষত একে তার গবেষণার নমুনা বয়ানে অন্তর্ভুক্ত না করে, তিনি মৌলিক অসাধুতার আশ্রয় নিয়েছেন।
২৫ মার্চের গণহত্যা বা সাধারণভাবে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ জনগোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাস-নির্যাতন সম্পর্কে নিস্তব্ধতা রয়েছে পাকিস্তানের ইতিহাস চর্চায়। এই নিস্তব্ধতা এখনো চলছে। হামিদ মীরের মতো সাহসী সাংবাদিক এর ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই, কিন্তু তারপরও এই উদাসীন্য চলছে। সে দেশের জনগণকে একাত্তরের প্রকৃত ঘটনা জানতে দেয়া হয়নি কখনো। এখনো তারা একাত্তরের গণহত্যার অধ্যায়টি সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানেন না। ২০০৭ থেকে ২০০৯ প্রায় তিন বছর বর্তমান লেখক বিশ্বব্যাংকের অর্থনীতিবিদ হিসেবে পাকিস্তানের ওপর কাজ করেছেন। পাকিস্তানের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রণালয়ে ও দফতরে তাকে যেতে হয়েছে কর্মোপলক্ষে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় আমি লক্ষ্য করেছি যে, ২৫ মার্চের গণহত্যা বা নয় মাসের অত্যাচার-নির্যাতন সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই সাধারণ পাকিস্তানিদের, এমনকি প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ আমলাদেরও। বাংলাদেশ 'বিযুক্ত হয়েছে' সামরিক শাসকদের এবং ভুট্টোর ভুলের কারণে_ এ পর্যন্ত তারা কেউ কেউ স্বীকার করেন; কিন্তু গণহত্যার আলোচনা সম্পর্কে তারা অজ্ঞ, অথবা তা জ্ঞানত বা অজ্ঞানত এড়িয়ে গেছেন। এদের মধ্যে যারা কিছুটা অসহিষ্ণু_ তারা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের জন্য ইন্দিরাকে দায়ী করেন এবং মুজিবকে সাধারণভাবে মনে করেন 'বিশ্বাসঘাতক'। পাকিস্তানের নানা শহরে পূর্ব পাকিস্তানের অনেক জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদের নামে সড়ক রয়েছে (শেরে বাংলা ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীসহ)। কিন্তু একটিও সড়ক নেই শেখ মুজিবের নামে। অফিসিয়াল এস্টাবলিশমেন্টের চোখে মুজিব এখনো 'সবচেয়ে ঘৃণিত' ব্যক্তি। ২০০৭ সালে লাহোরে সেন্সাস কার্যালয়ে নানা আপ্যায়নের মধ্যে আমার কাছে এ রকম একটি বক্তব্য জোরেশোরে তুলে ধরেছিলেন একজন উচ্চপদস্থ আমলা। আমি তাকে হাসান আসকারী রিজভীর লেখা ২০০৩ সালে প্রকাশিত 'মিলিটারি, স্টেট অ্যান্ড সোসাইটি ইন পাকিস্তান' বইটির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম। সেখানে এক জায়গায় রিজভী লিখছেন :
'(মার্চের) সামরিক পদক্ষেপ প্রতিরোধ আন্দোলনকে স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপান্তরিত করেছিল। আওয়ামী লীগের কট্টর অংশটি চেয়েছিল মার্চের শুরুতেই স্বাধীনতার ঘোষণা করতে; কিন্তু মুজিবুর রহমান তাদেরকে পিছু টেনে রেখেছিলেন। মার্চের আন্দোলনের পরে ... পাকিস্তানের সাথে যেটুকু ভঙ্গুর যোগাযোগ ছিল দেশটির, যদিওবা তার অবশিষ্ট কিছু থেকে থাকে সেসময়ে, তাও সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেল যখন সেনারা শহরে ঢুকল শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করতে।'
২৫ মার্চের গণহত্যা ছিল আমাদের সাধারণ জনচৈতন্যে তদানীন্তন পাকিস্তানের সাথে অবশিষ্ট মানসিক সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করার মুহূর্ত। এই কথাটা আমি লাহোরে কেন্দ্রীয় সেন্সাস কার্যালয়ে বিনয়ের সাথে উল্লেখ করেছিলাম। এরপর সভাকক্ষে এক ধরনের বিষণ্ন ও অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এসেছিল। ইতিহাস শুধু 'অনিবার্যতার' মাধ্যমে অগ্রসর হয় না, এর মধ্যে ক্রান্তিলগ্নের 'আকস্মিকতার' অবদানও ক্রিয়াশীল থাকে, যা নাটকীয়ভাবে ভিন্ন যুগের ভেতরে আমাদেরকে টেনে নিয়ে যায়। হ
লেখক
অর্থনীতিবিদ
প্রাবন্ধিক
http://www.samakal.net/print_edition/details.php?news=257&view=archiev&y=2013&m=03&d=26&action=main&menu_type=&option=single&news_id=336115&pub_no=1359&type=
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ১৫:২৪582569
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ১৫:২৪582569- গণহত্যার অংশীদার যারা
যতীন সরকার
____________________________________
১৯৭১ সালের ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই অবিস্মরণীয় ভাষণের মধ্য দিয়েই প্রকৃত প্রস্তাবে সেদিনকার বাংলাদেশে পাকিস্তানি শাসনের অবসান সূচিত হয়ে গিয়েছিল। কেবল ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ছাড়া আর কোথাও পাকিস্তানি পতাকা উড়তে দেখা যায়নি, গ্রাম-গঞ্জে পর্যন্ত সগৌরবে উড্ডীন হয়েছিল বাংলাদেশের মানচিত্র সমন্বিত লাল-সুবজ পতাকা। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই চলছিল দুর্বার অসহযোগ আন্দোলন।
মার্চের ১৫ তারিখে রাজনৈতিক সমাধানের ধোঁয়া তুলে তৎকালীন পাকিস্তানের জঙ্গি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এলেন ঢাকায়। এই দিনই ছাত্র-কৃষক-শ্রমিকসহ বিভিন্ন নেতার অনুরোধে দেশের ক্ষমতা তথা শাসনভার বঙ্গবন্ধু নিজের হাতে তুলে নেন। এক ঘোষণায় তিনি জানালেন, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি জনগণের কল্যাণের জন্যই এ দায়িত্ব তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। তাই ভবিষ্যৎ বংশধরদের মুক্ত মানুষ হিসেবে আত্মমর্যাদার সঙ্গে বসবাসের নিশ্চয়তা বিধান করার লক্ষ্যে যে কোনো ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকার জন্যও জনগণের প্রতি তিনি আহ্বান জানালেন।
এর পরদিন অর্থাৎ ১৬ মার্চ থেকে শুরু হলো মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা। ইয়াহিয়ার আমন্ত্রণে জুলফিকার আলী ভুেট্টা পাকিস্তান থেকে এসে এই আলোচনায় যোগ দেন। ভুট্টো ইয়াহিয়া চক্র আলোচনার নামে আসলে সময়ক্ষেপণ করছিল মাত্র। ভেতরে ভেতরে চলছিল বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালানোর প্রস্তুতি। সেই প্রস্তুতির অংশ রূপেই পাক-সেনারা এখানে-ওখানে চালাচ্ছিল নানা উস্কানিমূলক অপতৎপরতা। জয়দেবপুরে তারা তুচ্ছ অজুহাতে জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করে এবং তাতে অনেক লোক হতাহত হয়। ঢাকার মিরপুর ও রংপুরের সৈয়দপুরে বাঙালি-অবাঙালি সংঘাতের সূত্র ধরে সেনাবাহিনী গুলি চালিয়ে অনেক নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটায়। বিমানে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বহু সৈন্য ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছিল। সোয়াত জাহাজ যোগে চট্টগ্রাম বন্দরে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র এসে পেঁৗছে। বন্দরে কর্মরত বাঙালি শ্রমিকরা জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাতে অস্বীকার করে ও প্রবল প্রতিরোধের সৃষ্টি করে। ফলে ভয়াবহ সংঘর্ষে বহু বাঙালির মৃত্যু ঘটে।
মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকেরই একপর্যায়ে ইয়াহিয়ার নির্দেশ বাংলাদেশের পাক-বাহিনীর সমর অভিযান পরিকল্পনাটি চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করে। 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামের এই পরিকল্পনাটি কার্যকর করার দায়িত্ব গ্রহণ করে ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডর কুখ্যাত টিক্কা খান। তারই নির্দেশে ২৫ মার্চের মধ্য রাতের পর অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে, পাক-বাহিনী বাংলাদেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে সময়েই পিপিআরের ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে প্রেরিত এক বার্তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জানালেন, 'হয়তো এটাই আমার সর্বশেষ বার্তা, বাংলাদেশ আজ থেকে স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ যে যেখানে আছেন, আমার আহ্বান_ যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে দখলদার বাহিনীকে মোকাবেলা করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত শত্রু বাহিনীর একজন সৈন্য অবশিষ্ট থাকবে এবং যতক্ষণ না অর্জিত হবে চূড়ান্ত বিজয়, ততক্ষণ আপনারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন।' এর মধ্য দিয়েই ২৬ মার্চে শুরু হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু থেকেই পাক-বাহিনী অমানসিক বর্বরতার সঙ্গে যে গণহত্যা চালিয়েছিল, এখানে তার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে দেশ-বিদেশের সবাই অবহিত। মুজিবনগরে গঠিত বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত নয় মাসের যুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষের প্রাণ দিতে হয়েছিল, ২ লাখ মা-বোনকে দিতে হয়েছিল সম্ভ্রম বিসর্জন। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় এই, পাক-বাহিনীর এ বর্বরতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কতকগুলো সারমেয়প্রতিম কুলাঙ্গার বাঙালি সন্তানের সহযোগিতা। শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আলশামস প্রভৃতি নামে ছিল এদের পরিচয়। যাই হোক, অবশেষে একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটে চূড়ান্ত বিজয়। সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাঙালির মানসপটে জাগরূক থাকবে।
আমরা সেদিন মনে করেছিলাম, বাংলাদেশের সব শত্রুর নিপাত ঘটে গেছে। আশা করেছিলাম, স্বাধীন বাংলাদেশে আর কোনোদিন পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে না। কিন্তু অচিরেই আমদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো, আশাভঙ্গের বেদনায় আমাদের আক্রান্ত হতে হলো। স্বাধীনতার চার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই আমাদের জাতির পিতা সপরিবারে নিহত হলেন। কিছুদিন পর চার জাতীয় নেতাকে কারাগারে বন্দি অবস্থায় হত্যা করা হলো। '৭৫-এর ৭ নভেম্বর থেকে সূচিত হলো অন্যরকম খেলা। প্রতিনিয়ত চলল হত্যার পর হত্যা। এমনকি যে জেনারেল জিয়া সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাকে স্বাভাবিক মৃত্যুর অধিকারবঞ্চিত হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে হলো ঘাতকের হাতে।
আর কত বলব? প্রতিনিয়ত হত্যা, গুম করে হত্যা, ক্রসফায়ারের নামে হত্যা_ স্বাধীন বাংলাদেশে এ রকম হত্যার পর হত্যাকাণ্ড দেখে দেখে কেউ যদি বেঁচে থাকার কথাই ভুলে যায়, তাহলে তাকে কী দোষ দেওয়া যাবে? 'স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই'_ প্রয়াত নির্মল সেনের এই আকুল আকুতিটাই যেন সবার আকুতিতে পরিণত হয়েছে।
তবু, সব হত্যাকাণ্ডের মূল নায়ক ও নেপথ্য নায়কদের চিহ্নিত না করলেই নয়। স্বাধীনতার চার দশক পর সেই চিহ্নিত করার কাজটি সাধিত হয়েছে ঢাকার শাহবাগে, ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারির পঞ্চম দিনে। কাজটি করেছে একদল তরুণ। তারা ঠিক বুঝে পেয়েছে যে পরাজিত পাকিস্তানি শক্তি নেপথ্যে থেকে কলকাঠি নাড়ছে। তাদেরও নেপথ্যে আছে তারা, যারা সপ্তম নৌ-বহর পাঠিয়ে একাত্তরেই বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল। তারা পরাজিত পাকিস্তানিদের দোসর, তাদের বিশ্ব্বস্ত অনুচর এ দেশের জামায়াত-শিবিরকে মডারেট মুসলিম শক্তি আখ্যা দিয়ে ওদের জন্য জিয়ন রস জুগিয়ে যাচ্ছে। শাহবাগের তরুণ প্রজন্ম ঘোষিত 'ছয় দফা দাবি' পূরণ না হলে হত্যাকাণ্ডের আসল অপশক্তিটি ঝাড়বংশে বেড়েই যেতে থাকবে। আর যদি তরুণ প্রজন্মের আন্দোলনটি জয় যুক্ত হয়, তবেই হত্যাকাণ্ডের মূল উৎসটি শুকিয়ে যাবে। তাই ওই আন্দোলনে সবার সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে দাবিগুলো বাস্তবায়নের প্রয়াস গ্রহণ ছাড়া অন্য কোনো পথ আমাদের সামনে খোলা আছে বলে মনে হয় না। হ
লেখক :প্রাবন্ধিক
শিক্ষাবিদ
http://www.samakal.net/print_edition/details.php?news=257&view=archiev&y=2013&m=03&d=26&action=main&menu_type=&option=single&news_id=336116&pub_no=1359&type=
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ১৫:২৫582570
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ১৫:২৫582570- বাঙালির অস্তিত্বের প্রশ্নে
আকবর আলি খান
_______________________________
১৯৭১ সালের গণহত্যা মানুষের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায়। এ ধরনের গণহত্যার একটা অন্যতম কারণ হলো যে সকল সেনানায়ক দ্বারা পাকিস্তান শাসিত হচ্ছিল, তাদের কোনো মূল্যবোধে বিশ্বাস ছিল না। তারা কেবল তাদের স্বার্থ হাসিল নিয়েই উন্মত্ত ছিল এবং তা হাসিলের জন্য গণহত্যা করতেও পিছপা হয়নি। কিন্তু পাকিস্তানের যে মৌলিক সঙ্কট_ সেটা গণহত্যার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব ছিল না। এর ফলে যা হয়েছে তা হলো_ একাত্তরের গণহত্যায় শুধু যে দেশের সেরা মানুষরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তা নয়, এ গণহত্যা একেবারে প্রান্তিক, দুস্থ জনগোষ্ঠী থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত আপামর জনসাধারণ তথা বাঙালি জাতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ গণহত্যার ফলে আমরা যেমন আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হারিয়েছি, তেমনি হারিয়েছি অসংখ্য সাধারণ নিরপরাধ মানুষকে। বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ইচ্ছা ছাড়া যাদের হত্যার কোনো কারণ থাকতে পারে না।
গণহত্যা যারা করে, অবশ্যই তাদের বিচার হতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রাজনীতির কূটচক্রে পাকিস্তানি যেসব সেনা কর্মকর্তা এর সঙ্গে জড়িত ছিল, তাদের বিচার আমরা করতে পারিনি। এটা আমাদের একটা বড় ব্যর্থতা। সম্ভবত সে কারণেই; যেহেতু পাকিস্তানি মূল আসামিদের বিচার করা যায়নি, এর দোসরদের বিচার করতে তাই আমাদের বিলম্ব হচ্ছে। হয়তো এই রাজাকার-আলবদরদের বিচার আরও দ্রুত সম্ভব হতো যদি আরও আগেই পাকিস্তানি সমর নায়কদের বিচার করা সম্ভব হতো। বিশ্ব কূটনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তেমন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি। আরেকটা বিষয় হলো এরা শুধু বাংলাদেশেরই নয়, পাকিস্তানেরও অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশের নিরপরাধ মানুষের ওপর যেমন নানা ধরনের অত্যাচার চালিয়েছিল, সে ধরনের সমস্যা কিন্তু পাকিস্তানের ভেতরেও এরা সংঘটিত করেছে। বাঙালিদের ওপর তারা যে ধরনের নৃশংসতা চালিয়েছে, তার বিচার না হওয়ার কারণেই কিন্তু পরবর্তী সময়ে একই ধারায় এরা পাকিস্তানের ভেতরেও একই ধরনের নির্মম হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তারা জড়িত হয়েছে।
এ ধরনের গণহত্যার বিচার আন্তর্জাতিক আদালত ও জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। তা না হওয়ায় বাংলাদেশে যারা গণহত্যা চালিয়েছে, তারা পাকিস্তানের ছত্রছায়ায় বেঁচে গিয়ে পাকিস্তানেরই ক্ষতি করেছে। তাদের কারণে পাকিস্তানেরও যে নিজের সত্তা_ সেটা দিনে দিনে হুমকির মুখে পড়েছে। আরেকটি ব্যাপার হলো_ এ গণহত্যার জন্য পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের বিচারের বিষয়টি অনেকটা ভারত-পাকিস্তানের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। যা আমাদের জন্য অনেক বড় দায়িত্বের বিষয় হলেও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সে দায়িত্ব পালনের জন্য কূটনৈতিক ও অবকাঠামোগতভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না। আমরা সে বিচার করতে পারিনি। আর পারিনি বলেই তাদের দোসরদের বিচারও বিলম্বিত হয়েছে নানাভাবে। এ দুটি বিষয় অবশ্যই ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
বর্তমানের এ বিচারটা হওয়া কয়েকটি কারণে জরুরি। একটি কারণ হলো_ যারা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, তাদের একটা নৈতিক দায়িত্ব ছিল জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। যেহেতু তারা যে অন্যায় কাজ করেছে সেটা কোনোদিনই স্বীকার করেনি, সেহেতু সে সুযোগ আর নেই। এটা হলো রাজনৈতিক দিক। কিন্তু নৈতিক দিক থেকেও হত্যা, ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধের বিচার না করা হলে বা রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় যদি অপরাধীরা বেঁচে যায়, তাহলে সমাজে এ ধরনের অপরাধ বাড়তেই থাকে এবং বেড়েছেও। সুতরাং নৈতিক দিক থেকেও এ বিচারটা বাঙালির জন্য অবশ্য করণীয়। আর তার চেয়েও বড় একটা ব্যাপার নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন। তা হলো আমরা জানি যে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিরা আমাদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছে, কিন্তু সম্প্রতি কিছু মহল প্রচারণা চালাচ্ছে যে, এ গণহত্যা নাকি পাকিস্তানিরা করেনি। এ গণহত্যা নাকি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। এ ধরনের যে অপপ্রচারণা চালানো হচ্ছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের শর্মিলা বসু। তিনি এবং পাকিস্তানি কিছু লেখকরা এ ধরনের বই লিখেছেন। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং বিচার না করার ফলে আমাদের ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে। এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। কাজেই বিচার করে এ গণহত্যার সত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারলে এ ধরনের অপপ্রচার সম্ভব হতো না, এ ধরনের প্রশ্নও উত্থাপিত হতো না।
যত দেরি হবে ততই বিচার প্রক্রিয়া বিঘি্নত হবে। আমার ভয় হচ্ছে বিয়ালি্লশ বছর পরে বিচার করতে গিয়ে সব অপরাধী ও সাক্ষীকে আমরা খুঁজেও পাব না, তাদের বিচারও করতে পারব না। এ জন্য বিচারের পাশাপাশি সরকারের উদ্যোগে এ গণহত্যা এবং পাকিস্তানি অত্যাচারের ওপরে একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করা। যেখানে গণহত্যার সত্য নমুনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে। তা না হলে পরে শর্মিলা বসুর মতো এক পক্ষপাতদুষ্ট ঐতিহাসিকদের দ্বারা আমাদের ইতিহাস বিকৃত হতে থাকবে। সারাদেশ থেকে সকল তথ্য সংগ্রহ করে এ শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত। যে দলিলের মধ্যে কে কখন কোথায় এসব করেছে তার উল্লেখ থাকবে। এ গণহত্যার মূল হোতা পাকিস্তানি সেনানায়কদের বিচার না করতে পারি, অন্তত তাদের কার্যকলাপ প্রকাশ পাক। আমরা যেমন বন্ধুদের সম্মান জানাচ্ছি; যারা মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সহযোগিতা করেছিলেন, ঠিক তেমনভাবে শত্রুদেরও চিহ্নিত করা জরুরি।
আমরা আমাদের ইতিহাসের বিকৃতি রোধ করার কোনো সামান্য ব্যবস্থাও করিনি। রাজনৈতিক কারণে শত্রুদের জিইয়ে রেখেছে রাজনৈতিক দলগুলো। এ বিচার তো অনেক আগেই হতে পারত। বিচারের কাজ এত বেশি বিলম্বিত হওয়ার মানেই হলো এটার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত হয়ে যাওয়া। কিন্তু গণহত্যা কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নয়, গণহত্যা একটা ফৌজদারি অপরাধ। অন্যসব অপরাধীকে আমরা যেমনভাবে ঘৃণা করি, যুদ্ধাপরাধীদেরকেও আমাদের একইভাবে ঘৃণা করতে হবে। তারাও একই ধরনের ফৌজদারি অপরাধে অপরাধী।
আরেকটি বিষয় হলো যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য একটা স্থায়ী সংগঠন বা কমিটি থাকা উচিত। কারণ এটা যে, আমরা আগামী এক বছর বা দুই বছরের মধ্যে এ বিচার সম্পন্ন করতে পারব তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানিরা যে অপরাধ করেছে, তার দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ করে তাদের চিহ্নিত করা দরকার। তাদের যদি নাও পাওয়া যায়, তবু তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের বিচার করা উচিত। আর সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি তা হলো_ এ ব্যাপারে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
সম্প্রতি শাহবাগে এ নীরব ঐক্যের যে হঠাৎ বিস্ফোরণ আমরা দেখলাম, তা অভূতপূর্ব। শাহবাগ একটি মহৎ আবেগের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আবেগ সবসময় দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আমাদের যেটা দরকার তা হলো এ আন্দোলনকে একটা দীর্ঘস্থায়ী কার্যকর ব্যবস্থায় রূপান্তর করা। এ মহৎ আবেগের ভিত্তিতে আমাদের কাঠামোগুলো, প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলা উচিত_ যারা আসলে এ কাজটি করবে, যারা বিচারকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এবং শুধু বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীই নয়, পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কেও আমাদের কাগজপত্র অবশ্যই থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে আরেকটি বড় দুর্বলতা আমি মনে করি_ যাদের সহযোগিতায় এ সমস্ত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং যারা এগুলোকে আশকারা দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধেও অবশ্যই অভিযোগ গঠন করতে হবে। এ জন্য সরকারের সঙ্গে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আবার সরকারের পক্ষ থেকেও এ ব্যাপারে ঐকমত্য গঠন করতে হবে। এবং উভয় ক্ষেত্রেই বিষয়টাকে রাজনীতির বাইরে নিয়ে যেতে হবে। রাজনীতির ভেতরে থাকলে কখনই এ বিচার সঠিকভাবে বিকশিত হবে না। কারণ আমি দেখেছি সরকার, বিরোধী দল আবং আসামি পক্ষ সকলেই আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন। তারা প্রত্যেকেই এমন সব বক্তব্য দিয়েছেন, যা এ বিচারকে বিঘি্নত করে। এ ধরনের কথা বন্ধ করা উচিত এবং বিষয়টাকে রাজনৈতিকভাবে না দেখে সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। ৪২ বছরের অনৈতিক পরিস্থিতির চাপে যে আবেগের সৃষ্টি হয়েছে, সে আবেগকে সুসংহত করতে হবে, শোককে শক্তিতে রূপান্তর করতে হবে।
আমি আশাবাদী। এর কারণ হলো সত্য কখনও চাপা থাকে না। আর সত্য আমাদের পক্ষে। আমি নিশ্চিত যে, গণহত্যা হয়েছে_ সেটা ইতিহাসে একটা জঘন্যতম অধ্যায় হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি মনে করি যে, বাংলাদেশ চিরদিনের জন্যই এসেছে। এ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত যে, এর কোনো পরিবর্তন কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। বাঙালি জাতির কোনো ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, এমন বিষয় নিয়ে আমি চিন্তিত নই। আমি চিন্তিত যে, আমাদের ইতিহাসকে বিকৃত করা হচ্ছে। আমি চিন্তিত এ কারণে যে, অপরাধীদের যদি শাস্তি না দেওয়া হয়, তাহলে ভবিষ্যতের জন্য আরও অপরাধকে উৎসাহিত করা হবে। তাই আমি নৈতিক এবং আইনগত কারণে উদ্বিগ্ন। কিন্তু এ কথা বলছি, বাঙালি এখন যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, এ জাতিকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। হ
লেখক :প্রাবন্ধিক
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের
সাবেক উপদেষ্টা
http://www.samakal.net/print_edition/details.php?news=257&view=archiev&y=2013&m=03&d=26&action=main&menu_type=&option=single&news_id=336117&pub_no=1359&type=
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ১৬:০১582571
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ১৬:০১582571- পাকিস্তানিদের রাজনীতি ও গণহত্যা
আনু মুহাম্মদ
_____________________________
১৯৪৭ সালে রক্তাক্ত ভারত বিভাগে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে ভোটের মাধ্যমেই পূর্ব বাংলা যুক্ত হয় পাকিস্তানে। এই সময়ে বিপুলসংখ্যক মুসলমান ভারত থেকে পাকিস্তানে এবং বিপুলসংখ্যক হিন্দুর পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে যাওয়ার ঘটনা শান্তিপূর্ণ ও স্বেচ্ছায় ঘটেনি। বরং তা এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়, রক্তপাত ও বিদ্বেষের জন্ম দেয়। যার রেশ পুরো অঞ্চলের রাজনীতিতে এখনও বিষাক্ত ছায়া হয়ে আছে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে ইউরোপের পুরনো ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। যুদ্ধের পর বহু উপনিবেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হতে থাকে। এই সময়ে অন্য অনেক দেশের মতো ভারত ও পাকিস্তানও ব্রিটিশ আধিপত্য থেকে মুক্তিলাভ করে। ততদিনে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র বদলে গেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তখন অস্তমিত, বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নতুন সর্দার হিসেবে ততদিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবির্ভূত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একমাত্র অক্ষত বৃহৎ শক্তি তখন ব্রিটিশ সাবেক উপনিবেশগুলোয় নিজের ক্ষমতার জাল তৈরিতে নতুন আয়োজনে লিপ্ত হয়।
ভারত প্রথম থেকে স্থিতিশীলতা ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে সক্ষম হলেও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তা হতে পারেনি। প্রথম থেকেই ক্রমান্বয়ে অস্থিতিশীলতা ও পরে সামরিক শাসন তাকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে পঙ্গু করে দেয়। ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক রাখলেও তাদের আনুগত্যের মধ্যে প্রবেশ করেনি। বরং পরিকল্পিত ভারীশিল্পভিত্তিক উন্নয়নে ভারত ক্রমে সোভিয়েত সমর্থনে অগ্রসর হয়। আর অন্যদিকে পাকিস্তান হয়ে দাঁড়ায় এই অঞ্চলে মার্কিনি প্রধান অবলম্বন। পাকিস্তানকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদের দরকার ছিল তল্পিবাহক আমলাতন্ত্র এবং সামরিক বাহিনী। পাকিস্তানের এই দুই গোষ্ঠীই ছিল ক্ষমতার কেন্দ্রে। প্রশিক্ষণ, বিদেশি ঋণ, বিদেশ সফর, বৃত্তি ইত্যাদি মাধ্যমে এ সম্পর্কটিই পুনরুৎপাদিত হয়েছে বরাবর। এর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে রাজনৈতিক দলসহ অন্যান্য সামাজিক শক্তির তুলনায় বেঢপ মাত্রায় বিকশিত ও মোটাতাজা হয় সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্র, যাকে হামজা আলাভি বলেছেন, 'অতিবিকশিত' বা 'ওভারডেভেলপড'।
১৯৫৪ সালের মধ্যেই পাকিস্তান দুটো সামরিক চুক্তিতে যুক্ত হয়। একটি সিয়াটো, আরেকটি সেন্টো, যা বাগদাদ চুক্তি নামেও পরিচিত, পরে যা থেকে ইরাক সরে যায়। পাকিস্তান ইরান এবং তুরস্ক নিয়ে মার্কিনি সামরিক বলয় বরাবর কার্যকর ছিল। যুক্তরাষ্ট্র যখন পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য সামরিক বাহিনীর অস্ত্র প্রশিক্ষণ জোগান দেওয়ার মাধ্যমে স্থায়ী নির্ভরশীলতার বন্ধন তৈরি করছে ঠিক সেই সময়ে ভারতকেও তারা প্রতিরক্ষা সমর্থন দিয়েছে। ১৯৬২ সালে ভারত চীনের যুদ্ধের পর ভারতের সঙ্গে মার্কিন সামরিক ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। ভারত একদিকে যুক্তরাষ্ট্র, অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন দু'দিকের সমর্থনই গ্রহণ করতে থাকে।
পাকিস্তানের ক্ষমতার তিন খুঁটি_ সামন্তপ্রভু, আমলাতন্ত্র এবং সামরিক বাহিনীর সঙ্গে পরে যুক্ত হয় বাইশ পরিবার। এগুলো কেন্দ্রীভূত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, প্রধানত পাঞ্জাবে। এই রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষমতায় আবার পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বাসভূমি পূর্ব পাকিস্তানের কোনো শরিকানা ছিল না। সামরিক বাহিনীতে এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনেও আধিক্য ছিল পশ্চিমাদেরই। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ যে শোষণ, দমন-নিপীড়ন আর ভোগান্তির শিকার হয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তার সঙ্গে পেয়েছেন বাড়তি জাতিগত বিদ্বেষ, বৈষম্য আর নিপীড়ন।
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকালে ধারণা ছিল, এই দেশে মুসলমানরা, তাদের ভাষা বা গায়ের রঙ যাই থাকুক না কেন তারা সমান মর্যাদা নিয়ে থাকবে। (গরিব) মুসলমান হিসেবে (ধনী) বর্ণ হিন্দুদের কাছে অপমান ঘাড়ধাক্কা খেয়ে খেয়ে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে এই সমাধানই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। পাকিস্তানের সমর্থন ভিত্তিও অনেকখানি নির্ভরশীল ছিল বাঙালি মুসলমানের সমর্থনের ওপরই। অথচ বাঙালি মুসলমানদের অপূর্ণাঙ্গ মুসলমান হিসেবে দেখার এবং তাদের মুসলমান বানানোর জন্য বাংলা ভাষা সংস্কৃতিকে হেয় করা ছিল পাকিস্তানি শাসকদের একটি নিয়মিত চর্চা।
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই বাঙালি মুসলমানদের প্রতি অসম্মান ও তাদের 'খাঁটি মুসলমান' বানানোর চেষ্টার বহিঃপ্রকাশ ঘটে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টায়। এর বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের মানুষ নিজেদের সত্তাকেই নতুন করে আবিষ্কার করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে উচ্ছেদ করে দিয়ে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট যেসব কর্মসূচি নিয়ে আবির্ভূত হয় সেগুলো পাকিস্তানকেন্দ্রিক ক্ষমতার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই পাকিস্তানের আসল ক্ষমতার কাছে জনগণের এই নির্বাচিত ক্ষমতা টিকতে পারেনি।
১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সরাসরি প্রবেশ করল সামরিক বাহিনী। জেনারেল আইয়ুব খান প্রধান সামরিক শাসক হিসেবে পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক শাসনের অধীনে প্রবেশ করে। পুরো ষাট দশক পাকিস্তান আইয়ুব খান নেতৃত্বাধীন এই সামরিক শাসনের অধীনেই ছিল। ষাট দশকের শেষে পরবর্তী সামরিক শাসক হিসেবে ক্ষমতায় আসেন বাংলাদেশে গণহত্যার মূল চরিত্র জেনারেল ইয়াহিয়া খান।
ক্ষমতা গ্রহণের পরই জেনারেল আইয়ুব খান পুরো শাসনব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করেন এবং রাজনৈতিকভাবে পোক্ত অবস্থান নেওয়ার জন্য সুদূরপ্রসারী কর্মসূচি নেন। সামরিক বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী তার মাধ্যমেই নিজেদের একচ্ছত্র ক্ষমতার স্থিতি দেখতে পেয়েছিল। তা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র পুরো অঞ্চলে যে সামরিক ও রাজনৈতিক বলয় তৈরি করতে সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছিল সে ক্ষেত্রে পাকিস্তানে তার অনুগত স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা খুবই উপযোগী হয়েছিল।
১৯৫৬ সালে প্রণীত সংবিধান সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে বাতিল হয়। পরে 'পাকিস্তানের জন্য উপযোগী' মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় পরোক্ষ ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হয়। ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নাম দেওয়া হয় 'মৌলিক গণতন্ত্রী'। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লর্ড কর্নওয়ালিস বলেছিলেন, 'আমাদের এমন এক শ্রেণী সৃষ্টি করিতে হইবে যাহারা নিজেদের স্বার্থেই আমাদের টিকাইয়া রাখিবে।' মৌলিক গণতন্ত্রীদের পাকিস্তানের স্বৈরশাসন পাকাপোক্ত করার জন্য সে রকম এক শ্রেণী হিসেবেই গড়ে তোলা হয়েছিল।
শুধু সামরিক খাতেই যে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের বশ্যরাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল তাই নয়, উন্নয়ন ক্ষেত্রেও পাকিস্তান হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই অঞ্চলে তাদের টেস্টকেস। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড গ্রুপ এবং বিশ্বব্যাংক। ষাট দশকে পশ্চিম পাকিস্তান বিশেষত পাঞ্জাবকেন্দ্রিক কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়ন ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসূচি নেওয়া হয়। সারা পাকিস্তানের তুলনায় পাঞ্জাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয় ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। আর পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় সামগ্রিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় বরাদ্দ অনুপাত অনেক বেশি ছিল। পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রধান রফতানি পণ্য ছিল পাট। পাট থেকেই পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার বড় অংশ আসত। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তান বা পাঞ্জাবকেন্দ্রিক উন্নয়ন তৎপরতায়। এ ছাড়া পূর্ব পাকিস্তান থেকে সরকার যে রাজস্ব আয় করত তার তুলনায় অনেক কম ব্যয় হতো এখানকার উন্নয়ন কর্মসূচিতে। আর অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের আয়ের তুলনায় ব্যয় হতো অনেক বেশি। সরকারি ব্যয়ের প্রধান ভাগিদার ছিল সামরিক বেসামরিক প্রশাসন, সেখানে আবার ছিল প্রথমত অবাঙালি, দ্বিতীয়ত পাঞ্জাবিদের আধিক্য।
পাকিস্তানের ভেতর এরকম অসম উন্নয়ন গতি এবং বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি ও কর্মসূচিই ষাট দশকে বাংলাদেশের রাজনীতির ভাব ও ভাষা নির্ধারণে মূল ভূমিকা পালন করে। বৈষম্য ও বঞ্চনা শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। আগেই বলেছি, সাংস্কৃতিক অবজ্ঞা, বৈষম্যও প্রকট হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বাঙালিদের নিচু চোখে দেখা এবং বাঙালি মুসলমানদের মুসলমান হিসেবেই স্বীকৃতি দানে কার্পণ্য বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, যা বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে আত্মপরিচয়ের নতুন উপলব্ধি সৃষ্টি করে কিংবা পাকিস্তান জাতির ভঙ্গুর ভিত্তি সম্পর্কে সজাগ করে। বাঙালি মুসলমান তার বাঙালি পরিচয় এবং তার শেকড় নিয়ে মনোযোগী হয়ে উঠে।
পঞ্চাশ ও ষাট দশকে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এখানে একটি উল্লেখযোগ্য আকারের মধ্যবিত্ত বিশেষত শিক্ষক, উকিল, পেশাজীবী, শিক্ষার্থী গোষ্ঠী যেমন গড়ে উঠেছিল, তেমনি কিছু শিল্পায়নের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল একটি শিল্প শ্রমিক শ্রেণী। এই মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীই ষাট দশকে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান দুটি ভিত্তি ছিল। মৌলিক গণতন্ত্রীদের দাপটের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিবাদও ক্রমে বিস্তৃত হয়।
জাতিগত নিপীড়ন ও বৈষম্য উপলব্ধি এবং সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বিষয়ে নতুন মনোযোগে মধ্যবিত্তের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন বিদ্বৎসমাজ। ১ বৈশাখ, রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপন প্রতিবাদী কর্মসূচি হিসেবে শুরু হয় এবং ক্রমে তা ব্যাপকতা লাভ করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধারা শেকড় গাড়ে এই মধ্যবিত্তের মধ্যেই এবং তার প্রকাশ বিদ্বৎসমাজ থেকেই ঘটে। বিপ্লবী রাজনীতির মতাদর্শিক সংকট তার প্রভাব ক্রমে খর্ব করে এবং তার বিশাল অর্জনও যুক্ত হয় জাতীয়তাবাদী ধারায়।
১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত সর্বজনীন নির্বাচনে বাঙালি ও নিপীড়িত অঞ্চলের রাজনৈতিক শক্তি প্রবলভাবে নিজেকে প্রকাশ করল। সামরিক বাহিনী, আমলাতন্ত্র, বাইশ পরিবার ও সামন্তপ্রভুদের মধ্যে কেন্দ্রীভূত পাকিস্তানের ক্ষমতার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর হাতে গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর ছিল অসম্ভব চিন্তা বা দুঃস্বপ্নের বিষয়। এরকম কোনো সম্ভাবনার যাতে আর কোনো চিহ্ন না থাকে সে জন্য ক্ষমতার হস্তান্তরের বদলে তারা বেছে নিল গণহত্যার পথ। এই বর্বরতার সহযোগী হলো এ দেশেরই কিছু কুলাঙ্গার। নিরস্ত্র নারী-পুরুষের লড়াইয়ে অসাধারণ গৌরব নিয়ে জন্ম নিল বাংলাদেশ। গণহত্যাসহ বর্বরতার অমোচনীয় কলঙ্ক নিয়ে ভেঙে পড়ল পাকিস্তান রাষ্ট্র। হ
লেখক
প্রাবন্ধিক
অর্থনীতিবিদ
http://www.samakal.net/print_edition/details.php?news=257&view=archiev&y=2013&m=03&d=26&action=main&menu_type=&option=single&news_id=336118&pub_no=1359&type=
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ১৬:০২582572
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ১৬:০২582572- স্মৃতির দায়, অনুভবের দায়
মফিদুল হক
___________________________________________
১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাক বাহিনী ও তদীয় দোসরদের পরিচালিত গণহত্যায় প্রাণ বলিদান ঘটেছিল ত্রিশ লক্ষ মানুষের। যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তিন লক্ষাধিক নারী এবং দেশত্যাগ করে উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল প্রায় এক কোটি নাগরিককে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে ব্যাপকভাবে সংঘটিত নিষ্ঠুরতার পরিচয় সাধারণত এমনি এক বাক্যে প্রকাশ করা হয়, এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায় এমন যেখানে সংখ্যা দিয়ে নিষ্ঠুরতা পরিমাপের প্রয়াস নেওয়া হয়; কিন্তু সংখ্যা কি আদৌ আমাদের বয়ে নিয়ে যেতে পারে বেদনার সেই অতল সাগরের গভীরে; আমরা কি সংখ্যা দিয়ে অনুভব করতে পারব মানবদুর্ভাগ্যের বিপুলতা, প্রতিটি মানুষের বেদনা? করতে যে পারা যায় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে সংখ্যাকে চ্যালেঞ্জ করা, সংখ্যা নিয়ে রঙ্গ-তামাশা করা, সেই প্রবণতাও আমরা দেখি। যারা এমনটা করে থাকেন, তাদের সবাই যে অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে করেন, তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে ভেতরের কোনো জ্বালা অথবা বিভ্রান্তির চোরাস্রোতে ঘুরপাক খেতে খেতে কেউ এমনটা করেন; যেমন দেখা গিয়েছিল এবারকার জাতীয় কবিতা উৎসবের এক প্রবন্ধ-পাঠকের ক্ষেত্রে। আবার উদ্দেশ্যমূলকভাবে সংখ্যা ঘিরে বিভ্রান্তি ছড়ানোর আয়োজনও তো বেশ প্রবল। এমনটা যারা করেন তাদের অবস্থান আমাদের জানা, তাদের হোতারা আজ বিচারের কাঠগড়ায়, গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে অভিযুক্ত। যে-তিন অভিযুক্তের ক্ষেত্রে বিচার সম্পন্ন হয়েছে, সেখানে বিজ্ঞ আদালত লক্ষ্য করেছেন, বাংলাদেশে একাত্তরে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল এবং আদালত বলেছেন, "এর ফলে ৩ মিলিয়ন মানুষ হত্যার শিকার হয়েছে, প্রায় সিকি-মিলিয়ন নারী ধর্ষিত হয়েছে, ১০ মিলিয়ন মানুষ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে এবং আরো কয়েক মিলিয়ন দেশের অভ্যন্তরে আশ্রয়চ্যুত হয়েছেন।" আদালতে বাদীপক্ষের কেউ, এমনকি পালের গোদা গোলাম আযমের উকিল, মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি ও গণহত্যার ব্যাপকতার এই সংখ্যাগত পরিচয় চ্যালেঞ্জ করেননি। তারা সেটা স্বীকার করে নিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, তার মক্কেল এসব অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না। যুদ্ধাপরাধের বিচারের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক বাস্তবতার এমনি এক সার্বজনীন স্বীকৃতি জাতি অর্জন করতে পারল এবং সেটা এক ঐতিহাসিক সাফল্য। কিন্তু সংখ্যার মধ্য দিয়ে যে ব্যাপকতা ও নিষ্ঠুরতার প্রকাশ, সেই বেদনার পরিমাপ আমরা কীভাবে গ্রহণ করব?
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ইহুদি-নিধনের অন্যতম নায়ক অ্যাডল্ফ আইখম্যানের বিচারকালে ইসরায়েলের আদালতে উপস্থিত ছিলেন সাইমন ভিজেনথাল। গণহত্যা নিয়ে গবেষণা ও গণহত্যাকারীদের স্বরূপ উদ্ঘাটনে তিনি প্রায় ভূতগ্রস্তের মতো কাজ করেছেন এবং আর্জেন্টিনায় বেনামে আত্মগোপনরত নাৎসি যুদ্ধাপরাধী আইখম্যানের স্বরূপ তিনিই উদ্ঘাটন করেছিলেন। আদালতে অভিযোগনামা পাঠের পর রীতি অনুযায়ী অভিযুক্তকে বিচারক জিজ্ঞাসা করেন_ তিনি দোষী, কি নির্দোষ। এ সময়ে, সাইমন তার পাশে বসা মার্কিন সাংবাদিককে ফিসফিস করে বলেছিলেন, 'আমার মনে হয়, বিচারকের এই কথাটা ষাট লক্ষবার উচ্চারণ করা উচিত।' পরদিন বিশ্বব্যাপী প্রচার পায় সাইমন ভিজেনথালের এই উক্তি এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ষাট লক্ষ ইহুদি হত্যার নিষ্ঠুরতা অনুরণন পায় দুনিয়াজুড়ে। গোলাম আযমের বিরুদ্ধে যখন অভিযোগনামা পাঠ সমাপন করেছিলেন মাননীয় বিচারক এবং জানতে চেয়েছিলেন, তিনি দোষী, কি নির্দোষ_ সেই প্রশ্নও তাই উচ্চারিত হওয়ার দরকার ছিল ত্রিশ লক্ষবার। নৃশংসতার ব্যাপকতা অনুভবের সেটা বুঝি হতে পারত এক উপায়।
কানাডা প্রবাসী বাঙালি গণিতবিদ, কৃতবিদ্য অধ্যাপক মিজানুর রহমান এমনি প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, প্রতিটি সংখ্যার পেছনে আছে একটি অবয়ব, অবয়বের সঙ্গে জড়িত আছে প্রাণ। গণহত্যায় বিলীন হয়ে সংখ্যায় পরিণত হওয়া সেই প্রতিটি অবয়বে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাটাই তো স্মৃতির দায়, আমাদের দায়। মুক্তিযুদ্ধকালে এই দায়মোচনে এক অভিনব আয়োজন করেছিল ত্রাণসংস্থা অক্সফাম। অক্সফামের হিসাবমতে, একাত্তরের অক্টোবরে উদ্বাস্তুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৯ মিলিয়ন এবং দেশের ভেতরে নিরাশ্রয় হয়েছিল আরও প্রায় ৪৯ মিলিয়ন মানুষ। এদের জীবনের করুণ পরিস্থিতির প্রতি ব্রিটিশ নাগরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অক্সফাম একটি দিবস পালন করে এবং দুর্গত মানুষের সংখ্যা জ্ঞাপনের পাশাপাশি প্রতিটি সংখ্যা অর্থ যে একজন বিশেষ মানুষ, নাম-পরিচয় বহনকারী ব্যক্তিসত্তা, সেটা বোঝাতে তারা ৫৮ মিলিয়ন নাম জড়ো করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই লক্ষ্য থেকে অক্সফাম টেলিফোন ডাইরেক্টরি সংগ্রহ করে দফতরের সামনে রাস্তায় স্তূপাকারে সাজিয়ে দেয়, টেলিফোন বইয়ে যেমন নাম-পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে, প্রতিটি নাম পৃথক মানবসত্তার অস্তিত্ব প্রকাশ করছে, তেমনি দুর্গতজনের সংখ্যার পেছনে আছে রক্তমাংসের একেকজন মানুষ।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যে বিচার চলছে, সেখানে গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের সাধারণ ও বৃহত্তর চিত্রের পাশাপাশি বিশেষ কতক অপরাধের সবিস্তার উপস্থাপন, সাক্ষ্য-প্রমাণ যাচাই ও সওয়াল-জবাব চলছে এবং সবশেষে পূর্ণাঙ্গ রায় আমরা লাভ করছি। এর মাধ্যমে ঐতিহাসিক বাস্তবতার স্বীকৃতি পাওয়া যাচ্ছে বটে, তবে আদালতের বিবেচনার বাইরে রয়ে যাবে আরও যে অগণিত নিষ্ঠুরতার কাহিনী, সেসব তুলে আনবে কে? এই প্রশ্ন তো বড় হয়ে দেখা দেয় নির্যাতিত নারীর ক্ষেত্রে। ট্রাইব্যুনালে এমনি তিন-চারটি ঘটনা ইতিমধ্যে উপস্থাপিত হয়েছে, কাদের মোল্লা ও দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর অপরাধের ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ বিবেচিত হয়েছে এবং বিজ্ঞ আদালত নির্যাতিতের সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য ক্যামেরা ট্রায়াল বা রুদ্ধদ্বার শুনানির ব্যবস্থা করেছিলেন, যেখানে কোনো সাংবাদিক অথবা পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি ছিল না। সাক্ষী সুরক্ষার এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ট্রাইবুন্যালকে ধন্যবাদ জানাতে হয়, তবে সেই সঙ্গে আমরা এটাও লক্ষ্য করি, সাক্ষী-সুরক্ষা কেবল আদালতে নিশ্চিত করলে হবে না, প্রাক-বিচার ও বিচার-উত্তর সময়েও এমনি সুরক্ষা নিশ্চিত করা দরকার। সেই সঙ্গে এটাও বিবেচ্য, সিকি মিলিয়ন নারীর বেদনা ও দুঃখ বহনের পরিচয় নিয়ে আদালতে হাজির হবেন মুষ্টিমেয় কতক নারী, কিন্তু এই সুবাদে সমাজকে তো হদিশ করতে হবে সংখ্যার পেছনের অবয়বগুলোর, তাদের নির্যাতন ভোগের ভাষ্য তো কোনো না কোনোভাবে কোথাও খচিত রাখতে হবে, যেমন কোনো কোনো বন্দিশিবিরের দেয়ালে দেখা গেছে রক্তের অক্ষরে নির্যাতিতা লিখে গেছেন তার নাম। সেই নাম মুছে গেলেও স্মৃতিতে তা কীভাবে করে রাখা যায় অক্ষয়_ এ এক বড় চ্যালেঞ্জ। নিপীড়নের শিকার নারীদের কাছে পেঁৗছতে হবে সমাজকে। সেজন্য প্রয়োজন ভিন্নতর সাধনার। একাত্তরে নারীর নিপীড়নের দুঃসহ বাস্তবতা চকিতে অবলোকন করেছেন কেউ কেউ, জীবনে যা ভুলবার নয়। মার্কিন সাময়িকী টাইম-এর সংবাদদাতা ড্যান কগিন একাধিকবার এসেছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে, বৈধ ও অবৈধভাবে, এবং অক্টোবর মাসে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তার অসাধারণ রিপোর্ট, 'পূর্ব পাকিস্তানে এমন কি আকাশও কাঁদছে।' ড্যান রিপোর্টের সূচনায় লিখেছিলেন :
"ঢাকার নিষ্প্রভ ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে তারকাঁটা-ঘেরা এক সাদামাটা ভবনের সামনে প্রহরায় রয়েছে দুই সৈনিক। একদা যা ছিল গুদামঘর, তা এখন একটি বিশেষ কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, ভয়ঙ্করতার এক হারেম, যেখানে গত মার্চে পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ৫৬৩ জন বাঙালি নারীকে আটক রাখা হয়েছে। এদের সবাই তিন থেকে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা, অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত শিক্ষিত নারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাস ও শহরের বিভিন্ন বাসা থেকে তাদের ধরে আনা হয়েছে এবং তাদের বেশিরভাগ এখন হিস্টিরিক্যাল, অর্ধ-উন্মাদ, বরবাদ হয়ে গেছে তাদের জীবন। এক মাস আগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর সেনাবাহিনী স্থানীয় ডাক্তারদের সাহায্য নিয়ে এদের গর্ভপাত ঘটাবার চেষ্টা করেছে, যেন এর পর বন্দি মেয়েদের ছেড়ে দেয়া যায়। কিন্তু ঢাকার চিকিৎসক-বৃত্তে অথবা সামরিক ডাক্তারদের মধ্যে কেউ এই দায়িত্ব নিতে চাইছেন না। হয় বলছেন, আহতদের সেবায় তারা খুব ব্যস্ত কিংবা এমন কাজের সঙ্গে জড়িত হতে চাইছেন না। এমতাবস্থায় সামরিক বাহিনী সপ্তাহকাল ধরে তরুণী নারীদের একে একে মুক্ত করছে। এ পর্যন্ত ৭৫ জনকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। গোপন মুক্তিদানের অযোগ্য অতি-অপ্রকৃতিস্থদের ক্ষেত্রে কী ঘটবে তা অনিশ্চিত রয়েছে।
কয়েক সপ্তাহ আগে একজন বিদেশি কূটনীতিক ঢাকার এক ককটেল পার্টিতে সতর্কতার সঙ্গে লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির কে. নিয়াজির কাছে সৈনিকদের লালসার বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। ছয় ফুট দীর্ঘ মোটাসোটা গড়নের জেনারেল কাঁধ
ঝাঁকিয়ে চোখ টিপে হাসতে হাসতে কূটনীতিককে বললেন, 'ছোকরারা তো ছোকরাই থাকবে, বয়েজ উইল বি বয়েজ, কী বলেন'?"
এখানেও আমরা পাই সংখ্যা, পাই ৫৬৩, তার থেকে বাদ পড়ে ৭৫, কিন্তু জানতে পারি না কিছুই, কী হয়েছিল সেই তরুণীদের, কোথায় গিয়েছিলেন তারা, হদিশ তো কোনোভাবে খুঁজে পাই না সংখ্যার পেছনের অবয়বের, প্রাণের। এমনি আরেক ঘটনা আমরা জানতে পাই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাজের সুবাদে, ছাত্রছাত্রীদের সংগৃহীত একাত্তরের প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্যে। জামালপুর থেকে স্কুল-বালক এম. জিল্লুর রহমান জামিল লিখে পাঠিয়েছিল তার পিতার কাছ থেকে শোনা অভিজ্ঞতার কথা। পিতা তখন ছিলেন তারই বয়সী এক কিশোর, জামালপুর শহর-সংলগ্ন মুরাদাবাদ গ্রামে তাদের বাস, যুদ্ধের কারণে দুঃসহ হয়ে ওঠা জীবনে বালককেও পালন করতে হয় নানা দায়িত্ব, তার একটি ছিল মাঝে-মধ্যে দুধ নিয়ে জামালপুর শহরে গিয়ে বিক্রি করা। পরিবারের সমর্থ-জোয়ান কিংবা অন্য বয়স্ক সদস্যদের জন্য মিলিটারি-অধ্যুষিত জামালপুরে এমন কাজ ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় বালককেই পালন করতে হয় দায়িত্ব। একদিন দুধ নিয়ে যাওয়ার সময় থানায় ঘাঁটি গেড়ে-বসা পাকিস্তানি ক্যাম্পের সৈনিক তাকে ডাকে, বালতিতে দুধ আছে জেনে সেটা নিয়ে নেয় এবং সদাচারের পরিচয় দিয়ে বালককে কিছু মাংসও দেয় খেতে। আর দু-আনার মুদ্রা দেয় দুধের দাম বাবদ। ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে আসে বালক, কিন্তুু চকিত দৃষ্টিতে ভেতরে যা দেখেছিল সেটা জীবনে ভোলার নয়। সেখানে ঘরে আটক ছিল তিন নারী, নির্বস্ত্র, উদ্ভ্রান্ত, শরীরে নানা ক্ষতচিহ্ন এবং দৃষ্টি সম্পূর্ণ উদাসী, শীতল। পিতা সেই দৃশ্য ভুলতে পারেননি এবং বালকপুত্র জানিয়েছে, সেই মুদ্রা পরে পিতা আর কখনও খরচ করেননি, এখনও সেটি তার সংগ্রহে রয়েছে এবং সেটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদানে তিনি আগ্রহী।
যথাসময়ে পিতা-পুত্র এসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে মুদ্রাটি দান করে গেছেন। এই মুদ্রা অনেক ঘটনার সাক্ষী, অনেক নারীর দুর্ভাগ্যের প্রত্যক্ষদর্শী। এই মুদ্রা কীভাবে হয়ে উঠতে পারে বাঙ্ময়, সেটাই আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ, স্মৃতির দায়, অনুভবের দায়।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুন্যালে চলমান বিচার প্রক্রিয়া তাই সামাজিক অনেক কর্তব্য আমাদের সামনে মেলে ধরছে। এর এক বড় দিক হচ্ছে আমাদের বীর নারীদের তত্ত্ব-তালাশ করা, তাদের পীড়ন-ভোগের যথাযথ চিত্র পুনরুদ্ধার, যেক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাদের নাম-পরিচয়, সামাজিক অবস্থানের সম্পূর্ণ সুরক্ষা প্রদান এবং যেখানে সম্ভব নির্যাতিত নারীর কণ্ঠ জোরদার করা। তবে এসব কাজ তো করতে হবে নির্যাতিতার পাশে সংবেদনশীল ও অর্থময়ভাবে দাঁড়ানোর মাধ্যমে। সেজন্য যথাযথ প্রস্তুতি বহন করে বিশেষ গুরুত্ব।
লেনিনগ্রাদ, হালে যা আবার হয়েছে সেন্ট পিটার্সবুর্গ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে সেই শহর ছিল ৯০০ দিন অবরুদ্ধ, যুদ্ধের গোলার আঘাতে যত না মৃত্যু, তার চেয়ে বেশি মৃত্যু ঘটেছে ক্ষুধা ও অপুষ্টিতে, তবু শহরের মানুষ পরাভব মানেনি। শহরের উপকণ্ঠে পিসকারভেস্কায়া সমাধিস্থানে আছে লাখো মানুষের কবর, সেখানে কালো গ্রানাইট পাথরে খোদিত রয়েছে বাণী :'কিছুই আমরা ভুলব না, কাউকে আমরা ভুলব না।'
মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জোর গলায় সেই উচ্চারণ ব্যক্ত করা ও তা কাজে পরিণত করার এখন হয়েছে সময়। হ
লেখক
প্রাবন্ধিক
http://www.samakal.net/print_edition/details.php?news=257&view=archiev&y=2013&m=03&d=26&action=main&menu_type=&option=single&news_id=336119&pub_no=1359&type=
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ১৬:০৪582573
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ১৬:০৪582573- দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা
জয়া ফারহানা
__________________________________
বিশ শতকের ইতিহাসকে অমোচনীয় কলঙ্কে কলঙ্কিত করেছে যেসব গণহত্যা, বাংলাদেশে সংঘটিত পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা, নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা, ভয়াবহতা এবং সংখ্যানুপাতের ভিত্তিতে তার মধ্যে প্রধানতম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে এত ব্যাপক গণহত্যা আর ঘটেনি, এটা ইতিহাসের স্বীকৃত সত্য। তবে কম্পুচিয়ার পলপট বাহিনী পরিচালিত গণহত্যা বাংলাদেশে '৭১-এ সংঘটিত গণহত্যার প্রায় সমতুল্য ভাবা হয় সেটা ব্যাপকতার বিচারে। নৃশংসতার মানদণ্ডে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের যোগ্য অনুচররা বাংলাদেশে যে গণহত্যা চালিয়েছে তার তুল্য দৃষ্টান্ত আর নেই। '৭১-এ বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যা কোনো একটি দেশ বা অঞ্চলের সমস্যা নয় বা ছিল না, এটা ছিল বিশ্ব মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।
সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিল পাকিস্তানের পক্ষে আন্তর্জাতিক রিপোর্ট করার জন্য। তিনি পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়ান, নিজের চোখে তাদের ধ্বংস এবং হত্যাযজ্ঞ দেখে সম্পূর্ণ ঘুরে দাঁড়ান পাকিস্তানের বিপক্ষে। মাসকারেনহাসের ভাষায়, পাকিস্তানিরা বাঙালিদের চার ভাগে ভাগ করে গণহত্যার পরিকল্পনা করেছিল। প্রথম ভাগে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, আনসারের বাঙালি সৈন্য; দ্বিতীয় ভাগে বাঙালি হিন্দু, তৃতীয় ভাগে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এবং চতুর্থ ভাগে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী। বিশ্বব্যাংকের এ অঞ্চলের তৎকালীন প্রতিনিধি ঐবহফহফৎরশ ঠধহ উবৎ ঐবরলফবহ কুষ্টিয়া শহর ঘুরে এসে বলেছিলেন, 'মনে হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আণবিক বোমায় বিস্ফোরিত কোনো শহর দেখে এলাম। শহরের প্রায় ৯০ ভাগ বাড়িঘর বিধ্বস্ত, মানুষজন সব পালিয়েছে। [তথ্যসূত্র : অচিন দেশের ডকুমেন্টারি/শাহাদুজ্জামান]
পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে সংঘটিত বর্বর গণহত্যার আরেক স্বীকারোক্তির দলিল হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট। বলা প্রয়োজন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বরতার স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য হামুদুর রহমান কমিশন গঠিত হয়নি, বরং গণহত্যাকে আড়াল করে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তৎকালীন নেতৃত্বকে যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য দায়বদ্ধ করার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছিল এ কমিশন। বাংলাদেশে সংঘটিত বর্বরতা সম্পর্কে পাকিস্তানের জনগণকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়েছিল বলে রিপোর্টে বাস্তব বর্বরতার সামান্য অংশ মাত্র প্রকাশ করা হয়েছিল। আর তাতেই খোদ পাকিস্তানের জনমানসে সৃষ্টি হয়েছিল অভিঘাত। চমকে উঠেছিল পাকিস্তানেরই মানুষ। অসউইৎজের সামনে দাঁড়িয়ে এখনও প্রতিদিন অগণন মানুষ নাৎসি বাহিনীর নৃশংসতার কথা স্মরণ করে। বিশ্বের লাখ লাখ মানুষ সেই গণহত্যাকে মনে রেখেছে। অনেক বিষয় নিয়ে বিতর্ক আছে, কিন্তু অসউইৎজ নিয়ে নেই। আর আমরা এমনি বিশ্বাসঘাতক কোনো না কোনো স্বার্থের কারণে আমাদের গণহত্যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি করি। আমাদের নেতা-নেত্রীরা এবং মগজ বিক্রি করে দেওয়া বুদ্ধিজীবীরা '৭১-এর গণহত্যার সংখ্যা কমিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেন। ৩০ লাখের জায়গায় ৩ লাখ বলতে পারলে আত্মতৃপ্তিতে ভোগেন! অথচ ১৯৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি এক সভায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ত্রুক্রদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'ওদের ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করো, বাকিরা আমাদের পা চাটবে!' একাত্তরের ৯ মাসে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের সমর নায়করা বাংলাদেশের গণহত্যা সম্পর্কে জঘন্য মিথ্যা তথ্য দিয়েছিল। বাংলাদেশে সংঘটিত নজিরবিহীন গণহত্যার দুর্ভাগ্যের সেটিও একটি কারণ। স্নায়ুযুদ্ধপীড়িত তৎকালীন বিশ্বে নৈতিকতার চেয়ে রাজনীতি হয়ে উঠেছিল তুলনামূলকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যে কারণে বাংলাদেশে গণহত্যার নিন্দাবাদে বিশ্বব্যাপী সাধারণ নাগরিক সমাজ সোচ্চার হয়ে উঠলেও বিশ্বসংঘ এবং বিশ্বের রাষ্ট্রসমাজে, রাষ্ট্রীয়ভাবে এর বিরুদ্ধে সেভাবে প্রতিবাদ ওঠেনি। স্নায়ুযুদ্ধের সেই সময়ে এবং তার পরবর্তী সময়েও বাংলাদেশে পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যার বিচারের প্রশ্নটি মাটিচাপা পড়ে যায়। কিন্তু এ দেশের হাওয়ায় যারা আগামীতে নিঃশ্বাস নেবেন_ একটু একটু করে ইতিহাসের সেই কুয়াশা তাদের সরাতেই হবে। সেই কুয়াশা সরানোর সহায়ক অনুষঙ্গ হতে পারে প্রবল, প্রচণ্ড প্রাণবন্ত একাত্তরের প্রামাণ্যচিত্রগুলো। '৭১-এর ৯ মাসে বাংলাদেশে যে নিষ্ঠুরতম গণহত্যা চলেছে, তার তুল্য গণহত্যা যে বিশ্বের ইতিহাসে বিরল সেটা বুঝতে হলেও অন্তত আলোচিত এ প্রামাণ্য ছবিগুলো দেখলে গণহত্যা সম্পর্কিত বিভ্রান্তির কুয়াশা কাটা উচিত (যদি কেউ জেগে ঘুমানোর ভান না করেন)। ধর্মের অহিফেন এবং রাজনৈতিক বিভ্রম ছড়ানো সংকটের এ সময়ে গণহত্যা সম্পর্কিত এই প্রামাণ্যচিত্রগুলো তরুণ প্রজন্মের দেখাটাও খুব জরুরি বলে মনে করছি।
১. স্টপ জেনোসাইড [পরিচালনা :জহির রায়হান]
২. নাইন মানথস টু ফ্রিডম [পরিচালনা :এস সুকদেব]
৩. লিবারেশন ফাইটার্স [পরিচালনা :আলমগীর কবির]
৪. ইনোসেন্ট মিলিয়নস [পরিচালনা :বাবুল চৌধুরী]
৫. এক সাগর রক্তের বিনিময়ে [পরিচালনা :আলমগীর কবির]
৬. রিফিউজি '৭১ [পরিচালনা :বিনয় রায়]
৭. দি কান্ট্রি মেড ফর ডিজাস্টার [পরিচালনা :রবার্ট রজার্স]
৮. ডেটলাইন বাংলাদেশ [সংকলন ও সম্পাদনা :ব্রেইন টাগ]
৯. মেজর খালেদ'স ওয়ার [পরিচালনা :ভানিয়া কেউলে]
১০. জয় বাংলা [পরিচালনা :নাগিসা ওশিমা]
১১. রহমান :দি ফাদার অব নেশন [পরিচালনা :নাগিসা ওশিমা]
১২. লুট অ্যান্ড লাস্ট [পরিচালনা :এইচএস আদভানী, সিএল কাউল, ডিএস সাইনি, রঘুনাথ শেঠ, পান্ডু রাং, রেভাঙ্কর, পিএনভি রাও, এসটি বার্কলে হিল, মুশির আহমেদ, জিআর ঠাকুর]
'গণহত্যা'র সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে এই প্রামাণ্যচিত্রগুলোতে। স্বীকারোক্তি দলিলের মতো মেজর জিয়ার ঘোষণাপত্রটিও সংযোজিত হয়েছে। যেখানে মেজর জিয়া তার ভাষণে তিনবার বঙ্গবন্ধু এবং তিনবার জয় বাংলা রণধ্বনি দিয়ে তার ঘোষণা শেষ করেছেন। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত কবি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের অষ্টম খণ্ডে' উল্লেখ আছে, শুধু ২৫ মার্চ রাতেই (অপারেশন সার্চলাইটে) অন্তত ৫০ হাজার নিরস্ত্র বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। অবশিষ্ট ৯ মাসে কি তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে মাত্র আড়াই লাখ বাঙালি নিধন হলো? অথচ এখনও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ দাবিদার একটি দল মুক্তিযুদ্ধে নিহত শহীদের সংখ্যা ৩ লাখ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ লড়াইয়ে নেমেছে। শুধু সংখ্যার বিচারে একাত্তরের গণহত্যার নৃশংসতার স্বরূপ বোঝানো যাবেও না! তবু বিস্মিত হই, মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের সব সুবিধা ভোগ করে কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের মহিমাকে মলিন করা যায় অবিরত তারা সেই চেষ্টা করে যান! ২৫ মার্চের পর ঢাকা থেকে পালিয়ে যে লাখখানেক মানুষ এপারের বুড়িগঙ্গা নদী-তীরবর্তী গ্রামগুলোতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদের অধিকাংশই সেদিন নিহত হয়েছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল, অষ্টম খণ্ড, ৩৭৬-৭৮ পৃ.)। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জিঞ্জিরা অপারেশনের কোনো তুলনা নেই সমকালীন বিশ্বে। পাক সেনারা ২ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে জিঞ্জিরা এবং বড়িশুর বাজারটি সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দেয়। চুনকুটিয়া-শুভাড্যা ধরে বড়িশুর পর্যন্ত ৫ থেকে ৭ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় নারী, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে যাকেই হাতের কাছে পেয়েছে তাকেই গুলি করে মেরেছে। ঘটিয়েছে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ এবং অগি্নসংযোগের মতো চরম বর্বরতা। [রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, একাত্তরের দশ মাস]
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের চলচ্চিত্র, সাহিত্য, সঙ্গীত সব জায়গাতেই ফ্যাসিস্ট বা নাৎসিদের বীভৎসতার গাথা রচিত হয়েছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়েও সহস্রাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সঙ্গীত এবং নাটকেও প্রতিফলিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ; কিন্তু গণহত্যার বিষয়টি উপেক্ষিতই থেকে গেছে সর্বত্র।
'৭১-এর গণহত্যা আমাদের জাতীয় অনুভূতির গভীরতম ক্ষত। এই ক্ষত আমাদের জীবন থেকে কখনও মুছবে না। অথচ মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে কম আলোচিত দিকগুলোর একটি হলো গণহত্যা। কেন? কারণ কি এই যে, এই গণহত্যায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে রাজাকার, আলবদর, আলশামস জড়িত ছিল এবং গণহত্যার বিষয়টি ধামাচাপা দিতে পারলে পাকিস্তানি সেনাদের অনুগত চরদের (রাজাকার, আলবদর, আলশামস) বিচারের প্রসঙ্গটি দুর্বল হয়ে আসে! ওয়াহিদুল হক জাহানারা ইমাম স্মারক বক্তৃতায় যথার্থই বলেছিলেন স্বাধীনতার চেতনার মধ্যে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মধ্যে গণহত্যার চেতনা প্রধান। ... একমাত্র গণহত্যার চেতনাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে
নিকষিত হেমে পরিণত করতে পারে। এসব গণহত্যা যেসব রাজাকার, আলবদর তাদের প্রভুদের (পাকিস্তান সেনাবাহিনী) সহযোগিতায় (কোথাও কোথাও পাকিস্তান সেনাবাহিনীই সহযোগী) সংঘটিত করেছে তাদের বিচারের ধারণাও চ্যালেঞ্জ হওয়া উচিত। জনসমক্ষে যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় যার বিবরণ ছাপা হয়েছে তার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ কী? ৪২ বছরে, বহু সাক্ষী, বলা যায় অধিকাংশ সাক্ষীরই তো মারা যাওয়ার কথা। চাক্ষুষ নরক দর্শনের পর মানুষের আয়ু তো এমনিতেই কমার কথা! গণহত্যার প্রাসঙ্গিক দালিলিক প্রমাণের অপ্রতুলতা গণহত্যার নায়কদের বিস্মৃতির আড়ালে নিয়ে যাচ্ছে। তার ওপর আছে সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ। গণহত্যার নায়করা যারা যাবজ্জীবন পেয়েছেন বা ভবিষ্যতে পাবেন তাদের, বন্ধু দল ক্ষমতাসীন হলে সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদের ৪৯৩ ধারা ব্যবহার করে গণহত্যার মহানায়কদের (!) মুক্ত করে দিতে পারবেন। অথচ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে পাকিস্তানের অনিবার্য পরাজয়ের মধ্য দিয়ে যখন একটি জাতির উন্মেষ স্পষ্ট হতে শুরু করে, তখন এই তিন বাহিনী (রাজাকার, আলবদর, আলশামস) ব্যাপকহারে বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা করে, তা বাস্তবায়ন করে। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রশ্ন তো তখন মীমাংসিত। তাহলে কেন তারা সেই গণহত্যার উৎসব শুরু করেছিল? উদ্দেশ্য একটাই, মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধে বিশ্বাসী একজনকেও তারা বাঁচিয়ে রাখতে চায়নি।
মিরপুরের কালাপানি, জল্লাদখানা, মুসলিম বাজারসহ বিভিন্ন জায়গায় তারা গণহারে হত্যা করে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। হোমারের আগামেমননের সেই নিষ্ঠুরতম সংলাপটিকেই তারা ধারণ করেছিল_ 'এদের একজনকেও আমরা বাঁচিয়ে রাখব না; এমনকি মায়ের গর্ভের শিশুটিকেও নয়। এদের প্রত্যেককেই হত্যা করতে হবে যেন তাদের কথা মনে করার মতো কিংবা তাদের জন্য দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলার মতো কেউই আর অবশিষ্ট না থাকে।'
কোনো সম্প্রদায়ের মানুষদের শারীরিক, মানসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, নৃতাত্তি্বকসহ সর্বতোভাবে পঙ্গু ও নিশ্চিহ্ন করতে হত্যাসহ যাবতীয় ধারাবাহিক অত্যাচার ও নির্যাতনের নিরন্তর চেষ্টার নাম 'জেনোসাইড' বা গণহত্যা, যে গণহত্যা একবারই মাত্র সংঘটিত হয়েছিল এবং সেটা একাত্তরে। ৩০ লাখ শহীদের মর্মন্তুদ যুদ্ধাভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। যে শহীদদের রক্তস্নাত দেশের ওপর দাঁড়িয়ে আমরা প্রত্যেকে যে যার কাজ করছি। আজ কেউই জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে পারতেন না, টেলিভিশনে গলা ফুলিয়ে রাজাকারবাজি অথবা পত্রিকায় যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে লিখে ক্ষমতার মসনদীয় সুখ অনুভব করতে পারতেন না, যদি সেদিন তারা তাদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার না করতেন। স্তম্ভিত হয়ে যাই, এই বাংলাদেশ স্পষ্টতই এই জঘন্যতম গণহত্যার প্রশ্নেও জাতি দু'ভাগে বিভক্ত। ইতিহাসবিদ আর জে রাসেল বাংলাদেশে একাত্তরে সংঘটিত গণহত্যার নিবিড় গবেষণার পর সমাপ্তি টেনেছেন এভাবে_ 'নিহতের সংখ্যা পরবর্তী কয়েক দশকে রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। চূড়ান্ত সংখ্যাটি যা-ই হোক ওই যুদ্ধে লাখ লাখ মানুষ অকল্পনীয় রকমের নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিল। ১৯৭২-এ পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি করা যায়নি। কারণ পাকিস্তান বলেছিল, একজন পাকিস্তানি নাগরিকেরও যদি বিচার করা হয় তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত একজন বাঙালিকেও সেখান থেকে ফিরে যেতে দেওয়া হবে না।
মুক্তিযুদ্ধের সব রকম সুফল ভোগকারী নেতা এবং বুদ্ধিজীবীরা, যারা একাত্তরে তিন লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল বলে বহু কষ্টে স্বীকার করেন, তাদের আমি দোষ দিই না। কেননা তারা তো তাদের প্রভুদেরই বাণীর প্রতিধ্বনি তুলবেন! ইন্টারভিউ উইথ হিসট্রি সংকলনে ওরিয়ানা ফালাচির কাছে ভুট্টো বলেছেন, একাত্তরে বাংলাদেশে কোনো গণহত্যা হয়নি! ফালাচির জেরার মুখে অবশেষে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন, সেখানে (বাংলাদেশ) বড়জোর হাজার পঞ্চাশেক লোক মারা গেছে। তবে এ গণহত্যা নীতিসম্মত। জাতীয় ঐক্যের খাতিরে এ ধরনের গণহত্যার প্রয়োজন ছিল। এটা 'জাস্টিফায়েড।' পাঠক লক্ষ্য করুন, এ ভুট্টোই ১৯৭৪ সালের জুনের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশে সরকারি সফরে এসে বললেন, 'শেষ মহানবীর নামে আমি আপনাদের কাছে তওবা করছি।' ঢাকায় তার প্রথম নাগরিক সভায় ভুট্টো তার স্বভাবসুলভ নাটকীয়তায় তওবার কথা ঘোষণা করেন। ১৯৭১-এ পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশে যে গণহত্যা সংঘটিত করে এই তওবা তার জন্য। আমি আপনাদের দুঃখ ও বেদনা বুঝতে পারি। '৭১-এ আপনাদের যে ক্ষতি হয়েছে, তার জন্য আমি শোক প্রকাশ করছি। _নিউইয়র্ক টাইমস (৩০ জন, ১৯৭৪)
মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে শেনবার্গ নিউইয়র্ক টাইমসের জন্য শ'খানেক প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন। 'ডেটলাইন বাংলাদেশ : নাইন্টিন সেভেন্টি ওয়ান' সেসব প্রতিবেদনের যে সংকলন প্রকাশিত হয়েছে তার বর্ণে বর্ণে প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশের নির্বিচার গণহত্যার কথা। যে এলাকাটিতে সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল একাত্তরে, সেটি খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগরে। '৭১-এর ২০ মে ৫-৬ ঘণ্টায় নির্বিচারে গুলি করে ১০ হাজার নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউট গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী শত শত নারী-পুরুষের সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে। গাছে ওঠে, পানিতে ডুব দিয়েও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে প্রাণ রক্ষা করতে পারেনি সেদিন শত শত মানুষ। তিনটি পুকুরে কয়েক হাজার মানুষ পানির নিচে ডুবে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল বলে জানান পুষ্পরানী; কিন্তু গুলিতে এর বেশিরভাগই মারা যায়। পুকুর ঘেরাও করে থাকা পাকিস্তানি সেনাদের ভয়ে পানির নিচে ডুব দিলেও শিশুরা উঠে বারবার চিৎকার করার চেষ্টা করত। তাদের কান্নার শব্দে বিপদের আশঙ্কায় অনেকে জোর করে মুখ ও মাথা চেপে শিশুদের পানির নিচে ডুবিয়ে রাখে। গুলিতে আহত কাতরাতে থাকা মানুষকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছে। তাদের গুলির আঘাতে রক্তাক্ত খোঁড়া পা নিয়ে নদী পার হতে গিয়ে ডুবে মারা গেছে অনেকে। শরণার্থীদের এ মিছিলের আরেকটি যাত্রাবিরতির স্থান ছিল সাতক্ষীরার ঝাউভাঙ্গা। চুকনগরের নৃশংস ঘটনার দু'দিন পর ২৩ মে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী এখানেও ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর। একই দিনে এখানেও প্রাণ দিয়েছিল হাজারখানেক মানুষ। [১৯৭১ চুকনগরে গণহত্যা, সম্পাদনা : মুনতাসীর মামুন]
বাংলাদেশের চারদিকে এখন কু ক্লাক্স ক্লানদের কালো মুখোশ। চোখ বুজলে দেখতে পাই মুখোশ পরা ঘাতকদের জিপ ছুটে চলেছে ঢাকার সড়কে, গলিতে, উপগলিতে। করাঘাত করছে দরোজায়, মিলিয়ে নিচ্ছে ঠিকানা। জানতে চাইছে আলতাফ মাহমুদ কৌন হ্যায়? মাটি লেপা একটি মাইক্রোবাস ছুটে যাচ্ছে ড. আলীম চৌধুরীর বাসার দিকে। চোখ বেঁধে নিচ্ছে চিরদিনের মতো। মাইক্রোবাসটি ছুটে চলেছে সাংবাদিক সিরাজউদ্দীন হোসেনের চামেলীবাগের বাসার দিকে। মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লা কায়সার, ড. ফজলে রাব্বী, সাংবাদিক সেলিনা পারভীনের বাসা হয়ে মাটি লেপা মাইক্রোবাসটি আবার ছুটে যাচ্ছে আনোয়ার পাশার বিবর্ণ ফ্ল্যাটের দিকে। ইতিহাসের সেই খেরো খাতায় পরিষ্কার অক্ষরে লেখা আছে গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো সেসব নাম। কতজনের কথা বলব? এই নামের শেষ নেই। অথচ এই মহিমা শেষ করে দিতে উদ্যত কালো হাত_ যারা জেনোসাইড, হোমিসাইড আর সুইসাইডের ব্যবধান বোঝেন না। তাই তো মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ।
ইতিহাসের বিরুদ্ধে ইতিহাস। চেতনার বিরুদ্ধে চেতনা। অথচ মুক্তিযুদ্ধের প্রধানতম চেতনা যারা আমার ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল, যারা আমার বাংলাদেশ চায়নি, যারা পাকিস্তান পালিয়ে গিয়েও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, তাদের চিহ্নিত করা। নানা ঘটনার পাকচক্রে একটা বিষবৃক্ষ বাংলাদেশের মাটিতে শিকড় গজিয়ে ডালপালা মেলার সুযোগ পেয়েছে বলেই সে বিষবৃক্ষ এই পবিত্র মাটিতে স্থায়ী দাঁড়িয়ে থেকে বাংলাদেশকে বাংলাস্তান বানিয়ে ফেলবে, কিছুতেই তা হতে দেওয়া যাবে না। একাত্তরের গণহত্যা যা এ দেশে সংঘটিত একমাত্র গণহত্যা (আর কোনো হত্যাকাণ্ড ব্যাপকতা, নৃশংসতা, নারকীয়তায় এর তুল্য নয়) বাংলাদেশ কখনও ভুলবে না। কোনো দিন না। যে অক্সিজেন জীবন বাঁচায় তার অস্তিত্ব মানুষ কি ভুলতে পারে? জাতির সবচেয়ে বড় নৈতিক প্রশ্নকে অমীমাংসিত রেখে কোনোভাবেই আমরা সামনের দিকে এগোতে পারব না। কোনো আবেগ, আক্রোশ বা প্রতিশোধ নয়, ইতিহাসের প্রতি দায়, মানবতার প্রতি দায় থেকেই এ গণহত্যাকে আমাদের স্মরণ করতে হবে। গণহত্যা বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে যেমন তৈরি হয়েছে 'গণহত্যা জাদুঘর'_ বাংলাদেশেও সেটা করতে হবে যেন হাজার বছর পরের প্রজন্ম ও একাত্তরের অত্যাচার, অপমান আর নির্যাতনের কথা ভুলে না যায়। হ
লেখক
গল্পকার
প্রাবন্ধিক
http://www.samakal.net/print_edition/details.php?news=257&view=archiev&y=2013&m=03&d=26&action=main&menu_type=&option=single&news_id=336120&pub_no=1359&type=
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ১৬:০৬582575
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ১৬:০৬582575- একাত্তরের হৃদয় খুঁড়ে বেদনা...
মুজতবা আহমেদ মুরশেদ
________________________________
একটি জাতির মৃত্যু রুখে দেওয়া ডাক বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল একাত্তরে :এবারের সংগ্রাম_ আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। কিন্তু আমাদের মুক্তির সংগ্রামের পথকে রুখতে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল এ দেশের জনপদ পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী। পাকিস্তানের কৃত্রিম অখণ্ডতা রক্ষা করতে তাদের সমর্থন জুগিয়েছিল পাকিস্তানের দৈত্যের মতো ধনী পরিবারগুলো। এই ধনীদের বেশির ভাগই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে এবং যাদের অনেকেই উঠে এসেছিল সামরিক বাহিনী থেকে। আর দু'চারটে ছিল সে সময়ের পূর্ব পাকিস্তানে। সেসব ধনিক শ্রেণীর পুঁজিস্বার্থ রক্ষা করতে পাঞ্জাবি আর বালুচ মিলিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রবেশ করেছিল আমাদের এ বাংলার শহর-বন্দর-গ্রামগঞ্জ-হাটবাজার সবখানে। নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করে তাদের উপনিবেশ কায়েম করতে। সেই উপনিবেশ পরিচালনায় তাদের প্রয়োজন ছিল জনবল, নিজের তল্পিটানা চামচা। ইতিহাসের নিরিখে নির্ণয় করে বলতে গেলে এদের চিহ্নিত করা যায় ইসলাম ধর্ম রক্ষার দোহাই গায়ে মেখে নব্য প্রজাতির দাস হিসেবে। সেই নব্য দাস শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল সে সময়ের মুসলিম লীগ এবং জামায়াতের নেতা এবং অনুসারী দিয়ে।
সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হিসেবে জেনারেল ইয়াহিয়া এবং তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের নবনিযুক্ত গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানের নেতৃত্বে পাকিস্তানি শাসকদের হাতে জন্মানো এই নব্য দাসরা বাংলার প্রতিটি ঘরের দুয়ারে হানা দিতে থাকে জানোয়ারের মুখোশ পরে। এ মুখোশগুলো ছিল রাজাকার-আলবদর-আলশামস নামে। এসব বাহিনীর সদস্যরা কখনও বাংলার স্বাধীনতাকে সমর্থন করা নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করেছিল একা, আবার কখনও পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে করে বিশাল দল নিয়ে। কেন তারা ধর্মের দোহাই পেড়ে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে এই হত্যায় শামিল হয়েছিল? এটা করেছিল তারা নিহত মানুষদের ধন-সম্পত্তি লুট করে, তাদের জায়গা-জমি দখল করে ধনী হতে এবং নিজেদের উপনিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ণভাবে মদদ জুগিয়েছিল ওই সব খুনিকে। পাকিস্তান সরকার প্রকাশিত গেজেট অনুযায়ী মুসলিম লীগ এবং জামায়াতের নেতাকর্মী সমন্বয়ে গঠিত রাজাকার-আলবদর-আলশামস ছিল পূর্ব পাকিস্তান সামরিক কমান্ডের অঁীরষরধৎু ঋড়ৎপব. অর্থাৎ পাকিস্তান সরকারের সামরিক কাঠামোভুক্ত সহায়ক বাহিনী। এ বাহিনীর মুখ্য সংগঠক এবং শীর্ষ নেতা ছিলেন মওদুদিবাদী জামায়াতের গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামী।
এই যখন ছিল রাজনৈতিক পরিকাঠামো এবং অর্থনৈতিক হিসাব নিকাশের ভিত্তিতে বাঙালি হত্যার জন্য পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ম্যাপ, তখন বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের শুরুতেই ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যরা 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে নিরস্ত্র, নিরীহ বাঙালিকে হত্যায় মেতে উঠে সংঘটিত করে ইতিহাসের নির্মম ও জঘন্যতম গণহত্যা।
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিদের গণহত্যা কেবল তুলনীয় হতে পারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান কর্তৃক গ্যাস চেম্বার এবং ফায়ারিং স্কোয়াডে ইহুদি নিধন অথবা রুয়ান্ডার গণহত্যা। হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করার শুরু থেকেই পাকিস্তানি শাসকরা চেয়েছে গণহত্যার এ নৃশংস ভয়াবহতা যেন বাইরের জগতের কেউ টের না পায়।
সানডে টাইমসের সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহ্যাস ২৫ মার্চে পাঠালেন একটা ছোট্ট রিপোর্ট_ পাকিস্তানি সৈন্যরা সব বিদেশি সাংবাদিককে ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমানে রূপসী বাংলা) বাধ্যতামূলকভাবে আটকে রেখেছে। এ রাতেই ১১টার পর সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক বাঙালি নাগরিকদের ওপর গণহত্যা পরিচালনা করেছে। রিপোর্টাররা তাদের হোটেলের জানালা দিয়ে ট্যাঙ্ক এবং ভারী অস্ত্র সজ্জিত বাহিনী যেতে দেখেছেন।
পাকিস্তানি সৈন্যরা যখন সবাইকে একখানে আটকে রাখার জন্য হন্যে হয়ে হোটেল তল্লাশি করছিল, তখন এ পুরো দলটার ভেতর মাত্র দু'জন বিদেশি সাংবাদিক পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাদের একজন হলেন নিউইয়র্ক টাইমসের সিডনি শ্যানবার্গ এবং লন্ডনভিত্তিক ডেইলি টেলিগ্রাফের সাইমন ড্রিং। সাইমন ড্রিং সর্বপ্রথম ২৬ মার্চ ভোর থেকেই সারা শহর ঘুরে গণহত্যার ভয়াবহ চিত্র নোট করেছিলেন। হোটেলে বসেই অন্য সাংবাদিকরা যে রিপোর্ট লিখেছিলেন, তার সবকিছুই পাকিস্তানি সৈন্যরা বাজেয়াপ্ত করে। কিন্তু সাইমন ড্রিং কৌশলে তার রিপোর্ট রক্ষা করতে সক্ষম হন এবং অন্য সাংবাদিকদের সঙ্গে দেশে ফিরে ৩০ মার্চ ডেইলি টেলিগ্রাফের মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীকে সর্বপ্রথম জানান পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী কর্তৃক বাঙালিদের গণহত্যার ভয়াবহতা।
৩০ মার্চ, ডেইলি টেলিগ্রাফ_ সাইমন ড্রিং :
_শুক্রবারে প্রদেশের ঢাকা এবং অন্য বেশির ভাগ শহরে এলোপাতাড়ি এবং ঠাণ্ডা মাথায় গোলাগুলির মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান এখন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের সামরিক বাহিনীর হাতে অন্ততপক্ষে সাময়িকভাবে হলেও নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সৈন্যরা মধ্যরাতের কিছু আগে ঢাকার ক্ষমতা দখলে নিয়েছে এবং তারপরই ঘণ্টা তিনেক ধরে বিনা উস্কানিতেই শহরের নির্দিষ্ট কিছু স্থান ঘেরাও করে আক্রমণ করেছে।
সকাল বেলায়ও অনেক বিল্ডিং জ্বলছিল। রাজপথ একেবারেই মরুভূমি, রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ এবং সামরিক বাহিনী তাদের দখল সমাপ্ত করেছে। সারাদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্ষুদ্র অস্ত্রের গুলি এবং কামানের গোলার আওয়াজ হয়েছে। সামরিক কেমোফ্লেজ পোশাকে সামরিক লরি এবং ট্যাঙ্কে বোঝাই হয়ে সৈন্যরা সারা শহরেই তোলপাড় করে ছুটেছে।
তাৎক্ষণিকভাবে নিহতের সংখ্যা নির্ধারণ করা যাবে না। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ভবন এবং অন্যান্য স্থানে গোলাগুলির প্রচণ্ডতা বড় অঙ্কের হতাহতের সংখ্যাকে প্রমাণ করে। সৈন্যদের পক্ষে ক্ষতির পরিমাণ ছিল না। যদি থাকেও তবে তা অতি স্বল্পই হতে পারে। কেননা, শহরে সশস্ত্র প্রতিরোধের কোনো চিহ্নই ছিল না।
_১৯৭১ সালের মার্চে কেবল দশ পেরিয়ে এগারোতে পা দেওয়া স্মৃতিটা আমার এখনও অনেক প্রখর। বেশ মনে আছে, মার্চের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতেই দিনাজপুর শহরে আমাদের বাড়ির প্রায় উল্টো দিকে উর্মীয় কুঠিতে বাস করা পাকিস্তানি মেজর রাজার তিন তলার ছাদে সৈন্যরা ভারী মেশিনগান বসিয়ে দিয়েছিল। মেশিনগানের নলটা সোজা আমাদের বাড়ির দিকে তাক করা। এর একটা কারণ হতে পারে ভয় দেখানো, যেন তার বাড়ি কেউ আক্রমণ না করে। কেননা, আমাদের বাসায় সারাদিনে শত শত দলীয় কর্মী-সমর্থক আসছেন, যাচ্ছেন। আব্বা অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আজিজুর রহমান ছিলেন এমএনএ [পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য], বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক। (১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের জারি করা পরিপত্র অনুযায়ী তিনি মুক্তিযুদ্ধের ৭ নম্বর সেক্টরের লেফটেন্যান্ট পদমর্যাদায় সিভিল অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজার নিযুক্ত হন)। সেই মেশিনগান দিয়ে ২৫ মার্চের রাতে সে কী প্রচণ্ড গুলির তোড়! মনে হচ্ছিল, এই বুঝি দরজা-জানালা ছিন্নভিন্ন করে আমরা গুলিতে খতম হয়ে যাব। পরদিন কারফিউর বিরতি হলে আমরা যখন বিধ্বস্তভাবে পথে, তখন বাসার বেশ কাছেই দুটো লাশ পড়ে থাকতে দেখি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পৃথিবীর ইতিহাসে বর্বরতম গণহত্যায় সেই প্রথম কোনো নিহতের মুখের দিকে চোখ পড়ার বেদনাবহ স্মৃতি আমার।
বেদনায় ভারাক্রান্ত বাঙালির স্মৃতির মাঝে পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে। মার্চে যে হত্যাকাণ্ডের শুরু এবং চলমানতা, তার ভয়াবহ চিত্র বা সামগ্রিক বর্বরতা পুরো দেশের সব প্রান্তের লোকজন বা অন্য দেশের মানুষ টের পায়নি। যেখানে ঘটেছে নির্মম হত্যাকাণ্ড, কেবল সেই জনপদের মানুষই উপলব্ধি করেছে সেটা। আর সেসব হত্যাকাণ্ডের স্থান থেকে বেঁচে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থী বয়ে নিয়ে গেছে বেদনার ভার। বহির্বিশ্বে পুরো চিত্রের বিস্তারিত প্রথম প্রকাশিত হলো জুন মাসে। কিন্তু এর মধ্যেই ঘটেছে অসংখ্য নির্মম ঘটনা। যেগুলো অনেক পরে সাংবাদিকদের রিপোর্টে জানা গেছে। গুটিকতক ঘটনা এখানে উল্লেখ না করলে ভয়াবহতা কল্পনাও করা সম্ভব নয়।
২৬ মার্চ_ পাকিস্তানি সৈন্যরা সাবমেশিনগান এবং গ্রেনেড চার্জ করতে করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল (বর্তমানে সার্জেন্ট জহরুল হক হল) দখল করে সব ছাত্রকে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। তারপর পুরো হল জ্বালিয়ে দেয়।
একই সময় সৈন্যরা জগন্নাথ হলের ১০৩ জন হিন্দু ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করে এবং ছাত্রদের দিয়েই হলের মাঠে লাশগুলো মাটিচাপা দেয়। রোকেয়া হলের ছাত্রীদের ধরে নিয়ে যায়। যারা পালাতে চেয়েছে, তাদের অনেকেই হলের দোতলা-তিনতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। সেই দিনেই পুরান ঢাকার সদরঘাট টার্মিনাল বিল্ডিংয়ের ছাদে মেশিনগান বসিয়ে রেঞ্জের ভেতর সবাইকে হত্যা করে। বুড়িগঙ্গা নদীতে ভেসে গেল অসংখ্য লাশ, আর বাকিগুলো পুড়িয়ে ফেলল।
২৮ মার্চ_ পুরান ঢাকার শাঁখারীবাজারের শেষপ্রান্তে মেশিনগান বসিয়ে নিরস্ত্র সাধারণ লোকজনের ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে। সেই একই দিনে রমনা কালীবাড়িতে অবস্থিত প্রাচীন হিন্দু মন্দির দখল করে প্রায় ২০০ জনকে হত্যা করে।
২ এপ্রিল_ কেরানীগঞ্জের গ্রামে ৪০ জন পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে জামায়াত নেতা কাদের মোল্লা প্রবেশ করে ৬০০ গ্রামবাসীকে হত্যা করে। কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে গ্রামবাসী আজও অভিযোগ করে। ১০ মে_ খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার অন্তর্গত চুকনগর গ্রাম। ভারত সীমান্তের কাছাকাছি এ গ্রামে একাত্তর হাজার মানুষ একত্রিত হয়েছিল। অনেকে বলেন ১০ হাজার। সবাই এখান থেকে সীমান্ত পেরিয়ে কলকাতা যাবে। কিন্তু সকাল ১০টা নাগাদ এক প্লাটুন বা তার কিছু বেশি পাকিস্তানি সৈন্য হাজির হয়ে নিরীহ মানুষদের ঘিরে ফেলে। কেউ ক্ষমা পেল না। হালকা মেশিনগান এবং অটোমেটিক রাইফেলের গুলিতে তাদের ঝাঁঝরা করে হত্যা করল সৈন্যরা। গুলি শেষ হয়ে গেলে বাকিদের বেয়নেট চার্জে সমাপ্ত করে কিলিং মিশন। হাজার হাজার মানুষের রক্তে সেদিন পাশের ভদ্রা নদী লাল হয়ে গিয়েছিল। পুরো অঞ্চলটা মৃতপুরী। মৃত শিশুরা মায়ের বুকে জড়িয়ে আছে। স্বামীকে গুলি থেকে বাঁচাতে স্ত্রী তার হাত জাপটে ধরেছে প্রিয়কে। পিতা কন্যাকে জড়িয়ে আছে।...
সৈন্যদের গণহত্যার বর্বরতার বিষয় পাকিস্তান সরকার লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু ৭ এপ্রিল নিউইয়র্ক টাইমসে এডিটরিয়াল বেরুলো 'বাংলায় রক্তগঙ্গা' শিরোনামে। লিখল, 'পাকিস্তানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির ওপর ওয়াশিংটনের প্রেসিডেন্টের নীরবতা ক্রমান্বয়ে বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়ছে, যখন কি-না পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা নির্বর্িচারে পূর্ব বাংলার জনগণ এবং স্বাধিকারকামী দলের নেতাদের সুনির্দিষ্টভাবে হত্যা করার চাক্ষুষ সাক্ষী পাহাড়সম হয়ে উঠছে।'
কিন্তু বহির্বিশ্বে বিশদভাবে প্রকাশিত হলো সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহ্যাসের মাধ্যমে। কীভাবে তিনি সেটা করেছিলেন, সেই ঘটনাটা এখানে প্রথমে বলে নেওয়া আবশ্যক। মার্চ থেকে শুরু করে মে মাস পর্যন্ত শরণার্থী হিসেবে ভারতে প্রায় পঞ্চাশ লাখ আশ্রয় নেওয়া বাঙালির মুখে ভারতীয় জনগণ ও সাংবাদিকরা জানতে শুরু করেছিল নজিরবিহীন গণহত্যার বর্বরতা। কিন্তু পাকিস্তান সরকার প্রচার করেছে_ সবকিছু ঠিক আছে। এই প্রচারটাকেই জোরদার করতে পাকিস্তান সরকার এপ্রিল মাসে ৮ জন সাংবাদিককে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণ করল। তারা সামরিক বাহিনীর সঙ্গে থেকে পুরো ঘটনার ওপর ইতিবাচক রিপোর্ট প্রকাশ করবে যে, পূর্ব পাকিস্তানে পুরো পরিস্থিতি স্বাভাবিক। তাই করলও তারা। বাদ সাধলেন একজন। এই দলে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের মর্নিং নিউজের অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর অ্যান্থনি মাসকারেনহ্যাসও ছিলেন এবং বিপত্তি ঘটল সেখানেই। তার বিবেক এতে সায় দিল না। তিনি ১৮ মে বিমানে চেপে লন্ডন পেঁৗছে সোজা সানডে টাইমসের অফিসে গিয়ে খুলে বললেন সবকিছু। চাক্ষুষ দেখাটাই সত্য রিপোর্ট হিসেবে প্রকাশ করতে চাইলেন। সানডে টাইমস তার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করলে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে ১৩ জুন তার পুরো পরিবারকে বোঁচকাবুঁচকিসহ লন্ডনে নিয়ে গেলেন। আর সেই দিনই সানডে টাইমসের প্রথম পাতায় 'গণহত্যা' শিরোনামে বহির্বিশ্বের জন্য বিশদভাবে উঠে এলো পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর গণহত্যার বীভৎসতম ঘটনা।
১৩ জুন ১৯৭১। সানডে টাইমস প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনাম করল_ জোনোসাইড।
'মার্চের শেষদিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ধারাবাহিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের জারি করা খবরটি গায়েব করে দেওয়ার হুকুমের উল্টোদিকের এটাই ভয়াবহতম বাস্তবতার চিত্র।
ঠিক এ কারণেই এ পর্যন্ত প্রায় ৫০ লাখ মানুষ ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে কলেরা এবং দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে।
আর এই সত্যটাই পূর্ব পাকিস্তান ঘুরে চাক্ষুষ করছেন সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহ্যাস যে, পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যরা কী করছে এবং তিনি পাকিস্তান থেকে চলে এসেছেন বিশ্ববাসীকে বলতে। সৈন্যরা শুধু স্বাধীন বাংলার ভাবনা ধারণকারী সমর্থকদেরই হত্যা করছে না; তারা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যদেরও হত্যা করছে। হত্যা করছে হিন্দু এবং বাঙালি মুসলমানদের। তারা হিন্দুরে হত্যা করছে কেবল তারা হিন্দু এই কারণে। গ্রামের পর গ্রাম দিচ্ছে পুড়িয়ে।'
অ্যান্থনি মাসকারেনহ্যাস তার সুবিশাল রিপোর্টে লিখছেন। তার ভেতর কিছু কিছুু উল্লেখ করলেই পুরো চিত্রটার ভয়াবহ করুণ দিকটা উঠে আসে। তার রিপোর্টে এভাবে লেখা, "... এ সবকিছু কেন করছে সৈন্যরা, তার একটাই জবাব পাওয়া যাবে যে কোনো পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অফিসারের কাছে। বলবে, এটা পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখার জন্য করা।
আমার পর্যবেক্ষণে এই উন্মুক্ত সামরিক অপারেশনের দুটো সুনির্দিষ্ট দিক রয়েছে। সবকিছু ছারখার করে দেওয়াকে যৌক্তিক করার জন্য পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের কাছে মুখস্থ বাক্য_ 'এটা হলো শুদ্ধিকরণ অভিযান এবং অন্যটা হলো পুনর্বাসন।' আর এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই তারা পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি পূর্ণাঙ্গ উপনিবেশ বানাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ...এপ্রিলের দশ দিনে আমি পূর্ব বাংলায় অবিশ্বাস্যভাবে নিজের চোখে যা দেখেছি এবং যা শুনেছি, তাতে ভয়ঙ্করভাবে এটাই সত্য যে, মাঠ পর্যায়ে সামরিক কমান্ডের দ্বারা সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ড কোনো বিচ্ছিন্ন কর্ম নয়। তারা হত্যা করছে, নারীদের ধর্ষণ করেছে অথবা বিশেষ ধরনের ছুরি দিয়ে নারীদের স্তন কেটেকুটে ফেলেছে। ভয়াবহতা থেকে শিশুও নিস্তার লাভ করেনি। সৌভাগ্যবানেরা তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছে। আর লাখো হাজারো দুর্ভাগা শিশুর চোখ উপড়ে নেওয়া হয়েছে, হাত-পা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে রাখা হয়েছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটা শ্মশানঘাট। এখানের হিন্দু ছাত্রদের বাসস্থান গায়েব। পুরান ঢাকার শাঁখারীবাজার এবং ঢাকার প্রাণকেন্দ্র রেসকোর্সে রমনার মন্দির ঘিরে থাকা দুটো হিন্দু বাসস্থান একেবারেই হাওয়া। কোনো ব্যাখ্যাই নেই যে, ঢাকা এবং পার্শ্ববর্তী শিল্প শহর নারায়ণগঞ্জে উল্লেখ করার মতো আয়তনের হিন্দু জনসংখ্যা কীভাবে একেবারেই সম্পূর্ণভাবে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল ২৬ এবং ২৭ মার্চের কারফিউর ভেতর। একইভাবে সেখানে বসবাসকারী মুসলমানদের কারফিউর সময়ে ঘিরে ফেলে গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। এই লোকগুলোকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে সুপরিকল্পিত সামরিক অপারেশনের মাধ্যমে।
এই গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে অকল্পনীয় সংখ্যায়। ... আমি বারবার একটা কথাই যে কোনো অফিসারের কাছে শুনছিলাম, 'আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পূর্ব পাকিস্তানকে শুদ্ধ করতে এবং এখান থেকে সব প্রকার বিচ্ছিন্নতাবাদী হুমকি দূর করতে; এমনকি এতে যদি আমাদের (২ মিলিয়ন) কুড়ি লাখ জনগণ হত্যা করতে হয়, তাও করব এবং এটা করব আগামী ত্রিশ বছর এই প্রদেশকে একটা উপনিবেশ হিসেবে শাসন করার জন্য।'
নবম ডিভিশনের কমান্ডিং মেজর জেনারেল শওকাত রিজার মন্তব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। 'তুমি নিশ্চিতভাবেই জানবে যে, আমরা এই কঠোর এবং অর্থ আর জনবলের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যয়বহুল পদক্ষেপটি শুধু শুধুই গ্রহণ করিনি। আমরা একটি কাজ হাতে নিয়েছি। এটা আমরা সমাপ্ত করতে যাচ্ছি এবং কোনোভাবেই অর্ধসমাপ্ত রেখে রাজনীতিবিদদের কাছে তা হস্তান্তর করা যাবে না যে, তারা পুরোটাকেই আবার গুবলেট করে ফেলে।'
পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ঠিক সেটাই করছিল পূর্ব বাংলায় গণহত্যার বীভৎসতা প্রয়োগ করে।"
অ্যান্থনি মাসকারেনহ্যাসের রিপোর্টকে সমর্থন করে সেদিন নিউইয়র্ক টাইমসে খবর বেরুলো। শিরোনাম-সৈন্যদের দ্বারা ধ্বংসযজ্ঞে পাকিস্তানিরা অভিযুক্ত। লিখল, পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তানের সাংবাদিক ঘুরে দেখল পূর্ব পাকিস্তান যখন কি-না পাকিস্তানি সৈন্যরা সেখানে বিদ্রোহ দমনে ধ্বংস চালাচ্ছে। তিনি পাকিস্তানিদের পূর্ব বাংলায় 'ইচ্ছাকৃত গণহত্যা' চালানোর জন্য অভিযুক্ত করেছেন।
এটাই সত্যি, হৃৎপিণ্ড খামচে ধরা অ্যান্থনি মাসকারেনহ্যাসের রিপোর্টটি সারাবিশ্বের মানুষের অন্তরকে আর্তনাদে মথিত করে। এই ৪২ বছর পর অনেকের কাছেই যেন সেদিনের সেই ভয়াবহতা ফিকে হয়ে গেছে। অনেকে ইচ্ছা করেই সেসব এক ফুঁতে উড়িয়ে দিতে চায়। কেউ আবার আছেন ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যার সেই নির্মমতাকে এখনকার পরিস্থিতিতে ফেলে, সেই বীভৎসতাকে হালকা করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে সচেষ্ট।
১৯৭১ সালের জুন মাসে চাপের মুখে এবং অর্থনৈতিক সহায়তা লাভের প্রয়োজনে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার রাজি হলো বিশ্বব্যাংকের একদল প্রতিনিধি পূর্ব পাকিস্তান আসার অনুমতি দিতে। দলটি পূর্ব বাংলা থেকে ফিরে গিয়ে বিশ্বব্যাংক প্রধানের কাছে গণহত্যার ভয়াবহতা নিয়ে রিপোর্ট জমা দিল। কিন্তু বিশ্বব্যাংক প্রধান রবার্ট ম্যাকনামারা সেই রিপোর্ট চোখের আড়ালে সরিয়ে রাখলেন। কিন্তু সেটা ঠিকই তার হাতের ফাঁক গলিয়ে নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত হয়।
_জুন ১৯৭১। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রিপোর্ট। দলের একজন সদস্য রিপোর্ট প্রদান করেন এই ভাষায়, 'পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর প্রতি-আক্রমণের বোমা আর গোলায় কুষ্টিয়া শহর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জার্মান শহরের মতো দেখতে লাগছে। সেই শহরের জন্য এটা ছিল একটা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।' তিনি আরও লিখেছেন, সৈন্যরা জনপদকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছে হত্যার মাধ্যমে। বিশেষত হিন্দু জনগোষ্ঠী এবং সন্দেহভাজন আওয়ামী লীগের সদস্যরা তাদের লক্ষ্যবস্তু। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে সে সময়ে পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ এবং জামায়াতের সদস্যরা বিশ্বাসঘাতক হিসেবে সহায়তা দিয়েছিল; সেটা তাত্তি্বক পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লেষণে শুরুতেই উল্লেখ করা আছে। এ সম্পর্কেও বহির্বিশ্বের পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। নিউইয়র্ক টাইমস ১৬ নভেম্বর ১৯৭১ তারিখে যে রিপোর্টটি প্রকাশ করে, তার একটুখানি এখানে উল্লেখ করা হলো। "...দক্ষিণপন্থিরা পাকিস্তানে ক্রমান্বয়ে সংগঠিত। রাজাকার হলো পশ্চিম পাকিস্তানের পুলিশ, মুসলিম লীগ এবং জামায়াতে ইসলাম দলের সদস্য এবং তাদের সমর্থক মিলে একটি সমন্বয়। ... মুসলমান এবং হিন্দুরা মিলে তাদের বিরুদ্ধে রাজাকারদের গুপ্তচরগিরি, অত্যাচার এবং হত্যার জন্য অভিযুক্ত করছে। তারা ছোট শহরগুলোতে পুলিশ হিসেবে কাজ করছে, যেখানে পাকিস্তানি সৈন্যরা সাধারণত যেতে পারে না। রাজাকাররা একই সঙ্গে বিদ্রোহী আওয়ামী লীগের নেতাদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে এবং লীগের প্রচারকে প্রতিরোধ করে নিজেদের প্রচারযন্ত্র দিয়ে। ...পাকিস্তানি সৈন্যরা কোনো স্থানে অপারেশনে যাওয়ার পূর্বে রাজাকারদের সঙ্গে তথ্যের জন্য যোগাযোগ করে থাকে।" এক নদী রক্তের বিনিময়ে যখন এই বাংলাদেশ তার পতাকা লাভ করল, তখন ঢাকা থেকে নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিনিধি ২২ ডিসেম্বর রিপোর্ট লিখলেন, "কে জানে এই পূর্ব বাংলায় কত মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে? ... হাজারো লাখো মানুষের লাশ শিয়াল আর কুকুরে সাবাড় করে সমস্ত হিসাব থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।"
এই লেখাটায় আমি উপসংহার ধরনের কোনো কিছু লিখতে পারছি না। সবকিছু আমার বুকের ভেতর আর্তনাদে থমকে আছে। হ
লেখক
কবি
গল্পকার
রাজনৈতিক বিশ্লেষক
http://www.samakal.net/print_edition/details.php?news=257&view=archiev&y=2013&m=03&d=26&action=main&menu_type=&option=single&news_id=336121&pub_no=1359&type=
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ১৬:০৮582576
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ১৬:০৮582576- তথ্যে উপাত্তে '৭১-এর নৃশংসতা
সিরাজুল ইসলাম আবেদ
______________________________________
মানুষের অন্তহীন এক স্রোত। এরা সব শরণার্থী। আমরা ৫০০ গরুর গাড়ি গুনলাম। গাড়ির দুই পাশে হেঁটে চলা মানুষ। একেকটায় সাত-আটজন। তরুণ ও বৃদ্ধ। তারা দ্রুত হাঁটতে চেষ্টা করছে। হাত ওপরে তুলছে এবং চিৎকার করতে শুরু করেছে। মনে হলো, তাদের দুরবস্থার কথা আমাদের জানাতে তারা উদ্গ্রীব।
সামনের দিককার লোকজন দৌড়ে আমাদের কাছে এলো। চিৎকার করে যেদিক থেকে এসেছে, সেদিকে আঙুল তুলে বলতে শুরু করল। আমরা কেউ বাংলাভাষী নই। কিন্তু তাদের কথা বুঝতে আমাদের সমস্যা হলো না।
যে গ্রাম তারা ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে, তা আগুনে পুড়ছে। সাদা চুলের একজন বুড়ো মানুষ আকাশের দিকে হাত তুলে ক্ষোভে কেঁদে উঠল। অঙ্গভঙ্গিতে আমাদের বলল, তার আটটি সন্তানের সব ক'টি নিহত হয়েছে।
১৯৭১ সালে ভারতে আশ্রয় নেওয়া প্রায় এক কোটি শরণার্থীর প্রতি বিশ্বসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় অক্সফাম সে বছর অক্টোবর মাসে 'দ্য টেস্টিমনি অব সিক্সটি' নামে যে প্রচারপত্র প্রকাশ করে, তাতে নরওয়েজিয়ান চার্চ রিলিফের তথ্য কর্মকর্তা রলফ র্যাঞ্জ এভাবেই বর্ণনা করেছেন তার অভিজ্ঞতা। প্রথমটায়, 'গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে ফেলা, হত্যাকাণ্ড ও ধর্ষণের গল্প' তার কাছে 'উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা' বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু শরণার্থীদের স্রোত, ঘটনার বর্ণনা, কান্না এবং আহাজারি তাদেরকেও সংক্রমিত করে। তিনি লিখেছেন, 'আমি ক্যামেরাম্যানের দিকে তাকালাম। দেখলাম, ছবি তুলতে তার কষ্ট হচ্ছে। অশ্রু সংবরণ করতে একটু পরপর চোখ মুছে তা শুকনো রাখতে হচ্ছে। ক্যামেরায় চোখ রাখতে তার নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। কিন্তু তার কান্না আরও তীব্র হয়ে উঠছে। এবং শেষ পর্যন্ত সে ক্যামেরা থেকে হাত সরিয়ে নেয়।'
হত্যাযজ্ঞ কতটা নৃশংস হলে গ্রামের পর গ্রাম প্রায় এক কোটি মানুষ ভিটেবাড়ি ছেড়ে, শত মাইল অতিক্রম করে ভিনদেশে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়! এটা ছিল তার সামান্য খণ্ডচিত্র। এমন লাখো খণ্ডচিত্র একত্র করলেও বোধ হয় সম্ভব হবে না মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর খুন, ধর্ষণ, অগি্নসংযোগ আর নির্যাতনের চিত্র পূর্ণাঙ্গ করা। বাস্তবতা, সেই চিত্রগুলোর অনেকটাই এর মধ্যে হারিয়ে গেছে। এখনও অনুল্লেখ্য রয়ে গেছে অনেক বধ্যভূমি। চিহ্নিত বধ্যভূমিও সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে।
পাকিস্তানিরা এদেশের মানুষের ওপর এ হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল ঠাণ্ডা মাথায়, পরিকল্পনা করে। রবার্ট পাইন ১৯৭২ সালে প্রকাশিত তার 'ম্যাসাকার' গ্রন্থে লিখেছেন, মূলত ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ পশ্চিম পাকিস্তানি জেনারেলরা আওয়ামী লীগ ও তাদের সমর্থকদের খতম করার সিদ্ধন্ত গ্রহণ করে। ফেব্রুয়ারি মাসের এক সেনা-বৈঠকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেন প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান_ 'ওদের ৩ মিলিয়ন খতম করে দাও। দেখবে বাদবাকিরা আমাদের হাত থেকেই খাবার নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে।' সত্যি সত্যিই ৩ মিলিয়ন অর্থাৎ ৩০ লাখ নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষকে বর্বরেরা নির্মমভাবে হত্যা করে । ধর্ষণের শিকার হয় এদেশের ৪ লাখ নারী। তাদের হত্যা তালিকায় ছিল এদেশের রাজনৈতিক নেতাকর্মী, ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, হিন্দু ধর্মাবলম্বী। আর নারীরা শিকার হয়েছিল ধর্ষণ, গণধর্ষণ শেষে হত্যার। যার সূচনা হয় ২৫ মার্চ রাতে 'অপারেশন সার্চলাইট'-এর নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং পিলখানায় ইপিআর সদস্য বাঙালি জোয়ানদের হত্যার মধ্য দিয়ে। রবার্ট পাইনের মতে, এ সপ্তাহে শুধু ঢাকাতেই ৩০ হাজার মানুষ হত্যার শিকার হয়। এর পর গণহত্যা চলতে থাকে শহর পেরিয়ে গ্রামে। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে এমন স্থান পাওয়া যাবে না, যেখানে পাকিস্তানিরা নারকীয় তাণ্ডব চালায়নি। নদীমাতৃক বাংলাদেশের সর্বত্র ভাসতে থাকে লাশ আর লাশ।
বুড়িগঙ্গা পেরিয়ে ঢাকার অপর পারে হরিহরপাড়ায় পাকিস্তানিদের একটি নির্যতন সেলের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন রবার্ট পাইন। গণহত্যার স্বরূপ, পদ্ধতি ও হত্যা করার আগে কীভাবে এসব হতভাগ্য মানুষকে রাখা হতো তার বর্ণনায় তিনি লিখেছেন, 'শুধু হত্যার পদ্ধতি নয়, মৃত্যুর পর এসব হতভাগ্য মানুষের লাশ কীভাবে গুম করা হতো সেটিও কমবেশি চোখে পড়ে। এখানে 'বন্দিশালাটি' ছিল একটি বড় ধরনের গুদাম, যা ছিল পাকিস্তান অয়েল কোম্পানির। এই গুদামে লোকজন এনে ধরে রাখা হতো, নির্যতন করা হতো এবং এক সময় খুন করে সোজা নদীতে ফেলে দেওয়া হতো। সুবিধাটি ছিল এই, নদীতে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই লাশগুলো স্রোতের টানে ভেসে যেত। এ ধরনের হত্যাকা চলত রাতের পর রাত। তার বর্ণনা অনুসারে এসব মানুষের বেশির ভাগকেই একসঙ্গে দড়িতে বেঁধে গুলি করে বা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নদীতে ফেলা হতো। এ ধরনের নারকীয় গণহত্যার উদাহরণ মেলে আরমেনিয়ায় বা ১৯৩৭ সালে জাপানি সৈন্যদের দ্বারা সংঘটিত নানজিং গণহত্যায়।
৭ জুন, দ্য আইরিশ টাইমস-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়_ সৈন্যদল প্রায় ২০০০ পুরুষকে স্ত্রী-পুত্রের কাছ থেকে সরিয়ে এনে মেশিনগান চালিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। এই গুলিবৃষ্টিতে প্রায় ৮০০ জন মারা যায়। বাকিরা মৃতের ভান করে পড়ে থাকে এই আশায় যে, সৈন্যরা তাদের ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু সেনাবাহিনী বাচ্চাদের খেলাঘরের মতো মৃত ও জীবিত সবাইকে একত্রিত করে তাদের ওপর পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। ভাগ্যক্রমে তখন সন্ধ্যা হওয়ায় কিছু লোক জ্বলন্ত শরীর নিয়েই জঙ্গলে দৌড়ে পালায়। সাধরণ মানুষকে ছলনায় ভুলিয়ে পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মার পলি-জমা ছোট গ্রাম মাঝদিয়া ও মাছপাড়ায় গণহত্যা চালায় পাকিস্তানি হানাদারদের দোসর অবাঙালিরা। ১১ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনারা ঈশ্বরদী দখল করে নেওয়ার পর গ্রাম দুটোর মানুষ ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু অবাঙালিদের কথার চালে ভুলে এবং তাদের দেওয়া খাদ্যসামগ্রী পেয়ে তারা আবার গ্রামে ফিরে আসে। ২২ এপ্রিল ভোর না হতেই গ্রামে জ্বলে উঠল আগুন। পালাবে সে পথও ছিল না। তিন দিক থেকে রাইফেল উঁচিয়ে অবাঙালিরা ঘিরে ফেলে। তাদের হাতে রাইফেল, তরবারি ও বল্লম। শত শত মানুষ বুলেটের আঘাতে লুটিয়ে পড়ে। পাঁচশ'র মতো মানুষ সেদিন প্রাণ দিয়েছিল।
হানাদার এবং তাদের দোসরদের নৃশংস হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা মেলে ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে, নওগাঁর তাজ সিনেমা হলের নিকটবর্তী পুরনো পশু হাসপাতালটি অতিক্রম করে উত্তর দিকে কিছু দূর গেলেই দেখা যাবে, ছোট একটি মসজিদ। তার পাশেই রয়েছে একটি দালান বাড়ি। বসবাস করত এক বিহারী ব্যবসায়ী, নাম ইদ্রিস। তার বাসার ভেতর যেতেই যে কেউ চমকে উঠবেন। দেখতে পাবেন দুই ঘরের ভেতরে নির্মম হত্যার প্রমাণ চিহ্ন। একটি ঘরে অনেক দড়ি ঝুলে আছে। আর অপরটিতে রয়েছে অসংখ্য বাঙালির রক্তের ছাপ। বিহারী ব্যবসায়ীরা খানসেনাদের সহযোগিতায় যেসব বাঙালিকে ধরে এনে জবাই করতো, তাদের রক্তে তার অপবিত্র হাত রঞ্জিত করে, তা দিয়ে ঘরের জানালা রাঙিয়ে নিত, যেন আলতা দিয়ে সাজানো হয়েছে।
খুলনার প্লাটিনাম জুট মিলের হত্যাকা ছিল যেমন লোমহর্ষক, তেমনি নির্মম ও নিষ্ঠুর। মিলের জ্বলন্ত বয়লারের ভেতরে ফেলে কমপক্ষে ৫৬ জনকে হানাদাররা পুড়িয়ে হত্যা করে। বাঙালি শ্রমিকদের এনে বসানো হতো বয়লারের সামনে বিশ ফুট উঁচু পাকা প্রাচীরের পাশে। এরপর তাদেরকে বস্তাবন্দি করে পায়ের দিক থেকে জ্বলন্ত বয়লারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হতো। ঢোকানো অংশ পুড়ে গেলে দেহের বাকি অংশ ও মাথা একটু একটু করে বয়লারে ঢুকিয়ে দেয়া হতো।
গাইবান্ধার বোনারপাড়া জংশন রেল স্টেশন এলাকায় অবাঙালিদের সহযোগিতায় পাকসেনারা নির্মম হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছিল। সেখানে বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে আনা মানুষকে কয়লাচালিত ইঞ্জিনের আগুনে পুড়িয়ে মারা হতো। অনেক লোককে জবাই করে হত্যা করে রেললাইনের ধারে পুঁতে রাখা হতো।
এমন ঘটনা ছড়িয়ে আছে দেশজুড়ে। প্রায় পাঁচ শত সনাক্ত গণকবরে কয়েক লাখ শহীদের সন্ধান মিলে। আর হত্যাযজ্ঞ গুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায় হত্যার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তাই সবার সন্ধান মেলানো বেশ কষ্ট সাধ্য। তবে, হত্যাযজ্ঞের শিকার যে সবচেয়ে বেশি হয়েছে হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা তা সহজেই অনুমেয়।
সমাজবিজ্ঞানী আর জে রুমেল তার 'ডেথ বাই গভর্নমেন্ট' বইতে ইহুদীদের ওপর নাৎসীদের বীভৎস অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছেন, গোটা প্রদেশ জুড়ে যেভাবে গণহত্যা চলেছিল তাতে হিন্দুদের দেখামাত্র গুলি করা হতো। অন্যদিকে হিন্দু-মুসলিম পার্থক্য নির্ণয় করতে সৈন্যরা কাপড় খুলে তাদের লিঙ্গ পরীক্ষা করতো। যদি 'মুসলমানি' করানো থাকতো তাহলে হয়তো বাঁচা গেলেও বাঁচা যেতো। তা না হলেই অনিবার্য মৃত্যু।" তপন কুমার দে তার গণহত্যা গ্রন্থে লিখেছেন, পাকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের তাণ্ডব সব থেকে বেশি ঘটে কুড়িয়ানা, সসীদে বাউকাঠি ও জলাবাড়িতে। কেননা, উলি্লখিত এলাকাগুলো হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত। জলাবাড়ির ৩৩টি গ্রাম তারা নির্বিচারে জ্বালিয়ে দেয়। নাজিরপুর ও বানারীপাড়া থানায় তারা কয়েকশ' লোককে হত্যা করে। বৃহত্তর বরিশাল জেলায় মোট ৭৭,০০০ লোক শহীদ হন। শুধু পিরোজপুরের ৭টি থানাতেই তারা ৩০,০০০ লোককে হত্যা করে।
গণহত্যার শিকার এ হতভাগ্যদের প্রায় অর্ধেকই ছিল নারী। গবেষক সুজান ব্রাউনমিলার 'এগেইনস্ট আওয়ার
উইল :মেন-উইমেন অ্যান্ড রেপ' গ্রন্থে দাবি করেছেন, '১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে বাংলাদেশে ৪ লাখের মতো নারী পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছেন। সুজান লিখেছেন, 'অস্ত্রেশস্ত্রে বলীয়ান থাকায় পাকবাহিনীর পক্ষে তাদের অধিকৃত অঞ্চলে যখন-তখন যে কোনো ঘরবাড়িতে ঢুকে তাদের অধিকৃত অঞ্চলে ধর্ষণ চালানো খুবই সহজ ছিল।' তিনি লিখেছেন, 'বাংলাদেশের এই ধর্ষণ ঘটনাগুলো এমনই পর্যায়ে পেঁৗছেছিল যে ৮ বছরের শিশু থেকে ৭৫ বছরের বৃদ্ধাকে পর্যন্ত বর্বর পন্থায় নিপীড়ন করা হয়েছে।' তিনি আরও লিখেছেন, 'এমন উদাহরণও পাওয়া গেছে যে, কোনো কোনো মেয়েকে উন্মত্ত পাকিস্তানি সৈন্যরা এক রাতে দলগতভাবে ৮০ বার পর্যন্ত পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে।'
নারী নির্যাতনের করুণ নিদর্শন মেলে কুমিল্লার লাকসাম সিগারেট ফ্যাক্টরিতে। পাকহানাদার বাহিনী গ্রামগঞ্জ ও লাকসাম জংশনে অপেক্ষমাণ ট্রেন থেকে পুরুষদের সঙ্গে নারীদেরও ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের ওপর নৃশংস যৌন নির্যাতন চালায়। অনেকে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। অনেক নারী আত্মহত্যাও করে। বিকারগ্রস্ত পাকিস্তানি নরপশুরা অনেক নারীকে উলঙ্গ করে কারখানার রেলিংবিহীন ছাদে উঠিয়ে দু'হাত উপরে তুলে সারাদিন হাঁটতে বাধ্য করত। এই নির্যাতনে যেসব মেয়ে মৃত্যুবরণ করত অথবা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ত। তাদের মরদেহ কারখানার বিভিন্ন কোনে পুঁতে ফেলা হতো।
আর জে রুমেল তার 'ডেথ বাই গভর্নমেন্ট' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই গণহত্যা বিশ্ব ইতিহাসের ভয়ঙ্কর এক হত্যাযজ্ঞ। রুয়ান্ডায় যে ৮ লাখ লোক মারা গেছে, এমনকি ১৯৬৫-৬৯ সালে ইন্দোনেশিয়ায় ১০ থেকে ১৫ লাখ মারা গিয়েছিল, তার চেয়েও বেশি।
১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার তেত্রিশতম বার্ষিকী উপলক্ষে জাতিসংঘ একটি রিপোর্ট বের করে। ওই রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্বের ইতিহাসে যেসব হত্যার ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে স্বল্পতম সময়ে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের গণহত্যায়। রিপোর্টে নিহতের সংখ্যা সর্বনিম্ন গণনায় অন্তত ১৫ লাখ বলে উল্লেখ করে বলা হয় যে, ১৯৭১ সালের মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত দৈনিক গড় ৬ খেকে ১২ হাজার লোক নিহত হয়েছেন। মানব জাতির ইতিহাসে গণহত্যাযজ্ঞের ঘটনাসমূহে দৈনিক গড় নিহতের সংখ্যায় এটি সর্বোচ্চ। আর কম্পটনস এনসাইক্লোপিডিয়া এবং এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা অনুয়ায়ী সংখ্যাটি ৩০ লাখ। আর এসব তথ্য-উপাত্ত সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে_ মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড মানব ইতিহাসের জঘন্যতম এবং নৃশংসতম গণহত্যাযজ্ঞ।
http://www.samakal.net/print_edition/details.php?news=257&view=archiev&y=2013&m=03&d=26&action=main&menu_type=&option=single&news_id=336122&pub_no=1359&type=
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ১৭:০৮582577
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ১৭:০৮582577- পদাবলী
আল মাহমুদ
শেষের যাত্রা
তোমাদের শুরু আমার তো হায় সন্ধ্যাবেলা
পার হয়ে আসি উদয়ের কত রোদের খেলা
গোধূলির ধূলি আকাশে উড়ছে, আমি একেলা
এইতো শেষের সন্ধ্যাকালের
আলোর খেলা।
মুখের উপর ছায়া নেমে আসে
মায়ার ঝিলিক ঘরে ফিরে বুঝি নৃত্য করে!
অস্ত-সূর্য ডাক দেয় কারে ওই তো নামছে
ধূসর সন্ধ্যা শেষের বেলা নামটি ধরে।
পার হয়ে যাই হাঁটতে হাঁটতে একটা জীবন
পিছনে রয়েছে গভীর আঁধার আর ঘন বন
কে যেন আমায় ডাকে ইশারায়, বলে আয় আয়
আমি হেঁটে হেঁটে পথের মাঝেই একটু দাঁড়াই
পথের শব্দ কারা যেন বলে আরে নাই নাই
তবু আমি যাই অন্ধকারের ছায়ায় দাঁড়াই।
আমার নামটি কে যেন পুকারে বলে, এসো এসো,
আমি ডুবে যাই ছায়ার মায়ায় সাাঁঝের আলো হেসে বলে এসো
ফিরবে কি ঘরে, প্রদীপ জ্বালো।
তোমার মুখটি মায়ার ছলনা আর কিছু নয়
যাচ্ছো তো হেঁটে বহু কিছু ঘেঁটে তোমার বিজয়
লিখবে এমন কারা আছে বল।
আঁখি ছলছল, কাঁদছো কি তুমি!
পায়ের নিচেই আছে তোমার জন্মভূমি বাংলাদেশের
মাটির শীতল পাটি বিছিয়েছে তারা যেন ঠিকই
তোমার এখন যেতে হবে, দূরে নিতে হবে পথ ঠিকই।
রফিক আজাদ
তখন স্বপ্ন ছিলো দু'চোখে অনেক
আমরা আগুনমুখা নদীর তলদেশ থেকে
সাঁতরে উঠে এসেছিলাম_
আমাদের এই উত্থান তখন অবশ্য অনিবার্য ছিলো :
দুঃসময়ে উঠে এসে আমাদেরও ঐ
পায়ের নিচের মাটি খুব ভালোবেসেছিলাম_
অনন্তর হাতে হাত ধরে
মানববন্ধন হাতে হাত ধরে
মানববন্ধন করে সামনে এগোতে চেষ্টা করেছি,
_এগোনো কি যায়? কতো যে ঝড়ঝঞ্ঝা,
বাতাসের অবিশ্বাস্য গতিবেগ, বিরুদ্ধ বিষম স্রোত_
বিভিন্ন নৌপথে, ডাঙাতেও আগ্নেয় ঝড়,
মাইল-মাইলব্যাপী শস্যের প্রান্তর জ্বলছিলো,
সেই সে আগুন নেভাতে আগুনেরই মধ্যে
অন্তহীন আগুন হয়ে আমরা পেরিয়েছি
তেপান্তরের পথ,
তীব্র হিংস্র খল সব জলের স্রোতের বিপরীতে
আমরা উজিয়ে উঠে পেঁৗছি প্রার্থিত ডাঙায়_
বাতাসের তীব্র গতিবেগ পরাস্ত করে অবশেষে
গন্তব্যে তো পেঁৗছেছিলাম...
কিন্তু বন্যা, ঝঞ্ঝাবাতে, বিক্ষুব্ধ গর্কিতে, জলোচ্ছ্বাসে,
মারী ও মড়কে, অগি্নঝড়ে, মঙ্গায় পীড়িতজন
দৃঢ়পায়ে দাঁড়ানোর কোনো ঠাঁই-ই তো পেলাম না!
তা-হলে কি জন্মাবধি প্রাণান্তকর দুঃখজয়ী
ঐ প্রচেষ্টাটি আমাদের প্রিয় স্মৃতি ভাণ্ডারেই
জমা থাকলো!
অরুনাভ সরকার
নীল পাখি
'ভালোবাসা' কাঁচঘরে রঙিন তৃষ্ণার জলছবি
সোনার ছায়ার নিচে মোনালিসা হাসি
ঝর্ণাতলায় জ্যোৎস্নার ফুলঝরা ঘ্রাণ
জল থেকে টেনে তোলা তারাফুল ছায়া
কেউ তো মানতে রাজি নয় যুগল চোখের রোদ
নিভে যায় সন্ধ্যের হাওয়ায়
রাতে বাড়ে অথৈ আঁধারের মেঘ-জলে
হৃদয়ের গল্পে ভিড় করে ছেঁড়া জলের গুঞ্জন
ক্লান্ত চোখ থেকে ভেঙে পড়ে বর্ণিল হাসির শব্দ
তবু দ্যুতিময় কাঁচঘরে ছায়া পড়ে
নীল পাখিদের
সানাউল হক খান
যোগ্যাতা পূর্ণ হবে কবিতার খাতায়
বৃষ্টি তার জন্মদিন
আল্লা'র আরশ থেকে নেমে-আসা
ঝমঝমে আনন্দবার্তা
রৌদ্র যেন সোনারং মহোৎসব
তার আবার তিরোধান কী?
শব্দ দ্যায় হারানো-বিজ্ঞপ্তি:
কেউ টের পান কি?
কবিতা এগোয় বয়সের এক্কা-দোক্কায়
লুডুর ছকে জীবন পাঞ্জা-ছক্কায়
উজ্জীবনী ছায়া হয়ে আততায়ীর মতো পিছু নেয়
কবি ছোটে মৃত্যুর অধিক মহামরণের অন্বেষায়
বিষয় তার বর্তমান
পলকে-পলকে... দম-না-ফেলতেই,
সব কিছু যার অতীত
চন্দনের তিলক-টিপ, গোলাপের গুচ্ছ
অভিনন্দন: সবই খুব তুচ্ছ
চন্দন মুছে যায়
সুগন্ধি খুঁজে পায়
সরল রেখা : কবি বড্ড একা, তার শব্দ ভীষণ একা
তার একাকিত্ব আরও একা
অপরের নয়, হাত রাখো নিজের মাথায়
যোগ্যতা পূর্ণ হবে
কবিতার খাতায়।
নাসির আহমেদ
দাও সে শক্তি মা
গভীর কালো মেঘ অন্ধ আকাশের ঝড়ের আভাসেই আজকে
তোমাকে দেখি দেশ, তোমাকে দেখি মাগো, ওরাতো আলোকের শত্রু।
থ্রি নট থ্রি জং ধরা সে রাইফেলে ছিল মা কী সাহস শক্তি!
আজকে দেখো আমি এতটা ভীত মাগো, অথচ হাতে মারণাস্ত্র!
আমরা এনেছি যে আলোর সূর্যটা, তাতেই কালো মেঘ আজকে
ঘাতক সময়ের আস্ফালনে ফের কাঁপছে চারপাশ; যুদ্ধ
আবার যুদ্ধের আসছে ডাক মাগো আবার মুক্তির সংগ্রাম
গভীর কালো মেঘ হয়তো ঝড় হবে, এটাই শেষ ঝড় হয়তো।
এবার দুই ভাগে বিভক্ত এই দেশ, আবার মুখোমুখি শত্রু
এবার আঁকাবাঁকা কঠিন সর্পিল পথেই আমাদের যাত্রা।
আবার ফিরে চাই তোমার স্পর্শ মা, সাহসী বাণীটুকু প্রেরণার
স্নায়ুতে গেঁথে নিতে চাইছি স্মৃতি সেই একাত্তরেরই মা মার্চের।
গভীর থমথমে ঝড়ের কালোমেঘ এনেছে যারা দেশে আজকে
তাদের হটাতেই ফাঁসির দড়ি হাতে সারাটা দেশ মাগো দাঁড়িয়ে
আকাশে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু দেখো, বৃষ্টি রক্তই ঝরাবে
হিংস্র ভয় আজ যেখানে-সেখানে মা, মুক্তিযুদ্ধই চলছে।
এ যুদ্ধে জয়ী হতে হবেই হবে মাগো, দাও সে শক্তির মন্ত্র
দাও সে প্রেরণা মা_ মুক্তিযুদ্ধের বীরেরা কখনো যে মরে না।
দাউদ হায়দার
যুদ্ধ, পরমাণু
হেমন্ত সন্ধ্যায়
অবিবাহ বিচ্ছেদ হলো
আমাদের
এমতাবস্থায়
নদী আর দীঘির জলও
বিমুখ দেহাত্মবাদে
কে কখন
হারিয়েছ ভারসাম্য, কে জানে
অমিতাক্ষর ছন্দের বিপর্যয়!
ছিল না মেঘের আস্তরণ,
বন্যা-দুর্যোগ নিয়ে জাতিসংঘের পরিসংখ্যানে
যে-মতন বলা হয়
অবশ্য আমার বন্ধু
হাসান ফেরদৌস মানতে নারাজ
কেন একজন কবির সুদীর্ঘ পরবাস
দক্ষিণপন্থীরা সপ্তসিন্ধু
জুড়ে দিচ্ছে মহড়া, হত্যার আওয়াজ,
কৌমমাতার নামে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস
অবিবাহবিচ্ছেদের আগে
ছিলাম দুজন অহিংসপরায়ণ ,
দেশ জগতের প্রতি নতজানু
তিলককামোদ-রাগে
ভুলিনি কবিতার রক্ষণাবেক্ষণ
বিশ্বব্যাপী আজ অহিংস, শান্তির নামে যুদ্ধ, পরমাণু
মুহম্মদ সবুর
মহাপ্লাবন পেরিয়ে
যাচ্ছি পেরিয়ে মহাপল্গাবন, পেরিয়ে যাচ্ছি সাগর জলের ধাক্কা
আমরা যেসব মাঝি ও মাল্লা, নৌকাতেই জীবন ফকফকক্কা
বরফ গলে ডুবছে দেশ, ডুবছে নদী ভাসছে সব সাগর
তলিয়ে যায় মহাদেশও, তলায় শহর, গঞ্জগ্রাম এবং নগর
কে আর বাঁচে_ বাঁচাবে কে এমন অতল জলের গহনতলে
ডুবসাঁতারে টেকাও দায়, প্রবল স্রোতে দম মেলে না ঢলে
কোথায় মানুষ কোথায় জন্তু জীব_ আছে কোথায় বৃক্ষ বন
সব ভেসে যায় বরফ গলা জলের তোড়ে, উজাড় বিশ্বভুবন
জেগে শুধু থাকে তাক ডুমা ডুম ডুম বাংলাদেশেরই ঢোল
বাজিয়ে যায় ঢুলি আর বাদ্যতালে নৃত্যে তোলে কী বোল
নৌকোতে সব বাঙালি, আছে সব বৃক্ষ এবং কীট প্রাণী
নৌকো বাইচে মাতোয়ারা; লল্ফম্ফঝল্ফম্ফ তালেতে ঢলঢলানি
সাতটি রাত সাতটি দিন জলের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ শেষে
আবার আকাশ রঙিন হয়ে বাংলার মাটিতে এসে মেশে
ডাঙ্গায় এসে রোদের ঝরনায় নাইতে নেমে তারা শোনে
খেঁকশিয়ালের হচ্ছে বিয়ে;রৌদ্র-মেঘের দিন ক্ষণ গোনে
হাততালিতে মাতোয়ারা বেঁচে থাকা বাংলার নবীন দল
তাদের জন্য বিশ্বভুবন_ তাদের জন্যই বাংলাদেশ সমুজ্জ্বল।
কুমার চক্রবর্তী
দেশকালের ভেতর আমরা
কমলা বাগানের ওপর জমাট ছায়ার স্থিরচিত্র। এখানেই
আমরা উড়ে আসা একঝাঁক পাখি এসে গতিচ্যুত হই,
জোর করে শাখা-প্রশাখায় বসে পড়ি কিন্তু
আর উঠতে পারি না,
বুঝি লেগে গেছি চিরকালের জন্য মৃত্যুর পরাঙ্মুখ আটায়।
চোখ দিয়ে দেখি, নেকড়েরা চারপাশে ঘুরপাক খায়
ভয় পেয়ে তাই পাতায় পাতায় প্রতিশ্রুত মোমগুলো জ্বেলে দিই,
কাঁটাঝোপের ভেতর তারারা রাতে পা টিপে হাঁটাহাঁটি করে
সময় ঘটাংঘটাং শব্দে পেটায় মহাকালের ঘণ্টা
দেশকালের ভেতর আমরা আটকেপড়া প্রাণিকুল, কী আশ্চর্য
পাৎলুন-খোলা ঘাতকেরা এসে আমাদের মন্দাক্রান্তা ছন্দের ডানাগুলো কেটে দিয়ে যায়
আলতাফ হোসেন
মার্চ, ২০১৩
নরমু গুলো চলেছে হইহই করতে করতে
প্রত্যেকের হাতে লাঠি, দা, কিরিচ ...
চোখের কোটরে গোখরোজিভ
অপলক প্রভাত, সবুজ
হাত নাড়তে থাকব
অনেক মানুষ চাঁদে যাবে বলে লাইন দিয়েছে
আরও অনেক মানুষ আছে অপেক্ষায়
যেতে যেতে একদিন
প্রায় বিনা পয়সাতেও যাবে
শেষ ভিক্ষুকটিও চলে গেলে
পূর্বখলার টিলায় উঠে
হাত নাড়তে থাকব চাঁদকে লক্ষ্য করে
হাসান হাফিজ
দুরন্ত তিয়াসা
অনিঃশেষ লড়াইয়ের অন্য এক জ্বলজ্বলে নাম।
শুরু আছে, শেষ নাই, যবনিকা বলে কিচ্ছু নাই।
রক্তসিঁড়ি পার হওয়া, ক্রমাগত সিঁড়ি ভেঙে ওঠা।
তিতিক্ষা ও ত্যাগ শুধু। অশ্রুফোঁটা বিসর্জন_
সম্ভ্রমের মূল্যে তাকে পেতে হয়। কোনো ছাড় নাই।
সে এক আশ্চর্য তেজ, অহমিকা, শক্তি উদ্ভাসন।
ধুঁকতে ধুঁকতে পুড়তে পুড়তে সবই তছনছ।
ভাঙন ধ্বংস ও ক্ষয় বিপর্যয় অনন্ত প্রলয়।
সে দীর্ঘ প্রক্রিয়া। শুরু আছে। আবর্ত মন্থনও আছে।
আপাত-বিজয়ে নেই সন্তুষ্টির লেশমাত্র অবকাশ।
এই যুদ্ধ চলমান। এই সোনা আগুনেই পুড়ে খাঁটি হয়।
রক্তঋণে প্রতিরোধ, সশস্ত্র লড়াই, জাগ্রত চেতনা তুমি।
স্বাধীনতা অনশ্বর। দুরন্ত অস্থির এক অতৃপ্ত তিয়াসা।
শিহাব সরকার
মার্চের দুপুরে
সংকটে জেগে থাকতে হয়
খুনি ঘুরছে ছদ্মবেশে কালো আলখাল্লায়
অবসর ছেড়ে উঠে এসেছে মুক্তিসেনা
এবার জেগে থাকা দিনভর রাত্রিভর।
কে রুখতে পেরেছে জনজোয়ার
জাগ্রত মানুষেরা বিসুভিয়াস, সুনামি
আছড়ে পড়ে রক্তমাখা প্রত্ন প্রাসাদে
বাতাসে পূতিগন্ধ শকুনের পাখনা।
মার্চের দুপুরে নগরীর স্কোয়ারে
পচে গলে পিচে মিশে গেছে ড্রাকুলারা
পতাকা উড়ছে মঞ্চে, বালকের হাতে।
রাত্রিজাগা মানুষের স্লোগানে
মরা নদী থৈথৈ, এসে গেছে ফুলের মৌসুম
চোখেমুখে পবিত্র জলকণা।
ভুলিনি আমি একাত্তরে বাঙ্কারে
মুক্তিবাহিনীর জয়বাংলা, বিজয়োল্লাস।
রেজাউদ্দিন স্টালিন
বঙ্গভাষা
ভাষার ভুবন নিয়ে লেখা হয়ে গেছে বহু অমর রচনা। এসবের উপজীব্য অনটন, বিদ্রোহ, ব্যর্থতার দিনপঞ্জিকা। ভাষার চারটি ছেলে একজন অনুভূতি মেঘে মেঘে ঘোরে, মেজোটির নাম কথা_ ওড়ে পাতায় পাতায়। তৃতীয়টি ইচ্ছা_ ঘর ছেড়ে একদিন পাতাল রাজ্যে বসত বানাবে। কনিষ্ঠজন আকাঙ্ক্ষা_ কারাভোগরত। তাদের একত্রে না পেলে ভাষার সংসার কি করে যূথবদ্ধ হয়? এভাবে কোনোমতে কষ্টে-সৃষ্টে চলছিল বঙ্গভাষার সংসার। হঠাৎ ঘনিয়ে এলো ঈশানের আক্রমণ। পূর্বপুরুষের বহু মূল্যবান তৈজস অনেক অভাবে যা' ধরে রেখেছিল; সেগুলো রা করতে বন্দুকের সামনে দাঁড়ালো একে একে তিনটি সন্তান। আর কারাগারে বেঁচে গেল সর্বকনিষ্ঠ পুত্র_ আকাঙ্ক্ষা। মূল্যবান তৈজস রক্ষাকারী সন্তানের স্মৃতিতে বঙ্গভাষা বপন করল তিনটি অমর বৃ, একত্রে নাম দিলো শহীদ মিনার। বঙ্গভাষা অপোয় আছে তার কনিষ্ঠ সন্তান আকাঙ্ক্ষা মুক্তি পেলে একদিন সংসারের সব দায় তার কাঁধে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো বেরুবে বিশ্বদর্শনে।
ফারুক মাহমুদ
শাহবাগ
আমাদের ছোট-বড় দীর্ঘশ্বাসগুলো হেঁটে যাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে
ঝলসানো প্রাচুর্যে নয়, পথভ্রষ্ট কলরবে নয়, লালসার
বিশাল জঙ্গলে নয়। ওরা চায় মেঘভর্তি নর্তকী আকাশ
সবুজের নানা বর্ণ, শব্দ-ছন্দ, কাকচক্ষু জলের প্রচার
পেরিয়ে বিস্তর পথ আমাদের ছোট-বড় দীর্ঘশ্বাসগুলো
এসেছে বায়ান্ন থেকে, একাত্তর থেকে দলবদ্ধ-যুদ্ধাহত
এসেছে সম্ভ্রম ভেঙে। মনপোড়া নারীটির শরীর কাদায়
অনিচ্ছার জন্মফুল, বাতাসে ক্রন্দধ্বনি_ কে মোছাবে ক্ষত!
খয়েরি বুটের নিচ থেমে গেছে আমাদের নদীকলরব
সুর্মা, আতরের ঘ্রাণ, সফেদ জামার হাসি-এই হল দেশ
যে পাখি গানের পাখি, কণ্ঠে তারও গেঁথে গেছে অসবর্ণ বিষ
কারা আসে-অন্য পাখি, নেপথ্যে কাহার কণ্ঠ ' আহা বেশ বেশ'
আমাদের দীর্ঘশ্বাসগুলো পেয়েছে মুক্তির স্বাদ দৃপ্ত শাহবাগে
নতুন জোয়ার যেন-জেগে আছে বাংলাদেশ-মানবতা জাগে
হুমায়ুন মনি
মেঘনার খণ্ডচিত্র
স্বপ্নের সবটুকু পাই এইখানে,
অফুরন্ত ঝিঁ ঝিঁ পোকা রাতদিন
ডেকে যায় অবিরাম।
রাতের আঙ্গিনায় ছুটে যায়_আসে,
থোকা থোকা জোনাক পোকা ।
সব নিয়ম অর্থহীন হয়ে এখানে
গাছে নতুন পাতা আসে,
আসে শব্দ নিয়ে নতুন বাতাস।
ক্লান্তিহিন চোখ দেখে যায়,
মাঠের উপর চাঁদকে খুব কাছে মনে হয়।
এখানে দিনগুলো অন্যরকম_
ভাঙ্গনের শব্দ আছে_তবু স্বপ্ন দেখতে দোষ নেই,
একটু এগোলেই এভাবেই স্বপ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে_
মেঘনার পাড়ে নতুন বেড়িবাঁধ ।
পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব একজন আজগর, স্বপ্ন দেখে_
এভাবে সে দেখেছে একের পর এক একটি,
এগারটি বেড়িবাঁধ; এই মেঘনার পাড়ে ।
স্বপ্নরা তার হাসে আর হয়ে যায়,
সব হারিয়ে সে হারিয়েছে হারানোর ভয়
এখনও মেঘনা, তার সাথে
চোখে চোখ রেখে কথা কয়।
রোকসানা রফিক
চরমপত্র
বাঁধভাঙা জোয়ার এসেছে বাঙালির
জেগেছে তরুণ প্রাণ,
রাজাকারের ফাঁসির দাবিতে
লাখো কণ্ঠের স্লোগান।
কাঁপা কাঁপা মোমের আলোয়
ঘুচে যাক অন্ধকার,
শহীদের খুন রাঙ্গানো মাটিতে
হবেই ন্যায্য বিচার।
বীর বাঙালির ঘরে ঘরে আজ
ধি্বনছে চরমপত্র,
রাজাকার, আলবদরহীন মাটিতে
মুক্তির জয় একচ্ছত্র।।
সঞ্জয় ঘোষ
খোলস কিংবা সরল নদীর স্রোত
[কতিপয় পোস্টমডার্ন মৌলবাদীর প্রতি।
যারা বাঙালির জন্মসুতোয় চিকনে প্যাঁচ খেলায়]
প্যাঁচ বিষয়ক সন্ধ্যায়
বিভ্রান্তির পিচকারি খালি হয়ে এলে
তোমার অনির্ণিত আত্মাকে ঐকিকে সাধো
ভাবো, সবুজ নদীর স্রোতে
ভাবের_
তুমি কার কথা ঢালো
রক্ত না রোগের?
চেহারায় সেঁটে রেখে বাউল দিনের রক্তাক্ষর
কোন কামে লালনকে ধরো?
গোপনে গুনছো যতো আসমানী ঢেউ
ফেউ তুমি ফেউ
আমার উড্ডয়ন পথে
ফ্যাসিবাদ ধার করে আনো।
তার চেয়ে তরবারি রেখে
চলো বাতাসের তোরণের দিকে যাই।
টোকন ঠাকুর
ত্রিছত্র
স্বপ্নের ভেতরে দীর্ঘ, দীর্ঘ গগনডাঙা
আমি ও আমার বাইসাইকেল উড়ে যাচ্ছিলাম
মনে হলো, নিজেকে একবার ডাকি, কিন্তু
কী বলে ডাকব? ভাই? বোন-বন্ধু? কী হই
আমি আমার? কীইবা আমার নাম?
খ.
সৌন্দর্য, আমাকে তুই ঘুরিয়ে মারলি পথসুড়ঙ্গে
বছরের পর বছর
সৌন্দর্য, আমাকে তুই পুড়িয়ে মারলি, কী ক্ষতি
করেছিলাম তোর?
গ.
এক জাদুকরকে আমি চিনি, জাদুকরের নাম ... ঘোর
সে এমন (দুর্দান্ত) চোর ...
চুরি করে নিয়ে যায় বয়স, আমি ভুল করে
(ঘোরের পাল্লায় পড়ে, জাতীয় সনদপত্রে)
৪১ না লিখে লিখে দিছি ১৪ বছর ...
http://www.samakal.net/print_edition/details.php?news=257&view=archiev&y=2013&m=03&d=26&action=main&menu_type=&option=single&news_id=336123&pub_no=1359&type=
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ১৭:৩১582578
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৪ এপ্রিল ২০১৩ ১৭:৩১582578- নৃশংসতার অপর নাম গুডস হিল
আজ বিজয়ের মাসের ১৩তম দিন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের দোসর শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও বিভিন্ন মুজাহিদ বাহিনীর সহায়তায় সারাদেশে গণহত্যা, লুটপাট, অগি্নসংযোগ ও নারী নির্যাতন চালায়। এ ধরনের মানবতাবিরোধী কাজে সহায়ক বাহিনীর নেতারাও অংশ নেয়। এসব গণহত্যা নিয়ে ধারাবাহিক রচনার আজ তৃতীয় পর্বে চট্টগ্রামে গণহত্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংযোজিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের দলিল, গণতদন্ত কমিশনের রিপোর্ট, এমএ হাসানের একাত্তরের গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ, তপন কুমার দে রচিত গণহত্যা '৭১ ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন এবং ইন্টারনেটে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে নিবন্ধটি প্রস্তুত করেছেন সুভাষ সাহা কাজী আবুল মনসুর ও মাহফুজুর রহমান মানিক
_______________________________________________
ব্রিটিশ সাংবাদিক সায়মন ড্রিং ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর গণহত্যার চিত্র 'ট্যাংকস ক্রাশ রিভল্ট ইন পাকিস্তান' শিরোনামে ব্রিটিশ দৈনিক দি টেলিগ্রাফে প্রকাশিত তার প্রতিবেদনে এভাবেই তুলে ধরেছিলেন_ 'ঠিক কত নিরীহ মানুষ এ পর্যন্ত জীবন দিয়েছে সে হিসাব করা খুবই কঠিন। তবে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর এবং ঢাকার হিসাব যোগ করলে এ সংখ্যা ১৫ হাজারে দাঁড়াবে। যা মাপা যায় তাহলো সামরিক অভিযানের ভয়াবহতা। ছাত্রদের হত্যা করা হয়েছে তাদের বিছানায়, কসাই নিহত হয়েছে তার ছোট্ট দোকানটিতে, নারী ও শিশু ঘরের ভেতর দগ্ধ হয়েছে, হিন্দু ধর্মাবলম্বী পাকিস্তানিদের এক সঙ্গে জড়ো করে মারা হয়েছে। বাড়িঘর, দোকানপাট, বাজার জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।' হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা, নির্মমতা তিনিই প্রথম বিশ্ববাসীকে জানান। সারাদেশে তারা ওই একটি রাতে যেভাবে গণহত্যা চালিয়েছিল তা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল।
ঢাকার পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী চট্টগ্রাম। এখানে তাদের শক্তিশালী ক্যান্টনমেন্ট ছিল। রণপোতগুলোও এখানেই থাকত। স্বভাবতই হানাদার বাহিনীর গণহত্যা এখানে বেশি মাত্রায় ছিল। বিশেষ করে যেখানে যেখানে বাঙালি সৈনিক ও পুলিশ বিদ্রোহ করেছিল সেখানেই হানাদার বাহিনী অতিমাত্রায় নৃশংসতা চালিয়েছিল। তারা কতটা নৃশংস ছিল চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়ের গণহত্যাই তার প্রমাণ। স্থানীয় জনসাধারণের ধারণা, শুধু মিরসরাই ও সীতাকুণ্ডেই ১৫ থেকে ২৫ হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে। শুরু থেকেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এ নৃশংস গণহত্যার সহযোগী ছিল তাদের এ দেশীয় দালাল রাজনৈতিক দল, বিহারি ও অন্য পাক-পছন্দ গোষ্ঠী। পরে এসব দালালকে নিয়েই গড়ে ওঠে রাজাকার, আলবদর, আলশামস, নানা নামের মুজাহিদ বাহিনী। হানাদার এবং এদের সম্মিলিত নৃশংসতা এতটা ভয়াবহ ছিল যে, জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব উথান্ট এই গণহত্যাকে ইতিহাসের অন্যতম করুণ ঘটনা ও মানব ইতিহাসের অতি কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে অভিহিত করেন। মার্কিন সিনেটর জন এফ কেনেডি চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার বধ্যভূমিগুলো দেখে বলেন, 'মানুষের মস্তিষ্কে এ ধরনের বর্বরতার চিন্তা আসতে পারে এ কথা ভাবতেও কষ্ট হয়।' ফরাসি সাহিত্যিক আন্দ্রে মালরো বলেছেন, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসিদের নৃশংসতার নিদর্শন আমি দেখেছি, কিন্তু এখানকার নৃশংসতা তার চেয়ে অনেক বেশি।'
চট্টগ্রামে হানাদার বাহিনীর সহযোগী হিসেবে গণহত্যা, লুটপাট, অগি্নসংযোগ, নারী নির্যাতনসহ মানবতাবিরোধী অপরাধে যারা নেতৃত্ব দেন, তাদের মধ্যে ফজলুল কাদের চৌধুরী, তার ছেলে সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী, মীর কাসেম আলী, আহমদ সৈয়দ, মাওলানা শামসুদ্দিন অন্যতম। তারা বা তাদের নির্ধারিত অনুচর, বিভিন্ন সহায়ক বাহিনীর সদস্যরা কখনও হানাদারদের নিয়ে গিয়ে, কখনও নিজেরাই গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাত। পুরুষদের হত্যা করে বাড়ির কিশোরী, গৃহবধূদের ধরে এনে হানাদারদের হাতে তুলে দেওয়া এবং নিজেরাও অসহায় নারীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালানো ছিল তাদের নিত্যদিনের কাজ।
গুডস হিলে গণহত্যা : ১৯৭১ সালে পুরো মুক্তিযুদ্ধজুড়ে সাকা চৌধুরীর ব্যক্তিগত বাড়ি গুডস হিল গণহত্যা ও নির্যাতন কেন্দ্রে পরিণত হয়। এটি চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানার রহমতগঞ্জের একটি বাড়ি। সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও তার অনুসারী আবদুস সোবহান ১৯৭১ সালের ৪ বা ৫ এপ্রিল রাত ৯টার দিকে রাউজানের আঁধারমানিক গ্রামের অরবিন্দ সরকার, মতিলাল চৌধুরী, অরুণ চৌধুরী, শান্তি কুসুম চৌধুরী, যোগেশ চন্দ্র দে, পরিতোষ দাশ ও সুনীলকে গুডস হিলের নির্যাতন কেন্দ্রে নিয়ে যান। এর মধ্যে কম বয়সী হওয়ায় সুনীলকে ছুরিকাঘাত করে ছেড়ে দিলেও বাকি ছয়জনকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহায়তায় নির্মম নির্যাতন করে হত্যা করে। এ ছাড়া একাত্তরের মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানার ১৯ কাজল বাজারের শেখ মায়মুন আলী চৌধুরীকে গুডস হিলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সাকা চৌধুরী ও তার সহচররা মায়মুন আলী চৌধুরীকে হাত-পা বেঁধে দৈহিক নির্যাতন চালান। আর ৭ জুন চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানার জামালখান রোড থেকে স্থানীয় আশকরদীঘির উত্তরপাড়ার ৬৯ শাহী সাইফুদ্দিন খালেদ সড়কের ওমর ফারুককে অপহরণ করে গুডস হিলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সাকা চৌধুরীর নির্দেশে পাকিস্তানি সেনারা তাকে গুলি করে হত্যা করে। একাত্তর সালের ৫ জুলাই সন্ধ্যা ৭টা-সাড়ে ৭টার দিকে সাকা চৌধুরী ও আরও দু'তিনজন চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানার হাজারী লেন থেকে নিজামউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম ও সিরাজকে অপহরণ করে নিয়ে যান।
রাউজানে গণহত্যা : মুক্তিযুদ্ধের সময় চট্টগ্রামের রাউজানে সবচেয়ে বেশি গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। সেখানে ৬টি গণহত্যা হয়। যার নেতৃত্বে ছিলেন বর্তমান বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন কাদের (সাকা) চৌধুরী। তার নির্দেশে ও সহযোগিতায় হত্যাকা গুলো একাত্তরের ১৩ এপ্রিলে সংঘটিত হয়। সেদিন সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মোট ১২ ঘণ্টায় এই হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। প্রথমে সেখানে ৫ জনকে হত্যা করা হয়। এরপর সকাল সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ৯টার মধ্যে গহিরার বিশ্বাসপাড়ায় ৩ জনকে হত্যা করা হয়। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়ে নূতন চন্দ্র সিংহকে হত্যা করা হয়। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত জগৎমল্লপাড়ায় গুলি করে ৩২ জনকে হত্যা করা হয়। দুপুর ১টার দিকে সুলতানপুরের বণিকপাড়ায় হামলা চালিয়ে ৪ জনকে মারা হয়। একই দিন ঊনসত্তরপাড়ায় সাকার নেতৃত্বে হামলা চালিয়ে ৭০ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করে সাকার বাহিনী। ১৩ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৬টা-৭টার দিকে সাকা চৌধুরীর নেতৃত্বে ও সহযোগিতায় হানাদার বাহিনী চট্টগ্রামের রাউজান থানার মধ্য গহিরার হিন্দুপাড়ায় পরিকল্পিতভাবে সশস্ত্র অভিযান চালায়।
শাকপুরার গণহত্যা : ১৯৭১ সালের ২০ এপ্রিল সকালে সাকা চৌধুরী ও তার বাবা ফজলুল কাদের চৌধুরীর নির্দেশে তাদের অনুসারী মুসলিম লীগের রাজাকার খয়রাতি, জহির, জসিম ও পাকিস্তানি সেনারা চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানার শাকপুরা গ্রামে সশস্ত্র অভিযান চালায়। শাকপুরা প্রাথমিক স্কুলের কাছে জঙ্গলে ও ধানক্ষেতে লুকিয়ে থাকা ওই এলাকার লোকজনকে শাকপুরা দারোগার মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সাকা চৌধুরীর নির্দেশে ফয়েজ আহমেদ, জালাল আহমদ, হাবিলদার সেকান্দর আলী, আমীর হামজা, আবদুল হাশিমসহ ৭৬ জনকে গুলি করে ও বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়।
ফয়'স লেক-পাহাড়তলী গণহত্যা :চট্টগ্রামের গণহত্যাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে শহরের পাহাড়তলীর ফয়'স লেকে। তৎকালীন পাঞ্জাবি লেনের পাশে এই ফয়'স লেক। রক্তপিপাসু পাঞ্জাবি ও বিহারিদের মাত্র একদিনের হত্যাকাণ্ডে পাহাড়তলীর ফয়'স লেককে দেশের বৃহত্তম বধ্যভূমিতে পরিণত করে। রেল কলোনিবাসীদের বিহারিরা নির্বিচারে হত্যা করে। সেখানে রেলস্টেশনে লোকাল রুটের দোহাজারীগামী রেল থামিয়েও তারা গণহত্যা চালায়। বাঙালি কলোনি থেকে নারী-পুরুষকে ধরে এনে পা বেঁধে জল্লাদ দিয়ে মাথা দ্বিখণ্ডিত করে হত্যা করা হতো। তাদের হত্যা করে বাঙালিদের দিয়ে জোরপূর্বক গণকবর খুঁড়িয়ে সেই কবরেই মাটিচাপা দেওয়া হতো। সেনানিবাসে বন্দি নারীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করে এনে এসব গণকবরে পুঁতে রাখত।
১৯৭১ সালে রমজান মাসের ২০ তারিখে ঘটে নৃশংসতার আরেক ঘটনা। সেদিন ভোরে কয়েকজন মুসলি্ল নামাজ পড়ে বাসায় ফিরছিলেন। পথে এক অবাঙালি খবর দেয় পাহাড়ের পাদদেশে বাঙালিরা চারজন বিহারিকে হত্যা করেছে। সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তারা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যান। তাদের মধ্যে ছিলেন একেএম আফসার উদ্দিন, আকবর হোসেন. আবদুল গফুর ইয়াজদানি, মসজিদের মুয়াজ্জিনসহ আরও অনেকে। তারা গিয়ে দেখেন, দুই পাহাড়ের খোলা জায়গায় অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে অনেক অবাঙালি। যারা তাদের দেখে চিৎকার দিয়ে বলছে, খতম করো। সেখানে তারা অনেককেই হত্যা করে।
নন্দনকানন টিঅ্যান্ডটি অফিসে নির্যাতন : চট্টগ্রাম শহরের নন্দনকানন টিঅ্যান্ডটি অফিসের গণহত্যার মূল হোতা হলেন মীর কাসেম আলী। ১৯৭১ সালের প্রথম দিকে মীর কাসেম আলী ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি, পরে রাজাকার কর্মে কৃতিত্বের পুরস্কার হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সাধারণ সম্পাদকের পদ লাভ করেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের আলবদর বাহিনীরও প্রধান। চট্টগ্রাম শহরের নন্দনকানন টিঅ্যান্ডটি অফিসের পেছনের সড়ক যা ইতিপূর্বে টেলিগ্রাফ রোড বলে পরিচিত ছিল, সেখানে এক হিন্দু পরিবারের মালিকানাধীন 'মহামায়া ভবন'টিকে মীর কাসেম আলীর নেতৃত্বাধীন আলবদর বাহিনী কেড়ে নিয়ে তার নাম দেয় ডালিম হোটেল। আর দেশ স্বাধীন হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ডালিম হোটেলেই আলবদর, রাজাকারদের অন্যতম নির্যাতন কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিল চট্টগ্রামবাসীর কাছে। এই বন্দিশিবির ও নির্যাতন কেন্দ্রে আলবদর বাহিনী চট্টগ্রামের প্রধান মীর কাসেম আলীর পরিকল্পনা ও নির্দেশে খুন হয়েছেন অনেক মুক্তিযোদ্ধা, নির্যাতনের শিকার হয়েছেন স্বাধীনতাকামী বাঙালিরা। একাত্তরের মুিক্তযোদ্ধা ও বর্তমানে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক 'পিপলস ভিউ'র ডেপুটি এডিটর নাসিরউদ্দিন চৌধুরী এই আলবদর বাহিনীর হাতে আটক হয়ে ডালিম হোটেলে চরম নির্যাতনের শিকার হন। এই হোটেলে সারাক্ষণ চলত বন্দিদের ওপর নির্যাতন আর নির্যাতিতদের চিৎকার-কান্নাকাটি চলত। এখানে আটককৃত অনেককেই হত্যা করা হয়।
ওয়্যারলেস কলোনির গণহত্যা : চট্টগ্রাম শহরের ওয়্যারলেস কলোনিতে ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী এক নারকীয় তাণ্ডব চালায়। একাত্তরের ১০ নভেম্বর ওয়্যারলেস কলোনি এবং বাহাদুর শাহ কলোনির শিশু, যুবক-যুবতী, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধদের বাসা থেকে ধরে এনে সিভিল পাইওনিয়ার ফোর্সের লোকেরা। সেদিন অনেককে মিলিটারি অফিসার সাহেব ডাকছে বলে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায়। সেখানে জল্লাদরা ধারালো অস্ত্র ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালায়। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এই হত্যাযজ্ঞে আনুমানিক দুইশ' লোককে তারা হত্যা করে। শত শত নারী-পুরুষের লাশ সেখানে পড়েছিল। এই লাশগুলোকে একত্র করে হায়েনারা পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। অনেক লাশকে আবার গান পাউডার ব্যবহার করে ধ্বংস করে দেয়।
নাথপাড়ায় গণহত্যা : একাত্তরে বন্দরনগর চট্টগ্রামে গণহত্যা হয়েছিল হালিশহরের মধ্যম নাথপাড়ায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় স্থানীয় বিহারিরা এ হত্যাযজ্ঞ চালায়। নেতৃত্বে ছিল জল্লাদ শওকত। ওইদিন মাত্র কয়েক ঘণ্টায় কুড়াল, কিরিচ আর রামদা দিয়ে কুপিয়ে ৪০ জন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল (ইপিআর) সদস্য এবং ৩৯ নাথপাড়াবাসীসহ ৭৯ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আসলে '৭১-এর ২৫ মার্চ মুক্তিযুদ্ধের সূচনাকালে হালিশহর ইপিআর ঘাঁটি থেকে মেজর রফিকের নেতৃত্বে ইপিআর বাহিনী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এ সময় দক্ষিণ হালিশহরের লোকজন নানাভাবে ইপিআর বাহিনীর সদস্যদের সহযোগিতা করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে পাকবাহিনী। খবর পেয়ে ২৯ মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বঙ্গোপসাগর উপকূল হয়ে দক্ষিণ কাট্টলীর ইপিআর ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হয়। পরদিন পাকবাহিনী নগরীর উত্তরে গহনা খাল এবং দক্ষিণে ইপিআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকা ঘিরে ফেলে। সামান্য অস্ত্র নিয়ে ইপিআরের পক্ষে পাকবাহিনীকে মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল না। এ অবস্থায় অধিকাংশ ইপিআর সদস্য এলাকা ত্যাগ করলেও প্রায় ৪০-৪২ জন মধ্যম নাথপাড়ার বিভিন্ন বাড়িতে আশ্রয় নেন। বিহারিরা ৩১ মার্চ দুপুরের দিকে নাথপাড়ায় হত্যাকাণ্ড শুরু করে। বেছে বেছে তরুণ-যুবকদের হত্যা করা হয়। তারপর বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। নারী-শিশুদের আটকে রাখা হয় এক বিহারির ঘরে। পরে সেখান থেকে মেয়েদের ধরে নিয়ে পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়। ওইদিন বিহারিরা নাথপাড়ার চট্টগ্রাম কমার্স কলেজের বিকম শ্রেণীর ছাত্র দুলাল এবং চট্টগ্রাম কলেজের অনার্সের ছাত্র বাদল এ দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা করে। তারা সেদিন পাড়ায় আগুন দেওয়ার পর অন্য নারী-পুরুষরা পাড়া ছেড়ে চলে যাওয়ায় এসব মৃতদেহের পরিণতি কী হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে স্বাধীনতার পর পাড়ায় ফিরে বহু মানুষের মাথার খুলি এবং হাড়গোড় পাওয়া যায়। মাটি খুঁড়েও অনেক কঙ্কাল পাওয়া গেছে।
এভাবে স্বাধীনতার নয় মাসে হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা চট্টগ্রামকে মৃত্যুপুরী বানিয়েছিল।
http://www.samakal.net/print_edition/details.php?news=233&view=archiev&y=2012&m=12&d=13&action=main&menu_type=&option=single&news_id=313219&pub_no=1255&type=
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৮ এপ্রিল ২০১৩ ১৯:১৮582579
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ২৮ এপ্রিল ২০১৩ ১৯:১৮582579- Binod Bihari Chowdhury: The Last of the Mohicans
ASRAR CHOWDHURY
___________________________
April 18, 1930. 73 years after Sepoy Rajob Ali of Chittagong took arms that ignited the 1857 Sepoy Mutiny, Chittagong ignited once again. Master Da’ Surya Sen and his brave men and women attacked the ‘eyes of the dragon’. The Chittagong police and army armoury were raided. Telegraph and rail lines were snapped. For four days, Chittagong was free from the clutches of India’s colonial masters. In the end, The British brutally crushed the uprising. Master Da’ walked the gallows. Binod Bihari Chowdhury (1911-2013) remained ‘The Last of the Mohicans’ for decades to come. Alas! He too left on April 10, 2013.
Binod Bihari Chowdhury (Jan 10, 1911- Apr 10, 2013) was born in Uttar Bhurshi village of Boalkhali, Chittagong. He was the fifth child of Kamini Kumar Chowdhury (Lawyer) and Roma Rani Chowdhury (Housewife). At Coronation School at Fatikchhari, Binod met Ramkrishna Biswas, the first boy of Class X. Through books, Ramkrishna introduced Binod to a world of great men and revolutionaries. The book ‘Desher Kotha’ was an eye opener. It exposed the unjust British Rule in India. Binod decided to join the revolutionaries of his time. His chance came very soon.
Jugantor, Anushilon, Forward Block were among the leading revolutionary groups in 1920′s Chittagong. These groups believed British Colonial Rule in India could end through armed struggle. Through Ramkrishna, Binod became a member of Jugantor in 1928. The leader Master Da’ Surya Sen was then in jail. Binod’s first encounter with Master Da’ was in 1929 at Abhoymitra Cremation Ground at Boluar Dighi, Korbaniganj, Chittagong. Master Da’ discouraged Binod to join Jugantor, but Binod’s mind was set. A year later, Binod became a part of history.
The Chittagong Armoury Raid included women. Pritilata Waddedar and Kalpana Dutta were in the group. Master Da’ divided the team into four groups. Binod was in the group that would attack the Police armoury (Dampara, near today’s WASA). The operation started at 10pm on April 18, 1930. The revolutionaries succeeded in disconnecting Chittagong and also capturing the European Headquarter (in Pahartali, now Railway Office). Master Da’ proclaimed Chittagong free. The revolutionaries left the city and took refuge in the hills.
Unfortunately, April 18, 1930 was Good Friday. Many of the British officers were at home. They could thus take guard and prepare for a counter-attack. Four days later, April 22, 1930 thousands of troops ambushed the revolutionaries at the Jalalabad Hills (in today’s Chittagong Cantonment). The British troops crushed the uprising. Master Da’ and Binod survived, but Binod was wounded by a bullet that passed through the left side of his neck.
Master Da’ went into hiding and moved from one place to another. In 1933, one of his relatives, Netra Sen, informed the British for a ransom of Tk 10,000. Master Da’ was arrested February 2, 1933. Netra Sen could not enjoy his prize money. A member of Master Da’s group came and killed Netra Sen.
Tarekshwar Dastidar tried to rescue Master Da’ from Chittagong Jail. The British found out. Tarekshwar, Kalpana Datta and others were arrested. Master Da’ and Tarekshwar were sentenced to death. After brutal torture at the hands of the British, Master Da’ and Tarekshwar were hanged January 12, 1934. Chittagong’s freedom was short-lived, but it was a catalyst to 1947 when the Raj was partitioned in ‘freedom at midnight’.
After partition, Binod remained in Chittagong and contributed towards the society in his own way. His wife and life partner of seventy years, Biva Das (Died 2009), was a teacher of Aparna Charan Girls’ School. To run the family, Binod started private tuitions of students of Aparna Charan. In no time, he became popular. His students did well. Master Da’s lieutenant, Binod Bihari Chowdhury, now became Binod Dadu to the children. Many children of Chittagong have received lessons from Dadu. While passing on the spirit of freedom to the young generation, Dadu was always aware of his responsibilities in speaking out against injustice in the society.
In January this year, during my last visit to my birthplace and motherland, Chittagong, I promised my daughter, Annapurna, I would take her to historical places. We visited JM Sen Hall where busts of Master Da’ and other revolutionaries of 1930′s Chittagong are preserved. Amazing! Old age could not defeat Binod Dadu. Dadu had gone to Dhaka to celebrate his 104th birthday at the Muktijuddha Jadughar. I took my daughter to Dadu’s house in Momin Road (near Cheragi Pahar Roundabout). We learned Dadu returned and would give us a few minutes. There we were with ‘The Last of the Mohicans’ in a room decorated with memories of Master Da’, Pritilata and other revolutionaries of 1930′s Chittagong—a golden era in our history. I introduced Dadu to my daughter as Master Da’ Surya Sen’s youngest friend. Dadu’s gentle smile as a response is now sealed in my heart. We are very lucky Dadu blessed us.
Binod Dadu, Master Da’, Pritilata, Kalpana, Tarekshwar of Chittagong all played their part to establish a just society. Because of them, we found inspiration in 1947, 1952, 1969, 1971, 1991, and also now in 2013. The ball is now in the court of today’s Campus Generation to play their role in establishing a society free of discrimination. Binod Dadu- The Last of the Mohicans of glorious Chittagong- faretheewell, but never goodbye.
(The author teaches economic theory at Jahangirnagar University)
______________
http://www.thedailystar.net/beta2/news/binod-bihari-chowdhury-the-last-of-the-mohicans/
 বিপ্লব রহমান | 127.18.231.47 | ২২ আগস্ট ২০১৩ ০৮:৩৬582580
বিপ্লব রহমান | 127.18.231.47 | ২২ আগস্ট ২০১৩ ০৮:৩৬582580- [”অনুবাদকের নোট
একাত্তরে দেশী/বিদেশী ইংরেজী পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রকাশিত রিপোর্টগুলো আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়।
‘বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র’-এর উদ্যোগে একাত্তরে দেশী/বিদেশী ইংরেজী পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রকাশিত রিপোর্টগুলো বাংলায় অনুবাদ করা শুরু করি। এই অনুবাদগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে অনলাইনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে।– সাব্বির হোসাইন
:line:
১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফে প্রকাশিত ডেভিড লোশাকের রিপোর্ট:
২৭ মার্চ,১৯৭১
দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ
ডেভিড লোশাক, দিল্লী।
পূর্ব-পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে
‘শেখ মুজিবুর রহমান একজন বিশ্বাসঘাতক’…..জেনারেল ইয়াহিয়া
পূর্ব-পাকিস্তানে গতকাল হতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে।
ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের পশ্চিমাংশের সৈন্যদের সাথে পূর্বাংশের বাঙালীদের তীব্র যুদ্ধ হচ্ছে, অনেক মানুষ হতাহত হয়েছে। ভারতের মত বিশাল রাষ্ট্রকে মাঝখানে রেখে ভৌগলিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তান হতে হাজার মাইল দূরে থাকা পূর্ব পাকিস্তানের সাথে গতকাল রাত হতে সারা বিশ্বের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।
পশ্চিম পাকিস্তান হতে পাঠানো সত্তর হাজার সুসজ্জিত সৈন্যদের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর বাঙালী সদস্যদের প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হবার পর হতে পূর্ব-পাকিস্তানের বিদ্রোহী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। ঢাকার একটি সূত্র মতে, শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ঘনিষ্ট পাঁচ সহযোগীসহ গ্রেফতার করা হয়েছে।
ঢাকাসহ পূর্ব-পাকিস্তানের অন্যান্য শহরগুলোতে কারফিউ জারি করা হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা ঢাকা বেতারকেন্দ্র দখল করার দাবি করছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে ব্যাপক সংঘর্ষের এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে বিপুল সংখ্যক বেসামরিক বাঙালীকে হত্যা ও গ্রেফতারের খবর পাওয়া যাচ্ছে।
গতকাল রাতে পশ্চিম পাকিস্তান হতে বেতারে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশ্বাসঘাতক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী অভিহিত করে বলেছে, ‘এই অপরাধের শাস্তি পেতেই হবে। আমি এই ক্ষমতালোভী-রাষ্টদ্রোহীকে পাকিস্তানের বারো কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা করতে দেবো না।’
শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি অনুগত বাঙালী সৈন্যরা চট্টগ্রামের বেতারকেন্দ্রটি তুমুল যুদ্ধের পর পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার দাবি করেছে। গতকাল রাতে ‘স্বাধীন বাংলা বেতার’ নামে একটি বেতারকেন্দ্র, শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষনা করেছেন বলে প্রচার করেছে।
পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের ঘিরে ফেলেছে
ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পুলিশের বাঙালী সদস্যরা চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, যশোর, বরিশাল ও খুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে বলে ‘স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র’ হতে প্রচার করা হয়েছে।
শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, পূর্ব-পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল টিক্কা খানের অধীনে থাকা পশ্চিম-পাকিস্তানী সৈন্যরা রাজারবাগে অবস্থিত পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেলসের ব্যারাক ও পুলিশ লাইনে অর্তকিত আক্রমন করে অসংখ্য বাঙালীকে হত্যা করেছে। বাঙালীরা স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে লড়ছে। হে মহান আল্লাহ, স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের সাহায্য করুন।
অপরদিকে, পূর্ব-পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল টিক্কা খান বাঙালীদের স্বাধীনতার সংগ্রামকে যেকোন উপায়ে ধুলিসাৎ করা হবে বলে ঘোষনা দিয়েছে।
জেল পেনাল্টি
বাঙালীর স্বাধীনতার সংগ্রামকে নসাৎ করার জন্য পাকিস্তান সরকার বেশ কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করেছে।
• স্বাধীনতার ঘোষনা প্রচারকারীদের দশ বছরের কারাদন্ড দেয়া হবে।
• কোন রাজনৈতিক কর্মসূচী পালন করা যাবে না।
• পূর্ব-পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা নিয়ে কোন প্রকার প্রকাশনা করা যাবে না এবং বিদেশী কোন খবর পাঠানো যাবে না।
• শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে যেসব সরকারী ও আধা-সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী অফিস-আদালত বর্জন করেছেন, তাদের বাধ্যতামূলকভাবে অফিস-আদালতে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।
• সকল আগ্নেয়াস্ত্র সরকারের কাছে জমা দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। প্রকাশ্যে লাঠি নিয়েও বের হওয়া যাবে না।
• কোন প্রকার হরতাল বা, অসহযোগ কর্মসূচী পালন করা যাবে না।
• পাকিস্তান সেনাবাহিনী যেকোন সময় যেকোন প্রতিষ্ঠান বা, ব্যাক্তিকে জেরা ও তল্লাসী করতে পারবে।
জেনারেল টিক্কা খান বলেছে, বাঙালীরা পূর্ব-পাকিস্তানের পরিস্থিতি চরম অস্থিতিশীল করে তুলেছে। পাকিস্তানের অবস্থা স্বাভাবিক করতে হলে ও একতা ধরে রাখতে হলে বাঙালী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের লাগাম টেনে ধরতে হবে।
গতকাল রাতে পশ্চিম পাকিস্তানী সরকারের আদেশে ঢাকায় দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক সাইমন ড্রিং-সহ অন্যান্য বিদেশী পত্রিকার সাংবাদিকরা হোটেলে অবরুদ্ধ ছিলেন।
পশ্চিম পাকিস্তান হতেও সহিংসতার খবর পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে, ভূট্টোর সমর্থকরা বাঙালীদের ঘর-বাড়ি-দোকানে ব্যাপক হামলা চালায়। লাহোরের কাছে লালপুর শহরে বসবাসরত বাঙালীদের উপর ব্যাপক হামলার প্রেক্ষিতে সেখানকার প্রশাসন কারফিউ জারি করেছে।
আলোচনা ভেস্তে গেছে
পূর্ব-পাকিস্তানে উদ্ভুত অচলাবস্থা সমাধানকল্পে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে এগারো দিন ধরে আলোচনা করার পর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে হঠাৎ করে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙালীদের উপর সহিংসতা শুরু হয়।
গত কয়েকদিনের আলোচনা থেকে মনে হয়েছিল, পূর্ব-পাকিস্তানের অবস্থার উন্নতি ঘটবে কিন্তু বাস্তবতা হল সমঝোতা হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, বরং বাঙালী নেতাদের সাথে জেনারেল ইয়াহিয়ার নিষ্ফল আলোচনা পশ্চিম-পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে পূর্ব-পাকিস্তানে এসে নিজেদের অবস্থান গ্রহণে প্রচুর সময় করে দিযেছে।
এর আগে, মার্চের ০৬ তারিখ এক ভাষণে জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের অখন্ডতা ধরে রাখতে সামরিক হস্তক্ষেপ করার ইঙ্গিত দিয়েছিল।
সহিংসতার আশঙ্কা
পূর্ব-পাকিস্তানে দীর্ঘমেয়াদী মারাত্মক সহিংসতা হবার আংশকা করা যাচ্ছে। একটি সুসজ্জিত-শক্তিশালী সেনাবাহিনী মুক্তিকামী একটি জাতিকে দমিয়ে রাখতে পারবে কি-না, তা এখন দেখার বিষয়।
ভারত সরকার পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্যকার আকাশপথ বন্ধ করে দিয়েছে। এখন পশ্চিম পাকিস্তান হতে রসদ-বোঝাই বিমানগুলো শ্রীলংকা হয়ে ছয় ঘন্টার পথ পাড়ি দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানে যাচ্ছে। সমুদ্রপথে পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্তানের এই দূরত্ব এক সপ্তাহেরও বেশি।
পশ্চিম-পাকিস্তানী সেনাবাহিনী মারাত্মক শক্তি প্রয়োগ করে ও ব্যাপক সহিংসতার মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতার আন্দোলন হয়তো সাময়িকভাবে অবদমিত করতে পারবে কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতা অবিশ্বম্ভাবী।”]
http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=36929
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ১৫:৩১582581
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ১৫:৩১582581- আমাদের সময়ের নায়কেরা-০২
-- বিপ্লব রহমান
_________________________________
‘এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাওয়ার তার শ্রেষ্ঠ সময়’…। কবি হেলাল হাফিজের ‘নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়’ র অমর কবিতা। দ্বিতীয় প্রজেন্মের চলমান মুক্তিযুদ্ধে কবিতাটির অক্ষরগুলো যেনো প্রাণ ফিরে পেয়েছে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে, ১৯৯০ এর জে. এরশাদ সরকার বিরোধী ছাত্র-গণঅভ্যুত্থান থেকে শুরু করে অসংখ্য গণআন্দোলনে, মিছিলে, মিছিলে, গণসমাবেশে, দেওয়াল লিখনে, আন্দোলনের মঞ্চে অসংখ্যবার উদ্ধৃত হয়েছে এই অজয় কবিতা। শাহবাগের মোড় — প্রজন্ম চত্বরকে ঘিরে সারাদেশে চলমান গণজাগরনের মঞ্চগুলোতেও পাঠ হচ্ছে উদ্দীপনী এই কাব্যগাঁথা।
কিন্তু কি ছিলো এই কবিতা রচনার প্রেক্ষাপট? কেমন করে একজন কবির কলমের ডগায় গ্রন্থিত হয় এমন অবিনাশী অক্ষরসমূহ? কোন মন্ত্রবলে লেখা হয় এমন যুদ্ধের আহ্বান?
এইসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে ছাত্রত্ব ঘুচে যাওয়ার পর সাংবাদিকতার শুরুতে, একাধিক সাপ্তাহিকের প্রদায়ক হিসেবে কাজ করার কালে ১৯৯২ সালের দিকে এক পড়ন্ত বিকেলে আরো একজন সহকর্মীসহ মুখোমুখি বসা হয়েছিলো কবি হেলাল হাফিজের। তিনি তখন ‘দৈনিক দেশ’ নামক একটি সংবাদপত্রের সাহিত্য সম্পাদকের দায়িত্বে। সেগুন বাগিচায় ইংলিশ প্যাটার্নের পুরনো যে দোতলা বাড়িতে এখন গড়ে উঠেছে ‘মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর’, সেটিই তখন ছিলো পত্রিকারটি কার্যালয়। সাংবাদিকতায় যুক্ত হওয়ার সুবাদে কবি প্রেসক্লাবের সদস্যপদ পেয়েছিলেন। সেখানেরই গেস্ট ক্যান্টিনে ধূমায়িত চায়ের কাপ নিয়ে বসা গেছে।
এ কথা, সে কথা, কবিতার সঙ্গে কবির সংসার, অনিয়মিত পেশা, আয় ও অনাহার, সব কিছু অকপটে বলতে থাকেন কালো চাপ দাঁড়িতে সৌম্য দর্শনের হেলাল হাফিজ। তার কোনো প্রেম বা দ্রোহের কবিতাই শেষ পর্যন্ত ওই একটিমাত্র কবিতাটিকে ছাপিয়ে যায়নি কেনো? এমন প্রশ্নের জবাবে কবি বেশ খানিকটা থমকে যান। দু-এক মুহূর্ত কপালের দুপাশের রগ দুহাতে চেপে ধরে, চোখ বন্ধ করে ভাবেন। তারপর অনর্গল বলতে থাকেন একটি অক্ষয় কবিতা রচনার আদ্যপান্ত, বলাভালো, ইতিহাস।
সেদিন কবি হেলাল হাফিজ ক্ষুদে সাংবাদিককে যা বলেছিলেন, তা কবির বয়ানে অনেকটা এরকম:
দেখুন, একটি কবিতা একটানেই হয়তো লেখা হয়, কিন্তু এর নির্মাণ প্রক্রিয়া মাথার ভেতরে চলে দীর্ঘ সময় ধরে। বিখ্যাত লেখকেরা একে বলেন, প্রস্তুতিপর্ব। এটি নির্ভর করে শুধু কাব্যভাবনার ওপরে নয়, কবির চারপাশে যা ঘটছে, যা কবিকে ভাবাচ্ছে, অথবা কবি যা ভাবতে চান, সব কিছুর ওপর। বিষয়টি একটি ছোট্ট চারাগাছের জন্মের সঙ্গেই তুলনা করে চলে। এক সকালে আপনি দেখলেন, অনুর্বর জমিতে হয়তো উঁকি মেরেছে একটি ছোট্ট চারাগাছের দুটি কিশলয়। এটি আপনা-আপনি, নিজে নিজে প্রকৃতিতে ঘটে না। চারাগাছ জন্মের জন্য সুস্থ-সবল বীজ চাই। বীজটি সঠিক জমিতে, সঠিক আলো-হাওয়ায়, সঠিক সার-পানিতে বোনা চাই। তবেই এটি হয়তো একদিন মাটি ভেদ করে সূর্যের আলো দেখবে। কবিতাও ঠিক তেমননি। এটি কবিই কলমে দিয়ে কাগজে অক্ষর দিয়ে ফুঁটিয়ে তোলেন ঠিকই। কিন্তু এর নির্মাণকাল চারাগাছের জন্ম নেওয়ার মতোই একটি ঘটনা। গাছটি উপকারি হলে মানুষ যেমন একে যতœ করে যুগ যুগ বাঁচিয়ে রাখে, তেমনি কবিতাও মানুষের মনে আঁচড় কাটতে সক্ষম হলে এর পাঠকরাই একে যতœ করে বছরের পর বছর ধরে বাঁচিয়ে রাখে। …
সেটি ছিল ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাস। টগবগে লাভার ভেতরে ফুটতে থাকা উত্তাল পূর্ব বাংলা। ছাত্র-গণঅভূত্থানের সময়। ২১ জানুয়ারির বিকেলে শুনশান, নিস্তব্ধ এক অচেনা নগরীর পথ ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বন্ধুর রুমে রাতটুকু কাটানোর জন্য রিকশা ধরে যাচ্ছি। সন্ধ্যার পরেই আরো সংঘাত-সংঘর্ষের আশঙ্কায় দ্রুত আশ্রয়ে ফেরার জন্য সকলেরই খুব তাড়া। এর আগেরদিনই ২০ জানুয়ারি পাক-সামরিক জান্তার লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ- ইপিআর বাহিনীর (ইপিআর, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, সীমান্তরক্ষী বাহিনী) গুলিতে নিহত হয়েছেন ছাত্র নেতা আসাদ। পুরো ঢাকা শহর ক্ষোভের জ্বলছে। সারাদেশেই ছড়িয়ে পড়েছে গণ-বিক্ষোভ। ঢাকার এখানে-সেখানে ছাত্র-জনতা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। মিছিলের পর মিছিল। শ্লোগানের পর শ্লোগান। বিশালাকায় মিছিল-সমাবেশের আয়তন। প্রায় প্রতিদিনই পুলিশের গুলিতে কোনো না কোনো ছাত্র মারা যাচ্ছেন। তবু জনতার সংগ্রাম চলছেই। …
রিকশায় বসে বন্ধুর ছাত্রবাসে ফিরতে ফিরতে এইসবই ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছিল মাথার ভেতর। এরপর করণীয় কী? কি হবে বাংলার ভবিষ্যত? যুদ্ধ কি সত্যিই আসন্ন? স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হচ্ছে কবে? রিকশা যখন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর পেরিয়ে যাচ্ছে, তখন অস্থিরতার ভেতরেই বুড়ো মতোন রিকশা ওয়ালাকেই জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা চাচা মিয়া, বলেন তো, এই যে ছাত্ররা প্রতিদিন মিছিলে গুলি খেয়ে মরছে, তবু আন্দোলন চলছেই, এর শেষ কোথায়? আর কতো গুলি চলবে? আর কতো রক্তক্ষয় হবে? এখন কি করণীয়? বুড়ো রিকশাওয়ালা ঘাড় ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে এক নজর দেখে সেদিন যা বলেছিলেন, তা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন ওই বুড়ো আমাকে বলেছিলেন, বাবা, কিছু মনে করো না। আমার মনে হয়, অনেক ছাত্র খুন হইছে। এখন এর বিহিত করনের সময় হইছে। এখন ছাত্রদেরও উচিত হইবো কিছু পুলিশ-ইপিআর মাইরা ফেলা। কারণ, সব হত্যায় পাপ নাই!
এই কথা শুনে সেদিন আমার সর্ব শরীর কেঁপে উঠেছিল। কথাগুলো একদম কলজের ভেতরে গেঁথে যায়। বন্ধুর ছাত্রাবাসের রুমে গিয়ে আমি ভেতরে ভেতরে আরো অস্থির হয়ে উঠি। সেখানেও তখন ছাত্ররা মিছিল-মিটিং, আন্দোলন-সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে। হাতে লেখা পোস্টার তৈরি হচ্ছে। সর্বত্র যুদ্ধের আবহ। রাত হতে না হতে ক্যাম্পাসের শুনশান নিরবতা ভেদ করে দূর থেকে ভেসে আসতে থাকে শ্লোগানের ধ্বণী। সেদিন রাতে অনেক চেষ্টা করেও আর ঘুমাতে পারিনি। বার বার মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল বুড়ো রিকশাওয়ালার সেই কথাগুলো। কি যন্ত্রণায় মনে মনে ছটফট করতে করতে ভোর রাতে উঠে রুমের বাতি জ্বালাই। কাগজ-কলম টেনে নিয়ে একটানে লিখে ফেলি ওই কবিতাটি:
কোনো কোনো প্রেম আছে প্রেমিককে খুনী হতে হয় ।
যদি কেউ ভালোবেসে খুনী হতে চান
তাই হয়ে যান
উৎকৃষ্ট সময় কিন্তু আজ বয়ে যায় ।
এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময় ।…
[লিংক]
পরে সকাল হওয়ার জন্য অপেক্ষা করি। তখন আমাদের তরুণ কবিদের প্রেরণাদাতা ছিলেন আহমদ ছফা, ছফা ভাই। এখন যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ, এর উল্টোদিকের মাঠের এককোনো তখন ঝুপড়ি একটি রেঁস্তোরা ছিলো। আমরা কবি-সাহিত্যিকরা সেখানে বসেই আড্ডা দিতাম। ছফা ভাই প্রতি সকালে সেখানে আসতেন নাস্তা করতে। আমি দোকানটিতে গিয়ে ছফা ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। তিনি এলে পকেট থেকে কবিতা লেখা কাগজটি বের করে তাকে দেখাই। ছফা ভাই কবিতাটি একবার-দুবার পড়েন। এরপর আবারো পড়েন। তারপর হঠাৎ উল্লাস করে আমাকে জড়িয়ে ধরেন। বলেন, হেলাল, তুমি বোধহয় তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ লেখাটি লিখে ফেলেছো! এই কবিতাটিতেই তুমি আজীবন বেঁচে থাকবে।
সেদিন ছফা ভাই ওই কথা কেনো বলেছিলেন, বুঝতে পারিনি। পরে কবিতাটি ছফা ভাই উদ্যোগ নিয়ে লিফলেট আকরে প্রকাশ করেন। ছাত্র-জনতা কবিতাটিকে সারা বাংলায় ছড়িয়ে দেন। এটি অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরিস্থিতির কারণেই তখন কবিতাটি কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। …
তবে ছফা ভাই সেদিন বোধহয় ঠিকই বলেছিলেন। এরপর অনেক কবিতা লিখেছি। এখনো লেখার চেষ্টা করছি। প্রেমের কবিতা, প্রকৃতির কবিতা, সংগ্রামের কবিতা। কিছু কিছু কবিতা পাঠক প্রিয়তা পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু কোনো কবিতাই কখনোই ওই কবিতাটির জনপ্রিয়তাকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি। … একজন কবি জীবদ্দশায় তার নিজেরই লেখা একটি কবিতার এমন অবিশ্বাস্য জয়-জয়াকার দেখেছেন, এটি ওই কবিতার জনক হিসেবে আমার কাছে অনেক বড়ো পাওয়া। কবিতা বা জীবনের কাছে আমার আর কোনো প্রাপ্তি নেই। …
পরে কবির এই কথোপকথনটি সে সময় প্রয়াত সাংবাদিক মিনার মাহমুদ সম্পাদিত জনপ্রিয় সাপ্তাহিক ‘বিচিন্তা’য় ছাপা হয়। এর শিরোনাম ছিলো: ‘কোনো কোনো প্রেম আছে প্রেমিককে খুনী হতে হয়’… ।
http://biplobcht.blogspot.com/2013/02/blog-post_15.html
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ১৫:৩৪582582
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ১৫:৩৪582582- উসুয়ে হাওলাদারের দীর্ঘ সংগ্রাম!
--বিপ্লব রহমান
_________________________________
রাখাইন আদিবাসী নেতা উসুয়ে হাওলাদার (৮১)। গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালির কলাপাড়ায়। অগ্রসর চেতনার মানুষটি আজন্ম সংগ্রাম করে আসছেন সব ধরণের শোষণ-নিপীড়ন-বৈষম্যের বিরুদ্ধে। ১৯৫২ তে লড়েছেন রাষ্ট্রভাষার জন্য, ১৯৭১ এ দেশ মাতৃকাকে স্বাধীন করার জন্য সংগঠিত করেছেন মুক্তিযুদ্ধ ।
এখন এই শেষ বয়সে এসেও তার সংগ্রাম শেষ হয়ে যায়নি। এবার তিনি লড়ছেন নিজ স্বাধীন দেশে, নিজ দেশের শাসক-শোষক গোষ্ঠির নিপীড়নের বিরুদ্ধে। ... এ লড়াই নিজ মাতৃভাষা ‘রাখাইন’ রক্ষার। গ্রাম্য জোতদার, আর ভূমি দস্যুদের কবল থেকে আদিবাসীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার।
সম্প্রতি ঢাকার এক অনুষ্ঠানে অমায়িক মানুষটির সঙ্গে আলাপচারিতা হয়। পরে টেলিফোনেও কথা হয় তার সঙ্গে। জানা যায়, সংগ্রামী মানুষটির দেশের জন্য আত্নত্যাগ আর একনিষ্ঠার কথা।
উসুয়ে হাওলাদার বলেন, “আমার জন্ম ১৯৩২ সালে, পটুয়াখলি জেলার রাঙাবালির বড়বাইসদিয়া গ্রামে। বাবা প্রুহ্লাউ হাওলাদার ছিলেন ইউনিয়ন বোর্ড মেম্বার। বাবা-ঠাকুরদা সকলেই ছিলেন রাজনীতি সচেতন। ১৯৫২ সালে আমি বরিশাল মিশন স্কুলের ছাত্র। খুব কড়াকড়ি ছিলো স্কুলে। বাবাদের কাছে শুনেছিলাম, রাষ্ট্রভাষা পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষের [আদিবাসীদের দ্বিতীয়তম] ব্যবহারিক ভাষা "বাংলা"র বদলে "উর্দূ"কে রাষ্ট্রীয় তথা দাপ্তরিক ভাষা করার ঘোষণা দেয় পাক সরকার। প্রতিবাদে ফেটে পড়ে পূর্ব বাংলা। ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে নামে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভের ঢল। পুলিশ-ইপিআর [ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, সীমান্তরক্ষী বাহিনী] গুলি চালালে শহীদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউল প্রমুখ।
মুক্তিকামী জনতার বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে বৃহত্তর চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশালেও।
“সে সময় বাঙালি না হযেও মুক্তচিন্তার মানুষ হিসেবে আমি স্কুল পালিয়ে এসব প্রতিবাদী মিছিল-সমাবেশে নিয়মিত অংশ নিয়েছি। শ্লোগান তুলেছি সমান জোরগলায়, উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা করা চলবে না! তোমার-আমার-ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা!
“বাঙালি না হয়েও সে সময় রাখাইন আদিবাসী ছাত্র হিসেবে আমি বুঝেছিলাম, উর্দূকে পূর্ববাংলার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া হলে শুধু বাঙালিরাই বিপদে পড়বে তাই নয়, এই রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন থেকে আমরা আদিবাসীরাও শেষ পর্যন্ত কেউই বাদ যাবো না। তাছাড়া মন থেকে এতো বড়ো একটি নিপীড়নমূলক ষড়যন্ত্র আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। তাই স্কুল পালিয়ে জিলা স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে মিছিল-সমাবেশে নিয়মিত অংশ নিতাম। বরিশাল অশ্বনী কুমার হলের সামনে বড় বড় সমাবেশ হতো। সে সময়ের নেতা ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সংগঠক আব্দুল হামিদ, ব্যারিস্টার সাইদুর রহমান, আব্দুর রহমান এমএলএ প্রমুখ সব সময়ই আমাকে উৎসাহিত করছেন।
"সে সময়ই পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল, পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ববাংলার আর থাকা চলে না। এবার চাই স্বাধীন দেশ। ৬০ দশকে নানা ঘটনা, চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে অগ্নিগর্ভ দেশ ১৯৬৯ সালের ছাত্র-গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচন এসে যায়। ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সুবাদে পড়ালেখা ছেড়ে আমি তখন পুরোপুরি রাজনৈতিক কর্মী। কলাপড়া থেকে ন্যাপ- মোজাফফরের হয়ে এমপি নির্বাচনও করি। আমার অঞ্চলের আদিবাসী ও সাধারণ স্থানীয় বাঙালিরা আমাকে আকুণ্ঠ সমর্থন দেয়। তবে আওয়ামী লীগ সে সময় নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করলেও পাক সরকার কিছুতেই তাদের সরকার গঠন করতে দেয় না। ১৯৭১ এ দেশ স্বাধীনতার দোরগোড়ায় পৌঁছে। ২৫ মার্চের পর সবখানে পাক-সামরিক জান্তা আর তাদের সহযোগিরা গ্রামের পর গ্রাম লুঠপাঠ, অগ্নিসংযোগ আর হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকে। পাল্টা চলে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধ লড়াই। ...
“বরিশাল, পটুয়াখালি থেকে দলে দলে গৃহহীন মানুষ এসে আশ্রয় নেয় কলাপাড়ায়। সে সময় আমি দলবল নিয়ে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করি। রাজাকারদের রোষানল থেকে জীবন বাঁচাতে অনেককে বরগুনা, পাথরঘাটা, সুন্দরবন হয়ে ভারতে নৌ পথে পালিয়ে যেতে সহায়তা করি। আমার মাধ্যমেই সেখানের মুক্তিযোদ্ধারা খবরা-খবর পেতো। কিয়াঙগুলো (বৌদ্ধ বিহার) ছিল নিরাপদ আশ্রয়স্থল। সেখানে দিনের পর দিন অগণিত হিন্দু-মুসলিম নারী পুরুষকে আশ্রয় দেই। ...এই কাজ করতে গিয়ে এক সময় নিজেও রাজাকার বাহিনীর টার্গেটে পরিনত হলে এলাকা ছেড়ে পালাই।...
“...এখন স্বাধীন দেশে আবারো নতুন করে লড়াই করছি নিজ মাতৃভাষা রক্ষার জন্য। সরকারি-বেসরকারি মহলে নানাভাবে ধর্ণা দিচ্ছি অন্তত শিশুশ্রেণী পর্যন্ত যেন রাখাইন ছেলেমেয়েরা নিজ মাতৃভাষায় পড়াশুনা করতে পারে। অনেক চেষ্টা-তদ্বিরে কিছু সুফল পাওয়া গেছে। এখানকার কলাপাড়া, কুয়াকাটা, আমখোলা, মিশ্রীপাড়া, কালাচানপাড়া, তালতলিপাড়া, আগাঠাকুরপাড়া, কবিরাজপাড়া, সদাগরপাড়া ইত্যাদি রাখাইন অধ্যুষিত কিয়াঙগুলোতে রাখাইনভাষার স্কুল চলছে। রাখাইন ভাষাতেই আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দিতে পারেন, এমন শিক্ষকও আমাদের আছেন। কিন্তু বইপত্র, স্কুলের অবকাঠামো, শিক্ষকের বেতনসহ নানা বিষয়ে সহযোগিতা প্রয়োজন। সরকার এই কাছে সহযোগিতা করলে রাখাইন ভাষাটি অস্তিত্বের সংকট থেকে মুক্তি পায়। শিশু বয়সে নিজভাষায় আদিবাসীরা লেখাপড়া শিখতে পারলে ভবিষ্যতে তাদের ওপরের শ্রেণীতে সাধারণ পাঠক্রম বুঝতেও সুবিধা হয়।
“আশার কথা, বেসরকারি উদ্যোগে কিছুটা সুফল পাওয়া গেছে। কারিতাস নামক বেসরকারি সংস্থা রাখাইন ভাষার বইপত্র দিয়ে সহযোগিতা করছে। কিন্তু আমাদের স্কুলগুলোর প্রয়োজন পূর্ণ উদ্যোগে আরো অনেক সহযোগিতা। আমরা বৃহত্তর পটুয়াখালিতে আদিবাসীর মাতৃভাষায় শিক্ষাকে উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই।...
দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে কোনো হতাশা? এমন প্রশ্নের জবাবে উসুয়ে হাওলাদার বলেন, হতাশার তো শেষ নেই! চোখের সামনে ভূমি দস্যুরা আদিবাসী রাখাইনদের জমি-জমা, ব্যবসা-বাণিজ্য কেড়ে নিচ্ছে। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে একে একে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে রাখাইন ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্প। আমার নিজের জমি-জমা, বাড়িঘরও নিরাপদ নয়। নানা স্বার্থান্বেসী মহল এগুলো লুঠপাটের চেষ্টায় ব্যস্ত। অন্যদিকে সারাদেশ ছেয়ে যাচ্ছে রাজাকার আর মৌলবাদে। ... এইসব দেখে মাঝে মাঝে খুব হতাশ লাগে। মনে হয়, এই জন্য কি আমরা ভাষার আন্দোলন করেছি? এমন দেশের জন্য কি আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম? ...
“তবে হতাশ হয়ে বসে থাকলে তো আর চলবে না। তাতে কোনো কাজেই জয়ী হওয়া যাবে না। হতাশা চেপে রেখে দৃঢ় মনোবাসনা নিয়েই আমাদের সামনে এগুলোতে হবে।...তাই আদিবাসীর ভাষা রক্ষার প্রচেষ্টার পাশাপাশি এখন ভূমি দস্যু আর জমি জালিয়াতচক্রর হাত থেকে আদিবাসীর জমি রক্ষার জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। সংগ্রামের তো শেষ নাই!...”
http://biplobcht.blogspot.com/2013/07/blog-post_16.html
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ১৮:২৪582583
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ১৮:২৪582583- চন্দ্রমুখী জানালা
লিখেছেন: ভজন সরকার
_____________________
(মুক্তিযুদ্ধ, শরনার্থী ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের অবস্থা এবং অবস্থান নিয়ে ধারাবাহিক)
(১)
পড়ন্ত বেলায় বাবা কেন দেশ ত্যাগ করলেন আমি এখনও জানি না| শুনেছি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে একবার ইন্ডিয়া গিয়েছিলেন আমার মাতৃকুলের সবাইকে জানান দিতে যে, তিনি বেঁচে আছেন| পাকিস্তানী হানাদার কিংবা দেশীয় রাজাকারের হাতে তাঁর অপমৃত্যু হয়নি| এ কথা নাকি লোকমুখে সুদূর কলকাতাতেও চাওড় হয়ে গিয়েছিল যে, মানিকগঞ্জের এক অজ পাড়াগাঁয়ের বটগাছে পাকিস্তানী মিলিটারীরা এক জনকে ঝুলিয়ে রেখেছে| কালো কুঁচকুঁচে ছয় ফুট মানুষটির ক্ষতবিক্ষত দেহ প্রথমে গুলি করে ঝাঁঝরা করা হয়েছে| তারপর বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আরও বিভৎস্য করার চেষ্টা হলেও ঝুলিয়ে রাখা মানুষটিকে এলাকার সবাই চিনেছে| মৃত্যুর কথা যেমন হু হু বাতাসের বেগে চারিদিকে ছড়ায়, বাবার মৃত্যু সংবাদটিও তেমনি কলকাতা অব্দি ছড়িয়েছিল তখন|
এ মুক্তিযোদ্ধাটি নিজের জীবন বিপন্ন করে সদ্য জন্মনেয়া তার কন্যাসন্তানকে দেখতেই নাকি রাতের অন্ধকারে গ্রামে এসেছিলেন| যদিও তাঁর জানা ছিল পাকিস্তানী মিলিটারী ও তাদের সহযোদ্ধা আল-বদর আল-শামসের এলাকায় আনাগোনা| তবুও বড় এক অপারেশনের আগে সদ্য ভূমিষ্ট হওয়া কন্যা সন্তানকে দেখার ইচ্ছে অবদমিত করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি| তাই বর্ষাকালের থই থই জল পেরিয়ে বিলাঞ্চলের গ্রামটিতে এসে তিনি নাকি তার কন্যা সন্তানটির দেখাও পেয়েছিলেন| মাত্র কয়েক সপ্তাহের শিশুটির মাথায় হাত রেখে তিনি বলেছিলেন, আর একটু পরে এলেই তো স্বাধীন একটি দেশে জন্ম নিতে পারতিস, পাকিস্তানে জন্ম নেবার কলঙ্ক মাথায় পড়ত না তোর|
এটা থেকে ধরে নেয়া যায়, নিহত মুক্তিযোদ্ধাটি আগষ্ট কিংবা সেপ্টেম্বর মাসের কোন এক রাতে তার সন্তানকে দেখতে এসেছিলেন| কন্যা সন্তানটিকে দেখার কিছুক্ষণ পরেই তিনি বাড়ি থেকে বের হন এবং বিলের শেষ মাথায় রাজাকার ও পাকিস্তানী মিলিটারির প্রতিরোধের মুখে পড়ে আহত হন | পরে মৃত্যুবরণ করেন| এ সংবাদটি কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছিল তখন| আমার ছোট বোনটির জন্মও সে বছরই আগষ্ট মাসে| মায়ের সন্তান সম্ভাবার কথা কলকাতার সবাই জানতেন| তাই আনন্দবাজারের সংবাদটি পড়ে বাবার মৃত্যুর ব্যাপারে আমার মামাবাড়ির সবাই নিশ্চিত হয়েছিলেন| আমার মায়ের আত্মীয়-স্বজনেরা গয়ায় গিয়ে নাকি পিন্ডিও দিয়ে এসেছিলেন বাবার আত্মার সদগতির উদ্দেশ্যে?
আমার দাদু পিন্ডির দক্ষিনা ফেরত না-চাইলেও বাবার জন্য ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসেই কৃঞ্চনগর জেলার চন্দননগরের এক প্রতিষ্টিত হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন| কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ্ব বাবার ধমনীতে তখন সদ্য-স্বাধীনতার রক্ত| বাবা নাকি আমার দাদুকে উল্টো প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আপনিই বরং ফিরে চলুন| ৬৫-তে দাংগার সময়ে ফেলে আসা পুরানো ঢাকার বনেদী পগজ হাইস্কুলের সেকেন্ড মাষ্টারের চাকুরীটাই আপনাকে ফেরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা যাবেখন?
“ঔদ্ধ্যত ব্যবহারই বটে ছোকড়ার|” স্বাধীনতার প্রায় তিন দশক পরে বুড়োর সাথে দেখা হলে তিনি কলকাতার বাড়িতে বসে আমাকে একথা বলেছিলেন| আমি অনেকবারের মতো এবারও বাবার দেশ প্রেমের চেতনায় গর্বিত হয়ে হেসেছিলাম| যদিও তখন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কিয়দংশমাত্র অবশিষ্ট ছিল|
সেবার বাবা কলকাতা থেকে অনেক কিছু এনেছিলেন বাড়ির সবার জন্য| আমার জন্য ছোট্ট এক জোড়া পিওর লেদারের জুতো| যুদ্ধ চলাকালীন ৯ মাস না- দেখা আমি যে আর ছোটটি নেই, মুক্তিযোদ্ধা বাবা সেকথা বেমালুম ভুলে ছিলেন| তাই ছোট পিওর লেদারের জুতো জোড়া আমার আর পড়া হয়নি কোনদিন| প্রথম পাওয়া বিদেশী জিনিস না -সওয়ার সে আক্ষেপ এখনও আমার আছে|
একেবারেই শিশুর মাপে বানানো সুন্দর জুতো জোড়া আমি সযত্নে রেখেছি অনেকদিন| বাবার ব্রাশ নিয়ে বাবার মতো করে পালিশ করে ঝকঝকে তকতকে করে জুতোর তাকে তুলে রেখেছি বহুদিন| জুতো জোড়া যেন তখন আমার কাছে না-দেখা কলকাতার প্রতিচ্ছবি| শিশু বয়সে শোনা মুক্তিযুদ্ধের অসংখ্য রোমাঞ্চকর কাহিনির মতোই ওই জুতো জোড়াও তখন আমার এক শিহরিত সম্পদ| বাবা যখন বলতেন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন একটি দেশের কথা, আমি তখন ভাবতাম আমার জীবনের প্রথম পাওয়া সে জুতো জোড়ার কথা| যদিও অর্জণ আর পাওয়ার মধ্যে
যে পার্থক্যটি আছে তা আমি তখনও বুঝিনি| দীর্ঘদিন পরে এসেও যে সঠিক বুঝেছি সেটাও বলা যাবে না|
কাকতালীয় ভাবেই ৭৫-এর পরে বাবার কেনা সে ছোট্ট জুতো জোড়া আমি আর খুঁজে পাইনি| না, কোথাও না! বাড়ির আনাচে কানাচে, উঠোনের খানাখন্দে, এমনকি মায়ের গয়নার বাক্সেও| কোথাও পাওয়া যায়নি এক মুক্তিযোদ্ধার কেনা ছোট্ট এক জোড়া জুতো, যার বেঠিক সাইজের জন্য তার শিশুসন্তানটির কোন মন খারাপ ছিল না সেদিন| অথচ অব্যবহ্রত সে জুতো জোড়া হারিয়ে যাওয়ার পর তার শোকেই যত রাজ্যের হাহাকার!
(২)
বাবা কলকাতায় গেলেন স্বাধীনতার কয়েক মাস পরে| তখন সবে মাত্র ভারতীয় কংগ্রেস মার্চ মাসের নির্বাচনে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে| জাতীয় কংগ্রেসনেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বস্ত এবং কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে| পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় যে পশ্চিমবংগের রাজনীতিতে তেমন সিদ্ধ হস্ত সেটা নয়| কিন্তু ভারতীয় কংগ্রেস বিশেষ করে ইন্দিরা গান্ধী চাইছিলেন, তাঁর আস্থাভাজন কেউ রাজ্যের সংকট মোকাবেলা করুক| রাজনৈতিক সমাধানের চেয়ে প্রশাসনিক সমাধানের দিকেই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জোর দিচ্ছিলেন বেশী| বিশেষত নকশাল আন্দোলন দমনের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই|
যদিও তখন জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি পশ্চিমবংগের বাঙালী বিশেষত দেশবিভাগের ফলে পূর্ব্বংগের উদ্বাস্তু বাঙালীদের মোহভংগ ঘটে গেছে| কিন্তু পাকিস্তানকে ভেংগে দু’টুকরো করে দিতে সহায়তা এবং দু’কোটি শরনার্থীদের সমস্যার সমাধানের আশায় আবারও কংগ্রেসকে ভোট দিলেন তারা| ফলে যে বামপন্থী কম্যুনিষ্ট বিশেষত সিপিআই এবং সিপিআইএম আস্তে আস্তে উদ্বাস্তু-অধ্যুষিত শহর ও শহরতলীতে নিজেদের শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলছিল, সেখানেও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জয়যুক্ত হলো সে বারের নির্বাচনে|
অথচ ৪৭’এর দেশবিভাগের ফলে পূর্ববংগ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য থাকাই স্বাভাবিক ছিল| এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ৬০ দশকের শেষ অব্ধি সে আনুগত্য অটুটও ছিল যথারীতি| কিন্তু ৫০ থেকে ৬০ দশকে ক্রমান্বয়ে পূর্ববংগ থেকে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলো| এ উদ্বাস্তুদের একশো শতাংশ আবার হিন্দু| পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দাংগা এবং বাঙালীদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের চরম বৈষম্য উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বাড়িয়েই দিল দিনের পর দিন| ফলে পূর্ববংগে কংগ্রেসকে সমর্থন করলেও পশ্চিমবংগে উদ্বাস্তু হয়ে এসে অনেকেই দেখলেন কংগ্রেসের আচরণ তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়| এ সুযোগই খুঁজছিল একদার অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং পরবর্তীতে সিপিআইএম এবং প্রধানতঃ সিপিআই|
মূলতঃ কংগ্রেসের প্রতি মোহভংগ থেকে উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে গঠিত হলো ইউনাইটেড কাউন্সিল অব রিফিউজি কলোনিজ বা ইউ সি আর সি| ইউ সি আর সি-এর সাথে সংযুক্তদের অনেকেই পূর্ববংগ থেকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত এবং রাজনৈতিক ভাবেও সচতন| অথচ উদ্বাস্তু হওয়ার ফলে তাদেরকে শ্রমিকশ্রেনীর মতো মানবেতর পেশা ও জীবন যাপন করতে হচ্ছে| ফলে এতদিন শ্রমিক শ্রেনীর মধ্যে শক্ত অবস্থান গড়তে ব্যর্থ কম্যুনিষ্টরা উদ্বাস্তুদের মধ্যে সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে শুরু করে দিল| ফলে ৬৭’র নির্বাচনে কংগ্রেস এ উদ্বাস্তু কলোনিগুলোতে ভাল ফলাফল করতে পারল না| অজয় মুখার্জীর নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্টদের যুক্তফ্রন্ট স্বল্প সংখ্যক মেজরিটি নিয়ে সরকার গঠন করল| কিন্তু ৭২-এর নির্বাচনে ঘটল তার বিপরীত| আবার জাতীয় কংগ্রেস ক্ষমতায় এল মূলতঃ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে সদ্য জন্ম নেয়া বাংলাদেশকে সহায়তা দান, দু’কোটি শরনার্থী সমস্যার সমাধান এবং নকশাল আন্দোলনের প্রতি জনবিমুখতার কারণেই| যদিও সাংগঠনিকভাবে পশ্চিমবংগে জাতীয় কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্যের সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে|
সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ তো বটেই, পশ্চিমবংগের অবস্থাও তখন খুব সংগীন| এ অবস্থাতেই উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে বাবা কলকাতা এলেন| প্রথমে এসে উঠলেন কলকাতার উপকন্ঠ দমদম বারাসাত এলাকার একটু ভদ্রোচিত উদ্বাস্তু কলোনিতে| বাবার বাল্যবন্ধু অমল মন্ডল আগে থেকেই বাস করছিলেন সেখানে| পূর্ব পাকিস্তান থেকে ইতিহাসে মাষ্টার্স পাশ অমল কাকু ৬০-এর দশকের প্রথম দিকে ভাগ্যের সুপ্রসন্নতায় একটি কেরাণীর চাকুরী জুটিয়ে নিয়েছিলেন| দমদমের একটা উদ্বাস্তু কলোনির ঘরে বাস করছিলেন একা একা বেশ স্বচ্ছলভাবেই| সেই সাথে যুক্ত হয়েছিলেন সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিকভাবেও কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের সাথে|
কিন্তু অমল কাকুর সবকিছু এলোমেলো করে দিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ| উদ্বাস্তু কলোনির এক কামরার ঘরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে শরনার্থী হয়ে উঠে পড়লো মাসহ দুই ভাই ও তাদের পরিবার|
বাবা যখন তাঁর বাল্যবন্ধু অমলের বাসায় ৭২-এর এপ্রিল মাসে বেড়াতে এলেন, তখনও অমল কাকুর দুই ভাই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেননি| যদিও বাংলাদেশের বয়স তখন ছয় মাস পেরিয়ে গেছে| ফেলে আসা ঘরবাড়ি-জমাজমি-ব্যবসাবানিজ্য ফিরে পাবার এক অজানা আশঙ্কায় অনেক শরনার্থী্র মতো তারা তখনও রয়ে গেছেন পশ্চিমবংগে| যুদ্ধবিধ্বস্ত ভুখন্ডে যোগাযোগের অব্যবস্থা তো ছিলই, সেই সাথে ছিল সম্বন্বয়হীন প্রশাসনিক উদ্যোগ| সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ছিল না শরনার্থীদের ফিরিয়ে এনে পূনর্বাসণের যথোপযুক্ত পরিকল্পনা ও ইচ্ছে| ফলে শরনার্থীদের অনেকেই নিজ উদ্যোগে ফিরে এসে প্রশাসনিক তেমন কোন সাহায্য সহায়তা পায়নি | অনেকেই ফিরে পায়নি যুদ্ধের সময় ফেলে যাওয়া সম্পদ-সম্পত্তিটুকুও| স্থানীয় রাজনৈতিক টাউটদের খপ্পরে পড়ে অনেকেই আবার আংশিক সম্পত্তি ফিরে পেয়েছেন; বাকী অর্ধেক চলে গেছে হঠাত গজিয়ে ওঠা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে|
যুদ্ধের নয় মাসের অধিকাংশ সময়েই অনেকে নিশ্চুপ ছিল| অনেকে আবার ভারতে পালিয়ে যাওয়া হিন্দুদের বাড়িঘর ও জমিজমা নিজেদের দখলে রেখেছিল এ ভরসায় যে তারা আর কখনো ফিরে আসবে না এদেশে| বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে আবার হিন্দু বাড়ি দখল করে প্রথমেই একটি মসজিদ প্রতিষ্টা করা হয়েছিল| যদিও মানিকগঞ্জে তেমনটি করা সম্ভব ছিল না| কারণ, ঢাকার উপকন্ঠে অবস্থানের জন্য মুক্তি ও মিত্রবাহিনীর কাছে স্ট্যাটেজিক ভাবেই এ অঞ্চলটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ| তাছাড়া নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই পাকিস্তানী বাহিনী এবং তাদের দোসর রাজাকারদের তেমন আনাগোনা দেখা যায়নি| এর ফলে দু’একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া হিন্দুদের বাড়িঘর-ব্যবসাবানিজ্য অক্ষতই ছিল এ এলাকাতে|
এ রকম নানামুখী সংবাদে বিভ্রান্ত হয়ে অমল কাকুর ভাইয়েরা বাংলাদেশে ফিরে আসতে ভরসা পাচ্ছিলেন না তখনও| বাবার কাছে বিস্তারিত শুনে দু’দিন পরেই দুই ভাইকে পরিবারসহ বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিলেন অমল কাকু| অনেকদিন পরে যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা গেল|
কলকাতা তখন এক ভয়ের শহর| সদ্য ক্ষমতায় বসা জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক নেতা ও কর্মীরা প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শণ করে নকশাল খতমে নেমেছে| অলিতে গলিতে পড়ে থাকছে লাশ| শ্রেনীশত্রু খতমের রাজনীতিওয়ালাদের থেতলানো লাশের ওপর দিয়ে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে ইন্দিরা কংগ্রেসের গনতন্ত্র পূনরুদ্ধারের অভিযান তখন চলছে পুরোদমে| এক সময়ের উদ্বাস্তু আক্রান্ত কলকাতা তখন এক লাশের শহর| অমল কাকু শরনার্থী ভাইদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়ে ছোটবেলার বন্ধুকে নিয়ে ত্রাসের শহর কলকাতা ঘুরে দেখাতে বের হলেন সেদিনই|
(৩)
বনগাঁ থেকে শিয়ালদাগামী ট্রেনগুলোর কামরা এক রকম ফাঁকাই থাকে| অথচ শিয়ালদা থেকে বনগাঁর ট্রেনগুলো বাংলাদেশ থেকে আগত শরনার্থীতে ঠাসা| ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আত্মসমর্থণ করেছে| অথচ এখন এপ্রিলের প্রায় শেষ| এখনো শরনার্থীদের বাংলাদেশে ফিরে যাবার ঢল?
অমল কাকু ও বাবা বারাসাত থেকে প্রায় ফাঁকা কামরার একটা ট্রেনে চড়ে বসলেন| টিকেট কাটার ঝামেলা তেমন নেই| কারণ, শরনার্থীদের বিনেপয়সায় চলাচল করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যুদ্ধের প্রায় পুরো সময়টাতেই পশ্চিমবংগের রাজ্যপাল শাসিত সরকার| তাই বিনে পয়সার ট্রেন ভ্রমনের সময় সিগারেটে হালকা করে সুখটান দিলেন দুইবন্ধু| পা ছড়িয়ে দখল করে বসলেন একদিকের আসনগুলো| ততক্ষণে বারাসাত ছেড়ে পরের স্ট্রেশনের ট্রেন থেমেছে| উল্টো দিকের প্লাটফরমে উপচে পড়া মানুষের ভিড় দেখে সহসা অমল কাকু বলে উঠলেন, এ কয়দিন তো ব্যস্ততার কারণে তোকে দেশের কথা জিজ্ঞেস করাই হয়নি| মুক্তিযুদ্ধের কথা, কে কে বেঁচে আছে, কে মরে গেছে, কিছুই তো শোনা হলো না| যদিও অনেক কিছু কানে এসেছে, কিন্তু কতটুকু সত্যি কে জানে? এই ধর না তোর কথাই| একদিন তোর এক আত্মীয়ের সাথে কলকাতায় দেখা| সে তো বলল, তুই নাকি মরে গেছিস?
বাবা তখন প্ল্যাটফর্মের ওপার থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে বললেন, হ্যা আমি তো সেটা শুনেই দেখা করতে এলাম| আর যুদ্ধের কথা কি আর চলতি পথে বলা যাবে? আছি তো বেশ কিছুদিন, আস্তে আস্তে শোনাবো| আর এ দু’দিন তোর কাছে বেশ কিছু লোকের আনাগোনা দেখলাম| উদ্বাস্তুদের নিয়ে কিছু পোস্টার আর বইও দেখলাম|
হা তুই ঠিকই ধরেছিস| এখানে ইউনাইটেড কাউন্সিল অব রিফিউজি কলোনিজ বা ইউ সি আর সি নামে একটা সংগঠনের সাথে জড়িয়ে গেছি, অমল কাকু বললেন| দেখ না, বজ্জাত কংগ্রেস পূর্ববংগের উদ্বাস্তুদের সাথে কী আচরণ করছে সেই নেহেরুর সময় থেকেই| আসলে তো জানিস, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা ওরা তো আর্য| আর পূর্ববংগের আমরা কোথাকার কোন চাষাভূসা অনার্য দ্রাবিড়| আর বেটা নেহেরু তো ওদিকেরই লোক|
অমল কাকু ব্যাগ থেকে ইউ সি আর সি-র বই বের করে পাতার পর পাতা উল্টে একটি বড় চার্ট মেলে ধরলেন| বললেন, এই দেখ| পশ্চিম আর পূর্ব্বংগের উদ্বাস্তুদের পূনর্বাসণের খতিয়ান| সংখ্যার হিসেবে পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুরা বেশি হলে কি হবে, পূনর্বাসনের দিক থেকে শতকরা দশ ভাগও এদিকে খরচ হয়নি| তারপর আবার এই পাকিস্তানযুদ্ধের শরনার্থী?
বাবার কাছে এ পরিসংখ্যানের প্রায় সবকিছুই অপরিচিত লাগলো| নিজের কাছে একটু বেক্ষ্যাপ্পাই মনে হলো অমলকে| তাছাড়া জহরলাল নেহেরু কিংবা কংগ্রেসের সম্বন্ধে এ সমস্ত নেতিবাচক কথার কোন মানে আছে বলেও মনে হলো না বাবার| নেহেরু-কন্যা ইন্দিরার সাহায্য ছাড়া কি বাংলাদেশ এতো সহজে স্বাধীন হতো? কোটি কোটি শরনার্থীদের ভরণপোষন ইন্দিরা গান্ধী আর কংগ্রেসের সাহায্য ছাড়া কি সম্ভব ছিল?
অমল কাকু বললেন, এই মাত্র তো দমদম ক্যান্টনমেন্ট ছাড়ালাম| এখন দুইদিকে দেখবি উদ্বাস্তুদের বস্তি| দেশভাগ হয়ে গেছে সেও আজ পঁচিশ বছর, অথচ কলকাতার যত কাছাকাছি যাবি পূর্ববংগের বাংগালদের বস্তির সংখ্যাও তত বাড়বে| শিয়ালদা তো আরেক পূর্বপাকিস্তান| প্রথমে দেখলে কেউ কেউ ভাববে কলকাতাটাই শালা বাংগাল বাটিদের দখলে চলে গেছে| হারামি ঘটিরা সব হিন্দিঘেঁষা বিছুদ্ধ কথা কয়| ছিয়ালদাতে দাদাদের টিকিটা দেখতে পাবি না|
অমলের কথায় বিদ্রুপ আর শ্লেষ, অথচ দেখ এই হারামি নকশালরা সমাজতন্ত্র মারাচ্ছে জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে হারামি জোতদারদের মেরে| এত পারিস কলকাতা এসে দে শালা এই বড় বড় বিল্ডিং ভেংগে, দখল করে নে হারামি সুদখোর মাড়োয়ারীদের ব্যবসা| দেখবি পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসা কোটিখানিক বাংগাল গামছা খুলে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে নেমে পড়বে|
বাবা লক্ষ্য করলেন অমল শেষের কথাগুলো একটু নিঁচু গলায় বললেন| তারপর চারদিকে তাকিয়ে বাবার কানের কাছে ফিস ফিস গলায় বললেন, নকশালের খতমবাজগুলো নাকি কলকাতাতেও সিঁধিয়ে গেছে? দেখি শালারা রাইটার্স ওড়াতে পারে কিনা?
বাবা একটু ভড়কিয়ে গেলেন অমল কাকুর কথা শুনে| ইস্কুল জীবন থেকেই তো সমাজতন্ত্রের রাজনীতি করতো অমল| ৬০-এর দশকে ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সাথেই যুক্ত থেকেছে| অমলের কাছ থেকেই বাবার প্রথম হাতেখঁড়ি বামপন্থি রাজনীতিতে| তারপর ইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করার পরেও গোপনে কম্যুনিষ্ট পার্টির সাথেই যুক্ত ছিলেন| নকশাল আন্দোলন যখন পশ্চিমবংগের উত্তরের জেলাগুলোতে ছড়িয়ে গেল, বাবা তাঁর বামপন্থী বন্ধুদের সাথে সমান খুশী হয়েছিলেন| যদিও পশ্চিমবংগের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্বের কথা শোনা যাচ্ছিল, তবু বাবা ভেবেছিলেন অমল হয়তো নকশাল আন্দোলনকেই সমর্থণ করছে| বন্ধু অমলের কথাতে বেশ হতাশ হলেন বাবা|
অমল হঠাত নিজে থেকে সাবধান হয়ে বললেন, চারদিকে কিন্তু খতমবাজদের খতম চলছে| কথা বার্তায় একটু সাবধান! আর পুলিশে ধরলে সোজা ঢাকাইয়া ভানু মাইরা দিবি| কাদার মধ্যে পা হান্দাইয়া দিবি.. যাচ্ছি খাচ্ছি বলে বিছুদ্ধ বাংলা কওনের কোন দরকার নাই, বুঝলি| তা’ইলে পুলিশ ভাববো, তুই শালা শরনার্থী, নকশাল না!
প্রায় শূন্যকামরা অট্টহাসিতে ভরিয়ে তুললেন দুই বন্ধু| অনেকক্ষণ পরে বাইরে তাকিয়ে দেখলেন ট্রেন ততক্ষণে উল্টোডাংগা ছাড়িয়ে কলকাতার মধ্যে ঢুকে পড়েছে| অমল কাকু বললেন, আর একটু পরেই আমরা শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে যাব|
(চলবে)
http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=36770
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ১৮:২৮582584
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ১৮:২৮582584- চন্দ্রমুখী জানালা-পর্ব দুই
লিখেছেন: ভজন সরকার
____________________________
(৪)
আষাঢ় মাস পর্যন্ত বেশ একটু স্বস্তিতেই কাটানো গেল| ঢাকাতে যুদ্ধ শুরু হলো চৈত্রমাসের মাঝামাঝি| প্রথম দিকের মাসখানিক তো যুদ্ধের খবর গ্রামে আসতে আসতেই সময় কেটে গেছে| যদিও মুসলিম লিগের চেয়ারম্যান শওকত আলী্র নেতৃত্বে আশপাশের কয়েক গ্রামে পাকিস্তানরক্ষা কমিটি আর আলবদর গঠিত হয়েছে| যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে করণীয় ঠিক করতে করতেই বোশেখ মাসের শেষ| মাঝে মধ্যে শুধু শওকত চেয়ারম্যান হিন্দু পাড়ায় লোক পাঠিয়ে খবর নেয় মুক্তিবাহিনী গঠিত হচ্ছে কিনা?
পুরো এলাকা জুড়েই চাষাবাদের জমি| মাঝে মধ্যে কিছু জমিতে আমন কিংবা আউশ ধান; বাকী সব জমিতে পাটের চাষ| জৈষ্ঠ্য মাস শুরু হতেই পাট বড় হতে থাকে| ঘন বিস্তৃত পাট ক্ষেত এক গ্রামকে অন্য গ্রাম থেকে আলাদা করে রাখে| গ্রামের রাস্তা থেকে পাট ক্ষেতের ভিতর ঢুকে পড়লে কারও পক্ষে সম্ভব নয় খুঁজে বের করা| তাই মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা পাটের ভিতর দিয়ে অনায়াসে দিন দুপুরেই এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে চলে যায়| পাট ক্ষেতের ভিতর বসেই অনেকে শলা পরামর্শ করে| কখনো কখনো রেডিও শোনে|
মানিকগঞ্জ মহুকুমা শহর| যোগাযোগ শুধু নৌকা আর পায়ে হাঁটার পথ| পার্শ্ববর্তী থানা দু’টোও এলাকা থেকে বেশ দূরে| তাই অনায়াসেই পাকিস্তানী মিলিটারী আসার খবর জানা যায়| তাছাড়া মুক্তিবাহিনী ইতিমধ্যেই সন্দেহভাজন মুসলিম লিগারদের পেছনে টিকটিকি লাগিয়ে রেখেছে|
শওকত চেয়ারম্যানই একমাত্র লোক যে মহুকুমা সদর থেকে পাকিস্তানী মিলিটারিদের ডেকে আনতে পারে, এ আশঙ্কা থেকেই একদিন বাড়িতে মিটিং হলো| শওকত চেয়ারম্যানকে ভয় দেখাতে হবে; যাতে করে পাকিস্তানী মিলিটারি আনার সাহস না পায়| মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত হলো যে করেই হোক উলাইল ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসে দিনে দুপুরে একটি পটকা ফোঁটানো হবে| এতে এক ঢিলে দুই পাখি মরবে| শওকত চেয়ারম্যান যেমন ভয় পাবে, ইদানিং সৃষ্টি হওয়া রাজাকারেরাও একটু দমে থাকবে|
উলাইল বোর্ড অফিসটি দৌলতপুর থানা সদর থেকে পাঁচ মাইল দূরে, একেবারে থানা সংযোগ সড়কের পাশে অবস্থিত| তিন দিকে সড়ক আর সামনের দিকে ফাঁকা মাঠ| বোর্ড অফিসের দক্ষিন দিকের প্রায় এক মাইল দূরের গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত সে ফাঁকা মাঠে আবাদি জমি| জৈষ্ঠ্য মাসের আধাআধি সময় পেরিয়ে গেছে| পাট গাছ বড় হয়ে প্রায় দেড়-দু’ মানুষ সমান লম্বা| তাই পাট ক্ষেতের ভিতর দিয়েই অপারেশন করতে হবে মিটিংয়ে সে রকমই সিদ্দ্বান্ত|
সেদিন বুধবার| চেয়ারম্যান তখন অফিসে| সাপ্তাহিক মিটিং বসেছে ইউনিয়ন বোর্ডে| মেম্বার আর মুসলিম লিগের চ্যালা চামুন্ডারা শওকত চেয়ারম্যানের চারপাশে বসে আছে| হঠাত বিকট শব্দে একটা পটকা ফুঁটলো| কিছুক্ষণ পর পর আরো কয়েকটি| মিটিং রুমের সামনে টুলের উপর বসে ছিল আনিচ চৌকিদার| লাঠি হাতে এদিক-ওদিক দৌঁড়োদুঁড়ি শুরু করে দিল আনিচ| শওকত চেয়ারম্যান সম্ভাব্য বিপদ আঁচ করে ক্ষিতিশ মেম্বারকে বাইরে পাঠিয়ে ঘরের খিল আটকিয়ে দিল| ততক্ষণে মুখে গামছা জড়িয়ে কয়েক জন ছেলে সামনের পাটের ক্ষেতে নেমে গেছে| উঁচু সড়ক থেকে দেখা যাচ্ছে পাট গাছ ভেঙ্গে ভেঙ্গে ওরা দূরে চলে যাচ্ছে| আনিচ চৌকিদার লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে জোরে হাঁক দিচ্ছে, শালার মুক্তিবাহিনী, শালা মালাউনের বাচ্চা|
সন্ধ্যে বেলায় শওকত চেয়ারম্যান এলাকার কয়েকজনকে নিয়ে গ্রামে এলেন| বাড়ির উঠোনে কাঠের চেয়ার, বেঞ্চি আর চটের বস্তা পেতে সবাই বসেছে| চেয়ারম্যানের গলার সুর নরম| দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, ভয় পেয়েছেন| মিটিংয়ে সবাইকে তিনি আশ্বস্ত করলেন, এ এলাকায় পাকিস্তানী মিলিটারি আসবে না| কিন্তু মুক্তিবাহিনীকেও কথা দিতে হবে আর বোমাবাজি না করার|
সদ্য গঠিত মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার কমরেড হাকিম উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন| তিনি সম্মতি দিলেন| বললেন, শওকত ভাই, এ এলাকাটাতো আমাদের তাই না| আমরা খামোখা কেন বোমাবাজি করতে যাবো? কিন্তু আপনাকেও কথা দিতে হবে আশপাশের হিন্দু গ্রামগুলোতে যেন কোন অত্যাচার না হয়|
পাশ থেকে বাবা বললেন, ওপাশের পাড়া থেকে কালু নাকি রাত বিরেতে হিন্দুপাড়ায় এসে পাকিস্তানী মিলিটারির ভয় দেখায়| কাল রাতেই নাকি দিনেশকে ইন্ডিয়ায় পাঠিয়ে দেয়ারও হুমকি দিয়েছে|
কমরেড হাকিম উদ্দিন বললেন, ওকে আজ থেকে সাবধান করে দেবেন শওকত ভাই| শেখ সা’বের ডাকে আমরা যুদ্ধ করছি| খালি হিন্দুরাই কি পাকিস্তানীদের তাড়াতে চায়? মুসলমানরা চায় না? আপনি চান না?
ব’লেই তিনি শওকত চেয়ারম্যানের দিকে তাকালেন| কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে আছেন চেয়ারম্যান|
কমান্ডার হাকিম উদ্দিন আবার বলা শুরু করলেন, হিন্দুদের দোষটা কোথায়? কালুর সাহস থাকে তো ওকে কলিয়ার মুসলিম পাড়ায় পাঠাবেন| ও যদি আর হিন্দুদের ভয়-ভীতি দেখায় সে দায়িত্ব কিন্তু আপনাকে নিতে হবে| এলাকায় এটা আর চলবে না| আপনি আজই কালুকে ডেকে সাবধান করে দেবেন|
কথাটি শওকত চেয়ারম্যানের ভাল লেগেছে বলে মনে হলো না| কিন্তু ভয় আর শঙ্কায় কিছু না বলেই মিটিং শেষ করলেন সে রাতের মতো|
সেদিনের মিটিংয়ের পর থেকে হিন্দু গ্রামগুলোতে মুসলিম লিগের লোকজনের আনাগোনা কমে গেল| কিন্তু সবার মধ্যে একটা চাপা ভয় ও আশঙ্কা তো থেকেই গেল| গ্রামে কিংবা বাড়িতে থাকলে একটু স্বস্তিতে থাকা যায়| কেউ হাট-বাজারে গেলে বাড়িতে না-ফেরা পর্যন্ত সবাই আতঙ্কে থাকে| কখন কাকে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে!
এ ভাবেই আষাঢ় মাস এসে গেল| চারিদিকে আউশ আর জলি ধান কাটার ধুম| সেবার নতুন জল একটু তাড়াতাড়িই চলে এলো| মাত্র দিন দুয়েকের ব্যবধানেই গ্রামগুলো যেন এক একটা দ্বীপ| মাত্র সপ্তাহ দু’য়েক আগেই মাঠ ভরা ছিল পাটে| এখন আর কোথাও পাট গাছ নেই| বড় বড় আঁটি বেধে পাট পচানোর কাজ চলছে| নতুন আসা বর্ষার জলে বড় বড় বাঁশের সাথে পাটের আঁটিগুলো আটকিয়ে কচুরিপানা কিংবা কলাগাছ দিয়ে পাট ডুবিয়ে রাখা হয়েছে জলের নিচে| মাসখানেক পরেই বাঁশের মাচা বানিয়ে জলের ওপরেই পাটের আঁশ ছাড়ানো হবে| তারপর আঁশ ও পাটখড়ি দু’টোই বাড়িতে কিংবা উঁচু সড়কে এনে রোদে শুকানো হবে| উঁচু সড়কের দুপাশ দিয়ে মাইলের পর মাইল বাঁশ টাংগিয়ে পাট খড়ি শুকানোর এক মনমুগ্ধকর দৃশ্য| সড়কের মাঝ দিয়ে শুধু সরু পায়ে চলার পথ|
বর্ষার জল আর্থিক স্বচ্ছলতা নিয়ে এলেও আরেক বিপদ নিয়ে এলো| নৌকা করে সহজেই গ্রামগুলোতে যাতায়াত করা যায়| লুকানোর জায়গাও আর থাকলো না বললেই চলে| হঠাত করে এক বিকেলে পাশের গ্রামে বাবার বন্ধু অমল কাকুদের বাড়িতে বিরাট এক ঘাসি নৌকা করে কিছু রাজাকার এসে লুটপাট করে চলে গেল| অমল কাকু তো আগেই ইন্ডিয়া চলে গেছেন| বাড়িতে দুই ভাই তখন থানা সদরের কাপড়ের দোকানে| বউ ছেলেমেয়ে আর মা বাড়িতে শুধু| পেছনের নিমাই বিল দিয়ে এক বড় ঘাসি নৌকা করে জনা দশেক লোক এসে বাড়ির সোনা-দানা-ধান-চাল নিয়ে ভেগে গেছে| যাওয়ার সময় নাকি শাসিয়ে গেছে এ কথা মুক্তিবাহিনীকে বললে থানা সদরের দোকান থেকে দুই ভাইকে পাকিস্তানী মিলিটারির কাছে ধরিয়ে দেবে|
সবাই তো থ| এলাকায় এ রকম একটা ঘটনার আঁচ আগে থেকে কেউ করেনি| বর্ষার জন্য মুক্তিবাহিনীর অনেক ছেলেরা একটু উঁচু এলাকায় চলে গেছে| অনেকেই ট্রেনিংয়ের জন্য বর্ডার পাড়ি দিয়ে চলে গেছে ভারতে| বাবাসহ যারা তখনও এলাকায় তারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই এ ঘটনা ঘটে গেল| এলাকার মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার হাকিম উদ্দিনও তখন এলাকা ছেড়ে ভারতে| মানিকগঞ্জ সদরে হালিম ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে একটা গ্রুপ যুদ্ধ করছে| পাশের থানা ঘিওরেও কমাণ্ডার মনসুরসহ আরো কয়েকটি গ্রুপ সক্রিয়| টাঙ্গাইলে কাদেরিয়া বাহিনীর কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়| কিন্তু কেউ চারিদিকের থই থই জল পেরিয়ে এ বিল এলাকায় অপারেশনে আসছে না| তাছাড়া পাকিস্তানি মিলিটারিরা যে জলে ভয় পায় তখন সবাই এ সংবাদ জেনে গেছে| তাই বড় কোন অপারেশনের ঝুঁকি এ সমস্ত এলাকায় নেই জেনে মুক্তিবাহিনীর টার্গেট তখন থানা আর মহুকুমা শহর|
শওকত চেয়ারম্যানের প্রতিশ্রুতি আর কাজে আসবে না ভেবে আশপাশের হিন্দু গ্রামগুলোতে উতকন্ঠা| আর সে সুযোগেই কালু রাজাকারের বাড়বাড়ন্ত| দু’দিন পরেই পাশের আরেকটা হিন্দু বাড়ি লুট| অথচ মাস খানিক আগেই এলাকা ছিল একেবারে নিরাপদ| এখন মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামঘেঁষা পাড়াগুলো্তে রাত নামার আগেই এক অজানা আতঙ্ক নেমে আসে| অনেকে আবার যুবতী মেয়েদের আরো একটু ভিতরে হিন্দু এলাকার কোন আত্মীয় বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছে| কিছুদিন পরেই শোনা গেল রাতের অন্ধকারে কয়েকটি পরিবার পালিয়ে ভারতে চলে গেছে| গুজব এমন সংক্রামক যে,তিলকে তাল করে ফেলে| সহসাই পাশাপাশি তিন-চারটে হিন্দু গ্রামে এক ভয়ের রাজত্ব চেপে বসলো|
অনেকদিন পরে বাড়িতে গোপন মিটিং| যে করেই হোক এর একটা সমাধান করতে হবে| সিদ্ধান্ত হলো এখনই কোন অপারেশনে যাওয়া যাবে না| শওকত চেয়ারম্যানের মাধ্যমেই সবাইকে আবারও আশ্বস্ত করতে হবে| ভারতে পালিয়ে যাওয়ার যে হিরিক পড়ে গেছে সেটা আগে বন্ধ করতে হবে| তারপর না হয় সু্যোগ বুঝে নতুন করে অপারেশন!
(৫)
আষাঢ় মাসেই আরও কয়েকটা হত্যাযজ্ঞ ঘটালো পাকিস্তানী মিলিটারি| ততদিনে মহুকুমা সদর থেকে থানা পর্যায়ে পাকিস্তানী মিলিটারি চলে এসেছে| সে সুযোগে স্থানীয় চেয়ারম্যান মেম্বারেরা ইউনিয়নে ইউনিয়নে শান্তি ও পাকিস্তান রক্ষার নামে পিস কমিটি গঠন করছে| শান্তি রক্ষা তো নাম মাত্র| পিস কমিটির সদস্যদের প্রধান কাজই হলো পাকিস্তানী মিলিটারির নামে হিন্দু এলাকায় ভয়ভীতি দেখিয়ে জমি-বাড়ি, টাকা-পয়সা লুটপাট করা|
ঘিওর থানা সদরের রথযাত্রা উতসব মানিকগঞ্জ মহুকুমায় খুব বিখ্যাত| ধামরাইয়ের পরেই ঘিওরের রথযাত্রা| এলাকায় প্রচলিত আছে যে, বালিয়াটির জমিদার ঢাকা জেলার সব এলাকা থেকে শতাধিক কাঠমিস্ত্রী ডেকে এনে এক বছরেরও অধিক সময় ধরে ধামরাইয়ের রথ তৈরী করান| ৬০ ফুট উঁচু, ৪৫ ফুট চওড়া তিন তলা বিশিষ্ট বিশাল এ রথে ৩২ টি বিশাল বিশাল কাঠের চাকা| দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার চতুর্কোণে সুসজ্জিত কামরা বা নবরত্ন| রথের সামনে ও চারপাশে কাঠে খুদাই করা হিন্দু দেব-দেবীর চিত্র| ধামরাইয়ের প্রায় সব রাস্তায় তখন এ রথ টানা হতো| আর ভক্তরা রাস্তার দুই দিকে দাঁড়িয়ে উলুধ্বনির সাথে সাথে বাতাসা-কলা-চাল ছিটিয়ে দিত|
ধামরাইয়ের রথ আগে ছিল বাঁশের তৈ্রী| কাঠের এই নতুন রথ উদ্বোধনের সময় বালিয়াটির জমিদার বাহাদূর এলাকার ব্রাহ্মণ ও আশপাশের জমিদারদের নিমন্ত্রণ করলেন| নিমন্ত্রণের ত্রুটির জন্য তেরশ্রীর জমিদার কালী নারায়ণ রায় চৌধুরী ক্ষুব্ধ হয়ে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করলেন| পরের বছরই তেরশ্রীর কাছে ঘিওরের থানা সদরে আরেকটি জগন্নাথের রথ তৈ্রী করালেন| সীমিত অর্থের জন্য তিনি ধামরাইয়ের রথকে অতিক্রম করতে তো পারলেনই না; এমনকি ঘিওরের রথ উচ্চতা ও আয়তনে ধামরাইয়ের সমানও হলো না | কিন্তু তিনি ধামরাই রথ যাত্রার দিনেই ঘিওরের রথের চাকাও টানাতেন, যেন তার প্রজারা ধামরাই রথ দর্শণে না যেতে পারে|
সে বার রথ যাত্রার দিন সন্ধ্যাবেলায় পাকিস্তানী মিলিটারি ঘিওর বাজারের হিন্দুদের দোকান-পাটে হামলা করল| সাহা পট্টি পুড়িয়ে দিল| দূরদূরান্ত থেকে রথ যাত্রায় আগত পূন্যার্থীরা কোন রকমে পালিয়ে বাঁচল| কিন্তু পরের দিন ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে পাকিস্তানী মিলিটারি ও রাজাকারদের নৃশংসতার খবর জেনে সবাই শিহরিত| ঘিওরের সাহা পট্রিতে আগুন দিয়ে ফেরার পথে রাজাকার-আলবদরের লোকেরা নিতাই সাহাসহ আরও কয়েকজনকে ধরে পাকিস্তানী মিলিটারির হাতে তুলে দেয়| পরে থানার সামনে খালপাড়ে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দশজনকে হত্যা কর|
ঘিওর থানা সদর থেকে বিশ-পঁচিশটি পরিবার আশ্রয় নিল আমাদের বিল এলাকার গ্রামগুলোতে| সবাই তখন এক ভয়ানক আতঙ্কে| থানা সদরে পাকিস্তানী মিলিটারি আসবে এটা অনেকেই বিশ্বাস করেনি| তাই এক রকম স্বস্তির সাথেই সবাই বাস করছিল| শুধু রাজাকার ও শান্তিরক্ষা কমিটির লোকদের থেকে একটু সাবধানে চলা ফেরা| কিন্তু ঘিওরে পাকিস্তানী মিলিটারি এট্যাকের খবরে মুক্তিবাহিনীও হতচকিত হয়ে গেছে| ক্যাপ্টেন হালিম ও কমান্ডার মনসুরের নেতৃত্বে মানিকগঞ্জ সদরের উপকন্ঠে তরাঘাটে একটা ব্যর্থ অপারেশন হয়েছে| বাবা সবার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন| কিন্তু কমাণ্ডার হাকিম উদ্দিন মানে হাকিম ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ নেই| যে সীমিত অস্ত্র ও স্বল্প প্রশিক্ষণ তাতে থানা সদরে পাকিস্তানী মিলিটারির সাথে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়| তাই শওকত চেয়ারম্যান ও রাজাকার কালুকে চোখে চোখে রাখাই এলাকার মুক্তিবাহিনীর কাজ|
একদিন সন্ধ্যায় বাবা ফিরলেন ইস্কুল থেকে| ক্লাশ নেই, ছাত্র ছাত্রীরাও কেউ ইস্কুলে যায় না| তবুও ইস্কুলে যাবার নাম করে বাবা তাঁর ইস্কুলে সদ্য নিয়োগ পাওয়া অনিল শিকদারকে নিয়ে নৌকা করে সকালে বের হোন| যদিও একজন মাইনে করে রাখা আছে সারা বর্ষাকালের জন্য| প্রতিদিন নৌকা চালিয়ে বাবাকে ইস্কুলে নিয়ে যাওয়াই তার কাজ|
মফস্বলে শিক্ষকতায় এক ধরণের বনেদিপনা থাকে| ইস্কুল কলেজের শিক্ষকেরা তাই কেউ নৌকা চালিয়ে কোথাও যান না| সমহু বিপদে পড়লেও না| একা একা কখনো কখনো নৌকা বাওয়া যায় কিন্তু কাউকে নৌকায় যাত্রী হিসেবে বসিয়ে নৌকা চালালে সেটা বিরাট এক অসম্মানজনক কাজ| কিন্তু এ যুদ্ধের দিনে জীবন বাঁচানোই আগে জরুরী| তাই অনিল শিকদারকে ডিংগি নৌকার পেছনের গলুইয়ে বৈঠা দিয়ে বসিয়ে বাবা সামনের গলুইয়ে আরেক বৈঠা নিয়ে প্রতিদিন সকালে বের হয়ে যান| পূর্বপাশে আমাদের গ্রাম লাগোয়া একটি গ্রাম| জুগিন্দা| শওকত চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে মুসলিম লিগের শক্ত ঘাঁটি আগে থেকেই সে গ্রামটিতে|
জুগিন্দার পাশ দিয়েই একটি খাল চলে গিয়ে নিমাই বিলে পড়েছে| প্রায় আধা মাইল প্রস্থ নিমাই বিলটি পার হলেই আরেকটি গ্রাম| প্রায় চার পাঁচ হাজার লোকের বাস সেখানে| মুসলমান প্রধান এ গ্রামটিই মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি| এ গ্রামের পরেই তেরশ্রীর জমিদার বাড়ি| বাবার কর্ম ও আড্ডার স্থল সেখানেই|
সেদিন সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরেই থম থমে মেজাজ বাবার| ঘটনা বোঝা গেল আরেকটু রাত বাড়লে| বাড়ির সামনে বৈঠক ঘর| সেখানে গোল হয়ে বসে বিবিসি ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে শোনে প্রতিরাতে পাড়ার অনেকেই| সেই সাথে আকাশবাণীর সংবাদ দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায় আর নীলিমা স্যান্নালের কন্ঠে| সেখানেই শলা-পরামর্শ হয়| সেদিন রাতে বিবিসি ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শোনা বন্ধ| গলার স্বরও সবার নিচু|
অনিল মাস্টার শুরু করলেন, কালুর এত বড় সাহস, দাদাকে বলে, স্যার আর কতদিন এ দেশে থাকবেন? এবার ইন্ডিয়া কেটে পড়েন |
দাদা মানে বাবাকে ইন্ডিয়া যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কালু রাজাকার| বাবাও নাকি কালুকে আচ্ছা মতো ধমক দিয়ে শাসিয়ে এসেছেন| বলেছেন, তুই নিজের পথ দেখ কালু| আমার পথ তোকে বাতলে দিতে হবে না|
কালু রাজাকার নাকি রাগে গড় গড় করতে করতে চলে গেছে| সবার মনে আশঙ্কা কালু যে কোন অঘটন ঘটাতে পারে এ পাড়ায়| সমুহ বিপদের প্রস্তুতির জন্যই সেদিনে রাতে বসা| অনেকে পরামর্শ দিল পাড়ার বউদের ছেলেমেয়েসহ অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে|
কেউ কেউ মুক্তিবাহিনীর প্রতি হতাশ হয়ে বলল, আর এ দেশে থাকা যাবে না| চল আপাতত ইন্ডিয়া কিংবা কোন মুসলিম বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেই|
মন্টু পাশ থেকে বলে বসল, সব রঁসূনের গোড়া এক| কোন মুসলমানেরে বিশ্বাস করবো বলো| পাশের গ্রাম বহেরাতলির সবাইতো শেখ মুজিবের আওয়ামী লিগ করে| ওদের কিন্তু রাজাকারেরা কিছু বলে না| আমরা হিন্দুদেররই যত দোষ| দেশটা স্বাধীন হলে মনে হয় এ দেশে শুধু হিন্দুরাই থাকবো| ওরা মুসলমানেরা সব পাকিস্তানে চলে যাবে| কাকা, আপনি আর মুক্তিবাহিনী মুক্তিবাহিনী করবেন না তো? টিঁকিটি দেখছি না মুক্তিবাহিনীর| ব্যাটারা ইন্ডিয়া গেছে ট্রেনিং নিতে;এদিকে আমরা মরে ভুত হ্য়ে যাই তারপর ওনারা আসবেন| আমি আর ইউনিয়ন বোর্ডে পটকা-ফটকা ফাটাতে পারব না, কাকা| আমি বলে দিলাম স্পষ্ট করে|
সবাই বাবার দিকে তাকিয়ে| ভাবছিলেন বাবা মন্টুকে একটা জোরে ধমক লাগাবেন| বাবা চুপ করে থাকলেন| বললেন,কী করা যায় এখন? শওকত ভাই আসলে কোন কথাই রাখছেন না| কালু মনে হয় মিলিটারি না হলেও রাজাকার নিয়ে আসবে দু একদিনের মধ্যেই| রাতে রাতে গ্রামে পাহারা বসাতে হবে| মিলিটারি কিংবা রাজাকার আসলেও যেন কেউ কেউ পালিয়ে বাঁচতে পারে| আর আমি বহেরাতলিতে আমার যারা যারা ছাত্র আছে সবাইকে বলে রাখি, যদি ওরা কয়েকটা দিন আমাদের গ্রামে এসে থাকতে পারে|
অনিল মাষ্টার একটু ফোঁড়ন কাটল বাবার কথায়, ‘ শিয়ালের কাছে মুরগী জমা রাখার মতো কথা বললেন দাদা|
এটার মানে কী দাঁড়াল অনিল? বাবা বললেন|
রথ যাত্রার দিন ঘিওরের ম্যাসাকারের পর অখিল ঠাকুরের পরিবার নিরাপদ ভেবে মজিদ মাষ্টারের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল| দু’সপ্তাহ যেতেই মজিদ মাষ্টার ঘরে জোয়ান বউ আর ছেলে মেয়ে থাকতেও অখিল ঠাকুরের কলেজে পড়া বোনকে প্রথমে ইজ্জতহরণ করে পরে জোর করে বিয়ে করেছে, সে খবর জানেন?
মন্টু অনিলের কথায় একটু জোর পেল, অখিল ঠাকুরের বোনই শুধু বিয়ে করে নাই, অখিল ঠাকুরের বউ মাসহ পুরো পরিবারকে গরুর মাংশ খাইয়ে মুসলমান বানিয়েছে| কাকা, আর যাই করেন, ওই গরু-খাওয়া জাতকে দিয়ে আর বিশ্বাস নেই|
এবার বাবা ধমক লাগালেন মন্টুকে| ‘তোদের কথায় মনে হচ্ছে মুসলমান সবাই খারাপ, তাই না? সব মুসলমান খারাপ হলে শেখ মুজিবও খারাপ? কমান্ডার হাকিম ভাই, আফসার স্যার সবাই খারাপ? এই যে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করে মরে যাচ্ছে, ওদের কয়জন আর হিন্দু| সবাই তো মুসলমান| এবার বল ওদের সবাই খারাপ| সবাই মজিদ মাষ্টারের মতো বদমাইশ| কালুর মতো সবাই হলে তো এই চার মাসে হিন্দু পাড়া আর থাকতো না, সবাই মেরে কেটে লুট-পাট করে নিয়ে যেতো|
অনিল মাষ্টার মন্টুর কথায় সায় দিয়ে বললো, কিন্তু দাদা এই পুরো মানিকগঞ্জে শুনেছেন একটাও মুসলমান বাড়ি লুঠ হয়েছে? একটাও মুসলমানের দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে? একজন মুসলমানকেও পাকিস্তানী মিলিটারি বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে? মুক্তিযুদ্ধও করছে অধিকাংশ মুসলমান, দেশ স্বাধীন হলেও মুসলমানের দেশই তো হবে এটা| খামাখা আমাদের উপর অত্যাচার কেন? এরচেয়ে আমাদের ইন্ডিয়াতে সরকারী ভাবে পাঠিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়|
বাবা বললেন, অনিল তুমি শেষে যা বললে, এটাই তো পশ্চিম পাকিস্তান সরকার চাচ্ছে| সেই সাথে তাল মেলাচ্ছেন পূর্ব-পাকিস্তানের কিছু মুসলিম লিগার| শেখ মুজিব, আওয়ামী লিগ আর মস্কোপন্থী বামপার্টিগুলো পাকিস্তানের এ চক্রান্ত মানবে না বলেই তো এ যুদ্ধ| আমরা তো এদেশেরই মানুষ| ইন্ডিয়াতে যাব কোন দুঃখে? গেলে তো ৪৭’এর দেশ বিভাগের সময়েই যেতাম| দেশ ছেড়ে কোথাও যাব না| আর সে জন্যই আমাদের মুক্তিবাহিনীর সাথে থাকতে হবে|
বাবার উচ্চকন্ঠে ভিতর বাড়ি থেকে মা, জেঠীমা সবাই বাইরের উঠোনে চলে এসেছে| মাকে দেখে বাবা বললেন, তুমি আবার উঠে এসেছো কেন? ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক|
http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=36974
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ১৮:৩৫582586
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.20 | ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ১৮:৩৫582586- চন্দ্রমুখী জানালা- পর্ব তিন
লিখেছেন: ভজন সরকার
___________________________________
(৬)
মা তখন সাত মাসের অন্ত:সত্বা| দেশে যুদ্ধ চলছে| বর্ষাকাল| যোগাযোগ ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা| বিপদে আপদে হাসপাতাল কিংবা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া খুব কঠিন| গ্রামের হোমিওপ্যাথ জ়িতেন ডাক্তারই অগত্যার ভরসা; কিংবা তেরশ্রীর এলএমএফ ডাক্তার লোকমান হাকিম| তাছাড়া ঠাকুমায়েরও অগাধ সাহস এবং অভিজ্ঞতা| বাবাসহ নয় সন্তানের জন্ম দিয়েছেন ঠাকুমা| তারপরে সাত-সাতটি ছেলের বউদের সন্তান তো হচ্ছেই বাড়িতে প্রতি বছরই দু’একটি করে|
বাবা তাই তাঁর মা ও বৌদিদের উপর ভরসা করেই একরকম নির্ভাবনায় থাকেন| রাতে ঘুমের সময় একবার হয়ত জিজ্ঞেস করেন, তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো? ডাক্তার লোকমান ভাইকে একবার নৌকা পাঠিয়ে নিয়ে আসি?
মা সারাদিন কাটিয়ে দেন বই পড়ে আর রেডিও শুনে| অসুবিধে থাকলেও মুখ বুজে সব সহ্য করেন| বাবার কথার উত্তরে বলেন, না, দিদিরা তো আছে| তাছাড়া মাকেও মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করি খারাপ লাগলে|
বাড়িতে যৌথ পরিবার| ছেলেমেয়েসহ মোট ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জনের খাবারের যোগাড়আত্তি করতে হয় প্রতিবেলা| এক জেঠিমার ভাই তার দুজন সোমত্ত মেয়েকে নিরাপদ ভেবে পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে| বাবার এক চিরকুমার কাকা তখন মরনাপন্ন | তাছাড়া একান্নবর্তী পরিবারের নানাবিধ সাংসারিক জটিলতা তো আছেই| সেবার আউশ ও পাটের ফলনও হয়েছিল খুব ভাল| যুদ্ধের ফলে জ়েঠামশাইদের ব্যবসায়ের টানটান অবস্থা জমিতে ভাল ফলনের জন্য পুষিয়ে গেল| তাই অন্যান্য বছর বর্ষাকালে সংসার নির্বাহের যে চিন্তা থাকে এবারে সেটা আর নেই|
জলেও মাছ পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর| বাড়ির সামনের খালে প্রতি বছরের মতো সেবারও কার্তিক হালদার ভেসাল জাল দিয়েছে| প্রতিদিন বিকেলেই বাড়ি যাওয়ার আগে বাড়িতে একটু থামে আর জেঠাদের বলে, দাদা, এবার এতো মাছ ভগবান দিয়েছে ভাবতে পারিনা|
নৌকার তলা দেখিয়ে বলে, মাঝে মাঝে এমন একটা ঝাঁক আসে যে, পা দিয়ে ঠেলে জাল উপরে ওঠাতে পারিনা| আর মাছের এত তেল আগে কখনো দেখিনি, দাদা| থাকবেই না কেন, ধলেশ্বরী দিয়ে তো কলা গাছের মতো মানুষের লাশ ভেসে যায়| মরা মানুষের চর্বি আর পচা লাশ খেয়ে খেয়ে মাছের যে বিশাল সাইজ এবার!
শ্রাবন মাসের প্রথম সপ্তাহে বাবার ছোট কাকা, মানে ছোট দাদু মারা গেলেন| ছোট বেলায় রোগে পা দু’টো শুকিয়ে কাঠির মতো হয়ে গিয়েছিল ছোট দাদুর| সারাজীবন লাঠির উপর ভর দিয়েই চলাফেরা করে গেলেন| বিয়ে-থা করলেন না| ভাতিজাদের সংসারেই সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন| বাড়ির দক্ষিন দিকে নারকেল আর কড়ুই গাছের মাঝখানে জলের পুরানো টিউবওয়েল| টিউবওয়েলের গা লাগোয়া বৈঠক ঘর, যাকে কাছারি ঘর বলে সবাই| সে বিশাল কাছারী ঘরের এক পাশে ছোট দাদুর ঘর| শেষদিকে আর চলাফেরা বিশেষ করতে পারতেন না| ধরে ধরে পায়খানা-প্রস্রাব করাতে হোত| মুখে তুলে খাইয়ে দিতে হোত| বিছানার পাশে থাকা লাঠিটাই এক সময়ে সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিল ছোট দাদুর| একদিন সকালে সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন|
চারদিকে থমথমে অবস্থা| সকাল-সন্ধ্যা-রাত সব সময় এক উৎকন্ঠায় কাটে| সবার চোখ দক্ষিন দিকে| নিমাই বিলে কোন বড় নৌকা দেখলেই সবাই ভয়ে আঁতকে ওঠেন| এই বুঝি পাকিস্তানী মিলিটারিকে গ্রামে নিয়ে এলো রাজাকারেরা| বর্ষা এসেছে মাত্র মাসখানেকের বেশী হলো| তাই লঞ্চ নিয়ে এখনো মিলিটারি আসবে না; যদি লঞ্চের প্রোপেলার কোন কিছুতে আটকে যায় সে ভয়ে? তাই ভয় শুধু বড় বড় ছইওয়ালা নৌকায়|
ছোট দাদুর মৃত্যুতে বাড়িতে সবাই শোকে মূহ্যমান| কিন্তু কান্নার রোল নেই| অনেকে আবার হাঁফ ছাড়লেন এ ভেবে যে, বাড়িতে মিলিটারি আগুন দিলে সবাই পালাতে পারলেও ছোট দাদু কোথায় যাবেন? তাকে হয়তো বা ঘরের মধ্যেই পুড়ে মরতে হতো| তারচেয়ে ভগবান নিজ হাতে নিয়ে নিলেন সেটাই ভাল!
এদিকে ছোট দাদুর মরদেহ নিয়ে মুশকিলে পড়া গেল| গ্রামের শ্মশাণটা জলে প্রায় তলিয়ে গেছে| একটু টিবির মতো জায়গা তখনো জেগে আছে| কিন্তু যুদ্ধের এ অবস্থায় ছোট দাদুকে সৎকার করতে কেউ সাহসী হলো না| চিতার আগুন যদি পাকিস্তানী মিলিটারিকে হিন্দুগ্রাম চিনিয়ে দেয়?
বাবা মৃদু আপত্তি করলেন, পাকিস্তানী মিলিটারি কী আর চিতার আগুন দেখে চিনবে কোনটা হিন্দু গ্রাম? শুনেছি শওকত চেয়ারম্যান থানায় গিয়ে হিন্দু গ্রামগুলোর নাম-ঠিকানা দিয়ে এসেছে| কোন বাড়ির ছেলেরা মুক্তিবাহিনীতে গেছে, কোন বাড়িতে যুবতী বউঝি আছে সব তথ্য এখন থানায়| যাই হোক, তোমরা পুড়াতে না চাইলে, না পুড়াবে| তবে কাকার মৃতদেহকে তো কোথাও পুঁতে রাখতে হবে?
বড় জেঠামশাই বললেন, নৌকা করে ধলেশ্বরীতে নামিয়ে রেখে আসি কাকাকে| গঙ্গামার শরীরেই বি্লীন হয়ে থাকুক|
পাটের চটের বস্তা বড় একটা মশলা বাটার পাথরের পাটা ভরে লম্বা গলুইওয়ালা ছিপ নৌকায় তোলা হলো| শাস্ত্র মতে বাড়ির ঘাটে বড় জেঠা মুখাগ্নি করলেন ছোট দাদুর| তারপর চাঁটাই দিয়ে মুড়িয়ে নৌকার পাটাতনের নীচে লম্বা করে শুইয়ে দেয়া হলো| উপরে কাঠের পাটাতন বিছিয়ে কয়েকটা পাটের গাঁইটও তোলা হলো| যেন সবাই ভাবে, বেপারী নৌকা তরা হাটে যাচ্ছে পাট বেচতে|
ছোট দাদুর মৃতদেহ ধলেশ্বরী নদীতে চটের বস্তার সাথে বেধে নামিয়ে দেয়া হলো স্রোত দেখে মাঝ নদীতে| মরদেহ জলে নামানোর আগে মাথার দিকটা পূর্বদিক করে প্রথমে জলের সমান্তরাল করে রাখা হলো| তারপর ভারি চটের বস্তাটা জলের মধ্যে ছেড়ে দিল মন্টু | বাঁশের চাটাইয়ে জড়ানো ছোট দাদুর দেহ ধলেশ্বরীর জলে সোজা তলিয়ে গেল| বাঁশের চাটাই থেকে কয়েকটা জলের বুদবুদ উঠে ঢেউয়ের সাথে মিলিয়ে গেল নিমিষেই| মেঝো জেঠা তার আদরের কাকাকে মাঝ নদীতে ছেড়ে দেয়ার সময় হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন| বাকী সবাই ক্ষীনস্বরে ‘হরিবোল হরিবোল, বল হরি’ করতে করতে নৌকা গ্রামের দিকে নিয়ে এলো| প্রায় নিরবেই ছোট দাদুর অস্তিত্ব সংসার থেকে নেই হয়ে গেল সেদিন| পাড়ার কিছু মানুষ ছাড়া গ্রামের অধিকাংশ মানুষই জানলো না, বাড়ির ল্যাংড়া-খোড়া সে বুড়োটা আর নেই|
(৭)
ত্রিশ দিনের অশৌ্চ পালন করা হলো বৈশ্য মতে| ছোট দাদু ছেলের মতো ভালবাসতেন মেঝ জ়েঠাকে| তাই তিনিই ছেলের মতো নিয়ম মেনে অশৌ্চ পালন করতে চাইলেন| পারিবারিক ব্রাক্ষণ বললেন যেহেতু বড় জ়েঠা মুখাগ্নি করেছেন, তাই বড় জ়েঠাকেই এক কাপড়ে এক মাস ছেলের ব্রত পালন করতে হবে| মেঝ জ়েঠার মন খারাপ| কিন্তু মন খারাপের সময় নেই এ যুদ্ধের খারাপ সময়ে| বড় জ়েঠা আর বড় জ়েঠিমাই ছোট দাদুর ছেলে আর ছেলে-বঊয়ের নিয়মে শাস্ত্র মেনে মৃতের আত্মার সদগতির জন্য সদাকর্মে করতে লাগলেন|
বাড়ির সবার জন্য অল্প তেলে নিরামিষ রান্না হলেও মায়ের জন্য আলাদা রান্না হয় অনেকের অগোচরেই| মায়ের প্রসবের তখন আর মাস দেড়েক বাকী| তাই বড়মা অর্থ্যাত সেজো জেঠিমা বাবার সাথে যুক্তি করে মায়ের জন্য আমিষের ব্যবস্থা করতে লাগলেন| কার্তিক জেলের কাছ থেকে গোপনে মাছ চলে আসতো বড়মার কাছে| দুপুরে সবাই যখন বাড়ির অন্য কাজে ব্যস্ত বড়মা তখন পাশের বাড়ি থেকে মাছের ঝোল রেঁধে নিয়ে আসেন মায়ের জন্য|
মা একবার মৃদু আপত্তি করলে বড়মা ধমকে উঠে বললেন, ওই মেয়ে, তুই সন্তানের মর্ম বুঝবি কি করে লো? তোর তো দু’বছর পর পর বাচ্চা হচ্ছে; হতিস আমার মতো বাঝা তখন বুঝতিস? এই পেটে বিশ বছরে একটা সন্তানও ধরতে পারিনি| আমি বুঝি সন্তান পেটে ধরা কী জিনিস| যে গেছে তার জন্য শোক না করে, যে আসবে তার জন্য ব্যবস্থা কর|
বাবার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন বড় মা সংসারে আসেন| বড়মারই বা কত বয়স তখন? বড়জ়োর বারো তেরো হবে| তারপর থেকে নিঃসন্তান বড়মা সন্তান হিসেবে মানুষ করেছেন বাবাকে| বিয়ের পর এ সংসারে এলে বড়মাই মাকে আগলে রেখেছে কখনো বড় দিদি, কখনো বা মায়ের মমতায়| মায়ের প্রথম সন্তান হওয়ার মাস দুয়েকের মধ্যেই মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা, দু’মাসের সে শিশু সন্তানকে নিয়ে মহুকুমা শহরে গিয়ে পরীক্ষা দেয়া সেও তো সম্ভব ছিল বড়মার জন্যই| তার বছর দেড়েকের মধ্যেই আরেক কন্যাসন্তান| কিন্তু বড়মাই মায়ের লেখাপড়ায় বন্ধ করতে দেননি| বাড়িতে পড়েই মা তখন ইন্টারমিডিয়েটে প্রথম শ্রেনী পান প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে| সব কিছুরই পেছনে বড়মা|
বাবাও বড়মার কথার বাইরে কিছুই করেন না| তাছাড়া সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেক রাতে বাড়ি ফেরার অভ্যেস বাবার| এখন তো ইস্কুলে যাওয়ার কথা বলে সারাদিন মুক্তিবাহিনীতে রিক্রুট করা নিয়েই সারা এলাকা ঘুরে বেড়ান| বড়মার ভয় সেখানেই| বারবার বাবাকে বলছেন, শোন তুই ইণ্ডিয়া চলে যা| তোর শ্বশুর বাড়িতে কিছুদিন থেকে আয়| ছোট বউয়ের দায়িত্ব আমি নেব|
বাবা জানেন বড়মাকে কোন কথায় বশে আনা যাবে| বাবা বলেন, ঠিক আছে বৌদি, তুমি যখন বলছো ইন্ডিয়াতেই যাই| কিন্তু ছেলে আর স্ত্রীকেও নিয়ে যাবো সংগে| ওদের রেখে আমি যেতে পারবো না|
বড়মা এবার পিছু হটেন| ছেলেকে অর্থ্যাত আমাকে সারাক্ষণ বুকে-পিঠে করে রাখেন বড়মা| চোখের দূরে আমাকে নিয়ে যাবে শুনে বড়মা আঁতকে ওঠেন| কথা ঘুরিয়ে বলেন, বালাই-ছাট! আমাদের এ বিল এলাকায় মিলিটারি আসবে কোন সাহসে? শুনেছি ওই খান-সেনারা নাকি সাঁতারই জানে না? ওদের জীবনের মায়া আছে না?
কিন্তু তার এক সপ্তাহ পরেই বড়মার কথা মিথ্যে প্রমানিত হলো| সকাল গড়িয়ে সবেমাত্র দুপুর| বাবার সেদিন বেরোতে একটু দেরী হয়েছে| উত্তর দিকের বাঁশের ঝাড়ের কাছে রান্না ঘর আমাদের| বাবাসহ কয়েকজন রান্না ঘরের বারান্দায় কাঠের পিঁড়ি পেতে দুপুরের ভাত খাচ্ছেন| হঠাত করে কেউ একজন চিৎকার করে উঠলো, নিমাই বিলের মাঝ দিয়ে দৌলতপুর থানা থেকে দুই নৌকা মিলিটারি নাকি পূর্বদিকে অর্থ্যাত আমাদের গ্রামের দিকে আসছে|
কোথায় রইল ভাতের থালা? কোথায় খাবার-দাবার? সবাই যে যার মতো বাবাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলো| সবাই জানে গ্রামে মিলিটারি আসলে এ বাড়িতেই আসবে এবং টার্গেট বাবা| কয়েকদিন আগেই কালু রাজাকারের সাথে বাবার কথা কাটাকাটি হয়েছে| বাবা নির্বিকার রইলেন| আস্তে করে হাতটা ধুঁয়ে বললেন, কেউ চিৎকার-চেঁচামেচি করবে না| আমি আগে দেখি আসলেই মিলিটারির নৌকা কিনা?
বাবা ভিতর বাড়ি থেকে বাইরের উঠোনে এলেন| তারপর দক্ষিন-পশ্চিম দিকের কড়ুই গাছের নিচে ধানের খড়ের পালার আড়াল থেকে দেখলেন, দু’টো বড় বড় ছইওয়ালা নৌকা গ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণ দিকের বটগাছের পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে| নৌকার সাইজ ও ছইয়ের ওপর মানুষজনের নড়াচড়া দেখে বুঝলেন এগুলো পাকিস্তানী মিলিটারির নৌকা|
বাবা বড়মাকে বললেন, বৌ্দি তুমি ছেলে আর ছোট বউকে নিয়ে বহেরাতলির মুসলিম পাড়ায় চলে যাও| আর বাড়ির মেয়ে আর অন্য বউদেরকেও পারলে অন্য কোথাও পালাতে বলো| মনে হয় রাজাকারের পাকিস্তানী মিলিটারি নিয়েই আসছে এদিকে|
বড়মা বললেন, তুই কী করবি? তোরই তো আগে পালানো উচিত| তুইও চল আমাদের সাথে|
বাবা বললেন, আমি তো আর একা মিলিটারির সাথে লড়তে পারবো না| তাছাড়া এ বাড়িতে আমরা যত লোকজন অস্ত্র ছাড়া হয়তো কেউ ঢুকতে পারবে না| কিন্তু লাঠি নিয়ে তো আর অস্ত্রের সাথে যুদ্ধ করা যাবে না| তাছাড়া বর্ষার দিন, পালানোর জায়গাও নেই| তাক করে করে গুলি করবে ওরা| তাই আমাকেও পালাতে হবে| তবে তুমি আগে যাও ছোট বউকে আর ছেলেকে নিয়ে|
বাবা অন্য সবার মতো মাকে ছোট বউ বলতেন সবার সামনে| মাকে ডেকে বললেন, পূবদিকের ঘাটে ছোট ডিংগি নৌকাটা আছে| তুমি ছেলেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি মুসলিম পাড়াও যাও| বৌ্দি আর ভাস্তেদের কাউকে সাথে নিও নৌকা তো চালাতে হবে| দেরি করো না, তাড়াতাড়ি কর|
মা কিছু বলতে চাচ্ছিলেন| বাবার ধমকে মায়ের সে কথাটা আর স্পষ্ট করে বলা হলো না| বড়মা আমাকে কোলে নিয়ে মায়ের হাত ধরে পূবদিকের নৌকা ঘাটের দিকে দৌঁড় দিলেন|
নৌকায় ওঠার পর মায়ের মনে হলো মেয়েকে তো আনা হয়নি? আমার দু’বছরের বোন হয়তো কোন জেঠাতো বোনের কোলে ছিল| ওকে নিয়েই হয়তো জেঠাতো বোনটি আমাদের বিরাট বাড়ির কোন ঝোপজংগলে কিংবা ঘরের মধ্যে পালিয়েছে| মা তাঁর দুবছরের মেয়েকে রেখে পালাতে হচ্ছে বলে কেঁদে উঠলেন| ছোট ডিংগি নৌকায় তখন আমি,মা, বড়মা আর নয়-দশ বছরের আরেক জেঠাতো ভাই বীরেণ| কে নৌকা চালাবে? নৌকা সোজা করেই বা রাখবে কে? এত সব কিছুই মনে না করে বাবা তখন ঘাট থেকে নৌকা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়ে নিজে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন| আমি বড়মাকে জোরে জড়িয়ে ধরে, বাবা ,বাবা বলে কেঁদে উঠলাম| বড়মা আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে নৌকার মাঝখানের গুঁড়ার কাঠের মধ্যে জোর করে বসিয়ে দিল|
বড়মা বীরেণকে একটা বৈঠা দিয়ে বললো, বাবা, তুই পেছনের গলুইয়ে গিয়ে নাও সোজা করে রাখতে পারবি না?
নয়-দশ বছরের বীরেণ তখনই বৈঠা চালাতে শিখে গেছে| বীরেণ তাড়াতাড়ি পেছনের গলুইয়ে গিয়ে বৈঠা নামালো| বড়মা আরেকটা বৈঠা নিয়ে সামনের গলুইয়ে গিয়ে সামনের দিকে বৈঠা দিয়ে জল কাটতে শুরু করে দিলেন| মা আমার পাশে বসে অসহায়ের মতো বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন|
আমাদের বাড়িটি গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে| তার পাশ দিয়েই একটি ছোট খাল গিয়ে মিশেছে নিমাই বিলে| খাল দিয়ে সিকি মাইলের মতো গেলেই আরেকটি মুসলিম পাড়া| জুগিন্দা| খালের গা-লাগোয়াই রহিমুদ্দিন খলিফার বাড়ি| রহিমুদ্দিন চাচার কাছে লুংগি সেলাই থেকে শুরু করে ছোট খাঁটো জামা-কাপড় বানায় সবাই| আমাদের বাবা-জেঠাদের সাথেও রহিমুদ্দিন চাচা ও চাচীর ভাল সম্পর্ক| সে কথা চিন্তা করেই বড়মা বীরেণকে বললেন, নৌকা খলিফা বাড়ির দিকে ধরে রাখ|
খালের জলে তখন তেমন স্রোত নেই| কিছু কচুরিপানার থোক থোক ঝাঁক নৌকাকে মাঝে মাঝে থামিয়ে দিচ্ছে| বড়মা তার অনভ্যস্ত হাতে যত জোরে পারেন নৌকা সামনের দিকে চালাচ্ছেন| পেছন থেকে বীরেণ বারবার বলে উঠছে, জেঠি আর পারি না তো?
-আর একটু সোজা করে রাখ বাবা| এই তো একটু গেলেই খলিফা বাড়ি|
বীরেণ তার ছোট্ট হাতের দক্ষতায় বৈঠা দিয়ে জল কেটে কেটে বড়মাকে সাহায্য করছে| মা এক হাতে আমাকে, অন্য হাতে তলপেট শক্ত করে ধরে আছেন|
নৌকা রহিমুদ্দিন খলিফার বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তখন| হঠাত করে দেখা গেল রহিমুদ্দিন চাচার ছেলে বাঁশের বড় একটা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে| ঘাটে নৌকা ভিড়ানোর আগেই জোরে জোরে বলছে, মালাউনের কোন জায়গা নেই আমাদের বাড়িতে| যা অন্য বাড়িতে যা|
বড়মা বলছে, দিলু তোরা এই বিপদের দিনে এমন করছিস কেন? আমাদের একটু আশ্রয় দে, মিলিটারি গেলেই তো আমরা চলে যাবো| ও বুজি, তুমি দিলুরে একটু থামাও না|
বুজি অর্থ্যাত রহিমুদ্দিন খলিফার বউ বড়মার কথা না শোনার ভাণ করে অন্য দিকে সরে গেল| দিলু জলের আরো কাছাকাছি নেমে এসে লাঠি দিয়ে জলে আঘাত করতে লাগলো| একেবারে ঘাটের কাছাকাছি নৌকা চলে এসেছে দেখে দিলু আরো চিৎকার করে বলতে লাগলো, নাও ঘাটে ভিড়ালে কিন্তু লাঠি দিয়ে মাথায় মারবো, মালাউনের বাচ্চারা|
বীরেণ দিলুর লাঠি দেখে ভয় পেয়ে হাতের বৈঠা ছেড়ে দিয়ে উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলো| মা পেটে হাত দিয়ে ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলো| বড়মাকে বললো, দিদি চল বাড়ির দিকে যাই| আমি আর পারছি না|
বীরেণের হাতে আর নৌকার হাল নেই| বড়মার শত কাকুতি মিনতিতেও দিলুদের মন একটুও নরম হলো না| রহিমুদ্দিন চাচা কিংবা তার স্ত্রীকেও আর বাড়িতে দেখা গেল না| কিছুতেই নৌকা রহিমুদ্দিন খলিফার ঘাটে ভিড়ানো গেল না| নৌকা তখন খাল পেরিয়ে প্রায় নিমাই বিলের মুখে চলে এসেছে| মায়ের চিৎকারে আমি আর বীরেণ হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলাম|
বড়মা আবার শক্ত হাতে সবকিছু সামলানোর চেষ্টা করলেন| বীরেণকে আবার বললেন, বাবা, আর একটু সময় নৌকাটা সোজা করে রাখ| মাত্র একটু তো বিল| পাড়ি দিলেই বহেরাতলী| নুরুদের বাড়ি ওই দেখা যাচ্ছে| ধর একটু বাবা|
বীরেণ আবার নৌকায় তুলে রাখা বৈঠা জলে নামালো| বড়মা সামনে দিকে নৌকা চালাতে লাগলেন| আধামাইলের মতো নিমাই বিল তখন যেন এক মহাসমুদ্র| এদিক দিয়েই তো মিলিটারির নৌকা আসবে| তাই যত তাড়াতাড়ি বিলের ওদিকে ধান খেতের কাছে পৌঁছুতেই হবে|
অনেক কষ্টে নিমাই বিল পাড়ি দিয়ে ওপারে যেতেই দেখা গেল বহেরাতলী থেকে কয়েকজন একটা নৌকা নিয়ে এদিকে আসছে| বড়মা একটু সাহসে বুক বাঁধলেন| কিছুক্ষণ পরে নৌকাটা কাছে আসতে দেখা গেল নুরু আর আরশাদ কয়েকজনকে নিয়ে এগিয়ে আসছে| নুরু আরেকজনকে নিয়ে আমাদের নৌকায় এসে সজ়োরে বৈঠা চালিয়ে বহেরাতলীর তমিজদের বাড়িতে নৌকা ভিড়ালো| বড়মা মাকে হাতে ধরে নৌকা থেকে নামাতেই বড়মার গলা ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন মা| ততক্ষণে তমিজের বউ মাকে ধরে বাড়ির উঠোনে বসিয়েছে|
তমিজদের নৌকা ঘাটের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল পাকিস্তানী মিলিটারির নৌকা আমাদের বাড়ির ঘাটে ভিড়ে গেছ|
http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=37111
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... জয়ন্ত ঘোষ , অভিজিৎ চক্রবর্তী। , Kuntala)
(লিখছেন... অমিতাভ চক্রবর্ত্তী, অঞ্জনা ঘোষাল, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... Sara Man, প্যালারাম, যদুবাবু)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... dc)
(লিখছেন... &/, aranya)
(লিখছেন... রং, Kuntala)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... &/, dc, &/)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... &/, সিএস, &/)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... রঞ্জন , kk, Ranjan Roy)
(লিখছেন... পাপাঙ্গুল)
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : [email protected] ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত