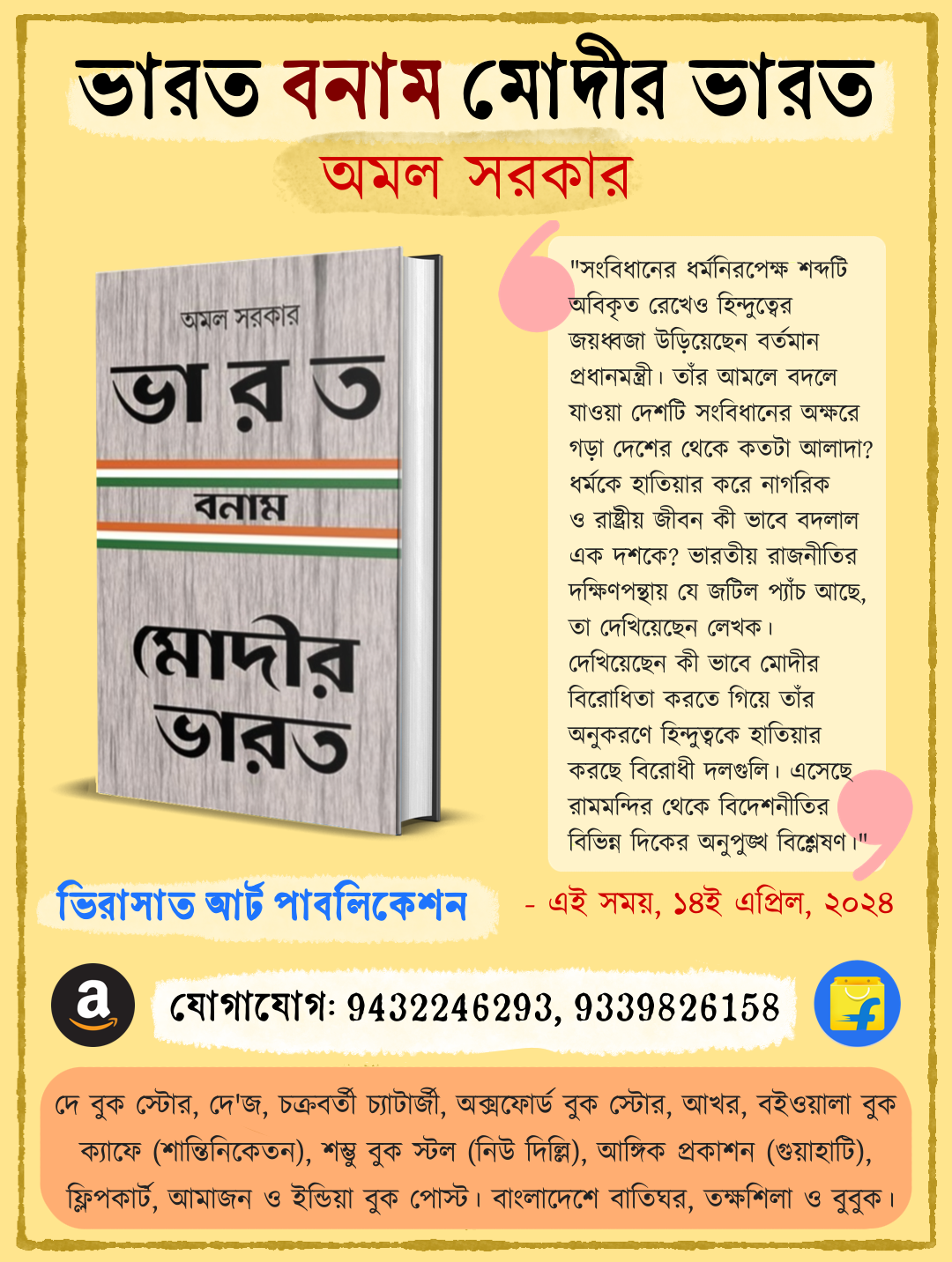- টইপত্তর অন্যান্য

-
১৯৭১ :: মুক্তিযুদ্ধের কথা
বিপ্লব রহমান
অন্যান্য | ০৯ ডিসেম্বর ২০১২ | ৫০০৪৩♦ বার পঠিত
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:১১582763
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:১১582763- জোয়ান বায়েজ : আমাদের মানচিত্র তোমাকে ডাকছে (উৎসর্গ অমি রহমান পিয়াল)
লিখেছেন: অভিজিৎ
তারিখ: ২ পৌষ ১৪১৮ (ডিসেম্বর ১৬, ২০১১)
__________________________________________________________
[এ লেখাটা পিয়ালের জন্য। তিনি মুক্তমনায় লিখেন না, মাঝে সাঝে হয়তো দু’ একটি মন্তব্য করেছেন এখানে ওখানে। এইটুকুই। আমার সাথে তার পরিচয় নেই সামনাসামনি, কিন্তু তার পরিচয় অন্যত্র। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে আমরা যেটাকে বুঝি সেটা আক্ষরিক অর্থেই সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার সংকল্প নিয়েছেন তিনি। অস্ত্র তার ইন্টারনেট। নিজের তারুণ্যের শক্তি আর দেশপ্রেমকে পুঁজি করে যেন আক্ষরিক অর্থেই কবর থেকেই উঠিয়ে এনেছেন মুক্তিযুদ্ধের এমন সব বিরল দলিল দস্তাবেজ যা আগে কোথাওই প্রকাশিত হয়নি। সে সব দলিলের পেছনে তার নিয়মনিষ্ঠ পরিশ্রমের ছাপ, দৌড়াদৌড়ির ছাপ, আর পাশাপাশি মেধা আর প্রাজ্ঞতা তো আছেই।
তার সর্বশেষ কাজটি নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় দু জন বিদেশী ব্যক্তি আমাদের স্বাধীনতার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। একজন ফরাসী যুবক জাঁ ক্যুয়ে, অন্যজন বেলজিয়ামের মারিও রয়ম্যান্স । জা কুয়ে ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর প্যারিসে পিআইএর একটি ফ্লাইট হাইজ্যাক করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের জন্য সাহায্য চেয়ে। আর মারিও রয়ম্যান্স বেলজিয়ামের এক যুবক যিনি চুরি করেছিলেন ভারমিয়ারের পেইন্টিং- ‘দ্য লাভ লেটার’। ওই একই উদ্দেশ্যে। এদের সম্পর্কে আমরা জানতামই না, পিয়ালের লেখার আগে। এর জন্য তার ফরাসী আর্কাইভ খুঁজতে হয়েছে, ফরাসী পত্রিকা থেকে বন্ধু বান্ধবের সাথে মিলে অনুবাদ করতে হয়েছে বাংলায়। পিয়াল নিজেই বলেছেন, “মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অনন্য অবদান রাখা এই দুই বিদেশীকে প্রকাশ্যে আনাটা আমার জীবনের সেরা কাজগুলোর মধ্যে পড়ে”। অথচ তারা সারা জীবনের সেরা কাজ বেহাত হয়ে যেতে দেখলেন তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই। গত ২ ডিসেম্বর প্রথম আলোর সাময়িকী অন্য আলোয় প্রচ্ছদ কাহিনী করা হলো ওরাও পাশে ছিলো নামে একটি লেখা। পুরোটাই অমি রহমান পিয়ালের ব্লগ আর্টিকেলের উপর ভিত্তি করে, কেবল সযত্নে পিয়ালের নামটি বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রথম আলোর লেখাটির নীচে পাঠকের মন্তব্যগুলো পড়লেই বিষয়টা বোঝা যায়। এর পর কালের কণ্ঠে আরেকটি লেখা বেরোয় মানবতার জন্য 'অপরাধ'নামে , পরে ইত্তেফাকে। সবগুলো লেখাই পিয়ালের পরিশ্রমলব্ধ লেখাগুলোর উপর ভিত্তি করে লেখা, কেবল মুল লেখকের কোন নামগন্ধ নেই। কৃতিত্ব দেয়া হয়েছে কোথাকার কোন পুলিশ বিভাগের এএসপি নাজিমুল হককে আর ‘এক ঝাঁক উজ্জ্বল তরুণ’কে। কোন এক চিপা দিয়ে পিয়ালের নাম এসেছে বটে, তবে উনাকে পরিচিত করা হয়েছে কোন এক ‘প্রবাসী ব্লগার’ হিসেবে। বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম এর কন্ট্রিবিউটিং এডিটর একটি সম্পাদকীয় লিখেছেন তার পত্রিকায় - শেষাবধি গবেষণাও ছিনতাই! নামে। পিয়ালও থাকতে না পেরে একটি শ্লেষাত্মক লেখা লিখেছেন ‘পুলিশের বিশেষ বিভাগের এএসপি ও একঝাক উজ্জ্বল তরুণকে আমার শুভেচ্ছা’ শিরোনামে। এর মধ্যে প্রথম আলো অবশ্য ক্ষমা চেয়েছে অপকর্মটির জন্য। কিন্তু কালের কণ্ঠ আর ইত্তেফাক এখনো নীরব!
পিয়াল ফেসবুকে আমার বন্ধু লিস্টে ছিলেন, কিন্তু কখনোই যেচে আলাপ করা হয়নি। আমার আর তার লেখালিখির ক্ষেত্রটি কিছুটা ভিন্ন বলেই হয়তো। কিন্তু মেধাসত্ত্ব চুরির ক্রমাগত হামলার পর আমি তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছিলাম, জাঁ ক্যুয়ে, এবং মারিও রয়ম্যান্স যথার্থ স্বীকৃতি পেলে সেটার পূর্নাঙ্গ অবদান যে অমি রহমান পিয়ালেরই জন্যই হবে সেটা '*লের কণ্ঠ' আর আলু পত্রিকা গোপন করার যত চেষ্টাই করুক না কেন, ফেসবুক আর ব্লগের কল্যাণে আমরা সবাই তা জেনে গেছি। অপদার্থ সাংবাদিক আর মেধাসত্ত্ব চোরদের দিন আর বেশিদিনের নয়। আপনার প্রতি আমার পরিপূর্ণ সমর্থন আর সহানুভূতি রইলো, পিয়াল।
পিয়াল নামের সুপরিচিত সাইবার সৈনিকটির প্রতি উৎসর্গীকৃত আজকের এই প্রবন্ধটি। আমার নিজের লেখাই চুরি গেছে অনেক। অনেকে আবার বইও লিখে ফেলেছেন আমার লেখার নানা সরঞ্জামকে পুঁজি করে; কিছু যে করতে পেরেছি তা নয়। কিন্তু আমার মূল্যহীন এলেবেলে লেখাগুলোর চেয়ে আপনার লেখা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, অনেক দামী। আপনার জন্য কিছু না করতে পারলেও অন্ততঃ পাশে আছি। ]
জোয়ান বায়েজের প্রতি ভালবাসা আমার খুব ছোটবেলা থেকে। ক্লাস সিক্স বা সেভেনে পড়ি। আমাদের বাসায় একটা গ্রামোফোনের লং প্লে রেকর্ড ছিলো, সেখানে একটা গান ছিল ব্যাঙ্কস অব দ্য ওহাইও (Banks Of The Ohio) নামে। গান টান যে তখন খুব একটা ভাল বুঝতাম তা নয়। ইংরেজি গান তো আরো নয়। কিন্তু তার মধ্যেও এই ব্যাঙ্কস অব দ্য ওহাইও গানটা যখনই বাসায় বাজতো তন্ময় হয়ে শুনতাম, হয়তো কান্ট্রি টিউনটার জন্য, আর হয়তো গানের কথাগুলোর জন্য –
httpv://
সেই থেকে শুরু। আমি যেখানে বড় হয়েছি – সেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোড এলাকা। আমাদের সময় আমাদের বন্ধুদের একটা বাতিক ছিলো রাস্তায় আড্ডা মারার ফাঁকে ফাঁকে গিটার বাজানো। কত ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে উদয়নের সামনে ব্রিটিশ কাউন্সিলের রাস্তায় আমার বন্ধুদের গীটার শুনে কাটিয়েছি, আর রাত করে বাড়ি ফিরে মা বাবার বকা খেয়েছি, তার ইয়ত্তা নেই। রাস্তার ধারে গীটার বাজানো বন্ধুদের অনেকেই এখন, মাইলস, ফিডব্যাক, ফিলিংস, এলারবি, আর্ক, অর্থহীন ব্যান্ডে গিটার বাজায়, কেউ কেউ সোলো আর্টিস্ট হিসেবেও অনেক নাম করেছে। কেউ বা আবার পরবর্তী জীবনে গিটার টিটার ফেলে অন্য পেশায় চলে গেছে। একটা বন্ধু ছিলো প্রতীক নামে, খুব সম্ভাবনাময় গিটারিস্ট ছিলো। পরে আর গান বাজনার সাথে জড়িত না থেকে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলো পদার্থবিদ্যা পড়তে। তার বাসায় ছিলো যত রাজ্যের ‘পুরোনো দিনের’ ইংরেজি গানের সংগ্রহ। তার কাছেই জোয়ান বায়েজের ‘ডোনা ডোনা’ নামের এই অপূর্ব গানটা শুনি । গানের থিমটা অসাধারণ – জবাই হয়ে যাবার আগে একটি হতভাগ্য বাছুরের মনের ভাবনা নিয়ে গান এটি।
httpv://
Calves are easily bound and slaughtered
Never knowing the reason why.
But whoever treasures freedom,
Like the swallow has learned to fly.
এই শিল্পীকে নিয়ে জানার আগ্রহ আমার বেড়ে চললো। জানলাম জোয়ান সেই ষাট-সত্তুর দশকের শিল্পী। অ্যাকোস্টিক গীটার হাতে নিয়ে গান গাইতেন তিনি। গাইতেন মানবতার গান, দিন বদলের গান। অনেকটা আজ যেমন বাংলায় গান করেন আমাদের সায়ান, লোপামুদ্রা কিংবা মৌসুমি ভৌমিকেরা। চোখ মুদে রোমান্টিক গান-শোনা আর বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ‘সখি, ভাবনা কাহারে বলে’ টাইপের ন্যাকা ন্যাকা গানের ভুবন থেকে যেমন টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে এসেছেন সুমন চট্টোপাধ্যায় (কবীর সুমন), নচিকেতা, অঞ্জন, মৌসুমি ভৌমিকেরা গত নব্বইয়ের দশকের শুরুতে, সূচনা করেছিলেন জীবনমুখী গানের ধারা – ঠিক সেই ব্যাপারটাই করেছিলেন জোয়ান বায়েজ আর বব ডিলান পশ্চিমা জগতে, তবে বহু আগে – সেই ষাট সত্তুরের দশকেই।
বব ডিলানের সাথে জোয়ান বায়েজ (১৯৬৩)
বব ডিলানের কথা বললাম কারণ সত্তুরের দশকের ব্যতিক্রমী শিল্পী বব ডিলানকে কমবেশি আমরা অনেকেই চিনি। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানি না যে অখ্যাত বব ডিলানকে মূলতঃ পরিচিত করে তুলেছিলেন জোয়ান বায়েজই। বায়াজের তখন প্রথম এলবাম বেরিয়ে গেছে, সঙ্গীত জগতে মোটামুটি পরিচিত হয়ে উঠেছেন, ঠিক এসময় নিউইয়র্ক সিটির গ্রিনউইচ গ্রামে ডিলানের সাথে পরিচয় হয় বায়েজের। গড়ে উঠে তাঁদের মধ্যে সখ্যতা, আর কিছুটা অন্তরঙ্গতাও। তারা দুজনে যাট এবং সত্তুরের দশকে বহু জায়গায় একসাথে কনসার্ট করেছেন, দেশ ভ্রমণ করেছন, গেয়েছেন ‘উই শ্যাল ওভারকাম’ কিংবা ‘ব্লোয়িং ইন দ্য উইন্ড’-এর মতো চির-সবুজ জনপ্রিয় গানগুলো। আমার নিজের বব ডিলানের ভার্শনটির চেয়ে বেশি ভাল লাগে জোয়ান বায়েজের একক কণ্ঠে গাওয়া গানটিই -
httpv://
কিন্তু আমি যেটা তখনো জানতাম না সেটা হল, বাংলাদেশের সাথে এই শিল্পীর আত্মিক যোগাযোগের ব্যাপারটা। জানলাম হঠাৎ করেই তার বিখ্যাত ‘সং অব বাংলাদেশ’ গানটি শোনার পর। সেটা আবার প্রথম শুনি আমি আমার বন্ধু নাসেরের বাসায়। এ গানটিই আমার আজকের প্রবন্ধের আলেখ্য। তবে গানটি নিয়ে কোন ধরণের আলোচনায় যাবার আগে, কিংবা গানটির গভীরে যাওয়ার আগে অবশ্যই আগে শুনে নেয়া দরকার। একবার নয়, কয়েকবার করে -
httpv://
জোয়ান বায়াজের সেই বিখ্যাত ‘সং অব বাংলাদেশ’ , যে গানটি গেয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের পাশে এসে।
১৯৭১ সালে জোয়ান বায়েজের বয়স সবে ত্রিশ ছুঁয়েছে। গীটার বাজিয়ে নানা জায়গায় গান করছেন তিনি। ঠিক সে সময় আরেক গোলার্ধে বাংলাদেশ (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান) নামের ছোট একটি দেশে ঘটে চলেছে শতাব্দীর বড় গণহত্যা। ২৫ শে মার্চের সেই ভয়াল গণহত্যার খবর জোয়ানের কানে কোনভাবে পৌঁছেছে। ব্যথিত হয় উঠলো এই শিল্পীর মন। তিনি বাঁধলেন তার অবিস্মরণীয় গানটি, কথায় আর সুরে এখনো আমার শোনা অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি গান।
জোয়ানের গানটি শুরুই হয়েছে এভাবে –
Bangladesh, Bangladesh
Bangladesh, Bangladesh
When the sun sinks in the west
Die a million people of the Bangladesh …
২৫ শে মার্চের রাতে ইকবাল হলের ছাত্ররা প্রতিদিনের কাজ কর্ম সেরে নিজেদের রুমে ঘুমাচ্ছে, কেউ বা করছিলো ঘুমানোর পায়তারা, ঠিক তখনই ‘সুসভ্য’ পাকিস্তান বাহিনী আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট এম-২৪ ওয়ার্ল্ড ওয়ার ট্যাঙ্ক, কামান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ঘুমন্ত ছাত্রদের উপর। শুরু হল ইতিহাসের করুণ-তম অধ্যায়, রচিত হল বাংলাদেশের রক্তাক্ত স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রচ্ছদপট। জোয়ান লিখলেন –
“..And the students at the university
Asleep at night quite peacefully
The soldiers came and shot them in their beds
And terror took the dorm awakening shrieks of dread
And silent frozen forms and pillows drenched in red…”
রাত সাড়ে ১১টায় ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হল হনন-উদ্যত পাকিস্তান সেনাবাহিনী। ছড়িয়ে পড়লো শহরময়, বিশেষতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে গর্জে উঠলো রাইফেল, মেশিন গান আর মর্টার। পাকিস্তানী বাহিনী সে রাতে ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি অধিকার করে সেটাকে ইকবাল হল আর জগন্নাথ হলের দিকে গোলা নিক্ষেপের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছিলো। এর কারণ আছে। একাত্তুরের মার্চ মাসের উত্তাল সময়গুলোতে ইকবাল হল ছিলো স্বাধীন বাংলা ছাত্রসমাজের মুল চারণভূমি। ছাত্রদের গণআন্দোলনের দিক নির্দেশনা আর স্ট্র্যাটিজি আসতো এই হলের কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতাদের কাছ থেকেই। কাজেই পাক-বাহিনীর মূল আক্রোশই ছিলো এই হলটিকে ঘিরে। মধ্যরাতের আগেই অতর্কিত নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো পাকসেনারা। গোলার আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলো ছাত্রাবাসের দেয়াল। চললো বর্বরোচিত নিধনযজ্ঞ আর ধ্বংসের উন্মত্ত তাণ্ডব। হতচকিত ছাত্ররা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে। ব্রিটিশ কাউন্সিল এলাকার রাজপথ, অলিগলি, ফুটপাত, খেলার মাঠ, ক্যাম্পাস সর্বত্রই মৃত্যুর করাল গ্রাস। অসহায় মানুষের কান্নায়, চিৎকারে, হাহাকারের শব্দে ভারী হয়ে এলো শহরের আকাশ। সেই কান্না ছাপিয়ে তখন আকাশে কেবলই মুহুমুর্হু আগুনের লেলিহান শিখা, শেল আর বারুদের তাজা গন্ধ। মধ্যরাতের ঢাকা হয়ে উঠলো যেন লাশের শহর। জোয়ান বায়েজ তার গানে লিখলেন –
The story of Bangladesh
Is an ancient one again made fresh
By blind men who carry out commands
Which flow out of the laws upon which nation stands
Which is to sacrifice a people for a land …
পাক-বাহিনীর ঘন্টাখানেকের তাণ্ডবেই ইকবাল হলের প্রায় দুইশ জন ছাত্র মারা যায়। সে রাতের ভয়াবহতা যে ঠিক কত বেশি ছিলো তা কিছুটা হলেও বোঝা যায় এর পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের একটি সাক্ষ্য পড়লেই -
“ইকবাল হলের সামনে কী যে হয়েছিলো তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। রাস্তা ঘাটে চারিদিকে হত্যাযজ্ঞের ছাপ, বস্তিতে আগুন জ্বলছে। বাড়ির সামনে পার্ক করা গাড়িতে আগুন। স্তূপ করা লাশ নিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে নীলক্ষেতের রেল গেট পেট্রোল-পাম্পের সামনে। গোলা বারুদ, ধোঁয়া আর আগুনের লেলিহান শিখা আক্ষরিক অর্থেই পুরো এলাকাটাকে নরককুণ্ডে পরিণত করে ফেলেছিল যেন। কিছু দূর পর পরই বিল্ডিং এর দেয়ালে গোলাগুলির চিহ্ন। এই সব ভয়াবহতার মধ্যে আমরা আমাদের পরিবার আর হলের ছাত্ররা জীবনের আশা একেবারে ছেড়েই দিয়েছিলাম, কেবল মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া আমাদের সামনে কোন পথই খোলা ছিলো না”।
এমন কী ঘটনার দুই দিন পরেও সারি সারি লাশ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে। দেখা গেছে লাশ ময়লা পানিতে ভাসতে। লাশের সারি, রক্তাক্ত করিডোর, গলার আঘাতে ছিন্নভিন্ন দেয়াল, রক্তাক্ত রাস্তা ঘাট, গুমোট গন্ধ দেখে যে কেউই বুঝবে কী ধকল সহ্য করেছে ২৫ শে মার্চের কাল রাত্রিতে ঢাকাবাসীরা। আমাদের মুক্তমনা সদস্য আবুল কাশেম সে সময় বুয়েটের (তখনকার EPUET)তরুণ ছাত্র। থাকতেন শেরে বাংলা হলে। তাঁর স্মৃতিচারণা মূলক একটি লেখায় ফুটে উঠেছে এর পরদিনের ঢাকা শহরে জমে থাকা ভয়াবহতার নগ্ন-রূপ –
“… The scene I saw in Iqbal Hall was beyond any description. The whole area was like a battlefield. I knew that DUCSU VP Tofail Ahmed used to live there. There were holes on the walls created by mortar shells. Those holes were visible from afar. When I arrived at the playground of the hall, I saw about 30 dead bodies all lined up for display to the public. Many of the dead bodies were beyond any recognition due to innumerable bullet holes on their faces. That was a gruesome sight. Many people started crying. My friend Jafar used to live in Iqbal hall. I did not see his dead body. Later, I learnt that his dead body was found in his bed. Needless to say, the displayed corpses were merely a small fraction of the students when Pak army had murdered in Iqbal Hall on that dreadful night.”
গণহত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি পাকিস্তানী বাহিনী, গণহত্যার পর দিন থেকেই পাকবাহিনী চেয়েছে গণহত্যার সমস্ত চিহ্নগুলো বহির্বিশ্ব থেকে গোপন করতে। তারা বলেছে, পাকিস্তানী বাহিনী ‘সুসভ্য’ বাহিনী, তারা কখনোই এভাবে গণহত্যা করে না। অথচ, ঢাকা শহরের রাস্তায়, আকাশে, বাতাসে ক্রন্দন আর হাহাকারের ছাপ, ছিন্ন ভিন্ন চারিদিক, সব জায়গায় গণহত্যার সুস্পষ্ট নিদর্শন। এই ধ্বংসযজ্ঞ আর রক্তের দাগগুলো কীসের আলামত তাহলে? এগুলো নাকি কিছু বোকা গাধা ছাত্রদের স্বেচ্ছায় ঢেলে দেয়া রুধির ! জোয়ানের গানে তারই রূপকাশ্রিত বর্ণনা –
Did you read about the army officer’s plea
For donor’s blood? It was given willingly
By boys who took the needles in their veins
And from their bodies every drop of blood was drained
No time to comprehend and there was little pain …
দিন দুনিয়ার হাল হকিকত জানা জোয়ান তখনই জানতেন যে একাত্তুরের মুক্তিযুদ্ধ কেবল যুদ্ধের ময়দানেই হচ্ছে না, সরাসরি যুদ্ধের পাশাপাশি এসেছে সাধারণ মানুষ, বুদ্ধিজীবী, নারী, কিংবা মায়েদের সর্বাত্মক আত্মত্যাগ। এর মাঝে মিলে মিশে আছে বীরাঙ্গনাদের উদাস দৃষ্টিও। তার গানে এভাবেই উঠে আসে যেন যুদ্ধের বাস্তব এক চলচ্চিত্র –
Once again we stand aside
And watch the families crucified
See a teenage mother’s vacant eyes
As she watches her feeble baby try
To fight the monsoon rains…
১৯৭১ সালে বাংলাদেশের আপামর জনগণ যখন দেশের জন্য যুদ্ধ করছে, লড়ছে না-পাক বাহিনীর হাত থেকে প্রিয় দেশ-মাতৃকাকে মুক্ত করতে, সে সময় ত্রিশ বছর বয়সী এক নারী শিল্পী বেছে নিয়েছিলেন যুদ্ধের এক অভিনব মাধ্যম, নিজের মতো করে। গিটার হাতে বাংলাদেশের মানুষদের উপর গণহত্যার প্রতিবাদ জানালেন তিনি। রচনা করলেন এক অমর সঙ্গীতের – SONG OF BANGLADESH। যে সঙ্গীতের চরণে চরণে মূর্ত হয়ে উঠেছিলো বাংলাদেশের ইতিহাসের অব্যক্ত বেদনা। ছাত্রদের উপর গণহত্যা, সেনাবাহিনীর তাণ্ডব, মানুষের হাহাকার, কুমারী মায়ের অসহায় দৃষ্টি, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, প্রতিরোধ সব কিছুই যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে গানটিতে –জোয়ান বায়েজের কথা আর সুরের এক স্বপ্নিল যাদুস্পর্শে । পুরো গানটিতে ২২ বার তিনি ‘বাংলাদেশ’ –এর নাম উচ্চারণ করে যুদ্ধরত একটি জাতির স্বীকৃতি দিলেন বিশ্বের দরবারে, স্বীকৃতি দিলেন মুক্তিকামী একটি জাতির, অর্ধ গোলার্ধ দূরের অচেনা অজানা একটি ছোট্ট দেশের, নাম বাংলাদেশ।
বিদেশ বিভূঁইয়ের এক শিল্পীর বাংলাদেশের প্রতি দরদের ব্যাপারটা হয়তো আমাদের জন্য অদ্ভুত মনে হবে, কিন্তু জোয়ানের জন্য তা ছিলো না কখনোই। তিনি সব সময়ই ছিলেন সংগ্রামী। সংগ্রামের প্রেরণা পেয়েছিলেন সেই ছোটবেলাতেই, তার পরিবারের কাছ থেকে। তার বাবা আলবার্ট বায়েজ ছিলেন খুব বিখ্যাত পদার্থবিদ, এমআইটির অধ্যাপক ছিলেন অনেকদিন। তাঁর আবিষ্কৃত এক্স রে ডিফ্রেকশন মাইক্রোস্কোপ এখনো মেডিকেলের জগতে ব্যবহৃত হয়। অথচ যখন এই বিখ্যাত পদার্থবিদকে ম্যানহ্যাটন প্রোজেক্টে কাজ কাজ করার জন্য তাকে অনুরোধ করা হয়েছিলো তিনি পারমাণবিক বোমা তৈরির প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানান। এমন কি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দেওয়া প্রতিরক্ষা প্রকল্পের লোভনীয় চাকুরী কিংবা পুরস্কারকেও হেলায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি তখন। বাবার এই আত্মত্যাগ, ঋজু মনোভাব খুব নাড়া দিয়েছিলো ছোট্ট জোয়ানের মনে। বড় হয়ে তিনিও তাই দাঁড়াতে পেরেছিলেন অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে। তিনি গান গাওয়ার পাশাপাশি ক্রমশ: বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে উঠেন। ষাটের দশকে মার্টিন লুথার কিং এর সাথে মিলে ‘সিভিল রাইটস মুভমেন্ট’এর সাথে জড়িত হন, জড়িত হন ‘ফ্রি-স্পিচ মুভমেন্টের’ সাথেও। সেখানেই তিনি পরিবেশন করেন তার বিখ্যাত গান ‘উই শ্যাল ওভারকাম সাম ডে’ বা ‘আমরা করব জয়, একদিন’ গানটি –
httpv://
জোয়ান আজীবন যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী সৈনিক। আজও তিনি ইরাকের উপর মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একই ভাবে সোচ্চার। ২০০৩ সালে ৬২ বছর বয়সে সানফ্রান্সিস্কোতে কনসার্ট করেছিলেন ইরাক যুদ্ধের অবসান চেয়ে। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে, শান্তি ও মানবাধিকারের স্বপক্ষে আজও তিনি এক জোরালো কণ্ঠস্বর। তিনি সমকামী, রূপান্তরকামী সংখ্যালঘু মানুষদের অধিকারের ব্যাপারেও গান গেয়েছেন অনেক, এমনকি তার ‘উই শ্যাল ওভারকাম’ গানটি একটু পরিবর্তন করে সংখ্যালঘুদের অধিকারের দাবীতে পোস্ট করেছেন ইউটিউবে ২০০৯ সালে। তবে, ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ ছিলো সবচেয়ে প্রকট। যুদ্ধের প্রতিবাদ করতে গিয়ে দুই দুইবার গ্রেফতার হন ১৯৬৭ সালে। তিনি এসময় মার্কিন সরকারকে ট্যাক্স দিতেও অস্বীকার করেন। তিনি রেভেনিউ সার্ভিসের কাছে পাঠানো একটি চিঠিতে বলেন –
“I do not believe in war. I do not believe in the weapons of war … and I am not going to volunteer 60% of my year’s income tax that goes to armaments.”
তিনি বাংলাদেশের গণহত্যার খবরে বিচলিত হবেন না তো কে হবেন? জোয়ান হয়েছিলেন। সুদূর আমেরিকায় বসে ভেবেছিলেন আমাদের কথা, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির কথা। লিখেছিলেন একটি অসাধারণ গান, যেটি প্রস্তুত করা হয়েছিলো ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে ১৯৭১ সালের অগাস্ট মাসে অনুষ্ঠিত ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’ এর জন্য। যদিও ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’ এ জর্জ হ্যারিসনের গাওয়া বাংলাদেশ গানটির কথা অনেকেই জানেন, কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে জোয়ান বায়েজের গানটি সেভাবে পরিচিতি পায়নি। জর্জ হ্যারিসনের গানটির কথা মাথায় রেখেও আমার কাছে জোয়ান বায়েজের এই বিষাদময় সুরেলো গানটিই বেশি প্রিয় ছিলো সবসময়ই। আজো – প্রতিবার যখনই গানটি শুনি চোখ ভিজে উঠতে চায়, বুকের গহীন কোনে কোথায় যেন বেজে উঠে রিনি রিনি এক ব্যথার সুর। ঠিক যেমন প্রতিবছর একুশের সকালে ‘আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো’ গানটা শুনলেও যে অনুভূতি হয় মনে!
জোয়ানের পুরো গানটি এখানে -
SONG OF BANGLADESH
-Joan Baez.
Bangladesh, Bangladesh
Bangladesh, Bangladesh
When the sun sinks in the west
Die a million people of the Bangladesh
The story of Bangladesh
Is an ancient one again made fresh
By blind men who carry out commands
Which flow out of the laws upon which nation stands
Which is to sacrifice a people for a land
Bangladesh, Bangladesh
Bangladesh, Bangladesh
When the sun sinks in the west
Die a million people of the Bangladesh
Once again we stand aside
And watch the families crucified
See a teenage mother’s vacant eyes
As she watches her feeble baby try
To fight the monsoon rains and the cholera flies
And the students at the university
Asleep at night quite peacefully
The soldiers came and shot them in their beds
And terror took the dorm awakening shrieks of dread
And silent frozen forms and pillows drenched in red
Bangladesh, Bangladesh
Bangladesh, Bangladesh
When the sun sinks in the west
Die a million people of the Bangladesh
Did you read about the army officer’s plea
For donor’s blood? It was given willingly
By boys who took the needles in their veins
And from their bodies every drop of blood was drained
No time to comprehend and there was little pain
And so the story of Bangladesh
Is an ancient one again made fresh
By all who carry out commands
Which flow out of the laws upon which nations stand
Which say to sacrifice a people for a land
Bangladesh, Bangladesh
Bangladesh, Bangladesh
When the sun sinks in the west
Die a million people of the Bangladesh
সম্প্রতি বাংলাদেশের বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী বাবু জোয়ান বায়েজের এ বিখ্যাত গানটি বাংলায় রূপান্তর করেছেন, এবং গেয়েছেন। বাবুর গাওয়া গানের কথাগুলো এরকমের –
বাংলাদেশ বাংলাদেশ
বাংলাদেশ বাংলাদেশ
অস্তাচলে যেখানে দিন শেষ,
লাখো প্রাণের রক্তে রাঙা দেশ
নতুন ইতিহাসে পুরানো সেই গল্প ফিরে আসে;
অন্ধ যারা তাদের হাতে ভার, দেশের সব বিধান বাঁচাবার,
মারছে তাই মানুষ বেশুমার।
বাংলাদেশ বাংলাদেশ
বাংলাদেশ বাংলাদেশ।।
বাংলাদেশ বাংলাদেশ
বাংলাদেশ বাংলাদেশ
অস্তাচলে যেখানে দিন শেষ,
লাখো প্রাণের রক্তে রাঙা দেশ
সবাই এসো দাঁড়াও হাতে হাত, মরছে দেখো মানুষ দিনরাত
কিশোরী মা দুচোখ ভেসে যায়, শিশুটি তার ধুকছে অসহায়-
বৃষ্টি আর ভীষণ কলেরায়।
রাতে যখন ঘুমের অবকাশ, পাকসেনারা ছাত্রাবাসে ত্রাস,
ছড়িয়ে পড়ে ভয়ের জটাজাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় মহাকাল,
শরীর হিম, বালিশ লালে লাল।
বাংলাদেশ বাংলাদেশ
বাংলাদেশ বাংলাদেশ।।
রক্ত চাই রক্তদাতা চাই,
বেরাতে এই আর্তি শুনো নাই
তরুণ যারা রক্ত দিতে হয়
বেদনাহীন সহজ নির্ভয়
দেশ ছাপিয়ে রক্ত নদী বয়।
বাংলা নামের দেশের ইতিহাসে পুরানো সেই গল্প ফিরে আসে
অন্ধ যারা তাদের হাতে ভার, দেশের সব বিধান বাঁচাবার,
মারছে তাই মানুষ বেশুমার।
বাংলাদেশ বাংলাদেশ
বাংলাদেশ বাংলাদেশ।।
বাবুর গানটি ইউটিউবে দেখা যাবে এখান থেকে -
httpv://
২০০৪ সালে আমি জোয়ান বায়েজের উপর ইংরেজিতে একটি লেখা লিখি, ‘Joan Baez and our Liberation War’ শিরোনামে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে জোয়ানের অবদান উল্লেখ করে একমাত্র লেখা ছিলো সেটি তখন ইন্টারনেটে। পরে সেটাকেই আরেকটু পরিবর্তিত করে প্রকাশ করি মুক্তমনায় ২০০৬ সালে, লেখাটি দেখা যাবে এখানে। আমার গর্ব হয় এই দেখে যে, ‘Joan Baez Bangladesh’ সার্চ দিলে লেখাটা সব সময়ই গুগলের প্রথম দিকেই থাকে। আমি আনন্দিত যে, আমার লেখাটি প্রকাশের পর অনেকেই জোয়ানের ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছেন, কেউ কেউ আমার লেখাটিকে রেফারেন্স হিসেবে নিয়ে ব্লগও লিখেছেন (যেমন, যূঁথীর একটি ব্লগ আছে এখানে)। দৈনিক সংবাদপত্রেও জোয়ানকে নিয়ে খবর আসছে ( যেমন দৈনিক সমকালের একটি লেখা এখানে ) । এগুলো দেখলে আমি উচ্ছ্বসিত হই, বাঙালি তবে বিস্মৃতি-পরায়ণ অকৃতজ্ঞ জাতি নয়। উপকারের মর্যাদা দিতে জানে। তারপরেও মনের গহীনে একটু খচখচানি তো ছিলোই – ব্লগে কিংবা বাংলা সংবাদে জোয়ান এসেছেন বটে, সরকারীভাবে জোয়ানকে তো স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ২০০৬ সালের লেখাটি আমি তাই শেষ করেছিলাম এই বলে -
প্রিয় পাঠক, একটি বার চিন্তা করুন তো – কত বছর আমাদের লেগেছে বীর প্রতীক সিতারা বেগম, বীর প্রতীক তারামন বিবি আর বীর প্রতীক ওডারল্যাণ্ডকে খুঁজে পেতে। সময় পেরিয়ে যাবার আগেই কি জোয়ান বায়েজকে আমাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মাননা জানানো উচিৎ নয়?
আমার এই ছোট্ট চাওয়াটি বোধ হয় অবশেষে সফল হতে চলেছে, মুক্তিযুদ্ধের চল্লিশ বছর পর। বিডি নিউজের গত ১২ ডিসেম্বরের খবরে দেখলাম, সরকারীভাবে ১২৭ জন বিদেশীকে সম্মাননা দেবার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে আমার প্রিয় শিল্পী জোয়ান বায়েজের নামও। খবরে প্রকাশ –
মুক্তিযুদ্ধে অবদান: সম্মাননা পাবেন ১২৭ বিদেশি
Mon, Dec 12th, 2011
ঢাকা, ডিসেম্বর ১২ (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম)- মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য সম্মাননা দিতে বিভিন্ন দেশের ১২৭ জন নাগরিকের নাম চূড়ান্ত করেছে সরকার।
সোমবার মন্ত্রীসভার বৈঠকে এ নামগুলো চূড়ান্ত হয়। আগামী বছরের শুরুতেই এই সম্মাননা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এ বি তাজুল ইসলাম।
সম্মাননা জানানোর তালিকায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী, কবি অ্যালেন গিনসবার্গ, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, সঙ্গীতশিল্পী জর্জ হ্যারিসন, জোয়ান বায়েজের নাম রয়েছে।
এ আমার জন্য এক বিশাল পাওয়া। মনে হচ্ছে অনেকদিন পরে যেন আমার ভাল ঘুম হবে, আনন্দে কাটবে এবারের বিজয় দিবসটি। এই বিজয়ের মাসেই তাকে সম্মাননা দেয়ার কথা; তবে শোনা যাচ্ছে প্রস্তুতির অভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা বিদেশীদের সম্মাননা নাকি নাও দেয়া হতে পারে এই ডিসেম্বরে। এবার যদি তাঁকে সম্মাননা নাও দেয়া হয়, নিশ্চয় দেয়া হবে সামনে কোন সময়। রাষ্ট্রীয়ভাবে যখন উদ্যোগ নেয়া হয়েই গেছে, তখন আমি খুবই আশাবাদী। খুবই প্রয়োজন ছিলো এই মহতী উদ্যোগের, আমরা তো জানিই – ‘দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ’।
সত্তুর বছরের চির সবুজ এ শিল্পীকে জানাই আমার অভিনন্দন, আর যারা যারা তাকে সম্মানিত করার জন্য প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন, সরকারী কিংবা বেসরকারীভাবে, সবাইকে আমার এবং মুক্তমনার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ।
সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা!
_______________________________
http://mukto-mona.com/bangla_blog/?attachment_id=20695
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:১৯582774
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:১৯582774- রক্তে ভেজা নীল আকাশঃ ০১-শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন
লিখেছেনঃ অনিমেষ রহমান (তারিখঃ শনিবার, ১৫/১২/২০১২ - ১৮:২৮)
_____________________________________________________
একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হতে চলেছে_
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্য,হে স্বাধীনতা।
-কবি শামসুর রাহমান
বাংলাদেশের নীল আকাশ সেদিন লাল হয়ে গিয়েছিলো হায়নার অস্ত্রের আঘাতে। ঝরে ঝরে পড়ছিলো লালরক্ত বাংলার জমিনে।টেকনাফ থেকে তেতুলিয়াতে রক্ত ঝরতে ঝরতে সেদিন মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকার উপকন্ঠে।চারদিকে চাপা উল্লাসের পদধ্বনি। ঠিক সেই মুহুর্তে সংগঠিত হলো ইতিহাসের নির্মম হত্যাযজ্ঞ।
পরাজয় নিশ্চিত জেনে পরাজিত পাকিস্তানী বাহিনী নবউদীয়মান জাতিকে চিরতরে স্তব্দ করে দিতে তাদের এদেশীয় জামাতি দোসর-রাজাকার, আল বদর, আল-শামস এবং বিহারীদের নিয়ে ঘঠিত কিলিং স্কোয়ার্ডের মাধ্যমে খুন করে দেশের শিক্ষক-সাংবাদিক-ডাক্তার সহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। যেনো বাংগালী জাতি মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। আজকে ঠিক ৪০ বছর পরে আর শাস্তি দাবী কিংবা প্রমান নিয়ে কথা বলার দরকার নেই-শুধু চেয়ে দেখি কেমন ছিলেন আমাদের জন্য প্রান দিয়ে যাওয়া সেই মানুষগুলি। যারা হারিয়ে গেলেন সেই ভয়াল ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১এ।
আজকে শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভিনের কথা লিখছি। শুনুন তাঁর একমাত্র পুত্র সুমন জাহিদের ভাষায়ঃ
আমার মা সেলিনা পারভীন। শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন। তাঁর হারিয়ে যাওয়ার কাহিনীটি আমার কাছ থেকে কোনোদিন হারিয়ে যাবে না। আমার মায়ের হারিয়ে যাওয়ার দিনটি আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ ও দুর্ভাগ্যজনক দিন।
সেদিন ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল। দেশ স্বাধীন হতে আর মাত্র তিন দিন বাকি। কোনো কোনো অঞ্চল ইতিমধ্যে মুক্ত হয়ে গেছে। আমরা তখন ছিলাম সিদ্ধেশ্বরীতে, তত্কালীন ১১৫নং নিউ সার্কুলার রোডে। আমাদের বাসায় আমরা তিনজন মানুষ- আমি, মা আর আমাদের উজির মামা। সেদিন শীতের সকালে আমরা ছাদে ছিলাম। মা আমার গায়ে তেল মাখিয়ে দিয়েছেন। একটু পর তিনি আমাকে গোসল করতে নিয়ে যাবেন। আমি ছাদে খেলাধুলা করছি আর মা একটা চেয়ার টেনে কী যেন লিখছেন। শহরে তখন কারফিউ। রাস্তায় মিলিটারি। পাকিস্তানী বাহিনীকে আত্মসমর্পণের জন্য বিমান থেকে চিঠি ফেলা হচ্ছে।
হঠাত্ দূরে একটা গাড়ির আওয়াজ হলো। আমাদের বাসার উল্টো দিকে খান আতার বাসার সামনে E.P.R.TC-এর ফিয়াট মাইক্রোবাস ও লরি থামে। সেই বাসার প্রধান গেইট ভেঙে ভিতরে ঢুকে গেল কিছু লোক। আমরা তিনজন ছাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে এই দৃশ্যটা দেখলাম।
কিছুক্ষণ পর মা আমাকে গোসল করানোর জন্য নিচে নিয়ে আসেন। গোসলের পর আমি আবার ছাদে চলে যাই। আর মা যান রান্না করতে। ছাদে আমার সঙ্গে উজির মামাও ছিলেন।
এরপর আবার গাড়ির শব্দ। এবার একটি গাড়ি এসে থামে আমাদের বাসার সামনে। ছাদে দাঁড়িয়ে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে আমরা দেখি কয়েকজন লোক আমাদের বাসায় ঢুকছে। তাদের সবাই একই রঙের পোশাক পরা ও মুখ রুমাল দিয়ে ঢাকা। এরা বাসার প্রধান লোহার কলাপসিবল দরজার কড়া নাড়ছে। আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের এক ভদ্রলোক বের হয়ে কলাপসিবল গেইট খুলে দেয়। গাড়িতে করে আসা লোকগুলো ভদ্রলোকের কাছে সেলিনা পারভীনের পরিচয় জানতে চায়। ভদ্রলোক আমাদের ফ্ল্যাটটি দেখিয়ে দেন। ভদ্রলোককে ঘরে চলে যেতে বলে লোকগুলো আমাদের ফ্ল্যাটে এসে কড়া নাড়ে। মা দরজা খুলে দেন। লোকগুলো মার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয় এবং বাসায় কে কে থাকে তাও জেনে নেয়। এ সময় মার সাথে লোকগুলোর বেশ কিছু কথা হয়। আমি আর উজির মামা ততক্ষণে সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা উঁকি দিলে ওরা দেখে ফেলে। আমাদের দিকে বন্দুক তাক করে। আমি ও উজির মামা ভয় পাই। মা আমাদের ডেকে নিয়ে লোকগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। আমি মার কাছে চলে আসি। এরপর মাকে তাদের সাথে যেতে বলে লোকগুলো।
মা লোকগুলোকে বলেন, 'বাইরে তো কারফিউ। এখন যাব কীভাবে?' লোকগুলো বলে, 'আমাদের সাথে গাড়ি আছে। তাছাড়া আমাদের সাথে কারফিউ পাশও আছে। কোনো সমস্যা হবে না।' ওরা নাছোড়বান্দা, আম্মাকে নিয়ে যাবেই। মা তখন বলেন, 'ঠিক আছে। আপনারা অপেক্ষা করুন। আমি শাড়ি বদল করে আসি।' ওরা বাধা দেয়। বলে, 'দরকার নেই। গাড়িতে করে যাবেন আবার গাড়িতে করেই ফিরে আসবেন।' আমিও তখন মার সাথে যেতে চাই। কিন্তু লোকগুলো আমাকে ধমক দিয়ে বলে, 'বাচ্চা লোক নেহি জায়েগা।' উজির মামা কিছু বলতে চাইলে তাঁকেও বলে, 'বাড়াবাড়ি করবেন না।'
আমি তখন মার খুব কাছে। তাঁর হাত ধরে আছি। মা আমার মাথায় হাত বুলান। তিনি আমাকে বলেন, 'সুমন তুমি মামার সাথে খেয়ে নিও। আমি যাব আর চলে আসব।' এই ছিল আমার জীবনে মার কাছ থেকে শোনা শেষ কথা।
এভাবেই সেদিন অনেকেই তাঁর প্রিয় মানুষদের শেষ কথা বলে গেছেন বলেই আজকে আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশ। লাখো বাঙ্গালী যুদ্ধের ময়দানে আর সেলিনা পারভিনের মতো মানুষেরা অবরুদ্ধ ঢাকায় বিভিন্নভাবে আমাদের মুক্তির যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন।শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন কিভাবে যুক্ত ছিলেন আমাদের মুক্তির লড়াইয়েঃ
১৯৬৯-এর রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তাল বাংলাদেশ৷ নিজেও শরিক হন গণঅভ্যুত্থানের আন্দোলন কর্মকাণ্ডে৷ ছেলেকে সঙ্গে নিয়েই বেরিয়ে পড়তেন '৬৯-এর ২১ ফেব্রুয়ারি পল্টনের জনসভায় বা শহীদ মিনার থেকে বের হওয়া নারীদের মিছিলে যোগ দিতে৷ শরিক হতেন বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদে আর সভায়ও৷ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার প্রমুখদের সাথে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে সমাজতন্ত্রের প্রতিও আস্থাশীল হয়ে পড়েন তিনি৷ এরই মধ্যে শুরু হলো ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ৷ মুক্তিযুদ্ধের সময় সেলিনা পারভীন ঢাকায় ছিলেন৷ তাঁর বাসায় মাঝে মাঝে রাত হলে কয়েকজন তরুণ আসতেন৷ খাওয়া-দাওয়া করে চলে যাওয়ার আগে এরা সেলিনা পারভীনের কাছ থেকে সংগৃহীত ঔষধ, কাপড় আর অর্থ নিয়ে যেতেন৷ শিলালিপির বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়েই তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করতেন৷ এই তরুণদের সকলেই ছিলেন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা৷
চারিদিকে তখন চলছে আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ, প্রতিরোধ৷ চারপাশে শুধু বুলেটের শব্দ আর বারুদের গন্ধ, চিৎকার, গোঙানি, রক্তস্রোত আর মৃত্যু৷ এরই মাঝে ললনা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম৷ শিলালিপির উপরও নেমে আসে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর খড়্গ৷ হাসেম খানের প্রচ্ছদ করা একটি শিলালিপির প্রকাশিতব্য সংখ্যা নিষিদ্ধ করে দেয় পাকিস্তান সরকার৷ পরে অবশ্য প্রকাশের অনুমতি মিললো তবে শর্ত হলো নতুনভাবে সাজাতে হবে৷ সেলিনা পারভীন বরাবরের মতো প্রচ্ছদ না নিয়ে তাঁর ভাইয়ের ছেলের ছবি দিয়ে প্রচ্ছদ করে আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে শিলালিপির সর্বশেষ সংখ্যা বের করেন৷ কিন্তু এর আগের সংখ্যার জন্যই সেলিনা পারভীন পাকিস্তানী ও তাদের দালালদের নজরে পড়ে যান৷ যেটাতে ছিল দেশ বরেণ্য বুদ্ধীজীবীদের লেখা এবং স্বাধীনতার পক্ষের লেখা৷ তাই কাল হলো৷ শিলালিপির আরেকটি সংখ্যা বের করার আগে নিজেই হারিয়ে গেলেন৷
১৩ ই ডিসেম্বর ধরে নিয়ে যাবার পর তাঁর মরদেহ পাওয়া যায় রায়েরবাজার বধ্যভুমিতে। যার চোয়ালে ছিলো বেয়নেটের খোঁচার দাগ আর বুকে গুলিঃ
১৮ ডিসেম্বর সেলিনা পারভীনের গুলিতে-বেয়নেটে ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া যায় রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে৷ খুব শীতকাতুড়ে সেলিনার পায়ে তখনও পড়া ছিল সাদা মোজা । এটি দেখেই তাঁকে সনাক্ত করা হয় । ১৪ ডিসেম্বর আরও অনেক বুদ্ধিজীবীর মতো পাকিস্তানের দালাল আলবদর বাহিনীর ঘৃণিত নরপশুরা সেখানেই সেলিনা পারভীনকে হত্যা করে৷ ১৮ ডিসেম্বরেই তাঁকে আজিমপুর কবরস্থানে শহীদদের জন্য সংরক্ষিত স্থানে সমাহিত করা হয়৷
সেলিনা পারভিনঃ সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি
জন্ম : সেলিনা পারভীনের জন্ম বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার ছোট কল্যাণনগর গ্রামে ১৯৩১ সালের ৩১ মার্চ। বাবা মৌলবি আবিদুর রহমান, মাতা মোসাম্মৎ সাজেদা খাতুন। শৈশবে পিতৃদত্ত নাম ছিল মনোয়ারা বেগম মনি। ১৯৫৪ সালে এফিডিয়েন্ট করে সেলিনা পারভীন নাম নেন।
শিক্ষাজীবন : ফেনী সরলা বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ১৯৪২ সালে ছাত্রজীবন বিঘ্নিত হয়। ফিরে যান গ্রামের বাড়ি ছোট কল্যাণনগরে। ১৯৪৯ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় (প্রাইভেট) অংশগ্রহণ। উত্তীর্ণ হতে পারেননি।
পরিবার : সম্ভবত ১৯৪৩ সালে তত্কালীন সামাজিক অবস্থার চাপে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে। স্বাধীনচেতা সেলিনা পারভীন সে সংসার করেননি। ১৯৪৮-এ বিবাহবিচ্ছেদ। পরে ১৯৬২ সালে বিবাহ হয় ফেনীর ছাগলনাইয়া নিবাসী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর-এর সঙ্গে। একমাত্র পুত্র সুমন জাহিদের জন্ম ১৯৬৩ সালের ৩১ মে। বিবাহবিচ্ছেদ ১৯৬৬ সালে।
কর্মজীবন : ফেনীতে ছাত্র পড়িয়ে কর্মজীবন শুরু। ১৯৫৬ সালে ঢাকায় আসেন। ১৯৫৭ সালে মিডফোর্ড (বর্তমানে সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ) হাসপাতালে নার্সিং ট্রেনিং গ্রহণ। ১৯৫৯ সালে রোকেয়া হলে মেট্রনের চাকরি। ১৯৬৬ সালে আজিমপুর বেবিহোমে শিক্ষকতা। ১৯৬৬ সালে 'সাপ্তাহিক বেগম' পত্রিকায় সম্পাদিকার সহকারী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৭ সাল থেকে আমৃত্যু 'সাপ্তাহিক ললনা'য় কাজ করেন।
পত্রিকা সম্পাদনা : 'শিলালিপি' ১৯৬৯ সাল। পত্রিকাটির প্রকাশনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব একাই পালন করতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় পত্রিকাটির প্রচ্ছদ ও অন্যান্য রচনা পাকসেনা প্রধানের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি।
শখ : ছবি আঁকা, সংগীত চর্চা, ব্লক তৈয়ারি এবং ডিজাইনের কাজেও পারদর্শী ছিলেন।
মুক্তিযুদ্ধে অবদান : ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকায় গেরিলা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সক্রিয় সহায়তা দান। মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর জীবনের কর্মকান্ডের প্রায় সমস্ত তথ্যই হারিয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যা শত্রুর জন্য ক্ষতিকর হয়েছিল।
মৃত্যু : একাত্তরের ১৩ ডিসেম্বর আলবদর বাহিনীর লোকেরা তাঁর সিদ্ধেশ্বরীর বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। ১৪ ডিসেম্বর অন্যান্য দেশ বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের সাথে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ১৮ ডিসেম্বর শহীদ সেলিনা পারভীনের দাফন হয় আজিমপুর নতুন গোরস্থানে।
আজকে চষে বেড়াই আমরা ঢাকা শহর-কেউ কেউ চষে বেড়াই সারা দুনিয়া।জীবন-জীবিকার কারনে! আমাদের স্বাধীন আকাশ করতে গিয়ে যারা চলে গেলেন অবেলায়-তাঁদের প্রতি আমাদের ঋন শেষ করতে পারবো? কিংবা জাতি হিসেবে আমাদের উত্থানে তাঁদের ত্যাগ প্রতিদিন আমাদেরকে আরো ঋনি করে দেয়। সময় হয়েছে ঋন শোধ করার-রুখে দাঁড়াই ঘাতকদের। আবারো ঐক্যবদ্ধ হই ৭১ এর চেতনায়।
জয় বাংলা!!
______________________
http://www.amarblog.com/animeshrahman/posts/156648
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:২৯582785
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:২৯582785- মার্কিন মাস্তানি -ডমিনিকান রিপাব্লিক আর একাত্তরের বাংলাদেশ
-ইরতিশাদ আহমদ
______________________________________
‘দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে’
পেশাগত কাজে গত মাসে (নভেম্বর, ২০১২) আমাকে বেশ কয়েকবার যেতে হলো ডমিনিকান রিপাব্লিকের রাজধানী সান্তো ডমিঙ্গো-তে। মায়ামি থেকে আকাশ পথে মাত্র দুইঘন্টার ফ্লাইট। দেশটা সম্পর্কে আগ্রহ জাগলো মনে। টুকটাক জেনে নিলাম ইন্টারনেট ঘেটে। যতই ঘাটি ততই মনে হয় ‘চিনি উহারে’।
দেশটা সম্পর্কে যতই নতুন নতুন তথ্য জানতে পারি, ততই মন খারাপ হয়। মন খারাপ হলেও অবাক হই না। ডমিনিকান রিপাব্লিকের ইতিহাসে যা ঘটেছে আমার জানা এই অঞ্চলের এবং ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট বিশ্বের অন্যান্য দেশের ইতিহাসের সাথে তার তেমন কোন অমিল নেই।
হিস্পানিওলা
সেই পঞ্চদশ শতকের গোড়া থেকে সাম্রাজ্যবাদের লিপ্সার শিকার ডমিনিকান রিপাব্লিকের মতো ক্যারিবিয়ান-ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বীপগুলো। হেইতির প্রতিবেশী এই দেশটা ছিল স্পেনের উপনিবেশ (১৪৯২ থেকে)। হেইতি পরে (১৬৬৮ থেকে) চলে যায় ফ্রান্সের হাতে। দুই দেশ মিলে এই অঞ্চলকে বলা হয় হিস্পানিওলা। ক্রিস্টোবাল কোলোন (ক্রিষ্টোফার কলম্বাসের স্প্যানিশ নাম) ক্যারিবিয়ান এই দ্বীপে ১৪৯২ সালে ঘাঁটি গাড়ার পরে নাম দিয়েছিলেন, লা ইসলা এস্পানোলা ইংরেজিতে যার মানে দ্য স্প্যানিশ আইল্যান্ড। সংক্ষিপ্ত হয়ে পরে এস্পানোলা এবং অবশেষে হিস্পানিওলা। এদের দূর্ভাগ্যের শুরু সেই সময় থেকে ।
কলম্বাস আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের দ্বারা নির্মিত বিশালাকৃতি দূর্গসদৃশ বাড়িগুলো এখনো বহাল তবিয়তে বিদ্যমান সান্তো ডমিঙ্গোতে। পর্যটকদের জন্য দর্শনীয় স্থান, যাদুঘর আর মহাকালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা ক্যারিবিয়ান সাগরের তীরে। ‘আলকাজার দ্যে দিয়েগো কোলোন’ নির্মিত হয়েছিল ১৫১৫ তে। ক্রিস্টোবালের ছেলে দিয়েগো কোলোন, সান্তো ডমিঙ্গোর গভর্ণর থাকাকালীন সময়ে বানিয়েছিলেন এই প্রাসাদটা।
কতশত স্থানীয় আর আফ্রিকার কালো মানুষের অশ্রু, ঘাম আর রক্তের বিনিময়ে গড়ে উঠেছে এই শহর কেউ তার হিসেব আর নেয় না এখন।
ডমিনিকান রিপাব্লিক ‘স্বাধীন’ একটা দেশ। এখন আর উপনিবেশ নয়। কিন্তু উপনিবেশ না হলেও সত্যিকার অর্থে স্বাধীন কি? এ যুগে ‘স্বাধীন দেশ কি ও কত প্রকার’ এই প্রশ্নের উত্তর খুব একটা সহজ-সরল নয়। স্বাধীন দেশ অনেক, কিন্তু ‘স্বাধীনতা’ অনেক রকমের। সম্রাট-সম্রাজ্ঞী এই দুনিয়ায় তেমন নেই আর – থাকলেও আছে প্রতীকী নখদন্তহীন দু’একজন। তবে সাম্রাজ্য আছে, আরো বেশি করে আছে সাম্রাজ্যবাদ। সেকালের উপনিবেশ আর নেই, তীব্রভাবে আছে এখনো ঔপনিবেশিকতা।
হিস্পানিওলার ইতিহাস এক শ্রেণির মানুষের বিরুদ্ধে আরেক শ্রেণির মানুষের জঘন্য নির্মমতার ইতিহাস। অর্থ আর প্রতিপত্তির লোভে মানুষ মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে আনে, আর নিজেরাও পরিণত হয় জানোয়ারে । কলম্বাসের আবিষ্কৃত সেই স্বর্গভূমিকে নরকে পরিণত করতে বেশি সময় লাগে নাই সেই মানুষরূপী জানোয়ারদের।
উপনিবেশবাদের রোগ শুধু নয়, ইউরোপিয়ানরা সাথে করে নিয়ে এসেছিলো আক্ষরিক অর্থেই রোগের জীবানু। স্থানীয় ‘তাইনো’ (Taino) নামে পরিচিত অধিবাসীরা অচিরেই আক্রান্ত হলো হাম আর গুটিবসন্তে। মারা গেলো অনেকেই। যারা বেঁচে ছিল তাদের ওপরে স্প্যানিশ হানাদারেরা চাপিয়ে দেয় বর্বর দাসপ্রথা।
চিপে রস বের করে নেয়ার পরে আখের ছিবড়া যেভাবে পরিত্যক্ত হয় হিস্পানিওলাও তাই হয়ে গেল স্প্যানিশদের কাছে। আসলেই, শেষের দিকে শুধু চিনি উৎপাদনের জন্য আঁখ চাষ আর মাড়াইয়ের কাজটাই হতো হিস্পানিওলায়। তাই ১৬৬৮তে ফ্রান্স যখ্ন হিস্পানিওলার পশ্চিমাংশ দখল করে নেয়, স্পেনীয়রা খুব একটা গা করে নি। অবশেষে ১৮০০ সালে হেইশিয়ান বিপ্লবী ভূতপূর্ব দাস তুসো ল’ওভেরতুরের নেতৃত্বে স্প্যানিশদের হটিয়ে পুরো হিস্পানিওলাকে এক দেশে রূপান্তরিত করেন। ল’ওভেরতুরের ক্ষমতা স্থায়ী হয় নি। দুইবছরের মাথায় ফ্রান্স তাঁকে ধরে নিয়ে মৃত্যুদন্ড দেয়। পরে ১৮০৪ সালে ল’ওভেরতুরের সাথী জাঁ-জাক দেসালিন-এর নেতৃত্বে হেইতি স্বাধীনতা ঘোষনা করে। হিস্পানিওলার পূর্বাংশে (ডমিনিকান রিপাব্লিক) থেকে যায় ফ্রান্সের কর্তৃত্ব। পরে এই কর্তৃত্ব ফ্রান্স ছেড়ে দেয় স্পেনের হাতে। হেইতির প্রেসিডেন্ট জাঁ-পিয়ের বয়ার ১৮২২ সালে আবারো দুই দেশকে একীভূত করেন। পরবর্তী বাইশ বছর পুরো হিস্পানিওলা হেইতির নিয়ন্ত্রণে থাকে।
ডমিনিকান রিপাব্লিক
ডমিনিকান রিপাব্লিকের স্পেনীয়রা হেইতির এই নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয় নি। হুয়ান পাবলো দুয়ার্তে-র নেতৃত্বে হেইশিয়ানদের হটিয়ে পূর্ব হিস্পানিওলার দুই-তৃতীয়াংশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে ১৮৪৪ এর সাতাশে ফেব্রুয়ারি। তখন থেকেই এই দেশের নাম ডমিনিকান রিপাব্লিক।
বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চিনি শিল্প আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে ডমিনিকান রিপাব্লিকে। আমেরিকানদের (যুক্তরাষ্ট্রের) অনেকেই তখন বিনিয়োগে আগ্রহী হয় এই শিল্পে। ১৯১৬ সালে মার্কিনীরা (US Marines) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ‘রক্ষাকর্তা’র ভুমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দখল করে নেয় ডমিনিকান রিপাব্লিক আর হেইতি। উদ্দেশ্য আর কিছু না, চিনি শিল্পের ওপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। ‘মুক্ত-বাজার অর্থনীতি’ শুধু নিজ দেশে কেন, প্রতিবেশী দেশগুলোতেও চালু না করলে কি চলে!
ডমিনিকান সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করে তাঁবেদার সরকার বসায় আমেরিকা সান্তো ডমিঙ্গোতে। জবরদখলকারী মার্কিন মেরিন কমান্ডারদের নির্দেশ মানতে বাধ্য ছিল তারা। আমেরিকার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে প্রায় আট বছর।
স্বৈরশাসক ট্রুহিও
ডমিনিকান রিপাব্লিক আর হেইতি ছেড়ে আসার আগে আমেরিকানরা তাদের বশংবদ সেনাবাহিনী গড়ে তোলে দুই দেশেই। রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র চলে যায় বেসামরিক রাজনীতিকদের হাত থেকে মিলিটারীর বন্দুকে। ডমিনিকান রিপাব্লিকে এই প্রক্রিয়ার ফলে একনায়ক হয়ে বসেন সেনাবাহিনীর কোয়ার্টারমাস্টার সাবেক টেলিগ্রাফ কেরানি রাফিয়েল লিওনিদাস ট্রুহিও। অপহরণ, নির্যাতন, খুন অবাধে চালিয়ে যেতে থাকেন ট্রুহিও তার ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার প্রয়াসে। যথারীতি, ‘বিশ্ব গণতন্ত্রের চ্যাম্পিয়ন’ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুগিয়ে যেতে থাকে মদদ। এই স্বৈরশাসক চারশো বছরের পুরনো শহর সান্তো ডমিঙ্গোর নামও বদলে দেন – নতুন নাম হয় ট্রুহিওনগর (Cuidad Trujillo বা Trujillo City)।
একটানা ত্রিশ বছর দোর্দন্ড প্রতাপে শাসন করার পরে ট্রুহিও’র দিনও শেষ হয়ে এলো। ততদিনে তার অন্ধ সমর্থকরাও বিরক্ত, বীতশ্রদ্ধ তার ওপরে। ট্রুহিওকে আর প্রয়োজন নেই আমেরিকারও। ১৯৬১-র মে মাসে তখনকার দিনে বিশ্বের অন্যতম ধনী রাষ্ট্রপ্রধান ট্রুহিও নিহত হন আততায়ীর হাতে। অনেকেই মনে করেন সিআইএ’র লম্বা হাত সক্রিয় ছিল এই হত্যাকান্ডের পেছনে। পাঠক, চেনেন নিশ্চয়ই এই করিতকর্মা মার্কিন এজেন্সীটাকে!
মার্কিন আগ্রাসন -১৯৬৫
এরপর থেকে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গেছে ডমিনিকান রিপাব্লিক। কিন্তু বেরোতে পারে নি আমেরিকার প্রভাববলয় থেকে। পারবেই বা কি করে! কয়েক বছর না যেতেই ১৯৬৫ –র এপ্রিল মাসে মার্কিন বীর পুঙ্গবেরা (প্রেসিডেন্ট জনসনের আমলে) আবারো পদধুলি দেন সান্তো ডমিঙ্গোতে। অজুহাত, সে দেশে অবস্থানরত আমেরিকানদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান।
আসল কারণ, ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে ‘আরেকটা কিউবা’র উদ্ভব ঠেকানো। সমাজতন্ত্রের জুজু আর সোভিয়েত-ভীতি তখন আমেরিকাকে ভালোই নাকানি-চুবানি খাওয়াচ্ছে।
আমেরিকার অজুহাতের অভাব নাই। সেই বাঘ আর মেষের গল্পের মতো। ‘উজানের পানি তুই ঘোলা না করলেও তোর বাপ করেছে!’ কিউবার সাহায্য নিয়ে নিজেদের পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য বিমানবন্দর নির্মান করছিলো ক্যারিবিয়ান ছোট্ট একটা দ্বীপদেশ, গ্রেনাডা। সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক ব্যবহারের জন্য বানানো হচ্ছে এই এয়ারপোর্ট, এই ভয়ে রিগ্যান প্রশাসন দখল করে নিয়েছিল গ্রেনাডা, ১৯৮৩ সালে। আমি যে বছর আমেরিকা আসি সে বছর। এর আগে আমি গ্রেনাডা নামে যে একটা দেশ আছে তাই জানতাম না। এহেন গ্রেনাডাও বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্রের লোভের থাবা থেকে নিস্তার পায় নি। পরে অবশ্য আমেরিকাই গ্রেনাডার বিমানবন্দরটা বানিয়ে দেয়, পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য! ভাবখানা যেন, ‘এয়ারপোর্ট লাগবে? আমাকে বললেই তো পারতে!’ মাস্তানি ছাড়া একে আর কি বলা যায়?
যাক, ফিরে যাই ডমিনিকান রিপাব্লিকে। ১৯৬৩-তে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত অবাধ নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন হুয়ান বশ। সমাজতন্ত্রের সমর্থক বশকে কম্যুনিস্ট আখ্যা দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নির্বাচিত হওয়ার মাত্র আট মাসের মাথায় তাঁকে এক ক্যুর মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করে ডানপন্থী সামরিক অফিসারেরা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ্য সহযোগিতায়। ক্ষমতা কুক্ষিগত করে মিলিটারি। কিন্তু আবার গোল বাধলো ১৯৬৫-তে। বশ-সমর্থকরা, তারাও মিলিটারির একটা ফ্যাকশন, কন্সটিটিউশনালিস্ট হিসাবে খ্যাত, ডানপন্থীদের হাত থেকে ক্ষমতা নিয়ে নেয় জনগণের ব্যাপক অংশের সমর্থনের জোরে। পাল্টা আঘাত হানে বশ-বিরোধীরা, সেনাবাহিনীর লয়্যালিস্ট অংশ। ব্যর্থ হয় তারা। মাঠে নামে আঙ্কল স্যাম। ১৯৬৫-র আটাশে এপ্রিল চল্লিশ হাজারেরও বেশি মার্কিন সেনা আক্রমণ করে ডমিনিকান রিপাব্লিক। এই হামলার নায়ক ছিলেন এডমিরাল জন এস. ম্যাককেইন – স্বনামধন্য রিপাব্লিকান সিনেটর ২০০৮-এর প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জন ম্যাককেইনের বাবা। পাঠক, সিনিয়র জন ম্যাককেইনের নামটা মনে রাখবেন। তার প্রসঙ্গ আবারো আসবে এই আলোচনার শেষের দিকে।
নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসন কি নতুন কিছু? সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় বসানো হয় জোকিন বালাগের-কে। বলা বাহুল্য, আমেরিকার স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি আদায় করা হয়েছিল তার কাছ থেকে আগেই।
আমেরিকার আধিপত্য
গত কয়েকদিনে স্থানীয় যাদের সাথে আমার পরিচয় হলো তাদের দুয়েকজনকে জিগ্যেস করেছিলাম ডমিনিকান রিপাব্লিকের এখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে। কিছুদিন আগে বিক্ষোভরত ছাত্রদের ওপরে গুলি চালানো হ্য়। মারা যায় একজন ছাত্র। বিক্ষোভের কারণ – সরকার দেশের সবচেয়ে নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়টাকে প্রাইভেটাইজ করতে চাচ্ছে। সোজা কথায়, ‘লাভজনক’ না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়টাকে ব্যাবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিতে চাচ্ছে।
তিনটা প্রধান রাজনৈতিক দল আছে এখন ডমিনিকান রিপাব্লিকে। জানতে চেয়েছিলাম, যে দলটা এখন ক্ষমতায় তারা কি মার্কিনপন্থী? পরিহাস মিশ্রিত সহাস্য জবাব, “কি যে বলেন! দল তিনটাই মার্কিনপন্থী”। প্রতিযোগিতা কে কত বেশি মার্কিনপন্থী তা নিয়ে। সেই জানা কাহিনি!
যে দেশটা পরিচিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নামে, তার সম্রাট নাই – তবে যেমনটি বলছিলাম – আছে সাম্রাজ্য। সেই সাম্রাজ্যের বিস্তার ল্যাটিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান, সেন্ট্রাল আমেরিকা ছাড়িয়ে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্যেও। ডমিনিকান রিপাব্লিকে আমেরিকার আধিপত্যের ইতিহাস তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, এই অঞ্চলে মার্কিন মাস্তানির একটা সাদামাটা ধারাবাহিক উদাহরণ হিসেবেই একে ধরা যেতে পারে। তাই বলছিলাম মন খারাপ হলেও আমি অবাক হই নি। কারণ, ‘চিনি উহাকে’।
ক্যারিবিয়ান-ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলোতে মার্কিন হামলার ফিরিস্তি দেখতে চাইলে গুগলে টাইপ করুন, ‘ইউএস ইনভ্যাশন্স ইন ল্যাটিন আমেরিকা’। বারো মিলিয়নের ওপরে রেজাল্ট দেখে আমারতো চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ্য করবেন, আমেরিকান সরকার-প্রভাবিত মিডিয়া এবং সরকারী মুখপত্রগুলো আমেরিকার মাস্তানিগুলোকে ইনভেশন বা আক্রমণ (invasion) বলার চেয়ে ইন্টারভেনশন বা হস্তক্ষেপ (intervention) বলাটা বেশি পছন্দ করে।
অ্যান্ডারসন পেপারস’
বিশেষ কোন কারণ ছাড়াই, মায়ামি থেকে সান্তো ডমিঙ্গো যাওয়া-আসার পথে পড়ার জন্য আমি তুলে নিয়েছিলাম যে বইটা তার নাম ‘অ্যান্ডারসন পেপারস’, জ্যাক অ্যান্ডারসন-এর লেখা। অ্যান্ডারসন ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের একজন সিন্ডিকেটেড কলামিস্ট। দেশে দেশে মার্কিন মাস্তানির কথা সবিস্তারে লিখেছেন অ্যান্ডারসন তার বইতে। ডমিনিকান রিপাব্লিকের কথা এসেছে, এসেছে বাংলাদেশের কথাও। পুলিতজার পুরষ্কার পাওয়া (১৯৭২) এই সাংবাদিককে অনেকেই ‘ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমে’র জনক মনে করেন। বিতর্কিত এই সাংবাদিক মার্কিন প্রশাসনের অনেক জারিজুরি ফাঁস করে দেন।
তাঁর বই-এর শেষ অধ্যায়টা বাংলাদেশকে নিয়ে, ‘বাংলাদেশঃ বার্থ বাই ফায়ার’। ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে ঘটা দক্ষিণ এশিয়ার ঘটনাবলী আর তার পরিপ্রেক্ষিতে নিক্সন-কিসিঞ্জারের ভুমিকাই মূলত আলোচ্য বিষয় এই অধ্যায়ের।
বই-এর এই অধ্যায়টা পড়ার আগে আমার ধারণা ছিল যুক্তরাষ্ট্র একাত্তরের ডিসেম্বরে বঙ্গোপসাগরে তার প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত সপ্তম নৌবহর পাঠালেও, আসলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সৈন্য পাঠানোর কোন পরিকল্পনা তাদের ছিল না। ভারত আর সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটু ঝাড়ি দেয়াই ছিল উদ্দেশ্য। তাই সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের হাওয়া খেয়েই ফিরে গিয়েছিল। এখন আমার মনে হয় আমার ধারণা ভুল ছিল। শুধু হাওয়া খেতেই তারা যায় নি। (অবশ্য আমার ভুল ধারণার পেছনে আমার পড়া অন্য কিছু বই-যেমন, সিসন আর রোজ-এর লেখা ‘ওয়ার অ্যান্ড সেসিশন’-এর প্রভাব ছিল।)
চীন আর রাশিয়াকে নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত ছিল আমেরিকা। ভিয়েতনাম যুদ্ধে তখন আমেরিকার কাহিল অবস্থা। পুরো এশিয়া কম্যুনিষ্টদের হাতে চলে যাওয়ার সম্ভাবনাকে যে করেই হোক ঠেকাতে বদ্ধপরিকর নিক্সন প্রশাসন। এই লক্ষ্যে পাকিস্তান তখন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সহযোগী আমেরিকার। ওদিকে ভারতের ঘাড়ে ভর করে সোভিয়েত ইউনিয়ন শক্ত অবস্থান নিয়েছে দক্ষিণ এশিয়ায়। নিক্সন-কিসিঞ্জার চীনকে যতটা পারা যায় নিউট্রালাইজ করতে সচেষ্ট। তার পাকিস্তানকে খুব দরকার চীনের ওপরে প্রভাব বিস্তারের জন্য। ভারতের সাথে চীনের দা-কুমড়ো সম্পর্কটাকেও কাজে লাগাতে হবে।
সপ্তম নৌবহর – টাস্ক ফোর্স ‘ও-ক্যালকাটা’
বৈশ্বিক রাজনীতির এই পটভুমিতে সপ্তম নৌবহরের ‘টিএফ ৭৪’ নামে একটা টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। তখনকার বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজ পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন যুদ্ধবিমানবাহী ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ ছিল এই বহরে। পঁচাত্তরটা বিমান, পাঁচটা হেলিকপ্টার আর পাঁচ হাজারেরও বেশি সৈন্য ধারণ করতো এন্টারপ্রাইজ। ওই টাস্ক ফোর্সে, যার নিক-নেইম ছিল ‘ও-ক্যালকাটা’, আরো ছিল, তিনটা গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার, চারটা গান ডেস্ট্রয়ার আর ছিল ট্রিপলি (হেলিকপ্টারবাহী জাহাজ) পঁচিশটা ‘মেরিন এসল্ট’ হেলিকপ্টারসহ। এন্টারপ্রাইজ আর ডেস্ট্রয়ার চারটা ভিয়েতনামের উপকূল ইয়াঙ্কি স্টেশন থেকে যাত্রা করে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে, ট্রিপলি আর গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ারগুলো ফিলিপাইনের সুবিক বে থেকে। হাওয়াই-এর প্রশান্ত মহাসাগরীয় কমান্ড, ওয়াশিংটন আর নৌবহরের জাহাজগুলোর মধ্যে ছিল সার্বক্ষণিক রেডিও যোগাযোগ সেই কটা দিন।
ডিসেম্বরের ১৫ তারিখে, বিজয় দিবসের একদিন আগে, টাস্ক ফোর্স বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে। ঢাকা থেকে মাত্র একহাজার নব্বই মাইল দূরে।
এই টাস্ক ফোর্সের তত্বাবধানে ছিলেন সেই জন ম্যককেইন, আশা করি পাঠকের মনে আছে তাঁর কথা, ১৯৬৫-তে ডমিনিকান রিপাব্লিক আক্রমণ করে যে মার্কিন মেরিন বাহিনী, তার দায়িত্বেও ছিলেন তিনি। হয়তো কাকতালীয়। (‘অ্যান্ডারসন পেপারস’ থেকে আরো জানতে পারলাম একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানে নিযুক্ত আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ছিলেন জোসেফ ফারল্যান্ড। ফারল্যান্ডের সাথে ইয়াহিয়ার সম্পর্ক ব্যাক্তিগত বন্ধুত্বে পরিণত হয়। গ্লাসের দোস্ত যাকে বলে! এই ফারল্যান্ডই ১৯৫৭-তে ডমিনিকান রিপাব্লিকে রাষ্ট্রদূত ছিলেন – আর ছিলেন ট্রুহিও-র বিশেষ বন্ধু। সন্দেহ নাই, স্বৈরশাসকদের সাথে বন্ধুত্ব পাতাতে বেশ পারদর্শী ছিলেন এই ভদ্রলোক। )
তবে সান্তো ডমিঙ্গোতে যেমন, ঢাকার ক্ষেত্রেও তেমনি অজুহাত ছিল, আমেরিকানদের জানমালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করার জন্যই এই কষ্টস্বীকার। বলা হচ্ছিল ঢাকা থেকে মার্কিন নাগরিকদের উদ্ধার করার জন্য সপ্তম নৌবহরের সবচেয়ে বড় যুদ্ধজাহাজ এন্টারপ্রাইজের বঙ্গোপসাগরে আগমন। সেই পুরোনো অজুহাত।
শ’খানেক মানুষের জানমাল রক্ষার জন্য বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন! মশা মারতে কামান দাগা বোধহয় একেই বলে! তার আগে নয়মাস ধরে যে একটা জনগোষ্ঠীর ওপরে নির্বিচারে হত্যযজ্ঞ চালানো হলো, যাকে জেনোসাইড ছাড়া আর কোন ভাবেই বর্ণনা করা যায় না, তা নিয়ে এই পরাশক্তি ছিল নির্বিকার। উপরন্তু ব্যস্ত ছিল হত্যাকারী পাকিস্তানের সাফাই গাওয়াতে।
গ্রেনাডায়ও মার্কিন মেডিকেল ছাত্রদের উদ্ধারের জন্য আমেরিকা আগ্রাসন চালিয়েছিল। মার্কিন প্রশাসন এই প্রোপাগান্ডাগুলো আসলে করে নিজ দেশের শান্তিকামী জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য। বিশ্ব জনমতের থোড়াই কেয়ার করে আমেরিকা! কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি, বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের সময়ে সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি সহ অনেকেই আমেরিকার পাকিস্তান-প্রীতির কড়া সমালোচক ছিলেন। আমেরিকার সাধারণ জনগণও বাংলাদেশের সমর্থক ছিলেন। মনে পড়ছে একাত্তরের অগাস্টে নিউ ইয়র্কে আয়োজিত সদ্যপ্রয়াত রবিশঙ্কর আর জর্জ হ্যারিসনের ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’-এর কথা। হাজার হাজার মানুষ গিয়েছিল শুনতে আর সমর্থন জানাতে।
বিজয় দিবস, ১৫ই ডিসেম্বর?
সময় ও সুযোগ আমেরিকার পক্ষে ছিল না একাত্তরের বাংলাদেশে। কিন্তু সেই সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টায় কোন ত্রুটি ছিল না। অ্যান্ডারসন-এর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের বিজয় অর্জনের মুহূর্তটাকে একুশ ঘণ্টা পিছিয়ে দেয়ার জন্য দায়ী মার্কিন কর্তৃপক্ষ।
নইলে বাংলাদেশের বিজয় দিবস হতো ১৫ই ডিসেম্বর, ১৬ই ডিসেম্বর নয়। হয়তো তাহলে বেঁচে যেতেন আমাদের হতভাগ্য শহীদ বুদ্ধিজীবিরা, যাঁদেরকে হত্যা করা হয়েছিল ১৪ তারিখ রাতে।
সেই কাপুরুষ হত্যাকারীরা রাতের অন্ধকারে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে খুন করার ওই স্পর্ধা আর সময়টুকু পেত না, যদি মার্কিন দূতাবাস সময়মতো এ.এ.কে নিয়াজির আত্মসমর্পণের বার্তাটা জগজিত সিং অরোরার কাছে সেই দিনই কালক্ষেপন না করে পৌঁছে দিতেন।
ডিসেম্বরের ১৪ তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় নিয়াজি ঢাকায় আমেরিকান কনস্যুলেট জেনারেলের অফিসে যান সাহায্যের আবেদন নিয়ে। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিতে চান, কিন্তু পারছেন না। কারণ তার নিজের রেডিও ট্রান্সমিটারটা ভারতীয় বোমার আঘাতে ধ্বংশ হয়ে গেছে। আমেরিকার কন্সাল জেনারেল হার্বার্ট স্পিভাক প্রটোকল রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, মানুষের জীবন বাঁচানোর ব্যাপারটা তার কাছে তেমন গুরুত্ব পেল না। স্পিভাক নিয়াজির আবেদনটা পাঠিয়ে দিলেন ওয়াশিংটনে, লাগলো ঘন্টাখানেক। ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্র দফতর (স্টেট ডিপার্টমেন্ট) নিয়াজির যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাঠিয়ে দিলেন রাষ্ট্রদূত ফারল্যন্ডের কাছে ইসলামাবাদে আর বলে দিলেন জেনে নিতে ইয়াহিয়া এই প্রস্তাবে রাজি আছে কিনা। ঢাকায় সময় তখন ১৫ই ডিসেম্বর রাত সাড়ে তিনটা।
হয়তো ঠিক সেই সময়েই আলবদরেরা সক্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় তাদের জঘন্য কাজে।
সেই একাত্তরেও মার্কিন সরকারের রেডিও ট্রান্সমিটার টেকনলজি ছিল বেশ উন্নত ও শক্তিশালী। ইচ্ছে করলে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে মুহূর্তের মধ্যে বার্তা পাঠাতে সক্ষম ছিল তাদের সিস্টেম। কিন্তু কি এক রহস্যজনক কারণে তারা অবলম্বন করলো দীর্ঘসূত্রিতার পথ। পরিহাসপ্রিয় অ্যান্ডারসন-এর ভাষ্যানুযায়ী এই বার্তাটা যেন মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে ছিল কূটনৈতিক অনুষ্ঠানের দাওয়াতপত্র পৌঁছে দেয়ার মতো একটা ব্যাপার।
জাতিসঙ্ঘের মার্কিন প্রতিনিধিদের পাঠানো হলো পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে খুঁজে বের করার জন্য। কাউকে না পেয়ে শেষতক বার্তাটা পৌঁছে দেয়া হয় নয়াদিল্লিতে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত কিটিং-এর কাছে। তখন দুপুর গড়িয়ে প্রায় একটা বাজে। আরো ঘন্টা দুয়েক লাগলো বার্তাটাকে তর্জমা করতে আর উপযুক্ত ভারতীয় কর্তৃপক্ষ খুঁজে বের করতে আর শেষমেশ পূর্বাঞ্চলে ভারতীয় কমান্ডার জেনারেল জগজিত সিং অরোরার হাতে পৌঁছে দিতে।
বাকীটুকু বহুলপঠিত ইতিহাস। নতুন করে লেখার কিছু নাই।
তবে পাদটীকায় এটুকু না বললেই নয়, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্রান্তিলগ্নে যে দেশের এমন গর্হিত ভূমিকা ছিল, সেই যুক্তরাষ্ট্রের সাথেই ১৯৭৪-এর মধ্যভাগ থেকে সম্পর্ক উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হতে শুরু করে। অল্প সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র পরিণত হয় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক সাহায্যদাতায়। তবে এজন্যে তাজুদ্দীন আহমদকে হারাতে হয় মন্ত্রীত্ব। ‘মার্কিন অর্থনৈতিক সাহায্য নেবো না’, অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে এমন দম্ভোক্তি করেছিলেন তিনি।
তাজুদ্দীন আহমদ, শহীদ বুদ্ধিজীবি আর মুক্তিযুদ্ধের লাখো শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করছি।
ডিসেম্বর ১৫, ২০১২।
তথ্যের উৎস ওয়েবসাইট আর বইএর তালিকা। ওয়েবসাইটগুলো দেখা হয়েছে নভেম্বর ২০১২-র শেষ দুই সপ্তাহে।
ডমিনিকান রিপাব্লিক হিস্ট্রি, http://dr1.com/articles/history.shtml
হিস্ট্রি অফ দ্য ডমিনিকান রিপাব্লিক, http://www.hispaniola.com/dominican_republic/info/history.php
ডমিনিকান রিপাব্লিকঃ গভর্ণমেন্ট এন্ড পলিটিক্স,
http://www.mongabay.com/reference/country_studies/dominican-republic/GOVERNMENT.html
হিস্ট্রি অফ ইউএস ইন্টারভেনশন্স ইন ল্যাটিন আমেরিকা,
http://www.yachana.org/teaching/resources/interventions.html
দ্য ইনভেশন অফ গ্রেনাডা, http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/reagan-grenada/
Anderson, J., The Anderson Papers, Ballantine Books, New York, 1974.
Sisson, R. and Rose, L.E., War and Secession – Pakistan, India, and the Creation of Bangladesh, University of California Press, Berkeley, 1990.
Gurtov, M., The United States and the Third World, Antinationalism and Intervention, Praeger Publishers, New York, Washington, 1974.
________________________________________
http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=31874#comment-101289
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:৩৯582796
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:৩৯582796- বেঁচে থাকুক মুক্তিযুদ্ধ, বেঁচে থাকুক বীরাঙ্গনা ৭১’
লিখেছেন: মুনসুর সজীব
তারিখ: ২৯ অগ্রহায়ন ১৪১৯ (ডিসেম্বর ১৩, ২০১২)
________________________________________________
একাত্তর। মজবুত হাড় মাংসের বুনিয়াদ, মাটি-প্রানের চর্বি, আঠালো রক্তের জমাট দলা, আর এক গর্তে সহস্র আত্মার গলিত আকুতি আর একটা স্বপ্নের নাম একাত্তর। একটা বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের সমাপ্তির নাম একাত্তর। মুক্তিযুদ্ধ। প্রাপ্তি আর ত্যাগের রক্তাক্ত সমীকরণ।
অতঃপর সবুজ ঘাসের চাদরে লাল সূর্যের দীপাবলি। মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ। আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয় নি। । বড় শক্ত এ জাতির ভিত্তি। বড় মজবুত এ বেড়ে ওঠা মানব শেকল। শেকলে শেকলে মুক্তির টান। মানুষে মানুষে প্রানের টান। তবু মুক্তি আসেনি। জীবিত আত্মার মুক্তি বিলম্বিত মৃত আত্মার ফুঁপিয়ে ওঠা কান্নার অসহ্য নীরব আর্তনাদে। কেঁদে ওঠে বুক, আর্তনাদ করে ওঠে ভেতরটা। এ জাতির বেড়ে ওঠার সুতায় রক্তের দাগ। কষ্ট-কান্না-রক্ত-অভিশাপের দাগ। কোটি মানবের কানে বাজে মৃত প্রানের ছায়ার নিনাদ।
পাপ মুক্তি চাই। স্বীকার করে নিতে চাই তোমরা ছিলে। মনে আছে তোমরা আছ। বিশ্বাসে নিলাম তোমরা থাকবে । তোমরা আছ আমাদের মাঝে। তোমরা থাকবে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনাচরণের লুকানো দীর্ঘশ্বাসে। তোমরা ৭১। তোমরা বিজয়। তোমরা প্রভাতফেরী। তোমরা স্বাধীনতার ঘোষণার প্রতি শব্দের স্পন্দন। তোমরা বিজয় মিছিলে আমাদের স্লোগানের সুর। তোমরা এই রাজপথ-সমাজ-মুক্তির নির্মাণ-কাব্যের প্রতি স্তবকে মিশে থাকা রক্তের ফোঁটা।
তোমরা মা। তোমরা জন্ম দাও নি। তবু বেয়নটের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত তোমাদের জরায়ুতে এ জাতির প্রথম প্রাণস্পন্দন। তোমরা লালন করনি। তবু তোমাদের কেটে নেয়া স্তন থেকে চুইয়ে পড়া রক্ত এ মাটিকে প্রথম মাতৃ দুগ্ধ পানের অনুভূতি দিয়েছে। তোমরা আঁচল দিয়ে আগলে রাখনি। তবু বদ্ধ ঘরের সিলিঙে ঝুলানো আঁচলে তোমাদের নিষ্প্রাণ দেহ এ জাতির বুকে জেগে-ওঠা রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছে। তোমরা বীরাঙ্গনা। তোমরা বীর মুক্তিযোদ্ধা। তোমাদের ইজ্জত-সম্ভ্রম আর আত্মত্যাগ এ জাতিকে বিজয় এনে দিয়েছে, মুক্তি এনে দিয়েছে। কথা দিচ্ছি ভুলবো না। কথা দিচ্ছি বাংলাদেশের বেড়ে ওঠা, বেঁচে থাকার ইতিহাসে তোমাদের নাম রক্ত-কালিতে লেখা থাকবে চিরকাল।
বলছি একাত্তরের কথা। বলছি বীরাঙ্গনাদের কথা। বলছি সেই মা-বোনদের কথা যাদের আত্মার কান্না আজও আমাদের মৃত প্রায় বিবেক বিজয় দিবসের প্রথম প্রহরে কিংবা নীরব গভীর রাতে শুনতে পায়। যাদের ছায়া আজো কোন বধ্যভূমির বদ্ধ আধার কুঠুরিতে মুক্তির প্রত্যাশায় আহাজারি করে যায়। যাদের লুণ্ঠিত সতীত্ব, যাদের রক্ত আমাদের স্বাধীনতার দলিলকে সতীত্ব দিয়েছে। যাদের নগ্ন-নিষ্প্রাণ-ধর্ষিত দেহ আজো আমাদের বুকে দায় মুক্তির নির্মম চাপের মতো অনুভূতি দেয়। অন্ধকার কুঠুরিতে তারা ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। প্রান ভিক্ষা চেয়েছে। সম্ভ্রম ভিক্ষা চেয়েছে। ভুল করেছে। তারা ওদের মানুষ ভেবেছিল। হায়নার হাসিকে আমাদের মায়েরা মানুষের হাসি ভেবে ভুল করেছিল।
Gen. A. A. Khan Niazi did not deny rapes were being carried out and opined, in a Freudian tone, “You cannot expect a man to live, fight, and die in East Pakistan and go to Jhelum for sex, would you?”
তারা হয়তো কোনদিনও জানতে পারেনি পাঠান পশুটা আর তার বাংলাদেশি আত্মগামী কুকুরগুলো তাদের গনিমতের মাল হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। আর লক্ষ লক্ষ পাকি পশুরা দীর্ঘ নয় মাস ধরে, এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার বর্গমাইল জুড়ে পাশবিক কামনায় রক্তাক্ত করেছে আমাদের চার লক্ষ মা বোনকে। আমাদের মায়েরা আমাদের বোনেরা প্রতিনিয়ত বাধ্য হয়েছে ইজ্জত বিলিয়ে দিতে। হায়নারা কামড়ে কামড়ে ছিলে নিয়েছে আমাদের মা বোনদের শরীরের রক্ত মাংস। লাঠি-বন্দুকের নল-বেয়নট দিয়ে খুছিয়ে ক্ষত বিক্ষত করেছে তাদের বুক,উরু,যোনি। অসহ্য দমবন্ধ এই নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারিয়ে যাওয়া বীরাঙ্গনারা হটাৎ জেগে উঠে আবারো আৎকে উঠেছে। তার চোখের সামনে, মুখের উপর বারেবার গলে পড়ছে পাকি মুখনিঃসৃত কামনার লালা। আবারো ধর্ষণ। গনধর্ষণ। বাঁচার আকুলতা নিয়ে বীরাঙ্গনাদের নির্লিপ্ত আর্তনাদ। দরজার ওপাশে বসে থাকা কিছু মাওদুদী বাদী জারজদের খিলখিল হাসি। পাশবিক কামনার কানাকানি। এ যে গনিমতের ফজিলত। এ যে যুদ্ধদিনের উপহার।
পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের সেনাবাহিনী এবং পা চাটা এ দেশীয় কুকুর গুলো ধর্মের দোহাই দিয়ে, পাকিস্তান রক্ষার(?) তাগিদে এ দেশে গণহত্যা আর গণধর্ষণ শুরু করেছিল। নিরীহ নিরস্র বাঙালি ললনারা ধর্মের দেয়ালের আড়ালে লুকিয়েও বাঁচতে পারে নি। বাঁচাতে পারে নি সম্ভ্রম। গণহত্যা-গণধর্ষণ-পাশবিকতার আবার ধর্ম কি? বাংলার হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান কেউ বাঁচতে পারে নি নয় মাসের মধ্যযুগীয় বর্বরতার কাছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চীনের জিয়ান জু প্রদেশের নানজিং শহরে জাপানীদের এবং রাশিয়ায় জার্মান নাযি বাহিনীর ধর্ষণলীলার সাথে একাত্তরের ধর্ষণকে তুলনা করে সুসান মিলার তার রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন-
In her ground-breaking book, Against Our Will: Men, Women and Rape, Susan Brownmiller likened the 1971 events in Bangladesh to the Japanese rapes in Nanjing and German rapes in Russia during World War II. “… 200,000, 300,000 or possibly 400,000 women (three sets of statistics have been variously quoted) were raped. Eighty percent of the raped women were Moslems, reflecting the population of Bangladesh, but Hindu and Christian women were not exempt. … Hit-and-run rape of large numbers of Bengali women was brutally simple in terms of logistics as the Pakistani regulars swept through and occupied the tiny, populous land …” (p. 81).
রক্ষা পায়নি ১৩ বছরের শিশুও। কি নির্মম কতো নিষ্ঠুর ছিল এই জাতির প্রতি পাকি ট্রূপ। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে কিংবা বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার পথে বহু মেয়ে শিশু-কিশোরীকে জোর করে ধরে নিয়ে করা হয়েছে পৌনঃপুনিক ধর্ষণ। মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ধর্ষণের শিকার হয়েছে এইসব বন্দী শিশুরা।
Khadiga, thirteen years old, was . . . walking to school with four other girls when they were kidnapped by a gang of Pakistani soldiers. All five were put in a military brothel in Mohammedpur and held captive for six months until the end of the war. Khadiga was regularly abused by two men a day; others she said, had to service seven to ten men daily. . . . At first, Khadiga said, the soldiers tied a gag around her mouth to keep her from screaming. As the months wore on and the captives’ spirit was broken, the soldiers devised a simple quid pro quo. They withheld the daily ration of food until the girls had submitted to the full quota.
- Khadiga, Kamala Begum: interview with Berengere d’Aragon3
যুদ্ধ দিনের বিয়ে। একটা প্রহসনের মতো ছিল। মেয়ের ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষার তাগিদে মেয়েকে কোন এক পুরুষের হাতে তুলে দিতে চাইত মা-বাবারা। এটাও কি কম ত্যাগ? কোন উৎসব থাকতো না সেই সব বিবাহে। থাকতো না নাচ-গান কিংবা ভগ্নিপতি-শ্যালিকার খুনসুটি। শুধুই মলিন নিরবতা। বাতাসের শব্দও তখন সেনা-বুটের গমগম আওয়াজের মতো মনে হতো। তবু কি শেষ রক্ষা হতো? তবু থেমে থাকেনি মৃত্যুর মিছিল। তবু থেমে থাকেনি বৈধব্যের গান। তবু থেমে থাকেনি ইজ্জত হারানোর নীরব আর্তনাদ। অভিশাপ দেই। বারংবার অভিশাপ দেই-
Two [Pakistani soldiers] went into the room that had been built for the bridal couple. The others stayed behind with the family, one of them covering them with his gun. They heard a barked order, and the bridegroom’s voice protesting. Then there was silence until the bride screamed. Then there was silence again, except for some muffled cries that soon subsided. In a few minutes one of the soldiers came out, his uniform in disarray. He grinned to his companions. Another soldier took his place in the extra room. And so on, until all the six had raped the belle of the village. Then all six left, hurriedly. The father found his daughter lying on the string cot unconscious and bleeding. Her husband was crouched on the floor, kneeling over his vomit.
বীরাঙ্গনা ফেরদৌসি প্রিয়ভাষিণী। একজন ভাস্কর। একজন জীবন্ত কিংবদন্তী। একজন বীরঙ্গনা একাত্তরে ২৩ বছরের তরুণী। কোমলমতি স্ত্রী। তিন সন্তানের মমতাময়ী মা। তার স্বামী-সন্তানের সামনে দিয়েই তাকে সেনা-ট্রাকে করে তুলে নিয়ে যায় পাক আর্মি। দীর্ঘ সাত মাস ঢাকার একটি সেনা ক্যাম্পে তার উপর চালানো পাশবিক অত্যাচার। তার ভাষায়-
“I was subjected to extreme physical and mental torture. They had no mercy. Many of my friends and relatives were killed in front of me,”
পশুরা ছাড়েনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদেরও। পাক অফিসারদের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী হল গুলো ছিল শিক্ষিতা, রূপবতী, নাচ-গান জানা মধ্যবিত্ত-উচ্চমধ্যবিত্ত মেয়ে পাওয়ার সবচেয়ে সুবিদা জনক স্থান। পাকি মেজর আসলাম ৩ অক্টোবর ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে গিয়ে দায়িত্বরত মহিলা সুপারেন্ডেণ্টকে জানান তেজগাঁও ক্যান্টনমেন্ট এ অনুষ্ঠেয় সেনাবাহিনীর একটা প্রোগ্রামে কিছু নাচ গান জানা মেয়ে পাঠানোর নির্দেশ দেন। কিন্তু মহিলা সুপারেন্ডেণ্ট জানান যুদ্ধের কারনে বেশিরভাগ মেয়েই হল ত্যাগ করেছে, মাত্র ৪০ জন আবাসিক ছাত্রী আছে হলে। নিজ দায়িত্বের অংশ হিসাবে তিনি তাদের তেজগাঁ পাঠাতে অস্বীকার করেন। মেজর আসলাম চলে যান এবং চারদিন পর ৭ অক্টোবর ১৯৭১ ফিরে আসেন আরও কিছু সেনা অফিসার নিয়ে। অসহায় মহিলা তত্ত্বাবধায়কের সামনে দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যান মেয়েদের। খোলামেলা ভাবেই চলতে থাকে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার। ১৬ ডিসেম্বরের পরে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকার বিভিন্ন সেনা ক্যাম্প থেকে রেডক্রস আর মুক্তিবাহিনী উদ্ধার করে শতশত মৃত-অর্ধমৃত, ধর্ষিতা লাঞ্ছিত আর অত্যাচারে মানসিক ভারসম্য হারিয়ে ফেলা ছাত্রীদের –
“ …..Some army officer raided the Rokeya Hall, the girls’ hostel of Dacca University, on October 7, 1971. Accompanied by five soldiers, Major Aslam had first visited the hostel on October 3, and asked the lady superintendent to supply some girls who could sing and dance at a function to be held in Tejgaon Cantonment. The superintendent told him that most of the girls had left the hostel after the disturbances and only 40 students were residing but as a superintendent of a girls’ hostel she should not allow them to go to the cantonment for this purpose. Dissatisfied, Major Aslam went away. Soon after the superintendent informed a higher army officer in the cantonment, over the telephone, of the Major’ s mission.
However, on October 7, at about 8 p.m. Major Aslam and his men raided the hostel. The soldiers broke open the doors, dragged the girls out and stripped them before raping and torturing them in front of the helpless superintendent. The entire thing was done so, openly, without any provocation, that even the Karachi-based newspaper, Dawn, had to publish the story, violating censorship by the military authorities. In seven days after liberation about 300 girls were recovered from different places around Dacca where they had been taken away and kept confined by the Pakistani army men. On December 26, altogether 55 emaciated and half-dead girls on the verge of mental derangement were recovered by the Red Cross with the help of the Mukti Bahini and the allied forces from various hideouts of the Pakistani army in Narayanganj, Dacca Cantonment and other small towns on the periphery of Dacca city.
পাকি সেনাবাহিনী এ দেশের নারীদের শরীরে স্থায়ী করে দিয়ে যায় অসহ্য যন্ত্রণার নির্মম বিষ। নির্লিপ্ত ধর্ষণে হাজার হাজার নারী হয়ে পড়ে অন্তঃসত্ত্বা। পেটে সন্তান। বুকে পাকি নির্যাতনের চাক চাক কস্টের দাগ। সাথে অনিচ্ছা মাতৃত্বের দায়। সন্তান জন্মদান আর বেঁচে থাকার মাঝের যে ভয়ংকর দোটানা। এ শুধু একজন বীরাঙ্গনাই জানেন। এই চাপ সহ্য করতে না পেরে অনেকে আত্মহত্যা করেন। পাকি বীর্য কেড়ে নেয় দুটি নিষ্পাপ প্রান। রেডক্রস আর অন্যান্য সংস্থার সহায়তায় অনেকে বেছে নেয় এবরশন এর পথ। সেটাও মোট ধর্ষিতার ১০ ভাগেরও কম।
That rape was endemic in 1971 contrary to some contentions that it was isolated. According to him, the numbers were high and many were forced to get abortions. “It is difficult to put a figure in it. About 100 a day in Dhaka and in variable numbers in lot of other towns. And some would go to Calcutta…(for abortions)
এতো গেল যারা প্রতিনিয়ত এবরশন করেছেন তাদের কথা। আর যারা তা করতে পারেন নি তাদের কি হল? তাদেরও সন্তান সময়ের আগেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে। না কোন ডাক্তার কিংবা নার্স না বরং পাকি কুকুর গুলো ধারালো অস্র দিয়ে কেটে নিয়েছে তাদের পেট। টেনে হিঁচড়ে বের করে এনেছে পেটের সন্তান। মৃত মা। মৃত সন্তান। সেনা ক্যাম্পের অন্ধকার ঘর গুলো হয়ে উঠলো রক্তাক্ত আঁতুড় ঘর। কাঁচা মাংসের কসাই খানা।
We have collected numerous evidences on the rape, molestation and torture of Bangalee women by the Pakistani army. Rauful Hossain Suja, the son of martyr Akbar Hossain of Pahartali, Chittagong, went to the FOY’S LAKE KILLING ZONE to look for his father’s dead body. They found dead bodies of approximately 10,000 Bangalees, most of them were brutally slaughtered. In their desperate search for their father’s dead boy, they found dead bodies of 84 pregnant women whose abdomens were slashed open. This type of brutality took place almost every where in Bangladesh. Raped women were also locked up naked in various military camps so as to deny them termination of their anguish through suicide.
আর যারা বেঁচে ছিলেন তাদের জীবন ছিল অভিশপ্তের চেয়েও বেশী কিছু। শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দীর্ঘ বন্দী জীবনের নোংরা কামনার কাঁচা দাগ। বুক জুড়ে যুদ্ধশিশু। পিতৃ পরিচয়হীন সন্তান নিয়ে সমাজে আশ্রয় নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে স্বামী-সমাজ এ সন্তান গ্রহনে অস্বীকৃতি জানায়। নিরুপায় তাদের অনেকে আত্মহত্যা করেন। কেউ কেউ স্বামীর হাতে নিহত হন। কেউ নিজ হাতে হত্যা করেন নিজের পাকি-শঙ্কর সন্তানকে। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদের বীরাঙ্গনার স্বীকৃতি দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে তাও সামগ্রিক ভাবে সফল হয় নি। কারন ৭১ এর নয় মাস কেড়ে নিয়েছে তাদের আবেগ, বেঁচে থাকার আকাঙ্খা। যারা পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্প গুলোতে রক্ষিতার মতো জীবন পার করেছেন তাদের অনেকেই পাকিস্তানি অফিসারদের পায়ে পড়ে ভিক্ষা চেয়েছেন যেন তাদের সঙ্গে করে পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্ত পাকিরা ভোগের বস্তুকে সঙ্গিনী করতে রাজি ছিল না।
Dr. Davis talks about how Sheikh Mujibur Rahman labeled the rape survivors as “war heroines” to help them reintegrate into their communities, but the gesture largely did not work. After being assaulted and impregnated by Pakistani soldiers, the Bangladeshi women were completely ostracized by society. Many were killed by their husbands, committed suicide, or murdered their half-Pakistani babies themselves. Some women were so scared to go back home after being held captive in Pakistani rape camps, they begged their Pakistani captors to take them back to Pakistan with them.
সবচেয়ে বড় সমস্যার জন্ম হয় যুদ্ধ শিশুদের লালন নিয়ে। সমাজ-পরিবার তাদের স্বীকৃতি দিতে বরাবরই অস্বীকার করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মা তার সন্তান রাখতে অস্বীকার করেন। এই সব যুদ্ধ শিশুদের লালনের জন্য এগিয়ে আসে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলো এবং মাদার তেরেসার মতো মানুষেরা। তারা শিশুগুলোকে বিভিন্ন হোমে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, যুক্তরাষ্ট্র, এবং কানাডার বিভিন্ন পরিবারে দত্তক হিসেবে পাঠানোর ব্যবস্থা নেন। যেখানে নিষ্পাপ এই শিশুরা, জন্মই যাদের পাপ ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন সংস্কৃতিতে, ভিন্ন পরিচয়ে, ভিন্ন ধর্ম পরিচয়ে বেড়ে ওঠার বাধ্য জীবনে পাচার হয়।
Rape was not the only issue but war babies were also a major problem that needed addressing. There were several agencies that became involved in organising these war children’s transfer to Europe where babies in new homes were very welcome. It had coincided with restrictions on availability of babies for adoption there.
কোলকাতায় মাদার তেরেসার হোমে সন্তানকে রেখে আসার আগে যুদ্ধ শিশু কোলে এক কিশোরী মা-
Bangladesh government, at instigation of US social workers, is setting up a legal machinery for international adoption of child victims of occupation and war, including unwanted offspring of women raped by Pakistani soldiers; This step is considered a significant precedent in Bangladesh, where adoption of children by strangers is an unknown concept; International Social Service American Branch General Director W C Klein says the service has suggested adoption as an alternative to prevailing practice of abortion, infanticide and selling of unwanted children to beggars, who use them to elicit sympathy. The New York Times, May 29, 1972 .
Dead Reckoning: Memories of the 1971 Bangladesh War বইয়ে শর্মিলা বোসের পাকি বাহিনীর যুদ্ধাপরাধ আর নারকীয় নির্যাতনকে হালকা করে দেখার নোংরা প্রয়াসকে ধিক্কার জানাই। অধ্যাপক বোস বারবার বুঝাতে চেয়েছেন এ দেশে পাকিরা কোন যুদ্ধাপরাধ করেনি। গণহারে ধর্ষণ নির্যাতন করেনি বরং এটা ছিল একটা গৃহযুদ্ধ। তিনি এটাও বলেছেন একাত্তরের ধর্ষণ গণহত্যা সম্পর্কে তথ্য বাংলাদেশী এবং ভারতীয় ইতিহাসবিদের বাড়িয়ে বলা। তার মতে এটা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ফায়দা নেয়ার প্রচেষ্টা। তিনি এও বলেছেন একাত্তরের ধর্ষণের বিবরণ লিখতে যেখানে ১০০ সব্দ প্রয়োজন সেখানে ৬৫০০ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি একাত্তরের নির্মম ধর্ষণের ইতিহাস ১০০ শব্দে লেখার পক্ষপাতি! তিনি আমাদের মুক্তিবাহিনীকে বিদ্রোহী বাহিনী (!) বলে আখ্যা দিয়েছেন।
“The issue of rape amounted to about 100 words out of a nearly 6,500 word paper on the subject of patterns of violence in 1971।
“As I pointed out in the discussion that followed, there is evidence elsewhere that rape certainly occurred in 1971. But it seems — from this study and other works — that it may not have occurred in all the instances it is alleged to have occurred.”
শর্মিলা বোসের উদ্দেশে বলতে চাই ওটা কোন গৃহযুদ্ধ ছিল না। ওটা ছিল আমাদের মহান মুক্তি সংগ্রাম। ওরা কোন বিদ্রোহী বাহিনী ছিলনা, ওরা ছিল মহান মুক্তিযোদ্ধা। ওরা ছিল আমাদের বিজয় রথের সারথি। একাত্তরের ধর্ষণ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। ওটা ছিল পাকি পাপে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া আমাদের মহান বীরাঙ্গনাদের অভিশপ্ত দিনযাপন। এ ইতিহাস ১০০ শব্দে নয় ১০০ কোটি শব্দে লিখেও শেষ করা যাবে না। একাত্তরে ধর্ষণ হয়েছে। প্রতিদিন আমাদের মা বোনেরা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। প্রতি মুহূর্তে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ইতিহাস মিথ্যা বলে না।
____________________________
http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=31681
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:৫১582807
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:৫১582807- আমাদের বীরাঙ্গনা নারী এবং যুদ্ধ শিশুরাঃ পাপমোচনের সময় এখনই
ফরিদ আহমেদ
________________________________________________________
(আকার আকৃতিতে এই লেখাটি নীল তিমির মতই দীর্ঘকায়। কারো যদি অসীম ধৈর্য্য এবং অফুরন্ত অলস সময় থাকে তাহলেই শুধুমাত্র এই দীর্ঘপথে পা বাড়াবেন বলে আশা করছি। না থাকলে আগে ভাগে সরে পড়াটাই হবে উত্তম কাজ।
পাঠকদের ধৈর্য্য এবং অলস সময়ের উপর অযাচিত চাপ না ফেলে একাধিক পর্বে ভাগ করে দিতে পারতাম ইচ্ছে করলেই। কিন্তু সেক্ষেত্রে বিরতির বিঘ্নতায় পাঠকদের লেখাটির সাথে আবেগগত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল প্রবল। যেটা কোনভাবেই কাম্য নয় আমার কাছে। সে কারণেই অসীম সাহসের সাথে অনেক সংশয়কে পাশ কাটিয়ে এক পর্বেই পোস্ট করলাম লেখাটি।
এই লেখাটির জন্য বীণা ডি’কস্টার লিখিত বীরাঙ্গনা নারী এবং যুদ্ধ শিশুদের উপর প্রবন্ধসমূহের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছি আমি। অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা রইলো বাংলাদেশের সন্তান এই গুণী, মেধাবী এবং পন্ডিত ব্যক্তিটির প্রতি। সেই সাথে অন্য যাদের লেখা থেকে তথ্য ব্যবহার করেছি তাদের প্রতিও আমার সবিশেষ কৃতজ্ঞতা।
একজনের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার কারণে লিখিত এই প্রবন্ধটি। বাহুল্য বিধায় তার নামটি উহ্য রাখা হলো। অন্তরালের সেই বিশেষ একজনের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত আমার এই লেখাটি।)
লজ্জায় মুখ ঢেকে আছেন একজন বীরাঙ্গনা। আসলেতো লজ্জিত হওয়ার কথা আমাদের। ছবিঃ নাইব উদ্দীন আহমেদ।
২০০২ সালে মন্ট্রিয়লবাসী ক্যানাডিয়ান পরিচালক রেমন্ডে প্রভেনচার যুদ্ধ শিশুদের নিয়ে ‘War Babies’ নামে একটি ডকুমেনটারি তৈরি করেন। সেই ডকুমেন্টারিতে তিনি ওয়াটারলু, ওন্টারিওতে বসবাসকারী এক ক্যানাডিয়ান যুবক রায়ানের পিছু নেন। এই যুবক তার অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতকে ছুঁয়ে দেখার জন্য যাত্রা করেছিল বহু বহু বছর আগে তার জন্ম হওয়া এক অজানা দেশের উদ্দেশ্যে।
বাবা মায়ের গভীর ভালবাসায় জন্ম নেয়ার সৌভাগ্য রায়ানের হয়নি। প্রেমবিহীন নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ায় ভালবাসাহীন পৃথিবীতে অনিচ্ছুক এবং অবাঞ্চিত আগমণ তার। রায়ান একজন যুদ্ধ শিশু। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের করুণতম পরিণতি সে। একাত্তর সালে পাকিস্তানী এক সৈনিকের অজ্ঞাত কোন বাঙালী রমণীকে বর্বরভাবে ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে তার জন্ম। বাহাত্তর সালে বাংলাদেশ থেকে তাকে দত্তক নিয়েছিল এক ক্যানাডিয়ান দম্পতি। সেখানেই তার বেড়ে উঠা। অতঃপর পরিণত বয়সে নিজের জন্মকালীন সময়কে অনুধাবন করা এবং মাকে খুঁজে পাবার সুতীব্র আকুতি থেকে রায়ানের বাংলাদেশ যাত্রা শুরু ।
তার নিজের লেখা এক কবিতায় রায়ান তার নিজের জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন এভাবে, ‘আমার নাম রায়ান বাদল। আমার দুইজন মা। একজন আমাকে ডাকে রায়ান বলে। আরেকজন আমাকে ডাকতো বাদল বলে। রায়ান বলে যিনি আমাকে ডাকেন, তাকে আমি আমার সারা জীবন ধরে চিনি। কিন্তু যিনি আমাকে বাদল বলে ডাকতেন তাকে আমি কখনো দেখিনি। তিনি আমাকে জন্ম দিয়েছিলেন বাংলাদেশে। সেই জন্মের তিন সপ্তাহ পরে আবার আমি জন্মেছিলাম আমার রায়ান নামে ডাকা ক্যানাডিয়ান মায়ের কোলে। বাদল নামে ডাকা আমার জন্মদাত্রী মাকে ১৯৭১ সালে ধর্ষণ করেছিল পাকিস্তানী এক সৈন্য। আমি একজন যুদ্ধ শিশু’।
অনেকদিন আগের ঘটনা। তাই নাম ধাম সব ভুলে গিয়েছি আমি। অষ্টাদশী এক তরুণী যুদ্ধ শিশু বুক ভরা আশা নিয়ে ক্যানাডা থেকে বাংলাদেশে গিয়েছিল তার হারিয়ে যাওয়া মায়ের খোঁজে। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মায়ের হদিস পায়নি সেই তরুণী। না দেখা সেই মাকে খোঁজার হৃদয় বিদারক যন্ত্রণা থেকে মর্মস্পর্শী একটি কবিতা লিখেছিল সে। যা ছাপা হয়েছিল ইংরেজী দৈনিক অবজার্ভারে।
এরও বছর দুয়েক আগে হবে হয়তো ঘটনাটা। কোন এক সাময়িকীর চিঠিপত্র কলামে ছাপা হয়েছিল এক কিশোর যুদ্ধ শিশুর চিঠি। বাংলাদেশের কোন এক মাদ্রাসার ছাত্র ছিল সে। সেখানে তাকে নিত্যদিন ‘জাউরা’, ‘পাকিস্তানীর পুত’সহ নানাবিধ টিটকারী শুনতে হতো সহপাঠীদের কাছ থেকে। সেই কিশোর যুদ্ধ শিশু করুণ আর্তিতে জানতে চেয়েছিল, এই দেশে কি তার কোনই অধিকার নেই। সে কি পাকিস্তানী কোন লম্পট ধর্ষক সৈনিকের ঘৃণ্য সন্তান, নাকি এই দেশের স্বাধীনতায় অবদান রাখা এক নির্যাতিতা মায়ের গর্বিত সন্তান? কোন পরিচয়টা তার আসল পরিচয়?
বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ায়ন ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়ান স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষকতায় নিয়োজিত ডঃ বীনা ডি’কস্টা বিভিন্ন এডোপশন এজেন্সী, বাংলা ওয়েবসাইট এবং সংবাদপত্রে আবেদন জানিয়েছিলেন যুদ্ধ শিশুদের সাথে কথা বলার জন্য। খুব অল্প কয়েকজনই তাদের জীবন কাহিনী জনসম্মুখে প্রকাশ করতে আগ্রহী ছিল। বীনা ডি’কস্টাকে লেখা ই-মেইলে এক যুদ্ধ শিশু লিখেছিল,
‘আমার দত্তক বাবা ছিল মহা বদমাশ এক লোক। সারাক্ষণই আমাকে অপমান করার চেষ্টা করতো সে…..আমি বছর চারেক আগে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলাম……..আমি সবসময়ই ভাবি যে আমি কেন এই ক্যানাডিয়ায়ান দম্পত্তির কাছে দত্তক হয়েছিলাম, যারা আমাকে দত্তক নেয়ার তিনমাসের মধ্যেই তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিল…….আমার শৈশব ছিল বিভীষিকাময়। আমার যখন খুব প্রয়োজন ছিল তখন আমার নিজের দেশ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আমার দিক থেকে। আর সে কারণেই আমি বাংলাদেশকে ঘৃণা করি। আমি মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে কাঁদি, কারণ আমার কোন শিকড় নেই। একারণেই আমি চেষ্টা করছি যেখানে আমি জন্মেছি সেই দেশ সম্পর্কে কিছুটা জানতে’।
সদ্য প্রয়াত খ্যাতিমান লেখক মুহাম্মদ জুবায়ের কোন এক যুদ্ধ শিশুকে নিয়ে করা হোম ভিডিও দেখার অভিজ্ঞতা থেকে তার নিজের ব্লগে লিখেছিলেন একটি হৃদয়স্পর্শী প্রবন্ধ। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল ‘একটি ভিডিওঃ ব্যক্তিগত বিজয়ের গল্প’। এই প্রবন্ধে তিনি একজন যুদ্ধ শিশুর তার মায়ের সাথে সাক্ষাতের বর্ণনা তুলে ধরেছেন এভাবে।
ভিডিওর শুরুতে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের শহুরে মধ্যবিত্ত বাড়ির একটি টেবিলে, ডাইনিং টেবিল বলে ধারণা হয়, দুটি চেয়ারে বসে আছে দু‘জন নারী। একজন বয়স্ক, চেহারায়, পোশাকে গ্রামীণ মানুষের ছাপ। কথা বলে বগুড়া শহর বা তৎসংলগ্ন অঞ্চলের ভাষায়। এই মুহূর্তে তার বয়স অনুমান করা যায় না, ধারণা করা যাবে ভিডিও দেখার পরে আনুষঙ্গিক কাহিনীটি জানা হলে। অন্যজন বয়সে তরুণী, মাথাভর্তি কোঁকড়া চুলগুলিই প্রথমে চোখে পড়ে। রং-চেহারায় পুরোপুরি বাঙালি ছাপ থাকলেও কথা বলে মার্কিনি ধাঁচের ইংরেজিতে। তার পরণের পোশাকটি অবশ্য কোনো তথ্য জানায় না, সূত্রও পাওয়া যায় না। আজকাল বাংলাদেশে শহরের অনেক মেয়েও এ ধরনের পোশাক পরে।
দুই নারী পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। একজন মহিলা দোভাষী, যাঁকে ক্যামেরায় দেখানো হচ্ছে না, একজনের কথা সাবলীলভাবে অনুবাদ করে জানাচ্ছেন অন্যজনকে। এই কথোপকথন থেকে অবিলম্বে জানা যায়, ইংরেজি-বলা তরুণীটি ওই বয়স্কার কন্যা।
বিবরণের সুবিধার জন্যে এদের একটি করে কাল্পনিক নাম দেওয়া যাক। আমরা বয়স্কাকে আমিনা এবং তরুণীকে সামিনা নামে চিনবো। তিরিশ বছর পরে, সামিনার জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার পর, এই তাদের প্রথম সাক্ষাত। ভিডিওতে ধরা ছবিতে দেখা যায়, একজন আরেকজনকে ক্রমাগত স্পর্শ করে, অনুভব করার চেষ্টা করে। পরস্পরের অজানা অসম ভাষায় হৃদয়ের যে আর্দ্রতা-ভালোবাসার পূর্ণ প্রকাশ ঘটতে পারে না, স্পর্শে তা সঞ্চারিত হতে থাকে। বস্তুত, প্রথমবারের সাক্ষাতে আজীবনের বিচ্ছেদ ও অদেখার তৃষ্ণা আর কিছুতেই মেটে না বলে বোধ হয়।
একসময় সামিনা ক্রমাগত চোখের পানি মুছতে থাকলে তার মা বলে ওঠে, ‘ওঙ্কা কর্যা চোখ মুছপার থাকলে চোখ বিষ করবি রে মা…‘। অনূদিত হয়ে কথাটি মেয়ের কাছে পৌঁছুলে কান্নাচোখেই হেসে ফেলে সে, ‘আমার চোখ সত্যিই ব্যথা করছে, মা‘। মায়ের মাথায়, কপালে, চুলে, গালে হাত বুলিয়ে মেয়ে একবার হাসে, একবার কেঁদে ওঠে, ‘এতোদিন পর সত্যি তোমার দেখা পেলাম, মা গো! এই দিনের জন্যে আমি অপেক্ষা করেছি আমার সারাটা জীবন ধরে!‘ মেয়ের তুলনায় মায়ের আবেগ খানিকটা নিয়ন্ত্রিত মনে হলেও তার চোখও ভিজে ওঠে।
সামিনাকে শিশুকালেই রেডক্রসের লোকেরা যুদ্ধ শিশু হিসাবে নিয়ে গিয়েছিল আমেরিকায়। সেখানে তাকে দত্তক নিয়েছিল আমেরিকান এক পরিবার। বড় হওয়ার পর সে জেনেছে যে সে আসলে একজন যুদ্ধ শিশু। আর তখন থেকেই তার শুরু হয় মাতৃপরিচয় উদঘাটনের অনুসন্ধান। অক্লান্ত পরিশ্রমে অনেক বছরের চেষ্টার পর মায়ের নাম ঠিকানা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় সে। বার বার খবর পাঠানোর পরেও তার জন্মদাত্রী মা আমিনা রাজী হয়নি মেয়ের সাথে দেখা করার। এমনকি স্বীকারও করেনি পুরো বিষয়টিকে। নাছোড়বান্দা সামিনা শেষমেষ এসে হাজির হয় বাংলাদেশে মাকে এক নজর দেখবার জন্য। তিরিশ বছর পর মুখোমুখি হয় সে তার জন্মদাত্রী মায়ের ।
সামিনার মত মাকে ছুঁয়ে দেখার, মায়ের চোখে চোখ রাখার, মায়ের সাথে কথা বলার সৌভাগ্য বেশিরভাগ যুদ্ধ শিশুরই হয়নি। তাদের বীরাঙ্গনা মায়েরা যেমন হারিয়ে গেছে আমাদের সমাজের অতল অন্ধকারে, যুদ্ধ শিশুরাও তেমনি হারিয়ে গেছে এই বিশাল পৃথিবীর সুবিশাল ব্যপ্তিতে। কেউ মনে রাখেনি তাদের কথা। অগণিত দুর্ভাগা মা আর তাদের হতভাগ্য সন্তানদের কথা মনে রাখার সময়ই বা কোথায় আমাদের।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে গণ ধর্ষণের শিকার হয়েছে বাঙালি রমণীরা। ঠিক কতজন যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে তার সঠিক কোন পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই। বীণা ডি’কস্টা তার “Bangladesh’s erase past’ প্রবন্ধে জানাচ্ছেন যে, সরকারী হিসাব অনুযায়ী একাত্তরে ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছিল দুই লক্ষ নারীকে। একটি ইটালিয়ান মেডিক্যাল সার্ভেতে ধর্ষণের শিকার নারীর সংখ্যা বলা হয়েছে চল্লিশ হাজার। লন্ডন ভিত্তিক International Planned Parenthood Federation (IPPF) এই সংখ্যাকে বলেছে দুই লাখ। অন্যদিকে যুদ্ধ শিশুদের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সমাজকর্মী ডঃ জিওফ্রে ডেভিসের মতে এই সংখ্যা এর চেয়েও অনেক বেশি। সুজান ব্রাউনমিলারও ধর্ষিতার সংখ্যা চার লাখ বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এনবিসি টেলিভিশনের করা ধর্ষিতা নারীদের উপর একটি ভিডিও রিপোর্ট নিচে তুলে দিলাম।
পাকিস্তান আর্মি যে পরিকল্পিতভাবে বাঙালি মহিলা এবং মেয়েদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ২০০২ সালের মার্চ মাসের বাইশ তারিখে ডন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি আর্টিকেল থেকে। যেখানে গণধর্ষণের বিষয়ে ইয়াহিয়া খানের মন্তব্যকে কোট করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট হিসাবে ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালে সরাসরি বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য পাকিস্তান আর্মিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যশোরে ছোট্ট একদল সাংবাদিকের সাথে কথা বলার সময় তিনি এয়ারপোর্টের কাছে জড়ো হওয়া একদল বাঙালির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন যে, ‘আগে এদেরকে মুসলমান বানাও’। এই উক্তির তাৎপর্য সীমাহীন। এর অর্থ হচ্ছে যে, উচ্চ পর্যায়ের সামরিক অফিসারদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে বাঙালিরা খাঁটি মুসলমান নয়। এই ধারণার সাথে আরো দুটো স্টেরিওটাইপ ধারণাও যুক্ত ছিল। বাঙালিরা দেশপ্রেমিক পাকিস্তানী নয় এবং তারা হিন্দু ভারতের সাথে অনেক বেশি ঘনিষ্ট।
ইয়াহিয়া খানের এই উক্তিতে উৎসাহিত হয়ে পাকিস্তান আর্মি বাঙালিদেরকে মুসলমান বানানোর সুযোগ লুফে নেয়। আর এর জন্য সহজ রাস্তা ছিল বাঙালি মেয়েদেরকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে তাদেরকে দিয়ে সাচ্চা মুসলমান বাচ্চা পয়দা করানো। পাকিস্তানী সৈন্য এবং তার এদেশীয় দোসররা শুধু যত্রতত্র ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি। জোর করে মেয়েদেরকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ধর্ষণ ক্যাম্পে। দিনের পর দিন আটকে রেখে হররোজ ধর্ষণ করা হয়েছে তাদের। পালাতে যাতে না পারে সেজন্য শাড়ী খুলে নগ্ন করে রাখা হতো তাদেরকে। সিলিং এ ঝুলে আত্মহত্যা যাতে করতে না পারে তার জন্য চুল কেটে রাখা হতো তাদের। ক্যাম্প থেকে পালিয়ে আসা এক তরুণীর কি করুণ দশা হয়েছিল তা জানতে পারবেন নিচের ভিডিও থেকে।
পাকিস্তান আর্মির দোসর রাজাকার এবং আলবদরেরা জনগণকে বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়কে সন্ত্রস্ত করে দেশছাড়া করে তাদের সম্পত্তি এবং জমিজমা দখলের জন্য ধর্ষণকে বেছে নিয়েছিল।
প্রথম আলো ব্লগে আইরিন সুলতানা তার প্রবন্ধ ১৯৭১: বীরাঙ্গনা অধ্যায় এ সুজান ব্রাউনমিলারের গ্রন্থ Against Our Will: Men, Women and Rape থেকে অনুবাদ করেছেন এভাবেঃ
Brownmiller লিখেছিলেন, একাত্তরের ধর্ষণ নিছক সৌন্দর্যবোধে প্রলুব্ধ হওয়া কোন ঘটনা ছিলনা আদতে; আট বছরের বালিকা থেকে শুরু করে পঁচাত্তর বছরের নানী-দাদীর বয়সী বৃদ্ধাও স্বীকার হয়েছিল এই লোলুপতার। পাকসেনারা ঘটনাস্থলেই তাদের পৈচাশিকতা দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়নি ; প্রতি একশ জনের মধ্যে অন্তত দশ জনকে তাদের ক্যাম্প বা ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হতো সৈন্যদের জন্য। রাতে চলতো আরেক দফা নারকীয়তা । কেউ কেউ হয়ত আশিবারেও বেশী সংখ্যক ধর্ষিত হয়েছে ! এই পাশবিক নির্যাতনে কতজনের মৃত্যু হয়েছে, আর কতজনকে মেরে ফেলা হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা হয়ত কল্পনাও করা যাবে না । (Brownmiller, p. 83)
পাকিস্তান আর্মির উচ্চ পদস্থ অফিসাররা যে ব্যাপকহারে ধর্ষণের ব্যাপারে জানতেন এবং তাদের যে এ ব্যাপারে প্রচ্ছন্ন সম্মতিও ছিল তাতে সেটা বোঝা যায় নিয়াজীর এক মন্তব্য থেকে। নিয়াজী একাত্তরে সংগঠিত র্ধষণের ঘটনা স্বীকার করার সাথে সাথে একটি অসংলগ্ন উক্তি করেছিলেন – আপনি এরূপ আশা করতে পারেন না যে, সৈন্যরা থাকবে, যুদ্ধ করবে এবং মুত্যু বরণ করবে পূর্ব পাকিস্তানে আর শারীরবৃত্তীয় চাহিদা নিবৃত্ত করতে যাবে ঝিলামে !
তবে পাকিস্তান আর্মির পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান স্বীকার করলেও সম্প্রতিকালে একজন বাঙালি গবেষক ১৯৭১ সালে পাকিস্তান আর্মি কর্তৃক বাঙালি রমণী ধর্ষণকে বিপুলভাবে অতিরঞ্জন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি হচ্ছেন হার্ভার্ড থেকে ডিগ্রিধারী ডঃ শর্মিলা বসু। তিনি তার Anatomy of Violence: Analysis of Civil War in East Pakistan in 1971 প্রবন্ধে এই উদ্ভট তথ্য প্রকাশ করেন। তার গবেষণা কর্ম ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে এবং অনেকেই তার গবেষণার পদ্ধতিকে অগভীর, ত্রুটিপূর্ণ এবং পক্ষপাতময় বলে পালটা আক্রমণ করতেও দ্বিধা করেননি। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন শর্মিলা বসুর গবেষণার সমালোচনা করে দৈনিক সমকালে একটি প্রবন্ধ লেখেন বাঙালি রমণীর পাকিস্তান সৈন্য প্রীতি নামে। নয়নিকা মুখার্জীও ওই প্রবন্ধকে সমালোচনা করে প্রবন্ধ লিখেছেন Skewing the history of rape in 1971 A prescription for reconciliation? নামে। এর বাংলা অনুবাদ করেছেন তানভীর, যা প্রকাশিত হয়েছে মুক্তমনাতেই।
কতজন ধর্ষিতা নারী গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং কতজন শিশু জন্মগ্রহন করেছিল তা পুরোপুরি অনিশ্চিত। সামাজিক অপবাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য অনেক মা-ই সেই সময় করেছিলেন আত্মহত্যা। অসংখ্য গর্ভবতী মহিলা চলে গিয়েছিলেন ভারতে বা অন্য কোথাও গোপনে সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য। অনেক শিশু জন্মেছিল ঘরে দাইয়ের হাতে যার কোন রেকর্ড নেই। দুঃখজনক হচ্ছে যে, নির্ভরযোগ্য এবং ত্রুটিহীন কোন পরিসংখ্যানই নেই আমাদের হাতে। ফলে, যুদ্ধ শিশুর সংখ্যা কত ছিল তার জন্য আমাদেরকে নির্ভর করতে হয় মুলত অনুমান এবং ধারণার উপর। সামান্য কিছু দলিলপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সরকারী এবং বেসরকারী সংগঠনের কাছে। কিছু কিছু আছে বিদেশী মিশন এবং মিশনারী সংস্থাগুলোর কাছে।
সরকারী এক হিসাবে জন্মগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা বলা হয়েছে তিন লাখ। কিন্তু সেই পরিসংখ্যানের পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। ডঃ ডেভিসের মতে প্রায় দুই লক্ষ রমণী গর্ভবতী হয়েছিলেন। কিন্তু এই সংখ্যা সম্পূর্ণ অনুমানের ভিত্তিতে করা, কোন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত নয়। সাংবাদিক ফারুক ওয়াসিফ তার ‘সেইসব বীরাঙ্গনা ও তাদের না – পাক শরীর’ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেনঃ
ধর্ষণের পরও বেঁচে থাকা নারীদের মধ্যে ২৫ হাজার জন গর্ভধারন করেছিলেন বলে জানা যায় (ব্রাউনমিলার, ১৯৭৫ : ৮৪)। ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিংস কমিটির পুরোধা এমএ হাসান দাবি করেন, ‘এ ধরনের নারীর সংখ্যা ছিল কমপক্ষে ৮৮ হাজার ২ শ’। ’৭২ সালের মার্চ পর্যন্ত ১ লাখ ৬২ হাজার ধর্ষিত নারী এবং আরো ১ লাখ ৩১ হাজার হিন্দু নারী স্রেফ গায়েব হয়ে গিয়েছিল। তারা বিলীন হয়ে গিয়েছিল বিশাল জনসমুদ্রে।’ এদের মধ্যে ৫ হাজার জনের গর্ভপাত সরকারিভাবে ঘটানো হয়েছিল বলে জানান আন্তর্জাতিক প্লানড ফাদারহুড প্রতিষ্ঠানের ড. জিওফ্রে ডেভিস। যুদ্ধের পরপরই তিনি এসব মা ও তাদের শিশুদের সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশে আসেন। ১৯৭২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি তার কাজের ওপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তৎকালীন দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার মতে, সরকার উদ্যোগ নেওয়ার আগেই ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার নারীর ভ্রুণ স্থানীয় দাই, ক্লিনিকসহ যার পরিবার যেভাবে পেরেছে সেভাবে ‘নষ্ট‘ করেছে।
ডঃ এম এ হাসানের তার প্রবন্ধ ‘The Rape of 1971: The Dark Phase of History’ তে বলেন যে, সারা দেশের গর্ভপাত কেন্দ্র এবং হাসপাতালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দশ শতাংশের চেয়েও কম সংখ্যক ধর্ষিতা সেগুলোতে ভর্তি হয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘরেই গর্ভপাতগুলো ঘটানো হয়েছে এবং সামাজিক পরিস্থিতির কারণে তা গোপন রাখা হয়েছে। এ ছাড়া যে সমস্ত মহিলারা সেপ্টেম্বরের পরে গর্ভবতী হয়েছেন বা ১৯৭২ সালের প্রথম দিকে যাদের গর্ভাবস্থা ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে তারা কেউই গর্ভপাত কেন্দ্র বা হাসপাতালে যায়নি।
বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘের আহবানে সাড়া দিয়ে ধর্ষিতা মহিলাদের গর্ভপাতের জন্য ঢাকায় পৌছায় ব্রিটিশ, আমেরিকান এবং অষ্ট্রেলিয়ান ডাক্তাররা। তারা বাংলাদেশে পৌঁছার পরেই প্রতিষ্ঠা করা হয় বেশ কিছু গর্ভপাত কেন্দ্র।। এই গর্ভপাতকেন্দ্রলো সেবাসদন নামে পরিচিত। সেখানে তারা বাংলাদেশি ডাক্তারদের সহযোগিতায় গর্ভপাত করানো শুরু করেন। সেই সময়কার সংবাদপত্রের ভাষ্য এবং বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ যেমন বিচারপতি কে, এম, সোবহান, মিশনারিজ অব চ্যারিটির সুপারভাইজর মার্গারেট মেরি, ডঃ জিওফ্রে ডেভিসের সাক্ষাতকার থেকে জানা যায় যে ঢাকার বিভিন্ন ক্লিনিকে দুই হাজার তিন শত গর্ভপাত করানো হয়েছে।
সারাদেশব্যাপী গড়ে তোলা বাইশটি সেবাসদনে প্রতিদিন তিনশ’ থেকে চারশ’ শিশু জন্ম নিতো। ক্যানাডিয়ান ইউনিসেফ কমিটির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর যুদ্ধপূর্ব এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। রেডক্রস প্রতিনিধি এবং ইউনিসেফের লোকজনের সংগে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অটোয়ার মূল অফিসে জানান যে, বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া যুদ্ধ শিশুর সংখ্যা আনুমানিক দশ হাজার। সুজান ব্রাউনমিলারের মতে সন্তান জন্ম দিয়েছিল এমন বীরাঙ্গনার সংখ্যা পঁচিশ হাজার।
বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতায় সেই সময় এই শিশুরা সমাজে তৈরি করে ভয়াবহ সংকট এবং সমস্যা। কেউ কেউ এই শিশুদেরকে বলে ‘অবাঞ্চিত সন্তান’, কেউ বলে ‘অবৈধ সন্তান’, কেউ বলে ‘শত্রু শিশু’ আবার কেউ বা নিদারুণ ঘৃণায় উচ্চারণ করে ‘জারজ সন্তান’ বলে। ফলে, এই সংকট থেকে কী করে মুক্তি পাওয়া যায় সেটাই হয়ে উঠে সেই সময়কার আশু চিন্তার বিষয়। সেই চিন্তা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়কেও ছুঁয়েছিল। শেখ মুজিব ধর্ষিতা নারীদেরকে বীরাঙ্গনা উপাধিতে ভূষিত এবং তাদেরকে নিজের মেয়ে হিসাবে উল্লেখ করলেও সেই মেয়েদের সন্তানদের ব্যাপারে তার কোন আগ্রহই ছিল না। তিনি পরিষ্কারভাবে বলে দেন যে, পাকিস্তানীদের রক্ত শরীরে আছে এমন কোন শিশুকেই বাংলাদেশে থাকতে দেওয়া হবে না। যুদ্ধ শিশুদের বিষয়ে নীলিমা ইব্রাহিম তার সংগে দেখা করতে গেলেও তিনি একথাই বলেন। এ বিষয়ে ফারুক ওয়াসিফ লিখেছেনঃ
‘যুদ্ধশিশু’ এবং তাদের মাদের একটা সুব্যববস্থা করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিম অনেক খেটেছিলেন। এদের ভাগ্যে কী হবে, তা জানতে তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তাকে বলেন, ‘না আপা। আপনি দয়া করে পিতৃপরিচয়হীন শিশুদের বাইরে (বিদেশে) পাঠিয়ে দেন। তাদের সম্মনের সঙ্গে মানুষের মতো বড় হতে দিতে হবে। তাছাড়া আমি এসব নষ্ট রক্ত দেশে রাখতে চাই না’। (ইব্রাহিম, ১৯৯৮ : ১৮)। এটি কেবল রাষ্ট্রের স্থপতি এক মহানায়কের সংকট নয়, এটা ছিল জাতীয় সংকট। গোটা জাতির হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, গ্লানি জমছিল।
শেখ মুজিবের এই বক্তব্যই হয়তো যুদ্ধ শিশুদেরকে দত্তকের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে তখন বাংলাদেশি কোন শিশুকে ভিনদেশে দত্তক দেওয়ার বিধান ছিল না, যদিও বাংলাদেশি পিতামাতা দত্তক সন্তান নিতে পারতেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত অনুরোধে জেনেভা ভিত্তিক International Social Service (ISS/AB) এর ইউএস ব্রাঞ্চ সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে যুদ্ধ শিশুদের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য। সরকারী দু’টি সংগঠন Central-Organization for Women এবং Rehabilitation and Family Planning Association কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে থাকে ISS এর পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের পুরো পর্যায় জুড়ে।
বিদেশী নাগরিকরা যাতে সহজেই যুদ্ধ শিশুদের দত্তক নিতে পারেন সে জন্য ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশে প্রজ্ঞাপিত হয় The Bangladesh Abandoned Children (Special Provisions) Order। বাংলাদেশ থেকে যুদ্ধ শিশুদের দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে সর্বপ্রথম যে দেশগুলো আগ্রহ দেখায় তাদের মধ্যে ক্যানাডা অন্যতম। মাদার তেরেসা এবং তার সহকর্মীদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং বাংলাদেশ সরকারের শ্রম এবং সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়ের চেষ্টায় দু’টো ক্যানাডিয়ান সংগঠন দত্তক প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। এর মধ্যে একটি ছিল মন্ট্রিয়ল ভিত্তিক অলাভজনক আন্তঃদেশীয় দত্তক প্রতিষ্ঠান Families for Children. এবং অন্যটি ছিল একদল উৎসাহি ক্যানাডিয়ানের গড়া টরন্টো ভিত্তিক অলাভজনক দত্তক প্রতিষ্ঠান Kuan-Yin Foundation। ক্যানাডা ছাড়াও আর যে সব দেশ এগিয়ে এসেছিল যুদ্ধ শিশুদের দত্তক নিতে তার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, সুইডেন এবং অষ্ট্রেলিয়া। এছাড়াও আরো অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থাও এগিয়ে এসেছিল সেই সময়। যুদ্ধ শিশুদের প্রথম ব্যাচ ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে ক্যানাডায় পৌঁছলে তা মিডিয়ার ব্যাপক মনযোগ আকর্ষণ করে।
আর এভাবেই রাষ্ট্র এবং সমাজের ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টায় আমাদের সন্তানেরাই মাতৃদুগ্ধ পান করার বয়সে মাতৃকোল ছেড়ে চলে যেতে থাকে অজানা দেশে, অচেনা মানুষজনের কাছে। এই চরম অমানবিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মত সবল কোন মানবিক শক্তি তখন ছিল না। মজার বিষয় হচ্ছে যে, নীলিমা ইব্রাহিম এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, মোল্লারাই বরং শুরুর দিকে এই দত্তক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। মোল্লাদের বিরোধিতার মূল কারণ ছিল যে, এই সমস্ত মুসলমান সন্তানদেরকে খ্রীস্টান দেশসমূহে পাঠানো হচ্ছে।
গীতা দাস তার মুক্তমনায় প্রকাশিত ‘তখন ও এখন’ ধারাবাহিকের ২৪তম পর্বে পাকিস্তান আর্মি কর্তৃক নির্যাতিতা তার কিশোরী মাসী প্রমিলার করুন পরিণতির কথা বর্ণনা করেছেন। সেই লেখায় আমি একটি দীর্ঘ মন্তব্য করেছিলাম। প্রাসঙ্গিক বিধায় সেই মন্তব্যটি এখানে তুলে দিচ্ছি।
আমাদের মুক্তিযুদ্ধের করুণতম অধ্যায়ের নাম হচ্ছে বীরাঙ্গনা নারী। যুদ্ধে সকল পক্ষেরই শত্রুর পাশাপাশি কোথাও না কোথাও মিত্রও থাকে। কিন্তু এইসব অসহায় নারীদের মিত্রপক্ষ বলে কিছু ছিল না। সকলেই ছিল তাদের শত্রুপক্ষ, তা সে শত্রুই হোক কিম্বা মিত্র নামধারীরাই হোক। যুদ্ধের সময় নয়মাস তাদেরকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী, আল বদর, আল শামস, রাজাকার আর বিহারীদের কাছে শারীরিকভাবে ধর্ষিত হতে হয়েছে। আর যুদ্ধের সময় বা পরে যারা তাদের মিত্র হওয়ার কথা ছিল, পরম স্নেহে বা ভালবাসায় বুকে টেনে নেবার কথা ছিল, সেই বাপ-চাচা, ভাই বেরাদারেরাই তাদেরকে ধর্ষণ করেছে মানসিকভাবে, আরো করুণভাবে, আরো কদর্যরূপে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বীরাঙ্গনাদেরকে তাচ্ছিল্য করে এর কাছাকাছি উচ্চারণের চরম অবমাননাকর একটা নামেও ডেকেছে অনেকে। আমি একে বলি সামাজিক ধর্ষণ। সামাজিক এই ধর্ষণ শারীরিক ধর্ষণের চেয়ে কম কিছু ছিল না বীরাঙ্গনাদের জন্য।
আমাদেরই কারণে যে পঙ্কিলে তাদেরকে পতিত হতে হয়েছিল অনিচ্ছুকভাবে, মমতা মাখানো হাত দিয়ে তাদের গা থেকে সেই পঙ্কিল সাফসুতরো করার বদলে নিদারুণ স্বার্থপরতা এবং হিংস্রতার সাথে আমরা তাদেরকে ঠেলে দিয়েছিলাম আরো গভীর পঙ্কিলের মাঝে। পাছে না আবার গায়ে কাদা লেগে অশুদ্ধ হয় আমাদের এই বিশুদ্ধ সমাজ। অনিচ্ছাকৃত যে গর্ভাবস্থা তারা পেয়েছিলেন শত্রুর কাছ থেকে, সমাজের রক্তচক্ষু এবং ঘৃণার কারণে তা লুকানোটাই ছিল সেই সময় সবচেয়ে বেশি জরুরী কাজ। সমাজকে বিশুদ্ধ রাখতে তাদের কেউ কেউ গর্ভনাশ করেছেন নীরবে, কেউ কেউ আবার নিজের জীবননাশ করেছেন সংগোপনে। আর যারা তা পারেননি, তারা লোক চক্ষুর অন্তরালে সন্তান জন্ম দিয়ে চলে গেছেন অজানার পথে। জন্ম মুহুর্তেই চিরতরে ছিন্ন হয়ে গেছে মা আর তার সন্তানের নাড়ীর টান। দেবশিশুর মত সেই সব যুদ্ধ শিশুরাও এখন কে কোথায় তার কিছুই জানি না আমরা। এর দায়ভার কার? আমাদের এই সমাজের নয় কি?
আমাদের উপর অত্যাচার নির্যাতনের জন্য, গণহত্যা চালানোর জন্য আমরা পাকিস্তানের ক্ষমা প্রার্থনা দাবী করি। আমরা নিজেরাই কি আমাদের সেইসব বীরাঙ্গনা এবং তাদের সদ্যজাত সন্তানদের উপর যে চরম অবিচার করেছি, যে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছি তার জন্য ক্ষমা চেয়েছি কখনো? চাইনি। চাইনি বলেই যে চাওয়া যাবে না এমন কোন কথা নেই। এখন সময় এসেছে সেই সব বীর নারীদের এবং তাদের প্রসূত যুদ্ধ শিশুদের কাছে জাতিগতভাবেই আমাদের করজোরে ক্ষমা প্রার্থনা করা। এই বিজয় দিবসে সেই অঙ্গীকারটুকুই বা আমরা করি না কেন?
দেশ স্বাধীনের পরেই পরিবারের সম্মানের কথা ভেবেই নিজেদেরকে লুকিয়ে ফেলেছিল বীরাঙ্গনা নারীরা। এই নিষ্ঠুর সমাজের কাছে কোন চাওয়া-পাওয়া ছিল না তাদের। নিয়তির কাছে সপে দিয়েছিল তারা নিজেদেরকে। যে দুঃসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাদেরকে একাত্তরে তার যাতনা ভুলে থাকা রীতিমত অসাধ্য ছিল তাদের জন্য। কিন্তু নিজের সমাজও তাদেরকে গ্রহণ করেনি সহজভাবে। বীরাঙ্গনা নামের উপাধি তাদের সম্মানের চেয়ে অসম্মান হয়ে এসেছিল বেশি। কোন কিছুর প্রত্যাশাই তারা আর করেনি আমাদের কাছ থেকে। তারপরও কি কোন এক দূর্বল মুহুর্তে মনের গহীন কোনে কোন আশা ঝিলিক দিয়ে উঠেনি তাদের মনে। আশা কি জাগেনি যে, যে দেশের জন্য তারা এতো অপমান আর যন্ত্রণা সয়েছেন সেই দেশের কেউ একজন সামান্য একটু সম্মান দেখাবে তাদের। সামান্য একটু মমতা দিয়ে জানতে চাইবে তাদের সুখ দুঃখের কাহিনী। নীলিমা ইব্রাহিমের আমি বীরাঙ্গনা বলছি গ্রন্থে বীরাঙ্গনা রীনা তার আকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন এভাবেঃ
একটি মুহূর্তের আকাঙ্খা মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত রয়ে যাবে। এ প্রজন্মের একটি তরুণ অথবা তরুণী এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে, বীরাঙ্গনা আমরা তোমাকে প্রণতি করি, হাজার সালাম তোমাকে। তুমি বীর মুক্তিযোদ্ধা, ঐ পতাকায় তোমার অংশ আছে। জাতীয় সংগীতে তোমার কন্ঠ আছে। এদেশের মাটিতে তোমার অগ্রাধিকার। সেই শুভ মুহূর্তের আশায় বিবেকের জাগরণ মুহূর্তে পথ চেয়ে আমি বেঁচে রইবো।
যে যুদ্ধ শিশুদেরকে আমরা আমাদের সমাজের শুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য বিতাড়িত করেছিলাম দেশ থেকে তারা কিন্তু বাংলাদেশেরই সন্তান। শুধু সন্তানই নয়, এই দেশের রক্তাক্ত জন্ম প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশও তারা। চোখ বন্ধ করে যতই আমরা তা অস্বীকার করি না কেন, বিবেক নামক কোন কিছুর যদি সামান্যতম অস্তিত্ব আমাদের থেকে থাকে, তবে সেখানে ঠিকই কিছুটা হলে রক্তক্ষরণ হওয়ার কথা। যদি কোনদিন ওই সমস্ত যুদ্ধ শিশুরা করুণ গলায় জিজ্ঞেস করে, বলো, কি আমাদের অন্যায় ছিল, যার জন্য তোমরা আমাদেরকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়েছো জন্ম মুহুর্তেই। বঞ্চিত করেছো আমাদেরকে মাতৃস্নেহ থেকে সারা জীবনের জন্য। এমনকি অপরিসীম ঘৃণায় দেশ থেকেও বিতাড়িত করেছো চিরতরে। আমরা কিছু বোঝার আগেই। আর সে কারণে আজ আমাদের কোন শিকড় নেই। নেই কোন মমতা মাখানো হাত দুঃসময়ে বুকে টেনে নেয়ার জন্য। নেই কোন জন্মভূমি যাকে আমরা ভালবাসতে পারি প্রাণ ভরে। আমাদের জীবনকে এরকম দুঃসহ, ছন্নছাড়া আর লণ্ডভণ্ড করে দেবার অধিকার তোমাদেরকে কে দিয়েছিল? আমাদের জন্মগত অধিকারকে কেন তোমরা কেড়ে নিয়েছিলে নিষ্ঠুরভাবে?
এর কি কোন জবাব আছে আমাদের কাছে?
জানি কোন জবাব নেই আমাদের। যে অন্যায় এবং অবিচার আমরা করেছি সাইত্রিশ বছর আগে তার প্রায়শ্চিত্ত এবং পাপমোচনের সময় এসে গেছে। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির এখন উচিত তার তাড়িয়ে দেওয়া, হারিয়ে যাওয়া হতভাগ্য যুদ্ধ শিশুদের কাছে নতজানু হয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করা। কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। পূর্ণ মর্যাদায় তাদেরকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করা। গভীর ভালবাসা দিয়ে বলা, তোমরা আমাদেরই সন্তান, আমাদেরই আপনজন। এই দেশ তোমাদেরই দেশ। কারো চেয়ে এক বিন্দু কম অধিকার নয় তোমাদের এই মাটিতে।
আসুন, বীরাঙ্গনা নারী এবং যুদ্ধ শিশুদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার মিছিলে সমবেত হই আমরা সবাই। অতীতের পাপমোচনের দায়ভার যে আমাদের সকলেরই।
মায়ামি, ফ্লোরিডা।
[email protected]
_________________________________
http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=721
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:৫৫582818
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:৫৫582818- TUESDAY, OCTOBER 23, 2007
একটি ভিডিও : ব্যক্তিগত বিজয়ের গল্প
Posted by মুহম্মদ জুবায়ের
__________________________________________
একটি ভিডিও দেখার সুযোগ হয়েছিলো। যাকে হোম ভিডিও বলা হয়, সেই গোত্রের। কোনো চলচ্চিত্র নয়, নয় কোনো নাটক বা বিনোদনের ছবি। এটি একজন মানুষের অত্যন্ত ব্যক্তিগত আত্ম-অনুসন্ধানের সফল ও আনন্দদায়ক পরিণতির ছোট্টো দলিল। কিন্তু তারপরেও সব মিলিয়ে ভয়াবহ এক করুণ গল্পের আভাস দেয় এই ভিডিও। ঘণ্টাখানেক দৈর্ঘ্যের ভিডিওটি অবশ্য শুধু ওই পরিণতির ছবিটি দেখায়, সম্পূর্ণ গল্প বলে না। সেই অর্থে ভিডিওটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। হওয়ার কথা নয়, কেননা গল্প বলা এর উদ্দেশ্য ছিলো না। এটি একান্তই ব্যক্তিগত দলিল। পরে প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য, পেছনের গল্প এবং পরবর্তী ঘটনাবলির ভাসা ভাসা বিবরণে যা জেনেছি, তারই একটি ছবি তুলে আনার চেষ্টা করা যায়।
ভিডিওর শুরুতে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের শহুরে মধ্যবিত্ত বাড়ির একটি টেবিলে, ডাইনিং টেবিল বলে ধারণা হয়, দুটি চেয়ারে বসে আছে দু'জন নারী। একজন বয়স্ক, চেহারায়, পোশাকে গ্রামীণ মানুষের ছাপ। কথা বলে বগুড়া শহর বা তৎসংলগ্ন অঞ্চলের ভাষায়। এই মুহূর্তে তার বয়স অনুমান করা যায় না, ধারণা করা যাবে ভিডিও দেখার পরে আনুষঙ্গিক কাহিনীটি জানা হলে। অন্যজন বয়সে তরুণী, মাথাভর্তি কোঁকড়া চুলগুলিই প্রথমে চোখে পড়ে। রং-চেহারায় পুরোপুরি বাঙালি ছাপ থাকলেও কথা বলে মার্কিনি ধাঁচের ইংরেজিতে। তার পরণের পোশাকটি অবশ্য কোনো তথ্য জানায় না, সূত্রও পাওয়া যায় না। আজকাল বাংলাদেশে শহরের অনেক মেয়েও এ ধরনের পোশাক পরে।
দুই নারী পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। একজন মহিলা দোভাষী, যাঁকে ক্যামেরায় দেখানো হচ্ছে না, একজনের কথা সাবলীলভাবে অনুবাদ করে জানাচ্ছেন অন্যজনকে। এই কথোপকথন থেকে অবিলম্বে জানা যায়, ইংরেজি-বলা তরুণীটি ওই বয়স্কার কন্যা।
বিবরণের সুবিধার জন্যে এদের একটি করে কাল্পনিক নাম দেওয়া যাক। আমরা বয়স্কাকে আমিনা এবং তরুণীকে সামিনা নামে চিনবো। তিরিশ বছর পরে, সামিনার জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার পর, এই তাদের প্রথম সাক্ষাত। ভিডিওতে ধরা ছবিতে দেখা যায়, একজন আরেকজনকে ক্রমাগত স্পর্শ করে, অনুভব করার চেষ্টা করে। পরস্পরের অজানা অসম ভাষায় হৃদয়ের যে আর্দ্রতা-ভালোবাসার পূর্ণ প্রকাশ ঘটতে পারে না, স্পর্শে তা সঞ্চারিত হতে থাকে। বস্তুত, প্রথমবারের সাক্ষাতে আজীবনের বিচ্ছেদ ও অদেখার তৃষ্ণা আর কিছুতেই মেটে না বলে বোধ হয়।
একসময় সামিনা ক্রমাগত চোখের পানি মুছতে থাকলে তার মা বলে ওঠে, 'ওঙ্কা কর্যা চোখ মুছপার থাকলে চোখ বিষ করবি রে মা...'। অনূদিত হয়ে কথাটি মেয়ের কাছে পৌঁছুলে কান্নাচোখেই হেসে ফেলে সে, 'আমার চোখ সত্যিই ব্যথা করছে, মা'। মায়ের মাথায়, কপালে, চুলে, গালে হাত বুলিয়ে মেয়ে একবার হাসে, একবার কেঁদে ওঠে, 'এতোদিন পর সত্যি তোমার দেখা পেলাম, মা গো! এই দিনের জন্যে আমি অপেক্ষা করেছি আমার সারাটা জীবন ধরে!' মেয়ের তুলনায় মায়ের আবেগ খানিকটা নিয়ন্ত্রিত মনে হলেও তার চোখও ভিজে ওঠে।
আরো খানিকক্ষণ এই ধরনের কথোপকথন চলে। পরস্পরকে জানা হয়, স্পর্শে আনন্দ-বেদনার বিনিময় ঘটে। তারপর দেখা যায়, মা-মেয়েতে মিলে বগুড়ায় গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছে। কোনোদিন-না-দেখা আমেরিকানিবাসী এই গ্রামের মেয়েটিকে প্রথমবারের মতো দেখতে মানুষ ভেঙে পড়ে। মায়ের বাড়িঘরের হতদরিদ্র (হয়তো বাংলাদেশের বিচারে অতোটা খারাপ নয়, কিন্তু মেয়েটির অনভ্যস্ত চোখে তো তাই মনে হবে!) চেহারা দেখে মেয়ে। দেখে তার গ্রামের মানুষদের। কোনোদিন না-দেখা এক ভাইকে জড়িয়ে ধরে সে কাঁদে।
ভিডিওটি মোটামুটি এইভাবে শেষ হয়। অনিবার্যভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠে আসে। এই দু'জন নারী, যারা পরস্পরের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত, একের থেকে অন্যজন আলাদা হয়ে গিয়েছিলো কীভাবে? কেন তাদের পরস্পরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের জন্যে তিরিশ বছর অপেক্ষা করতে হলো? ভিডিওতে দু'জনের সাক্ষাতের আবেগার্দ্র মুহূর্তগুলো দেখে কৌতূহল বেড়ে উঠতে থাকে। বন্ধু দম্পতির বয়ানে কাহিনীটি জানা হয়। সেই গল্প যেমন করুণ ও হৃদয়বিদারক, তেমনি নিবিড় অনুসন্ধানী এক নারীর জয়ী হওয়ার ইতিবৃত্ত।
ভিডিও ধারণের তিরিশ বছর আগে আমিনা ছিলো গ্রামে বেড়ে ওঠা সাধারণ পরিবারের একজন সদ্য-তরুণী। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশে পনেরো-ষোলো বছর বয়সী তরুণীদের জন্যে নিরাপদ কোনো জায়গা ছিলো না। পাকিস্তানী উর্দিধারীদের হাতে পড়েছিলো আমিনা। তার সদ্য-তারুণ্যের স্বপ্ন হয়ে উঠেছিলো দুঃস্বপ্ন। যে বয়সে চারদিকের পৃথিবী রঙিন হয়ে ওঠার কথা, আমিনার জগৎ সেই সময়ে ঘিরে ফেলেছিলো এক নিকষ অন্ধকার। পরবর্তী কয়েক মাস তার বদ্ধ পৃথিবীতে কালো ছাড়া আর কোনো রং ছিলো না, যন্ত্রণা ও গ্লানি ছাড়া কোনো অনুভূতি ছিলো না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর উদ্ধার পেয়ে নিজেকে সে আবিষ্কার করে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক জায়গায়, তার নাম-ধামও সে জানে না। শুধু বুঝেছিলো, জায়গাটা নিজের গ্রাম থেকে অনেক দূরে।
একদিক থেকে হয়তো ভালোই হয়েছিলো, তখন তার ঘরে ফেরা সম্ভব ছিলো না। শরীরের ভেতরে আরেকজন মানুষের উপস্থিতির সমস্ত লক্ষণ তখন প্রকাশ্য। অচেনা জায়গাই তার জন্যে স্বস্তিকর তখন। অল্পদিন পরে একটি মেয়ে ভূমিষ্ঠ হলে শিশুটিকে রেডক্রসের লোকদের হাতে তুলে দিয়ে আমিনা ফিরে গিয়েছিলো নিজের গ্রামে। মেয়েটির জন্যে তার কোনো অনুভূতি বা ভালোবাসা তৈরি হয়নি, তাকে তো আমিনা ভালোবেসে জন্ম দেয়নি। এক পাশবিকতার ফসল হয়ে সে এসেছিলো পেটে, তার জন্যে সুন্দর অনুভূতি তৈরি হওয়ার কোনো সুযোগই ছিলো না! দুঃস্বপ্ন কোনো ভালো অনুভূতি দেয় না।
এতোকিছুর পরেও মানুষের বেঁচে থাকার সহজ প্রবণতাই হয়তো আমিনাকে স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিলো। কালক্রমে তার বিয়ে হয়, স্বামী-সন্তান নিয়ে সংসারও হয়। তবু কখনো কোনো উদাস মুহূর্তে পরিত্যক্ত মেয়েটির কথা কি কখনো তার মনে হয়নি? নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু কোনোদিন কাউকে বলা যায়নি সে কথা। ভয়াবহ ও গোপন এই কাহিনী কারো সঙ্গে ভাগ করা যায় না, নিজের মনের গহীনে লুকিয়ে রাখতে হয়।
এদিকে সামিনাকে সেই শিশুকালেই রেডক্রসের লোকেরা যুদ্ধশিশু হিসেবে আমেরিকায় নিয়ে যায়। পরে একটি পরিবার তাকে দত্তক নেয়। বোধ-বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে দত্তক নেওয়া পরিবারেরই একজন হিসেবে নিজেকে জেনে এসেছে সে। পরে বড়ো হয়ে একসময় জেনেছে, সে আসলে যুদ্ধশিশু। তখন থেকে তার অনুসন্ধানের শুরু। সে বুঝে যায়, পৈত্রিক পরিচয় কোনোদিনই আর উদ্ধার করা যাবে না, কিন্তু মায়ের সন্ধানে সে অক্লান্ত, একাগ্র হয়ে থাকে।
অনেক বছরের সন্ধানের পরে আমিনার নাম-ঠিকানা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় নিজের মা হিসেবে। রেডক্রসের কাগজপত্র ঘেঁটে নিশ্চিত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রনিবাসী বাংলাদেশের এক বন্ধুর মাধ্যমে সে আমিনার কাছে এই মর্মে খবর পাঠায় যে, হারিয়ে যাওয়া মেয়েটি তার সাক্ষাৎপ্রার্থী। যোগাযোগ করা হলে আমিনা এ বিষয়ে কোনো উৎসাহ দেখায় না, কোনো কথা বলতে আগ্রহী নয় সে, ব্যাপারটাকে সত্যি বলেও স্বীকার করে না।
আমিনার মৌখিক অস্বীকারের যুক্তি বোঝা দুরূহ নয়। যে সত্য এতো বছর ধরে সে আড়াল করে এসেছে, স্বামী-সন্তান-সংসারের বাস্তব পৃথিবীতে যে সত্যের কোনো অস্তিত্ব এতোদিন ছিলো না, সেই সত্য তার যাবতীয় অন্ধকার ও দুঃখস্মৃতিসহ সামনে এসে উপস্থিত হলে তাকে মেনে নেওয়া সহজ নয়। আমিনার সমস্ত পৃথিবী যে ওলটপালট হয়ে যাবে! জানাজানি হলে মানুষের কাছে মুখ দেখাবে সে কী করে? আরো কঠিন কথা, যে মেয়েকে জন্মের পরেই সে পরিত্যাগ করেছে, নিজের সন্তান বলে স্বীকৃতি দেয়নি মনে মনেও, মা হয়ে তার সামনে দাঁড়াবে কোন দাবিতে?
এই দোটানারও শেষ হয় একদিন। সামিনা আরো কয়েকবার চেষ্টা করেও আমিনার মন গলাতে পারে না। শেষমেশ সামিনা খবর পাঠায়, সে বাংলাদেশে আসছে এবং নিজে মায়ের সামনে দাঁড়াবে। তখন দেখবে, কেমন করে মা তাকে অস্বীকার করে, ফিরিয়ে দেয়!
আমিনার তখন সত্যের মুখোমুখি না হয়ে উপায় থাকে না। বুকভরা আকুতি আর চোখভরা জল নিয়ে সে ঢাকায় আসে মেয়ের সঙ্গে মিলিত হতে। তিরিশ বছর পর।
তার আগে এই সত্য স্বয়ং আমিনাকেই উন্মোচন করতে হয় স্বামীর কাছে, পুত্রের কাছে। গ্রামের প্রতিবেশীদের কাছে। আত্মীয়-পরিজনের কাছে। সে বিস্মিত হয়ে দেখে, তার আশঙ্কা সত্যি হয়নি। তার নিজের চেনা পৃথিবী উল্টে যায়নি। কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন করেনি, অভিযোগের আঙুল তার দিকে তোলেনি, কলঙ্কের ছবিও কেউ আঁকতে বসেনি। বরং ভালোবাসা, সহানুভূতি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। আমিনা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে, মানুষ আজও মানুষ আছে। বয়স্কদের মনে সেই সময়ের স্মৃতি এখনো খুবই জাগ্রত। সেইসব মানুষেরা জানে, মানুষের মতো দেখতে একদল অমানুষ আমিনাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলো, কিন্তু তাতে সে অপবিত্র হয়নি।
তারা আরো জানে, সামিনার জন্মের ইতিহাস তার নিজের রচিত নয়, সেই ইতিবৃত্ত রচনায় তার কোনো ভূমিকাও ছিলো না। যে লোকটি এখন আমিনার স্বামী, সামিনাকে সে কন্যার স্নেহ দিতে কার্পণ্য করে না, তার পুত্র - সমপর্কে সামিনার সৎভাই - সামিনাকে বোন বলে জড়িয়ে ধরে। দুই ভাইবোনে গলা জড়িয়ে কাঁদে।
সামিনার সঙ্গে আমিনার প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তটিতে ভিডিওর শুরু। বেদনাময় মধুর তার পরিসমাপ্তি।
যুদ্ধ, বিপ্লব বদলে দেয় রাষ্ট্র ও সমাজ, তা নিয়ে রচিত হয় ইতিহাস। তার প্রতিক্রিয়ায় ব্যক্তিমানুষের জীবন যে কীভাবে পাল্টে যায়, যুদ্ধের হিংস্র ও দয়াহীন নখর যে কী গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত তৈরি করে রেখে যায় কারো কারো জীবনে, তারই এক আশ্চর্য ও অসামান্য দলিল এই ভিডিও। এই দলিল ইতিহাস বটে, তবে তা ব্যক্তিগত। কেতাবী ইতিহাস ব্যক্তিমানুষের জীবন বা তার অনুভবের কারবারী তো নয়!
___________________________
http://muhammedzubair.blogspot.com/2007/10/blog-post_6785.html
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:৫৮582829
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:৫৮582829- Bangladesh's erased past
Bina D'costa
Dec 30, 2008
____________________________________
Every year Bangladesh celebrates its Victory Day on December 16 – a day when a new nation was born in 1971. Here Australian National University researcher Bina D'Costa digs the past of the country and finds that there are still many troubling memories that linger, especially those of ‘war babies’.
Bangladesh celebrated its birth on 16 December 1971 – now celebrated as Victory Day, a day of reminiscence for citizens of the new nation. But many memories are troubling, especially those of the ‘war babies’ – children born during or after the War of Liberation, as a result of the often-planned and systematic rape of Bangladeshi women.
If we turn back the pages of Bangladesh’s history, we can get some rare glimpses of the marginalised; but there is still complete silence when it comes to the babies of war.
The nine months of armed conflict that resulted in East Pakistan breaking away to become an independent Bangladesh is a story of blood and tears.
Official and unofficial estimates of deaths range widely between 300,000 and three million. In addition to the mass killings, a large number of Bangladeshi women were subjected to sexual violence; the official figure is some 200,000.
Official and unofficial estimates of deaths range widely between 300,000 and three million. In addition to the mass killings, a large number of Bangladeshi women were subjected to sexual violence; the official figure is some 200,000.
In denial mode
While Pakistan has not been immune from the trauma of war, its government has repeatedly denied the allegations of genocide in East Pakistan/ Bangladesh. Some recent sceptics have also questioned the numbers both of people killed and of women raped.
How do we know that targeting women in this manner was a deliberate strategy on the part of the Pakistan Army? An article in the Dawn published on 22 March 2002 quotes Yahya Khan on the matter. As president, Yahya had directly ordered the army crackdown on East Pakistan in 1971. While talking to a small group of journalists in Jessore, in southwest Bangladesh, he pointed towards a Bengali crowd that had assembled on the fringes of the Jessore airport.
According to the article’s account, he said, in Urdu, Pehle inko Musalman karo (First, make them Muslim). This anecdote is significant, for it demonstrates that at the senior-most level of the Pakistan Army there was a perception that Bengalis were not loyal Muslims. These perceptions also fed into two other stereotypes: that Bengalis were not patriotic Pakistanis, and they were too close to Hindu India.
This complex relationship among the three countries can be traced through the bitter Partition memories of abduction, the rape of thousands of women and children, and the ‘train incidents’ in which passengers of one community or the other were murdered en masse. The tragedy of the mass exodus in 1947 has shaped India’s and Pakistan’s stances towards each other, and East Pakistan became a significant pawn in this rivalry.
From the beginning, Pakistan held India responsible for the Bangla national movement; in the process, it overlooked the growing discontent of the people of East Pakistan due to economic and political inequality with West Pakistan, and underestimated the people’s power.
From the beginning, Pakistan held India responsible for the Bangla national movement.
The leadership in Islamabad had always considered Bengalis to be not only weak and powerless, but Hinduani – too close to Hindu religious and cultural practices. As such, for Pakistan, Bengalis/ East Pakistanis needed to be purged off this Hindu-ness.
Salma Sobhan, an activist and scholar, documented that from the initial stages of the conflict, the Pakistan Army boasted about its opportunity to “convert East Pakistan through engendering true Muslims” – meaning forced impregnation. Yahya’s order to make Muslims out of Bengalis was carried out most cruelly and literally during the nine months of conflict, when an estimated 200,000 women and children were systematically subjected to rape.
Pakistani soldiers and their collaborators raped women in their homes, in their local areas, or even forcibly took them to ‘rape camps’. In this process, there were various lists created of names and numbers, which many social workers talked about with this writer. Many of those lists were deliberately burned by the post-war government in 1972, and the remaining lists were all destroyed during 1978-80 and again in 1985-86 by subsequent governments.
Besides forced impregnation, there were other rationales for widespread rape, as well. The army used rape to terrorise the populace, to extract information about the insurgency, to boost the morale of soldiers, and to crush the burgeoning Bangladeshi national identity.
In addition, the Pakistan Army’s local militia, known as the Razakaar and al-Badr, used rape to terrorise, in particular the Hindu population, and to gain access to its land and property.
In addition, the Pakistan Army’s local militia, known as the Razakaar and al-Badr, used rape to terrorise, in particular the Hindu population, and to gain access to its land and property.
It should also be noted that sexual violence was also perpetrated against women in the Urdu-speaking Bihari community, in particular immediately after the emergence of an independent Bangladesh.
A large number of Biharis believed in a unified Pakistan, and actively supported its military crackdown. As a result, after the war, many Bihari women and young girls were raped to avenge rapes of Bengali women.
25,000 cases
Due to the nature of their conception, war babies in Bangladesh experience significant stigma and prejudice, and it is unsurprising that they are rarely, if ever, represented in the Victory Day celebrations of Bangladesh. After the war, Pakistan denied charges of genocide and mass rape. But Islamabad’s refusal to take responsibility was matched by Dhaka’s failure to hold the perpetrators responsible for these war crimes.
Official documents suggest that there were at least 25,000 cases of forced pregnancy in the aftermath of the war. Bangladeshi leaders entrusted social workers and medical practitioners with the primary responsibility of dealing with the raped women; as a result, International Planned Parenthood, the Red Cross and the Catholic Church became involved in rehabilitation programmes.
These organisations also became responsible for carrying out the daunting task of dealing with the pregnancies. Two activities thus began to take place simultaneously: the programme that allowed pregnant women to have abortions, and the programme for the adoption of war babies.
From this writer’s interviews with some prominent social workers and medical practitioners directly involved with the war babies, it is clear that while many of these workers were genuinely committed to supporting the victims, there were occasions when decisions of terminating pregnancy or giving up the baby for adoption went contrary to the women’s own choices.
In addition, there were instances in which pleadings by young pregnant girls one way or the other were ignored, with the women being considered too young to make mature decisions.
Confusion over how to deal with the war babies appears to have gone to the very highest levels. Then-Prime Minister of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman repeatedly referred to these birangona (valiant) women as his “daughters”, and asked the nation to welcome them back into their communities and families.
However, he also declared that “none of the babies who carry the blood of the Pakistanis will be allowed to remain in Bangladesh.”
Nilima Ibrahim, a prominent social worker and feminist author, recalls her meeting with Sheikh Mujibur, in her book Ami Birangona Bolchi. When questioned about the status of the war babies, the prime minister said, “Please send away the children who do not have their father’s identity. They should be raised as human beings with honour. Besides, I do not want to keep those polluted blood in this country.”
Perhaps such statements aided the push for adoption. In addition, however, through state-sponsored programmes, International Planned Parenthood and the International Abortion Research and Training Centre, local clinics helped women to carry out abortions. Clinics were set up with the support of the Bangladesh Central Organisation for Women’s Rehabilitation in Dhaka and 17 outlying areas, in order to cope with unwanted pregnancies.
Geoffrey Davis, a medical graduate from Australia who worked in Bangladesh for a half-year in 1972 with International Planned Parenthood and other organisations, was one of the key individuals involved in administering the government-sponsored abortion programme.
In an interview with this writer in 2002, he recalled some of the appalling stories he had heard, including of women who reported being raped multiple times by Pakistani soldiers.
According to Davis, women considered pretty were kept for the officers, while the rest were distributed among the ranks. The women did not get enough to eat, and when they fell ill, many died in the camps.
A large number of survivors would never be able to bear children due to psychological and physical abuse. Davis reported that prior to the official abortion programme, most of the survivors had already undertaken abortions with the assistance of local dais (midwives) or untrained local doctors.
A large number of survivors would never be able to bear children due to psychological and physical abuse.
By the time he arrived in Bangladesh, shortly after the Liberation War, nearly 5000 women had already managed to abort their babies through medically unsafe methods. He also accused the new government of providing inaccurate information concerning the number of women subjected to sexual violence during the nine months of Pakistan Army occupation.
Furtive adoptions
An appeal was issued by Mother Teresa urging women not to have abortions, and instead to contact the Missionaries of Charity, which offered to take care of the war babies. In December 1971, Mother Teresa and M, a social worker who does not want to be named, visited some of the camps for rape victims in Bangladesh.
In an interview, M recalled that Mother Teresa did not find girls at the camps, but only their hair, petticoats and a few other items. Their hair had been cut off because the Pakistan Army soldiers feared that the girls would attempt to commit suicide by tying their hair to ceiling fans, as some had already done. M went back to Bangladesh at the request of Mother Teresa on 21 January 1972, where she arranged for the adoption of war babies, most of whom were adopted by families in Canada, with some were also sent to France and Sweden.
In 1972, the Bangladesh government established the Women’s Rehabilitation Organisation to institutionalise women’s-rehabilitation projects, with the National Central Women’s Rehabilitation Board coordinating the government’s post-war policies.
Under the Bangladesh Abandoned Children (Special Provision) Order of that year, the government encouraged foreign adoption agencies to take war babies from Bangladesh. The US branch of the Geneva-based International Social Service was the first international adoption agency to work in post-war Bangladesh.
Through the Missionaries of Charity, other institutions also became involved in the programme, including Families for Children and the Kuan-Yin Foundation (both in Canada), the Holt Adoption Program (US) and Terre des Hommes (Switzerland).
In an interview, Nilima Ibrahim said that Muslim clerics initially protested about the adoption policies because the babies were being sent to Christian countries. But this resistance was not the only obstacle to overcome. “Many girls cried and did not want to give their babies away … We even had to use sedatives to make the women sleep and then take the babies.”
Ibrahim’s recollections highlight the fact that women had limited, if any, choice about the future of their babies. The social workers obviously wanted to help these women, but eventually the trauma experienced by the women was mostly ignored. This seems to have come about due to the ‘purity’ of the state being given higher priority than the social workers’ perspective that the women should be protected.
B, another prominent social worker who was also reluctant to be named, confirmed that in the aftermath of the war, the Bangladesh government responded in two ways, neither of which were sensitive to the women’s needs. First was through abortion programmes, and the second was the enactment of adoption laws, though only for the immediate post-conflict period.
Adoption of Bangladeshi children is not permitted under the country’s law; and while Bangladeshi citizens can be foster parents, this is a difficult process. While talking about the rejection of some of these women by their families, B recalled the case of one young girl who had given birth. Prior to delivery, she said she wanted to give her baby for adoption,” B said. “But when the time came, she refused to do so, and cried so much.”
An erased past
Some of the interviews conducted by this writer suggest that social workers and medical and humanitarian practitioners often employed their own personal strategies, based on their understanding of the realities that surrounded them. Ibrahim, for instance, supported the women in their silence. M encouraged and expedited international adoption. B implemented state policies regarding women’s reintegration. And Davis carried out the abortion programmes according to the state’s policies.
While scattered narratives point to the experiences of children who fought during the war and were raped by the Pakistan Army or brutally killed, almost nothing is known about the destiny of the war babies. By now, they have largely disappeared from the official history of Bangladesh.
While scattered narratives point to the experiences of children who fought during the war and were raped by the Pakistan Army or brutally killed, almost nothing is known about the destiny of the war babies.
The state acted as the moral agent, deciding who could stay and who could leave. Although the social workers and humanitarian and medical practitioners considered themselves to be working in the best interests of the war babies and their mothers, the assumption that they should be separated ultimately deprived the babies a chance to be raised by their birth mothers. This also generated additional trauma for already distressed women.
Today, there is very little information about these children – about how they have developed, about how they often lived without social recognition within their societies, about what happened to those who were adopted by people from other countries. In recent years, the humanitarian community has shown interest in integrating children born out of sexual violence during conflict through post-conflict humanitarian efforts, migration policies and refugee-settlement programmes.
This writer sent an appeal to several adoption agencies, Bengali websites and newspapers to talk about the war babies, but only a few of them wanted their stories to be public. The following e-mail was sent by one website owner: “I had a lousy dad, who just insulted me … I tried to commit suicide four years ago … I often wonder why I am here in Canada, adopted by parents who divorced three months after I was adopted … I hated being a kid, and I am angry at Bangladesh for not taking care of me when I needed it most. I don’t have any roots and that makes me cry. So that is why I am trying to learn more about where I was born.”
There is no way of knowing the fate of all the adopted war babies. Undoubtedly, however, their past and the trauma of violence that is linked to their births have haunted nearly all of them. Perhaps, by tracing through their histories, it could be possible for Bangladesh to obtain crucial data regarding its own interlinked past.
But in this, it must be understood that it is not ethical to try to find these individuals, nearly all of whom have no intention to be found. Instead, it is more important to understand how, three and a half decades ago, the state, families and communities united to construct a destiny for Bangladeshi women and the war babies. This understanding would also benefit the movement in Bangladesh to seek redress for war crimes committed in 1971.
Bina D'Costa is a research fellow at the Centre for International Governance and Justice at the Australian National University.
_____________________
http://southasia.oneworld.net/peoplespeak/bangladeshs-erased-past#.UMyFveSGzIc
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ ২০:০২582840
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ ২০:০২582840- ৭১ এর জেনোসাইড(পাক সেনাবাহিনী)
লিখেছেন: সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড
তারিখ: ৪ শ্রাবণ ১৪১৯ (জুলাই ১৯, ২০১২)
__________________________________________
খাবার পেলে প্রথমেই সবল ঝাঁপিয়ে পড়ে,ছিঁড়ে খুড়ে খায় আর দূর্বল দূরে দাড়িয়ে দেখে। সবলের উদর পূর্ণ হলে সবল ঢেঁকুর তোলে আর দূর্বল মাঠে নামে,এর পর আস্তে আস্তে আসে আরো শক্তিহীনেরা।
মৃত হরিনের বুক খাবলে বাঘ যখন চলে যায় তখন খেকশিয়াল ঝাঁপিয়ে পড়ে,খেকশিয়ালও যখন চলে যায় তখন আসে কাক,চিল,শকুন।
বাংলাদেশ নামক এই ছোট পাখিটার বুক খামচে খেয়েছে শাসকেরা কয়েক দফায়। প্রথমে খেয়েছে আংরেজ সাহেবেরা,এর পর খামচে খেয়েছে পাকিস্তানী শাসক, সেনা আর তাদের দোসরেরা।
বাংলাদেশে যখন সেনা মোতায়ন করা হয় ১৯৭১ সালে,তখন তাদের গনহত্যার আদেশ দিয়েই পাঠানো হয়,এবং সাধারন সৈনিকও বুঝে ফেলে এই মিশনে এবং এর পরবর্তীতে তাদের কোন জবাবদিহিতা করতে হচ্ছে না। আর সেই সাথে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে নিরীহ,নিরস্ত্র বাঙালীকে,বিজয় নিশ্চিত ভেবেই হিংস্র ও অমানুষিক হয়ে ওঠে পাক সেনারা।
মাও সে তুং এর একটা বিখ্যাত কথা আছে ” বন্দুকের নলই সকল ক্ষমতার উৎস”। ১৯৭১ সালে পাক সেনাদের হাতে ছিল অস্ত্র আর ম্যাসাকারের আদেশ,হাতে অস্ত্র থাকলে মানুষের শরীরে নাকি অদ্ভুত এক ক্ষমতার আবেশ চলে আসে,ব্যতিক্রম হয়নি ১৯৭১ সালেও। সেনারা হাসতে হাসতে আগুন দিয়েছে গ্রামে,বেয়োনেটে গেথেছে শিশুকে,মায়ের কোল থেকে শিশুকে টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে আগুনে।
সারা বাংলাদেশের নারীকে করছে রেপ,শুধু রেপ করেই ক্ষান্ত হয়নি হায়েনার দল,দু পায়ের মাঝে বেয়োনেট ঢুকিয়ে হত্যা করেছে,স্তন কেটে নিয়েছে,খোলা মাঠে নগ্ন নৃত্য করাতে বাধ্য করেছে।
৭১ এর জেনোসাইড নিয়ে লেখা এই পর্বে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তৎকালীন গণহত্যার সাক্ষী কিছু মানুষের বক্তব্য,কিছু বই ও আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রের অংশবিশেষ।
এন্থনি মাসকেরহানস
The rape of Bangladesh
পৃষ্ঠা- ১১৬-১১৭
বাংলাদেশের উপরে চালানো গণহত্যার লক্ষ্য নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। মূলত তারা ছিলেন
১) বাঙালী সৈনিকেরা,যারা কর্মরত ছিলেন সামরিক বাহিনীতে ( ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট),পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসে,পুলিশ এবং আধা সামরিক আনসার বাহিনীতে।
২) হিন্দু জনগোষ্ঠী- কিছু কিছু সৈনিকের বক্তব্য ছিল এমন “ আমরা শুধু হিন্দু পুরুষদের হত্যা করছি,নারী এবং শিশুদের মুক্তি দেয়া হবে।“ তাদের ধারনা ছিল একজন নিরীহ ও নিরস্ত্র হিন্দু পুরুষকে হত্যার মধ্যে হয়ত গৌরব রয়েছে।
৩) আওয়ামিলীগার- সকল সমর্থক,কেন্দ্রীয় পর্যায়ের নেতা থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের সকল নেতা কর্মী ছিল হত্যার লিস্টে।
৪) শিক্ষার্থী- কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় এর ছাত্র ছাত্রী,এবং আন্দোলনরত কিংবা মিছিল মিটিঙে অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থী।
৫) বাঙালী বুদ্ধিজীবী- বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষক,প্রফেসর এবং খ্যাত ব্যক্তিবর্গ।
প্রফেসর হরিধন দাসের নিজের কিছু কথা পাওয়া যায় Genocide in Dhaka University: 1971 বইটিতে। সেখানে তিনি বর্ননা করেছেন পাক সেনাবাহিনীর বীভৎসতার কথা।
প্রফেসর হরিধন দাস
ভিক্টোরিয়া কলেজ,কুমিল্লা।
(Quoted from “Genocide in Dhaka University: 1971, The Jagannath Hall” by Prof Ratanlal Chakraborty, Dept of History, University of Dhaka)
“দরজায় ভারী বুটের আঘাত। হাত মেলানোর পর আমরা একে অন্যের থেকে আলাদা হয়ে গেলাম। যত জোরে সম্ভব আমরা তিনজনে চিৎকার দিয়ে উঠলাম। এরপর তিনজন ঘরের তিন কোনায় ছড়িয়ে পড়লাম। আমি ছিলাম দরজার পেছনে। ভারী গুলির বর্ষনে দরজা ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেলো। হঠাৎ দুটি গ্রেনেড বিস্ফোরিত হল। খুনিটি বলে উঠলো, “বল জয় বাংলা,বাইনচোদ! শেখ মুজিবর কোথায়?” একটি পেন্সিল টর্চের সাহায্যে ওই ঘাতকগুলো ওদের ধ্বংসযজ্ঞ দেখে নিল। এরপর ওই দানবগুলো পরবর্তী দরজার দিকে পা বাড়াল। তাদের ওই ধ্বংসযজ্ঞ বিরতিহীনভাবে সকাল পর্যন্ত চললো। এরই মধ্যে আমার রুমে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল।
গানপাউডারের গন্ধে আমার শ্বাসরোধ হয়ে আসছিলো। ভাঙ্গা দরজার নিচে চাপা পড়ে আমি সব কষ্ট সহ্য করছিলাম। সুশীল এবং অন্যান্য বন্ধুদের কি হয়েছে দেখার জন্য আমি বহু কষ্টে আমি ভাঙ্গা দরজার নিচ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসলাম। ওরা কোথায়? সারা রুম হন্তদন্ত হয়ে খুঁজে আমি কিছুই পেলাম না। কিভাবে এতো পানি আর পিচ্ছিল পদার্থ এলো আমার রুমে? যেহেতু ধীরে ধীরে আমার জ্ঞান ফিরে আসছিলো আমি বুঝতে পারলাম যে ভারী গুলি বর্ষণ এবং গ্রেনেড চার্জের কারনে ওদের শরীর ঝাঁঝরা/ছিন্নবিন্ন হয়ে গিয়েছে।
ওরা শহীদ…………আমি দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারছিলাম না, মনে হচ্ছিলো আমার বাম পা শরীর থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছে। আঙ্গুলগুলো অসাড় হয়ে গিয়েছিল। রক্তে এবং ক্ষতে আমার সারা শরীর ভরে গিয়েছিল। আমি আমার গায়ের হাফ হাতার শার্টটি দিয়ে পা কোনমতে মুড়িয়ে ফেললাম।
আর বারুদের শব্দ, গ্রেনেড আর মৃত্যুর আর্তনাদ……..
জন হেস্টিংস এর কিছু কলাম নিউজউইকে ছাপা হয়,সেগুলো ছিল সত্যি হৃদয়বিদারক। হেস্টিংস তার বেশ কিছু কলামে রুমেল এর তথ্যসূত্র ও বক্তব্যও ব্যবহার করেন।
John Hastings, A Methodist missionary worked in Bangladesh for 20 years.
(from Newsweek)
আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি তারা সাধারন জনগণের উপরে কি নির্মম অত্যাচার করেছে। রক্ষা পায়নি শিশুও। তারা খেলার ছলে শিশুকে ছুঁড়ে দিয়েছে উপরে,তারপরে তাকে গেঁথেছে রাইফেলের বেয়োনেটে। রক্ষা পায়নি নারীও। তারা পালাক্রমে ধর্ষণ করেছে নারীকে,তারপর হত্যা করেছে দু পায়ের মাঝে বেয়োনেট গেঁথে।
এছাড়াও নিউজ উইকের আর একটি সংবাদ সবাইকে নাড়িয়ে যায় ভীষণ ভাবে। নীচে সংবাদটির অনুবাদ দেয়া হোল।
Neewsweek
লাল এবং সবুজ ফুলওয়ালা জামা পরা মেয়েটির গল্পে আছে এক আজব বীভৎসতা। সে কারো জন্য ক্ষতির কারন ছিল না। আমি ওর সাথে দেখা করেছিলাম কৃষ্ননগর, বিচলিতভাবে অন্যান্য রোগীদের মাঝে আটকে ছিল, যেখানে এক পাকিস্তানি সৈনিক তার বেয়নেট দিয়ে নির্মমভাবে খুঁচিয়ে ওর গলায় নীল ক্ষতের চিহ্ন বানিয়েছিল সে জায়গাটি হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। “আমি ইসমত আরা, মৃত ইশাক আলীর কন্যা” সে আমাকে ভদ্রতা করে বলছিল।
“আমার বাবা ছিলেন কুষ্টিয়ার একজন ব্যবসায়ী,প্রায় দুই মাস আগে সে বাসা থেকে বের হয় এবং তার দোকানে যায় এবং এরপর আমি আর তাকে দেখিনি। ওই একই রাত্রে আমি বিছানায় যাওয়ার পর চিৎকার এবং তীব্র আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিলাম,এবং কি ঘটনা ঘটছে যখন দেখতে গেলাম তখন ওখানে পাঞ্জাবী সৈনিকেরা ছিল। আমার ৪ বোন মেঝেতে মৃত পড়েছিল এবং ওরা যখন আমার মাকে মেরে ফেলছিল তখন সেটা আমি দেখেছিলাম। আমি যখন ওখানে ছিলাম ওরা আমার ভাইকে গুলি করেছিল, সে ছিল বিজ্ঞানে স্নাতক। এরপর একজন সৈনিক আমকে দেখে ফেলে এবং তার ছুরি দিয়ে আমাকে আঘাত করে। আমি মেঝেতে পড়ে গিয়ে মৃতের অভিনয় করি। যখন ওরা চলে গেলো আমি পালিয়ে আসি এবং একজন লোক আমাকে সাইকেলে উঠিয়ে এখানে নিয়ে আসে।
হাসপাতালটি বর্ডার থেকে আধা মাইল দূরে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলাতে এবং ইতিমধ্যেই সেটা উত্তেজিত পাকিস্তানিদের শিকার অসহায় মানুষ দ্বারা কানায় কানায় পূর্ন ছিল। সেখানে ছিল পেটে গুলি লাগা সত্ত্বেও বেঁচে যাওয়া ৪ বছরের এক বালক এবং এক মহিলা যে কিনা ক্লান্তভাবে বলে যাচ্ছিলো কিভাবে পাকিস্তানিরা তার দুই সন্তানকেই তারই চোখের সামনে হত্যা করেছে এবং এরপর তাকে গুলি করে যেহেতু তার ছোট বাচ্চাটি তার কোলে ছিল। “গুলিটি বাচ্চার পশ্চাৎদেশ দিয়ে গিয়েছিল এবং এরপর মহিলার বাম বাহুর মধ্য দিয়ে” বলছিলেন ওখানকার চিকিৎসা পরিচালক ডাক্তার আর দত্ত। কিন্তু পুনরায় জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে নিজেকে এবং বাচ্চাকে নিয়ে বর্ডারে সরে আসে।
আরেকজন আহত নারী যার পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেছে গুলিতে ,কোলে বাচ্চাকে নিয়ে দোলাচ্ছিল। সে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর সময়ের আগে ই বাচ্চাটিকে জন্ম দেয় এক ধানের ক্ষেতে। তারপরও বাচ্চাটিকে এক হাতে নিয়ে এবং অন্যদের সাথে নিজেকে টেনে নিয়ে এসেছে এই বর্ডারে।
“যদিও আমি জানি এই মানুষগুলোর অবস্থা,আমি অনবরত অবাক হচ্ছি ওদের দৃঢ়তা দেখে” বলছিলেন দত্ত। তারপরও কিছু আছে যারা এখনো মেনে নিতে পারছে না। আমি যেতে যতে দুটো বাচ্চা ছেলেকে মেঝেতে শুয়ে থাকতে দেখেছি, ওরা বানরের মত একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ছিল। “রিফিউজিরা বলল ওদের গ্রাম একসপ্তাহ আগে পুড়ে গেছে এবং সেখানে কেউ বেঁচে নেই শুধু এই দুজন ছাড়া। ওরা আমাদের সাথে আছে ৩দিন ধরে অথচ এখনো আমরা জানি না ওরা কারা। ওরা যে দেখেছে তাতে এতোই ভীত-সন্ত্র্বস্ত যে ওদের বাকশক্তি ফুরিয়ে গেছে। ওদেরকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব এবং খাওয়ানো ও বেশ সময়ের ব্যাপার/ কষ্টসাধ্য। এটা বলা কষ্টকর যে কখন ওরা ওদের ভাষা ফিরে পাবে বা আবার স্বাভাবিক জীবনযাপনের সামর্থ্য ফিরে পাবে”
মেজর জেনারেল এস এস উবান এর দেয়া তথ্য থেকে পাক বাহিনীর ভয়াবহ বীভৎসতার প্রমান পাওয়া যায়,সারা বাংলাদেশে তারা অত্যাচার আর নির্মমতার রোলার চালিয়েছে সেটা বুঝতে বাকি থাকে না এক ফোটাও।
মেজর জেনারেল এস এস উবান
Major General SS Uban: Phantoms of Chittagong
২৬শে মার্চ
হাটখোলা রেললাইনের দু পাড়ের বস্তিতে বাসকারী মানুষগুলো কসাই সেনাবাহিনীর চেহারা দেখার আগেই ভারী মেশিনগানের গুলিতে কচুকাঁটা হয়ে যায়।
পুরান ঢাকার নয়াবাজার বস্তিতে একই রকম হামলা হয়,তবে সেখান থেকে দয়া করে যুবতী ও তরুণী মেয়েদের রেহাই দেয়া হয়,যাদের পরবর্তীতে পালাক্রমে ধর্ষণ করে গনকবর দেয়া হয়।
সিলেট-
সিলেট শহরে জারি করা কারফিউয়ের প্রথম প্রদর্শনী দেখা যায়,কারফিউ সম্পর্কে কোন রকম সতর্ক করা হয়নি সিলেটবাসীকে,কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় ব্যরিকেড ও বাঙ্কার বসানো হয়েছিল।
একজন বৃদ্ধ মানুষ বিকেলের দিকে মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে ফিরছেলেন। পাক সেনারা তাকে গুলি করে হত্যা করে,এর পর তার সাথের দুই ছেলেকে আদেশ দেয়া হয় তার লাশ নিয়ে যাবার জন্য। দুজন ছেলে যখন লাশের দিকে এগিয়ে যায়,তাদেরকেও গুলি করে হত্যা করা হয়। এই তিনটি লাশ এরপর প্রদর্শনীর জন্য রাস্তায় ফেলে রাখা হয়,যাতে সামনে কেউ কারফিউ ভঙ্গ না করে।
এছাড়া সিলেটে এক মসজিদে এক কাতারে নামায আদায়রত একদল মুসল্লিকে মেশিন গানের গুলিতে হত্যা করা হয়। বলা হয় এরা সহিহ বা সত্যিকারের মুসলমান নন,তাই মসজিদে নামাজ আদায়ের অধিকার এদের নেই।
সিলেটের মৌলভিবাজার এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহেই লুট হয়ে যায়,আর শহরের মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হয় ক্যাম্পে। রাতভর ধর্ষনের পর সেখান থেকে নগ্ন অবস্থায় তাদেরকে একটি মাঠে নিয়ে আসা হয়,এবং নাচতে বাধ্য করা হয়,অবাধ্য মেয়েদের গুলি করা হয়। এর পর তাদেরকে শিবপুর আর্মী ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়,এই মেয়েদের কোন খোঁজ পরবর্তীতে আর পাওয়া যায়নি।
চট্টগ্রাম-
একইদিনে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে হামলা চালানো হয়,পাক বাহিনীর সাথে ছিল বিহারী মুসলমানেরা। মুহূর্তের মধ্যে হত্যা করা হয় ৩০০০ মানুষকে। ধর্ষণ করা হয় প্রতিটি মেয়েকে। অপেক্ষাকৃত সুন্দরী মেয়েগুলোকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যাম্পে। বিহারীদের হাতে ছিল রামদা,চাপাতি এবং ড্যাগার।
উদ্ধারকৃত অনেক মেয়ের মধ্যে একটি মেয়ে জানায়,এক সময় পাক সেনাদের ধর্ষণ সহ্য গিয়েছিল,কিন্তু সারা শরীরে আর মুখে ছিটকে পড়া পাক সেনাদের বীর্যর তাপ অসহ্য লাগতো।
৫/৬ এপ্রিলে চট্টগ্রাম একটি পরিত্যক্ত শহরে পরিনত হয়,প্রায় সব বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে,কিছু মেয়েদের হত্যা করা হয়েছে,বাকিরা ক্যাম্পে। নগ্ন ধর্ষিতা মেয়েদের নদীর দিকে মার্চ পাস্ট করানো হয়,সেখানে তাদের হাত পা বেধে গোসল করানো হয়,এবং ক্যাম্পে ফিরিয়ে আনা হয়। প্রতিদিন প্রতিটি মেয়েকে গড়ে ১৫-২০ জন সৈন্য ধর্ষন করেছিল।
১লা এপ্রিল
হোলাটি গ্রাম,সাভার
বীভৎস হৃদয় বিদারক ঘটনার অবতারনা হয় এখানে। পাক সেনারা গ্রাম এই হিন্দু গ্রামটিকে ঘিরে ফেলে,সাথে ছিল ড্যাগার আর চাপাতি হাতে বিহারীরা। পুরো গ্রামে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়,বাচেনি গরু,ছাগল,কুকুর,বেড়ালও। কিছু মেয়েদের বাচিয়ে রাখা হয় আনন্দের জন্য। মায়ের কোল থেকে বাচ্চাকে টেনে নিয়ে ছুঁড়ে দেয়া হয় তাক করা বেয়োনেটের দিকে।
একটি ছয় বছরের বাচ্চা ‘ জয় বাংলা’ স্লোগান বলে ওঠে আপনমনে। এতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয় পাক বাহিনী। পাক বাহিনীর সদস্যরা বাচ্চাটিকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে ৫০ টুকরা করে ফেলে। এবং পোড়ানোর আগে গ্রামের হিন্দুদের সেই মাংশের টুকরো খেতে বাধ্য করা হয়।
জে রুমেল
J. Rummel ” Death By Government, p. 329
পাক সেনাবাহিনীর অন্যতম লক্ষ্য ছিল,কিশোর ও যুবকদের বিলুপ্ত করা। তরুন ও যুবকদের যেখানে দেখা গেছে গুলী ছুড়ে হত্যা করা হয়েছে। এরপর লাশগুলো পড়ে ছিল মাঠে,ইটের ভাটায়,আর্মি ক্যাম্পের আশে পাশে। ভেসে উঠেছিল নদীতে,১৫-২৫ বছরের যুবকদের জন্য সময়টা ছিল বিভীষিকাময়। বাড়ির নারীরাও তাদেরকে পালিয়ে যেতে বলেছিলেন। অনেক যুবককে হত্যা করা হয়েছে পালাবার সময়,সীমান্ত এলাকায়। অনেককে ধরে এনেছে বিহারীরা আর্মি ক্যাম্পে।
রবার্ট পেইন
Robert Payne, Massacre [Macmillan, 1973], p. 55
পাক সেনাবাহিনী যে শুধু গনহত্যা চালিয়েছে সেটা বললে ভুল বলা হবে,তারা মৃতদেহের উপর চালিয়েছে পরিক্ষা নিরীক্ষা। বুড়িগঙ্গা নদির পাড়ে যে বদ্ধভুমি আবিষ্কার করা হয়েছে,সেখানে তিনটি আলাদা আলাদা কামরার সন্ধান পাওয়া গেছে,একটি কামরাতে বন্দীদের আটকে রাখা হত,একটি কামরাতে হত্যা করা হত,আর তৃতীয় কামরা থেকে লাশ সরিয়ে ফেলাম ব্যবস্থা করা হত। রাতের পর রাত ধরে মানুষ হত্যা করা হয়েছে,ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে নদী স্রোতে। কিছু কিছু লাশ জায়গা পেয়েছে গনকবরে।
এসব হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছিল পাকিস্তান সরকার অধিকৃত তেল কোম্পানির ভবনে,গোডাউনে এবং খোলা আকাশের নিচে বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে।
_______________________
http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=27429
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ ২০:০৭582847
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ ২০:০৭582847- ৭১ এর জেনোসাইড (নিক্সন-কিসিঞ্জার)
লিখেছেন: সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড
তারিখ: ২২ চৈত্র ১৪১৮ (এপ্রিল ৫, ২০১২)
_________________________________________________
বটমলেস বাকেট অর্থাৎ তলাবিহীন ঝুড়ি খ্যাত হেনরি কিসিঞ্জারের সেই বিখ্যাত উক্তি কম বেশি আমরা সবাই শুনেছি।
আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিদেশী বন্ধুদের কথা(তালিকা দেবার প্রয়োজন বোধ করছি না) আমরা সব সময় হৃদয়ে রাখবো। কিন্তু একজন বিদেশী যুদ্ধাপরাধীর কথা না বলে আর পারছি না, মানবতা পায়ে ঠেলার মতো উপমা শুনেছি,হেনরি কিসিঞ্জারের কথা জেনে উদাহরণ জানার বিলাসিতাও হয়েছে।
ব্যবচ্ছেদ করলে একটা সহজ সমীকরণে আসা যায় খুব সহজে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিগুলো ছিল,ভারত,তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ব্রিটেন। আর ঘোরতর বিরোধী ছিল যুক্তরাষ্ট্র,চীন এবং সৌদি আরব। ইতিহাস এবং দলিল এদের প্রমাণ দেবে।
আমেরিকার কেন্দ্রীয় প্রশাসন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা লগ্নেই পাকিস্তানের সপক্ষে তার নীতি ঘোষণা করে। তারা গণতন্ত্রকামী বাংলাদেশের জনগণের সমর্থনে এগিয়ে আসেনি। তারা দাঁড়িয়েছে পাকিস্তানের অখণ্ডতার নামে স্বৈরাচারী সামরিক জান্তা অগণতান্ত্রিক শক্তির সপক্ষে। তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন রিচার্ড এম. নিক্সন এবং হেনরি কিসিঞ্জার ছিলেন নিক্সনের একান্ত আস্থাভাজন ব্যক্তি, যিনি তখন আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক প্রেসিডেন্টের একান্ত সহকারী।
এই নিক্সন-কিসিঞ্জার নিয়ন্ত্রিত মার্কিন নীতিই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকা পাকিস্তানের এমন একটি অত্যাচারী সরকারের সপক্ষে দাঁড়াল যে সরকার তার পূর্বাঞ্চলের নিরীহ জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। পাকিস্তানের পক্ষে নিক্সন-কিসিঞ্জারের প্রকাশ্য সমর্থন কিংবা পাকিস্তানের প্রতি ঝুঁকে পড়া নীতি অনুসরণ নিছক পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকা ছিল না। তখনকার মার্কিন প্রশাসনের নীতি এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়, যা ঐ ঝুঁকে পড়ার সীমা ছাড়িয়ে যায়। বলা যায়, প্রায় অনেকটা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে তথা পাকিস্তানের সপক্ষে আমেরিকার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ কিংবা মদদদান। আমেরিকা ঐ অবস্থান গ্রহণ করার কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বানচাল করতে পাকিস্তানকে সামরিক ও নৈতিক সমর্থন জানায়।
পাকিস্তানের পক্ষে নিক্সন প্রশাসনের ঝুঁকে পড়ার নীতির এক বলিষ্ঠ প্রয়োগকারী ব্যক্তি হচ্ছেন- হেনরি কিসিঞ্জার, যিনি তখন বাংলাদেশের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অত্যন্ত আগ্রহী ও পারদর্শী। কিসিঞ্জার তাঁর নিজের উচ্চতর ক্ষমতা ও যোগ্যতার অধিকারী হয়ে এবং প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত সমীকরণের বলে তিনি এমনই একজন শক্তিশালী ব্যক্তিতে পরিণত হন যার ফলে তিনি বাংলাদেশের ব্যাপারে মার্কিন নীতি প্রণয়নের কেন্দ্রীয় চরিত্রে আবির্ভূত হন।
নিক্সন-কিসিঞ্জার ছিলেন একাত্তর সালের বাংলাদেশ বিষয়ে আমেরিকার নীতি নির্ধারণে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত দুজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁরা গোপনে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। যুদ্ধের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তারাই ১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর আমেরিকার সপ্তম নৌ-বহর বঙ্গোপসাগরে মোতায়েনের নির্দেশ দেন, যার মূল লক্ষ্য ছিল ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে সর্বোচ্চ ভীতিপ্রদান এবং পূর্ববাংলা থেকে সরে আসতে পাকিস্তান যেন কিছু সময় পায়।
এ ছাড়াও ব্লাড টেলিগ্রাম এর কথা বলতে হয়। আর্চার কেন্ট ব্লাড একজন মার্কিন নাগরিক যিনি ১৯৭১-এ বাংলাদেমে মার্কিন কনসাল জেনারেল হিসাবে কর্মরত ছিলেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থন দিয়েছলেন। নিক্সন-কিসিঞ্জারের পাকিস্তানপন্থী অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকার জন্য তাকেঁ “বাংলাদেশের যুদ্ধবিবেক” হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সর্বপ্রথম তিনি ঢাকায় এসেছিলেন ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে, পূর্ব পাকিস্তানস্থ মার্কিন দূতাবাসে পলিটিক্যাল কর্মকর্তার দায়িত্ব নিয়ে। আর্চার ব্লাড তাঁর দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ বইয়ের সূচনায় লেখেন, ‘একাত্তর নিয়ে লিখতে বসে আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। কারণ আমার বহু বন্ধুর মুখ ভেসে উঠছে, যারা শহীদ হয়েছে।
২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ঢাকা শহরে গণহত্যা শুরু করে। ৬ এপ্রিল ১৯৭১ ঐতিহাসিক মার্কিন দূতাবাস থেকে একটি তারবার্তা পাঠানো হয়েছিল ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে। ঢাকায় কর্মরত মার্কিন কর্মকর্তারা ২৫ শে মার্চের ‘কলঙ্কিত রাতের’ গণহত্যা এবং সে বিষয়ে নিক্সন-কিসিঞ্জারের অন্ধ ইয়াহিয়া-ঘেঁষা নীতির প্রতিবাদ জানাতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন।
তাঁরা খুব ভেবেচিন্তে একটি তারবার্তা লিখেছিলেন যাতে স্বাক্ষর করেছিলেন ব্লাড ও তাঁর ২০ জন সমর্থক সহকর্মী। তাঁরা তাতে ঢাকায় ইয়াহিয়ার গণহত্যার প্রতি ওয়াশিংটনের অব্যাহত নীরবতার নিন্দা করেছিলেন। ব্লাড তাতে কেবল স্বাক্ষরই দেন নি, বাড়তি এক ব্যক্তিগত নোটও লিখেছিলেন। এতে তিনি রিখেছিলেন, “আমি বিশ্বাস করি, পূর্ব পাকিস্তানে এখন যে সংগ্রাম চলছে, তার সম্ভাব্য যৌক্তিক পরিণতি হলো বাঙালিদের বিজয় এবং এর পরিণতিতে একটি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা।“ এই ‘ব্লাড টেলিগ্রাম’ বস্তুত তখনকার নিক্সন-কিসিঞ্জারের দুর্গে বোমা ফেলেছিল। ‘’দ্য ট্রায়াল অব হেনরি কিসিঞ্জার’’ নামীয় গ্রন্থের লেখক ক্রিস্টোফার হিচেন্স মতে ‘মার্কিন ইতিহাসে ব্লাড টেলিগ্রামের কোনো তুলনা নেই।’ কিসিঞ্জার এ জন্য ব্লাডকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিলেন।
ক্রিস্টফার হিচেন্স তার দি ট্রায়াল অফ হেনরি কিসিঞ্জার বইয়ের একটি পর্বে বাংলাদেশ,৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিবর্তী কিসিঞ্জারের ভূমিকা সম্পর্কে লেখেন।
আর একটি কথা না বললেই নয়,কিসিঞ্জার শুধু বাংলাদেশ জেনোসাইড নয়, পৃথিবীর আরও বেশ কয়েকটি দেশের মানবতাবিরোধী কর্মকান্ডে তার যোগ থাকার বিষয় নিশ্চিত করা হয়।
হিচেন্স এর বইটির যে পর্বে বাংলাদেশ কথা ও কিসিঞ্জারের কথা উল্লেখ রয়েছে সে পর্বটি অনুবাদ করছি।
অনুচ্ছেদ- বাংলাদেশ
পৃষ্ঠা-৪৪
১৯৭১ সাল গণহত্যা শব্দটি বিশ্বের দরবারে খুব পরিচিত করে তোলে!! ততকালীন সময়ে পাকিস্তানের ‘বাঙ্গালী’ জনগোষ্ঠির, তথা বাংলাদেশীদের পক্ষে ইউনাইটেড স্টেট কনসিউলেট তাদের স্টেট ডিপার্টমেন্টে একটি বার্তা পাঠায়। বার্তাটি পাঠানো হয় ৬ এপ্রিল ১৯৭১, যেখানে প্রধান স্বাক্ষরকারী ছিলেন তৎকালীন ঢাকার কনাস্যিউল জেনারেল আর্চার ব্লাড। অন্য অর্থে এটাকে হয়ত ব্লাড টেলিগ্রামও বলা যেতে পারে! মার্গেন্থাসের বিবরনী থেকে ভিন্ন এই বার্তাটি সরাসরি ওয়াশিংটনে পাঠানো হয়, যেখানে গনহত্যার বিষদ বর্ণনার চেয়ে গণহত্যা সম্পর্কে আমেরিকার সরকারের ভূমিকা নিয়ে বেশি সমালোচনা করা হয়। এর মূল বক্তব্য ছিলঃ
‘আমাদের সরকার গণতন্ত্র বিরোধী কাজের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের সরকার গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই সরকার সাধারণ জনগনের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে পশ্চিম পাকিস্থানী শাসক গোষ্ঠিকে নিয়ন্ত্রন করতে , এমনকি বিশ্বের দরবারে তাদের আসল রূপ প্রকাশেও তারা সক্ষম হয়নি যা কিনা অন্যান্য দেশের সাথে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের সাক্ষী আমাদের সরকার, আর হাস্যকরভাবে ঠিক একই সময় তারা গনতনত্রের ব্যাখ্যা দিয়ে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের কাছে একটি বার্তা পাঠায়, যেখানে পূর্ব পাকিস্থানের প্রবল জনপ্রিয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ ভাবে বিজয়ী নেতাকে আটকের প্রতিবাদ করা হয়। সেই সাথে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধের আহবানও জানান হয়……… কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা নিরব দর্শকের ভূমিকা নেই- এমনকি মানবিক দিক থেকেও। এটি একটি দেশের অভ্যন্তরীন বিষয় বলে আমরা স্রেফ মুখ বুজে রইলাম যা একসময় গনহত্যায় রূপ নিল! সাধারন আমেরিকানরা এখন এর প্রতিবাদ করছে, সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে আমরাও সরকারের এই নিরবতাকে সমর্থন করি না, বরং আশা করছি সরকার এক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রেখে আমাদের গণতান্ত্রিক রাজনীতির একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করবে।‘
এই বার্তাটিতে তৎকালীন বাংলাদেশে বসবাসরত বিশ জন আমেরিকান কূটনৈতিকের সাক্ষর করেন, পরবর্তীতে স্টেট ডিপার্টমেন্টে আসার পর আরো নয় জন কর্মকর্তা এতে একাত্নতা প্রকাশ করে সাক্ষর করেন। স্টেট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমাদের স্বাধিনতার স্বপক্ষে এটাই সবচেয়ে জননন্দিত এবং শক্তিশালী বক্তব্য ছিল।
২৫শে মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী তৎকালীন রাজধানী ঢাকা আক্রমন করে,এবং শেখ মুজিবর রহমান কে অপহরন করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল মুজিব অনুসারি এবং সাধারন জনতাকে লক্ষ্যহীন করা। সমস্ত বিদেশী মিডিয়াকে ঢাকা থেকে জোর পূর্বক বের করে দেয়া হয়,ততকালীন ম্যাসাকারের সরাসরি প্রমান পাওয়া যাবে,মার্কিন রেডিও থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রচারকৃত বার্তা সমুহে। আর্চার ব্লাড নিজে সরাসরি একটি বার্তা তখন কিসিঞ্জারের অধিকৃত জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে পাঠান।
সেনাবাহিনীর সৈনিকেরা তখন সাধারন মানুষের বাড়িতে আগুন দেয়া শুরু করে,এবং মানুষগুলোকে গুলি করে হত্যা করে।( এই বন্দুকগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক এসিসটান্ট প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল)
এই সময় লন্ডন টাইমস এবং সানডে টাইমস যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে,এন্থনি মাসকারহেনাস এর সেই প্রতিবেদন গুলো তারা সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য প্রচার করে কালো রাতের মুখোশ উম্মোচন করে। খুন,ধর্ষণ,এবং সাধারন মানুষের উপর অত্যাচারের সেই রিপোর্টগুলো মানুষকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। শিশু ও নারী হত্যা করে সেনাবাহিনী তখন সাধারন মানুষকে দমিয়ে রাখতে চেয়েছিল।
প্রথম ৩ দিনে ১০ হাজার বেসামরিক মানুষকে হত্যা করা যায়,পরের কয়েকদিনের হিসাবে যা মিলিওন এর হিসাবে গিয়ে ঠেকে।
সকল হিন্দু ধর্মালম্বী জনগন তখন বাস করছিলেন একটি নারকীয় পৃথিবীতে।
প্রায় ১০ মিলিওন উদ্বাস্তু মানুষ তখন ভারত সীমানা পথে যাত্রা শুরু করে।
পুরো জেনসাইড কে তিনটি পয়েন্টে বর্ণনা করা যায়
১) সাধারন নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে জটিলতার অবতারনা।
২) পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে একটি আগ্রাসি সিধান্তের উদাহরন।
৩) সল্প সময়ের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক ক্রাইসীস সৃষ্টি।
নিউ দিল্লিতে অবস্থান রত তৎকালীন মার্কিন কূটনিতিক কেনেথ কেটিং বাংলাদেশের সাধারন মানুষের পক্ষে অবস্থান নেন। তিনি ছিলেন সাবেক নিউ ইয়র্ক সিনেটর, তিনি ২৯ মার্চ মার্কিন প্রশাসনকে বলেন “ “promptly, publicly, and prominently deplore this brutality” এছাড়াও তিনি এই বর্বর অপারেশন অবিলম্বে বন্ধ করতে প্রশাসনকে সতর্ক করে দেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেন “ “prior to inevitable and imminent emergence of horrible truths.”
নিক্সন ও কিসিঞ্জার এই বার্তার পরিপ্রেক্ষিতে অতি দ্রুত পদক্ষেপ নেন,আর্চার ব্লাডকে তার পদ ঠেকে অব্যাহতি দেয়া হয়,আর কেটিং কে বলা হয় যাতে তিনি তার ভারত ঘেঁষা আচরন শুধরে নেন। তাকে সরাসরি বলা হয় “taken over by the Indians.”
এপ্রিল মাসের শেষ দিকে,ঠিক যখন গনহত্যার হার সব ঠেকে উচু,হেনরি কিসিঞ্জার ইয়াহিয়া খানকে একটি বার্তা পাঠান,যেখানে কিসিঞ্জার ইয়াহিয়াকে তার সময়োপযোগী সাহসী সিধান্ত ও কূটনীতির ভূয়সী প্রশংসা করেন।
নিক্সন- কিসিঞ্জারের এই পাকিস্তান প্রশাসন ঘেঁষা মনোভাব,ও সেনাবাহিনীর যুদ্ধ অপরাধ সমর্থনের কারণ খুজতে গেলে আরও একটি বিষয় উঠে আসে।
কেন নিক্সন- কিসিঞ্জার জেনারেল ইয়াহিয়াকে সমর্থন জানিয়েছিল?
এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্রের টেবিল টেনিস দলকে চীনের বেইজিং এ একটি ট্যুরনামেন্ট খেলতে আমন্ত্রন জানানো হয়,মাধ্যম হিসেবে ব্যাবহার করা হয় পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রদূতকে। এবং সেই রাষ্ট্রদূত টেবিল টেনিস খেলার আমন্ত্রন পত্রের সাথে চীন প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য একটি নৌ বহর পাঠানোর সুপারিশ নিয়ে আসেন। নিক্সন- কিসিঞ্জার আন্তর্জাতিক রাজনীতির দখল নিতে মিত্র পক্ষের সমর্থন পাবার নিমিত্তে,লাখ লাখ মৃত্যুগামী জনগণকে জেনে শুনে আগুনে ফেলেছেন,নীরবে সমর্থন দিয়ে গেছেন সেই সেনাবাহিনীর অপারেশনকে। কি নির্মম,বর্বর ক্ষমতালোভী দুজন রাজনীতিবিদ।
পৃষ্ঠা – ৫০
যুদ্ধকালীন বাংলাদেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে তার বিতর্কিত ভুমিকা নিয়ে কিসিঞ্জারকে সাংবাদিকদের বেশকিছু বিব্রতকর এবং বিদ্রুপাত্মক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল,যা তার আনন্দঘন চীন ভ্রমনের অনেকটাই ম্লান করে দেয়।তিনি বাংলাদেশের জনগণ এবং নেতাদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন,এবং শেখ মুজিবকে তিনি(তার তৎকালীন সহকারী রজার মরিস এর ভাষ্যমতে) Salvador Allende এর সাথে তুলনা করেন।
১৯৭৩ সালে কিসিঞ্জার সেক্রেটারি অব স্টেট হওয়া মাত্রই,গনহত্যার প্রতিবাদে যোগদানকারী প্রত্যেকেই তার তীব্র রোষের সম্মুখীন হয়।
১৯৭৪ এর নভেম্বরে কিসিঞ্জার একটি সংক্ষিপ্ত এবং দায়সারা উপমহাদেশ সফরকালে বাংলাদেশে আটঘন্টার একটি যাত্রাবিরতি নেন,এবং তিন মিনিটের একটি সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করেন। সেখানে ১৯৭১ সালে বঙ্গোপসাগরে তিনি কেন নৌ-বহর পাঠিয়েছিলেন জানতে চাওয়া হলে,তিনি উত্তর দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।তার ফিরে যাবার তিন সপ্তাহের মধ্যে, এখন আমরা জানি,ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের একাংশ বাংলাদেশি সামরিক কর্মকর্তাদের একটি দলের সাথে গোপন সাক্ষাৎ শুরু করে,যারা মুজিবের বিরুদ্ধে একটি অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করছিল। ১৯৭৫ সালের ১৪ই আগস্ট,মুজিব এবং তার পরিবারের ৪০ জন সদস্য একটি সামরিক হামলায় নিহত হন।এর কয়েকমাস পরে,তার কিছু নিকটতম রাজনৈতিক সহকর্মীদেরও কারাবন্দী অবস্থায় নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।
__________________________
http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=24554
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৪:৩৭582849
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৪:৩৭582849- বাবার খোঁজে
লিখেছেন: অমি রহমান পিয়াল
০১ লা ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ দুপুর ১:৪৩
_____________________________________
[নাদিম কাদির একজন সাংবাদিক। শুধু সাংবাদিক নন, বিখ্যাত সাংবাদিক- ওকাবের প্রেসিডেন্ট। উপস্থাপক। বাজারে তিনটি বই বেরিয়েছে। আমার কাছে তার এসব পরিচয়কে ছাপিয়ে গেছে তিনি একজন শহীদের সন্তান। উত্তরসূরী ফোরামে তার একটি লেখা পড়ে চোখে জল এলো। অনুবাদ করার লোভ সামলাতে পারলাম না। মনে পড়লো জহির রায়হানের ছেলে অনল রায়হানের কথা। বাবার মৃত্যু রহস্য উদঘাটন করতে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছিলেন, সফল হয়েছিলেন। অনলের সঙ্গে নাদিমের তফাত, তিনি জানতেন তার বাবাকে কারা মেরেছে। অনলের মতোই নাদিম তার বাবার কবর খুঁজে বেরিয়েছেন। সফল হয়েছেন, কিন্তু ট্রাজেডিটা এখানেই। । তার বাবা কোথায় শায়িত জেনেও কিছু করতে না পারার অক্ষমতা কুড়ে খাচ্ছে তাকে। এ গল্প এক অসহায় সন্তানের গল্প। যে জায়গার কথা বলা হচ্ছে তার আশপাশ দিয়ে ছিলো আমার নিত্যকার আসাযাওয়া। সে কারণেই বেদনাটা হয়তো বেশীই বুকে বেজেছে আমার।
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক যে কোনো পোস্ট এখন থেকে শুধু জন্মযুদ্ধ গ্রুপে দেওয়া হবে। এই পোস্টটি এর আগে শুধু চট্টগ্রাম গ্রুপ ও জন্মযুদ্ধ গ্রুপে গেছে। বিষয়টি সমসাময়িক এবং আলোচিত বলেই প্রথম পাতায় আবার পোস্ট করা হলো। ]
১৫ এপ্রিল ১৯৭১। ঘুম ভাঙলো ফজরের আজানে। বিশ্বাসীদের উপাসনার ডাক দেয়া হচ্ছে। অব্শ্য এদের বেশীরভাগই ততদিনে হয় পালিয়েছেন, নয়তো মারা পড়েছেন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে। বাবাকে দেখলাম লুঙ্গি আর গেঞ্জি পড়ে বাসার পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলাম, “কোথায় যাচ্ছো বাবা?” উনি আমার দিকে তাকালেন, তারপর থেমে আমার কাছে ফিরে আসলেন। আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বললেন, “তোমার বাবা কোথাও যাচ্ছে না।”
এরপর এলো সেইদিন, ১৭ এপ্রিল ১৯৭১। দুয়ারের ঘণ্টি বাজলো, সেইসঙ্গে বুটের সপাট লাথি। অনেকগুলো সেপাই নিয়ে একজন পাকিস্তানী ক্যাপ্টেন আমাদের বাসায় ঢুকলেন। দরজা খুলতেই আমাকে জিজ্ঞেস করল, “তোমার বাবা কোথায়?” আমার পিছু নিয়ে তারা শোবার ঘরে ঢুকল আর বাবাকে বললো, “তুমি একজন বেইমান। তোমাকে গ্রেপ্তার করা হলো... তৈরি হয়ে নাও।“
এরপর সেই ক্যাপ্টেন আমার বাবা লেফট্যানেন্ট কর্ণেল মোহাম্মদ আবদুল কাদিরকে (ইঞ্জিনিয়ারিং কোর) স্ত্রীর সঙ্গে জরুরী কোনো কথা থাকলে সেরে নিতে বললো। আমার গর্ভবতী মা তখন নিথর নিশ্চুপ তার পাশে দাঁড়িয়ে। একটা নেভি জিপে করে তাকে নিয়ে যাওয়ার সময় আমি দৌড়ে গেলাম সিড়ির দিকে, তাকে হাতনেড়ে বিদায় দিলাম। বাবাও হাত নাড়লেন। আমি কখনোই ভাবিনি এটাই আমাদের শেষ দেখা হতে যাচ্ছে। এরপর আমি অনেক প্রার্থনা করেছি যাতে বাবার সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়। ভাবিনি কয়েক যুগ পরে এসে তাকে স্বশরীরে না পেলেও তার শেষ বিশ্রামের জায়গাটাকে খুজে পাবো।
আমি শুধু সত্যিটা জানতে চেয়েছি। জানতে চেয়েছি ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল আমার বাবা ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের লে. কর্ণেল মোহাম্মদ আবদুল কাদিরের ভাগ্যে কি হয়েছিল। গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার পর তার আর খোঁজ মেলেনি। তার ফেরার অপেক্ষায় প্রহর গুনে গুনে ১৯৯৯ সালে মারা গেছেন তার স্ত্রী হাসনা হেনা কাদির। আমার ভাইবোনদের মতো আমিও একই কথা বিশ্বাস করতে চেয়েছি। কিন্তু একইসঙ্গে চেয়েছি সত্যের মুখোমুখি হতে। ভালোভাবেই জানতাম সেটা সুখকর কিছু হবে না। তারপরও তার শেষ ঠিকানাটা জানা আমার কাছে খুব জরুরি ছিলো।
১৬ বছর খোঁজাখুজির পর আমি অবশেষে একটা সূত্র পেলাম। সূত্রের সূত্র আমাকে নিয়ে গেলো চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ এলাকায় বধ্যভূমিতে। ১৯৭১ সালে ৭০ নং পাঁচলাইশে থাকতাম আমরা, তার খুব কাছেই অবস্থান সেই গণকবরের। সে জায়গায় একটা দালান উঠছে। মালিকপক্ষ মুখ খুলতে নারাজ। সেখানে মাটি খোড়ার সময় তারা কিছু পেয়েছিল কিনা নাকি তারা স্বেচ্ছায় তা আবার মাটিচাপা দিয়েছে সেটা জানা গেলো না।
আমি সেখানে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। চেচিয়ে বলতে ইচ্ছে করছিলো, “বাবা, শেষ পর্যন্ত পেয়েছি তোমাকে। দ্যাখো তোমার অন্তু বাবা এসে গেছে। ” চিৎকার করে কাঁদতে পারছিলাম না, কেউ না দেখে মতো চোখ মুছছিলাম শুধু। সেই অর্ধ-নির্মিত ভবনের গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আমি নিরবে প্রার্থনা করছিলাম আমার বাবার জন্য।
মুহূর্তের জন্য হারিয়ে গিয়েছিলাম, খুব অসুস্থ লাগছিল। কিন্তু আমার উপায ছিল না কোনো। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছিলাম আমাকে শক্তি দিতে যাতে বাবার সহযোদ্ধাদের সাহায্য নিয়ে জায়গাটার বিনির্মাণ করতে পারি। উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে এবং আশা করছি শুধু তার কবরটিই সুবিচার পাবে না, সেইসঙ্গে যোগ্য সম্মান দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে তার ভূমিকাও স্পষ্ট করা হবে।
লেখাটা যখন লিখছি, তখনও আমার বড় বোন ও ছোটভাই এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। লেখাটা বেরুনোর আগেই তাদের বলবো অবশ্য। বোনের জন্যই বেশী চিন্তা হচ্ছে কারণ উনি কতটা শক্ত থাকতে পারবেন তা নিশ্চিত বলতে পারছি না। আর কবরটা সংরক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত সেখানে গিয়ে বাবার জন্য প্রার্থনা করাও তার জন্য সম্ভব হবে না। কিন্তু এটাই বাস্তবতা যার মুখোমুখি আমাদের হতে হয়েছে।
চট্টগ্রামে বেশ ক’বার আসাযাওয়ার পর মাকে বলেছিলাম যে তার প্রিয়জনের কবরের খোঁজ পেয়েছি। কিন্তু তাকে জীবন্ত ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। রেডক্রসের ট্রেসিং এজেন্সি ১৯৭৪ সালেই বলে দিয়েছিলো যে বাবা ‘নিখোজ এবং ধারণা করা হয় তাকে মেরে ফেলা হয়েছে’। কিন্তু তাতে তার পরিবার সন্তুষ্ট হয়নি। অনেক খোজখবর নেয়া হয়েছে কিন্তু কেউ বলতে পারেনি তাকে কোথায় মারা হয়েছে।
শুরুতে কেউ কেউ বলেছিল তাকে চট্টগ্রামের ফয়স লেকের ওখানে মারা হয়েছে। আমি প্রতিবছর সেখানে যেতাম। ফুল দিতাম, প্রার্থনা করতাম। ১৯৯১ সালে পেশাগত কারণে চট্টগ্রাম যাওয়ার কারণে আমি জোরেসোরেই তার হদিশ বের করতে উঠেপড়ে লাগলাম। বাবার ছবি নিয়ে পাঁচলাইশ এলাকায় অনেকবার গিয়েছি। চিনতে পারে ভেবে যুদ্ধের সময় কিংবা তার পরপর চট্টগ্রামে ছিল এমন লোকজনকে দেখিয়েছি। কিন্তু কিছুই মেলেনি। ২০০৪ সালের দিকে কে যেন বলল শহরের কোন পাহাড়ে নাকি হত্যা করা হয়েছে তাকে। কিন্তু কোনো প্রমান পাওয়া যায়নি।
যখন হাল প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম, মহান আল্লাহতায়ালা আমাকে চট্টগ্রাম নিয়ে গেলেন একটা বিশেষ কাজে। ২০০৭ সালে আমি সুদানে ছিলাম, সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতেই জাতিসংঘের একটি শান্তি মিশনের সদস্যদের উদ্দেশ্যে লেকচার দিতে সেখানে গিয়েছিলাম। কথায় কথায় অফিসারদের বলেছিলাম যে ১৯৭১ সালে আমার বাবাকে সেই শহরে হারিয়ে ফেলেছি, তার আর খোঁজ পাইনি। এরপর বিশাল একটা সূত্র মিললো। চট্টগ্রাম ব্রিগেডের লে. কর্ণেল বায়েজিদ আমাকে ডা. মাহফুজুর রহমানের লেখা ‘বাঙালীর জাতীয়বাদী সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধে চট্টগাম’ নামে একটি বই দেখালেন। লেখক শুধু খ্যাতিমান চিকিৎসকই নন, বিখ্যাত গবেষকও। সেই বইয়ের ৩৭১ নং পৃষ্ঠায় উনি লিখেছেন যে পাঁচলাইশে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের সামনে এপোলো পলি ক্লিনিকের পেছনে আরো ৩৫ জনসহ কর্ণেল কাদিরকে হত্যা করা হয়েছিল।
আমি ডাক্তার রহমানকে খুজে বের করলাম, তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে। নুরুল ইসলাম নামে এই ব্যবসায়ী ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামে আওয়ামী লিগের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন। পরিচয় করিয়ে দিতেই তিনি ভেঙে পড়লেন। জানালেন কর্ণেল কাদিরকে তিনি চিনতেন। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল পাঁচলাইশের একটা খালি জায়গায় কমপক্ষে আরো ১৮ জন সহ তাকে গুলি করে মেরেছিল পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যাদের সমাহিত করেছেন তিনি। কমপক্ষে পাঁচটি বুলেট বুকে নিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন কর্ণেল কাদির। এও নিশ্চিত করলেন কর্ণেল কাদির তার অফিসের (অয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন যা এখন পেট্রোবাংলা) স্টোর থেকে বিস্ফোরক বিলি করেছিলেন এবং ১৯৭১ সালের মার্চে অফিসে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে ছিলেন। তার পরিবারের সদস্যরা তাকে দেখেছে ৭০ নং পাঁচলাইশের সরকারী বাসভবনে বাংলাদেশের পতাকা ওড়াতে।
জিজ্ঞেস করলাম আমার বাবাকে কিভাবে চিনতেন। উত্তর দিলেন কর্ণেল কাদিরের মতো লোকজনের সঙ্গে সখ্য গড়তে দলীয় পরিকল্পনার অংশ ছিলো তা। নির্বাচন পরবর্তী অচলাবস্থা শুরু হওয়ার পর থেকে নিয়মিতই তার অফিস আর বাসায় আমি যেতাম। ইসলাম সাহেব একটি স্ট্রোকের শিকার হওয়ার পর থেকে আংশিক পক্ষাগাতগ্রস্থ। তারপরও কষ্ট স্বীকার করে আমাকে সেখানে (দার উস সালাম, ৩৪/এ পাঁচলাইশ) নিয়ে গেলেন। একাংশে দার উস সালাম, অন্য অংশে নতুন একটি ভবনের কাজ চলছে। এথানেই অবস্থান সেই গণকবরের। বললেন, “নির্বাচনের পরপরই তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। অনেকবার তার অফিসে গেছি, বাসায়ও।” ইসলাম সাহেব যোগ করলেন যে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল দুপুর দুটোর দিকে তিনি গুলির শব্দ শোনেন। কাছাকাছি বিভিন্ন বাড়ির দারোয়ান এবং চাকরদের কাছে জানলেন কর্ণেল কাদিরসহ অনেক লোককে মেরে ফেলা হয়েছে।
যোগ করলেন, “অনেক ঝুঁকি নিয়ে সেখানে গিযেছিলাম... সঙ্গে আরো কয়েকজন ছিলো... কাছেই মক্কী মসজিদের ইমাম সাহেবকে ডেকে এনেছিলাম আমরা। খুব দ্রুত আর কেউ না জানে মতো আমরা মৃতদের ঠিকমতো দাফন করতে চাইছিলাম।” জানাজা পড়িয়ে একটা খালি জায়গায় তাদের দাফন করা হয়। কাছেই এলাকার একটা বড় ড্রেন গেছে জমিটার উপর দিয়ে।
এরপর হঠাৎ করেই ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজের একজন শিক্ষিকা মিসেস রোকেয়া চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয় আমার। উনিও আমাকে গণকবর হিসেবে একই জায়গা দেখিয়ে দিলেন। উনিও শুনেছেন যে একজন বাঙালী সেনা কর্মকর্তাকে সেখান সমাহিত করা হয়েছিল। ভবনটির কেয়ারটেকারকে দেখিয়ে বললেন, “ভবনের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই আমি এখানে এসে শ্রমিকদের জিজ্ঞেস করেছি তারা দেহাবশেষ পেয়েছে কিনা... কিন্তু তারা সবসময় চুপ থেকেছে নয়তো অস্বীকার করেছে।” এও বললেন, “গণকবরের জায়গাটা অন্য অংশের থেকে একটু উঁচু।”
দাফনের জায়গার খুব কাছাকাছি থাকেন এমন একজন সাবেক ব্যবসায়ীকে খুঁজে বের করলাম। উনি তার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। জানালেন তার অল্পবয়সী চাকর (দোহারের অধিবাসী আলাউদ্দিন, এখন আর তার ওখানে নেই) দাফনকারীদের সঙ্গে ছিলেন। জায়গাটাও দেখিয়েছেন। ১৪ থেকে ১৮ জন ছিলেন ওখানে। বললেন আগে কিছু মানুষ সেখানে এসে কবর জেয়ারত করতেন, কিন্তু তারা এখন আর আসেন না। তার ছেলেও সায় দিয়ে জানালনে যে তারা জমির মালিককে অনুরোধ করেছিলেন কবরের ওপর একটা বাগান বানাতে, কিন্তু ‘কিছু কারণে’ বেশি চাপাচাপি করেননি। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক সেই এলাকায় সেনাদের নেতৃত্ব দেওয়া ক্যাপ্টেনের কথাও বললেন। লুটপাটসহ তার কিছু কর্মকাণ্ডের কথাও জানলাম।
আমার এই তদন্তের সময কিছু মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে যারা গোটা ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। খোজ নিয়ে জানলাম যুদ্ধকালে তাদের ভূমিকা ছিল বিতর্কিত। স্থানীয় টাস্কফোর্সের কাছে আমার অনুরোধের প্রেক্ষিতে ২০০৮ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে এক সপ্তাহের জন্য ভবনের নির্মাণকাজ বন্ধ ছিল। গণকবরে কর্ণেল কাদিরের লাশও ছিলো জানতে পেরে কর্ণেল রেজা দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।
প্রিয় বাংলাদেশের জন্য যারা জীবন দিয়েছে তাদের সম্মাণ করতেই আমাদের এখন এলাকাটা দ্রুত সংরক্ষিত করতে হবে।
আমাদের স্বাধীনতায় অবদান রাখার জন্য আমাদের উচিত হবে কর্ণেল কাদিরকে যথাযোগ্য সম্মাণ দেওযা। সেজন্য এটাকেই সঠিক সময় বলে মানছে তার পরিবার। হয়তো এজন্যই আল্লাহ আমাকে সেখানে নিয়ে গেছেন যাতে দীর্ঘ এক যন্ত্রণাময় যাত্রার শেষ হয।
বাবাকে নিয়ে নাদিম কাদিরের একটি ফুটেজও তুলে দিলাম
কৃতজ্ঞতা : উত্তরসূরী, জন্মযুদ্ধ।
_________________
http://www.somewhereinblog.net/blog/omipialblog/28766049
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৪:৩৯582850
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৪:৩৯582850- সেল্যুট, মাই কর্নেল...
লিখেছেন: বিপ্লব রহমান • প্রকাশকাল: 23 সেপ্টেম্বর 2011 - 5:45অপরাহ্ন
___________________________________________________________
স্বাধীনতার ৪০ বছর পর মুক্তিযুদ্ধে শহীদ লেফটেনেন্ট কর্নেল আব্দুল কাদিরের প্রতীকী দেহাবশেষ গণকবর থেকে উত্তোলন করে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হলো।
শহীদ সন্তান, বিশিষ্ট সাংবাদিক নাদিম কাদির একান্ত আলাপচারিতায় এই লেখককে বলেন, অনেক দেরীতে হলেও মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী আমার পিতার প্রতি দেশ যথাযথ সন্মান জানালো। দীর্ঘ ৩০ বছর অনুসন্ধান চালিয়ে চট্টগ্রামের পাঁচলাইশে, যেখানে পাকিস্তানী সেনারা আমার বাবাসহ ১৮ জন মুক্তিযোদ্ধাকে গুলি করে হত্যা করেছে, সেই বধ্যভূমিটি আবিস্কার করি। কিন্তু সরকারের কাছে বহু ধর্ণা দিয়েও এতোদিন বধ্যভূমিটি খনন করে শহীদদের দেহাবশেষ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সেখানে চার তলা বাড়ি গড়ে ওঠায় বাড়ির মালিকের সদিচ্ছার অভাব ও সরকারের উদ্যোগহীনতায় সেখানে একটি নামফলক পর্যন্ত লাগানো যায়নি। …
তিনি বলেন, আমার বাবা কতোখানি দেশকে ভালবেসে নিজের জীবনকে দেশের জন্য উৎসর্গ করেছেন, আমরা তার পরিবারের সদস্যরা তা জানতাম। যে পতাকার জন্য তিনি জীবন দিয়েছিলেন, সে পতাকায় মুড়ে তাকে যথাযথ মর্যাদায় দাফন করা হলো, সেটি আমাদের জন্য তো বটেই, পুরো জাতির জন্যই গৌরবের। এটি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপেই সম্ভব হয়েছে।
নাদিম কাদির বলেন, রাজনৈতিক কারণে দেশ আজ নানা দল ও মতে বিভক্ত। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে সবাই ঐক্যবদ্ধ, এটিই সবচেয়ে আশার কথা। আমার বাবা শহীদ কর্নেল কাদির ১৯৭১ এ বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন। সে সময় চট্টগ্রামে অবস্থান রত মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গেও তিনি যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। আজ বঙ্গবন্ধু কন্যা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণেই তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা সম্ভব হলো। অন্যদিকে, ওই দিন গত বৃহস্পতিবার বিরোধী দলের হরতাল থাকার পরেও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে নাটোরের কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্টে যেন জনসাধারণ শহীদ কর্নেল কাদিরের সমাধীতে শ্রদ্ধা অর্পন করতে পারেন, সে জন্য সংশ্লিষ্ট পথে হরতাল শিথিল ঘোষণা করা হয়েছিল। এছাড়া বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার একজন প্রতিনিধি টেলিফোনে আমাকে টেলিফোনে সহানুভূতি জানিয়েছেন। এসব ঘটনা আমাদের মনে আশা জাগায়, শহীদরা যে ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে রাজনীতিকরা সকলেই ঐক্যবদ্ধ।
তিনি জানান, একাত্তরে নৃশংস হত্যার শিকার হয়ে নিখোঁজ থাকা নামে কর্নেল কাদিরের কবরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল ২০০৭ সালে। গত বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম নগরীর পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকায় একটি গণকবর থেকে কর্নেল কাদিরের প্রতীকী দেহাবশেষ সংগ্রহ করে তা পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় নাটোরের কাদিরাবাদ সেনানিবাসে নেওয়া হয়। পরে সেখানেই তাকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পুনঃসমাহিত করা হয়।
বেশ কিছুদিন আগে আরেক আড্ডায় নাদিম কাদিরের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যুদ্ধদিনের কথা। তখন তিনি বলেছিলেন, দেখুন তখন আমি নেহাতই বালক। আর যুদ্ধদিনের সব স্মৃতি আমার বাবা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা লেফটেনেন্ট কর্নেল আব্দুল কাদিরকে ঘিরে। …
এটিএন নিউজের এই সাংবাদিকের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, পাকিস্তান সেনা বাহিনীর সেই বিদ্রোহী মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল কাদিরের কথা।
তিনি বলেন, আমি বড় হয়ে মা’র (হাসনা হেনা কাদীর, ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির অন্যতম সংগঠক, ১৯৯৯ সালে প্রয়াত) কাছেই বেশীর ভাগ কথা শুনেছি। আমার স্মৃতিতেও বাবার বেশ কিছু কথা রয়েছে। আর এখন তো সাংবাদিক, গবেষকরা নিজস্ব উদ্যোগে অনুসন্ধান করে জানাচ্ছেন, মুক্তিযুদ্ধে আমার বাবা কতোটা অবদান রেখেছিলেন।
স্মৃতি হাতড়ে তিনি বলে চলেন, পাকিস্তান সেনা বাহিনীতে আমার বাবা বরাবরই বাঙালি সেনা কর্মকর্তা হিসেবে গর্বিত ছিলেন। তিনি অনেকটাই খোলামেলাভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সায়ত্বশাসন তথা ছয় দফার পে কথা বলতেন। এ জন্য পাক-সেনারা তাকে ‘ভাষানী’ বলে ডাকতো। এমনও হয়েছে, তাকে একবার এক পাঞ্জাবি সেনা কর্মকর্তা ’এই বাঙালি, ইথারমে আও’ বলে ডেকেছে। আর বাবা গিয়ে তাকে একটা চড় মেরে বলেছেন, বাঙালি কি আমার নাম? এ জন্য তাকে কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি পর্যন্ত হতে হয়। পরে সেখানে বাবা নির্দোষ প্রমানিত হন।…
আমার মনে আছে, ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ যেদিন রেডিওতে প্রচার হয়, সেদিন বাবা খুশীতে খুবই উৎফুল্ল ছিলেন। বার বার বলছিলেন, যুদ্ধ শুরু হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। এবার আমরা স্বাধীন হবো। …
এরপর একদিন বাবা আমাদের ছোট-ভাইবোনদের জন্য কিনে দেন স্বাধীন বাংলার একটি বড় পতাকা। সেটি বাঁশ পুঁতে চট্টগ্রামের পাঁচলাইশের যে কোয়ার্টারে তখন আমরা থাকতাম, সেখানে লাগানো হয়। আর বাবা নিজের গাড়িতে লাগাতে শুরু করেছিলেন স্বাদীন বাংলার ছোট একটি পতাকা। তখন অনেকে তাকে বলেছেন, কর্নেল সাহেব, আপনি যে এসব করছেন, দেখবেন শিগগিরই হয়তো আপনার বিপদ হবে। কিন্তু তিনি এ সবের তোয়াক্কা করেননি।
সে সময় পূর্ব পাকিস্তান তৈল-গ্যাস উন্নয়ন সংস্থার প্রধান নিয়ন্ত্রক (অপারেশন) পদে থাকার সময় আমার বাবা শহীদ জাতীয় নেতা কামরুজ্জামানকে একটি চিঠি লিখেছিলেন (পরে এই চিঠিটির ফটোকপি আমি সংগ্রহ করি), যেখানে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান কীভাবে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে অসহযোগিতা করছে, তা তিনি বিস্তারিত জানিয়েছিলেন। আর তেল-গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধানের জন্য যে সব বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়, বাবা সে সময় প্রচুর পরিমানে এ সব বিস্ফোরক গোপনে সরবরাহ করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের। তারা শোভাপুর ব্রিজ উড়িয়ে দিয়েছিলেন এই বিস্ফোরক ব্যবহার করে। …
এদিকে ২৭ মার্চ পুরো চট্টগ্রামের দখল নেয় পাকিস্তানী সেনা বাহিনী। সে দিন রাতে আমরা পাঁচলাইশের বাসায় পর্দা টেনে ভয়াবহ আতংকের রাত কাটাই। সারারাত ভয়াবহ গোলাগুলির শব্দ শুনি। ৭-৮ এপ্রিলের দিকে বাবা বাসা থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে যান। পরে ১৪ এপ্রিল বাসায় ফিরে তিনি মাকে বলছিলেন, নাহ, বের হয়ে যেতে পারলাম না। সব রাস্তায় ওরা পাহারা বসিয়েছে। আমি কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে ফিরেছি। …
পরে জেনেছি, বাঙালি সেনা কর্মকর্তা মেজর রফিক, এমআর সিদ্দিকীসহ আরো কয়েকজনের সঙ্গে বাবা পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, প্রত্যেকের বাড়িতে দুটি করে গাড়ি পাঠানো হবে। একটিতে করে বাবাসহ বিদ্রোহী অন্য বাঙালি সেনা কর্মকর্তারা সরে পরে কোনো একটি গোপন স্থানে জড়ো হবেন, মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করবেন। আর অন্যটি করে আমরা পরিবারের সদস্যরা নিরাপদ স্থানে সরে পড়বো। একই ভাবে সব বিদ্রোহী সেনা কর্মকর্তাদের পরিবারকেও নিরাপদ কোনো স্থানে সরিয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য কোনো কারণে এই গাড়িগুলো আর আসেনি।
আমার এখনো মনে আছে, ১৭ এপ্রিল সকালে পাঁচলাইশের দোতলা বাসায় বাবা নাস্তা সেরে নিজের শোবার ঘরে বসে আছেন। আমি মা, আর আমার ছোট বোন নাস্তা খাচ্ছি। এমন সময় বাসার দরজায় জোরে জোরে ধুম-ধাম ঘা পড়তে লাগলো। আমাদের দুজন স্টাফ জানালা দিয়ে উঁকি মাকে জানালো, আর্মি এসেছে। আমি গিয়ে বাবাকে বললাম, আমি কি দরজা খুলে দেবো? বাবা বললেন, হ্যাঁ, খুলে দাও। …
দরজা খুলে দিতেই একজন পাক ক্যাপ্টেন ও কয়েকজন সোলজার বন্দুক উঁচিয়ে ঘরে ঘরে ঢুকে পড়লো। তারা সরাসরি শোবার ঘরে ঢুকে বললো, ইউ আর আন্ডার এরেস্ট! বাবা তার প্রিয় শার্ট-প্যান্ট পড়ে তৈরি হয়ে নিলেন। ঘড়িটি হাতে নিলেন, মানি ব্যাগ পকেটে পুরলেন। চলে যাওয়ার সময় মাকে বললেন, নিজের দিকে খেয়াল রেখো, বাচ্চাদের দিকে ল্য রেখো। আমার ছোট ভাইটি তখন মার পেটে। …
গলায় আটকে আসা কান্না চেপে নাদিম কাদির বলে চলেন, পাক সেনারা যখন বাবাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তখন আমি পিছু পিছু সিঁড়ি পর্যন্ত ছুটে যাই। সিঁড়ি বারান্দার জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, বাবাকে বন্দুকের মুখে সেনা বাহিনীর জিপে তোলা হচ্ছে। গাড়িতে ওঠার আগে বাবা একবার মাথা উঁচিয়ে তাকালেন, আমাদের বাসার দিকে। তিনি আমাকে দেখলেনও। আমি তাকে দেখে হাত নাড়লাম। জবাবে তিনিও একবার হাত নাড়লেন। সেটাই আমার বাবাকে শেষ দেখা।…
জানতে চাওয়া হয়েছিল, এর পর আপনার বাবা শহীদ কর্নেল কাদিরের কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো?
তিনি ছোট্ট একটি শ্বাস চেপে বললেন, নাহ। কেউ তাঁর কোনো সন্ধান দিতে পারেনি। এমন কী দীর্ঘ ৩৪ বছর আমরা জানতেও পারিনি, কী নির্মমভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো! …
তিনি স্মৃতি চারণ করে বলেন, ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল সকালে আমাদের চট্টগ্রামের পাঁচলাইশের বাসা থেকে পাকিস্তানী সেনারা ধরে নিয়ে যাওয়ার আমরা সেনা নিবাসে তাঁর খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাঁর কোনো খবরই পাওয়া যাচ্ছিলো না।
কয়েকদিন পর পাক সেনার এক ক্যাপ্টেন কয়েকজন সোলজারসহ বন্দুক উঁচিয়ে আমাদের বাসায় আসে। তারা মা’র (হাসনা হেনা কাদির) কাছে জানতে চায়, আমার বাবার বন্দুকটি কোথায়? তিনি তাকে বন্দুকটি এনে দেন। এর পর সেই ক্যাপ্টেন বার বার মাকে বলেন, কর্নেল সাহেবের পিস্তল কোথায়? সেটি আপনি কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন? মা বরাবরই অস্বীকার করেন, বাবার কোনো সার্ভিস-পিস্তল ছিলো না। কিন্তু ক্যাপ্টেন এ কথা বিশ্বাস করে না। সে মাকে বলে, জিজ্ঞাসাবাদে বাবা নাকি তাদের জানিয়েছে, তার একটি পিস্তলও আছে।
বাদানুবাদের এক পর্যায়ে ক্যাপ্টেনের আদেশে মা, আমার চেয়ে সামান্য বড় বোন ও আমাকে লাইন-আপ করা হলো। সোলজাররা আমাদের দিকে বন্দুক তাক করে দাঁড়ালো। ক্যাপ্টেনটি হুমকি দিয়ে মাকে বললো, জলদি বলুন, পিস্তল কোথায়? নইলে সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলবো। আমার মা তাদের বলেন, মারতে হয় আমাকে মারো। কিন্তু খবরদার! বাচ্চাদের গায়ে কেউ হাত দেবে না!
ক্যাপ্টেনটি বলে, নাহ। আপনাকে খুন করা ঠিক হবে না। কারণ আপনি গর্ভবতি ( সে সময় আমার ছোট ভাই মার পেটে)।
পরে সে সোলজারদের নিয়ে মার শোবার ঘরে ঢোকে। মাকে স্টিলের আলমারি খুলে গহনা-গাঁটি, টাকা-পয়সা — যা কিছু ছিলো, সব দিয়ে দিতে বলে। মা আলমারী খুলে সব তাদের দিয়ে দেন।
তারা যখন চলে যাচ্ছিলো, তখন আমি ক্যাপ্টেনের কাছে জানতে চাইলাম, আঙ্কেল, আমার বাবা কবে বাসায় আসবেন?
ক্যাপ্টেন অনেকণ চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো। তারপর বললো, আ জায়গা। ফিবরে মাত করো।…
এদিকে বাবার অফিসের গার্ড এসে মাকে বলেন, আমি খবর নিয়ে জেনেছি, স্যারকে মেরে ফেলা হয়েছে। কিন্তু মা তাঁর কথা বিশ্বাস করেননি।
আমার মনে আছে, একদিন আমি জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, আমাদের বাসার পাশেই পাহাড়ের ওপর হিন্দুদের ‘প্রবর্তন সংঘে’ পাক-সেনারা ঢুকে পাহাড়ের কিনারে লাইন করে দাঁড় করিয়ে পাখির মতো গুলি করে মারছে। আর মানুষগুলো গুলি খেয়ে একে একে গড়িয়ে পড়ছে খাদের ভেতর। আমি ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠি, এসব কি হচ্ছে! এ সব কি হচ্ছে! আমার মা এসে চোখ চেপে ধরে আমাকে জানালা থেকে সরিয়ে দেন।
সাংবাদিক নাদিম কাদির যুদ্ধদিনের কথা বলে চলেন, এমননি পরিস্থিতিতে আমার মা বুঝতে পারছিলেন, ওই বাসায় থাকলে হয়তো একদিন আমরাও সবাই মারা পড়বো। তিনি বাসা থেকে পালানোর একটা উপায় খুঁজছিলেন। প্রতিবেশীর একটি গাড়ি পেয়ে তিনি আমাদের নিয়ে বাবার পরিচিত একজনের বাসায় আশ্রয় নেন। কিন্তু তিনি পাক-সেনাদের টেলিফোন করে জানিয়ে দেন যে, কর্নেল কাদিরের স্ত্রী ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে তার বাসায় উঠেছে। এমন অবস্থায় আমার মা কাঁদতে শুরু করেন।
এদিকে কারফিউ শিথিল হলে এক দূর সম্পর্কের চাচা রহুল আমিন বাবার গ্রেফতারের খবর পেয়ে আমাদের খোঁজ করতে এসে জানতে পারেন, আমরা কোথায় আছি। তখনই তিনি একটি গাড়ি জোগাড় করে সেখানে এসে চট করে আমাদের নিয়ে সরে পড়েন। পরে আমরা বহুদিন তার বাসায় লুকিয়ে থেকেছি। তারই সহায়তায় ছদ্মনামে মাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই ছোট ভাই জন্ময়। মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী বলে মা হাসপাতালের ডাক্তার-নার্স সকলের বিশেষ সেবা পেয়েছিলেন।
স্বাধীনতার পর আমরা চট্টগ্রামের পাট চুকিয়ে দিয়ে ঢাকায় চলে আসি। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আমরা জানতে পারিনি, আমার বাবা আদৌ বেঁচে আছেন কী না? অথবা কী ঘটেছে তাঁর ভাগ্যে?
নাদিম কাদির একটু দম নিয়ে বলেন, স্বাধীনতার পর পরই রেড ক্রিসেন্ট তাদের নিজস্ব অনুসন্ধানের সূত্র ধরে জানিয়েছিলো, কর্নেল কাদির ওয়াজ কিল্ড ইন অ্যাকশন। কিন্তু তারা এর স্বপে কোনো প্রমান দেখায় নি।
১৯৯৯ সালে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমার মা কোনদিনই বিশ্বাস করেননি যে, বাবাকে হত্যা করা হয়েছিলো। তিনি বলতেন, আগে যথেষ্ট তথ্য প্রমান পাই, তারপর না হয় বিশ্বাস করবো।
১৯৭৭ সালে এসএসসি পরীক্ষার পর ঢাকা থেকে আমি একাধিকবার কখনো একা, কখনো মা-সহ চট্টগ্রামে ছুটে ছুটে গিয়েছি, কেউ আমার নিখোঁজ বাবার কোনো সন্ধান দিতে পারেন কি না। আমরা অসংখ্য লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছি, বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান চালিয়েছি। কিন্তু কেউ আমাদের সঠিক কোনো তথ্য দিতে পারেনি। এ অবস্থায় আমার মা ১৯৯৯ সালে আমার বাবার কোনো তথ্য জানতে না পেরেই মারা যান। আমি ২০০৭ সালে চট্টগ্রাম সেনা নিবাসে একটি বক্তৃতা দিতে গেলে কর্নেল বায়োজিত আমাকে জানান, তিনি চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি বইয়ে একবার পড়েছিলেন, পাক-সেনারা আমার বাবাসহ ১৮ জন পাঁচলাইশে হত্যা করেছে।
এরপর ওই বইটির লেখক ডা. মাহফুজুর রহমানের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, তিনি এই তথ্য পেয়েছিলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা নূরল ইসলামসহ আরো কয়েকজন প্রত্যদর্শীর সহায়তায় বধ্যভূমিটিকে খুঁজে পাই। এরপর মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সেনা বাহিনী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ সরকারের উচ্চ পর্যায়ে বহু ধর্ণা দিয়েছি। কিন্তু কেউই বধ্যভূমিটিকে সংরণ বা শহীদদের দেহাবশেষ উদ্ধারের বিষয়ে কোনো উদ্যোগই নেয়নি। উপরন্তু বধ্যভূমিটি দখল হয়ে গিয়ে সেখানে এখন গড়ে উঠেছে চারতলা বাড়ি। আর সরকারের উদ্যোগহীনতায় এখনো সেখানে শহীদদের স্মরণে একটি নামফলক পর্যন্ত লাগানো যায়নি!
ছোট্ট একটি বিরতির পর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রসঙ্গ আসে।
সাংবাদিক নাদিম কাদির খুব স্পষ্ট করে জানান, দেশের শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীদের পেছনে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মদদ রয়েছে বলে তাদের বিচার যেনো না হয়, সে জন্য বিচার কার্যের শুরুতে সরকারের ওপর মধ্যপ্রাচ্যের প্রবল চাপ কাজ করেছে। বরং এ জন্য পাকিস্তান সরকারের চাপ অতটা প্রবল নয়। মধ্যপ্রাচ্যে যেহেতু প্রচুর সংখ্যক জনশক্তি রপ্তানী হয়, সে সব দেশ থেকে বিপুল পরিমান বৈদেশিক মূদ্রা আয় হয়, সে কারণে সরকার এই বিচার কাজ শুরু করতে দেরী করেছে।
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হতেই হবে– এ কথা জানিয়ে বিশিষ্ট এই সাংবাদিক আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারের মাধ্যমে আমরা ইতিহাসের একটি পর্ব অতিক্রম করেছি। এখন সারাদেশের মানুষ দীর্ঘ প্রতিক্ষায় আছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য। অবিলম্বে এ বিচার হতেই হবে। নইলে ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না। আর জাতি হিসেবেও আমরা কখনোই ঐক্যবদ্ধ হতে পারবো না।
আওয়ামী লীগ সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গিকার, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার — এ কথা উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, এই অঙ্গীকারের জন্যই তারা ৩০ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজয় লাভ করেছে। এখন সরকার গঠনের পর তারা যদি এ কাজে ব্যর্থ হয়, আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দল হিসেবে হবে পুরোপুরি ব্যর্থ। সে ক্ষেত্রে হয়তো আর কোনোদিন এই বিচার হবে না। কারণ অন্য কোনো সরকার কখনোই এ বিচার করবে না।…
—
http://unmochon.net/node/936
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৪:৫৩582851
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৪:৫৩582851- রশীদ তালুকদার: একটি ব্যক্তিগত কথন
লিখেছেন: বিপ্লব রহমান • প্রকাশকাল: 27 অক্টোবর 2011 - 8:01অপরাহ্ন
____________________________________________________________
তখনো বালক বেলা একেবারের ছেড়ে যায়নি, নবম কী দশম শ্রেণীতেই যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের অন্যপাঠ সর্ম্পকে আগ্রহ জন্মে। এ কারণে ১০ জানুয়ারি, ২১ ফেব্রুয়ারি, ৭ মার্চ, ২৫ মার্চ, ৭ নভেম্বর, ১৪ ডিসেম্বর, ১৬ ডিসেম্বর -- ইত্যাদি বিশেষ দিবসের কাগজগুলোর নিবিড় পাঠ করা হতো।
সে সময়ই নজরে আসে সাদা-কালো সংবাদপত্রের যুগে ঐতিহাসিক কিছু সাদাকালো ছবি, এর সব কয়েকটির আলোকচিত্রী ছিলেন রশীদ তালুকদার।
স্মরণ করা ভালো, ২১ এ ফ্রেব্রুয়ারিতে ইত্তেফাকের একটি লিড ফাইল ফটোতে দেখা হয়েছিল ১৯৭১ এর অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশের বেদনা বিধুর শহীদ মিনার। ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চ-লাইটে কামানের গোলায় পাকিস্তানি সেনারা গুড়িয়ে দিয়েছিল শহীদ মিনার। সে সময় ২১ ফেব্রুয়ারি পালন করার জন্য ছাত্ররা একই স্থানে ইট দিয়ে ছোট্ট একটি স্তম্ভ নির্মাণ করে একটু কাগজে আঁকাবাঁকা হরফে 'শহীদ মিনার' লিখে স্তম্ভের গায়ে সেঁটে দিয়েছিল। ১৯৭১ এ সেখানেই শ্রদ্ধার্ঘ দিয়েছিল নিস্পেষিত, বিক্ষুব্ধ বাঙালি।
আবার ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসের আরেক লিড ছবি ও ফাইল ফটোতে দেখা যায়, পাকিস্তানি সেনা বাহিনীর ট্যাংঙ্ক হামলায় বিধ্বস্ত টিকাটুলির ইত্তেফাক ভবন। এই ছবিটির আলোকচিত্রীও ছিলেন রশীদ তালুকদার। অবশ্য সে সময় ২৫ মার্চের গণহত্যার ফাইল-ফটো নিয়ে যে একপাতার ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হতো, সেখানে তার তোলা বিধ্বস্ত প্রেসক্লাব ভবন থেকে শুরু করে হত্যাযজ্ঞের মর্মান্তিক একাধিক ছবিও স্থান পেতে।
৭ নভেম্বর সিপাহী-জনতার অভ্যূত্থান দিবসে তার তোলা ইত্তেফাকের আরেকটি লিড ও ফাইল ফটো ছিল অনেকটা এ রকম, ওই ছবিতে দেখা যায়, একটি খোলা সামরিক ট্রাকে করে বিদ্রোহী সৈনিকরা অস্ত্র উঁচিয়ে কয়েকজন উর্দ্ধতন সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছেন, গ্রেফতারকৃতরা ট্রাকে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন, তাদের প্রত্যেকের মুখ ও মাথা কাপড় দিয়ে ঢাকা। আর বিদ্রোহী সৈনিকরা ট্রাকটিতে দাঁড়িয়ে...তাদের চোখে-মুখে বিজয়ের উল্লাস।
আবার রশীদ তালুকদারের ৭ নভেম্বরের আরেকটি ফাইল ফটো ছিল এ রকম, বিদ্রোহী সৈনিকদের নেতা জেনারেল জিয়াউর রহমান কালো রোদ চশমা পরে হাত উঁচিয়ে জনতাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, তাকে ঘিরে রেখেছেন সামরিক-বেসামরিক বিদ্রোহীরা, পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে জিয়ার মাথায়।
আর ১৬ ডিসেম্বরের অনিবার্য ছবি ছিলো, খোলা ট্রাকে করে ফাঁকা গুলি ফোটাতে ফোটাতে বীর বেশে মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকায় প্রবেশ করছেন, তাদের অভিনন্দন জানাতে ট্রাকের পিছু নিয়েছে সদ্য স্বাধীন দেশের উল্লসিত মুক্তিকামী জনতার একাংশ।
আসলে ওই ঐতিহাসিক ছবিগুলো ছাড়াই এমনি করে ছবির পাঠ হয়তো খানিকটা অস্পষ্টতাই বাড়িয়ে দেয়। তবে ব্লগাড্ডার এই পর্বে এইটুকু নাম ভূমিকার হয়তো দরকারি; আর ওই ছবিগুলোর যখন অন্তর্জাল সংস্করণই নেই। এর বাইরে এই লেখায় প্রদর্শিত ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে শেখ মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, ৭ মার্চ পল্টন ময়দানের জনসমূদ্রে শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণ, ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে রায়ের বাজার বধ্যভূমির দৃশ্য, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের কালে ডামি রাইফেল নিয়ে ঢাকার রাজপথে ছাত্রীদের মার্চপাস্টসহ ১৯৭১ এর আরো অসংখ্য ছবি তো ছিলই।
তবে এই লেখককে চমকে দিয়েছিল, সব ছবি ছাপিয়ে ছিল এই লেখার সূচনা ছবিটি। সেখানে দেখা যায়, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানেরকালে ঢাকার রাজপথে বের হয়েছে ছাত্র-জনতার এক বিশাল মিছিল। সেখানে খালি গায়ে, খালি পায়ে একটি ঢোলা হাফট্যান্ট পরা এক টোকাই বালক ডান হাত উঁচিয়ে জোর শ্লোগান দিচ্ছে, তার জামাটি গুটিয়ে কোমড়ে বাঁধা।...
আটের দশকে ছাত্র অবস্থাতেই প্রচ্ছদ ছবি হিসেবে ওই ছবিসহ বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত এক ফটো-অ্যালবাম লেখকের হাতে আসে। সেখানে শুধু আলোকচিত্রী হিসেবে রশীদ তালুকদারের নামটুকু ছাড়া তেমন কোনো তথ্য না থাকায় ছবিটি আরো কৌতুহল আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল।
আরো পরে ছাত্র জীবন শেষে তথ্য সাংবাদিকতার পেশাগত সূত্রে ২০০২ সালে দৈনিক ভোরের কাগজে কর্মরত অবস্থায় খবর পাওয়া গিয়েছিল, পুরনো ঢাকায় একটি শিশুর লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের। ওই খবর সংগ্রহ শেষে পুলিশের ভাষ্য নিতে যাওয়া হয়েছিল কোতয়ালী থানায়। ব্রিটিশ আমলের থানা ভবনটিতে বসে ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তার (ওসি)ভাষ্য নেওয়ার কালে সেখানে এসে উপস্থিত হন আরেক সহকর্মি কাজী হাফিজ, তিনি তখন দৈনিক মানবজমিনে কাজ করতেন, এখন কালের কণ্ঠে একই সঙ্গে কর্মরত। দুপুর গড়িয়ে আসছে প্রায়।
এই সময় বড় ফ্রেমের চশমা পরা, কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগ ঝুলিয়ে খুবই সাদাসিধে পোষাকের একজন ফটো-সাংবাদিক এসে ওসির রুমে প্রবেশ করেন। রিপোর্টার দুজনই একসঙ্গে চমকে উঠেন-- ইনি রশীদ তালুকদার!
দ্রুত সালাম দিয়ে তাকে চেয়ার এগিয়ে দেওয়া হয়, ওসির সঙ্গে ওনার পরিচয় করিয়ে দিতে পুলিশ কর্মকর্তা নিজেও তটস্থ হয়ে ওঠেন: স্যার, বলুন, আপনার কী খেদমত করতে পারি। আপনি কী লাঞ্চ করেছেন? আপনার জন্য আমাদের পুরনো ঢাকার বিখ্যাত বিরিয়ানি আনতে বলি?
রশীদ ভাই মৃদু হেসে তাকে নিবৃত্ত করেন। বিনয় করে রিপোর্টার দুজনকে বলেন, আপনারা কাজ শেষ করুন প্লিজ। আমি আপনাদের কাজে ব্যঘাত ঘটাতে চাই না।
ততক্ষণে সরকারি চা এসে গেছে। ওসির সঙ্গে আলাপ-চারিতার শেষ পর্যায়ে হঠাৎ খেয়াল করা হয়, থানার ওই ছোট্ট ঘরের ভেতরেই মুক্তিযোদ্ধা আলোকচিত্রীর মটরস্পিডের এনালগ ক্যামেরার ফ্ল্যাশ ঝলসে উঠছে বার বার। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বোঝা যায়, রশীদ ভাইয়ের ছবির বিষয় থানার দেওয়ালের একদিন জুড়ে জালের মতো ছড়িয়ে পড়া বট-পাকুড় গাছের শেকড়ের বিচিত্র নকশা। পুরনো থানা ভবনটির ছাদে তখন জন্মেছিল ওইসব গাছ, এর শেকড় ইট-সিমেন্ট ভেদ করে থানার দেওয়াল দখল করে ফেলেছিল।
সহকর্মী হাফিজ ভাই কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলেন, দেখলেন তো রশীদ তালুকদারের চোখ! আমরা এতোক্ষণ ধরে থানায় বসে আছি, অথচ বিষয়টি এতোক্ষণ খেয়ালই করিনি!
এই ফাঁকে বেশ খানিকটা বিচলিত ওসি বলে চলেছেন, পুরনো ভবনটির নানা দুরাবস্থার কথা। সামান্য বৃষ্টিতেই থানার ছাদ চুঁইয়ে পানি পড়ে, নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ওপর মহলে অনেক লেখালেখি করেও ফল হয়নি-- ইত্যাদি।
এর আগে '৯০ এর ছাত্র-গণআন্দোলনে লেখক নিজেও জড়িয়ে পড়লে এরশাদ বিরোধী একের পর এক হরতাল, অবরোধ, ঘেরাও -- ইত্যাদি রাজপথের কর্মসূচিতে রশীদ তালুকদারের ক্যামেরাবাজি চোখে পড়েছে। পরে নিজস্ব সাংবাদিকতার জীবনেও প্রেস ক্লাবে তার সঙ্গে বেশ কয়েকবার কুশল বিনিময় হয়েছে, তবে সামনা-সামনি গুনিজনকে একান্তে পাওয়া ওই প্রথম। সুযোগটিকে কাজে লাগাতে হঠাৎ আলাপের মোড় ঘুরিয়ে জানতে চাওয়া হয়, ১৯৬৯ এর বিদ্রোহী টোকাই ছবিটির ইতিবৃত্ত। ...
রশীদ ভাই সে সময় সামান্য হেসে, চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে যা বলেছিলেন, তা অনেকটা এরকম:
তখন তো ঢাকা জুড়ে প্রতিদিনই বিশাল সব মিছিল-মিটিং হচ্ছে। শ্লোগান উঠেছে: ছাত্র-জনতা ভাই, ভাই/ আইয়ুব শাহীর রক্ষা নাই! ছাত্রমিছিলগুলোতে শ্রমিক, কর্মচারি, পেশাজীবী নানা মানুষ নিয়মিত অংশ নিচ্ছে। পুলিশ-ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, সীমান্তরক্ষি আধা-সামরিক বাহিনী) এখানে-সেখানে গুলি চালাচ্ছে। ২০ জানুয়ারি ছাত্র নেতা আসাদ গুলিতে শহীদ হওয়ার পর ঢাকাসহ পুরো দেশ বিক্ষোভে একেবারে ফেটে পড়েছে। ...
এরকমই একদিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র-জনতার বিশাল একটি মিছিল রাজপথে বের হয়েছে। মিছিলটি নীলক্ষেত হয়ে ঢাকা কলেজের দিকে যাচ্ছে। আমি মিছিলের সামনে থেকে একের পর এক ছবি তুলছি। কিন্তু আমরা সঙ্গে ওয়াইড লেন্স না থাকায় মিছিলের সামনের চওড়া সারিটি কিছুতেই একই ফ্রেমে আসছিল না। মিছিলটি বলাকা বিল্ডিং (বলাকা সিনেমা হল) ছাড়িয়ে আরেকটু সামনে আসতে, এখন যেখানে ওভার ব্রিজ হয়েছে (গাউছিয়া মার্কেটের সামনে) সেখানে দেখি কোথা থেকে একজন টোকাই মিছিলের আগে আগে যাচ্ছে। সেও মিছিলের সঙ্গে হাত উঁচিয়ে খুব শ্লোগান দিচ্ছে।
ওয়াইড লেন্সের অভাব পূরণ করতে আমি মিছিলের সামনের সারিটি বেশ কয়েকটি ফ্রেমে ক্যামেরা বন্দি করতে থাকি। আমার চিন্তা ছিল, পরে সবগুলো ছবি জোড়া দিয়ে একটি পুরো ছবি তৈরি করবো যেখানে মিছিলের সবটাই ধরা পড়বে।...
হঠাৎ সেখানে ওত পেতে থাকা পুলিশ-ইপিআর একসঙ্গে গুলি করতে শুরু করলো। আমি ছবি তোলার পর পরই দেখি গুলিতে টোকাই শিশুটি ছিটকে পড়লো। সবাই প্রাণ বাঁচাতে ছুটোছুটি শুরু করে দিল। আমিও নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে দৌড় লাগালাম। পরে জেনেছি, পুলিশের গুলিতে শিশুটি ঘটনাস্থলেই মারা গেছে। ...
রশীদ ভাইয়ের সঙ্গে সেই শেষ বারের মতো একান্তে আলাপ। এরপর তার সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে একাধিকবার দেখা হলেও কুশল বিনিময় ও হ্যান্ডশেক ছাড়া আর তেমন কথা হয়নি।
আজ যখন এই মহান ইতিহাসের বিদায় বেলায় তারই স্মৃতিকথা বলা হচ্ছে, তখন গভীর বেদনা ভাড়ি হয়ে আসছে বুক। শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসছে মাথা। রশীদ তালুকদার, আপনি সশ্রদ্ধ সালাম গ্রহণ করুন।।
_____________________
http://unmochon.net/node/1071
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৮:৪৭582852
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৮:৪৭582852- মিথ্যাচারের ঐতিহ্য : আ স্ট্রেঞ্জার ইন মাই ওন কান্ট্রি
লিখেছেনঃ প্রীতম (তারিখঃ রবিবার, ২৬/০৮/২০১২ - ০১:২৫)
__________________________________________________________
পাকিস্তান - একটি ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাসঘাতক রাষ্ট্র।একই সাথে মিথ্যাচারের ঐতিহ্যও মিশে আছে পাকিস্তানিদের রক্তের পরম্পরায়। অভিশপ্ত এই দেশটির রাষ্ট্র ও সেনানায়কেরা বাঙালি জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করেছে ১৯৪৭ সাল থেকেই,একটি অবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানের জন্মের পরপরই। সেই ধারাবাহিকতা তারা বজায় রেখেছে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত। ২৫ মার্চ,১৯৭১ ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংস গণহত্যাগুলোর একটির সূচনা করে পাকিস্তানি সেনানায়কেরা,এবং তাতে প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সহযোগিতা দেয় পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতারা ( কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম ধর্তব্য নয় )।
গণহত্যার সেই নয়টি মাস এইসব পাকিস্তানি প্রচার করেছে বাংলাদেশের কোন গণহত্যা ঘটছে না,সামরিক পদক্ষেপ যা নেয়া হয়েছে তা মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য অপরিহার্য ছিল।মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধা বলে কিছু নেই - পুরোটাই ভারতের ষড়যন্ত্র।বলা বাহুল্য,এইসব পাকিস্তানি মিথ্যাচার বিশ্বনাগরিকের যুক্তিবোধের কাছে ধোপে টেকেনি।যার ফলাফল রণাঙ্গনে পরাজয়।
তবে এতে হতোদ্যম নয় মিথ্যাচারের জিনবাহী পাকিস্তানি সেনানায়কেরা।একের পর এক তারা আত্মজীবনী লিখেছে,প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে তারা নির্দোষ।কেউ দায় চাপিয়েছে রাজনৈতিক নেতাদের ঘাড়ে,কেউ চাপিয়েছে অন্যান্য সেনানায়কের ঘাড়ে।সকলেরই আক্রমণের সাধারণ লক্ষ্য শেখ মুজিব,কারো কারো ক্ষেত্রে ভুট্টোও।বাঙালির ত্যাগকে অস্বীকার করে সবকিছুকে ভারতের ষড়যন্ত্র বলে চালিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করেনি কেউ।এই তালিকায় আছে সিদ্দিক সালিক,আছে গণহত্যার দুই প্রধান খলনায়ক আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি এবং রাও ফরমান আলি,আছে জেড এ খান,এ আর সিদ্দিকি এবং আরো অনেকে।সেই তালিকায় সর্বশেষ যুক্ত হয়েছে খাদিম হোসেন রাজা।আ স্ট্রেঞ্জার ইন মাই ওন কান্ট্রি নামে ছয়শো পঁচানব্বই রুপী মূল্যের একশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠার একটি বই লিখে কয়েকদিন ধরেই আলোচনার শীর্ষে বিরাজমান এই প্রয়াত পাকিস্তানি সেনানায়ক।
এই খাদিম হোসেন রাজার পরিচয় কী?কেন তাকে নিয়ে এত আলোচনা?
খাদিম হোসেন রাজা একজন সাবেক পাকিস্তানি জেনারেল,১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের একেবারে প্রথম পর্যায়ে তার অবস্থান বাংলাদেশেই ছিল।হঠাৎ তাকে নিয়ে এত আলোচনার কারণ হলো তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত পূর্বোক্ত বইটি।এতে নাকি অনেক গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে,যা জীবদ্দশায় প্রকাশের হিম্মত হয়নি জেনারেল রাজার।কী সেই গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য?বইটিতে স্বীকার করা হয়েছে যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যা হয়েছে,হিন্দু নিধন হয়েছে,ধর্ষণের মাধ্যমে বাঙালি নারীর পেটে পাকিস্তানি সন্তান ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।এবং সব কিছুর মূল হোতা টিক্কা খান ও নিয়াজি।
কথা একেবারে মিথ্যে নয়।যা যা ঘটার কথা বলা হয়েছে তা যে আসলেই ঘটেছে সে তো প্রমাণিত সত্য।পাকিস্তানি লেখকেরাই এসব কথা স্বীকার করেছে ( যেমন সিদ্দিক সালিক,তাজাম্মাল হুসাইন মালিক )।তাহলে এই বই নিয়ে এত মাতামাতির কারণ কী?বিস্তারিত জানতে বইটি এমাথা ওমাথা চিরুনি চষা হলো এবং শেষ পর্যন্ত জানা গেল - কোন বিস্ফোরক তথ্যই এতে নেই,বরং রয়েছে কিছু নির্লজ্জ মিথ্যাচার।রয়েছে রাজার নিজের হাতে লেগে থাকা রক্তের দাগ হালাল করার নোংরা চেষ্টা,রয়েছে পাকিস্তানিদের চিরাচরিত বাঙালি বিদ্বেষ,হিন্দু বিদ্বেষ।সাথে অতি অবশ্যই মুজিব বিদ্বেষ,ভারতের চক্রান্ত নিয়ে গৎবাঁধা বকবক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান - নিয়াজির ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে,অপারেশন সার্চলাইটের অন্যতম প্রধান পরিকল্পনাকারী এবং বাস্তবায়নকারী হিসেবে নিজের পরিচয়টির উপরে খুব কৌশলে প্রলেপ দেয়ার চেষ্টা।গণহত্যা এবং নারী ধর্ষণ সংক্রান্ত সে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে,সেগুলোর জন্য বরাদ্দ রয়েছে বইয়ের একেবারে শেষের দিকে অল্প কয়েকটি অনুচ্ছেদ,সেটি আরেকজনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে পীর-দরবেশ প্রমাণের চেষ্টা ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়।এছাড়া পুরো বইটি ভিত্তিহীন আবর্জনায় ভরা।শেষ পর্যন্ত বইটি ঐতিহ্যবাহী পাকিস্তানি মিথ্যাচারের আরেক নিদর্শন হয়ে রইলো।
খুব সংক্ষেপে বইটির একটি সামারি দেখে নেয়া যাক।
## একেবারে প্রথমেই প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে - বাঙালি এবং হিন্দু মোটামুটি সমার্থক।এদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই।পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্বে হিন্দুর সংখ্যা বেশি,তাই এই অঞ্চলের সংস্কৃতি হিন্দু ঘেষা।রাজার যশোরে থাকার অভিজ্ঞতা দিয়ে বলা হয়েছে ভারতের সাথে প্রায় মুক্ত সীমান্তের কথা,হিন্দুদের সম্পত্তি ভারতে পাচার করা কথা।সমরীকরণটি এরকম - বাঙালি মানেই হিন্দু;হিন্দু মানেই ভারতীয়;ভারতীয় মানেই পাকিস্তানের শত্রু;নেট ফলাফল বাঙালি মানেই পাকিস্তানের শত্রু।
## এর পর ইনিয়ে বিনিয়ে বহু কথা দিয়ে রাজা সাহেব বলতে চেয়েছেন পশ্চিম পাকিস্তানি সেনানায়কেরা বরাবরই পূর্ব পাকিস্তানের সৈনিকদের উপর নরম গরম আচরণ করেছেন,কিন্তু এই বাঙাল জাতটাই খারাপ।তারা আত্মকেন্দ্রিক,অমিশুক,তারা পশ্চিমের লোকজন পছন্দ করে না।এখানকার সাইনবোর্ড বাংলায় লেখা হয়,উর্দুতে হয় না বলে ভারি গোস্বা তার।মাঝে মধ্যেই রাজা সাহেব নিজে অথবা অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসাররা বাঙালিদের সাথে মিশতে গিয়ে অপমানিত হয়েছেন,দুই একবার চড় থাপ্পড়ও খেয়েছেন।
## সমান্তরালে এসেছে মুজিব বিদ্বেষ।মুজিব এবং আওয়ামীলীগ মিথ্যাবাদী।দুই প্রদেশের মাঝে বৈষম্যের যেসব বিবরণ আওয়ামীলী সত্তরের নির্বাচনের আগে প্রচার করেছে তা নির্জলা মিথ্যাচার।অবাঙালিদের প্রতি মুজিব এবং বাঙালিরা বন্ধুভাবাপন্ন নয়।মুজিব ক্ষমতালোভী।একই সাথে মুজিবের ইমেজ খর্ব করার একটি চেষ্টাও করা হয়েছে,মুজিবকে আসলে যতটা বড় ভাবা হয় ততটা বড় তিনি নন।
## সব দোষ ইয়াহিয়ার।রাজা সাহেব কখনোই সামরিক হস্তক্ষেপ চাননি।এর প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগও করতে চেয়েছিলেন।কিন্তু বেয়াড়া রাজনৈতিক নেতাদের গোয়ার্তুমি ঠান্ডা করতে গিয়ে কিছুটা কঠোর হতে হয়েছে,অবশ্যই ইচ্ছের বিরুদ্ধে।অপারেশন সার্চলাইটের পরিকল্পনা তিনি বানিয়েছেন সত্য,তবে তা নিজের ইচ্ছেয় নয়।দেশের সার্বিক মঙ্গলের জন্য এ ছাড়া উপায়ও ছিল না।ভাবখানা এমন,মুজিব-ভুট্টো আপোষে আসতে পারেনি বলে নিতান্ত ঠেকায় পড়েই দেশের নাগরিকদের কল্যানে এপথে পা বাড়াতে হয়েছে তাকে।এর পর নিজের দায়িত্ব সততা এবং পেশাদারিত্বের সাথে পালন করেছেন তিনি।সেজন্য তিনি বিন্দু মাত্র অনুতপ্ত নন,বরং নিজের সেনাবাহিনীর দক্ষতায় গর্বিত।ছাব্বিশে মার্চ সৈনিকেরা তার নামে স্লোগানও দিয়েছে।
সামারি মোটামুটি এই।সবশেষে গণহত্যার দোষ সব টিক্কা-নিয়াজির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তিনি সুফী দরবেশ হিসেবে দেশে ফিরে গিয়েছেন।উল্লেখ্য,প্রবল হিন্দু বিদ্বেষের পাশাপাশি নিজের মুসলমান পরিচয়টিকে হাইলাইট করতে ভুলে যাননি রাজা সাহেব।বইয়ের একেবারে প্রথম দিকেই নিজের হজ্ব পালনের কথা লিখেছেন তিনি,বেশ ফলাও করেই।
এবার আমরা একটু তথ্য উপাত্তের দিকে তাকাবো।খাদিম হোসেন রাজার ভূমিকাটি আসলে কী ছিল সে সময়ে?
প্রথমেই মনে রাখতে রাখতে হবে সেসময়ে খাদিম হোসেনের ক্ষমতা ও দায়িত্বের পরিধি। ১৯৭১ সালে,মিলিটারি ক্র্যাকডাউন অর্থাৎ গণহত্যা যখন শুরু হয়,সেসময়ে খাদিম হোসেন রাজা ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র ডিভিশন ১৪ ডিভিশনের জিওসি ( জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং )।রাও ফরমান আলি ছিলেন বেসামরিক প্রশাসনের মেজর জেনারেল।এর অর্থ হচ্ছে,রাজা সাহেব সম্মত হোন বা অসম্মত হোন,ব্যথিত হৃদয়ে চোখ মুছতে থাকুন কিংবা হুইস্কির গ্লাস হাতে হাসতে থাকুন - তিনি পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত এখানে যেসব সামরিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার সবকিছুর চূড়ান্ত দায়-দায়িত্ব তার ঘাড়ে আসবেই।
অপারেশন সার্চলাইটের পুরো পরিকল্পনাটি তৈরি হয় রাও ফরমান আলি এবং খাদিম হোসেন রাজার হাতে।এবং এতে রাজা সাহেবের আগ্রহ বা উৎসাহের কোন কমতি ছিল না।রাও ফরমান আলির স্মৃতিকথা হাউ পাকিস্তান গট ডিভাইডেড বইতে খাদিমকে শান্তিকামী সাধুপুরুষ বানানোর চেষ্টা করা হলেও ফাঁক গলে অনেক কিছুই বেরিয়ে গেছে।পরিকল্পনাটি তৈরির উল্লেখ আছে সিদ্দিক সালিকের উইটনেস টু সারেন্ডার বইতেও।
অপারেশন সার্চলাইট আসলে অপারেশন ব্লিৎজের উত্তরপুরুষ।ব্লিৎজের জন্মদাতা জেনারেল ইয়াকুব,একাত্তরের ফেব্রুয়ারিতে এই পরিকল্পনাটি তৈরি করা হয়।এর পর ১৮ মার্চ জেনারেল হামিদের নির্দেশে একাট্টা হন রাও এবং খাদিম,দুইজনে শলা পরামর্শ করে সিদ্ধান্তে আসেন - চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ব্লিৎজ খুব একটা কাজে আসবে না,অতএব একে সময়োপযোগী করতে হবে।পুরো প্রক্রিয়াটির বর্ণনা দিয়েছেন সিদ্দিক সালিক,
On 18 March(morning), Major-Gen Khadim Raja and Major-General Rao Farman Ali met in the G.O.C's office to draft the basic operational plan. Both of them agreed that the basis of operation BLITZ was no longer relevant, as has been amply demonstrated since 1 March. They also agreed that the aim of operation 'BLITZ' ( to enforce Martial law in its clasical role'), had likewise been superseded by events.Now, if and when an action was taken, it would have to aim aoverthrowing Mujib's de facto rule and re-establishing government authority.I
n the same sitting, General Farman wrote down the new plan on a light blue office pad, using an ordinary school pencil.I saw the original plan in General Farman's immaculate hand.General Khadim wrote its second part, which dealt with distribution of resources and allocation of tasks to brigades and units.The plan, christened 'Operation SEARCHLIGHT', consisted of sixteen paragraphs spread over five pages ( See Appendix III). It presumed that all Bengali troops, including regular East Bengal battalions, would revolt in reaction to its execution. They should therefore, be disarmed. Secondly, the 'non?cooperation' movement launched by Mujib should be deprived of its leadership by arresting all the prominent Awami League leaders while they were in conference with the President. The plan also listed, as an annexure, sixteen prominent persons whose houses were to be visited for their arrest.
The hand-written plan was read out to General Hamid and Lieutenant?General Tikka Khan at Flagstaff House on the afternoon of 20 March. Both of them approved the main contents of the plan but General Hamid struck out the clause pertaining to disarming the Bengali troops as `it would destroy one of the finest armies in the world'. He, however, approved the disarming of paramilitary forces like the East Pakistan Rifles and the Police. He asked only one question, 'After distribution of these troops for various tasks, are you left with any reserves?' 'No, Sir,' was the prompt reply from the G.O.C.
এখানে রাও ফরমানের সাথে এবং হামিদের সাথে খাদিমের আলোচনা খেয়াল করার মত।অপারেশন সার্চলাইটের চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ আসে হামিদের কাছ থেকে।এরপর পুরো দায়িত্বটি ন্যস্ত হয়েছে রাও এবং খাদিম হোসেনের উপর।তারা দুজন মিলেই সিদ্ধান্তে এসেছেন একটি রক্তক্ষয়ী পরিকল্পনা প্রয়োজন।এরপর পরিকল্পনা তৈরি হয়ে গেলে হামিদ যখন দুই একটি পয়েন্ট নিয়ে মৃদু সন্দেহ তুলেছেন,খাদিম আত্মবিশ্বাসের সাথে তা নাকচ করে দিয়েছেন।
প্রশ্ন আসতে পারে,দুইজন মিলে প্ল্যান করেছেন,এর মধ্যে খাদিমের অংশ কতটুকু।উত্তর হলো আধাআধি।এবং তা কোন দিক থেকেই ফরমানের অংশের চেয়ে কম ভয়ঙ্কর নয়।অপারেশনের মূল কৌশলগত দিকগুলি সাজিয়েছেন ফরমান,খাদিম হিসেব কষেছেন কোন খানে কী পরিমান ট্রুপ রাখলে পরিকল্পনা শতভাগ সফল হবে।পরিকল্পনার আরো ভেতরে গেলে দেখা যায়,এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব অনেকখানিই খাদিমের।পরিস্কারভাবে বললে ঢাকা ঠান্ডা করার দায়িত্ব রাও ফরমান আলির,প্রদেশের বাদবাকি অংশে বিদ্রোহ দমন করবেন খাদিম হোসেন রাজা।
এরপর,রাও ফরমান আলির বই থেকে দেখা যাচ্ছে,২৩ মার্চ খাদিম নিজেই রাও ফরমানকে ডেকে পাঠিয়েছেন তার হেডকোয়ার্টারে,পরিকল্পনাতে আখেরি ঘষামাজা করার জন্য।আরেক পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লা খান তার ইস্ট পাকিস্তান টু বাংলাদেশ বইয়ে লিখেছেন অপারেশন সার্চলাইট বাস্তবায়নে খাদিমের তৎপরতার কথা।২৪ মার্চ এই সাদুল্লাকে ডেকে পাঠিয়ে খাদিম হোসেন বলেছেন,
আমরা ২৫/২৬ তারিখে আঘাত হানবো।হয়তো আওয়ামীলীগও প্রস্তুত হচ্ছে।তারাও একটি ডি'ডে ঠিক করেছে।নির্দিষ্ট তারিখ আমরা জানি না,কিন্তু এটুকু জানি,তাদের সামরিক প্রস্তুতি যা করার ছিল তা হয়নি।আমি ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার গ্যারিসন কমান্ডারদের সাথে ব্রিফ করেছি।ফরমান যশোর ও খুলনার কমান্ডারদের ব্রিফ করেছে।আগামীকাল তুমি রংপুরের কমান্ডারদের ব্রিফ করো।রাজশাহীর কমান্ডিং অফিসার গতকাল হজ থেকে ফিরেছে।আমি তাকে বলবো কী করতে হবে।রংপুর থেকে ফেরার পথে তাকে রাজশাহী নামিয়ে দিও।
অর্থাৎ সব দিক দিয়েই প্রমাণিত - অপারেশন সার্চ লাইটের মত একটি নৃশংস পরিকল্পনা তৈরির দায় এড়ানোর কোন উপায় খাদিম হোসেন রাজার নেই।রাজনৈতিক সমাধানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তার আদৌ ছিল না,অন্য সব রক্তলোলুপ পাকিস্তানি সৈনিকের সাথে খাদিমের এক চুল পার্থক্য নেই।
এবার দেখা যাক,পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যাপারে কেমন ক্যারিশমা দেখিয়েছেন খাদিম হোসেন রাজা।রাজার দায়িত্বে ছিল ঢাকার বাইরে পুরো বাংলাদেশ।২৫ মার্চের সেই ক্র্যাকডাউনের পরে ঢাকার ভেতরে কি বাইরে - সারা দেশ জুড়ে কী চলেছে তা নতুন করে বলার কিছু নেই।খাদিম নিজে চট্টগ্রাম নিয়ে উৎসাহী ছিলেন,একথা তার বইতে তিনি লিখেছেন।চট্টগ্রামের কয়েকটি ঘটনার দিকে চোখ দিলেই বোঝা যাবে পুরো ব্যাপারটি।চট্টগ্রামে তিনি নিজেই উড়ে গিয়েছিলেন পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখার জন্য।পরে বেকায়দা দেখে হেডকোয়ার্টারই সরিয়ে নিয়া যান চট্টগ্রামে।এ প্রসঙ্গে এখানকার সাফল্য সম্পর্কে উচ্ছসিত মন্তব্য পাওয়া গেছে তার বইতে,
The recapture of Chittagong had broken the back of the rebels.They were on the run everywhere,trying to make for the nearest Indian territory.More troops reinforcements were arriving daily.The build-up of the 9 and 17 Divisions was progressing smoothly.Every day we were getting news of our troops retaking important towns.
বিদ্রোহীদের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিয়েছেন খাদিম।সৈনিকেরা প্রতিদিন নতুন নতুন এলাকা দখলে আনছে।এই শিরদাঁড়া ভাঙ্গাভাঙ্গির কিছুটা বিবরণ দিয়েছেন বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক সিডনি শনবার্গ।তার দুই একটি দেখে নেয়া যাক।
এপ্রিলের সাত তারিখে শনবার্গ লিখেছেন,
আর্মি বস্তি পোড়াচ্ছে
বিদেশীরা আরো জানিয়েছেন যে,২৬ মার্চ শুক্রবার খুব সকালে লড়াই শুরু হয়ে যায় এবং স্বাধীনতার সমর্থক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীর্ণ বস্তিগুলো সেনাবাহিনী পুড়িয়ে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।গতকাল সকালে সেনাপ্রহরায় যখন তাদের বন্দরে নিয়ে যাওয়া হলো এসব বাঁশের ঘরবাড়ির পোড়া ছাই ধিকিধিকি জ্বলছিল।
পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে রেডিও পাকিস্তান দাবি করেছে যে,গোটা পূর্ব পাকিস্তান শান্ত রয়েছে এবং জীবন যাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসছে।
' কোন কিছুই শান্ত নয়,কিছুই স্বাভাবিক হয়ে আসেনি' , বলেছেন মিস্টার মার্টিনুসেন।ডেনমার্কের আব্রাহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ-র পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে পাকিস্তানের রাজনীতি অধ্যয়নের জন্য তিনি স্ত্রী কারেনকে নিয়ে সাত মাস আগে চট্টগ্রামে এসেছিলেন।
তিনি আরো বলেন, ' ওরা পরিকল্পিতভাবে গরিব মানুষের ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে,কেননা ওদের মনে হয়েছিল এইসব বস্তিতে ভালোভাবে তল্লাশি চালানো সম্ভব নয়।যথেচ্ছ হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো তারা উপভোগ করছে বলেই মনে হয়। ' ...
স্বাধীনতা আন্দোলন
কৃশকায় এক ছাত্র বললেন, ' এতো বিপুলসংখ্যক বাঙালি যে বাংলাদেশ চাচ্ছে,তারা সেটা পাবে বলে আমি নিশ্চিত।
তার মতের প্রতিধ্বনি করলেন ২৬ বছর বয়স্ক মিস্টার ও'টুল।সেনাবাহিনী চট্টগ্রাম নিয়ন্ত্রণ করছে' , তিনি বলেন, ' নিয়ন্ত্রণ করছে বর্বর শক্তি ও সন্ত্রাসের দ্বারা।সৈন্যরা এগিয়ে আসছে।তারা নাগরিকদের গুলি করছে।আমরা বহু লাশ দেখেছি,মৃত্যুর পঁচা গন্ধ পেয়েছি।'
খাদিম বাংলাদেশ ত্যাগ করেছেন ১১ এপ্রিল।তার আগ পর্যন্ত ঢাকার বাইরে বাংলাদেশ ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটি হত্যাকান্ডের দায় তার ঘাড়ে বর্তায়,অপারেশন সার্চলাইটের রূপরেখা অনুসারেই।শনবার্গের প্রতিবেদনটি ৭ এপ্রিল লেখা।অর্থাৎ ২৮ মার্চ খাদিম চট্টগ্রামে পৌঁছানোর ঠিক পরের পরিস্থিতিই বলেছেন শনবার্গ।এই হলো বিদ্রোহ দমনের চিত্র,এই কাজের জন্যই গর্বিত খাদিম।এবং পুরো বইয়ের কোথাও এসবের পেছনে নিজের দায়টুকু স্বীকার করেননি খাদিম।
চট্টগ্রাম ছাড়া অন্যান্য অঞ্চল সম্পর্কেও একই রকম মন্তব্য খাদিমের।বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না গণহত্যা সম্পর্কে কী মনোভাব ধারণ করেন এই পাকিস্তানি জেনারেল।
চট্টগ্রামেরই আরো একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।এর বিবরণ খাদিমের বইতে আছে,আছে সাদুল্লা খানের বইতেও।তবে এই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে খাদিম একটি গুরুতর মিথ্যাচার করেছেন।ঘটনাটি সাবেক সাংসদ প্রয়াত ব্রিগেডিয়ার এম আর মজুমদারকে নিয়ে।চট্টগ্রামের বাঙালি সৈনিকদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে সংগঠিত করার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের।স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানি সৈনিক ও অফিসারদের সুনজরে ছিলেন না তিনি।অপারেশন সার্চলাইটের চূড়ান্ত পরিকল্পনাতে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের ব্যাপারে আলাদাভাবে একটি পয়েন্ট ছিল,খাদিম হোসেনের উপরেই বর্তায় তাকে সাথে নিয়ে আসার দায়িত্ব।এই ব্যাপারে খাদিম তার বইতে মোটামুটি মোলায়েমভাবে মজুমদারের সাথে তার সাক্ষাতের বর্ণনা দিয়েছেন,এর পর তাকে খুব যত্নের সাথে তুলে নিয়ে আসা হয়,যুদ্ধের বাকি ক'দিন পাকিস্তানে আরামেই ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মজুমদার।এটি একটি জলজ্যান্ত মিথ্যাচার।ব্রিগেডিয়ার মজুমদার নিজেই এ ব্যাপারে স্মৃতিচারণ করেছেন শাহরিয়ার কবির সম্পাদিত Tormenting 71 বইয়ে,
Tension continued for the next couple of days. On March 24, General Khadim Hossain Raja and General Mitha Khan came to the East Bengal Regimental Centre by two helicopters. They told me that the President would hold a meeting that evening. “All senior officers have been asked to join the meeting. So you’ll have to go.”
I said, “A tense situation is prevailing now in Chittagong. If I go, trouble may occur here. Particularly, civilians are very agitated.” As I was suspicious about the meeting at Dhaka, I asked Captain Amin (now a Major General), “Make a call to Colonel Osmani and enquire wheather or not I should go to Dhaka to attend the meeting but in vain.”
Tikka Khan said, “You must come because the President wants to talk to all senior officers. After the meeting, if necessary, we’ll send you back.” Unfortunately, I believed him. I thought what he told me could be true. So, I boarded the helicopter to Dhaka. Amin accompanied me.
এইভাবে মিথ্যে বলে নিয়ে যাওয়া হয় ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে,এর পর চালানো হয় নির্যাতন,সে বিবরণ আছে একই স্মৃতিচারণে।শিরোনামই বলে দেয় কেমন ছিল সেই অত্যাচারের চেহারা - " I was put in a gunny bag and kept in the scorching sun "
ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ৫ নভেম্বর,১৯৭৩ দেশে ফেরেন।এর আগ পর্যন্ত পাকিস্তানে যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক ছিলেন তিনি।
আরেকটি পরিস্কার মিথ্যাচারের নমুনা দেই।বইটিতে পাঞ্জাবী এবং বিহারিদের প্রতি বিরূপ মনোভাবের কথা বেশ ফলাও করে লিখেছেন খাদিম।তবে চট্টগ্রাম,ঢাকার মিরপুর,ঈশ্বরদী প্রভৃতি এলাকায় যে পরিকল্পিত ভাবে বিহারিদের নিয়ে আসা হচ্ছিল,গোপনে অস্ত্র মজুদ করা হচ্ছিল তাদের কাছে,সহিংসতার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল সেটা লেখেননি তিনি।যাই হোক,এটি আপাতত মুখ্য নয়।যে জিনিসটি চোখে লাগে তা হলো দু'টি গালির উল্লেখ।বাঙালিরা নাকি পাঞ্জাবী আর বিহারিদের শালা পাঞ্জাবী,শালা বিহারি এসব বলে গালি দিত।গালি দিতেন মুজিব নিজেও।এটি স্পষ্টত একটি মিথ্যাচার।বাঙালি-বিহারি বা বাঙালি-পাঞ্জাবী সম্পর্ক সুখকর ছিল না সত্য,কিন্তু এধরণের গালির কথা এখন পর্যন্ত কোন বই,প্রতিবেদন বা প্রত্যক্ষ্যদর্শীর বর্ণনায় পাওয়া যায়নি।বিচ্ছিন্ন দুই-একটি ঘটনা অস্বাভাবিক নয়,'শালা' এদেশে খুব অপ্রপচলিত শব্দও নয়,তবে সেটিকে ব্যবহার করে পুরো বাঙালি জাতির ঘাড়ে এরকম দায় চাপানোটা উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যাচার।
এরকম মিথ্যাচার আরো প্রচুর রয়েছে।বস্তুত পুরো বইটিই একটি আস্ত মিথ্যাচার।পঁচিশে মার্চ রাতে পিলখানায়,রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ক্যাজুয়ালিটি উভয়পক্ষ মিলে টেনেটুনে দশ।নিজের অপকর্মকে জায়েজ করার জন্য অখণ্ড পাকিস্তানের দোহাই দিয়েছেন খাদিম।এরপর মায়া কান্না কেঁদেছেন,বেয়াড়া বাঙালিরাই ঠেলে গুতিয়ে সামরিক হস্তক্ষেপের দিকে যেতে বাধ্য করেছে সেনাবাহিনীকে।মার্চের ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষিতে তার মনোভাব,
The most disturbing aspect of the overall situation was that the Bengali troops were seething with revolt,and widespread mutiny seemed to be in the offing.This would have provoked a civil war situation which we wanted to avoid at all cost.
এ পর্যন্ত যতটুকু দেখা গেল,তিনটি বিষয় পরিস্কার,
১) খাদিম হোসেন রাজা একজন ঠাণ্ডা মাথার হত্যাকারী,তার পরিকল্পনা এবং সক্রিয় তত্ত্বাবধানে বাঙালিদের হত্যা করা হয়েছে,শিশু হত্যা করা হয়েছে,চালানো হয়েছে ব্যাপক ধ্বংসলীলা।
২)পুরো বইটিতে একবারের জন্যও এসব অপকর্মের জন্য অনুতাপের কোন চিহ্ন দেখা যায়নি,বরং গর্বিত হতে দেখা গেছে।একবারই তাকে চেতে উঠতে দেখা যায়,তাকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার আদেশে।টিক্কা খানের উপর তিনি এই রাগ ঝাড়েন।এই ঘটনার বিবরণ দেবার সময়েও বাংলাদেশ যা করেছেন তার জন্য গর্বিত তিনি,বরং এমন স্মরণীয় সাফল্যের পর,দেশের জন্য এমন নিবেদিত ভাবে কাজ করার পর এমন প্রতিদানই তাকে বিমূঢ় করে দিয়েছে।
৩)সমস্ত হত্যাকাণ্ড,ধর্ষণ,গণহত্যা জায়েজ করার চেষ্টা করা হয়েছে পাকিস্তানের অখণ্ডতার দোহাই দিয়ে।
এবার বাঙালি,হিন্দু,আওয়ামীলীগ এবং শেখ মুজিবের প্রতি তার বিদ্বেষের দুই একটি ছোটখাট নমুনা দেখা যাক।প্রথম অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে খাদিম লিখেছেন,
Bengalis,in general,were dreaming of a Sonar Bangla,which was expected to be a 'heaven on earth' . At that time they lost all sense of rality for they did not realize that,on its own,their land had nothing much to offer other than hunger and poverty for the masses.
এটি একটি ছোট নমুনা,এমন অনেক আছে।বাঙালিরা দরিদ্র,এদেশে কোন সম্পদ নেই,পশ্চিম পাকিস্তান আর কী করবে।বৈষম্যের যে অভিযোগ তোলা হয় তা সঠিক নয়,কারণ এদেশ উন্নয়ন সম্ভব নয়।বাঙালিদের সামরিক ঐতিহ্য নেই,সেনাবাহিনীতে তাদের বেশি রাখলে অকল্যানই বেশি হবে।এমন অজস্র কথায় বাঙালিদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন খাদিম হোসেন রাজা।
বইটিতে দু'জন হিন্দু ব্যবসায়ীর বর্ণনা পাওয়া যায়।খাদিম লিখেছেন,এরা ধনী ব্যবসায়ী তবে এদের কাছে মাত্র কয়েক হাজার টাকা ছিল।অথচ এদের মাসিক আয় কয়েক লক্ষ টাকা।এত টাকা কোথায় যায়?আর কোথায় ! ভারতের ব্যাঙ্কে।রাজা সাহেব অবশ্য কোন প্রমাণ ট্রমাণের ধার ধারেননি।
Last Words শিরোনামে শেষ অধ্যায়ে মুজিব সম্পর্কে রাজা লিখেছেন,
One of Mujib's favourite targets was Bihari community,which was invariably under fire and maligned for grabbing jobs which,he claimed,rightfully belonged to the Bengalis.He quoted mountains of statistics that were false.Bengal,which in my opinion was a bottomless well of problems,was depicted as goose that laid the golden egg.
এমনি করে,একশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠার বইটির প্রতি অধ্যায়ে,কয়েক পৃষ্টা পরপরই বাঙালি বিদ্বেষ,হিন্দু বিদ্বেষ,নিজের অপকর্মকে সুমহান কীর্তি বলে চালিয়ে দেয়া বোলচাল।
এই নির্লজ্জ মিথ্যাচার নতুন কিছু নয়।পাকিস্তানের আরো অনেক সেনানায়ক এমন বই লিখেছেন,তার বেশিরভাগই এমন মিথ্যাচার।সেখানে কিছু কাদা ছোড়াছুড়ি থাকে,আর থাকে সেনাবাহিনীকে সাধুপুরুষ বানানোর চেষ্টা।সেই মিথ্যাচারের পরম্পরা বেশ ভালোভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন খাদিম হোসেন রাজা।ঠিক এই ব্যাপারটিই অসাধারণভাবে বলেছেন মুনতাসীর মামুন,
একজন পাকি জেনারেল অন্তিমে পাকি জেনারেলই।তার আনুগত্য প্রধানত পাঞ্জাব আর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতি,তার দেশের প্রতিও নয়।পৃথিবীতে এ রকম বাহিনী খুব বিরল,যাদের দেশের প্রতি কোন ভালবাসা নেই,কমিটমেন্ট নেই,তবে আছে নিজ দেশ দখলের তীব্র বাসনা।
তাহলে দাঁড়াল এই - এরকম একটি উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যাচারে পরিপূর্ণ,নিম্নমানের আবর্জনার ডিপো নিয়ে অহেতুক উৎফুল্ল হওয়ার কোন কারণ নেই।
তবে চিন্তার কারণ থেকেই যায়।কারণ এই বই নিয়ে প্রথম আলো গোষ্ঠীর মাত্রাতিরিক্ত মাতামাতি।এতক্ষন যতটুকু দেখা গেল তাতে করে যেকোন আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন বাঙালির অন্তর পূর্ণ হয়ে যাবে এই বই এবং তার লেখকের প্রতি ঘৃণায়।তাহলে কেন এই মাতামাতি?নিয়াজি হত্যা করেছে সেই কথাটা এত ফলাও করে প্রচার করা হলো বাংলাদেশের মিডিয়াতে অথচ বাঙালি জাতি সম্পর্কে,বাংলাদেশ সম্পর্কে এমন আপত্তিকর মন্তব্যগুলো কেন প্রচার করে না প্রথম আলো?
উত্তর খুব সহজ।বইটির যা প্রয়োজন ছিল তা হলো প্রচারণা।সেই উদ্দেশ্যেই হাড়ির খবর চেপে গিয়ে বাছাই কিছু অংশ প্রচার করা হয়েছে।এতে করে একেবারে নিকৃষ্ট মানের এই বইটি নিয়ে আগ্রহ বেড়েছে মানুষের,বিক্রি বেড়েছে।বাংলাদেশে এই কাজটি করেছে প্রথম আলো।হয়তো ক'দিন পর এর অনুবাদও প্রকাশ করবে প্রথমা প্রকাশনী।অনুমান করা যেতেই পারে - বিক্রিবাট্টাও মন্দ হবে না।এর আগে খাদিম হোসেন রাজার এই যে সত্যবাদী ইমেজ তৈরি করলো প্রথম আলো,এর মাধ্যমে বাঁধা হবে রিকন্সিলিয়েশনের সেতু।।কলা বেচা তো হবেই,রথ দেখাটাও ফাও।খুবই দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিকল্পনা।
একাত্তরের গণহত্যার কালপ্রিট যেমন নিয়াজি,টিক্কা খান তেমনি খাদিম হোসেন রাজাও।নিয়াজির পাপ খাদিমের পাপকে কিছু মাত্র হালাল করে না।তাই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এইসব মিথ্যাবাদীদের।এখন কথা হলো,তাহলে কি বইটি আমরা পড়বো না?অবশ্যই পড়বো,মিথ্যাচারের পরিচয় জানার জন্য পড়বো।তবে পয়সা খরচ করে কিনে নয়,এসব আবর্জনার পেছনে অর্থ ব্যয় যেমন অযৌক্তিক,তেমনি এই মিথ্যাচারে পূর্ণ বই কিনে কয়েকটি পাকি বাস্টার্ডকে বড়লোক বানানোরও কোন মানে নেই।ঠিক এই স্ট্র্যাটেজিকে সামনে রেখেই আমারব্লগডটকম বইটির একটি পিডিএফ ভার্শন তৈরি করেছে।বইটি ডাউনলোড করতে ক্লিক করুন উপরে বইটির প্রচ্ছদ প্রিভিউতে অথবা এখানে ।এছাড়া অনলাইনে পড়তে চাইলে ক্লিক করুন এখানে ,এই লিঙ্কেও ডাউনলোড সুবিধা পাবেন।পড়ুন,জানুন - কীভাবে এই বিশ্বাসঘাতকেরা মিথ্যাচার করে,বিকৃত করে ইতিহাস।যেখানেই অপপ্রচার,যেখানেই মিথ্যাচার,যেখানেই আমাদের গৌরবের ইতিহাসের বিরুদ্ধাচরণ - সেখানেই প্রতিবাদ,সেখানেই প্রতিরোধ।
এইসব শুয়োরের বাচ্চার ব্যবসার মুখে ছ্যাঁত ছ্যাঁত করে থুতু মারুন,থুতু মারুন তাদের এদেশী এজেন্ট-মেন্টরদের মুখেও।
তথ্যসূত্র :
১) Witness To Surrender - Siddiq Salik
২) ডেটলাইন বাংলাদেশ নাইনটিন সেভেনটি ওয়ান - সিডনি শনবার্গ ( মফিদুল হক অনুদিত )
৩) পাকিস্তানি জেনারেলদের মন বাঙালি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ - মুনতাসীর মামুন
৪) বাংলাদেশের জন্ম - রাও ফরমান আলি ( মুনতাসীর মামুন অনুদিত )
৫) The Way It Was - Brig (Retd) Z A Khan
৬) Tormenting 71 - Edited by Shahriar Kabir
________________________________________________
http://www.amarblog.com/pritomdas/posts/151900
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৮:৫৫582853
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৮:৫৫582853- মুক্তিযুদ্ধের কয়েকটি কার্টুন
লিখেছেনঃ প্রীতম (তারিখঃ সোমবার, ০৬/০৮/২০১২ - ০৪:৫২)
__________________________________________________
যেকোন ধরণের অসংগতি বা অন্যায়ের প্রতিবাদ হিসেবে কার্টুন-ক্যারিকেচার অত্যন্ত কার্যকরী একটি মাধ্যম।ইতিহাসের স্মরণীয় বিপর্যয়গুলোর সময়েও কার্টুন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।কার্টুন-ক্যারিকেচার মানুষের চিন্তাকে স্পর্শ করে যেতে পারে তীক্ষ্ণ ভাবে,নাড়া দিয়ে যেতে পারে ভেতরের বোধকে।বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের কার্টুনিস্টরা বসে ছিলেন না।বাংলাদেশের শিল্পীরা তো বটেই,ভারত,যুক্তরাষ্ট্র সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা কার্টুন এঁকেছেন,বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন,ইতিহাসের অন্যতম নৃশংস গণহত্যার নিন্দা জানিয়েছেন।এইসব শিল্পীর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।
কয়েকদিন আগে বইপত্র ঘাটতে গিয়ে কিছু এমন কিছু কার্টুন বেরিয়ে গেল।এগুলোর বেশিরভাগই ভারতীয় শিল্পীদের আঁকা,কয়েকটি এঁকেছেন মার্কিন শিল্পীরা।আন্তর্জালে খুঁজে খুঁজে এরকম আরো কিছু কার্টুন মিলেছে।কয়েকটি পাওয়া গেছে সেই সময়ের পত্র-পত্রিকায়।কার্টুনগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কারণে।প্রথমত,এগুলো বাংলাদেশের ইতিহাসের অনন্য দলিল।দ্বিতীয়ত,এই কার্টুনগুলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সুহৃদদের সমর্থনের স্মৃতিচিহ্ন।তৃতীয়ত,কার্টুনগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের একেবারে মূলধারার বাইরে কয়েকটি বিষয় উঠে এসেছে।যেমন,পাকিস্তানের মিডিয়ায় মুক্তিযুদ্ধ এবং পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রোপাগান্ডা,যুক্তরাষ্ট্র এবং জাতিসংঘের ভূমিকা,ইয়াহিয়া খান এবং জুলফিকার আলি ভুট্টোর সম্পর্ক ইত্যাদি।
সবগুলো কার্টুনের শিল্পীর নাম জানা সম্ভব হয়নি।অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশের মাধ্যম এবং তারিখও অজানা থেকে গেছে।এসব সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েই এই পোস্ট।ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান হিসেবে এধরণের ডকুমেন্ট ছড়িয়ে দেয়া জরুরি।
যেকোন শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেই শিল্পীর সম্মানটুকু যথাযথ ভাবে দেয়া গুরুত্বপূর্ণ।এখানে যেসব কার্টুনের শিল্পীর নাম এবং অন্যান্য তথ্য জানা সম্ভব হয়নি সেগুলোর ব্যাপারে আমারব্লগের কোন পাঠকের কাছে কোন তথ্য থেকে থাকলে অনুগ্রহ করে জানিয়ে যাবেন,আপনার প্রতি আমার অগ্রিম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখলাম।আপাতত এইসব নাম জানা এবং না জানা শিল্পীর প্রতি আমার নতজানু শ্রদ্ধা।
নিচের কার্টুনটি ৫ জুলাই,১৯৭১ নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, South Asia : The Approach of Tragedy শিরোনামের একটি প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্তি হিসেবে ।এঁকেছিলেন শিল্পী ব্র্যাড হল্যান্ড।
গণহত্যার একটি খণ্ডচিত্র।এই কার্টুনটি প্রকাশিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের দি ওয়াশিংটন ডেইলি নিউজ পত্রিকায়,১৫ জুন ১৯৭১ তারিখে। এর সাথের সংবাদটির শিরোনাম ছিল - Slaughter In East Pakistan । স্বাক্ষর থেকে শিল্পীর নাম বোঝা সম্ভব হয়নি।কেউ যদি উদ্ধার করতে পারেন জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো।
বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের মধ্যে সমঝোতার ব্যপারে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ এবং একচোখা নীতি নিয়ে এই কার্টুনটি প্রকাশিত হয়েছিল ভারতের শঙ্কর'স উইকলি পত্রিকায়।কার্টুনে হাত এবং মুখ বাঁধা অবস্থায় বাঙালি জাতির নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখানো হয়েছে,বিপরীতে আগ্রাসী একটি ভঙ্গীতে দেখানো হয়েছে ইয়াহিয়া খানকে।
শিল্পী এবং প্রকাশকাল : অজ্ঞাত
নিচের কার্টুনে ভুট্টোকে ইয়াহিয়ার পা-চাটা কুকুর হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।সম্ভবত মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত কোন একটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল এই কার্টুনটি।
শিল্পী এবং প্রকাশকাল : অজ্ঞাত
এই কার্টুনেও ভুট্টোকে ইয়াহিয়ার নাচুনে পুতুল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।বামে সামরিক পোষাকে ডুগডুগি হাতে ইয়াহিয়া,ভিক্ষার থালা হাতে বানরটি ভুট্টো।ডানে (সম্ভবত) যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন।এই কার্টুনটি প্রকাশিত হয়েছিল ভারতের হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায়।
শিল্পী ও প্রকাশকাল : অজ্ঞাত
মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবার পরপরই ভারতীয় শিল্পী আর কে লক্ষণ নিচের কার্টুনটি আঁকেন।বিষয়বস্তু - বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে ইন্ধন দিতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ধ্বস্তদশা।প্রকাশের সঠিক তারিখ এবং কোন মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল জানা সম্ভব হয়নি।
গণমাধ্যমে পাকিস্তানি প্রোপাগান্ডা।শিল্পীর নাম নয়ান।প্রকাশকাল অজ্ঞাত।
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিভিন্ন সময়ে ভারতীয় শিল্পীদের আঁকা আরো কয়েকটি কার্টুন -
" He looks hungry enough to devour you both! " শিরোনামের কার্টুনটি এঁকেছিলেন স্টুয়ার্ট ম্যাকক্রে -
এনাটমি অফ আ ক্রাইম শিরোনামের এই কার্টুনটি ছাপা হয় সেইন্ট লুই-পোস্ট ডিসপ্যাচ পত্রিকায়,২ অগাস্ট,১৯৭১ ।বিষয়বস্তু - পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃক পরিচালিত গণহত্যায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদদ ও সামরিক সহযোগিতা।স্বাক্ষর থেকে শিল্পীর নাম বোঝা সম্ভব হয়নি।
ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এই কার্টুনগুলো যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি এগুলোর শিল্পমূল্যও কম নয়।একই সঙ্গে একটি জাতির জাগরণের সাথে,একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মের সাথে সরাসরি যুক্ত এই কার্টুনগুলোর প্রত্যেকটি বাঙালির কাছে আবেগের সম্পদ হিসেবেই বিবেচিত হবে।
পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রান্তে যেসব মহানুভব ব্যক্তি বাংলাদেশ ও বাঙালির জন্য সময়,শ্রম,মেধা এবং অশ্রু ব্যয় করেছেন তাদের প্রত্যেকের জন্য অন্তহীন শ্রদ্ধা।
সূত্র :
১) আমরা স্বাধীন হলাম - কাজী শামসুজ্জামান
২) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কার্টুন - আহম্মেদ কিশোর,টুনস মাগ বাংলা
৩) Stewart McCrae cartoon collection
বিশেষ কৃতজ্ঞতা : এম এম আর জালাল
_______________________________________
http://www.amarblog.com/pritomdas/posts/151197
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:০৩582854
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:০৩582854- ৭১’-এর সেই জনযুদ্ধ যেমনটা দেখেছি
সাজ্জাদ আলী | ১৫ december ২০১২ ৬:৩৯ অপরাহ্ন
________________________________________
১৯৭১ এর মে মাসের প্রথম সপ্তাহের কোন একটা দিন, দুপুরের দিকে, আমার দাদীর বাড়ীতে অন্যদের নিয়ে খেলায় মত্ত আমি। তৃতীয় শ্রেনীর ছাত্র, তবে স্কুলে যাওয়ার বালাই নেই, কারন যুদ্ধ লেগেছে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে, স্কুলের স্যাররা সবাই যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, দু একজন নাকি চলেও গেছে। সারাদিনই শুধু খেলা আর খেলা। হঠাৎ বড়দের মধ্যে ভিশন হৈ চৈ, আমার চাচারা ও তাদের বন্ধুরা যাঁরা ভেতরের বাড়ীতে জটলা করছিল, সবাই দৌড়াচ্ছে বাইরের বাড়ীর কাঁচারী ঘরের দিকে। সেখানে আমার আব্বা অনেক লোকজন নিয়ে প্রতিদিনের মতই সেদিনও সলা-পরামর্শ করছিলেন, বোধকরি দেশের যুদ্ধ নিয়েই। আমাদের বাড়ী সংলগ্ন খেলার মাঠ থেকে আমিও দৌড়ালাম কাঁচারী ঘরের দিকে। যেতে যেতে দেখলাম আশেপাশের বাড়ীগুলো থেকেও পরিচিতরা সবাই আমাদের বাড়ীর দিকেই ছুটে আসছে। গিয়ে দেখলাম একজন লোক একটা ঘোড়ার পিঠে বসা (সেই সময়ে আমাদের এলাকায় দ্রুততার সাথে সংবাদ প্রেরণের একমাত্র অবলম্বন ছিল ঘোড়সওয়ার হওয়া), উচ্চস্বরে আব্বাকে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে এতই উত্তেজিত যে কেউই তার কথার কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। এক পর্যায়ে তার পরনের লুঙ্গির গিট খুলে একটা চিরকুট বের করে আব্বার হাতে দিল। মুহুর্তেই তিনি কাগজের ভাজ খুলে চিঠিটি পড়ে ফেললেন। তাঁর মুখের ফ্যাকাসে অবস্থা দেখে ছোট্র আমারও বুঝতে বাকী রইল না যে ঐ চিরকুটে কোন একটা মহা বিপদের বার্তা আছে। আব্বা সম্প্রতি যুদ্ধ প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ‘বাংলা বাহিনী’ নামে একটা দল গঠন করেছেন, ২৫/৩০ জনের এই দলটি গত কয়েক মাস হল মোটামুটিভাবে আমাদের বাড়ীতেই থাকে, খায়। এদের কাজ এলাকার যুবকদের সংগঠিত করা, মিটিং মিছিলের আয়োজন করা, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কেউ কোন শব্দ উচ্চারণ করলে তাকে শয়েস্তা করা ইত্যাদি। তারা আব্বার অত্যন্ত অনুগত, বিনা বাক্য ব্যায়ে যে কোন নির্দেশ বাস্থবায়নে জীবন দিতেও প্রস্তুত। বড়দের বলাবলি করতে শুনেছি ওরা সবাই খুব তাড়াতাড়ি যুদ্ধে চলে যাবে এবং দেশ স্বাধীন করে তবেই ফিরবে। আব্বা হুঙ্কার দিয়ে এই বাংলা বাহিনীকে হুকুম দিলেন,- ‘তোরা এক্ষুনি বেরিয়ে যা, আশেপাশের সব গ্রামে খবর দে, সবাই যেন ঢাল, সড়কি, লাঠি, বল্লম যার যা কিছু অস্ত্র আছে সব নিয়ে এক্ষুনি চলে আসে’। ‘মোক্তার সাহেব’ (আমাদের এলাকার নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য) খবর পাঠিয়েছেন, ভাটিয়াপাড়া ওয়ারলেস স্টেশনে পাকিস্তানি মিলিটারীর ৪০/৫০ জনের একটি দল আজ সকালেই এসে ঘাঁটি গেড়েছে। মোক্তার সাহেবের নির্দেশ, আশপাশের পঞ্চাশ গ্রাম থেকে হাজার হাজার লোক নিয়ে মিলিটারীদের ঘিরে ফেলতে হবে এবং একজন একজন করে পিশে মারতে হবে।
তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহাকুমার কাশিয়ানি থানার এক প্রত্যন্ত গ্রামে আমার দাদির বাড়ী। বংশানুক্রমে আব্বা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং থানা আওয়ামী লীগের সম্পাদক, অঞ্চলের মানুষ তাঁকে ভালবাসে, সমীহ করে, শ্রদ্ধা করে, দুষ্টু লোকেরা ভয়ও করে। আক্তার উদ্দিন মিয়া, পেশায় গোপালগঞ্জ মহাকুমা ফৌজদারী আদালতের মোক্তার, কাশিয়ানী থানা আওয়ামী লিগের সভাপতি। এলাকার সাধারন মানুষ সন্মান করে তাঁকে ‘মোক্তার সাহেব’ বলে ডাকে। ১৯৭০ এর সাধারন নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যাবধানে মুসলিম লিগের ডাকসাইটে প্রার্থির জামানত বাজেয়াপ্ত করে দিয়ে প্রাদেশিক সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। আক্তার কাকাকে আমাদের পরিবারের একজনই মনে হত আমার কাছে, আমার আব্বার থেকে বয়সে বেশ বড়, তাঁর নাম ধরে ‘টিপু মিয়া’ বলে ডাকেন, তবে দীর্ঘ দিনের নিবীড় বন্ধুত্ব ও বোঝাপড়া দুজনার মধ্যে। ‘দল চালাবার টাকা’ এবং স্থানীয় আওয়ামী লিগের যে কোন নীতিগত সিদ্ধান্তের জন্য মোক্তার সাহেব আব্বার উপরেই নির্ভরশীল ছিলেন।
দু তিন ঘন্টার মধ্যেই আমাদের বাড়ীর সামনের মাঠ হাজারো মানুষে পরিপুর্ন। সবাই উত্তেজিত, প্রত্যেকের হাতেই দেশী অস্ত্র। কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ, কেউই বাদ যায় না, লাঠী/সড়কীর শির্শে স্বাধীন বাংলার পতাকা। শ্লোগানে শ্লোগানে মুখর সারা গ্রামের আকাশ বাতাস। মুক্তিকামি হাজারো মানুষের গগন বিদারী চিৎকার,- ‘বীর বাঙালী অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর’, ‘পিন্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা’, ‘তোমার নেতা আমার নেতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব’, ‘ইয়াহিয়ার চামড়া, তুলে নেব আমরা’, ‘শেখ মুজিবের কিছু হলে, জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে’ ইত্যাদি। এ যেন হাজারো মানুষের সম্মিলিত শক্তির মহাবিষ্ফোরণ, কি তার তেজ, কি বিক্রম ! কে রুখবে এদের স্বাধীনতা ? নিরীহ, নিরন্ন মানুষদের এমন প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, পৃথিবী আর দেখেছে বলে আমার জানা নেই, এ অহংকার কেবল বাঙালীরই সাজে।
আমাদের ভেতরের বাড়ীতে দৃশ্যটা অন্যরকম। আমার দাদী বসে আছেন উঠনের মাঝখানে তাঁর সেই চেয়ারখানায়, মাঝে মধ্যেই হাকডাক করে সবাইকে তটস্থ রাখছেন, আমার আম্মা আর মেঝচাচী রান্নার তদারকীতে ব্যস্ত। অন্তত দশটা চুলায়, বড় বড় ড্যাগে (বিশাল সাইজের রান্নার পাত্র) ভাত ও খেসাড়ীর ডাল রান্না হচ্ছে। কোন একটা ড্যাগের রান্না শেষ হওয়ার সাথে সাথেই বাংলা বাহিনীর লোকেরা সেটা বাইরের বাড়ীর উঠোনে নিয়ে লম্বা লাইনে বসা ক্ষুধার্থ মানুষদের কলাপাতার থালায় খাবার বেড়ে দিচ্ছে। মাঝেমধ্যেই আমার দাদী তদারকী করতে বাইরের উঠোনে আসছেন আর বলছেন সবাইকে ‘পেট ভরে খাও, যুদ্ধে যাচ্ছ তোমরা, আবার কখন খেতে পাবে সেতো আল্লাহই জানে’!
বাঙলা বাহিনীর ছেলেরা আমাদের মাঠে ইতিমধ্যেই একটা কাঠের চৌকির উপরে আরো একটা চৌকি দিয়ে ষ্টেজ বানিয়ে ফেলেছে। বেলা দুইটার দিকে আব্বা সেই ষ্টেজে উঠলেন, হাতে নিলেন তাঁর প্রিয় হ্যান্ড মাইকটি। হাজার হাজার মানুষ, মাঠে তিলধরাবার জায়গাও নেই, কেউ কোন শব্দ করছে না, সবাই অপেক্ষায় নির্দেশের! উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি হুঙ্কার দিয়ে বললেন,- আজ রাতেই ভাটিয়াপাড়া মিলিটারী ঘাটি ঘেরাও করে ৫০/১০০জন পাঞ্জাবী যাই থাকুক সবাইকে জীবিত বা মৃত ধরে এনে এলাকা শত্রুমুক্ত করতে হবে। ‘জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে হাজারো জনতা এ প্রস্তাবে সমর্থন জানালো, এ যেন তাদের সকলেরই মনের চাওয়া! নিজেদের শক্তি সামর্থের একটা ছোটখাট বর্ণনাও দিলেন আব্বা। প্রধান শক্তি হল দেশী অস্ত্রে সজ্জিত কয়েক হাজার সসস্ত্র মানুষ এবং তাঁদের তাদের অদম্য সাহস আর মাত্র দুটো বন্দুক। আমাদের বন্দুকটা দোনলা, উপস্থিত সাধারন মানুষদের ধারনা অনেকটা এরকম যে, ঐ দোনলা বন্দুকটা পৃথিবীর সর্ব শ্রেষ্ট মারণাস্ত্র, ওটা যাঁদের সাথে আছে, জয় তাদের সুনিশ্চিত ! যাই হোক, শক্তি বর্ণনার শেষ পর্যায়ে আব্বা চাইলেন জনতাকে সেই শক্তির প্রদর্শনীর ব্যাবস্থা করে চাঙা করতে। তিনি স্টেজে ডাকলেন তাঁর ইউনিয়ন পরিষদের দফাদারকে, সে আব্বার নিত্য সহচর ও বিস্বস্ত, ছায়ার মত তাঁকে অনুসরণ করে সব সময়, ২৬শে মার্চ থেকে, অর্থাৎ যুদ্ধ শুরুর পরপরই এই দফাদার ভদ্রলোক নিজে থেকেই আব্বার দেহরক্ষিতে পরিনত হয়েছে। সব সময়ই সে বন্দুকটা নিয়ে তাঁর সাথে। আব্বার ইসারায় দফাদার ভাই স্টেজের উপর উঠে বিশেষ কৌশলে দোনলা বন্দুকের দুটো গুলি পরপর এমনভাবে ছুড়লো যেন উপস্থিত জনতার মনে হল ’ব্রাস ফায়ার করা যায় এ বন্দুক দিয়ে’। গুলির শব্দের পরে জনতার যে উল্লাস, তেজ ও বিক্রম সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলাম, সেকি লিখে প্রকাশ করা যায় ?
পরিকল্পনামত যাত্রা শুরু করলো ৩/৪ হাজার জনতার এক বিশাল মুক্তিযোদ্ধার দল, গন্তব্য ভাটিয়াপাড়া ওয়ারলেস স্টেশন মিলিটারী ক্যাম্প। রাতের কোন একটা সুবিধাজনক সময়ে বিশাল এ যোদ্ধার দল একযোগে ঝাপিয়ে পড়বে হানাদারদের উপর, ওরা কিছু বুঝে উঠার আগেই সব শেষ করে দেবে।। শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে জনতা এগিয়ে চলছে ফসলের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে। আমিও চলেছি সাথে। কিছুদুর যেতেই বদর ভাই (আমার ফুফাত ভাই) পেছন থেকে আমাকে ধরে ফেললো, বললো তোকে মামী ডাকে। আমি দৌড় দেবার চেষ্টা করতেই সে আমাকে চ্যাংদলা করে ঘাড়ে তুলে সোজা বাড়ীতে এনে আম্মার সামনে হাজির করলো। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, দেখি সেখানে আমার দাদী আছেন ! দাদীকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না আমার, বায়না একটাই, ‘সবাই যুদ্ধে যাচ্ছে, আমিও যাব’। আমার ইংলিস প্যান্টের পকেট থেকে কাঠের ছোট্র পিস্তলটা বারে বারে বের করছি, দাদীকে দেখাচ্ছি, আর আমার শক্তির উৎসটা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করছি (আমাদের পশ্চিম পাড়ার কাঠমিস্ত্রী খগেন দাদু পিস্তলটা সম্প্রতি আমাকে বানিয়ে দিয়েছেন)। আমার আব্দার না করার ক্ষমতা, আমার ক্ষমতাশালিণী দাদীর কোনদিনই ছিলনা, আর আমার মায়েরও জানা ছিল যে দাদীর ইচ্ছাই চুড়ান্ত। দাদী তাঁর গোমস্তাকে ডেকে বললেন, একে নিয়ে যা যুদ্ধ করাতে, ঘাড়ে করে রাখবি সব সময়, মাটিতে ছাড়বি না, আধা মাইল দুরে থাকবি এবং সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরিয়ে আনবি। দাদীর প্রশ্রয়ে, মায়ের রক্তচক্ষু অতিক্রম করে এই শিশুযোদ্ধা তার কাঠের পিস্তল নিয়ে ঈমান দাদার ঘাড়ে চড়ে জনযোদ্ধাদের মিছিলে সামিল হল।
আমাদের গ্রাম থেকে ভাটিয়াপাড়া ৭/৮ কিলোমিটার দুর। শুকনা মৌসুমে হাটা আর বর্ষায় নৌকা ছাড়া অন্য কোন যাতায়াত ব্যাবস্থা নেই। হাজারো মানুষের কাফেলা এগিয়ে চলেছে দৃপ্ত পদক্ষেপে, এদের কোন ধারনাই নেই শত্রুর সম্পর্কে বা তাদের মারনাস্ত্রের মানুষ মারার সামর্থ সম্পর্কে। বিশাল এই জনযোদ্ধার কাফেলা একটির পর একটি গ্রাম পার হচ্ছে, আসপাশের গ্রামগুলো থেকে আরো শত শত মানুষ সসস্ত্র অবস্থায় যোগ দিচ্ছে এই দলে, কাফেলা বড় হচ্ছে প্রতি মুহুর্তেই, এতক্ষনে বোধকরি ৫/৭ হাজার ছাড়িয়ে যাবে। প্রতিটি গ্রামেই কিছুক্ষনের জন্য এ গণমিছিল থামছে, হ্যান্ড মাইকে আব্বা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা/অনুরোধ রাখছেন, কখনও বা সেই গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁদের একাত্বতা প্রকাশ করে বক্তব্য রাখছেন, আবার এগিয়ে চলছে এই জনযোদ্ধার দল।
গ্রামগুলো যখন পেরুচ্ছে এই বিশাল মিছিলটি, তখন আশপাশের বাড়ীগুলো থেকে মহিলারা মুড়ি, চিড়া, গুড়, পানি, যাঁর বাড়ীতে যা কিছু শুকনো খাবার আছে সব জড় করে পথের পাশে দাড়িয়ে থাকছে, যদি কেউ ক্ষুদার্থ থাকে? সেদিনের একটি ছোট্র ঘটনা আমার শিশু মনকে স্পর্শ করেছিল যা আজো আমি স্পষ্ট মনে করতে পারি। যোদ্ধাদের এই বিশাল কাফেলা ‘ঘোনাপাড়া’ নামক গ্রামের বাজারে কিছুক্ষনের জন্য থামলো। বৃত্তাকারে প্রায় এক মাইল, শুধু মানুষ আর মানুষ, ঈমান দাদার ঘাড়ে আমি। অসতিপর এক বৃদ্ধা ঐ ভিড়ের মধ্যে লাঠি ভর দিয়ে আমার আব্বাকে খুজছে, তাঁর কাছে যেতে চাইছে। ‘বাঙলা বাহিনীর’ ছেলেরা বৃদ্ধাকে পথ করে দিল, তিনি আমার আব্বাকে তাঁর হাতের লাঠিখানা দিয়ে বললেন, ‘ বাবা আমিতো তোমার সাথে যেতে পারবো না, তুমি আমার লাঠিখানা নাও, অন্তত একজন খানকে এই লাঠি দিয়ে মারা চাই।’ অত্যন্ত আবেগ ও শ্রদ্ধার সাথে আব্বা সেই লাঠিখানা নিলেন এবং তাঁর কৌসুলি অবস্থান থেকে বৃদ্ধাকে ঐ কথাগুলো আবারো বলতে অনুরোধ করে মাইকটি তাঁর মুখের কাছে এগিয়ে দিলেন। কাঁপা কাঁপা কন্ঠে তাঁর সে নির্দেশ ‘আমার লাঠি দিয়ে পিটিয়ে খান সেনাদের খতম করবা’, যেন বারুদের মত বিস্ফোরিত হল জনতার মধ্যে। ‘বীর বাংগালী অস্ত্র ধর, খান সেনাদের থতম কর’ ধ্বনিতুলে আবার এগিয়ে চললো কাফেলা।
মাঝে আর কোন বাড়ীঘর নেই, আনুমানিক দুই কিলোমিটার লম্বা একটা বিল পেরুলেই ভাটিয়াপাড়া মিলিটারী ক্যাম্প, । সন্ধ্যা প্রায় ৬টা, জনযোদ্ধাদের এই কাফেলা এগুচ্ছে, শুধু ঐ বিলটাই পেরুতে হবে। হঠাৎ গুলির শব্দ, প্রচন্ড শব্দ, বিরামহীন একটানা, শব্দের উৎপত্তিস্থল বোঝাই যাচ্ছে ভাটিয়াপাড়া। পরিস্থিতি অনুধাবনে জনযোদ্ধাদের মিছিল থমকে দাড়ালো। কিছুক্ষনের মধ্যে ঐ দুর থেকেই আমরা দেখতে পেলাম ধোয়ার কুন্ডলী আকাশে, মাঝেমধ্যে আগুনের শিখা, গুলির শব্দ আরো বাড়ছে, কিছুক্ষণ পরপর ভারী গোলার শব্দে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে। ২৫/৩০ মিনিটের মধ্যেই দেখতে পেলাম শত শত নারী, পুরুষ, শিশু দৌড়ে বিল পার হয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। নেতৃবৃন্দের নির্দেশে হাজার হাজার মানুষের কাফেলা বিলের মধ্যে বসে পড়লো। জানা গেল, খান সেনাদের ৫/৭জনের একটি দল বিকেলে টহলে বের হয়েছিল ভাটিয়াপাড়া বাজারে। গ্রামের যুবক ছেলেরা দল বেধে ঝাপিয়ে পড়ে ঐ টহল দলের উপরে, সড়কি ছুড়ে একজন খান সেনার গলা ফুটো করে দেয়। এরপর থেকেই সেনারা দল বেধে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিতে ঝাঝরা করতে থাকে, যাকে সামনে পায় তাকেই। পুরো বাজারে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, গ্রামের মধ্যে ঢুকে নির্বিচারে চালাচ্ছে গুলি। প্রত্যক্ষদর্শিদের বর্ণনায়, শত শত লাশ পড়ে আছে বাজারে ও গ্রামের পথে পথে।
সন্ধ্যা লেগেছে, তবে তখনও কিছু আলো আছে, কাছাকাছি সবই দেখা যায়। খবর এলো ‘মোক্তার সাহেব’ (এ.এল.এ সাহেব) আসছেন। সবার মধ্যেই যেন নতুন প্রানের সঞ্চার হল। মোক্তার সাহেবের সাথে আরো দুজন, তাঁরা বয়সে তরুন, দেখতে শহুরে, পরে জেনেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা তাঁরা (তাঁদের নাম আজ আর মনে নেই)। মোক্তার সাহেব বিলের মধ্যে এসেই আব্বাকে কাছে ডাকলেন, দুজনে কি যেন সলা পরামর্শ করলেন (!), ‘বাংলা বাহিনীর’ ছেলেরা জনতাকে তাঁদের কাছে ঘেসতে দিচ্ছে না। কিছুক্ষন পরে সেই দুই ছাত্রনেতাসহ চারজনে মিলে কথাবার্তা বলে মোক্তার সাহেব মাইক হাতে নিলেন। সবাইকে সেই রাতেরমত বাড়ী ফিরতে অনুরোধ করলেন তিনি। হাজারো জনতা সমস্বরে নেতার এ নির্দেশ অমান্য করে বসলো, তাঁরা সেই রাতেই খান সেনাদের ক্যাম্প আক্রমন করবে,- এই তাদের সংকল্প! নেতা অসহায়ের মত মাইক হাতে দাড়িয়ে। ছাত্র নেতাদের একজন মাইক হাতে নিলেন, সুবক্তা তিনি, সেই রাতে আক্রমন করলে হানাদারদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কতটা এবং পরিস্থিতি কেমন ভয়ংঙ্কর হতে পারে তা বুঝালেন সবাইকে, একে একে বর্ণনা করলেন পাক সেনাদের ব্যবহৃত মারনাস্ত্রগুলোর কর্মক্ষমতা। আমরা হাজার হাজার মানুষ সেদিনই তাঁর মুখে প্রথম শুনলাম টমিগান, ষ্টেনগান, সাব-মেশিন গান, চাইনিজ অটোমেটিক রাইফেল, এ.এল.আর, মেশিন গান, রকেট লান্সার, গ্রেনেড, ডিনামাইট ইত্যাদি সব মারনাস্ত্রের নাম এবং আরো জানলাম এ অস্ত্রগুলোর মানুষ মারার ক্ষমতা সম্পর্কে। উপস্থিত হাজারো জনযোদ্ধার ধারনা ছিল খান সেনা মানেই হাতে ৩০৩ রাইফেল, এদের কাবু করা কঠিন হবে না। কিন্তু ঐ ছাত্র নেতার বর্ণনার পরে জনতা যেন বুঝতে পারলো যে এই হাজার হাজার যোদ্ধাকে পাখির মত মেরে ফেলতে হানাদারদের ১০ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না এবং তারা তা করতে দ্বিধাও করবে না।
জনযোদ্ধারা একটু শান্ত হতেই মোক্তার সাহেব আবার মাইক নিলেন, সবাইকে অনুরোধ করলেন সে রাতের মত বাড়ী ফিরতে। এরপর তিনি বললেন একেবারে নতুন সব কথা! আশার কথা! বললেন, ‘কিছুক্ষনের মধ্যেই আমি ইন্ডিয়া রওনা হচ্ছি, আপনাদের জন্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ আনতে। দেশের মধ্যেই আপনারা অস্ত্র চালনার ট্রেনিং করবেন, প্রয়োজনে আপনাদের ইন্ডিয়া পাঠাবো ট্রেনিং নিতে। এরপর শুরু করবেন গেরিলাযুদ্ধ। গেরিলাযুদ্ধ! সেটা আবার কি? জনতার অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা ? গেরিলাযুদ্ধের সাদামাটা একটা ব্যাখ্যা দিলেন মোক্তার সাহেব, বললেন, ‘হানাদারদের চলার পথে পথে ওৎ পেতে থেকে, তাদের খতম করে, দ্রুত ঐ স্থান ত্যাগ,- এই হল গেরিলাযুদ্ধ।’
‘গেরিলাযুদ্ধ’, ‘স্টেনগান’, ‘গ্রেনেড’, ‘ডিনামাইট’,- কথাগুলো সেই প্রথম শোনা। এই শব্দগুলো যেন কোন এক যাদুর ছোয়ায় উপস্থিত হাজারো মানুষের মনে এক নতুন আশার সঞ্চার করলো। মুহুর্তেই যেন সবাই বুঝে ফেললো এভাবে হবে না, যুদ্ধের কৌশল বদলাতে হবে। কিছুটা অপেক্ষা, অস্ত্রহাতে ট্রেনিং, তারপরেই মরণ আঘাত। আপাততুষ্ট জনতা ততক্ষনে বাড়ী ফিরতে শুরু করেছে। মোক্তার সাহেব আমার আব্বাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষন কাঁদলেন, তারপর বললেন, ‘টিপু মিয়া, আমি যাই, যদি বেঁচে থাকি আবার দেখা হবে। হাজার হাজার অসহায় এবং নিরস্ত্র যোদ্ধাদের আপনার হেফাজতে রেখে গেলাম, এঁদের দেখে রাখবেন’।
______________________________
http://arts.bdnews24.com/?p=4821
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:২৫582855
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:২৫582855- স্বাধীনতার ঘোষণা: বেলাল মোহাম্মদের সাক্ষাৎকার
প্রদীপ চৌধুরী | ২৮ মার্চ ২০১০ ৭:৪৭ অপরাহ্ন
__________________________________
[মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অবদান ছিল অপরিসীম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের স্থপতি বেলাল মোহাম্মদের এই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় ২১ মে মার্চ ২০১০ তারিখে। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের সিনিয়র রিপোর্টার প্রদীপ চৌধুরী। এর লিখিত অংশে কিছু সম্পাদনা করা হয়েছে। তিনটি পর্বে সাক্ষাৎকারটি পরিবেশিত হবে। বি. স.]
ভিডিও ১
ভিডিও ২
ভিডিও ৩
১.
প্রদীপ চৌধুরী: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কীভাবে স্থাপন করলেন এবং বঙ্গবন্ধুর দেওয়া স্বাধীনতার ঘোষণা কীভাবে জাতির কাছে পৌঁছে দিলেন সেটা একটু আমাদের বলবেন।
বেলাল মোহাম্মদ: মুক্তিযুদ্ধের সূচনা লগ্নে ২৬ শে মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন দখলদার বাহিনী আগের রাতে অর্থাৎ ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে হঠাৎ করে নিরস্ত্র জনতাকে আক্রমণ করে। ঢাকায় বিশেষ বিশেষ কি-পয়েন্ট স্টেশনগুলো দখল করে নেয়। তার মধ্যে রেডিও স্টেশনও ছিল। রেডিওতে গিয়ে তারা বিভিন্ন প্রচার শুরু করে।
এদিকে অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু যে অসহযোগ আন্দোলন ডেকে ছিলেন তার প্রভাবে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ দলমত নির্বিশেষে সবাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। কতিপয় কুলাঙ্গার, রাজাকার, আলবদর যারা ছিল তারা ছাড়া বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের মুখে একটি স্লোগান ছিল ‘জয় বাংলা’ এবং ‘জয় বঙ্গবন্ধু’। একক স্লোগান, একক নেতৃত্ব।
সেই সময় রেডিওতে রেডিওর লোক যারা ছিল তারাও উদ্বুদ্ধ ছিল এবং ৭ই মার্চের বক্তৃতায় সুস্পষ্টভাবে রেডিওর কর্মচারীদের উপরও নির্দেশ ছিল, যদি রেডিওতে বাঙালিদের স্বার্থে কথা বলতে না দেওয়া হয় তাহলে কোনও বাঙালি যেন রেডিও অফিসে না যায়।
২৬শে মার্চ সকাল বেলা স্বাভাবিক ভাবে আমরা লক্ষ করলাম, ঢাকা কেন্দ্র থেকে সামরিক বাহিনীর কথা বলা হচ্ছে। ওদের বক্তব্যই শুধু বলা হচ্ছে। কাজেই আমরা আর যাইনি রেডিওতে। আমি আর আমার সমমনা যারা আছি তারা চিন্তা ভাবনা করছি, যে কী করা যায়। এখন ঢাকা কেন্দ্র হলো ১০০ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার আর চট্টগ্রাম মাত্র ১০ কিলোওয়াট। আমাদের ৫০ মাইল ব্যসার্ধ রেডি আছে, ঐ ১০ কিলোওয়াট দিয়েই একটা কাউন্টার প্রোগ্রাম করার উদ্যোগ নেওয়া যায়।
প্রস্তুতি যখন নেওয়া হচ্ছিল প্রথমে আমি ছিলাম এনায়েতগঞ্জে, দাদা ডা. শফির বাড়িতে, সেখান থেকে আওয়ামী লীগের একটা অফিস ছিল জহুর হকার্স মার্কেটে, সেখানে গেলাম আমি। তিন দিনই তার সঙ্গে দেখা করার জন্য গেলাম, কিন্তু তার দেখা পেলাম না। ওখানে তরুণ যারা আমাকে একটা জীপ গাড়ি দিলেন, গাড়িটা নিয়ে প্রস্তুতি পর্বে সর্ব প্রথম কেন্দ্রকে পাহারা দেওয়ার জন্য গেলাম ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের কাছে। তাকে পাওয়া গেল। তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ আমি পাহারার ব্যবস্থা করছি। আপনি কাজ আরম্ভ করেন।’
তো এক পর্যায়ে ব্রটকাস্টিং হাউজের সামনে পেলাম গোসাইলডাঙ্গা আওয়ামীলীগ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ডা. আনোয়ার আলীকে। তিনি বললেন, ‘রেডিও যে চালু করবেন তাতে কী প্রচার করবেন?’ আমি বললাম, ‘কী আর প্রচার করবো বঙ্গবন্ধু আর স্বাধীনত
তিনি আমার হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিলেন। কাগজটা হলো ২৬শে মার্চ সকাল বেলা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা মাইকিং করেছে চট্টগ্রামের প্রধান প্রধান সড়কে যে ঢাকায় আক্রমণ হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে আমাদের মহান নেতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এই বক্তব্যটুকু তার বার্তা আকারে গিয়েছিল ডা. আনোয়ার আলী বললেন।
তিনি সেটাকে বাংলায় অনুবাদ করে… তখনকার দিনে হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রেকর্ড করা হতো এবং সেটা দিয়েই আমরা শুরু করেছি। আমরা সন্ধ্যা ৭ টা ৪০ মিনিটে চালু করতে পেরেছি এবং বিভিন্ন কণ্ঠে নাম ছাড়া ওই বক্তব্যটুকু প্রচার করেছি।
কিছুক্ষণ পর ওখানে এলেন এম এ হান্নান। তাকে আমি চিনতাম না। ডা. জাফর ছিলেন তখন জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ। তিনি আমাকে পরিচয় করে দিলেন যে ইনি আমদের হান্নান ভাই। হান্নান ভাই বললেন, ‘আমার নাম অ্যানাউন্স করো না, আমি একটা ভাষণ দেবো।’
আমি বললাম, ‘আপনার নাম অ্যানাউন্স করবো না। আপনি এমনি ভাষণ দেবেন কারণ আমরা ঘোষণা করেছি আগামী কাল, পরশু ও তরশু এমনি ভাবে প্রচার করবো। ধারাবাহিক ভাবে আমাদের পরিচিত নাম প্রচার হলে শত্রুপক্ষ বুঝে ফেলবে যে এটা কোথা থেকে হচ্ছে। আপনার কণ্ঠস্বরটাই যথেষ্ট।
উনি বললেন, ‘যে দুপুর বেলা আমি কিন্তু আপনার এই কেন্দ্র থেকে ছোট্ট আকারে একটি ঘোষণা প্রচার করেছিলাম।’ সেটা আমি জানি না। অর্থাৎ সেই একই দিন ২৬ শে মার্চ দুপুর বেলা উনি (এম এ হান্নান) রেডিওর কয়েক জন পরিচিতকে নিয়ে… যারা অনিচ্ছুক ছিল এই রকম কয়েকজনকে নিয়ে রেডিও অন করিয়ে। ওটাকে বলা হবে চট্টগ্রাম বেতারের বিক্ষিপ্ত একটা অধিবেশন। সেখানে বঙ্গবন্ধু দেশের স্বাধীনতা করেছেন এই মর্মে একটা বক্তব্য রয়েছে।
একই বক্তব্য তখন একটু বড় করে লিখে এনেছেন উনি। সেটা আবার দ্বিতীয় বার প্রচার করলেন। এবারও নাম ছাড়া। এম এ হান্নান সাহেব ২৬ তারিখে দুই বার আসার পরে আর আসতে পারেন নি। এর পর উনি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন।
অন্যদিকে রফিকুল ইসলাম সাহেবকে আমি যে বলে ছিলাম সৈন্য পাঠিয়ে পাহারার ব্যবস্থা করার জন্য কিন্তু তিনি পাঠান নাই। যার ফলে অত্যন্ত অসহায় বোধ করেছিলাম। রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান শেষ করার পর দেখা গেল ওখানে কেউ নেই। যে দুইজন ইঞ্জিনিয়ারকে জোর করে কাজ করিয়ে ছিলাম তারা চলে গেছে। লিসেনারদের বলেছি, আপনারা আগামী দিন সকাল ৯টায় আমাদের অনুষ্ঠান শুনবেন। যদি পর্যাপ্ত সংখ্যক সহকর্মী না আসে তাহলে তো প্রচার করা যাবে না।
এখন দুঃশ্চিন্তা হলো প্রথমত কালুর ঘাট থেকে এনায়েত বাজার পর্যন্ত আমরা হেঁটে পার হয়ে গেছি, আগামী কাল প্রোগ্রাম কীভাবে করবো। এদিক সেদিক টেলিফোন করেছি টেলিফোন দেওয়ার পর চন্দনপুরের তাহের সোবাহান নামে আমার এক বন্ধু ছিল, তিনি বললেন, ‘রফিকুল ইসলাম ক্যাপ্টেন কেন যে কথা দিয়ে কথা রাখলেন না জানি না। তার চেয়ে বড় একজন উচ্চ পদের মেজরের সন্ধান আমি জানি, তবে নাম জানি না। তিনি পটিয়াতে আছেন। তিনি হেড কোয়ার্টারের বাইরে এসেছিলেন বাবর এবং সোয়াত জাহাজের অস্ত্র খালাশের জন্য। তিনি আজ রাতে, মানে ২৬ শে মার্চ দিবাগত রাতে সিচুয়েশন অবজার্ভ করার জন্য পটিয়াতে আছেন।’
আমাকে উনি অ্যাডভাইজ করলেন, ২৭ তারিখ যদি পটিয়াতে যেতে পারেন নিশ্চয়ই ওনাকে ওখানে পাবেন। যেহেতু বাইরে আছেন নিশ্চয়ই উনি বঙ্গবন্ধুর সাপোর্টার হবেন। আমার আর এক বন্ধুর সাহায্যে আমরা একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে পরের দিন সকাল বেলা রওনা হয়েছি পটিয়ায়। আর আমার সহকর্মীদের বলে দিয়েছি কালুর ঘাটের দিকে আস্তে আস্তে যাবে। আমি পটিয়া থেকে আসার পর প্রোগ্রাম শুরু হবে।
পটিয়ায় পৌঁছেই দেখা গেল আর্মি গিজ গিজ করছে। ওখানকার দারোগা আমার পরিচিত মানিক মিয়া। ওনাকে জানলাম।
এখানে যে আর্মি অফিসার আছে তার নাম মেজর জিয়াউর রহমান। তার সঙ্গে দেখা হলো। তাকে বললাম, ‘আপনি তো এখানে ব্রটকাস্ট শুনেছেন।’
তিনি বললেন, আমরা যে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেছি তা শুনেছেন এবং খুশি হয়েছেন।
আমি বললাম, ‘আপনি যদি দয়া করে আপনার এই ছাউনিটা এখান থেকে সরিয়ে কালুর ঘাটে নিয়ে যেতেন তা হলে বাড়িটা প্রটেক্ট হবে। আমরাও ওখানে স্থায়ীভাবে থাকতে পারবো। স্থায়ীভাবে না থাকতে পারলে কোনো কমিটমেন্ট করা যাবে না। ঠিক টাইমে রেডিওতে প্রোগ্রাম দেওয়া অ্যাডভেঞ্চার নয়। বেশ কিছু লোক লাগে। সব রকমের পয়েন্টে লোক বসে থাকা লাগে।’
তার পর উনি আর দেরি করেন নাই। সৈন্যদেরকে রওনা করিয়ে দিলেন। নিজেও একটা জীপে করে রওনা হলেন। আমাদের গাড়িটা ওনার গাড়ির পেছনে পেছনে চললো। পথে যেখানেই উনি বেশি মানুষের জটলা দেখেছেন, যারা কর্মস্থল ছেড়ে পোটলা-পাটলি নিয়ে চলে যাচ্ছে সেখানে তিনি দাঁড়িয়ে একটা বক্তৃতা দিলেন। ‘আপনারা যার যার কাজের জায়গায় চলে যান। ইনশাল্লাহ দু’এক দিনের মধ্যে আমরা পাঞ্জাবিদের খতম করে দেবো। আর উর্দু ভাষায় যারা কথা বলে তারা সব আমাদের দুশমন। তাদেরকে শেষ করে দেন।’
এটাই ছিল ওনার বক্তব্য। এই দশ জায়গায় থেমে থেমে যাওয়ার জন্য আমাদের কালুর ঘাটে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। গিয়ে দেখলাম কালুর ঘাটে পাহাড়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। হুইসেল পড়লো, একজন সেন্ট্রি হাত বাড়িয়ে দিল। আমাদের দুটো গাড়ি ঢুকলো।
২.
আমার সহকর্মী যারা উপস্থিত ছিল, তারা প্রোগ্রাম শুরু করলো। একসময় জিয়াউর রহমান ও আমি একটা রুমে বসেছি। আমার এক সহকর্মী আমাকে কিছু কাগজপত্র দেখাচ্ছে। আমি কী মনে করে বললাম, “আচ্ছা মেজর সাহেব, এখানেতো আমরা সবাই মাইনর আপনিই একমাত্র মেজর। আপনি কি নিজের কণ্ঠে কিছু বলবেন?”
উনি বললেন, “হ্যাঁ সত্যিই তো, কী বলা যায়?”
একটা কাগজ এগিয়ে দেওয়া হলো। তার প্রতিটি শব্দ তিনিও উচ্চারণ করেছেন এবং আমিও উচ্চারণ করেছি। এইভাবে লেখা শুরু হলো।
“আই মেজর জিয়া অন বিহাফ অব আওয়ার গ্রেট ন্যাশনাল লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ডু হেয়ার বাই ডিক্লেয়ার ইন্ডিপেনডেন্স অব বাংলাদেশ।”
তারপরে লেখা হলো পাঞ্জাবিরা যেসব অস্ত্র ব্যবহার করছে। তাদের দমন করতে আমাদের দুই দিন কি তিন দিনের বেশি সময় লাগবে না। তার পরে শেষ করা হলো ‘খোদা হাফেজ জয় বাংলা’ বলে।
এই ঘোষণাটির খসড়াও তৈরি হলো আমার সঙ্গে আলাপ করে। আমি সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদও লিখলাম। আর আমার সহকর্মীদের বলে দিলাম একটা ঘোষণা দিতে থাকো, “মেজর জিয়াউর রহমান একটি জরুরি ভাষণ দেবেন। জিয়াউর রহমান বলবেন না, মেজর জিয়া বলবেন।”
কিছুক্ষণের মধ্যে মেজর জিয়া একটা জরুরি ভাষণ দেবেন - এভাবে দুই তিনবার অ্যাডভান্স অ্যানাউন্সমেন্ট করা হলো। তারপর তিনি নিজের কণ্ঠে ইংরেজিটা পড়েছেন। বাংলাটা আমার সহকর্মী আব্দুল্লাহ আল ফারুকের কণ্ঠস্বর ভাল, তাকে দিয়ে শুনিয়েছি। এইভাবেই হলো। কোন রকম পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না, পরিকল্পনা ছিল না এবং এটা স্বাধীনতা ঘোষণা না। এটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে একই কথার পুনরুক্তি করা।
রাষ্ট্রপতি জিয়া কোনোদিন নিজেকে স্বাধীনতার ঘোষক বলেননি। ২৬ তারিখও বলেননি, উনি সবসময় ২৭ তারিখই বলেছেন। এবং ৭ই মার্চের বক্তব্যকে তিনি একটা প্রবন্ধে একটা পত্রিকায়, সম্ভবত বিচিত্রায়, জাতির জনকের গ্রিন সিগন্যাল বলেছেন। পরবর্তী সময় যে ঘোষক-টোষক বলা হয়েছে এগুলো তৈরি করা। রাষ্ট্রপতি জিয়া এগুলো ক্লেইম করেননি।
আমি এখন যে কথাটুকু বললাম যে ওনাকে ঠাট্টার মতো প্রস্তাব দিয়েছি, ওনার জীবদ্দশায় আমি এ নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছি। সে সব প্রবন্ধ উনি পড়েছেন। উনি কোনো আপত্তি করেননি। যেমন আমি ওনাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছি, কিন্তু এক জায়গায় উনি বলছেন, “উই ক্যাপচার্ড রেডিও অন টোয়েন্টি সেভেন,” এই ‘ক্যাপচার্ড’, এটা সামরিক ভাষা। আর্মিকে আমি ডেকে নিয়ে গেলেও তারা পজেশন নিলেই তারা তাদের ভাষায় বলবে আমরা ক্যাপচার করেছি। এতে মাইন্ড করি না।
প্রদীপ চৌধুরী: জিয়াউর রহমানই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন - এই বিষয়ে আপনার বক্তব্য?
বেলাল মোহাম্মদ: এটা সম্পূর্ণ মতলবি এবং রাজনৈতিক। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা এটা ছেলে খেলা নয়, এটা যে কেউ দিতে পারে না। বাংলাদেশে স্মরণকালের ইতিহাসে নবাব সিরাজ-উদদৌলার পর থেকে যদি ধরি, অনেক বড় নেতার উদ্ভব হয়েছে। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রায়, শেরেবাংলা একে ফজলুল হক এরা কেউই স্বাধীনতার ঘোষণার পরিবেশ পাননি। একমাত্র ১৯৭১ সালে বঙ্গদেশের একটা খণ্ডিত অংশ পূর্ববঙ্গের বাঙালীরা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের একচ্ছত্র নেতৃত্বে বাঙালী জাতীয়তাবাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পেরেছিল।
আমাদের স্মরণকালের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুই একমাত্র সব রকমের ক্রাইটেরিয়া পূরণ করে স্বাধীনতা ঘোষণার পরিবেশ পেয়েছিলেন। স্বাধীনতার ঘোষণা তো ছেলেখেলা নয়। সেই স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারে যার জনপ্রতিনিধিত্ব থাকে ব্যাপক। সেই স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারে যার আন্তর্জাতিক পরিচিতি থাকে, সামরিক বাহিনীর সাপোর্ট থাকে এবং সেই মুহূর্তে শ্যাডো গভর্নমেন্ট ফর্ম করার প্রস্তুতি থাকে।
এই সবগুলো ক্রাইটেরিয়ার একমাত্র ষোলকলা পূর্ণ হয়েছিল ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। কাজেই স্বাধীনতার ঘোষণা আমি তো বললাম নেতাজীও করতে পারেননি, দেশবন্ধুও করতে পারেননি। আমাদের স্মরণকালের ইতিহাসে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সর্ব প্রথম বাঙালীর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি হয়েছিল বাংলাদেশের খণ্ডিত অংশে ।
আমি দাবি করে থাকি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্ব প্রথম সাংগঠনিক তৎপরতা। আমরা ক্ষুদ্র একটি দল যখন সংগঠিত হয়েছিলাম তখনও আমাদের প্রধান দল যে সামরিক বাহিনী তাও সংগঠিত হয়নি। আমরা বরং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বলেছি মুক্তিবাহিনী গঠন করার জন্য, দলে দলে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য এবং এটা শত্রুপক্ষ ঠিকই ধরে নিয়েছিল। তাই শত্রুপক্ষের প্রথম বোম্বিংয়ের লক্ষ্য ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। ৩০শে মার্চ কালুরঘাটের ওপরই বোমা বর্ষণ হয়েছিল এবং সেটাই ছিল হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর সর্ব প্রথম বিমান হামলা। অর্থাৎ তারা আমাদের ধরে নিয়েছিল তাদের সেই মূহূর্তের প্রধানতম শত্রু।
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আমি আগেই বলেছি বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের সুস্পষ্ট নির্দেশনার দ্বারা অভিভূত বা উদ্বুদ্ধ বেতার কর্মীরাই গঠন করেছে। রাজনৈতিক নেতারা রেডিও চালু করতে কেন আসবে? তারা এসে পার্টিসিপেট করতে পারে। সামরিক বাহিনী রেডিও চালু করবে কেন? তারা পাহারার ব্যবস্থা করতে পারে।
৩.
প্রদীপ চৌধুরী: কালুরঘাটে যে আপনারা রেডিও স্টেশনটা স্থাপন করেছিলেন ওটা তো চট্টগ্রাম রেডিওতে আপনারা যারা ছিলেন তারাই এটা করেছিলেন?
বেলাল মোহাম্মদ: আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছিলাম। এই নামটা আমার দেওয়া। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে আমার সঙ্গে পেয়েছি আবুল কাশেম সন্দীপকে। ইনি বেতারের বহিরাগত। আমার সঙ্গে থাকতেন ফ্যামিলি মেম্বারের মতো। তিনি একটা কলেজে অধ্যাপনা করতেন। আর আব্দুল্লাহ আল ফারুক রেডিওর জুনিয়ার অফিসার ছিলেন। এই দুইজনকে আমি প্রথম দিন পেয়েছি। আর যারা এসেছিল তারা কাজে সহায়তা করে ইচ্ছা করে চলে গেছে রাখতে পরিনি।
তার পরের দিন (২৭ মার্চ) এসেছেন কাজী হাবীবউদ্দিন, আর একজন কর্মী এবং রেডিওর ইঞ্জিনিয়ার বিভাগের কর্মী আমিনুর রহমান। ২৮ তারিখে এসেছেন সারফুজ্জামান ও রাসিদুল হোসেন, ২৯ তারিখে এসেছেন সৈয়দ আব্দুর সাগির, মোস্তফা আনোয়ার ও রেজাউল করিম চৌধুরী। এই কজন হলাম আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের স্থপতি। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে একমাত্র এম এ হান্নান একদিন এসেছেন, পরে আর কোনোদিন আসেননি। তিনি ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক নেতাও আসেননি।
প্রদীপ চৌধুরী: তাহলে কি কেন্দ্রটি আপনারাই চালিয়েছিলেন?
বেলাল মোহাম্মদ: হ্যাঁ, আমরাই চালিয়েছি। রেডিও আমাদের কাজ, ওরা আসবে কেন? ওদের অন্য কাজ, রাজনৈতিক নেতাদের তো অন্য রোল। তারা আর সামরিক বাহিনী তো বেতার প্রতিষ্ঠা করে নাই। সামরিক বাহিনীকে অনুরোধ করে নিয়ে আসা হয়েছে। নিয়ে আসার পর পাহারার ব্যবস্থা উনি করেছেন এবং ওদের সঙ্গে যিনি মেজর ছিলেন তিনি আমার তাৎক্ষণিক একটি প্রস্তাবে ঘোষণাটি পাঠ করেছেন। এর জন্য উনার কোনোরকম পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। উনি রেডিওতে কিছু বলবেন - এমন কোনো আভাসও উনি দেন নাই। আমি ওনাকে ঠাট্টার মধ্যে মেজর ও মাইনর বলেছিলাম বলেই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বক্তব্য দিলেন। আর উনি আরো কিছু বক্তব্য দিলেন। দ্বিতীয় তৃতীয় বক্তব্য আছে, প্রথম বক্তব্যটার কথা আমরা বলি যেটা বঙ্গবন্ধুর নামে। এখন নানান রকমের উদ্ভট কথাবার্তা বলা হয় প্রত্যক্ষদর্শীদের কথাটা উপেক্ষা করে।
অনেকেই, আমাদের অনেক বুদ্ধিজীবীদের বলতে দেখি প্রথমে নাকি জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর নাম বলেন নাই। তখন প্রেশার দিয়ে নাম দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলে তারা নিজেদের উদ্যোগে নিয়ে এসেছে। আপনারা যদি নিজেরাই নিয়ে আসেন, তা হলে বঙ্গবন্ধুর নাম বলেন না কেন? উনি তো বঙ্গবন্ধুর অনুসারী হিসাবে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আমরা লক্ষ করেছি তো তার কথাবার্তা। বাঙালী একজন মেজর, বঙ্গবন্ধুর অনুসারী হবে না কেন?
হ্যাঁ, ওনার আদর্শগত অন্যকিছু যেটা, সেটা উনি যখন পাওয়ারে এসেছেন, তখন হয়তো আমরা সেটা লক্ষ করেছি। উনি যখন সংবিধানের ওপর হাত দিয়েছেন তখন আমরা বুঝতে পেরেছি উনি বাঙালী জাতীয়তার প্রতি বিশ্বাস করেন না। এর আগে তো বুঝতে পারিনি। ওই সময় তো আমরা ওনাকে অনুগত দেখেছি। ওই সময় তো উনি-আমরা অভিন্ন ছিলাম। উনি যুদ্ধ করেছেন এবং ওনার ভাষণের একটা গুরুত্ব ছিল সেটা অস্বীকার করা যাবে না। অন্য যত কণ্ঠস্বর একটা যুদ্ধক্ষেত্রে এক্স, ওয়াই, জেডের কণ্ঠস্বর ওগুলো। কারণ সামরিক বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে একটা দেশ। সামরিক বাহিনীর লোকও এই দলে আছে, বঙ্গবন্ধুর দলে একজন মেজর থাকা মানে একটা গ্রুপ আছে। এটা মানুষের মনোবল অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। মেজর জিয়াউর রহমানের কণ্ঠস্বর ওই সময়, মুক্তিযুদ্ধের সময় ২৭ শে মার্চ, জনগণকে নৈতিক সাহস দিয়েছে এইভাবে যে, আমরা আক্রান্ত হলেও ভয়ের কিছু নাই। আমাদের দলেও আর্মি আছে। এটা বিরাট কাজ হয়েছে। এটা কাকতালীয়ভাবে হয়েছে, কিন্তু এটা করার জন্যই যে জিয়াউর রহমানকে আনা হয়েছে বা তিনি করেছেন তা নয়, এটা আকস্মিকভাবে হয়েছে।
আর রেডিও যদি চালু নাও হতো তাহলে কি মুক্তিযুদ্ধ হতো না? ৭ই মার্চের বক্তব্যেই পরিষ্কারভাবে মুক্তিযুদ্ধের সব ধরনের নির্দেশনা আছে। তারপর যার হাতে যা আছে তা নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার কথা আছে। সব কিছুই বলা আছে, একেবারে ভবিষ্যৎ বাণীর মতো মনে হয়। আর কাব্যিক ভঙ্গিতে বলা হয়েছে, কারণ একেবারে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হলে ওনাকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে ঘোষণা করা হবে আন্তর্জাতিক বিচারে। কাজেই তখন কায়দা করে বলা হয়েছে। সেটা বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। যেহেতু উনি রাজনৈতিক নেতা। তার পক্ষেই এটা সম্ভব হয়েছে, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম” কাব্যিক ভঙ্গিতে বলা। আমি এই মুহূর্তে স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম। আমরা চাইলাম, এটা আমরা চাইছি - এমন বললে সে দিন এই লক্ষ লক্ষ লোককেও মেরে ফেলতো ওরা। বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলত ওরা। আন্তর্জাতিক বিচারে বলত একটা রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে - এসব বলতো। কাজেই সেদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না কেন এগুলো সব আজে-বাজে কথা। আর বঙ্গবন্ধু ছাড়া অন্য কাউকে স্বাধীনতার ঘোষক বলা - এত নীচতা কোনোভাবেই বিজ্ঞানে ফেলা যায় না।
বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান সেটা পাঠ করেছিলেন। অবিকল সেটা পাঠ করেনি। বঙ্গবন্ধুই হলেন একমাত্র ঘোষক স্মরণকালের ইতিহাসে। স্বাধীনতা ঘোষণা করার অধিকার উনিই একমাত্র পেয়েছিলেন। আর রেডিওতে যারা জয়েন করেছে তারা সব বেতার ঘোষক। বেতার ঘোষকদের তখনকার সময় ফি ছিল ১৫ টাকা, এখন কত আমি জানি না। আমরা সবাই বেতার ঘোষক। তো সেই বেতার ঘোষক ২৬ মার্চ থেকে হিসাব করলে আমি, আমার সহকর্মীদের নামগুলো সব যদি বলতে থাকি তাহলে ২৭ তারিখে জিয়াউর রহমানের অবস্থান হল ৯ নম্বর বেতার ঘোষক।
প্রদীপ চৌধুরী: আপনি তো এবার স্বাধীনতা পদক পেয়েছেন, আপনার অনুভূতিটা জানতে চাচ্ছি।
বেলাল মোহাম্মদ: স্বাধীনতা পদক আমাকে দেওয়া হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের জন্য। আমি এতক্ষণ যে কথাগুলো বলেছি তা আমি একা করিনি। আমি যে কাজটা করেছি ইট ওয়াজ এ জয়েন্ট ভেঞ্চার। রেডিও একা কেউ চালাতে পারে না। আমি দশজন সহকর্মীর নাম বলেছি ইতিমধ্যে। আমাদের এই দশজনকেই জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২৫ শে মার্চ ‘বঙ্গবন্ধু স্বর্ণপদক’ ঘোষণা করেছিলেন একটা সার্কুলারে। তার কয়েক মাস পরেই অভিশপ্ত দিন ১৫ আগস্ট। মানব জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে নির্মমতম হত্যাকাণ্ডের দিনটি এসে যাওয়ায় ওই পুরস্কার আর কার্যকর হয়নি। আমার মনে হয় আমরা সেই পুরস্কারই পেয়ে গিয়েছিলাম। ওই পুরস্কারটাকেই আমি অনেক বড় করে দেখি।
প্রদীপ চৌধুরী: আপনাদের কত জনের নামে ওই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল?
বেলাল মোহাম্মদ: সেই পুরস্কার মোট ২২ জনের নামে ঘোষণা হয়েছিল। তো ওটা আমরা পেয়েছি মনে করি। একটা স্বর্ণপদক হাতে ঝুলানোর চেয়ে বঙ্গবন্ধুর সময় ওনার স্বাক্ষরে ঘোষণা করা হয়েছে - এটা আমাদের বড় পাওয়া। এর চেয়ে আর বড় পাওয়া কিছু নেই। এর পরে যত পুরস্কারই আসুক, আমরা অনেক বড় করে দেখি বঙ্গবন্ধুর স্বর্ণপদককে।
প্রদীপ চৌধুরী: বেলাল মোহাম্মদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, পাঠক ও শ্রোতাদের পক্ষ থেকে আপনাকে কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাই।
বেলাল মোহাম্মদ: আমি আমার বক্তব্যে সর্বশেষে সবসময় যা উচ্চারণ করি তাই করছি, ‘জয় বাংলা’।
[email protected]
_______________
http://arts.bdnews24.com/?p=2769
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:৩৮582856
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:৩৮582856- ‘২৫শে মার্চ রাতে আমি ছিলাম প্রেসক্লাবে, একা’
ফয়েজ আহ্মদ | ২৬ মার্চ ২০১১ ৩:১০ পূর্বাহ্ন
_______________________________________
ঢাকার রাস্তায় বেসামরিক লোকদের মারছে পাকিস্তানি সেনারা, ১৯৭১
২৫ শে মার্চ সকাল থেকেই আমরা অনুভব করেছিলাম যে পাকিস্তান বাহিনী হয়তো আজই আক্রমণ শুরু করতে পারে। আমরা ইয়াহিয়া খানকে তখন ঢাকায় পেয়েছিলাম, ভুট্টো ঢাকায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লেফট সাইডের এবং মুসলিম লীগের বিখ্যাত, বিখ্যাত নেতারা তখন অনেকেই এই ক্রাইসিস পিরিয়ডে ঢাকা এসেছিলেন। ইয়াহিয়া খান প্রথম ভাব করেছিলেন যে তিনি কোন একটা মিমাংসামূলক প্রচেষ্টায় ঢাকায় আসছেন; অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা তা নয়। তাদের আয়োজন—আক্রমণের ব্যবস্থা, সমস্ত কিছুর প্রযোজনে তারা আরো একটু সময় চেয়েছিল এবং আলোচনার উছিলা করে, সময় ক্ষেপণ করে, অস্ত্র আমদানি করা হচ্ছিল। এমন কি ভারত যখন নাকি ওভার-ফ্লাই করতে দিলো না পাকিস্তানকে অস্ত্র নিয়ে, ইস্ট পাকিস্তানে, তারা তখন চীন হয়ে আসার চেষ্টা করলো।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণহত্যার ভিডিও ফুটেজ
আমরা দুইজন পাইলটকে পেয়েছিলাম। আমি আর আমার এক বন্ধু—যে নাকি স্বরাজ পত্রিকায় আমাকে সাহায্য করেছে—এম আর আখতার মুকুল, আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমাদের কাছে তার আগের দিন মানে ২৪ তারিখ দুইজন খুব স্মার্ট লোক এসে উপস্থিত, বিকালবেলা, সন্ধ্যার আগে এবং তারা এসে বললো–এই কাগজে প্রমাণ যে এটা চীন হয়ে এই প্লেন আসছে। দেখা গেলো এটা একটা লগ-বুকের দু’টি পাতা। প্লেন যারা চালায় সেই পাইলটদের লগ-বুক থাকে, সেই লগ-বুকে সমস্ত লেখা থাকে টাইমলি কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে, প্লেনের কী অবস্থা। সেই লগবুকের পাতা—দুটো তারা নিয়ে এসেছে এবং ঐ লগ-বুকটার ঐ পাতাতে এনডোর্স করা আছে—উড়ুমচি। উড়ুমচি হচ্ছে চীনের উত্তর অঞ্চলের প্রদেশের রাজধানী এবং উড়ুমচি হয়ে, ওরা ওখান থেকে তেল নেয়, পাকিস্তান থেকে উড়ুমচি আসে, উড়ুমচি থেকে ঢাকায় আসে।
তারা কয়েকদিন যাবৎ এইভাবে সোলজার এবং অস্ত্র আনছিল চায়না হয়ে ঘুরে, কারণ ভারতের উপর দিয়ে আসতে বাঁধা ছিল। তো এই উড়ুমচি ওখানে এনডোর্স করা ছিল, ঐ কাগজে—সেই পৃষ্ঠা দুটো আমাকে দেওয়া হয়। তো আমি আর মুকুল তখন দেখে তো অবাক—যে এই দুই পাইলট উপস্থিত এখানে—এরা দু’জন বাঙালী পাইলট। এরা আর্মির লোক। এখন এই দু’জনের এই কাগজটা নিয়ে আমি চলে গেলাম শেখের কাছে, গিয়ে তাকে দিয়ে বললাম—এই যে দেখেন প্রমাণ যে চায়নার মাধ্যমে সোলজার আসছে এবং অস্ত্র আসছে। সে পেয়ে খুব খুশি, কারণ সে সাহায্য পাইল। তো আমরা চলে এলাম, পাইলট দু’জনও চলে গেলো। শেখ সাহেব বিকাল বেলা এটা পেয়ে এটা নিয়ে সে ইয়াহিয়া খানকে দেখিয়েছে যে—তোমার সোলজাররা চীন হয়ে আসছে, এই যে প্রমাণ দেখো, এই লগ-বুকে দস্তখত করা আছে উড়ুমচি এয়ারপোর্ট; তোমাদের লোক এসেছে, এই প্লেনটাই ঢাকায় আসছে তার নাম্বার (…এত এত)।
এটা খুব বড় কাজ হয়েছে। আমি সেদিন রোজকার মতোই সন্ধ্যার পরে—আমরা জনা ১০/১২ জন রিপোর্টার প্রতিদিন শেখের বাড়িতে যেতাম। এটা রুটিন ওয়ার্ক ছিল, বিভিন্ন পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টাররা ছিল, কোন কোন সময় এডিটর ছিল, কেউ সাব এডিটর ছিল এবং রিপোর্টার ছাড়াও অন্য লেখক–তারা থাকতো এবং তারা—শেখের কথাবার্তা শোনার জন্য আমরা যেতাম; কী বলে—প্রতিদিন। সহজ কথা হইছে, তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে এবং সরকারী সমস্ত অফিস—পাঁচ লক্ষ লোক তখন স্ট্রাইক করে, ধর্মঘট করে–সরকারী কর্মচারীরা কেউ অফিসে যায় না, সব—রুমগুলি তালা বন্ধ, সেক্রেটারিয়েটসহ! এই অবস্থায়—শেখ সাহেবের নির্দেশেই, তার বাড়ি থেকে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা চলতো তখন। তো এই অবস্থার মধ্যে আমরা ২৫ তারিখের সন্ধ্যার পরে, হঠাৎ শেখের বাড়িতে আসলো সীমান্ত গান্ধীর ছেলে এবং তাকে বলে গেলো যে এরা আক্রমণ করবে, তোমাদের এই অনুমানটাই কারেক্ট এবং আমিও তোমার সাথে শেষ দেখা করে গেলাম। সে আমাদের পক্ষের লোক ছিল।
সন্ধার আগে ঘটনা, আমরা রোজই ঐ সময় থাকি, এই কয়দিন যাবত। রাতে প্রায় ৯টার দিকে দেখলাম যে শেখ সাহেব কারো কথা মানতে রাজি না; উনি বলছে যে তোমরা চলে যাও, যার যার পথে। আমি আমার ব্যবস্থা করবো এবং কী ব্যবস্থা করবেন তা কিন্তু বলছেন না আমাদেরকে। তখন তাজউদ্দিন সাহেব শহীদ নজরুল ইসলাম—এরা সবাই একে একে আসলো এবং তারা তাকে বুঝালো যে আপনি এই জায়গাটা ছাড়েন, এই বাড়িটা ছাড়েন, এই বাড়িতে আক্রমণ হবে। তখন সে বললো যে আমি ব্যবস্থা করবো, কী করতে হবে না হবে আমি জানি, তোমরা আমাকে ছাড়ো এবং তিনি রয়ে গেলেন এবং তার অন্যান্য নেতারা সব চলে গেল। তখন আমি ঐ ১০ টার দিকে, আমি আমার অফিসে আসি এবং অন্যান্য রিপোর্টাররাও চলে আসে। তখন বুঝতে পারছি না যে শেখ সাহেব কী করবে—থাকবে, ধরা দিবে, নাকি পালাবে—কারো কাছে বলতে রাজি না তিনি। এই পরিস্থিতিতে শেখ সাহেবকে নিয়ে যখন এত চিন্তা এবং সবাই মিলে ভাবতে থাকি—তাকে রক্ষা করা যায় ক্যামনে, তখন শেখ সাহেব তার নিজের পথ অবলম্বন করলেন। আমরা চলে আসলাম।
আমি তখন স্বরাজ পত্রিকার এডিটর। তোপখানা রোডে একটা অফিস ছিল, দোতলায় অফিস, ওখানে আসলাম দৌড়াদৌড়ি করে। তখন সাড়ে দশটা-এগারোটা, লোকজন কমে গেছে, রাস্তায় লোক নাই, খুব কম লোক, গাড়িগুড়ি নাই, দুই-একটা গাড়ি সাঁই সাঁই করে আসে, যায়। আর রিক্সাও কমে গেছে। তখন আমি ওখানে, আমার অফিসে কাজকর্ম কালকে কী হবে না হবে সেইগুলি বন্দোবস্ত করে দিয়ে বেরিয়ে আসলাম। তখন এগারোটা বেজে গেছে, রাস্তায় দেখি—একটা কাকও নাই, সব খালি এবং একটা রিক্সাও নাই গাড়ি তো দূরের কথা। তখন আমি কোনো উপায় না পেয়ে–আমি যাবো আজিমপুরের দিকে আমার বাসা—কীভাবে যাবো? হাঁটা দিলাম, হাঁটা দিয়ে একটা রিক্সা পাইলাম রাস্তায়, রিক্সা দ্রুত চলে যাচ্ছে, তখন রিক্সাওয়ালাকে বললাম যে আমাকে একটু ধানমণ্ডিতে নামিয়ে দাও। আমার বাসায় যেতে হবে না, ঐ কাছাকাছি কোথাও নামিয়ে দাও। ধানমণ্ডির ঐ কোনায় আমি থাকি, মসজিদের কাছে আমাকে নামিয়ে দাও। তখন সে অনিচ্ছাসত্ত্বে আমাকে নিতে বাধ্য হইল। কিন্তু তাকে নিয়ে খুব দ্রুত যখন চলে আসছি তখন হাইকোর্টের মোরে এসে দেখি আর রিকশা যাবে না। রিকশাওয়ালা কয় এখন স্যার নামেন, আর তো রিক্সা যাবে না। আমি রিকশা রেখে চলে গেলাম, সে পাগলের মতো চিৎকার করছে, আমি আর সে এবং রাস্তায় আর কেউ নাই তো এবং আবদুল গণি রোডের মাথার ঐ মোড়টায়, ওই কোনাটায় আইসা দেখি বড় কতগুলি গাছ মুক্তিযোদ্ধারা কেটে রাস্তায় ফেলে রেখেছে এবং ঐ রাস্তার সমস্ত বড় বড় গাছই কাটা হয়ে গেছে, সন্ধ্যা থেকে এবং কোনো গাড়ি ওদিক থেকে যেতে পারে না। গাড়ি তো পারেই না, রিকশাও পারে না। ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছে সাধারণ লোক, যে আক্রমণ হবে, আক্রমণ হলে যেন তারা আসতে না পারে। তো এই অবস্থার মধ্যে আমার রিকশাওয়ালা আমাকে বলছে—আপনি নেমে যান, না গেলে আমি রিকশাসহ রেখে রওনা দিলাম। আর আপনে যদি নামেন তাহলে আমি ঘুরে যাবো, অন্য দিক থেকে। তো আমি ওকে রিকোয়েস্ট করলাম যে তুমি পিছিয়ে আমাকে প্রেসক্লাবে নামিয়ে দাও। আমি ওখানে নেমে যাবো। তো প্রেসক্লাবে নেমে আমার পকেটে ১০/১২টা টাকা ছিল, ওকে দিলাম। প্রেসক্লাবে আমাদের ‘খয়ের’ বলে একজন পিয়ন ছিল, তখন সোয়া এগারোটা, আমি নামলাম এবং গিয়ে আমি তাকে বললাম যে—আমাকে আশ্রয় দাও। তখন সে আমাকে দোতলায় নিয়ে বাহির দিক থেকে তালা দিয়ে চলে গেল। খুব চালাক ছেলে, কিন্তু সে ভাবতে পারে নাই যে এখানে বিপদ হবে। এইটার উপর যে গুলি হবে, এই রুমে, এটা সে ভাবে নাই।
তো ঐখানে আমি ছিলাম। নিঝুম অবস্থা, হঠাৎ গুলির আওয়াজ সাড়ে এগারোটার দিকে। অনেক দূরে। আমি তখন ঐ ঘরে অন্ধকারের মধ্যে একা, সাড়ে এগারোটা থেকে। ১২টার দিকে হঠাৎ চারিদিক থেকে আগুন—কাছে—এবং গুলির আওয়াজ, চারিদিকে, ওল্ড টাউনের মুখে গুলি হচ্ছে—ঐ নবাবপুরে মুখে রেললাইন ছিল তখন, রেললাইনের গায়ে যে বস্তি ঐ বস্তিতে গুলি হচ্ছে, তাদের মাইরা ফালাইছে, বস্তির লোক সব মারা গেলো তো। রেললাইনের উপরে বস্তি ছিল, কয়েক হাজার লোক থাকত। তখন তো ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশন ছিল। নারায়ণগঞ্জ থেকে যে রেললাইনটা আসলো, ঐ ফুলবাড়িয়ায় রেলস্টেশনে আসলো; তো ঐ রেলের লাইনের উপরে কয়েক হাজার লোক আশ্রয় নিয়েছিল। আগে থেকেই ওইখানে ঝুপড়ি করে থাকতো। ঐ বস্তিতে আগুন দিয়ে দেয়, গুলি করে সবাইকে মেরে ফেলে। একেবারে কাছে, আমার চারিদিকে গুলির আওয়াজ পাচ্ছি।
এই অবস্থায় প্রেসক্লাবের দোতলায় একটা রুমে আমি একা, আর সব রুম খালি, তখন এমনিই আমার ভয় করছিল। প্রেসক্লাব তখনো আক্রমণ করে নাই। আমি পরে জানলা–দু’টো অপারেশনাল রুট ছিল আর্মির, একটা অপারেশনাল রুট হচ্ছে ঢাকা ক্লাবের সামনে দিয়ে এসে ফরেন অফিস যেটা এখন, এই ফরেন অফিসটার ভিতরে তারা ১৫/২০টা ট্যাংক রেখেছিল। আরেকটা রুট হচ্ছে ঢাকা ক্লাবের পিছন দিক থেকে, শাহবাগের পিছন দিক থেকে রাস্তাটা এসে ঐ আউটার সার্কুলার রোড দিয়ে ওল্ড টাউনে ঢুকেছে।
তো বারোটার দিকে শুনি ধর-ধর, মার-মার, চিৎকার, গুলির শব্দ। রাজার বাগ পুলিশ লাইনে তারা আক্রমণ করেছে। তারপরে শুনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির দিকে কোলাহল। পরে আরো দূরে, পশ্চিম দিকে গুলির শব্দ, ওইটা পিলখানায়। পিল অর্থ হাতি, মোগলদের হাতি থাকতো ওইখানে। সমস্ত জায়গায় শব্দ, আলো প্রেসক্লাবে বসে আমি পাচ্ছি। আমি অনুমান করতে পারছি কোনটা কোথায়, পরে দেখলাম আমি কারেক্ট। আমি একা, রুমে ছুটাছুটি করছি, কোন দিকে যাবো, কী করবো আমি তো জানি না, কিছুই জানি না। বাইর দিক থেকে তালা মারা, আমি তো বের হতে পারবো না।
রাত দু’টা পর্যন্ত চললো এই আওয়াজ, দু’টোর পরে ওল্ড টাউনে হঠাৎ শুনি আজানের আওয়াজ, আজান কেন? আজান হচ্ছে কারণ যারা গলিতে, বাড়িতে আছে তারা আজান দিয়ে বলছে—আমরা মুসলমান, তোমরা হিন্দু মারতে আসছো, অন্য জায়গায় হিন্দু, এই জায়গায় হিন্দু নাই। আজান দিয়া তারা প্রমাণ করলো।
এমন সময় হঠাৎ আমি দেখি—চামেলী হাউজ আছে প্রেসক্লাবের বাঁ দিকে, ১৯০৫-এ পার্টিশানের পরে এ বাড়িটি তৈরি করা হয়, অনেক বাড়ি তৈরি করা হয় ঢাকায়। এইটাও তৈরি করা হয়, সরকারি অফিসারের জন্য। তো ওই বাড়িতে হঠাৎ দেখি জানালার ফাঁক দিয়ে যে একটা ট্যাংক। কথাবার্তা শুনে আমি তাকাই। তখন আমি ক্লিয়ার হয়ে যাই যে এই ট্যাংকটাই প্রেসক্লাব আক্রমণ করবে। এবং ট্যাংকের কামানের নলটা প্রেসক্লাবের দিকে, পশ্চিম দিক থেকে, আর আমিও প্রেসক্লাবের পশ্চিম দিকের লাস্ট রুমে, আমার রুমেই আসতে হবে গুলি। উপায় নাই, তখন আমি অস্থির হয়ে গেলাম আরো—এখন তো আমি আক্রমণে পড়লাম! এই কথা ভাইবা যখন আমি রুমের এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছি তখন প্রথম গুলি আসে, কামানের গোলা আসলো। রুমের পশ্চিম দিকের যে দেওয়াল সেটা সম্পূর্ণটা ভেঙে, অনেকখানি জায়গা ভেঙে এসে আমার উপরে পড়লো। এই যে আমার উরুতে এসে লাগে প্রথম গুলিটাই। নিচের দিকে, একটু উপরের দিকে যদি পড়ে তাইলে তো আমি আর নাই। রক্ত পড়তেছে। আমার যদ্দূর মনে আছে, ট্যাংকের নাম হচ্ছে এম-২৪। ওদের ওইখানে তো আলো ছিলো, আমার এইখানে অন্ধকার, আমি সেই আলোতে দেখলাম। আমি জানালার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, ছোট ট্যাংক—এম-২৪, গলি-গালিতে ঢুকতে পারে যেন। তো প্রথম গুলিতেই আমি পড়ে গেলাম, এইরকম তিনটা গোলা তারা ছাড়লো প্রেসক্লাবে। তিনটাই প্রেসক্লাবে আছে এখনো, খোসাগুলি আছে। তিনটার পরে তারা বন্ধ করলো, চিৎকার নাই, কোলাহল নাই। তারপর তারা ওই জায়গাটা ছাড়লো, দেখলাম শুয়ে শুয়ে। মাথা উঁচু করলেই তো দেখা যায়। তারপরে—কতক্ষণ পরে আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। আমি অজ্ঞান হয়েই ছিলাম ঘণ্টা দুই-আড়াই। এবং ভোর প্রায় সাড়ে পাঁচটা-ছয়টার দিকে আমার জ্ঞান ফেরে। আমি মনে করছি আমি মইরা গেছি, জ্ঞান ফেরার পরে দেখলাম আমি জীবিত! তখন ব্যথা-ট্যথা কমছে, রক্ত পড়া কমে গেছে। তখন আমি বাথরুমের ভিতর দিয়া বের হইয়া, একটা গাছ ছিলো—পেয়ারা গাছ, সেই গাছ বেয়ে আমি নাইমা গেলাম। নিচে নাইমা প্রেসক্লাবের ডাইনিং রুমে আসলাম, শুইয়া রইলাম, ওইখানে রক্ত পড়লো অনেক। প্রেসক্লাবের গা দিয়া, উল্টা দিকে, সেক্রেটারিয়েটের পিছনে এখন যে বড় রাস্তাটা ওইটা তখন ছিল একটা পায়ে হাঁটা রাস্তা, পাশে খালের মতো ছিল, সাইডে ছিলো একটা বড় পুকুর, এখন ওগুলি নাই। আমি প্রেসক্লাব থেকেই দেখলাম ওইখানে অনেক লোক আশ্রয় নিছে। আমি জানি এই ট্যাকটিকটা যে যেখানে আক্রমণ হয় সেখানে পরে, ভোরের সময় সোলজাররা আবার আসে, দেখতে আসে কী করলো এবং কে কে জীবিত আছে, তাদের মারে। এইটা আমি পড়াশুনা কইরা জানি। সুতরাং আমি ওইদিকে উইঠা গেলাম, উইঠা ল্যাংড়াইয়া ল্যাংড়াইয়া খালের পাড়ে ওই লোকগুলার কাছে গেলাম। ওইখানে ৫০/৬০জন লোক ছিলো—দোকানদার, হকার, রিকশাওয়ালা—এরা। তারা বললো, স্যার, আমরা বুঝতে পারছি, রাতের বেলা গুলি হইছে, সেই গুলিতে আহত হইছেন আপনি। তারা চৌকির নিচে রাখলো আমাকে, দেখা যেন না যায়। কতক্ষণ পরে আইসা বললো—আমরা চইলা যাবো, আপনি কী করবেন? তখন নয়টা। আমি বললাম, আমাকে তোমরা সেক্রেটারিয়েটের ভিতরে নামাইয়া দাও। সেক্রেটারিয়েটের ভিতরে মসজিদ আছে, মসজিদটার গা দিয়া, বাইরের দিকে কয়েকটা বড় বড় গাছ আছে, আমাকে ওই গাছে উঠাইয়া দিল দুই-তিনটা ছেলে, আমি মসজিদে যাইয়া নামলাম। ওইখানে প্রায় ৫০/৬০ টা কনস্টেবল পুলিশ পাওয়া গেল, ওরা আমার সাথে কথা-বার্তা কইলো। আমি সব মিছা কথা কইলাম, আমি সাংবাদিক আর বলি নাই। বললে ঘটনা-রটনা হবে তাড়াতাড়ি। সেইজন্য বললাম যে আমার ভাই আছে হলে, তাকে দেখতে আইছিলাম, আইসা বিপদে পড়ছি।
তো তারা আমাকে সেক্রেটারিয়েটের প্রথম গেটের কাছে যে ১৩ তলা আছে, এইটায় নিয়া গেল। সমস্ত রুম বন্ধ, ১ তারিখ থেকে বন্ধ তো, অসহযোগ আন্দোলন। উঠতে উঠতে ছয়তলাতে একটা রুম খোলা পাওয়া গেল। ওই রুমটাতে ওরা আমাকে রাইখা দিল, খ্যাতা-ট্যাতা আইনা দিল, বালিশ দিল, ২৬ তারিখ সারাদিন আমি ওইখানে ছিলাম, রাতেও ওইখানেই ছিলাম। আহত অবস্থায়, না-খাওয়া। ২৫ তারিখ দুপুর বেলায় আমি খাইছি। ২৫ তারিখ তো সারারাত আর খাই নাই, ২৫ তারিখ তো গুলি খাইলাম, ২৬ তারিখ সকালে এইখানে আসলাম, এইখানে খাদ্য নাই। সুতরাং তারা আমাকে আদর-যত্ন কইরা রাখলো, কিন্তু খাইতে দিতে পারলো না। খাওয়ার নামই নিল না, আর নাই-ও। তারা কোত্থেকে দেবে, তারা তো এক বেলা খাবার নিয়া আইছিল। এরা হচ্ছে—প্রতিদিন রাতের বেলা এক্সট্রা ৫০ জন কনস্টেবল সেক্রেটারিয়েটে আসে, তাদের ডিউটি, তারা আবার ভোরে চইলা যায়। তো এই ২৬ তারিখ রাতের বেলা আমি ছাদের উপর উইঠা কোথায় কোথায় গুলি হইতেছে—তখন কার্ফ্যু চলতেছে, তুইলা নেয় নাই কিন্তু। ওরাও ছিলো, ওদের সাথে; ওরা আমাকে বললো—স্যার চিন্তা কইরেন না, আমাদের বন্দুকে যতক্ষণ গুলি আছে, আমরা গোলাগুলি কইরা—আমরা হত্যা কইরা তারপরে হত্যা হবো, আমরা গুলি করবোই, এই গেট ভাঙলেই আমরা গুলি কইরা দেবো। যুদ্ধ হবে, এই যে আমরা রেডি—দ্যাখেন।
২৭ তারিখ সকাল বেলা একটা ছেলে দৌড়াইয়া আইসা বললো, সানি তার নাম, কার্ফ্যু উইথড্র হইছে। ওই প্রথম খবরটা দেয়। মোতালেব কন্ট্রাক্টর বলে এক বিখ্যাত কন্ট্রাক্টর ছিল। সেক্রেটারিয়েটে তার কাজকর্ম হয় রেগুলার, ওইখানে তার জিনিসপত্র আছে, কাঠ আছে, টিন আছে, কর্মচারি আছে; সানি হইলো তার একটা কর্মচারি। তো ১০টার দিকে আমরা বের হইলাম, ১ নম্বর গেট দিয়া, পিছন দিকে, যেদিকে ওসমানী মিলনায়তন—ওই দিক দিয়া। বাইরাইয়া আইসা রাস্তার উপরে, এক রিকশাওয়ালা ঘুমাইতেছিল, ওই রিকশায় আমাকে তুইলা দেওয়া হয়। আমি আমার বন্ধুর বাড়িতে যাই, তোপখানা রোডে মুকুলের বাড়ি। ওইখান থেকে হলিডে’র এডিটর এনায়েতুল্লাহ খান আমাকে নিয়া যায় ধানমণ্ডিতে, এক ডাক্তারের কাছে। নিউ মার্কেটের উল্টা দিকে হকার্স মার্কেটের পিছনে পলি ক্লিনিক বলে একটা ক্লিনিক ছিল। এই ডাক্তারের নাম ডাক্তার আজিজ, ডাক্তার আজিজ জিয়া সরকারের মন্ত্রী হইছিলো। তার বউও ডাক্তার—ডাক্তার সুলাতানা। তারা আমার চিকিৎসা করে। আমার আহত পায়ের চিকিৎসার সময় ৫/৬ জন মেয়ে দাঁড়িয়েছিল পাশে, নার্সের পোশাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম—এরা এইখানে কেন? ডাক্তার আজিজ বললো, কারণ আছে। ওই যে লম্বা মেয়েটা দেখছেন—উনি কাজী জাফরের বউ, বাকিরাও সবাই আশ্রিতা। আর্মির রেইড হলে যাতে ধরা না পড়ে সে কারণেই এই নার্সের পোশাকে রাখা।
[অনুলিখন। আগামী পর্বে সমাপ্য।]
—
http://arts.bdnews24.com/?p=3562
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:৩৯582857
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:৩৯582857- দূরের সংবাদপত্রে বাংলাদেশ ১৯৭১
আন্দালিব রাশদী | ১৬ december ২০১০ ১২:১২ পূর্বাহ্ন
________________________________________
জয়েন্ট কমাণ্ডের প্রধানের নিকট জেনারেল নিয়াজীর আত্মসমর্পণ
[১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবাদ-মাধ্যমে এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন রিপোর্ট বা সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। এগুলো পরে ভারতের ‘বাংলাদেশ ডকুমেন্ট’ এবং বাংলাদেশের ‘মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র’-এ একত্রে প্রকাশিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এরকম কিছু রিপোর্ট ও সম্পাদকীয়-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। আন্দালিব রাশদী ভারতের ‘বাংলাদেশ ডকুমেন্ট’ এবং বাংলাদেশের ‘মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র’ থেকে এগুলো নির্বাচন ও অনুবাদ করেছেন।-বি.স.]
এএফপি’র একটি প্রতিবেদন যা প্রচারিত হয়নি
পিকিং, নভেম্বর ১৫,১৯৭১ (এএফপি)
বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, চীন স্পষ্টভাবে এবং উপর্যুপরি পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিযেছে যে, ভারতীয় উপমহাদেশে যুদ্ধ বেঁধে যাক—এটা চীন চায় না।
উৎস জানাচ্ছে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ঝুঁকির বিষয়টি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার দূত জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং সেনাবাহিনীর তিন প্রধানকে এক সপ্তাহ আগের একটি বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই এবং অন্যান্য চীনা নেতারা অবহিত করেছেন।
বিশেষ করে তিন জন পাকিস্তানী কমান্ডারের সঙ্গে আলোচনার সময় চীনারা ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য জোর দিয়েছে। এই পাকিস্তানীদের তিন দিনের পিকিং সফরের সময় ভারপ্রাপ্ত চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী চি পেং ফি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ‘ভারতের অমার্জনীয় হস্তক্ষেপ’-এর নিন্দা করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন যে, দুই দেশের মধ্যকার বিরোধ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা উচিত, যুদ্ধের মাধ্যমে নয়।
ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বে চীনাদের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করে বলা হয়, ভুট্টোর সফরের ফলশ্রুতিতে কোন যৌথ ইশতেহার প্রকাশিত হয়নি, এর বিপরীতে ভারতের প্রতি সোভিয়েত প্রতিশ্রুতি ব্যাপক প্রচারণা পায়।
চীনের সরকারি সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া গত সপ্তাহে ভারত সম্পর্কে মন্তব্য করে আগের সাত মাসে পূর্ব ভারতের সম্প্রসারণবাদ নীতিকে নিন্দা করা হয়েছিল।
ভারত-পাকিস্তান সমস্যায় চীনের কৌশলগত অবস্থানের পেছনে কুটনৈতিক সূত্র মতে চারটি কারণ রয়েছে:
১. চীন দেখাতে চায় যে জাতিসংঘে দেশটির অন্তর্ভূক্তির ফলে এই বিশ্ব সংস্থাটি আরও দক্ষ হয়ে উঠেছে।
২. চৌ এন লাই-এর কুটনৈতিক পরিকল্পনা হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে (দক্ষিণ এশিয়াও) দুটি পরাশক্তির দ্বন্দ্ব বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের হাত থেকে রক্ষা করা।
৩. ভারতের সঙ্গে আঁতাত সৃষ্টির সুযোগ নষ্ট হয়—এমন পদক্ষেপ নেয়ার প্রশ্নে পিকিং অনাগ্রহী থাকবে। জাতিসংঘে চীনের অন্তর্ভূক্তির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী চৌ এবং ইন্দিরা টেলিগ্রাম বিনিময় করেছেন। মিসেস গান্ধী বলেছেন, বিশ্ব সংস্থায় তিনি চীনের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন এবং চৌ এন লাই বলেছেন চীন ও ভারতের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি পিকিং-এ অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টে চীন ভারতীয় দলকে স্বাগত জানিয়েছে এবং গত ১৫ বছরের মধ্যে এই প্রথম দুজন ভারতীয় সাংবাদিককে চীন আমন্ত্রণ জানিয়েছে।
৪. স্বাধীন বাংলাদেশ না চীনের স্বার্থ, না চীনের আদর্শ—কোনটাই রক্ষা করবে না।
চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের মৈত্রীর সম্পর্ক এতে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ভারসাম্য ওলটপালট হয়ে যাবে।
ভুট্টোর সফরের সময় চি পেং ফি তাঁর ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের গালমন্দ করেন এবং বলেন, কেবলমাত্র পাকিস্তানী জনগণই যুক্তিযুক্ত পথে পুর্ব পাকিস্তান সমস্যার নিষ্পত্তি করবে।
এই ভাষণে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার সমাধানে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ববাদী হস্তক্ষেপের প্রতি সমর্থন জানানো হয়নি।
মুজিবের রাষ্ট্রদ্রোহের প্রকৃতি
দ্য সানডে টাইমস, জাম্বিয়া ২২ আগস্ট ১৯৭১
১১ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার শুরু হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছে। পাকিস্তানের শুরু থেকেই রাষ্ট্রদ্রোহের ধরণ ও ইতিহাস বোঝা প্রয়োজন।
…১৯৬৬ সালে যখন মুজিবুর স্বায়ত্তশাসনের জন্য ছয় দফা ঘোষণা করলেন—যার ওপর ভিত্তি করে গত নির্বাচনে তার নিরঙ্কুশ বিজয় ঘটল—তখনই তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানো হল। সরকারের সমর্থনপুষ্ট সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলে তাদের উদ্ভাবিত অভিযোগ এক সময় ঝেড়ে ফেলতে হয়।
স্বায়ত্তশাসনে দাবি জানানো নতুন কিছু নয়। এমনকি পাকিস্তানের ভিত্তি হিসেবে খ্যাত লাহোর প্রস্তাব, যার খসড়া জিন্নাহ নিজেই প্রণয়ন করেছিলেন, তাতে বলা হয়েছে, ভারতকে এমনভাবে ভাগ করতে হবে—পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিমে মুসলিম সংখ্যাগিরষ্ঠ অংশে একের অধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে যার ইউনিট গুলো হবে স্ব-শাসিত ও স্বায়ত্তশাসিত। কিন্তু পূর্বাঞ্চলীয় ইউনিট রাষ্ট্র হয়ে উঠতে পারেনি। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকরা পূর্বাঞ্চলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রাধান্য বিস্তার করে শাসন করে গেছে।
কিন্তু পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ১৯৭০ সালে মুজিব ও তার দলকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগিরষ্ঠতায় বিজয়ী করে নিয়ে আসে।
তারপর গণহত্যা শুরু হয়, মুজিব আবার বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত হন। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে—লাহোর প্রস্তাবে যে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছে, মুজিবের ছয় দফায় তাও চাওয়া হয়নি। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয় দিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন।…
২৬ মার্চ ১৯৭১
সানডে পোস্ট, নাইরোবি
ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশ পরিস্থিতি
শরণার্থী সামাল দেয়া এবং শরণার্থীর কারণে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক যে হুমকি তা মোকাবেলা করতে যতটুকু প্রয়োজন পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ওইটুকুই। যেসব প্রচারণা শুরু হয়েছে তা যদি বিশ্বাস করতে হয়, মনে হবে বাস্তুচ্যুত শরণার্থীদের ভারতের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের খাঁচায় পুরে রাখা হয়েছে এবং বলপূর্বক তাদের দেশে ফিরে যাওয়া ঠেকিয়ে রাখা হচ্ছে।
এই শরণার্থী শিবিরগুলো উন্মুক্ত ও স্বাধীন। কেউ যদি শিবির ছেড়ে চলে যেতে চায়, চলে যাবে। কোন বাধা বা নিষেধ নেই।
যে কুটচালের বাহুল্যে এসব কথা বলা হচ্ছে তাতে শরণার্থীর সংখ্যা এত বেশি হওয়ার কথা নয়। একটি পরিসংখ্যানের সূত্র মতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিশ থেকে পঁচিশ লক্ষ লোক চলে গেছে।ইয়াহিয়া খান একজন সাংবাদিকের কাছে স্বীকার করেছেন শরণার্থীর সংখ্যা ত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ হতে পারে, আশি বা নব্বই লক্ষ—অসম্ভব। বিবিসির একটি অনুসন্ধানী ধারাভাষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা ফিরে আসছে তাদের তিন থেকে চার বার পরীক্ষা করা হচ্ছে যেন প্রকৃত বাস্তুচ্যুতই কেবল ঢুকতে পারে, কোন প্রতারক নয়।
ধারাভাষ্যে আরও বলা হয়, সব শরণার্থীর অবস্থান শিবিরে নয়; শিবিরে আছে কেবল যারা দরিদ্রতম এবং সবচেয়ে অসহায়। পূর্ব পাকিস্তানের অনেকেই আশ্রয় পেয়েছে কলকাতাও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে।
তাদের প্রকৃত সংখ্যা কখনোই রেকর্ড করা হয়নি। সবাই ফিরে যেতে চায়। কিন্তু পৃথিবীর সামনে যে বিশাল ট্র্যাজেডি তা হচ্ছে কেউ কেউ মনে করছেন নব্বই লক্ষ মানুষ কোন বোঝাই নয়—যে দেশে নিজেদের জনসংখ্যা বাড়ে বছরে এক কোটি বিশ লক্ষ। এই নব্বই লক্ষ্যের দায় রাষ্ট্রের। আর এ সময় যেসব সন্তান জন্ম গ্রহণ করছে তার দায় সন্তানের পিতা-মাতার।
(২২ নভেম্বর ১৯৭১ প্রকাশিত)
মাইনিচি ডেইলি নিউজ, টোকিও
সম্পাদকীয়
পূর্ব পাস্তিানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসা পর্যন্ত শরণার্থী সমস্যা সমাধানের কোন সুযোগ নেই। যুদ্ধের বিপজ্জনক আশঙ্কার কথাও উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। ইয়াহিয়া খান সরকার বেসামরিক সরকার পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপ নিচ্ছে। কিন্তু এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েই গেছে। খাদ্যের ঘাটতি রয়ে গেছে। জাপানসহ অন্যান্য দাতাদেশ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আনা পর্যন্ত পাকিস্তানকে সাহায্য দেয়া স্থগিত রেখেছে। আশা করা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করে যত শীঘ্র সম্ভব সাহায্য প্রবাহ পুনরায় চালু করাতে পাকিস্তান সচেষ্ট হবে।
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি মেনে চলে। কিন্তু শরণার্থীদের ট্র্যাজিক অবস্থা এবং পাকিস্তান যে সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তাতে কারও পক্ষে নির্বিকার থাকা সম্ভব নয়। বিষয়টি নিয়ে সমস্ত মানবাজাতিরই ভাবা উচিত। এখন জাতিসংঘের অধিবেশন চলছে, বিষয়গুলো উত্থাপনের এটাই সঠিক ফোরাম বলে মনে হচ্ছে।
(৩ অক্টোবর ১৯৭১ প্রকাশিত)
দ্য বাল্টিমোর সান
ভয়ই পূর্ব পাকিস্তানে একমাত্র আইন
পাটকলের এক যুবক সুপারিনটেনডেন্ট বলল মাত্র ক’ঘন্টা আগে তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। সেনাবাহিনী গ্রামে ঢোকার পর গ্রামটা জ্বালিয়ে দিয়েছে, এক তরুণ গ্র্যাজুয়েটকে হত্যা করেছে। সেনাবাহিনী কেন এসেছে তাঁর জানা নেই। রাস্তা ধরে আরও এগোবার পর দেখা গেল ছটা গ্রাম পুড়িয়েছে। গেরিলা তৎপরতার প্রতিশোধ হিসেবে ক’জন গ্রামাবাসীকেও হত্যা করেছে।
যখন জিজ্ঞেস করা হল কাজটা ভুলে মুক্তিবাহিনীই করেছে কিনা একথা শোনার পর যেন ব্যক্তিগতভাবে অপমানিত বোধ করেছে—এভাবে এগিয়ে এলো সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং একজন স্কুল শিক্ষক।
‘না স্যার, না। পাকবাহিনী, ওরা পাকবাহিনী, পাক বাহিনী।’
পাটকলের সুপারিনটেনডেন্ট বলল, আমাকে পালাতে হয়েছে কারণ সেনাবাহিনী সব শিক্ষিত লোকদের মেরে ফেলছে। যাতে কেউ আর নেতৃত্ব দিতে না পারে। স্কুল শিক্ষক তাঁর কথায় সায় দেয়।
একমত ঢাকার কুটনীতিবিদরাও—যারা সেনাবাহিনীর নির্যাতনের সাক্ষ্য সংগ্রহ করছেন। তারাও মনে করেন দেশের অধ্যাপক, ডাক্তার, আইনজীবী, ছাত্র ও অন্যান্য শিক্ষিত মানুষকে পদ্ধতিগত হত্যা করা হচ্ছে কিংবা কারাগারে নিক্ষেপ করা হচ্ছে।
(১৩ নভেম্বর ১৯৭১ প্রকাশিত)
—-
http://arts.bdnews24.com/?p=3273
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:৪৮582858
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:৪৮582858- ধর্ষিত বাংলাদেশ: মানবেতিহাসের কৃষ্ণতম অধ্যায়
আহমেদ মাখদুম
| ২২ december ২০০৯ ৬:২৩ অপরাহ্ন
অনুবাদ: মফিদুল হক
_______________________________________
১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর নয় মাসব্যাপী গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিয়ে পরিসমাপ্ত হয় কাপুরুষতা ও অমানবিকতার চরম নৃশংস ও রোমহর্ষক, কলঙ্কময় ও ন্যাক্কারজনক, অসম্মান ও অপমানকর, মসীলিপ্ত ও কুখ্যাত অধ্যায়। এই দিন বর্বর, পাশবিক ও নৃশংস পাকিস্তান সেনাবাহিনী—উর্দি-পরিহিত ৯৬,০০০ পশু—আত্মসমর্পণ করে ভারতীয় বাহিনীর কাছে। এর পূর্ববর্তী নয় মাসের সন্ত্রাস, পীড়ন ও স্বৈরাচার মানবতার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে চিহ্নিত হবে সবচেয়ে কৃষ্ণ অধ্যায় হিসেবে।
এবং আমি আমার এই পাপী চোখে দেখেছি বঙ্গকন্যার ধর্ষণ, আমার আঙিনায় ঘটেছে অপাপবিদ্ধ বঙ্গসন্তানদের হত্যাযজ্ঞ, আর আমি বেঁচে আছি দুনিয়াবাসীকে বলতে যা আমি দেখেছি!
—————————————————————–
আমি যখন গোপন অবস্থান থেকে বের হয়ে আসি ততদিনে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। আমার বাঙালি বন্ধুরা আমাকে সাহায্য করে, আশ্রয় ও আহার যোগায়, যত্ন-আত্তি নেয় এবং ভালোবাসা, প্রীতি ও করুণায় সিক্ত করে। তাঁরা আমার সিঙ্গাপুর যাওয়ার বিমান-ভাড়ার ব্যবস্থা করে দেয়, যেখানে আমি নতুন জীবন শুরু করি, উন্মোচিত হয় জীবনের আরেক অধ্যায়, আমার মাতৃভূমি আমার পিতৃভূমি সিন্ধু থেকে বহু বহু যোজন দূরে। এরপর চল্লিশ বছর ধরে সিঙ্গাপুর হয়ে আছে আমার আবাস এবং বাঙালি বন্ধুরা আমার হৃদয়, মন ও আত্মায় গড়ে তুলেছে আরেক আবাস, যতদিন বেঁচে থাকি তা আমি লালন করে চলবো।
—————————————————————-
২০০৯ সালের ৭ নভেম্বর শনিবার আমি ছিলাম লন্ডনে, যোগ দিয়েছিলাম সেখানকার আইরিশ কালচারাল সেন্টার আয়োজিত অনুষ্ঠানে, যেখানে সমবেত হয়েছিল বিশ্বের নানা দেশের স্বৈরশাসন-পীড়িত, নির্যাতিত, অত্যাচারিত ও সন্ত্রস্ত মানবতার প্রতিনিধি। সিন্ধুর এক অধম সন্তান হিসেবে আমিও ছিলাম সেই সমাবেশে, সঙ্গে ছিল আমার বোন চিরসবুজ সংগ্রামী সুরাইয়া এবং সিন্ধি টুপি পরিহিত গর্বিত নিবেদিত ব্যক্তি শাহ আচার বুঝদার।
সেখানে হাজির ছিল প্যালেস্টাইনি, ইরাকি, তুরস্ক ও ইরাক থেকে আগত কুর্দি, মরক্কোর পোলিসারিও এবং বাংলাদেশের বাঙালি। তুরস্কের কুর্দিদের একটি দল তাঁদের ঐতিহ্যবাহী গীত ও বাদন দ্বারা সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। মানবাধিকার ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত, সচেষ্ট, আত্মোৎসর্গকৃত বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিরা তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেছিল। আমারও সুযোগ হয়েছিল বর্বরতার শিকার আমার মাতৃভূমি ও পিতৃভূমি সিন্ধুর কথা বলবার, খোদাহীন, সাহসহীন, বোধহীন দেশ পাকিস্তানের শকুন, হায়েনা ও যুদ্ধবাজদের দ্বারা যে-ভূমি আজ লাঞ্ছিত।
আমি কোনো গায়ক নই, তবুও এক আইরিশ যুবা ও অপর এক কুর্দি তরুণীর গান এবং তুর্কি বাদনদলের সুরলহরী শুনে এতোটা অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম যে মঞ্চে এসে বেসুরো গলায় সিন্ধুর একটি গান গাইলাম। গান করলাম আমার মাতৃভূমির মিষ্টি ভাষা সিন্ধিতে:
‘হে প্রিয় হে বন্ধু আমার, তোমার আশীর্বাদে সম্পদে ভরে উঠুক আমার সিন্ধুদেশ/ হে আমার ভালোবাসার ধন, তোমার করুণায় সিঞ্চিত হোক নিখিল ভুবন।’
গানের পর মধ্যবয়সী সুদর্শন এক বাঙালি ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমাকে আলিঙ্গন করলেন, জানতে চাইলেন উনিশ শ একাত্তর সালে আমি কোথায় ছিলাম। আমি তাঁকে যা বলেছিলাম সেটাই এখানে পুনর্ব্যক্ত করছি।
১৯৬৪ সালে আমি চট্টগ্রামের জলদিয়া মেরিন একাডেমীতে ভর্তি হই দু-বছরের নৌবিদ্যা কোর্স সম্পন্ন করার জন্য। একাডেমীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যাচের ছাত্রদের মধ্যে আমরা তিনজন ছিলাম সিন্ধি। আলতাফ শেখ পরে চিফ ইঞ্জিনিয়ার হয়েছিলেন এবং সিন্ধি ভ্রমণসাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন, বশির ভিসত্রো মাস্টার মেরিনার হয়েছিলেন এবং করাচির একটি জাহাজ কোম্পানিতে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন, আর তৃতীয় জন ছিলাম আমি।
আমাদের কয়েকজন বাঙালি বন্ধু ছিল, ঢাকা ও চট্টগ্রামে তাঁদের বাসায় আমাদের যাওয়া হতো এবং পরিচিত ছিলাম বাড়ির লোকজনের সঙ্গে। এইসব মার্জিত, সংস্কৃতিমনা, সাহিত্যবোধ-সম্পন্ন, ভদ্র, সজ্জন ও প্রিয়ভাষী বাঙালিদের সঙ্গে আমাদের আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমরা সিন্ধিরা ছিলাম তাঁদের পরিবারের সদস্যের মতো, পেয়েছিলাম অশেষ ভালোবাসা, প্রীতি ও সম্মান। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল ঢাকার নূরুল আমিন। তাঁরা ছিল সাত ভাই ও এক বোন, ছোট্ট এই বোন, মিষ্টি চেহারার সুকণ্ঠধারিণী দ্বাদশ-বর্ষিয়া চন্দ্রমুখী মেয়েটিকে সবাই ডাকতো ‘চম্পা’, তার ঝুটি-বাঁধা লম্বা চুলে গোঁজা থাকতো ফুল। কী অসাধারণ প্রতিভাবান ছোট্ট দেবশিশুই না ছিল সে! গান গাইতো হারমোনিয়াম বাজিয়ে—প্রায় প্রতিটি বাঙালি পরিবারেই যা দেখা যায়—মিষ্টি ও সুরেলা কণ্ঠে যখন সে গান ধরতো, আমরা বিহ্বল হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম তার গান ও বাদন।
একটি বিশেষ গান আমরা বারবার শুনতে চাইতাম। আমাদের ফরমায়েশ সে কখনো অমান্য করে নি। গানটি ছিল, ‘ও সাত ভাই চম্পা জাগো রে, ঘুম ঘুম থেকো না ঘুমিয়ে রে।’ আজ অবধি আমি ভুলিনি সেই গান, ঝুটিবাঁধা চুল নিয়ে চাঁদপনা বালিকা মধুরকণ্ঠে গাইছে, ‘ও সাত ভাই চম্পা।’
১৯৭১ সালে জাহাজে কাজ করবার সূত্রে আমি এসেছিলাম চট্টগ্রামে, রোটারডাম ও অ্যান্টওয়ার্প বন্দরের জন্য পাট বোঝাই করছিলাম জাহাজে। হঠাৎ চারপাশে শুনি ঘোলাগুলির শব্দ। আমার বিশেষ বন্ধু বাঙালি সেকেন্ড অফিসার ও অপর এক বাঙালি নাবিককে পাকিস্তানি পাঞ্জাবি সেনাবাহিনীর উর্দি পরিহিত জংলি, বর্বর, কাপুরুষ সদস্যরা গুলি করে হত্যা করেছিল। জাহাজের সম্মুখভাগের গুদামঘরে চারদিন কোনো দানা-পানি ছাড়া লুকিয়ে থেকে আমি প্রাণে রক্ষা পাই।
আমি যখন গোপন অবস্থান থেকে বের হয়ে আসি ততদিনে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। আমার বাঙালি বন্ধুরা আমাকে সাহায্য করে, আশ্রয় ও আহার যোগায়, যত্ন-আত্তি নেয় এবং ভালোবাসা, প্রীতি ও করুণায় সিক্ত করে। তাঁরা আমার সিঙ্গাপুর যাওয়ার বিমান-ভাড়ার ব্যবস্থা করে দেয়, যেখানে আমি নতুন জীবন শুরু করি, উন্মোচিত হয় জীবনের আরেক অধ্যায়, আমার মাতৃভূমি আমার পিতৃভূমি সিন্ধু থেকে বহু বহু যোজন দূরে। এরপর চল্লিশ বছর ধরে সিঙ্গাপুর হয়ে আছে আমার আবাস এবং বাঙালি বন্ধুরা আমার হৃদয়, মন ও আত্মায় গড়ে তুলেছে আরেক আবাস, যতদিন বেঁচে থাকি তা আমি লালন করে চলবো।
ফিরে যাই ১৯৭১ সালে। চট্টগ্রামে যা আমি দেখেছি আমার অন্তরাত্মায় তার স্থায়ী ছাপ রয়ে গেছে। ধর্ষক, বর্বর, হন্তারক পাকিস্তানি সৈন্যদের সৃষ্ট ক্ষত আমি দেখেছি, দেখেছি বাঙালির রক্তে রঞ্জিত পথ, ধর্ষণের পর ক্ষত-বিক্ষত বাঙালি নারী, নৃশংসভাবে হত্যা করা শিশু।
আমি ঢাকা যাই প্রিয় বন্ধু নূরুল আমিন ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে, বিশেষভাবে আবার শুনতে সেই মিষ্টি গান সাত ভাই চম্পা। সেখানে সব দেখে-শুনে স্রষ্টার উদ্দেশে আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম, ‘হায় খোদা, কেন, কেন এমন হবে?’ কাপুরুষ পাকিস্তান আর্মি হত্যা করেছে আমার প্রিয় বন্ধুকে, আর আমার বারো বছরের সেই মিষ্টি বোনটিকে দল-বেঁধে ধর্ষণ করেছে বর্বর পাকবাহিনী, ধর্ষণের পর হত্যা করেছে নিষ্ঠুরভাবে।
বাঙালিরা আজ স্বাধীন। অনেক মূল্য ও বিপুল আত্মদানের বিনিময়ে এসেছে এই স্বাধীনতা। তারা আজ নিজ ভাগ্যের নিয়ন্তা।
বাংলাদেশের সন্তান-সন্ততিরা, সাহসী ভ্রাতা ও ভগিনীরা, আমরা সিন্ধিরা একদা তোমাদের ভালোবেসেছিলাম, আমরা সবসময়ে তোমাদের ভালোবেসে যাবো। বাংলাদেশের জয় হোক, জয় হোক সিন্ধুর!
মুরশিদ শাহ আবদুল লতিফ ভিটাই বলেছিলেন :
‘মনে করো প্রিয়, তুমি এসেছ কাছে/ তোমার গরিমা দূরে, দূরে ঠেলে/ সব শান-শওকত সত্তার গহিনে ডুবিয়ে/ আবরণ ঘুচিয়ে মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করছো বাণী/ মনে করো প্রিয়, তুমি-আমি নতজানু এক কাতারে/ অন্তরে একই সুরধ্বনি, গাইছি যুগলে তোমারি মহিমা।’
ইমেইল:
আহমেদ মাখদুম: [email protected]
মফিদুল হক: [email protected]
______________
http://arts.bdnews24.com/?p=2605#more-2605
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:৫১582860
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:৫১582860- স্মৃতি: ষোলই-ডিসেম্বর ঊনিশ শ’ একাত্তর
রবিউল হুসাইন | ১৬ december ২০০৯ ৯:০৬ পূর্বাহ্ন
_____________________________________
কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন গত ৭ ডিসেম্বর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ঢাকার অ্যাপোলো হাসপাতালের আইসিসি ইউনিটে চিকিৎসারত। ষোলো ডিসেম্বর নিয়ে তাঁর এ লেখাটি আজ বিজয়ের দিনে পুনঃউপস্থাপিত হলো। বি. স.
________
আমার বয়স তখন ২৮ বছর। ষোলই ডিসেম্বরে লালবাগে এক বন্ধুর বাড়িতে ভাড়া থাকা কালীন আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনাটি ঘটেছিলো। ছুটে বেরিয়ে এসেছিলাম। শুনেছিলাম পাকসেনারা সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে আত্মসমর্পণ করেছে। হাজার হাজার মানুষ ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। তখন শীতকাল। পথে অসংখ্য মানুষ। শহীদ মিনারের দিকে যাচ্ছি। মুখে জয় বাংলা আর বঙ্গবন্ধুর শ্লোগান। মাঝে মাঝে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জীপ কিংবা কনভয় রাস্তায় দেখা যাচ্ছে। তাদের দেখে পথচারীরা হাততালি দিয়ে উঠছে। কেউ ফুলের মালা ছুঁড়ে দিচ্ছে, কেউ কেউ গাড়ি থামিয়ে তাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে, কোলাকুলি করছে। আমার কাছে এক প্যাকেট সিগারেট ছিলো। হঠাৎ একটি গাড়িভর্তি ভারতীয় বাহিনী এলে সেটি ছুঁড়ে দিলাম তাদের দিকে। তারা হাসতে হাসতে লুফে নিলো। অন্য পথচারীরা দৌড়ে দৌড়ে ওদের অনুসরণ করতে করতে গাড়ির পিছন থেকে হাতে হাত মিলাতে গেল।
—————————————————————–
হঠাৎ এক মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু আমার পোশাকের দিকে তাকিয়ে বেশ কড়া সুরে বলে উঠলো, খুব আরামেই ছিলে। আমরা যুদ্ধ করে মরি আর তোমরা দেখা যাচ্ছে কোট-টাই পরে বেশ আরাম-আয়েশেই ছিলে। তারপর দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে হুঁ হুঁ করে কেঁদে উঠলো, ভাঙা গলায় আবার বলে উঠলো, আমরা সত্যিই কি স্বাধীনতা পেলাম আমরা কি সত্যিই স্বাধীন হলাম, না কি স্বপ্ন দেখছি।
—————————————————————-
মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ঢাকায় ছিলাম। এতো ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে যেতে পারিনি। সেই সময় আমি কঠিন যক্ষা বা ক্ষয়কাশে ভুগছি। এটি আমার সারা জীবনের আফসোস। এর বিকল্পে এখানে থেকেই যদ্দুর পারি মুক্তিযুদ্ধের সহায়তা করার কাজে লেগে পড়েছিলাম। বুয়েট অর্থাৎ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বন্ধু-শিক্ষকের ফ্ল্যাটে ভাগাভাগি করে থাকতাম। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাও চলছিলো। স্বাধীনতার কিছু দিন আগে লালবাগের বাসা ভাড়া নিই। বুয়েটের সেই ফ্ল্যাট বাড়ির নিচতলা মুক্তিযুদ্ধের একটি গোপন ঘাঁটির মতো হয়ে পড়ে। বন্ধু মুক্তিযোদ্ধারা সেখানেই আশ্রয় নিতো। টয়লেটের ছাদে অস্ত্র জমা রাখা হতো। পরে সুবিধামতো সময়ে সেগুলো তারা নিয়ে যেতো পুরনো ঢাকার ভেতর দিয়ে বুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে এদিক সেদিক। যাতায়াতের সুবিধায় জন্যে জায়গাটা মোক্ষম ছিলো। সাতই মার্চে মাঠে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর সেই অবিস্মরণীয় ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ সেই স্বাধীনতার ডাক শুনতে পারিনি। খুব অসুস্থ ছিলাম।
সেই ডাক শুনেছিলাম রেডিওতে। সে কী দারুণ উত্তেজনা আর আশঙ্কা। সবাই বলাবলি করছিলো বঙ্গবন্ধু যদি সরাসরি স্বাধীনতার ডাক দেন তাহলে পাক সেনারা সরাসরি মাঠে বোমা ফেলবে যেমন করে তারা বেলুচিস্তানে কিছুদিন আগে ফেলেছিলো। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এমন রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদর্শী কায়দায় স্বাধীনতার ডাক দিলেন যে তাতে তাদের পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব হলো না। কিন্তু পরে রাজনৈতিকভাবে যখন কিছুতেই পেরে উঠলো না তখন পচিশে মার্চের গভীর রাত থেকে মরণ কামড় শুরু করে দিলো। এর আগে গাজীপুরে ঊনিশে মার্চে প্রথম যুদ্ধ হয় পাক সেনাদের সঙ্গে, পরে খোলাখুলিভাবে পঁচিশে মার্চ থেকে। সারা শহর হঠাৎ করে প্রকম্পিত হতে থাকলো মূহুর্মূহু কামানের গোলার আওয়াজে। চারিদিক থেকে আর্ত মানুষের চীৎকার আর গোলাগুলির অফুরন্ত শব্দ, যেন সেইদিনই পৃথিবীর শেষ দিন। আমরা ছুটে ঘরের বাইরে, কেউ সোজা ছাদে। যে দিকে তাকাই সেই দিক আগুনের লেলিহান শিখা, সম্পূর্ণ আকাশ লালে লাল হয়ে উঠেছে। সারারাত ঘুম হয়নি। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে দেখি অদ্ভুত এক দৃশ্য। সামনের রাস্তা দিয়ে দলে দলে মানুষ, সব বয়েসের ছেলে-মেয়ে বুড়ো-শিশু রিক্সায়, গাড়িতে কিংবা হেঁটে, বেশির ভাগ হেঁটে পুরনো ঢাকার দিকে চলেছে। যে যা পাচ্ছে হাতের কাছে, তাই নিয়েই তারা তাদের প্রিয় শহর ঢাকা ছেড়ে নদী পার হয়ে গ্রামের দিকে চলছে। এ যাওয়ার যেন কেনো শেষ নেই। আমার সব বন্ধু একে একে চলে যাচ্ছে। আমি অসুখের জন্যে কোথাও যেতে পারছি না। এইভাবেই নয়মাস ঢাকাতেই ছিলাম। প্রতি পদে পদে প্রতি দিন প্রতি রাত ভয়ে ভয়ে কেটেছে। এর মাঝে থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে খবর সংগ্রহ, টাকা-পয়সার জোগাড়, গরম কাপড় বাড়ি বাড়ি গিয়ে নেয়া, প্রচারপত্র বিলি, ঢাকা শহরের কিছু কিছু জায়গার ম্যাপ তৈরি ইত্যাদি ব্যাপারে সক্রিয় ছিলাম। আমরা কয়েকজন মিলে এইসব কাজ করতাম গোপন গোয়েন্দা সংস্থার মতো। সেই সময় সংসদ ভবনের কাছে একটি এতিমখানায় পাক সেনারা প্লেন থেকে বোমা ফেলে ধ্বংস করলো, অপপ্রচার চালালো যে এই কাজ দুষ্কৃতিকারী অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধারা করেছে। এরপর থেকে গভীর রাতে আকাশে কোনো প্লেনের শব্দ শুনলেই মনে হতো এই বুঝি আমাদের ঘরের ওপরই পড়লো। নয় মাসের প্রতিটি সময় এইভাবে কেটেছে। পাকিস্তানীরা তিরিশ লক্ষ নির্দোষ-নিরস্ত্র বাঙালিদের হত্যা করেছিলো। হিসেবে করলে দেখা যায় যে তারা প্রতিদিন প্রায় বারো হাজার মানুষ হত্যা করেছিলো, নয় মাস ধরে অর্থাৎ ২৬৭টি দিনে। এই সময় দুবার পাক-সেনারা আমাকে সন্দেহ করে ধরেছিলো। কিন্তু কপাল জোরে বেঁচে যাই। একবার কোট-টাই-ভালো পোশাক পরার সুবাদে আর একবার মানিব্যাগের ভেতর একটি ডাক টিকিটের আকারে পাকিস্তানী পতাকা পাওয়ার কারণে। এসব কারণে সব সময় বাধ্য হয়ে ভালো পোশাক পরে থাকতে হতো।
পঁচিশে মার্চের সময় আমি যেহেতু একেবারে একা ছিলাম এবং শহীদ মিনার কামান দিয়ে ভাঙার সময় ওই এলাকায় থাকতাম, তাই আমাকে অনেকদিন না দেখে সবাই ভেবে নিয়েছিলো আমি বোধহয় আর নেই, মারা পড়েছি। তাই সেই সময় একদিন আজিমপুর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আমার এক বন্ধু দেখে চীৎকার করে নাম ধরে ডেকে উঠে চললো, আরে তুই বেঁচে আছিস। পরে ওদের বাসায় নিয়ে গিয়ে মা-ভাই-বোনকে ডেকে একটি উৎসবের মতো আয়োজন করে ফেললো। বঙ্গবন্ধুকে পাকিনস্তানীরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। কেউ কেউ বললো, তাঁর ধরা পড়া ঠিক হয়নি। উনি ভারতে পালালেন না কেন। স্বাধীনতার ডাকও সরাসরি দিলেন না সাতই মার্চে। আর পাকিস্তানীদের অত্যাচারও তাঁর গ্রেপ্তারের কারণে থেমে থাকলো না। আসলে বঙ্গবন্ধু তো বিপ্লবী ছিলেন না যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দেশ স্বাধীন করবেন। তিনি গণতান্ত্রিক উপায়ে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার সঙ্গে ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে তার আত্মপ্রকাশ বিশ্ব মানচিত্রে বোধকরি প্রথম ও অনন্য একটি ঘটনা। এই ধারাবাহিকতার শুধু তিনি একা তৈরি করেননি, আমাদের জাতীয় নেতা শেরেবাংলা, ভাসানী, সোহরাওয়ার্দি সবাই করেছেন। তিনি শুধু নিজের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, আত্মত্যাগ আর আপসহীন সংগ্রাম এবং সাহসের কারণে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিলেন।
কেন তিনি পালাবেন, তিনি তো কোনো অন্যায় করেন নি। নির্বাচনে সংখ্যাসংরিষ্ঠ ভোট পেয়েছিলেন, সেই অনুযায়ী তিনি ক্ষমতার ন্যায়সঙ্গত দাবিদার। তা তাকে দেয়া হলো না। তাছাড়া তিনি কোথায় পালাবেন? এদেশ সমভূমির দেশ, পাহাড়-জঙ্গল এখানে নেই যে গেরিলা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করবেন। তাঁর সাতই মার্চের বক্তৃতা, ধরা পড়া সবাই তো নিয়মের মধ্যে থেকেই এক রাজনৈতিক উন্নত অবস্থার জন্যে পরিকল্পিত। ভারতে গিয়ে পালালে বা স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে সবাই বিশেষ করে আন্তর্জাতিক দেশসমূহ মনে করতো তিনি দেশদ্রোহীতা করেছেন ভারতের সঙ্গে মিলে। সেই প্রেক্ষিতে তিনি কোনোভাবেই আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতা-সহমর্মিতা বা সমর্থন পেতেন না।
চৌদ্দই ডিসেম্বরের বিকেলটা ভোলার নয়। হলিউডি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সিনেমার মতো ঢাকার আকাশে পাকিস্তানী আর ভারতীয় জঙ্গী বিমানের আকাশ-যুদ্ধ। অসম্ভব এক দৃশ্য! হঠাৎ একটি পাকিস্তানী প্লেন আঘাত পেয়ে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এবং উল্টোপুল্টি খেতে খেতে নদীর ওপারে কামরাঙ্গির চরের দিকে চলে যেতে থাকলো। মনে হলো আমাদের ছাদের ওপরেই ঘটনাটা ঘটবে। এপর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখি জাহাজের ওই অবস্থা থেকেই পাকিস্তানী পাইলট ককপিট থেকে শূন্যে উঠে প্যারাসুট মেলে দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে এবং একটু পরে বিকট এক শব্দে চারদিক কেঁপে উঠলো অর্থাৎ প্লেনটি সজোরে মাটির ওপর আছড়ে পড়ে এক কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি করলো। সিনেমাহীন এই রকম অবাক-করা দৃশ্য অনেকের সঙ্গে নিজের চোখে দেখে আমরা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলাম। রক্তের মধ্য দিয়ে এক শিহরণ বয়ে গেল। সেই রাতটি আরও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। ভারতীয় প্লেন রাতের অন্ধকারে সেনানিবাস আক্রমণ করেছিলো। সেই কারণে পাকিস্তানীরা হাউই ছুঁড়ে সারা উত্তর আকাশকে আলোকিত করে তুললো। ফট্ ফট্ আর প্লেনের সাঁই সাঁই বিকট শব্দ যেন একটি আনন্দ উৎসবের জন্যে যেন আলোর ফল্গুধারা। সে দৃশ্য ভোলা যায় না। মনে হচ্ছিলো রাতের অন্ধাকারে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন দেশের জন্মলগ্নের আলোকিত আনন্দ-উৎসব।
ষোলই ডিসেম্বরে বিকেল বেলার দিকে শহীদ মিনারের সামনের রাস্তায় অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা হাতে রাইফেল এবং রণক্লান্ত চেহারা নিয়ে সমবেত হচ্ছেন। আমরা পথের দুধারে দাঁড়িয়ে তাদের হাততালি দিয়ে এবং কোলাকুলি করে বরণ করে নিচ্ছি। চোখে আনন্দাশ্রু। হঠাৎ এক মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু আমার পোশাকের দিকে তাকিয়ে বেশ কড়া সুরে বলে উঠলো, খুব আরামেই ছিলে। আমরা যুদ্ধ করে মরি আর তোমরা দেখা যাচ্ছে কোট-টাই পরে বেশ আরাম-আয়েশেই ছিলে। তারপর দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে হুঁ হুঁ করে কেঁদে উঠলো, ভাঙা গলায় আবার বলে উঠলো, আমরা সত্যিই কি স্বাধীনতা পেলাম আমরা কি সত্যিই স্বাধীন হলাম, না কি স্বপ্ন দেখছি।
তখন চারিদিক মুক্তিযোদ্ধাদের রাইফেলের ঠা-ঠা গুলির আনন্দশব্দে প্রকম্পিত। সমবেত কণ্ঠে মাঝে মাঝে শোনা যেতে থাকলো জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধ্বনি।
[email protected]
—-
http://arts.bdnews24.com/?p=2024#more-2024
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:৫৪582861
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ১৯:৫৪582861- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : মুসলিম দেশগুলোর ভূমিকা
লিখেছেনঃ প্রীতম (তারিখঃ বৃহঃ, ১২/০৭/২০১২ - ০২:৩১)
_____________________________________
১.
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে প্রায় সারা পৃথিবীতেই জটিল মেরুকরণ ঘটেছিল।প্রাচ্যে-মধ্যপ্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে এমনকী আফ্রিকাতেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে-বিপক্ষে বিভাজন দেখা দেয়।বাংলাদেশে যখন গণহত্যা চলছে,গণহত্যার বিপরীতে একটি জাতির মুক্তিসংগ্রাম চলছে পাকিস্তান সরকার তখন এই মুক্তিযুদ্ধকে ইসলাম ধ্বংসের চক্রান্ত,ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র হিসেবে প্রচার করেছে।দুঃখজনক হলেও সত্য,ধর্মকে ব্যবহার করে তৈরি করা এই প্রোপাগান্ডা-আফিম গিলেছে বিশ্বের বেশিরভাগ ইসলামী বা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র।এর সাথে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক স্ট্র্যাটেজি।যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের ঘনিষ্ট মিত্র,অন্যদিকে আমাদের আলোচ্যমান রাষ্ট্রগুলোর সাথেও পাকিস্তানের চমৎকার বোঝাপড়া ছিল।এর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের কম্যুনিজম বিরোধী অবস্থানের সঙ্গী থাকার কারণে এসব রাষ্ট্র পাকিস্তানের মিত্র হিসেবেই কাজ করেছে যা প্রকারান্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা হিসেবেই চিহ্নিত হবে।
এইসব রাষ্ট্রকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিপক্ষ হিসেবেই দেখতে হবে।এদের মধ্যে সৌদি আরব,জর্ডান,ইরান,লিবিয়া এবং তুরস্ক সরাসরি সামরিক সাহায্য দিয়েছে পাকিস্তানকে।সৌদি আরব ও লিবিয়া এর সাথে অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিকভাবেও সমর্থন দিয়েছে।মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য' ইয়াহিয়া খানের গৃহিত পদক্ষেপকে ( পড়ুন গণহত্যা ) সমর্থন দিয়েছে।নাইজেরিয়ার গণমাধ্যমে বাংলাদেশ বিরোধী প্রোপাগান্ডা চলেছে।একমাত্র ব্যতিক্রম দেখতে পাই মিশরকে।এছাড়া অন্যান্য আরব দেশগুলো এসময় চুপ থাকার নীতি অবলম্বন করে।
২.
সামরিক এবং কূটনৈতিক বিরোধিতা
আরব বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শত্রুর নাম হিসেবে নির্দ্বিধায় সৌদি আরবের কথা বলা যায়।মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই সৌদি আরব প্রকাশ্যে এর বিপক্ষে অবস্থান নেয়।পাকিস্তানকে প্রায় সবধরণের সহযোগিতাই দিয়েছে সৌদি আরব।পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষার অজুহাতে তারা গণহত্যাকে সমর্থন করে এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে।জুনের শেষ সপ্তাহে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত বাইশ জাতি মুসলিম সংস্থার সম্মেলনে পাকিস্তানি আগ্রাসনের সমর্থনে একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়।এতে উল্লেখ করা হয় - পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় বাইশ জাতি মুসলিম সংস্থা পাকিস্তানের কার্যক্রম সমর্থন করে।পাকিস্তানের সাথে একটি অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক চুক্তিতেও আবদ্ধ হয় সৌদি আরব।যুদ্ধের নয়টি মাস তারা সব ধরণের আর্থিক সুবিধা দিয়েছে পাকিস্তানকে[১*]। সাহায্য করেছে সামরিকভাবেও।সৌদি আরব পাকিস্তানকে বেশ কয়েকটি এফ-৮৬ যুদ্ধবিমান দেয়[২]।
যুদ্ধাকালীন সময়ে পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ মিত্রজোট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ইরান-জর্ডান-লিবিয়া।যুদ্ধের একেবারে শেষের দিকে তিনদেশই পাকিস্তানকে যুদ্ধবিমান দিয়ে সহায়তা করে এবং আরো সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়।এদের সাথে যোগ দেয় তুরস্ক।ইরান থেকে লিবিয়ার যুদ্ধবিমান পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য তুরস্কের আকাশসীমা ব্যবহার করেছিল।
এই সময় বেশ কিছু কূটনৈতিক মারপ্যাঁচ দেখা যায়।ডিসেম্বরের ৫ তারিখ,একজন মার্কিন কর্মকর্তা ( নাম জানা যায়নি ) ইরানের শাহ মুহম্মদ রেজা পহ্লভীর সাথে দেখা করে পাকিস্তানকে সামরিক সহায়তা দিতে অনুরোধ করেন।পহ্লভী রাজি হন[৩*]। ৮ তারিখে তেহরানের ইউএস এমব্যাসির একজন কর্মকর্তা পহ্লভীর সাথে দেখা করে এই সহায়তা প্রদানের সম্ভাব্য উপায় নিয়ে আলোচনা করেন।এসময় পহ্লভী আবারো সহায়তার ব্যাপারে তার সম্মতি জানান।তবে এবার আরো কিছু বিষয় যোগ করা হয়।
ভারত সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির প্রেক্ষাপটে ইরান সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে কোন ধরণের সংঘর্ষে যেতে রাজি ছিল না,পহ্লভীর ভাষায় সেই প্রস্তুতি তাদের ছিল না।অন্যদিকে পাকিস্তানকে সহায়তা দিতেও তারা আন্তরিকভাবে রাজি।এই অবস্থায় পহ্লভী জর্ডানের মাধ্যমে এই সহায়তা দেয়ার প্রস্তাব দেন।প্রস্তাবটি ছিল এরকম,জর্ডানকে যেহেতু পাকিস্তান এবং যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা দেয়ার অনুরোধ করেছে সেজন্য জর্ডান পাকিস্তানকে যুদ্ধবিমান ( এফ-১০৪ ) দেবে।অন্যদিকে এর রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে ইরান জর্ডানকে যুদ্ধবিমান দিয়ে তাদের অভ্যন্তরীন সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে[৩**]।পহ্লভী জর্ডানকে দুই স্কোয়াড্রন এফ-১০৪ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন[৪]।
এর আগেই পাকিস্তান জর্ডানের কাছে সাহায্য চেয়েছে।৫ তারিখেই মার্কিন এম্বাসাডর ডীন ব্রাউন জর্ডানের বাদশাহ হোসেনের সাথে দেখা করতে গেলে হোসেন তাকে ইয়াহিয়া খানের পাঠানো একটি চিঠি দেখান।চিঠিতে এফ-১০ এবং এফ-১০৪ যুদ্ধবিমান চাওয়া হয়েছে[৩*]। ৭ ডিসেম্বর,আম্মানের ইউ এস এমব্যাসিতে বাদশাহ হোসেন একটি বার্তা পাঠান ।বার্তায় পাকিস্তানের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে হোসেন যুদ্ধবিমান সরবরাহের ব্যাপারে প্রস্তুত থাকার কথা জানান।
তবে এখানে অন্য একটি সমস্যা এসে পড়ে।জর্ডান যে এফ-১০৪ যুদ্ধবিমান দিতে চেয়েছে পাকিস্তানকে সেগুলো যুক্তরাষ্ট্র জর্ডানকে দিয়েছিল,এ অবস্থায় কোন তৃতীয় পক্ষকে এই বিমান দিতে গেলে যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি নিতে হবে।ঠিক ওই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি অনুমতি দিতে পারছিল না কারণ পাকিস্তানে আর কোন সামরিক সহযোগিতা না দেয়ার ব্যাপারে একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে তারা।এই অবস্থায় হোসেনকে যুক্তরাষ্ট্র জানায় যে তার প্রস্তাবটি বিবেচনাধীন রয়েছে।বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথেই নেয় যুক্তরাষ্ট্র।
শেষ পর্যন্ত এই বিমান পাকিস্তান পেয়েছিল।১৪ ডিসেম্বর তারিখে ইস্যু হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের সিচুয়েশন রিপোর্ট জানাচ্ছে ১২ এবং ১৩ ডিসেম্বর জর্ডানিয়ান এফ-১০৪ পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে।
অন্যদিকে আগেই উল্লেখ করা সমস্যা থাকার পরেও ইরানের কাছ থেকে পাকিস্তান এফ-৮৬ এবং সি-১০৩ বিমান পেয়েছে বলে জানা যায়[২]
এদিকে এই মিত্রজোটে লিবিয়াও যুক্ত হয়ে গেছে। ২৯ ডিসেম্বর তেহরানের ইউএস এমব্যাসি থেকে পাঠানো তারবার্তায় উল্লেখ করা হয় যে পাকিস্তান তিনটি লিবিয়ান এফ-৫ বিমান পেয়েছে।বিমানগুলি ছেড়ে গেছে তেহরান বিমান ঘাটি থেকে,চালকেরা ছিল পাকিস্তানি।এর জন্য তুরস্কের আকাশসীমা ব্যবহার করা হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে এই বার্তায়।তিনটি ভিন্ন অনুচ্ছেদে একজন মার্কিন ব্যবসায়ী,একজন ইরানের বিমানবাহিনীর একজন অফিসার এবং এবং অন্য একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাত দিয়ে এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করা হয়।
তবে এই বিমানগুলো পাকিস্তানের হাতে আসে সম্ভবত ২৭ ডিসেম্বর,একই তারবার্তায় ২৬ তারিখে এই বিমানের তুরস্কে অবস্থান করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।এসময় দুটি ফ্রন্টেই যুদ্ধ শেষ হয়েছে,পাকিস্তান আত্মসমর্পন করেছে।এই অবস্থায় যুদ্ধ বিমান দিয়ে পাকিস্তান কী করেছিল সেটা একটা প্রশ্ন।তবে যুদ্ধের সময়েই পাকিস্তান কমপক্ষে ২৪ টি লিবিয়ান মিরাজ বিমান পেয়েছে যেগুলো,ধারণা করা হয়,লিবিয়া থেকেই এসেছে।আরো ধারণা করা হয়,যুদ্ধের সময়ে পাকিস্তান লিবিয়া থেকেই এফ-৫ বিমান পেয়েছে যেগুলো প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে সারাগোদা নামক স্থানে।ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি প্রতিবেদনে এর উল্লেখ পাওয়া যায়[২]।
এর পাশাপাশি জর্ডানের বাদশাহ হোসেন এবং ইরানের শাহ পহ্লভী বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ প্রশ্নে পাকিস্তানকেই সমর্থন দিয়েছেন,সমর্থন দিয়েছে তুরস্কও।লিবিয়ার অবস্থান কট্টরভাবে পাকিস্তানের পক্ষে ছিল ( পরের অংশে আলোচিত )।এর সাথে যুক্ত হয় মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া।বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু হওয়ার পরে ২৮ মার্চ ১৯৭১ ইন্দোনেশিয়া এবং ইরান পাকিস্তানকে সমর্থন করে বিবৃতি দেয়।মালয়েশিয়া এবং তুরস্ক তাদের সমর্থন জানায় ৪ এপ্রিল[১]।
প্রোপাগান্ডা : ধর্মীয় সুড়সুড়ি এবং নির্লজ্জ মিথ্যাচার
ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে এসব মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চলেছে পুরোদমে।পুরো ব্যাপারটিকে ইসলামী দেশ পাকিস্তান ধ্বংসের জন্য ভারতের ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করা হয়েছে।আওয়ামীলীগ এবং শেখ মুজিবকে মূল কালপ্রিট সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে।এক কোটি ঘরহারা শরণার্থীর বিষয়টিকে সাজানো বলে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।
প্রথমেই সৌদি আরবের একটি পত্রিকার খবর।পাকিস্তানে যে একটি যুদ্ধ চলছে সেটাই অস্বীকার করা হয়েছে জেদ্দা থেকে প্রকাশিত দৈনিক আল মদিনার ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে।সম্পাদকীয়র শিরোনাম Where Is War ।লিখেছিলেন সম্পাদক আদনান কামেল সালাহ।
একেবারে প্রথম অনুচ্ছেদেই বলা হয়েছে বাংলাদেশ থেকে যে বিপুল সংখ্যক শরণার্থী ভারতে পাড়ি জমিয়েছে তারা ভারতীয় 'স্যবোটাজ' থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই পালিয়েছে।
It is certain that a large number of of refugee crossed into India but not 9 million as the Indian propaganda puts it,The refugees went to to India in order to escape the saboteurs coming from Indian territories.
এর পরের অনুচ্ছেদেই পাকিস্তানের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে,পরিস্থিতি মোকাবেলায় পাকিস্তনা সরকারের সক্ষমতার কথা বলা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে - যেহেতু সব ধরণের স্যাবোটাজ মোকাবেলার ক্ষমতা পাকিস্তান সরকার রাখে কাজেই যুদ্ধের ব্যাপারটি পুরোপুরিই অপপ্রচারণা।এবং যেহেতু যুদ্ধ হয়নি কাজেই গণহত্যা জাতীয় কিছুর প্রশ্নই আসেনা।
And, in spite of the sabotage activities from India, The Pakistan Government could control all parts of East Pakistan and ensure security there,and the saboteurs could only move in some border of Pakistan with INdia,and that too often under protection of the Indian army.So,wgile talking about the danger of war what pusses Russia to pretend that it will ensure that no war arises in the area?
এর পরে আরো দুটি অনুচ্ছেদে এরকম মিথ্যাচার চালানো হয়েছে।ভারতকে স্যাবোটাজ না করতে নসিহত করা হয়েছে।তারিখটি খেয়াল করুন,সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখে তারা দাবি করছে কোন যুদ্ধই হয়নি !
এবার লিবিয়ার ত্রিপোলি থেকে প্রকাশিত দৈনিক আল থাউরা পত্রিকার Situation In Pakistan শিরোনামের সম্পাদকীয়টি দেখা যাক।এটি প্রকাশিত হয়েছে ২২ সেপ্টেম্বর।আল থাউরা লিবিয়ার সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা।প্রথম অনুচ্ছেদেই পাকিস্তানের কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছে।কারণ শুধু মুসলিম ব্রাদারহুডই নয়,বরং একটি right and just cause কে সমর্থন দেয়ার জন্যই তাদের অবস্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।এর পরে শেখ মুজিব সম্পর্কে কিছু মিথ্যাচার।শেখ মুজিবকে সাতচল্লিশের দাঙ্গায় মুসলিম হত্যাকারী হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে।তাদের দেয়া ডাটা অনুসারে সত্তরের নির্বাচনে শেখ মুজিব সাতচল্লিশ শতাংশ ভোট পেয়েছেন তার মধ্যে মুসলিম ভোট মাত্র বিশ শতাংশ।এইভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আওয়ামীলীগ মোটেই মুসলিম বান্ধব কোন দল নয়।পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য সম্পর্কে যেসব উপাত্ত পাওয়া যায় সেগুলো পাশ্চাত্য জায়নিস্ট মিডিয়ার প্রচারণা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।মার্চের আলোচনার সময়ে পর্দার আড়ালে পাকিস্তানি সৈন্যদের পূরব পাকিস্তানে নিয়ে আসার ঘটনাটিও একইরকম প্রোপাগান্ডা।গণহত্যা,শরণার্থী সংক্রান্ত যেসব খবর বিবিসি সহ অন্যান্য মাধ্যমে পাওয়া গেছে তা সবই জায়নিস্ট এবং ভারতীয় অপপ্রচারণা।
Sitting in Calcutta,relying on Indian interpreters for their conversation with refugees and competing with each other for dramatic news stories to boost their papers' readership,can one honestly expect these journalists to give a fair picture?...The figure has been been believed by some friends of Pakistan despite the fact that Pakistan has published the result of a through enquiry of the number of refugees which shows the exact figure is two million.But the volume of propaganda from BBS,Voice of America, and the western and zionist sources is louder and more impressive.
আগেই বলা হয়েছে নাইজেরিয়াতেও বাংলাদেশ বিরোধী প্রোপাগান্ডা চলেছে।এবার নাইজেরিয়ার পত্রিকা ডেইলি মর্নিং পোস্টের সম্পাদকীয় দেখা যাক।এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১০ সেপ্টেম্বর,১৯৭১।লিখেছলেন তুনজি এডিওসান, Secession Attempt In Pakistan শিরোনামে।
এখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সাধুপুরুষ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণহত্যার ঘটনা সাজানো।বুদ্ধিজীবী নিধনের ঘটনা মিথ্যা।
The picture of trigger-happy Pakistan Army is completely false one.In an attempt to refute most of these false reports,the Pakistani Government has taken around foreign correspondents to see the Dacca University falsely reported to have been razed to the ground.Many scholars alleged to have been killed along with their families have appealed on Dacca television and contradicted the false reports.
শেখ মুজিব সব ধরণের আলোচনা-সমঝোতার চেষ্টা নস্যাৎ করেছেন।পাকিস্তানের গণ্যমান্য নেতারা এমনকী প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত তার কাছে পাত্তা পায়নি।ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের প্রতি চূড়ান্ত অসম্মান দেখিয়ে দখলদারী মানসিকতার শেখ মুজিব বলেছেন - 'Take it over'।
এর পরে মর্নিং পোস্ট পাকিস্তান পরিস্থিতি সম্পর্কে 'সত্য' জানিয়েছে।বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রতিরোধ করতেই যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সামরিক ব্যবস্থাই নেয়া হয়েছে মাত্র,তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানবাসীর সমর্থনও আছে এবং সেটা 'যুদ্ধ' নয় -
The truth is that a military action supported by a majority of East Pakistanis was ordered against the secessionists,and not a war between East Pakistan.Neither it be right to describe the Government of Pakistan as "West Pakistan Government".
এখানে সবগুলো পত্রিকাতেই মূল সুরটি লক্ষণীয়।সবগুলোতেই শেখ মুজিব-আওয়ামীলীগ-ভারতকে কালপ্রিট সাজিয়ে পাকিস্তানের দোষ আড়াল করার চেষ্টা চোখে পড়ে,এর সাথে ধর্মীয় অনুভূতি ব্যবহার করে জনসমর্থন তৈরির চেষ্টা যোগ হয়েছে।
৩.
মিশরের ভূমিকা :
মুসলিম এবং আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মিশর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করেছে।বাংলাদেশের পক্ষে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের শরিক ভারতের অবস্থানকেই সমর্থন করেছে তারা,সেই সূত্রেই গণহত্যার বিপরীতেই অবস্থান ছিল মিশরের।১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দিকের রাষ্ট্রগুলোর একটি মিশর।মিশরের মিডিয়াতেও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে লিখেছেন অনেকেই।সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে কায়রোর আধাসরকারি সংবাদ পত্র আল আহরামে সম্পাদক ড. ক্লোভিস মাসুদ ভারত থেকে শরণার্থীদের নিরাপদে এবং নিঃশঙ্কভাবে দেশে ফেরার একটি ব্যবস্থা করতে আনত্ররজাতিক সম্প্রদায়কে তাগিদ দেন।এর পাশাপাশি একটি গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমাধানের কথাও বলেন।রাজনৈতিক সমাধানের সংজ্ঞাও পরিস্কার করেছিলেন তিনি - শেখ মুজিবের নিঃশর্ত মুক্তি এবং সত্তরের নির্বাচন অনুসারে ক্ষমতা হস্তান্তর।ড. মাসুদ অখণ্ড পাকিস্তানেরই পক্ষপাতী তবে তিনি এও উল্লেখ করেছে,পরিস্থিতি এরকম চলতে থাকলে অখণ্ড পাকিস্তানের বিনিময়ে এই নৃশংস গণহত্যা মেনে নেয়াও সম্ভব না।বাংলাদেশ ইস্যুতে আরবদের আরো কার্যকরী ভূমিকা রাখতেও অনুরোধ করেছেন মাসুদ[৫]।
৪.
একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই পাকিস্তান তার ইসলামী রাষ্ট্র পরিচয়টি ব্যবহার করে আরব এবং মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে পক্ষপাতিত্ব আদায় করে নিতে পেরেছিল।ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে এসব দেশে পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারণা চলেছে যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করেছে।তবে সামরিক এবং কূটনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে মূল চালগুলো যুক্তরাষ্ট্রই চেলেছে।তাদের আগ্রাসী কূটনীতির সাথে জড়িতে থাকা এসব দেশের পাকিস্তানকে সহায়তা করার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ।একই সাথে পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার সমীকরণগুলোও কাজ করেছে পাকিস্তানের পক্ষেই।তার সাথে ধর্মীয় সুড়সুড়ির সংযোগ ঘটেছে চমৎকারভাবে।
'মুসলিম' রাষ্ট্রগুলো তাই সমষ্টিগতভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শত্রু হিসেবেই চিহ্নিত হবে ইতিহাসে।
তথ্যসূত্র :
১) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বহির্বিশ্বে শত্রুমিত্র - সিরু বাঙালি ( পৃ - ২ )
২) IAF COMBAT KILLS - 1971 INDO-PAK AIR WAR - B. Harry
৩) Foreign Relations of the United States, 1969–1976,Volume XI,South Asia Crisis, 1971 - Louis J. Smith,Edward C. Keefer ( *pg - 610,**pg - 700 )
৪) Revisiting 1971 War and IAF’s Role:India’s Interests and Compulsions - Air Vice Marshal Kapil Kak
৫) গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ,দশম খণ্ড - হাসিনা আহমেদ,পৃ - ১২০
_____________
http://www.amarblog.com/pritomdas/posts/150192
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ২০:০২582862
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ২০:০২582862- ডেভিড ম্যাকাচ্চন: আমার একাত্তরের নির্জন সুহৃদ
লিখেছেনঃ শনিবারের চিঠি (তারিখঃ বৃহঃ, ১৭/০৫/২০১২ - ০২:০২)
_________________________________________________
কিছুদিন ধরে একজন মানুষ আমায় খুব ভাবিয়ে তুলেছেন। আমার চিন্তার ফ্রেমে বারবার একটি প্রশ্ন রেখে গেছেন- ‘আমি কী বলি নাই?’ তিনি বলেছিলেন, বহুদূরের কণ্ঠস্বরের ক্ষীণ সুরের পালে হাওয়া লাগিয়ে তিনি সত্যিই বলেছিলেন; বলেছিলেন:
আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, পূর্ব পাকিস্তান থাকবে না- এর ভেতরে একটি নূতন রাষ্ট্র নবজাতকের মতো চিৎকারে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে
কিন্তু এইটুকু বলে দেয়াতেই কী সব হয়ে যায়? যায় না। বাঙালির বন্ধু ভাগ্য কতোটা সুপ্রসন্ন তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে, কিন্তু বাঙালির শত্রুভাগ্য এক কথায় ঈর্ষণীয়। দূরের ছবি না দেখলেও সে-ই পাকিস্তান সময় থেকেই বর্বরতার খড়গ নিয়ে পাকিস্তান বাঙালিকে গ্রাস করতে চেয়েছিলো। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১- দীর্ঘতর না হলেও দীর্ঘ একটি সময়; এই সময়কালে ইতিহাস তৈরি হয়েছে, ভেঙেছে বেঈমানীর চার দেয়াল, তৈরি হয়েছে একটি রাষ্ট্র, স্বাধীনতার সুউচ্চ সৌধে যার নাম বাঙলাদেশ।
এই বাঙলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিও বেশ অদ্ভুত একটা নিয়তি নিয়ে বড়ো হয়। বাঙলাদেশ তার শৈশব পেরোনোর আগেই পিতৃহারা হয়, চালান হয়ে যায় শয়তানের ভাগাড়ে; পঁচাত্তর থেকে বাঙলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিতে কোনো কনে দেখা রোদ আসেনি, কেবল শকুন চিনে নেবার রাত নেমেছে। সঙবিধান থেকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে দুটি স্তম্ভ- ‘সমাজতন্ত্র’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’। আর সেখানে ঠাঁই দেয়া হয়েছে কিছু কুৎসিত কথা, পবিত্র সঙবিধানকে করে তোলা হয়েছে স্পর্শের অযোগ্য; রাষ্ট্র নামের ‘বাঙলাদেশ’ রাষ্ট্রের প্রেত হয়ে বড়ো হতে থাকে- তার বয়স বাড়ে একাত্তর থেকে একাশি, একাশি থেকে একানব্বই, একানব্বই থেকে দু হাজার এক, দু হাজার এক থেকে দু হাজার এগারো.. ..কড়ায় গুনে চল্লিশ বছর- কিন্তু বাঙলাদেশ আসলে শৈশব থেকে জঠরের অন্ধকারে যেতে থাকে। ক্রমশ অন্ধকার; সাড়ে সাত কোটি বাঙালির দেশ আজ ষোলো কোটি শুয়োরের বাচ্চার দেশ, তাজউদ্দীন আহমেদের অর্থ-পরিকল্পনার বাঙলাদেশ আজ ঋণখেলাপীর গ্যালারির বেশ্যা.. ..।
তবুও অচেনা এক কারণে এই বাঙলাদেশকে ভালোবেসেছেন অনেকেই, জানি না কেনো- হয়তো ‘বাঙলাদেশের’ চোখ দুটো খুব সুন্দর, মায়াবী; কিঙবা তার অধরে একটা তিল আছে হয়তো, ভোরের সূর্যালোকের মতো ধ্রুব, উজ্জ্বল; এবঙ এটাও আশ্চর্য যে- বাঙলাদেশকে ভালোবাসেন যাঁরা, তাঁদেরও খেতে হয় গলাধাক্কা; সায়মন ড্রিঙ এর কথা মনে করা যেতে পারে; পরের ইতিহাস যাই হোক এই বাঙলাদেশে এমন সরকারও আসে যারা সায়মন ড্রিঙ এর মতো মানুষকে বের করে দেয়।
এসব কিছু নিয়ে আমি যখন ভীষণ ভাবনায় মত্ত- তখনই নামে বৃষ্টি, বৃষ্টির সাথে আমার ঘরে আসেন ডেভিড ম্যাকাচ্চন, তাঁর হাতে একাত্তরের সেই অবিনাশী কবিতাখানি। অনেকখানে ছিঁড়ে গেছে, পাবলিক লাইব্রেরির শীর্ণ দু’তালার পুরোনো পত্রিকা থেকে জোড়াতালি দিয়ে যেটুকু উদ্ধার করা হলো, সেটুকু নিয়েই এসেছেন ডেভিড ম্যাকাচ্চন।
.. ..he spoke of killing still going on Dacca.. ..
.. ..wrote that the sun rises and sets
and the sky is blue as though nothing had happened
and here too in England!
It has been a wonderful spring of warm days,
blue skies, fresh breezes and flowers,
the trees so green,
the air delicious with scented freshness,
and the students lie about on the grass
in bright clothes making it impossible to believe
that life could be so miserable, elsewhere. (১)
কবিতাটির ব্যর্থ বাঙলা অনুবাদ
বন্ধুর চিঠিতে খবর
হত্যার তাণ্ডবলীলা প্রবল গতিতে চলছে,
বিশেষত ঢাকায়।
লিখেছে বন্ধু- সেখানে সূর্য ওঠে আবার অস্ত যায়!
আকাশ নাকি আগের মতোই সুন্দর-স্বচ্ছ-নীল,
মনে হবে যেনো কিছুই ঘটেনি, স্বাভাবিক রাত আর দিন!
আর এখানে, এই ইঙল্যান্ডে?
একটা আশ্চর্য সুন্দর উত্তাপের দিনে গড়া
বসন্তের আবির্ভাব ঘটেছে।
আকাশ তেমনি নীল, সঙ্গে
নির্মল মৃদু হাওয়া আর সতেজ ফুলের পাপড়ি।
গাছগুলো কতো সবুজ!
চারদিক স্নিগ্ধ আমেজে ভরা!
আর ছেলেমেয়েরা উজ্জ্বল পোষাকে
গড়িয়ে পড়ছে ঘাসে।
পৃথিবীর কোথাও কোথাও মানুষের জীবন
কতো কষ্ট আর হাহাকারে পূর্ণ।
চিঠিটি লেখা হয়েছিলো একাত্তর সালে, বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়; মানে কবিতাটিও সে সময়েই লেখা। ডেভিড ছিলেন মূলত মন্দির গবেষক। ইঙল্যান্ডের কভেন্টির এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ডেভিডের জন্ম হয় ১৯৩০ সালের ১২ আগস্ট। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ‘কভেন্টির কিঙ হেনরী এইট গ্রামার স্কুল’ এ তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ। তারপর আঠারো মাস (১৯৪৯-৫০) দেশের আইনানুযায়ী সামরিক কর্মে যোগদান। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা শুরু। কেম্ব্রিজের ‘যেশাস কলেজ’ এ অধ্যয়ন ১৯৫০ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত। ১৯৫৫ সালে ইঙরেজী-ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষা-সাহিত্যে ‘ট্রাইপস’ পেয়ে স্নাতক এবঙ ১৯৫৭ সালে কেম্ব্রিজ থেকে স্নাতোকোত্তর হন। কর্মজীবনের শুরুতে (১৯৫৩-১৯৫৫) ডেভিড দক্ষিণ ফ্রান্সের দুটি ফরাসী বিদ্যালয়ে ইঙরেজী ভাষার শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা করেন। এরপর দু’বছর পিতা-মাতার সঙ্গে কভেন্ট্রিতে বসবাস করেন। ১৯৫৭ সালে ভারতে আসেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঙরেজীর প্রভাষক হিসেবে। ১৯৬০ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষা সাহিত্যের প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন এবঙ ১৯৬৪ সালে ঐ বিভাগের রিডার পদে উন্নীত হন। বিলেতে থাকাকালীন সময়ে তিনি ছিলেন ‘ট্যাগোর সোসাইটি’র একজন উদ্যোক্তা (২) ; ভারতবর্ষ ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট কৌতুহল। তাই বাঙালি সঙস্কৃতির প্রতি তাঁর একটি অনবদ্য মায়া ছিলো। তিনি তাঁর এক লেখায় লিখেছেন-
বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে একটা প্রাণ আছে যা এই অঞ্চলের মানুষদের বাঁচিয়ে রাখে। এই সংস্কৃতি কোন ধর্ম-সমাজ-বর্ণ বা গোত্র দ্বারা বিভক্ত না, যদিও এখানে বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। (৩)
১৯৬১ সালের কথা। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদযাপন করতে দেবে না পাকিস্তান সরকার। বেতারে টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করা হলো। কিন্তু বাঙালি তার হৃদ-স্পন্দন ভুলবে কীভাবে? শুরু হলো আন্দোলন। ডেভিড তখন কোলকাতায় থাকেন। কোলকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটিতে সন্ধ্যার পর বসতেন। নিয়মিত ডায়রি লিখতেন তখন, এবঙ তাঁর ডায়রির অধিকাঙশটুকুই এশিয়াটিক সোসাইটিতে বসে লেখা (৪)। ১৯৬১ সালের ০৮ মে, বাঙলা ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮ সালে ডেভিড তাঁর ডায়রিতে লিখছেন-
মানুষকে সব-সময়ই যুদ্ধ করতে হয়েছে বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে- কিন্তু পূর্ব- পাকিস্তানের মানুষ আজ বুঝিয়ে দিলো গান গেয়েও যুদ্ধ করা যায়। পাকিস্তান সরকার তাদের কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করে তারা একটি জাতিকে নিষ্পেষিত করার চক্রান্ত চূড়ান্ত করেছে। আমার বিশ্বাস- পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ সেটা প্রতিহত করতে পারবেই। (৫)
২০১২ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় ‘রবীন্দ্র-উত্তর বাঙালি দর্শন’ শীর্ষক সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধের একস্থানে রয়েছে-
ইংরেজ অধ্যাপক ডেভিড ম্যাকাচ্চন ১৯৬২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি উদযাপনের জন্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেখানে সমবেত শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণ একত্রে গান গান-
কে এসে যায় ফিরে ফিরে আকুল নয়ননীরে।
কে বৃথা আশা ভরে চাহিছে মুখ’পরে।
সে যে আমার জননী রে।।
কাহার সুধাময়ী বাণী মিলায় অনাদর মানি।
কাহার ভাষা হায় ভুলিতে সবে চায়।
সে যে আমার জননী রে।। (৬)
১৯৬৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে তিন থেকে চার সপ্তাহের জন্যে ডেভিড আসেন বাঙলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান)। তিনি আসের মূলত মন্দির-মসজিদ ও প্রাচীন অট্টালিকা দেখার জন্যে। অশ্রান্তভাবে ঘুরে বেড়াতে থাকেন যাত্রার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। সে সময় বাঙলায় চলছে স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন। সে সময়ের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ডেভিড একটা নিবন্ধ লিখেছিলেন দ্যা রেডিক্যাল হিউম্যানিস্ট পত্রিকায়। তিনি লেখেন-
পাকিস্তানের জনগণ যে সুখে নেই, সেটা বোঝা যায়। অনেকেই বলতে চাইছেন সেখানে একটি অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে, কিন্তু আমার মনে হয়েছে উল্টো- পশ্চিম পাকিস্তানের আচরণ (পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি) অসহ্য। আমি গ্রামে ঘুরে ঘুরে দেখেছি সেখানকার মানুষদের মধ্যে কোনো হিন্দ-মুসলমান বিভেদ নেই, কিন্তু পাকিস্তান সরকার ধর্মের ধুয়া তোলে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে।.. ..শুনেছি এদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকেও নাকি সাম্প্রদায়িকীকরণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পাকিস্তানে হিন্দুরা কোনো উৎসব অনুষ্ঠান করতে পারে না, এটা যতোটা না পড়শি মুসলমানের বাধা তার চেয়ে বড়ো বাধা সরকার ও তার লোকজন। .. ..পূর্ব পাকিস্তানে হাঙ্গামা জটিল হয়ে পড়ছে মূলত দুটি কারণে; একটি হলো- সরকারের বৈষম্যনীতি ও পূর্ব পাকিস্তানিদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, অন্যটি হলো- অবাঙালিদের (বিহারিদের) সরকার কর্তৃক মৌলবাদী সুবিধা প্রদান করা। ... পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশের একটি বড়ো কারণ হলো পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যনীতি; কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিরা দমন-পীড়নের আশ্রয় নিতে ব্যস্ত। পশ্চিম পাকিস্তানিদের ধারণা এটা হচ্ছে অজ্ঞতার কারণে, তাই তারা সেখানে ‘পাকিস্তান কাউনসিল’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ নেয়। এদের অনুষ্ঠানে আমিও ছিলাম। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ খোলা হবে, এতে নাকি পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষা হবে। আমার কষ্ট হয়েছি এই ভেবে যে- শেষ পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবহৃত হচ্ছে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে। .. ..কিন্তু একটি বিষয় আমার বারবার মনে হয়েছে, বিশেষত পাবনায় গিয়ে যে- পূর্ব পাকিস্তানের ভেতরে একটি নূতন দেশ লুকিয়ে আছে, তার প্রতিবাদ যেনো সে দেশের ছবিটাই দেখায়। (৭)
ডেভিড মারা যান ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি; উডল্যান্ড নার্সিঙ হোমে। বাঙলাদেশ তখন স্বাধীন। বাঙলাদেশ স্বাধীন হবার আগেই ডেভিড বলে গিয়েছিলেন-
আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, পূর্ব পাকিস্তান থাকবে না- এর ভেতরে একটি নূতন রাষ্ট্র নবজাতকের মতো চিৎকারে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে
ডেভিড ম্যাকাচ্চন বিশ্বাস করতেন- বাঙালির ভাষা ও সঙস্কৃতি বাঙালির প্রধান বৈশিষ্ট্য- হিন্দু, মুসলমান কিঙবা বৌদ্ধধর্ম নয়। বাঙলাদেশে যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়- ডেভিড ছিলেন তখন ইঙল্যান্ডে। পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর অত্যাচারের সঙবাদে তিনি উদ্বিগ্ন সময় কাটিয়েছেন এবঙ সে সময়টাতে তিনি ছিলেন খুব অসুস্থ। সে সময় তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও গবেষক, সমালোচক ড. সুহৃদকুমার ভৌমিকের কাছে লেখা এক আবেগঘন চিঠিতে আমরা পাই-
সুহৃদ- কী হচ্ছে বাঙলাদেশে? এভাবে পাকিস্তান সরকার মানুষ হত্যা করছে? তোমরা চুপচাপ কেনো? সঙবাদমাধ্যমে তো সব খবর পাই না। গার্ডিয়ানের একটা খবরে পড়লাম সেখানে নাকি নারী নির্যাতন চালাচ্ছে ‘স্টুপিড সোলজাররা’ ? সুহৃদ- আমার ভালো লাগছে না; নার্সিঙ হোমের দিনগুলো খুব কষ্টে কাটছে। আমি কী কিছুই করতে পারবো না বাঙলাদেশের মানুষগুলোর জন্য? আমি যেবার সেখানে গিয়েছিলাম, তাঁদের আতিথেয়তা দেখেছি। তাঁরা কেমন আছে সুহৃদ? কী ঘটছে চারপাশে? আমি কেনো অক্ষম হয়ে গেলাম এই যুদ্ধের সময়ে?
শুনেছি শরণার্থীরা নাকি ভারতীয় সীমান্তে এসে আশ্রয় নিয়েছে? তুমি খোঁজ করো- ওঁদের মধ্যেই হয়তো আছেন ময়মনসিঙহের সেই পরিবারটি, যাঁরা আমাকে খাওয়ানোর জন্যে একবেলা না খেয়েছিলো। সুহৃদ- অনুজ আমার, তুমি এশিয়াটিক সোসাইটিতে যাও, আমার লকারে Kodak-Duo ক্যামেরাটা আছে, আর যোগাযোগ করো অমিয় ব্যানার্জীর* সঙ্গে- তাঁর কাছে আমার Agfa-Isolatte ক্যামেরা আর Weston Master III মডেলের এক্সপোজারটা আছে। এগুলো বিক্রি করো সুহৃদ- আবেগ দেখানোর সময় এখন না; এগুলো বিক্রি করে যা পাও তা নিয়ে শরণার্থী শিবিরে যাও। ওইখানে বাঙালিরা রয়েছেন- যারা মাটির কাছে থাকেন, যাঁদের শান্তির নীড়ে হায়না হানা দিয়েছে, তাঁদের পাশে দাঁড়াতে না পারলে মানবজীবন সার্থক হবে না সুহৃদ। তুমি যাও। কী করলে দ্রুত জানিও। আমি পঙ্গু হয়ে নার্সিঙ হোমে পড়ে না থাকলে তোমাকে এই কষ্টটা করতে হতো না।
ডেভিড ম্যাকাচ্চন- সেদিনের সেই চিঠিটাই নাকি ছিলো আপনার লেখা শেষ চিঠি? আমি অবশ্য কোনো গ্রহণযোগ্য সূত্র পাইনি।‘অনুস্টুপ’ এর শরৎ সঙখ্যায় প্রতিভা সান্যালের ‘পটুয়া আর্ট’ এর উপর এক লেখায় বিক্ষিপ্তভাবে এসেছে। এটা কী সত্যি আপনার লেখা শেষ চিঠি?
যদি তাই হয়- তবে শুনুন ডেভিড ম্যাকাচ্চন; এর কোনো উত্তর ড. সুহৃদ আপনাকে দিয়েছিলেন কি না আমি জানি না, আপনার ক্যামেরাগুলো বিক্রি করে কয়জন শরণার্থীকে সাহায্য করা গিয়েছিলো আমি জানি না, জানি না ময়মনসিঙহের সেই পরিবারটি বেঁচে আছে কি না- এসব কোনো কিছুই জানবার দরকার নেই আমার।
তবে আপনাকে কয়েকটি কথা জানাতে চাই। যে রাষ্ট্রটি ‘স্বাধীন হবেই’ ভেবে আপনি নার্সিঙ হোমে ভর্তি হয়েছিলেন, সত্যি সে রাষ্ট্রটা স্বাধীন হয়েছে; ডেভিড- ওই হায়নারা ত্রিশলক্ষ বাঙালিকে হত্যা করেছে, এর বিচার হয়নি; দুইলক্ষাধিক বীরাঙ্গনার দীর্ঘ-ভারী নিঃশ্বাস এখনও আমাদের বিবেকের পর্দা দুলিয়ে যায়, এরপরও এগুলো নিয়ে মিথ্যাচার করে শর্মিলা বসুর মতো মেধা-বেশ্যারা। ডেভিড- তারপরেও আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি, বাঙলাদেশ এখন চল্লিশ পেরোনো গাঙচিল, অজস্র মিথ্যাচারের মধ্যেও এখনও এই বাঙলাদেশে প্রতিদিন সকালে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীরা গায়- ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি.. ..’ পৌরাণিক বৃষ্টির মতো ধ্বঙস নেমে আসে মাঝে মাঝে, তারপরেও রবীন্দ্রনাথের মতো স্থির-ধ্রুব-অবিচল জেগে থাকে বাঙলাদেশ, উন্মুক্ত নীলিমার দিকে তাকিয়ে; ওইতো আসছে ১১ই জ্যৈষ্ঠ ‘সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা’ নিটোল বাঙলাদেশ দেখবেন কেমন আলগা করে খোঁপার বাঁধন, প্রিয়া নয়- রাণী হয়ে আসে। এই আমার বাঙলাদেশ ডেভিড ম্যাকাচ্চন, যার স্বাধীনতা যুদ্ধে ‘কিছু করতে পারেননি বলে’ আপনি আপনার শেষ বয়সের পঙ্গুত্বকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।
ডেভিড ম্যাকাচ্চন- আপনি যেখানেই থাকুন- ভালো থাকুন।
মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি শরণার্থীদের সাহায্য করার জন্যে আপনি আপনার প্রিয় ক্যামেরাগুলো বিক্রি করে দিতে চেয়েছিলেন; আজ বিয়াল্লিশ বছর পর আমার হৃদয়-প্রহরের ঊর্ণাজালে আমি আপনাকে, আপনার সৃষ্টিকর্মকে ঘিরে রাখবো ডেভিড। ১৯৭১ সালে আমার এই বাঙলাদেশের জন্যে আপনি নার্সিঙ হোমে বসে কেঁদেছিলেন; আজ বিয়াল্লিশ বছর পর আমি আপনার জন্যে রাজপথে দাঁড়িয়ে কাঁদবো। অঝোর কাঁদবো। বিরামহীন বুক ভাসানো কান্না কাঁদবো।
আপনার কোনো ঋণ তো আর আমি শোধ করতে পারবো না- কেবল এই কান্নাটুকু ছাড়া, সেটুকুই শোধ করে যাবো আমার বাকিটা জীবন। ইতিহাসের খেরোপাতায় নাকি ‘কান্নার দায়’টা শোধ করে যেতে হয়।
তথ্যসূত্র
১। সমালোচক ড. সুহৃদকুমার ভৌমিকের প্রবন্ধসমগ্র- ০২ এ উল্লিখিত ‘ম্যাকাচ্চন ও তাঁর হেঁয়ালী জীবন’ প্রবন্ধে উল্লেখ আছে- ‘ডেভিড একবার আমাদিগকে বলিয়াছিলেন তাহার কোনো এক প্রিয় ছাত্রের কথা। নামখানা বড়ো খটোমটো, মনে পড়িতেছে না.. ..পরে এশিয়াটিক সোসাইটিতে দ্যা লেইট মেডিভ্যাল টেম্পেলস অব বেঙ্গলের উপর কাজ করিবার সময় তিনি একখানা আত্মজীবনী লিখিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির তরুণ প্রুফ রিডার জগন্নাথ কাজখানা করিতে সম্মত হইলো। কিন্তু হেঁয়ালীপনার কারণে উহা শেষ হইলো না। পরে অর্ধসমাপ্ত পা-ুলিপিতে ‘ছাপানোর কিছু আছে কিনা খুঁজিতে যাইয়া’ এই কবিখানা পাইয়াছি। সম্ভবত ইহা কোনো পত্রের অংশ কেননা পোস্টকার্ড জুড়িয়া ছিলো আর যতোদূর মনে হয় পত্রখানা সেই প্রিয় ছাত্রকেই লিখা হইয়াছিলো’ (ড. সুহৃদকুমার ভৌমিকের প্রবন্ধসমগ্র- ০২, এশিয়াটিক সোসাইটি কোলকাতা হতে প্রকাশিত, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা: ১৯৭)
২। বিলেতে প্রতিষ্ঠিত ট্যাগোর সোসাইটির কার্যনির্বাহিী কমিটির তালিকায় ‘এক্সিকিউটিভ মেম্বার’ হিসেবে ডেভিড ম্যাকাচ্চনের নাম পাওয়া যায়। The Tagore Society Journal-XXVIII, p. 335-347
৩। Calcutta Review 1966 এ প্রকাশিত প্রবন্ধ Field guide to the ancient Bangle Culture থেকে অনূদিত, পৃষ্ঠা: ৫৬
৪। ডেভিড ম্যাকাচ্চন ও ফরস্টারের ভাষায় ইংরেজ জাতি, অশোক রায় চৌধুরী, প্রতিভাস, কোলকাতা, ২০০৯, পৃষ্ঠা: ২৯
৫। অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিতে ডেভিড ম্যাকাচ্চন, সুহৃদকুমার ভৌমিক ও জগন্নাথ রায়, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৯২, পৃষ্ঠা: ১০০-১০১
৬। সেমিনার বক্তৃতা সংকলন নথি- ২০১২, বাংলা একাডেমী
৭। Impression of East Pakistan, The Radical Humanist, 1965 থেকে অনূদিত।
*। অমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায়- বিখ্যাত আলোকচিত্রসংস্থা ‘বর্ন এন্ড শেফার্ড’ এর আলোকচিত্রী এবঙ আকাশবাণীর সঙবাদপাঠক দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়ের মাতুল।
০২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৯
____________________________
http://www.amarblog.com/scmyblog7/posts/147661
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ২০:০৬582863
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ২০:০৬582863- রক্তে ভেজা নীল আকাশঃ ০২-শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেন
লিখেছেনঃ অনিমেষ রহমান (তারিখঃ রবিবার, ১৬/১২/২০১২ - ১৮:২৬)
_________________________________________________________
দাম দিয়েছে বুদ্ধিজীবি নামী দামী লোক কত
এই জনমে ফুরাবে কি আমার বুকের সেই ক্ষত!
ঊনিশশো একাত্তর সনে ওরে ষোলই ডিসেম্বর সকালে
অবশেষে দুঃখিনী এই বাংলা মা যে আমার হয়
দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা কারো দানে পাওয়া নয়।
-আবদুল লতিফ
আজ ষোলই ডিসেম্বর দুই হাজার বারো। চারদিকে উতসব। আমাদের বিজয়ের দিন। মুক্তির দিন।ঢাকাসহ সারাদেশের রাজপথে নেমে এসেছে হাজার-লাখো-কোটি জনতা।বিজয়ের উতসব! নতুন দিনের আবাহন। লাখো শহীদের রক্তের সাগরে সাঁতরে আসা আমাদের স্বাধীনতার এই দিনে স্মরণ করছি তাঁদেরকে যারা হাসিমুখে বরন করেছিলেন দেশের জন্য আত্মত্যাগ। ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর চামেলীবাগের বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় জল্লাদরা সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেনকে। আজো সবাই প্রতীক্ষায় থাকেন হয়তো তিনি ফিরে আসবেন! কারন তাঁর মৃতদেহ ফেরত পাওয়া যায়নি। আরো অনেকের মতো সারা স্বদেশকে নিজের কবর করে হয়তো কোথাও কোনো কোনে শেষ শয্যা পেতেছেন এই সুর্য সন্তান।
স্বাধীনতার প্রাক্কালে ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসর আল-বদর ও রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা তাঁকে তাঁর চামেলীবাগের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। এরপর তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেন ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাক-এর কার্যনির্বাহী ও বার্তা সম্পাদক। তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে এ দেশের বঞ্চিত মানুষের কথা অসাধারণ দক্ষতায় সংবাদপত্রের পাতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।
১৯৭১ সালে অবরুদ্ধ এই দেশে সাহসিকতার সঙ্গে সাংবাদিকতা করে গেছেন সিরাজুদ্দীন হোসেন। তিনি প্রবাসী সরকারের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের আমেরিকান কনস্যুলেটের গোপন প্রতিবেদনটি পাঠিয়েছিলেন, যা পরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বারবার প্রচারিত হওয়ার পর বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে উঠতে সাহায্য করে। তিনি ছিলেন এ দেশে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জনক। সিরাজুদ্দীন হোসেন ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনয়ন লাভ করেছিলেন।
শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেনের পুত্র সাংবাদিক শাহীন রেজা নুর যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনালে প্রদত্ত জবানবন্দি এখানে প্রাসঙ্গিকঃ
চেয়ারম্যান বিচারপতি এটিএম ফজলে কবিরের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ তিনি জবানবন্দী প্রদান করেছেন। জবানবন্দীতে সাক্ষী বলেন, আলবদর সদস্য চৌধুরী মাঈনুদ্দীন ও আশরাফুজ্জামান খান বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। একাত্তরে দেশের শীর্ষ স্থানীয় দৈনিকগুলোতে এ খবর ছাপা হয়েছিল। মুজাহিদ সেই আলবদর বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন। তাঁরই তত্ত্বাবধান, পরিচালনা ও নির্দেশনায় বুদ্ধিজীবী নিধন চলে।
এক ঘণ্টার বেশি সময় দেয়া জবানবন্দিতে শাহীন রেজা নূর ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর রাতে তাঁর বাবা সিরাজউদ্দীন হোসেনকে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিবরণ দেন। তিনি বলেন, তাঁর বাবা সিরাজউদ্দীন হোসেন ওই সময় ইত্তেফাক-এর নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক নিবন্ধ লিখে তিনি তাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। তাই তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।
শাহীন রেজা নূর আরও বলেন, ১৮ ডিসেম্বর রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে সেলিনা পারভীনসহ অনেক বুদ্ধিজীবীর লাশ পাওয়া গেলেও তাঁর বাবার লাশ পাওয়া যায়নি। জবানবন্দী শেষে তাঁকে জেরা করেন মুজাহিদের আইনজীবী মুন্সি আহসান কবির। ১৬ অক্টোবর পরবর্তী জেরার দিন ধার্য করা হয়েছে। এ সময় আসামির কাঠগড়ায় মুজাহিদ উপস্থিত ছিলেন।
সাক্ষী তার জবানবন্দীতে আরও বলেন, ওই দিন রাত আনুমানিক ১২টা থেকে সাড়ে ১২টার দিকে আমাদের ৫নং চামিলীবাগের বাসার দরজায় প্রচ- কড়া নাড়ার শব্দে আমার বাবা বাইরে বের হয়ে টর্চ মেরে কাউকে না দেখে আবার ঘুমিয়ে পড়েন। পরে রাত ৩টা থেকে সাড়ে ৩টার দিকে আবারো দরজার কড়া নাড়ে। তখন আমি দরজা একটু ফাঁক করতেই ৫/৬টি বন্দুক তাক করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই ৭/৮জন লোক হ্যান্ডসআপ বলে ঘরের ভেতরে ঢোকে। আমারা হাত উঁচু করে দাঁড়াই। সঙ্গে বাড়িওয়ালার শ্যালক ও আমার ছোট ভাই ছিল।
তিনি বলেন, আগত লোকগুলো ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় উর্দু বলছিল এবং তাদের মুখে মাংকি টুপি ও গলায় মাফলার দিয়ে মুখ ঢাকা ছিল।
শাহিন রেজা নুর জবানবন্দীতে বলেন, ‘আমাদের হৈ চৈ শুনে মা-বাবা জেগে ওঠেন। তখন গানপয়েন্টে ৪/৫ জন লোক আমাদের নিয়ে ভেতরে ঢোকে। বাবার পরনে সেন্ডু গেঞ্জি ও নীল রঙের লুঙ্গি। তিনি আলনা থেকে একটি পাঞ্জাবি নিতে চাইলে একজন হ্যান্ডসআপ, হ্যান্ডস আপ বলে চেঁচিয়ে উঠল। তখন বাবার হাত থেকে পাঞ্জবিটা পড়ে যায়। লোকগুলো ভাঙ্গা উর্দুতে জিজ্ঞেস করে ‘কিয়া নাম হ্যায়, তুম কিয়া করতা হ্যায়’। জবাবে বাবা বললেন, ‘সিরাজুদ্দিন হোসেন, এক্সিকিউটিভ এডিটর ডেইলী ইত্তেফাক’। তারা বলল- ‘আও হাম লোক কা সাথ।‘ তারা বাবাকে পিঠে বন্দুক ঠেকিয়ে নিয়ে গেল। ওই সময় তারা একটি গামছা চায়। মা গামছা খুঁজতে খুঁজতে কান্নাকাটি করছিল। তারা বাবাকে নিয়ে যায় এবং যাওয়ার সময় বলে ‘বাহার আয়েগাতো গুলি খায়েগা।’ শুনতে পেয়েছি মাইক্রোবাসে করে বাবাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
শহীদ সিরাজুদ্দীন হোসেন ১৯২৯ সালের মার্চে মাগুরা জেলার শালিখা থানার শরম্নশুনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে টানাপড়েনের সংসারে তিনি বড় হতে থাকেন। মাত্র তিন বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। তার অসহায় মা ছোট ছোট সনত্মান নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। এ সময় সিরাজুদ্দীন হোসেনের বড় চাচা মৌলভী মোহাম্মদ ইসহাক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। চাচা মৌলভী মোহাম্মদ ইসহাক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। চাচার কাছে থাকাকালে সিরাজুদ্দীন মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর স্কুল ও যশোর জেলা স্কুলসহ প্রভৃতি স্কুলে পড়াশোনা করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি চাচার কাছ থেকে চলে এসে তার ভগ্নিপতির কাছে থাকেন। কিন্তু নানা অসুবিধাজনিত কারণে তিনি সেখান থেকে চলে আসেন। শেষে যশোর ঝিকড়গাছার মিছরিদিয়ারা গ্রামে এক বিধবা পরিবারে জায়গির থেকে তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যান। এ বিধবার বাড়ি থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন এবং যশোর মাইকেল মধুসূদন কলেজে আইএতে ভর্তি হন। আইএ পাস করার পর সিরাজুদ্দীন হোসেন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে বিএ পড়া শুরু করেন। কলেজজীবনে তার বইপুস্তক কেনার মতো আর্থিক অবস্থা না থাকার কারণে তিনি সব সময় সহপাঠীদের বই নিয়ে এবং অধ্যাপকদের বক্তৃতা নোট করে পড়া তৈরি করতেন। এভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে লেখাপড়া করে ১৯৪৭ সালে তিনি বিএ পাস করেন। এ সময় 'দৈনিক আজাদ'-এ সিরাজুদ্দীন হোসেন সাংবাদিকতা শুরু করেন। তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে আজাদের বার্তা সম্পাদক পদে উন্নীত হন। ১৯৫৪ সালে আজাদ থেকে বেরিয়ে ঢাকার ইউএসআইএস অফিসে জুনিয়র এডিটর হিসেবে কাজ করেন এবং এক বছর পর তিনি ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক নিযুক্ত হন।
সিরাজুদ্দীন হোসেন দীর্ঘদিন ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক থাকার পর ১৯৭০ সালে নির্বাহী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এর আগে ১৯৬৬ সালে আইয়ুবী দুঃশাসনামলে ইত্তেফাক বন্ধ হয়ে গেলে সিরাজুদ্দীন হোসেন সংবাদ প্রতিষ্ঠান পিপিআই-এর ব্যুরো চীফ নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে ইত্তেফাক পুনরায় প্রকাশিত হলে তিনি পিপিআই থেকে ইত্তেফাকে ফিরে আসেন। এভাবে তিনি তার মহৎ কর্মপ্রবাহ দিয়ে জাতীয় উন্নয়নে নানামুখী ভূমিকা রেখেছেন।
ব্যক্তিগত জীবনে সিরাজুদ্দীন হোসেন ছিলেন সৎ ও আদর্শবান, বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ। তার লেখালেখি শুধু সংবাদকেন্দ্রিক ছিল না। নানা সৃজনশীলতার পরিচায়ক তার নানা মাত্রিক রচনা। তিনি ছিলেন অনুবাদ কর্মের নিপুণ কারিগর। গদ্য রচনাতেও তার অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। অনুবাদ ছাড়াও 'ছোট থেকে বড়ো', 'মহীয়সী নারী', 'ইতিহাস কথা কও' প্রভৃতি গ্রন্থের জনক তিনি। বাংলাদেশের পূর্ণ ইতিহাস রচনার জন্য সিরাজুদ্দীন হোসেন বহু নোট লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তার সাংবাদিকতা মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের মানুষকে অপার প্রেরণা দিয়েছে।
তাঁর স্ত্রীর নাম নূরজাহান সিরাজী।তাঁদের পুত্ররা হলেন প্রকৌশলী নাসিম রেজা নূর, প্রকৌশলী শাহিদ রেজা নূর, দৈনিক প্রথম আলোর সহকারী সম্পাদক জাহিদ রেজা নূর, পিএইচডি গবেষক তৌহিদ রেজা নূর, ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক ও প্রজন্ম '৭১'র সভাপতি শাহীন রেজা নূর।
না শহীদ সিরাজুদ্দিন হোসেন আর ফিরে আসেননি। ফিরে আসেননি আমাদের এই স্বাধীন বাংলায়। আমাদের স্বাধীনতার মুল্য দিতে গিয়ে দিয়ে দিলেন নিজের প্রান। লাখো শহীদের রক্তে রাঙ্গা আমাদের জাতীয় পতাকার সেই লাল সুর্যের দিকে তাকাতেই ঝাপসা হয়ে আসে চোখ।লাল সালাম!
শহীদ স্মৃতি অমর হোক।
জয় বাংলা।
_________________________________________
http://www.amarblog.com/animeshrahman/posts/156703
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ২০:০৯582864
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ ২০:০৯582864- রক্তে ভেজা নীল আকাশঃ ০১-শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন
লিখেছেনঃ অনিমেষ রহমান (তারিখঃ শনিবার, ১৫/১২/২০১২ - ১৮:২৮)
_____________________________________________________
একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হতে চলেছে_
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্য,হে স্বাধীনতা।
-কবি শামসুর রাহমান
বাংলাদেশের নীল আকাশ সেদিন লাল হয়ে গিয়েছিলো হায়নার অস্ত্রের আঘাতে। ঝরে ঝরে পড়ছিলো লালরক্ত বাংলার জমিনে।টেকনাফ থেকে তেতুলিয়াতে রক্ত ঝরতে ঝরতে সেদিন মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকার উপকন্ঠে।চারদিকে চাপা উল্লাসের পদধ্বনি। ঠিক সেই মুহুর্তে সংগঠিত হলো ইতিহাসের নির্মম হত্যাযজ্ঞ।
পরাজয় নিশ্চিত জেনে পরাজিত পাকিস্তানী বাহিনী নবউদীয়মান জাতিকে চিরতরে স্তব্দ করে দিতে তাদের এদেশীয় জামাতি দোসর-রাজাকার, আল বদর, আল-শামস এবং বিহারীদের নিয়ে ঘঠিত কিলিং স্কোয়ার্ডের মাধ্যমে খুন করে দেশের শিক্ষক-সাংবাদিক-ডাক্তার সহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। যেনো বাংগালী জাতি মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। আজকে ঠিক ৪০ বছর পরে আর শাস্তি দাবী কিংবা প্রমান নিয়ে কথা বলার দরকার নেই-শুধু চেয়ে দেখি কেমন ছিলেন আমাদের জন্য প্রান দিয়ে যাওয়া সেই মানুষগুলি। যারা হারিয়ে গেলেন সেই ভয়াল ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১এ।
আজকে শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভিনের কথা লিখছি। শুনুন তাঁর একমাত্র পুত্র সুমন জাহিদের ভাষায়ঃ
আমার মা সেলিনা পারভীন। শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন। তাঁর হারিয়ে যাওয়ার কাহিনীটি আমার কাছ থেকে কোনোদিন হারিয়ে যাবে না। আমার মায়ের হারিয়ে যাওয়ার দিনটি আমার জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ ও দুর্ভাগ্যজনক দিন।
সেদিন ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল। দেশ স্বাধীন হতে আর মাত্র তিন দিন বাকি। কোনো কোনো অঞ্চল ইতিমধ্যে মুক্ত হয়ে গেছে। আমরা তখন ছিলাম সিদ্ধেশ্বরীতে, তত্কালীন ১১৫নং নিউ সার্কুলার রোডে। আমাদের বাসায় আমরা তিনজন মানুষ- আমি, মা আর আমাদের উজির মামা। সেদিন শীতের সকালে আমরা ছাদে ছিলাম। মা আমার গায়ে তেল মাখিয়ে দিয়েছেন। একটু পর তিনি আমাকে গোসল করতে নিয়ে যাবেন। আমি ছাদে খেলাধুলা করছি আর মা একটা চেয়ার টেনে কী যেন লিখছেন। শহরে তখন কারফিউ। রাস্তায় মিলিটারি। পাকিস্তানী বাহিনীকে আত্মসমর্পণের জন্য বিমান থেকে চিঠি ফেলা হচ্ছে।
হঠাত্ দূরে একটা গাড়ির আওয়াজ হলো। আমাদের বাসার উল্টো দিকে খান আতার বাসার সামনে E.P.R.TC-এর ফিয়াট মাইক্রোবাস ও লরি থামে। সেই বাসার প্রধান গেইট ভেঙে ভিতরে ঢুকে গেল কিছু লোক। আমরা তিনজন ছাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে এই দৃশ্যটা দেখলাম।
কিছুক্ষণ পর মা আমাকে গোসল করানোর জন্য নিচে নিয়ে আসেন। গোসলের পর আমি আবার ছাদে চলে যাই। আর মা যান রান্না করতে। ছাদে আমার সঙ্গে উজির মামাও ছিলেন।
এরপর আবার গাড়ির শব্দ। এবার একটি গাড়ি এসে থামে আমাদের বাসার সামনে। ছাদে দাঁড়িয়ে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে আমরা দেখি কয়েকজন লোক আমাদের বাসায় ঢুকছে। তাদের সবাই একই রঙের পোশাক পরা ও মুখ রুমাল দিয়ে ঢাকা। এরা বাসার প্রধান লোহার কলাপসিবল দরজার কড়া নাড়ছে। আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের এক ভদ্রলোক বের হয়ে কলাপসিবল গেইট খুলে দেয়। গাড়িতে করে আসা লোকগুলো ভদ্রলোকের কাছে সেলিনা পারভীনের পরিচয় জানতে চায়। ভদ্রলোক আমাদের ফ্ল্যাটটি দেখিয়ে দেন। ভদ্রলোককে ঘরে চলে যেতে বলে লোকগুলো আমাদের ফ্ল্যাটে এসে কড়া নাড়ে। মা দরজা খুলে দেন। লোকগুলো মার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয় এবং বাসায় কে কে থাকে তাও জেনে নেয়। এ সময় মার সাথে লোকগুলোর বেশ কিছু কথা হয়। আমি আর উজির মামা ততক্ষণে সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা উঁকি দিলে ওরা দেখে ফেলে। আমাদের দিকে বন্দুক তাক করে। আমি ও উজির মামা ভয় পাই। মা আমাদের ডেকে নিয়ে লোকগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। আমি মার কাছে চলে আসি। এরপর মাকে তাদের সাথে যেতে বলে লোকগুলো।
মা লোকগুলোকে বলেন, 'বাইরে তো কারফিউ। এখন যাব কীভাবে?' লোকগুলো বলে, 'আমাদের সাথে গাড়ি আছে। তাছাড়া আমাদের সাথে কারফিউ পাশও আছে। কোনো সমস্যা হবে না।' ওরা নাছোড়বান্দা, আম্মাকে নিয়ে যাবেই। মা তখন বলেন, 'ঠিক আছে। আপনারা অপেক্ষা করুন। আমি শাড়ি বদল করে আসি।' ওরা বাধা দেয়। বলে, 'দরকার নেই। গাড়িতে করে যাবেন আবার গাড়িতে করেই ফিরে আসবেন।' আমিও তখন মার সাথে যেতে চাই। কিন্তু লোকগুলো আমাকে ধমক দিয়ে বলে, 'বাচ্চা লোক নেহি জায়েগা।' উজির মামা কিছু বলতে চাইলে তাঁকেও বলে, 'বাড়াবাড়ি করবেন না।'
আমি তখন মার খুব কাছে। তাঁর হাত ধরে আছি। মা আমার মাথায় হাত বুলান। তিনি আমাকে বলেন, 'সুমন তুমি মামার সাথে খেয়ে নিও। আমি যাব আর চলে আসব।' এই ছিল আমার জীবনে মার কাছ থেকে শোনা শেষ কথা।
এভাবেই সেদিন অনেকেই তাঁর প্রিয় মানুষদের শেষ কথা বলে গেছেন বলেই আজকে আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশ। লাখো বাঙ্গালী যুদ্ধের ময়দানে আর সেলিনা পারভিনের মতো মানুষেরা অবরুদ্ধ ঢাকায় বিভিন্নভাবে আমাদের মুক্তির যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন।শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন কিভাবে যুক্ত ছিলেন আমাদের মুক্তির লড়াইয়েঃ
১৯৬৯-এর রাজনৈতিক আন্দোলনে উত্তাল বাংলাদেশ৷ নিজেও শরিক হন গণঅভ্যুত্থানের আন্দোলন কর্মকাণ্ডে৷ ছেলেকে সঙ্গে নিয়েই বেরিয়ে পড়তেন '৬৯-এর ২১ ফেব্রুয়ারি পল্টনের জনসভায় বা শহীদ মিনার থেকে বের হওয়া নারীদের মিছিলে যোগ দিতে৷ শরিক হতেন বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদে আর সভায়ও৷ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার প্রমুখদের সাথে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে সমাজতন্ত্রের প্রতিও আস্থাশীল হয়ে পড়েন তিনি৷ এরই মধ্যে শুরু হলো ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ৷ মুক্তিযুদ্ধের সময় সেলিনা পারভীন ঢাকায় ছিলেন৷ তাঁর বাসায় মাঝে মাঝে রাত হলে কয়েকজন তরুণ আসতেন৷ খাওয়া-দাওয়া করে চলে যাওয়ার আগে এরা সেলিনা পারভীনের কাছ থেকে সংগৃহীত ঔষধ, কাপড় আর অর্থ নিয়ে যেতেন৷ শিলালিপির বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়েই তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করতেন৷ এই তরুণদের সকলেই ছিলেন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা৷
চারিদিকে তখন চলছে আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ, প্রতিরোধ৷ চারপাশে শুধু বুলেটের শব্দ আর বারুদের গন্ধ, চিৎকার, গোঙানি, রক্তস্রোত আর মৃত্যু৷ এরই মাঝে ললনা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম৷ শিলালিপির উপরও নেমে আসে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর খড়্গ৷ হাসেম খানের প্রচ্ছদ করা একটি শিলালিপির প্রকাশিতব্য সংখ্যা নিষিদ্ধ করে দেয় পাকিস্তান সরকার৷ পরে অবশ্য প্রকাশের অনুমতি মিললো তবে শর্ত হলো নতুনভাবে সাজাতে হবে৷ সেলিনা পারভীন বরাবরের মতো প্রচ্ছদ না নিয়ে তাঁর ভাইয়ের ছেলের ছবি দিয়ে প্রচ্ছদ করে আগস্ট-সেপ্টেম্বরের দিকে শিলালিপির সর্বশেষ সংখ্যা বের করেন৷ কিন্তু এর আগের সংখ্যার জন্যই সেলিনা পারভীন পাকিস্তানী ও তাদের দালালদের নজরে পড়ে যান৷ যেটাতে ছিল দেশ বরেণ্য বুদ্ধীজীবীদের লেখা এবং স্বাধীনতার পক্ষের লেখা৷ তাই কাল হলো৷ শিলালিপির আরেকটি সংখ্যা বের করার আগে নিজেই হারিয়ে গেলেন৷
১৩ ই ডিসেম্বর ধরে নিয়ে যাবার পর তাঁর মরদেহ পাওয়া যায় রায়েরবাজার বধ্যভুমিতে। যার চোয়ালে ছিলো বেয়নেটের খোঁচার দাগ আর বুকে গুলিঃ
১৮ ডিসেম্বর সেলিনা পারভীনের গুলিতে-বেয়নেটে ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া যায় রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে৷ খুব শীতকাতুড়ে সেলিনার পায়ে তখনও পড়া ছিল সাদা মোজা । এটি দেখেই তাঁকে সনাক্ত করা হয় । ১৪ ডিসেম্বর আরও অনেক বুদ্ধিজীবীর মতো পাকিস্তানের দালাল আলবদর বাহিনীর ঘৃণিত নরপশুরা সেখানেই সেলিনা পারভীনকে হত্যা করে৷ ১৮ ডিসেম্বরেই তাঁকে আজিমপুর কবরস্থানে শহীদদের জন্য সংরক্ষিত স্থানে সমাহিত করা হয়৷
সেলিনা পারভিনঃ সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি
জন্ম : সেলিনা পারভীনের জন্ম বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার ছোট কল্যাণনগর গ্রামে ১৯৩১ সালের ৩১ মার্চ। বাবা মৌলবি আবিদুর রহমান, মাতা মোসাম্মৎ সাজেদা খাতুন। শৈশবে পিতৃদত্ত নাম ছিল মনোয়ারা বেগম মনি। ১৯৫৪ সালে এফিডিয়েন্ট করে সেলিনা পারভীন নাম নেন।
শিক্ষাজীবন : ফেনী সরলা বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ১৯৪২ সালে ছাত্রজীবন বিঘ্নিত হয়। ফিরে যান গ্রামের বাড়ি ছোট কল্যাণনগরে। ১৯৪৯ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় (প্রাইভেট) অংশগ্রহণ। উত্তীর্ণ হতে পারেননি।
পরিবার : সম্ভবত ১৯৪৩ সালে তত্কালীন সামাজিক অবস্থার চাপে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে। স্বাধীনচেতা সেলিনা পারভীন সে সংসার করেননি। ১৯৪৮-এ বিবাহবিচ্ছেদ। পরে ১৯৬২ সালে বিবাহ হয় ফেনীর ছাগলনাইয়া নিবাসী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর-এর সঙ্গে। একমাত্র পুত্র সুমন জাহিদের জন্ম ১৯৬৩ সালের ৩১ মে। বিবাহবিচ্ছেদ ১৯৬৬ সালে।
কর্মজীবন : ফেনীতে ছাত্র পড়িয়ে কর্মজীবন শুরু। ১৯৫৬ সালে ঢাকায় আসেন। ১৯৫৭ সালে মিডফোর্ড (বর্তমানে সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ) হাসপাতালে নার্সিং ট্রেনিং গ্রহণ। ১৯৫৯ সালে রোকেয়া হলে মেট্রনের চাকরি। ১৯৬৬ সালে আজিমপুর বেবিহোমে শিক্ষকতা। ১৯৬৬ সালে 'সাপ্তাহিক বেগম' পত্রিকায় সম্পাদিকার সহকারী হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৭ সাল থেকে আমৃত্যু 'সাপ্তাহিক ললনা'য় কাজ করেন।
পত্রিকা সম্পাদনা : 'শিলালিপি' ১৯৬৯ সাল। পত্রিকাটির প্রকাশনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব একাই পালন করতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় পত্রিকাটির প্রচ্ছদ ও অন্যান্য রচনা পাকসেনা প্রধানের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি।
শখ : ছবি আঁকা, সংগীত চর্চা, ব্লক তৈয়ারি এবং ডিজাইনের কাজেও পারদর্শী ছিলেন।
মুক্তিযুদ্ধে অবদান : ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকায় গেরিলা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সক্রিয় সহায়তা দান। মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর জীবনের কর্মকান্ডের প্রায় সমস্ত তথ্যই হারিয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যা শত্রুর জন্য ক্ষতিকর হয়েছিল।
মৃত্যু : একাত্তরের ১৩ ডিসেম্বর আলবদর বাহিনীর লোকেরা তাঁর সিদ্ধেশ্বরীর বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। ১৪ ডিসেম্বর অন্যান্য দেশ বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের সাথে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ১৮ ডিসেম্বর শহীদ সেলিনা পারভীনের দাফন হয় আজিমপুর নতুন গোরস্থানে।
আজকে চষে বেড়াই আমরা ঢাকা শহর-কেউ কেউ চষে বেড়াই সারা দুনিয়া।জীবন-জীবিকার কারনে! আমাদের স্বাধীন আকাশ করতে গিয়ে যারা চলে গেলেন অবেলায়-তাঁদের প্রতি আমাদের ঋন শেষ করতে পারবো? কিংবা জাতি হিসেবে আমাদের উত্থানে তাঁদের ত্যাগ প্রতিদিন আমাদেরকে আরো ঋনি করে দেয়। সময় হয়েছে ঋন শোধ করার-রুখে দাঁড়াই ঘাতকদের। আবারো ঐক্যবদ্ধ হই ৭১ এর চেতনায়।
জয় বাংলা!!
__________________________________________
http://www.amarblog.com/animeshrahman/posts/156648#comment-1324332
 বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ২৫ ডিসেম্বর ২০১২ ১৫:৪২582865
বিপ্লব রহমান | 212.164.212.14 | ২৫ ডিসেম্বর ২০১২ ১৫:৪২582865- শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী
যুদ্ধাপরাধের বিচার ও স্মৃতিতে একাত্তর
ডিসেম্বর ২১, ২০১২
____________________________________________________________
১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই তো বাঙালিরা বুঝে গেল তারা প্রতারিত হয়েছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র ভিন্ন ধরনের ভিন্ন চেহারার শাসকদের দ্বারা বাঙালিকে আবার সেই একই শোষণ ও দমনের চক্রে বেঁধে ফেলল। বাঙালি বুঝল, প্রভু বদল হয়েছে মাত্র, তাদের অবস্থার বদল নয়। তাই প্রতিবাদ শুরু হয়ে গেল পাকিস্তানের জন্মের এক বছরের মধ্যেই। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের বীজ পোঁতা হয়ে গেল।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে পাকিস্তানের তখনকার জাতীয় নেতা বা জাতির জনক হিসেবে অভিহিত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহের বক্তব্য ‘উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা’ ছাত্রদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করেছিল। আর প্রত্যক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন এদেশের ছাত্র-জনতা।
এরপরের আড়াই দশক পাকিস্তানিদের দ্বারা বাঙালিদের নানাভাবে নিপীড়িত হওয়ার করুণ গল্প। সে গল্পের পথ ধরেই না আমাদের স্বাধীনতালাভের অনিবার্যতা, একটি যুদ্ধের মাধ্যমে অনেক অর্জনের স্বত:স্ফুর্ততা।
একাত্তরের প্রতিটি দিনের স্মৃতিই যেন আমার কাছে এই সেদিনের মতো। বাঙালি তখন কী বিপুল আবেগে অপেক্ষা করছে স্বাধীনতার জন্য। আশা ছিল আলোচনার মাধ্যমেই পাকিস্তানের বাঙালি-অধ্যুষিত অংশটি আলাদা একটি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাবে। যেভাবে ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান।সে লক্ষ্যেই ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আলোচনা চলছিল। আলোচনা যখন ভেস্তে গেল তখন সাধারণ মানুষই বুঝে গেলেন একটি যুদ্ধ অনিবার্য।
বাঙালি জাতি কিন্তু এই যুদ্ধের ব্যাপারে মনে মনে প্রস্তুত ছিলেন। তাই ৩ মার্চেই ছাত্রনেতারা বঙ্গবন্ধুর হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিয়েছিলেন।বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দিলেন। কিন্তু ২৫ মার্চের সেই অতর্কিত হামলার বিষয়টি ছিল আমাদের অজানা। জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে পাকিস্তানের সামরিক সরকার হামলার পরকল্পনা করেছিল।তারা ওই রাত থেকে শুরু করে সারা বাংলায় যে বিরাট পরিকল্পিত গণহত্যা চালিয়েছিল- যে হত্যাযজ্ঞে পাক হানাদার বাহিনীকে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছিল এদেশেরই রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী, এটা তো ইতিহাসের অন্যতম নৃশংস গণহত্যা।
এটুকু ইতিহাস বাঙালি জানেন। নতুন করে বলার কিছু নেই। তবু আজ বারবার ভাবতে হয়, বলতেও হয় যখন যুদ্ধাপরাধের জন্য অভিযুক্তদের পক্ষে কাউকে কাউকে সাফাই গাইতে দেখি। যখন শুনি এদেশের জনগণের ওপর যে ব্যাপক ও পরিকল্পিত গণহত্যা চালানো হয়েছিল, তার জন্য দায়ী জামায়াত ইসলামীর নেতারা দায়ী নন। রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনীর যে ঘৃণ্য তৎপরতা আমাকে নিজের চোখে দেখতে হযেছে, যাদের বর্বর সহযোগিতায় আমার স্বামী আলীম চৌধুরী নিহত হয়েছেন- আজ ক্ষোভের সঙ্গে দেখতে হয়, শুনতে হয় তারা নাকি কোনো অন্যায়ই করেনি! তারা সুফি, ধর্মপ্রাণ মুসলমান! তাদের অহেতুক বিচারের মুখোমুখি করে হয়রান করা হচ্ছে। আমার মতো শহীদ পরিবারগুলোর পক্ষে এ ধরনের কথা শোনা যে কত কষ্টের তা বলে বা লিখে বোঝানো মুশকিল।
পঁচিশে মার্চের কালরাত ও তার পরের ন’মাসের কিছু স্মৃতি এখানে তুলে ধরছি। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ইয়াহিয়ার আলোচনা ভেস্তে যাওয়ায় অনেকেই ঢাকা ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়েছিলেন। আমরা যাইনি নানা কারণে। আমরা তখন থাকতাম পুরানা পল্টনে। বাবা ছিলেন অসুস্থ। পুরোপুরি পক্ষাঘাতগ্রস্থ। তাই তাঁকে নিয়ে ওই মুহুর্তে ঢাকার বাইরে যাওয়াটা অসম্ভব ছিল। তাছাড়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ওই রাতে তিনি তাঁর বাসা ছেড়ে আমাদের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁকে রক্ষা করা তখন আমাদের একটি দায়িত্ব হয়ে গিয়েছিল। তাঁকে দেখলাম, ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছেন। মুখটা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। দেশ একটি বড় বিপর্যয়ৈর মুখে, এ ভাবনা তাঁকে আলোড়িত করছিল।
আমরা দেখলাম, আমাদের বাসায়ও তিনি নিরাপদ নন। কারণ তাঁর আত্মীয়ের বাসা বলে তাঁকে খুঁজতে পাকবাহিনী এখানে চলে আসতে পারে। তাই তাঁকে নিরাপদে সরিয়ে ভারতে পাঠানোর পরিকল্পনা হল। আমার মা আর শাশুড়ি তখন তাঁকে বোরকা-শাড়ি পেরিয়ে, মাথায় খোঁপা বেঁধে দিয়ে, পায়ে মেয়েদের জুতো পরিয়ে দিলেন। পরে আমার ভাই তাঁকে রিকশায় করে অলি-গলি ঘুরে ঘুরে হোসেনী দালানে পৌঁছে দিলেন। ওখান থেকে তিনি পরে চলে গেলেন ভারতে।
এ ঘটনার পরও আমরা পুরো ন’মাসই ওই বাসায় থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছি। আমার স্বামী ডা. আলীম চৌধুরী তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই এ বাসায় এবং চেম্বারে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার সুযোগ করে দিতেন। তাই সবাই এ বাসার কথা জানত। পঁচিশে মার্চ রাত এগারোটা পর্যন্ত তিনি অনেককে নিজে গাড়ি চালিয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়ে এসেছেন।
তাই পরের মাসগুলোতে আমাদের ঠিকানা ছিল অনেকের জন্য নিরাপদ আশ্রয়। বিপদ দেখলে আলীম কখনও কখনও মুক্তিযোদ্ধাদের চোখে ব্যান্ডেজ বেঁধে শুইয়ে রেখে দিতেন রোগী বানিয়ে। টাকা-পয়সা তো সবই দিয়ে দিয়েছি। তখন বেশিরভাগ দেশপ্রেমিক বাঙালিই তাই করতেন। শুধু নিজেদের চলার টাকাটা রেখে বাকিটা যুদ্ধের জন্য বিলিয়ে দিতেন।
আমাদের বাসায় এভাবে লুকিযে আশ্রয়-প্রশ্রেয় পেতেন বলেই কিনা কে জানে, জুলাইয়ের এক বৃষ্টির দিনে বাসায় এসে হাজির হল একজন। তার নাম মওলানা মান্নান, সেই ইনকিলাবের মান্নান। সে ছিল আশ্রয়প্রার্থী। বলল, পাকিস্তানিরা তার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, ছেলেমেযে নিয়ে কোথায় যাবে, চার-পাঁচ দিন থাকতে চায় ইত্যাদি ইত্যাদি। আলীম রাজি হয়ে গিযেছিলেন। কিন্তু আমার একদম প্রথম দেখাতেই লোকটাকে ভালো লাগেনি। তাই বেঁকে বসলাম, না, এর জায়গা হবে না। তিনি খুব অবাক হলেন। কারণ কত মানুষকে আমরা এ বিপদে সাহায্য করেছি, আর মান্নানের বেলায় আপত্তি কেন? তিনি বুঝতে পারছিলেন না। পরে আমার শাশুড়ি যখন আমাকে এসে এ কথাটা বললেন, তাঁর মুখের ওপর আর ‘না’ বলতে পারলাম না। কিছু করতে না পেরে অঝোরে কাঁদলাম। মনে হচ্ছিল কী যেন একটা সর্বনাশ হযে গেল আমার। মানুষের বোধহয় সিক্সথ সেন্স থাকে!
মান্নান তো ওই ক’টা দিন থাকল না, পরে আমাদের নিচতলাটা ভাড়া নিয়ে নিল। ক’দিন পর জানাল, সে আলবদর বাহিনীর অন্যতম সংগঠক।আমাদের সদর দরজা পাহারা দিতে শুরু করল পাকিস্তানি আর্মির সহযোগী ওই বাহিনীর সদস্যরা। পরনে আলবদরদের পোশাক। ছাই রঙের প্যান্ট আর নীল শার্ট। হাতে অস্ত্র। আলীম খুব বিরক্ত হতেন। আর মান্নান বলত, ‘আপনার বাসায় আছি বলে মুক্তিযোদ্ধারা আমাকে মারবে না, তাই আলবদররাও এ বাড়ি পাহারা দেয়।’ পরে বুঝেছিলাম, আলীমের আশ্রয়ে থেকে সে আসলে মুক্তিযোদ্ধাদের হাত থেকে বেঁচে গিযেছিল।
এরপর কয়েক মাস এভাবে কেটে গেল। আলীমকে মাঝে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে বদলি করা হল। উনি কিছুদিন ওখানে থেকে পরে আবার পারিবারিক সমস্যা দেখিয়ে বদলি হয়ে মিটফোর্ডে চলে এলেন। কারণ আমি তখন দুই শিশুকন্যা নিয়ে অসহায়। বাবা বিছানায়। এ অবস্থায় উনি তো দূরে থাকতে পারেন না। আলীমকে বদলি করা হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের জন্যই। আলীম অনেককে সাহায্য করছেন এ খবর প্রশাসনের কাছে নিশ্চয়ই ছিল।
তিনি ফিরে এলেন ৩ নভেম্বর। ডিসেম্বরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পরিণতির দিকে যাচ্ছে। ভারতীয় মিগ আকাশজুড়ে চক্কর দিচ্ছে, বোমা ফেলছে দেখে আলীম বলতেন, ‘পাকিস্তানিরা বোকার স্বর্গে বাস করছে। ভাবছে যুক্তরাষ্ট্র বুঝি সপ্তম নৌবহর নিয়ে এসে ওদের যুদ্ধে জিতিয়ে দেবে। এটা হবে না। শিগগির আমরা স্বাধীনতা পাচ্ছি।’
এরপর এল ১৫ ডিসেম্বর। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে আলবদরদের একটি গাড়ি এসে থামলিআমাদের বাড়ির সামনে। এরকম রোজই আসে। আমরা আলাদা করে কিছু ভাবিনি। আমরা দুজন বারান্দায় বসে গল্প করছিলাম। ওরা আলীমকে নিয়ে যেতে চাইল, এক কাপড়ে, শীতবস্ত্র ছাড়া। আলীম তখন নিচে মান্নানের বাসার দরজায় আঘাত করতে লাগলেন। মান্নান সবসময় বলত, ‘আমি আছি তো, আলবদররা আপনাকে কিছু বলবে না।’ অথচ তখন আলীমের এত ধাক্কাধাক্কির পরও দরজা খুললই না। বরং ভেতর থেকে বলে দিল, ‘আপনি যান, কোনো ভয় নেই।’
আলীমকে ওরা নিযে চলে গেল। আমি দৌড়ে গেলাম তার বাসায়। আমাকেও বারবার আশ্বাস দিয়ে রাখল সে। নির্ঘুম, দুশ্চিন্তায় ঘেরা একটি রাত কাটানোর পর এল ১৬ ডিসেম্বর। সকালে দেখলাম ঢাকা জুড়ে এক উৎসবের আমেজ। মানুষ জাতীয় পতাকা নিয়ে চলাফেরা করছে। বুঝলাম আমরা স্বাধীন হয়ে গেছি। কিন্তু আলীম কোথায়? আমি পথে পথে ঘুরে তাকে খুঁজলাম। কোথাও পেলাম না। মান্নান পালিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা বাসায় এলেন। বললেন, কোথায় সে মান্নান যে আলীমকে খুন করেছে!
আমি ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি আলীম নেই। এক পরিকল্পিত ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন তিনি। এরপর তো তাঁর লাশই পেলাম।
মওলানা মান্নান ধরা পড়েছিল। আবার ছাড়াও পেয়েছে। আসলে ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গিয়েছিল তখন থেকেই। তাই বুঝি পরে একটা প্রজন্মকে আমরা কোনো ইতিহাস জানতে না দিয়ে বড় করে তুললাম। এ প্রজন্ম ঠিকঠাক ইতিহাস জানতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর কথা শোনেনি। বুদ্ধিজীবী হত্যার কথা বোঝে না। একচল্লিশ বছরেও রাজাকারদের বিচার হয়নি বলে ওরা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে গিয়েছে। জিয়া, এরশাদ আর খালেদা জিয়ার সরকার ওদের পুনর্বাসন করেছেন।
এখন বিচার ওদের হতেই হবে। নইলে আমরা জাতি হিসেবে অস্তিত্বের সংকটে পড়ব। এই যে হ্যাকিং করছে ওরা, বিচার বানচালের চেষ্টা করছে, কোটি কোটি টাকা দিয়ে লবিস্ট নিয়োগ করে বিচার ভিন্নখাতে নিতে চাচ্ছে- এসব চলতে দেওয়া যাবে না। সব ষড়যন্ত্র দূর করে আমরা যুদ্ধাপরাধের বিচার করতে পারব বলেই আমি আশাবাদী।
http://opinion.bdnews24.com/bangla/2012/12/21/%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE/
 বিপ্লব রহমান | 127.18.231.28 | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ০৯:৩২582866
বিপ্লব রহমান | 127.18.231.28 | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ০৯:৩২582866- তোমাদের যা বলার ছিলো, বলেছে কি তা বাংলাদেশ?
লিখেছেন: বিপ্লব রহমান
___________________________________________________________
এক। প্রজন্ম ‘৭১ এর সাইদুর রহমানের সঙ্গে আমার পরিচয় সাংবাদিকতার শুরুতে সেই ১৯৯২ – ৯৩ সালের দিকে। তখনও রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে বর্তমান শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতি সৌধটি গড়ে ওঠেনি। তবে সে সময় প্রজন্ম ‘৭১ নিজ উদ্যোগে একটি ছোট্ট স্মৃতিসৌধ গড়ে সেখানেই প্রতিবছর ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আসছিলো। সরকারের কাছে এ নিয়ে তারা অনেক ধর্ণা দিয়েও সরকার পক্ষকে উদ্যোগি করতে পারেননি।
সে সময় ‘সাপ্তাহিক খবরের কাগজ’ এ অরক্ষিত রায়ের বাজার বধ্যভূমির ওপর একটি প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করার জন্য আমি শহীদ বুদ্ধিজীবী পরিবারগুলোর সঙ্গে একে একে দেখা করে সাক্ষাৎকার নিতে শুরু করি।
দুই। সে সময় সাইদুর রহমানের সঙ্গে আমার কথা হয় তার কর্মস্থল মতিঝিলের একটি ব্যাংকের সদর দপ্তরে। তিনি বলছিলেন ‘৭১ সালের কথা।
তখন তিনি পাঁচ-ছয় বছরের শিশু। সৈয়দপুরে যৌথ পরিবারের আদরে আনন্দময় শৈশব জীবন কাটছে তার। ‘৭১ এর উত্থাল দিনগুলোতে বিহারী রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি হিসেবে চিহ্নিত তাদের বাড়ি আক্রমণ করে বসে।
বাড়ির বড়রা শিশু সাইদুর আর তার পিঠেপিঠি দুই বোনকে একটি বড়ো ঘরে খাটের নীচে হাঁড়িকুড়ির পেছনে লুকিয়ে রাখেন।
তারপরেই ঘটে যায় তার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি!
রাজাকাররা ওই ঘরে সাইদুরের মা-বাবা, অন্যান্য ভাই-বোন, আত্নীয় – স্বজন সবাইকে ধরে এনে কসাইয়ের মতো জান্তব উল্লাসে রাম দা দিয়ে একে একে কুপিয়ে হত্যা করে!
আর এ সবই ঘটে যায় শিশুটির চোখের সামনে। জীবনের ভয়ে ছোট্ট সাইদুর টুঁ শব্দটি করার সাহসও পায়নি।
তিন। এর পর বহুবছর ওই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের স্মৃতি তাকে তাড়া করে ফেরে। বেশ কিছুদিন শিশুটি মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভুগেছে। এখনো স্বজনের আর্তনাদ তাকে আর ১০টা মানুষের মতো স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে দেয় না।…
ব্যাংকার সাইদুর রহমান যখন তাঁর এই দুঃসহ স্মৃতিকথা আমাকে বলছিলেন, তখন বার বার গভীর বেদনায় কুঁকড়ে যাচ্ছিলো তার মুখ, ভেঙেচুরে যাচ্ছিলো তার কন্ঠস্বর!
কথা বলতে বলতে তিনি বলপয়েন্ট দিয়ে নিউজপ্রিন্টের একটি প্যাডের পাতায় কাটাকুটি করে কি যেনো একটি কথা বারবার লিখছিলেন।
সাক্ষাৎকার শেষে তার অনুমতি নিয়ে আমি নিউজপ্রিন্টের ওই কাগজটি চেয়ে নেই। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, অনেক কাটাকুটির ভেতর ঝকঝকে হরফে তিনি একটি কথাই বারবার লিখেছেন:
তোমাদের যা বলার ছিলো, বলেছে কি তা বাংলাদেশ?
তোমাদের যা বলার ছিলো, বলেছে কি তা বাংলাদেশ?
তোমাদের যা বলার ছিলো, বলেছে কি তা বাংলাদেশ?
শেষ পর্যন্ত খবরের কাগজের ওই প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের ভেতর স্ক্যান করে সাইদুর রহমানের হাতে লেখা নিউজপ্রিন্টের টুকরো অংশটিও তুলে দেওয়া হয়। লেখাটির শিরোনামও দেই:
তোমাদের যা বলার ছিলো, বলেছে কি তা বাংলাদেশ?
প্রতিবেদনটিতে সরকারি উদ্যোগে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে একটি স্মৃতিসৌধ গড়ার জন্য শহীদ পরিবারগুলোর আকুতি তুলে ধরা হয়। পরে প্রজন্ম ‘৭১ এই লেখার শিরোনাম নিয়ে একটি পোস্টারও প্রকাশ করে।
চার। এরপর বিএনপি সরকার বদ্ধভূমিতে স্মৃতিসৌধ স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করলেও এর নথি আর উর্ধ্ব দিকে ধাবিত হয় না। সাইদুর রহমানসহ প্রজন্ম ‘৭১ এর সদস্যরা সরকারি উচ্চ মহলে দৌড়-ঝাঁপ শুরু করেন। তবু কিছুতেই কিছু হয় না। একটি একটি করে বছর গড়ায়।
প্রজন্ম ‘৭১ এর নিজেদের গড়া ছোট্ট স্মৃতি সৌধটি প্রতি বছর ভেঙে পড়ে। প্রতি বছর পিলার আকৃতির ওই সৌধটি ১৪ ডিসেম্বরের আগে আবার গড়া হয়। আবারও দিন যায়।
শেষে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে স্মৃতি সৌধর সরকারি প্রকল্পটি আলোর মুখ দেখে। তৈরি হয় বর্তমান সৌধটি।
পাঁচ। সাপ্তাহিক খবরের কাগজের ওই প্রচ্ছদ প্রতিবেদন লেখার পর বহুবছর সাইদুর রহমানের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই।…
২০০০ সালের দিকে একুশে টেলিভিশনের (ইটিভি) কারওয়ান বাজারের ভবনে কি একটা কাজে বিখ্যাত সাংবাদিক সায়মন ড্রিং এর কাছে গিয়েছি। লিফটের ভেতর এক অচেনা ব্যক্তি আমার নাম ধরে ডাকেন। লোকটিকে আমার খুব চেনা চেনা মনে হলেও আমি তাকে পুরোপুরি চিনে উঠতে পারি না। তখন তিনি নিজের নাম বলতেই হঠাৎ এক নিমিষে আমার মনে পড়ে যায় সব।
সাইদ ভাই তখন ইটিভিতে সংবাদ পাঠক হিসেবে খণ্ডকালীন কাজে যোগ দিয়েছেন। ইটিভি বন্ধ হওয়ার পর তিনি চ্যানেল আই এ সংবাদ পাঠ করতে থাকেন।
এখনো প্রায় রাতে চ্যানেল আই সংবাদ দেখতে বসলে আমি তাকে খবর পড়তে দেখি। মাঝে চ্যানেল আই টক-শোতে কয়েকবার অংশ নিয়েছি। প্রতিবার কাজ শেষে সাইদ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে এসেছি।
নতুন করে শুরু হওয়া ইটিভির একটি অনুষ্ঠানে কিছুদিন আগে আবারো দেখি তাকে। সেদিন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নে একটি টক-শোতে সরাসরি প্লাজমা টিভিতে স্টুডিওতে হাজির সাইদুর রহমান।
তিনি খুব স্পষ্ট গলায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করে বললেন:
যতদিন এই বিচার না হবে, ততদিন অন্তত আমি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাইতেই থাকবো। … এমন কি মৃত্যূর সময় শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে যদি একটি মাত্র মুহূর্ত পাই, তখনও এ দেশের মানুষের কাছে বলবো, আমি এর বিচার চাই!…
___
http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=31837
 বিপ্লব রহমান | 127.18.231.28 | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ০৯:৩৯582867
বিপ্লব রহমান | 127.18.231.28 | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ০৯:৩৯582867- অপারেশন মোনায়েম খান কিলিং
বিপ্লব রহমান
________________________________________________
১
তার সঙ্গে আমার পরিচয় বছর চারেক আগে দৈনিক যুগান্তরে কাজ করার সময়। তখন বন্যায় ঢাকার নিম্নাঞ্চল ডুবতে শুরু করেছে।মোজাম্মেল হক, বীর প্রতীক (৫০) আবার ঢাকার উপকণ্ঠ ভাটারা ইউনিয়ন পরিষদ
চেয়ারম্যান। তো বন্যা দুর্গত আর ও ত্রাণ তৎপরতা নিয়ে তিনি তখন খুব ব্যস্ত। কালো রঙের একটি সেড তোলা টুপি পড়ে দিনরাত মোটর সাইকেল দাবড়ে বেড়াচ্ছেন।
আমি মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সাহসী ভূমিকার কথা আগেই জেনেছিলাম পত্রিকা পড়ে। সে সময় তাঁর ব্যস্ততার কারণে অবশ্য এ নিয়ে কথা হয়নি। তবু পেশাগত সম্পর্কের বাইরে এক ধরনের শ্রদ্ধাপূর্ণ বন্ধুত্ব হয়। মানুষ হিসেবে তিনি খুব স্পষ্টবাদী, কাউকে তোয়াক্কা করা তার ধাঁতে নেই।
সে সময় একগাদা সাংবাদিকের সামনে এক দুপুরে চরম বিরক্তির সঙ্গে তিনি বলেই ফেললেন, “খোকা ভাই (মেয়র সাদেক হোসেন খোকা) আসবেন
বিকালে। এর আগে ত্রাণ দিতে উনি নিষেধ করেছেন। মেয়র হিসেবে উনি ত্রাণ কাজের উদ্বোধন করতে চান! আরে মিয়া, সেই সকাল থেকে বন্যার্তরা এক হাতা খিচুড়ি খাওয়ার জন্য রোদের মধ্যে বসে আছে। খিদা কি আর এই সব মেয়র - ফেয়র, আর টিভি ক্যামেরা বোঝে? ত্রাণ লাগাও, ত্রাণ লাগাও। মেয়র আসলে তখন দেখা যাবে!”
তার নির্দেশে তখনই খিচুড়ি বিতরণ শুরু হয়ে যায়।
স্থানীয় বিএনপি নেতারা আর পুলিশ কর্মকর্তারা কী যেনো তাকে বোঝাতে চান, মাইকের শব্দে ভাল করে বোঝা যায় না। মোজাম্মেল ভাই শুধু মাথা নাড়েন। মাছি তাড়ানোর মতো বার দুয়েক হাত নাড়েন নেতা আর পুলিশ কর্তাদের উদ্দেশে।
জনপ্রিয় এই মানুষের সঙ্গে ঘন্টা তিনেক আলাপচারিতা হয় সেদিন। বিষয় -- মহান মুক্তিযুদ্ধ। প্রিয় পাঠক, আসুন তারই বয়ানে শুনি, ১৯৭১ এর সেই আগুন ঝরা দিনগুলোর কথা। শুনি, কিশোর মুক্তিযোদ্ধার সেই দুর্ধর্ষ 'অপারেশন মোনায়েম খানকিলিং'এর কথা।...
“১৯৭১ সালে আমি শাহীনবাগের স্টাফ ওয়েল ফেয়ার হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। বয়স মাত্র ১৪ বছর। বাড্ডা, ভাটারা, ছোলমাইদ তখন পুরোপুরি গ্রাম। মাইলের পর মাইল ধানের ক্ষেত, খাল - বিল - জলায় বিস্তৃর্ণ এলাকা। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টও তখন খুব কাছে মনে হয়। পাকিস্তানী সেনারা প্রায়ই আমাদের গ্রামের আশেপাশের মাঠে প্রশিক্ষণ নিতো।...আমার বাপ - চাচারা সবাই কৃষক, নিরক্ষর মানুষ। আমরা স্কুলে পড়ি। পড়ার ফাঁকে তাদের কৃষিতে সাহায্য করি, গরু চড়াই।”
“২৫ মার্চের রাতে বাবা ধানী জমিতে সেচ দিচ্ছিলেন। আমি গিয়েছি তাঁর জন্য খাবার নিয়ে। হঠাৎ ক্যান্টনমেন্ট থেকে গুলির শব্দ। মর্টারের ফায়ার আর ফ্লেয়ার গানের আলোয় পুরো আকাশ মাঝে মাঝে ঝলসে ওঠে।... বাবা বললেন, যুদ্ধ শুরু হয়েছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি চল।”
আমি তাকে জিগেষ করি, “আপনি ওই বয়সে যুদ্ধে গেলেন কোন চেতনা থেকে?”
তিনি বলেন, “তখন ওই বয়েসেই ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের পাক সেনাদের অত্যাচারের বেশ কিছু কথা আমরা শুনেছিলাম। গ্যারিসন সিনেমা হলে স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন আমাদের গ্রামের এক লোক। পাক সেনারা তাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে তার স্ত্রীকে গণধর্ষণ করে। এছাড়া আমাদের গ্রামের পাশে প্রশিক্ষণ নিতে এসে তারা সদ্য প্রসূতি আরেক গৃহবধূকেও গণধর্ষণ করে।”
“আমরা বাসে চড়লে অবাঙালী কন্ডাক্টর - হেল্পাররা আমাদের সিট থেকে তুলে দিয়ে বিহারীদের সেই সিটে বসতে দিতো। তাছাড়া সে সময়ের ছাত্রলীগ নেতা, বিকমের ছাত্র আনোয়র হোসেন (বীর প্রতীক) ভাই আমাদের বলতেন, পূর্ব পাকিস্তানে কাগজের কল হওয়া সত্বেও এখানে কাগজের দিস্তা যখন ১৪ আনা, তখন পশ্চিম পাকিস্তানে কাগজের দাম ছিলো ৬ আনা। বাবার কাছে শুনেছিলাম, ১৯৬১ - ৬২ তে পাকিস্তান সরকার আমাদের তিন একর জমি অধিগ্রহণ করে মাত্র দেড় হাজার টাকা দাম দিয়েছিল।”
“আনোয়ার ভাই বলতেন, দেশ স্বাধীন করে বাঙালিদের নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করা না গেলে এই সব অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। ২৫ মার্চের পর রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের খবরে শুনতাম পাক সেনাদের বর্বরতার কাহিনী। শুনতাম মুক্তি বাহিনীর অগ্রযাত্রার খবর। এ সবই আমাদের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে।”
মোজাম্মেল হক বলে চলেন, “আমি অন্য তিন চাচাতো ভাই আজাহারুল ইসলাম বকুল, গিয়াস উদ্দিন ও আবু সাঈদের সঙ্গে পরামর্শ করলাম, এক রাতে রহিমুদ্দীন ও আনোয়ার ভাইয়ের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে কুমিল্লা বর্ডার দিয়ে ত্রিপুরা যাবো। সেখানে ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করবো। কিন্তু পরিকল্পনা বাড়িতে আগেই ফাঁস হয়ে যাওয়ায় আমি, বকুল আর সাঈদ পালাতে পারিনি। অন্য ঠিকই ত্রিপুরা চলে গিয়েছিলো।”
“এদিকে আমার মন মানে না। স্বাধীন বাংলা বেতারের খবর শুনি, দেশের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে। মনে হয়, সব তরুণ - যুবারা যুদ্ধ করছে, আর আমরা মায়ের আঁচলের ছায়ায় আরাম - আয়াশে আছি। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়। ১০ - ১৫ দিন বাড়িতে বসে থাকার পর আমি আর সাঈদ আবার যুক্তি করলাম, বাড়ি থেকে পালাবো, যুদ্ধে যাবো। এবার বাবা - মাকে বললাম, যদি টাকা - পয়সা দিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি না দাও, তাহলে টাকা - পয়সা ছাড়াই বাড়ি থেকে পালাবো। তখন বাপ - চাচারা পরামর্শ করে টাকা - পয়সা দিয়ে আমাদের যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দেন।”
“তাহলে শেষ পর্য়ন্ত বাড়ির সম্মতিতে যুদ্ধে যান?”
“হ্যাঁ, আমি আর সাঈদ কিছু টাকা জুতোর ভেতর আলাদা করে লুকিয়ে, জামা - কাপড় গুছিয়ে এক রাতে রওনা হই। নরসিংদী পর্যন্ত বাসে, তারপর লঞ্চে কমিল্লার নবীনগর। শুনেছিলাম, কুমিল্লার সিএনবি রোড পার হলেই ত্রিপুরার বর্ডার। পথে পথে শত শত মানুষের দেখা পাই, যারা পরিবার - পরিজন নিয়ে দলে দলে শারণার্থী হিসেবে ভারত যাচ্ছেন। কেউ বা আবার যাচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে। কুমিল্লা পৌঁছে আমরা একটি রিকশা ভাড়া নেই সিএনবি রোড যাবো বলে।”
“কিন্তু রিকশা ওয়ালা আমাদের ঘুর পথে নিয়ে যেতে যেতে সন্ধ্যা করে ফেলে। তখন আমরা রিকশা ছেড়ে দিয়ে হাঁটা শুরু করি। পথ - ঘাট কিছুই চিনি না। এক লোক আমাদের এসে বলে, আপনারা আমার বাসায় চলেন, রাতটা কাটান, ভোরে আমরাই আপনাদের বর্ডার পার করে দেবো। আমরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক।”
“উপায় না দেখে আমরা সেই রাতে ওই লোকের বাসায় উঠি। রাতে খাবারের জন্য একটা মোরগ কিনবে বলে সেই লোক আমাদের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নেয়। সারারাত বর্ডারে মর্টার বিনিময়ের শব্দ শুনি। গোলাগুলি বন্ধ হলে ভোরের দিকে দুজন লোক আমাদের সিএনবি রোডে নিয়ে যায়। তারা গোমতি নদী দেখিয়ে বলে, ওই পারে ইন্ডিয়া। লোক দুজন আমাদের পকেট হাতড়ে টাকা - পয়সা সব রেখে দেয়। জুতার ভেতরে লুকানো সামান্য কিছু টাকা তখন আমাদের শেষ সম্বল।”
“লুঙ্গী পরে ছোট্ট গোমতি নদী হেঁটে পার হই। ত্রিপুরা সীমান্তের উঁচু পাহাড় দেখা যায়।”
আমি বলি, “তাহলে, সীমান্ত পার হয়ে ট্রেনিং নিলেন। আর যুদ্ধ শুরু হলো?”
“আরে নারে ভাই, অত সহজে হয় নাই। প্রথমবার ভয়ে পালিয়ে এসেছি। ওপারে গিয়ে কোনাবন হয়ে কলেজটিলা ট্রিনিং ক্যাম্পে পৌঁছাই। সেখানে ক্যাম্প চিফ ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা রশিদ ভাই। সেখানে আমাদের ১৫ দিন রাখা হয়। থাকা - খাওয়ার অবস্থা আর বলতে! খাবার বলতে শুধু ডাল আর ভাত। আর ডাল যে দুর্গন্ধ হতে পারে, তা বলার নয়। আমরা রশিদ ভাইকে অতিষ্ট করে মারি, ভাই, আমাদের ট্রেনিং এ পাঠাবেন না?”
“তিনি আমাদের পাঠালেন পাশের নির্ভয়পুর ট্রেনিং ক্যাম্পে। সেখানে পৌঁছে দেখি, ক্যাম্পের নামই শুধু নির্ভয়পুর, আসলে নবাগতদের ভয় পাওয়ানোর মতো সব রকম ব্যবস্থাই সেখানে আছে। ট্রেনিং নিতে আসা মুক্তিযোদ্ধাদের সবার ‘চোখ উঠেছে’। জ্বর আর ডায়রিয়ায় একেকজনের অবস্থা কাহিল। পরিস্থিতি দেখে নামধাম রেজিস্ট্রি করার আগেই আমার চাচাতা ভাই বেঁকে বসে। সে আমাকে বলে, ‘চল, আমরা পালিয়ে দেশে ফিরে যাই। এখানে ট্রেনিং নিতে গেলে আর বাঁচতে হবে না। যুদ্ধের আগেই অসুখে এখানেই আমাদের মরতে হবে!’...তার কথা শুনে আমি সত্যি সত্যি ভয় পাই। সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে আমরা চোরের মতো পালিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আবার গ্রামে ফিরে আসি।”...
২
“রোগ - শোকের ভয়ে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং না নিয়েই ত্রিপুরা থেকে দুই ভাই পালালেন, দেশে গ্রামের বাড়িতে ফিরলেন। তারপর?” আমি তাকে জিজ্ঞেস করি। মোজাম্মেল হক একটু স্থির হয়ে দম নেন। তারপর স্মৃতি হাতড়ে বলতে শুরু করেন আবার।
“তো ঢাকার গ্রামের বাড়ি ভাটারায় ফিরে সবার কাছে সত্যি কথাটাই বললাম। বাড়ির লোকজন তো মহাখুশী, যাক, ঘরের ছেলে ভালোয় ভোলোয় ঘরে ফিরেছে। ওই সব যুদ্ধের ভুত পালিয়েছে।”
“তখন রহিমুদ্দীন মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে। সে আমাকে বলে, ইন্ডিয়ায় যে গেরিলা ট্রেনিং নিয়েছি! আর হাতিয়ার আমাদের দিয়েছে! বুঝলি, তোদের মতো ভীতুদের আর দরকার নেই। এবার আমরাই দেশ স্বাধীন করে ফেলবো।”
“রহিমুদ্দীনের কথাটা আমার খুব মনের ভেতরে গিয়ে লাগে। ১০ - ১৫ দিন খুব অস্থিরতার মধ্যে কাটে। একদিন তাঁকে আবার ধরি, রহিম ভাই, আমি ভুল করেছি, তুমি আমাকে ট্রেনিং এ পাঠাও। আমি যুদ্ধে যাবো। সে কিছুতেই রাজী হয় না। শেষে আমাকে বলে, মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার আগে তোমাকে সাহসিকতার পরীক্ষায় পাস করতে হবে। পাস করলে তারপর দেখা যাবে।”
“আমি রাজী হলে, জুন - জুলাই মাসে রহিমুদ্দীন এক সন্ধ্যায় আমাকে একটি হ্যান্ড গ্রেনেড দেয়। এর ব্যবহার শিখিয়ে দিয়ে বলে, এই বোমার ৩৬ টি টুকরো আছে। এটি ফাটলে ৩০ গজের মধ্যে যারা আছে, তারা সবাই মারা যাবে। তোমাকে এটি বিদেশীদের মার্কেটে মারতে হবে। পারলে সাহসিকতার পরীক্ষায় পাস।”
“পরে গ্রেনেডটিকে আমি প্যান্টের পকেটে নিয়ে রহিমুদ্দীনসহ গুলশান ২ নম্বর ব্রিজের পাকিস্তানী চেক পোস্ট সহজেই পার হয়ে যাই। সেখানে পাক সৈন্যদের সহায়তা করতো যে বাঙালি, সে আমাদের গ্রামেরই এক লোক। তাছাড়া ছাত্র হিসেবে আমার পরিচয়পত্র ছিলো। আমার অসুবিধা হয় না।”
“দুজনে একটা বেবী ট্যাক্সি নিয়ে গুলশান ১ নম্বর ডিআইটি মার্কেটে যাই। সেখানে বিদেশীদের আনাগোনা। রহিমুদ্দীন ‘রেকি’ করে বলে, এখানে সুবিধা হবে না, প্রচুর মিলিটারির পাহারা।”
“আমরা দুজনে একটি আরেকটি বেবী ট্যাক্সি নিয়ে মহাখালি টিবি হাসপাতাল গেটের দিকে যেতে থাকি। পথে বিদেশী পতাকা ওড়ানো একটি বাসা দেখি। ট্যাক্সি ঘুরিয়ে আবারো ওই পথে যাওয়ার সময় রহিমুদ্দীন আমাকে ইশারা করে। আমি চলন্ত বেবী ট্যাক্সি থেকে গ্রেনেডটির পিন খুলে ওই বাড়ির ভেতর ছুঁড়ে মারি।”...
“কিছুদূর যাওয়ার পরেই বিকট শব্দে গ্রেনেডটি বিস্ফোরিত হয়। অবাঙালি বেবী চালক ব্রেক কষে আমাদের বলে, কেয়াঁ হুয়া হ্যায়? রহিমুদ্দীন তাকে ধমকে বলে, বোমা ফুটায়া! সালে লোগ, চালাও বেবী!”
“কিছুদূর গিয়ে আমরা বেবী ছেড়ে দিয়ে ঘুর পথে বাড্ডায় এক আত্নীয়র বাসায় ওই রাতটি কাটাই। পরদিন পত্রিকায় দেখি, বড় বড় হেড লাইনে খবর -- দুস্কৃতিকারীরা বিদেশী দূতাবাসে গ্রেনেড হামলা করেছে! সেটি কোন দূতাবাস ছিল, এখন আর মনে নেই।”...
*
“তারপর?” বালক - বিস্ময়ে আমি জানতে চাই।
মোজাম্মেল ভাই বলেন, “আর কী! রহিমুদ্দীনের পরীক্ষায় পাস। একদিন রাতে বাড়িতে ফিরে দেখি মা কাঁঠালের পিঠা বানিয়েছেন। সেই পিঠা খেতে খেতে মাকে আমি বলি, মা, আমি কাল সকালেই ট্রেনিং নিতে ইন্ডিয়া যাবো। আমাকে কিছু টাকা দিতে পারো?”
“মা বলেন, তোর বাবা তো বাড়িতে নেই। আর আমার কাছে তো টাকা - পয়সা থাকে না। দেখি, তোর চাচীর কাছে কিছু পাওয়া যায় কী না।”
“মা টাকা ধার করতে চাচীর বাসায় গেছেন। একটু পরে চাচা এসে আমাকে ধমকানো শুরু করলেন, এই সব কী? দুদিন পর পর যুদ্ধ, যুদ্ধ করে বাসায় অশান্তি করা! একবার আমার ছেলেকে (চাচাতো ভাই সাঈদ। ওই যে অসুখ - বিসুখের ভয়ে আমরা দুজন ত্রিপুরা থেকে ট্রেনিং না নিয়েই পালালাম!) উস্কানী দিয়ে ইন্ডিয়ায় নিয়ে গেলি। ট্রেনিং না নিয়েই পালিয়ে এলি। এখন আবার ট্রেনিং এর যাওয়ার জন্য বায়না ধরা।... এবার যেতে হলে তুই একই যা। আমার ছেলেকে সঙ্গে নিবি না!”
“আমি বললাম, টাকা দাও, না দাও, এবার আমি যাবোই। একাই যাবো, মরতে হলে একাই মরবো। তোমার ছেলেকে এবার নেবো না।”
“তো পরদিন ভোরে মা’র ধার করা ২৪৬ টাকা নিয়ে আমি গুলশান ২ নম্বর বাস স্ট্যান্ডে যাই। সেখানে মুক্তিযোদ্ধা রহিমুদ্দীন আগে থেকেই আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। দুজনে ইপিআরটিসির বাস ধরে ভাঙা পথে কুমিল্লা পৌঁছাই। আবার সেই গোমতি নদী পর হয়ে পৌঁছাই মেলাঘর ট্রেনিং সেন্টারে। সেখানে ২ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর এটিএম হায়দার আমাকে দেখেই রহিমুদ্দীনকে ধমক, কী সব পোলাপাইন নিয়ে এসেছো! এই সব দিয়ে কী যুদ্ধ করা যায়? রহিমুদ্দীন আমার পক্ষে ওকালতি করে বলে, স্যার, ও ছোট হলেও খুব সাহসী। ঢাকার বিদেশী দূতাবাসে হ্যান্ড গ্রেনেড চার্জ করেছে!”
“শুরু হলো ট্রেনিং? কী কী অস্ত্র চালানো শিখলেন?”
“হ্যাঁ, মেজর হায়দারের সম্মতিতে এইবার সত্যি সত্যি গেরিলা ট্রেনিং শুরু হলো মেলাঘরে। ২১ দিনের ট্রেনিং এ আমি লাইট মেশিন গান (এলএমজি), কয়েক ধরণের রাইফেল, স্টেন গান, প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, এন্টি ট্যাংক মাইন, ১৬ ইঞ্চি মাইন, ফসফরাস বোমা, গ্রেনেড থ্রোইং, অ্যামবুশ প্রশিক্ষণ নেই।”
“২১ দিন পর ১৫ জন নিয়ে আমাদের ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গেরিলা গ্র“প তৈরি হলো। এর গ্র“প কমান্ডার হলেন এমএন লতিফ। আর সেই রহিমুদ্দীনকে করা হলো ডেপুটি কমান্ডার।”
“একদিন মেজর ফেরদৌস, ক্যাপ্টেন আয়েন উদ্দীন ও আনোয়ার হোসেন (বীর প্রতীক) আমাদের একটু ভাল খাইয়ে - দাইয়ে রাতের বেলা বিদায় দিলেন। কিন্তু যাদের সীমান্ত রেকি করতে পাঠানো হয়েছিলো, তার ঠিক ভাবে ডিউটি না করেই ক্লিয়ারেন্স দেয়। আমরা ১৫ জন কুমিল্লার সিএনবি রোডে উঠতেই পাক সেনাদের অ্যামবুশের মুখে পড়লাম। তিন - চারটা ব্যাংকার থেকে শুরু হলো ক্রমাগত মেশিনগানের গুলি।”
“ওই রাতে এক পাট ক্ষেতে পালিয়ে পরদিন বুকে ভর দিয়ে একটু একটু করে আবার ইন্ডিয়ার মেলাঘরে পৌঁছাই। দেখি আমরা ১৫ জনই অক্ষত আছি। কিন্তু মেজর হায়দার এবার বেঁকে বসলেন, এদের মর্যাল ডাউন হয়ে গেছে। এদের দিয়ে আর যুদ্ধ হবে না! তিনি নির্দেশ দিলেন, আমাদের কোনো একটি গেরিলা ইউনিটে গোলা বারুদ বহনকারী হিসেবে যোগানদারের দায়িত্ব পালন করতে!”
*
মোজাম্মেল হক বলে চলেন, “এই কথায় সবার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। এতো কষ্ট করে ট্রেনিং নিলাম, আর শেষে কী না যোগানদার! আমরা কী যুদ্ধ করবো না!”
“আমি বুদ্ধি করে প্রতিদিন রুটিন করে মেজর হায়দারের অফিসের সামনে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে লাগলাম। ১৫ - ২০ দিন পর উনি আমাকে ডেকে বললেন, এই তোর কী হয়েছে? প্রত্যেক দিন এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস কোনো? আমি বলি, স্যার আমাদের যুদ্ধে পাঠান। আমরা মরতে ভয় পাই না। মেজর সাহেব বলেন, তোদের দিয়ে তো যুদ্ধ হবে না। তোদের মর্যাল বলতে আর কিচ্ছু নেই। আমি নাছোড়বান্দা, না স্যার। আমরা পারবো। আমাদের একটা অপারেশন দিয়েই দেখুন না!”
“মেজর হায়দার বলেন, তুই কাউকে মারতে পরবি? কোনো চিন্তা না করেই বলি, স্যার, পাকিস্তানের স্পীকার আব্দুল জব্বার খানকে মারতে পারবো। মেজর সাহেব আমাকে একটা চড় মারেন। বলেন, বেয়াদব, জানিস, এটা কতো কঠিন কাজ? আচ্ছা, তুই ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকার বাসিন্দা পাক গভর্নর মোনায়েম খানকে মারতে পারবি?”
“এইবার আমি বলি, স্যার, এটা আমার জন্য অনেক সহজ। আমি তার বাসা চিনি। ছোট বেলায় তার বাসার ওখানে খেলতে গিয়েছি। আমার এক দূর সম্পর্কের জব্বার চাচা তার বাসার গোয়ালা।”
“মেজর হায়দার হেসে হুকুম দেন, গেট টেন, উল্লুক কা পাঁঠা।”
“সঙ্গে সঙ্গে আমি ১০ টা বুক ডন দিতে লেগে যাই। বুঝতে পারি, আমাকে মোনায়েম খান কিলিং অপারেশনের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে!”
“এবার আমি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করি, স্যার, যদি অপারেশন সাকসেস হয়, আমাকে কী পুরস্কার দেবেন?”
“তুইই বল, তুই কী চাস?”
“অপারেশন শেষে আমি আপনার কোমরের রিভলবারটা চাই!”
“গেট লস্ট! উল্লুক কা পাঁঠা!”
“...ক্যাম্পে ফিরে গ্র“পকে এই খবর বলি। কেউ বিশ্বাস করে না। একটু পরে অর্ডার আসে, আমাদের ঢাকায় অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে! খুশীতে সবাই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে।”
“এরপরেও সীমান্তের একটি ছোটখাট যুদ্ধে আমাদের সাহসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। আমরা ১৫ জনের গ্র“প নারায়নগঞ্জের রূপগঞ্জে পৌঁছাই। সঙ্গে যার যার হাতিয়ার জামার নীচে আর ব্যাগের ভেতর লুকানো।”
“সেখান থেকে আমি ভাটারার গ্রামে ফিরি। আমার মাথায় তখন একটাই চিন্তা -- অপারেশন মোনায়েম খান।”...
“আমি মোনায়েম খানের গোয়ালা জব্বার চাচাকে খুঁজে বের করে তাকে সব কিছু বলি। তিনি আমাকে বলেন, তুই তার রাখাল শাজাহানের সঙ্গে খাতির কর। তোর কাজ হবে। খবরদার, আমার কথা কিছু বলবি না!”
“জব্বার চাচা একদিন দূর থেকে শাজাহানকে চিনিয়ে দেন। সে তখন বনানীতে মোনায়েম খানের বাসার পাশে গরু চড়াচ্ছে। আমি তার সাঙ্গে এটা - সেটা গল্প জুড়ি। মোনায়েম খানের ওপর রাখালের খুব রাগ।”
“কথায় কথায় শাজাহান বলে, মোনায়েম খান একটা জানোয়ার! আমাকে বেতন তো দেয়ই না, উল্টো নানান নির্যাতন করে। একেকটা সিন্ধী গাই ২০ - ২৫ সের দুধ দেয়। এক ফোঁটা দুধও আমাকে খেতে দেয় না। গাই দোয়ানোর সময় মোড়া পেতে সে নিজেই বসে থাকে, যেনো দুধ চুরি না হয়। পাঁচবার বাসা থেকে পালিয়েছি। প্রত্যেকবার পুলিশ দিয়ে আমাকে ধরিয়ে এনেছে। মুক্তিরা এতো মানুষকে মারে, এই ব্যাটাকে মারতে পারে না!”
“আরেকটু খাতির হওয়ার পর একদিন শাজাহানকে আমি বলি, আমার সঙ্গে মুক্তিদের যোগাযোগ আছে। আপনি যদি সহায়তা করেন, তাহলে আমি তাদের খবর দেই, আপনি মোনায়েম খানকে মারার ব্যবস্থা করুন। শাজাহান রাজী হয়। আরও দু - একদিন ঘোরানোর পর শাজাহান অস্থির হয়ে পড়ে, কই, আপনার মুক্তিরা তো আসে না!”
“একদিন বিকালে আমি একটি চটের ব্যাগে আমার স্টেন গান, দুটি ম্যাগজিন, একটি হ্যান্ড গ্রেনেড আর একটি ফসফরাস বোমা নিয়ে শাজাহান ভাইয়ের কাছে হাজির হই। তাকে বলি, আজ সন্ধ্যায় একটু দেরীতে গরুগুলোকে মোনায়েম খানের বাসায় ঢোকাতে হবে। আর আমাকে লুকিয়ে নিয়ে যেতে হবে বাসার ভেতর। সেই প্রথম শাজাহান ভাই বোঝেন, এতোদিন আমার কাছে মুক্তিবাহিনীর যে গল্প তিনি শুনেছেন, আমিই সেই মুক্তি বাহিনী! তিনি আমার প্রস্তাবে রাজী হন।”
৩
আমি বলি, “তো অস্ত্র - শস্ত্র নিয়ে মোনায়েম খানের বাসার ভেতর ঢুকলেন? শুরু হলো অপারেশন?”
মোজাম্মেল ভাই বলেন, “ওই দিন বাসার ভেতরে ঢুকতে পারলেও সেদিনই অপারেশন করতে পারিনি। পর পর দুবার ব্যর্থ হই। ... প্রথমবার ওই সন্ধ্যায় মোনায়েম খানের বাসায় ঢুকে গেটের পাশের কলাবাগানের ঝোঁপে ঘাপটি মেরে বসে থাকি। একটু পরে তার রাখাল সেই শাজাহান ভাই এসে খবর দেয়, মোনায়েম খানের শরীর খারাপ। সে দোতলায় উঠে গেছে। দোতলায় যেতে গেলে তার ছেলের ঘরের সামনে দিয়ে যেতে হবে। আবার বাড়ি ভর্তি লোকজন।”
“অপারেশন ওইদিন স্থগিত রেখে আমি সেখান থেকে চলে যাই পাশের বনানী খ্রিস্টান পাড়ায়। সেখানে প্রচুর ইটের পাঁজা ছিল। ইটের পাঁজায় হাতিয়ারের ব্যাগটি লুকিয়ে চলে আসি।”
“পরে আরেকদিন সন্ধ্যায় হাতিয়ারের ব্যাগ নিয়ে শাজাহান ভাইয়ের সঙ্গে আবার মোনায়েম খানের বাসায় যাই। আবার সেই কলাবাগানে ঘাপটি মেরে বসা। কিন্তু তখন একটি উজ্জল বৈদ্যুতিক বাল্বের আলোয় চারপাশের সব কিছু পরিস্কার। আমি অন্ধকারের আড়াল পেতে সেই বাতিটি ইট মেরে ভেঙে ফেলি। এতেই বিপত্তি দেখা দেয়।”
“একজন চাকর ভাঙা বাল্ব দেখে চিৎকার - চেঁচামেচি শুরু করে, বাড়িতে চোর ঢুকেছে! মোনায়েম খানের বাসা পাহারা দিতো যে সব বেলুচিস্তানের অবাঙালি পুলিশ, তারা হুইসেল বাজিয়ে, টর্চ মেরে চোর খোঁজাখুঁজি শুরু করে। আমি বিপদ দেখে আবার পালাই।”
*
আমি বলি, “ও আচ্ছা। কিন্তু এতোদিন পত্রিকায় কিন্তু এই সব ঝক্কি - ঝামেলার কথা পড়িনি। আমি ভেবেছি”...।
মোজাম্মেল ভাই হাসেন, “আরে পত্রিকা ওয়ালারা এতো কথা লিখতে চায় না। ওরা হচ্ছে, সংক্ষেপে বিস্তারিত!”
“তো তারপর তো আমার মন খুব খারাপ। পর পর দুবার অপারেশনে বাধা। আর বুঝি হবে না! এদিকে শাজাহান ভাই ভাটারা এসে একদিন আমাকে ধরে, কী ভাই, যুদ্ধ হবে না? তার কথায় আবার মনোবল ফিরে পাই।”
“এবার সহযোগি হিসেবে সঙ্গে নেই আনোয়ার ভাইকে (আনোয়র হোসেন, বীর প্রতীক)। আবারো সন্ধ্যার পর মোনায়েম খানের বাসার ভেতরের সেই কলাঝোপে দুজন লুকিয়ে বসে থাকি। একটু পরে শাজাহান ভাই এসে খবর দেয়, আজকে অপারেশন সম্ভব। মোনায়েম খান, তার মেয়ের জামাই (জাহাঙ্গীর মো. আদিল) আর শিক্ষামন্ত্রী (আমজাদ হোসেন) বাসার নীচ তলার ড্রইং রুমে বসে গল্প - গুজব করছেন।”
“আমি জানতে চাই, কে মোনায়েম খান, চিনবো কী ভাবে? শাজাহান ভাই জানান, একটি সোফায় তিনজনই একসঙ্গে বসে আছে। মাঝের জনই মোনায়েম খান, তার মাথায় গোল টুপি রয়েছে।...আমি অপারেশনের পরের পরিস্থিতি আন্দাজ করে গোয়লা জব্বার চাচা আর শাজাহান ভাইকে জামা - কাপড় নিয়ে বাসা থেকে পালাতে বলি।”
“শুনশান নিরবতার মঝে হাতিয়ার বাগিয়ে আমরা দুজন মূল বাড়িটির দিকে এগিয়ে যাই। আমার প্ল্যান হচ্ছে, স্টেন গানের একটি ম্যাগজিন পুরো খরচ করবো মোনায়েম খানের ওপর। বাকি দুজনকে আরেকটি ম্যাগজিন দিয়ে ব্রাশ করবো।...ব্যাকআপ আর্মস হিসেবে হ্যান্ড গ্রেনেড আর ফসফরাস বোমা তো আছেই।”
“আমরা বাড়ির ড্রইং রুমের দরজায় পৌঁছে দেখি দরজাটি খোলা। দরজার দিকে মুখ করে তিনজন একটি সোফায় ঘনিষ্টভাবে বসে মাথা নীচু করে কোনো শলা - পরামর্শ করছে। মাঝখানে গোল টুপি মাথায় মোনায়েম খান। আমি স্টেন দিয়ে ব্রাশ করি। কিন্তু একটি মাত্র সিঙ্গেল ফায়ার বের হয়, গুলিটি মোনায়েম খানের পেটে লাগে। সে ‘ও মা গো’ বলে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ...বাকি দুজন ভয়ে ‘বাবা গো, মা গো, বাঁচাও, বাঁচাও’ চিৎকার শুরু করে।...আমার স্টেন গান দিয়ে আর ফায়ার হয় না। আমি ম্যাগজিন বদলে বাকী ম্যাগজিন দিয়ে ফায়ার করার চেষ্টা করি, তাতেও কাজ হয় না। আনোয়ার ভাই সেফটি পিন খুলে গ্রেনেডটি ছুঁড়ে মারেন। এবারো ভাগ্য খারাপ। গ্রেনেডটিও ছিলো অকেজো, সেটি দেয়ালে বারি খেয়ে ফেরত আসে।”
“এদিকে তার বাড়ির বেলুচিস্তানী পুলিশরা চিৎকার - চেঁচামেচি শুনে একের পর এক ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করতে থাকে। আমরা দেয়াল টপকে পালাই।”
“দৌড়ে গুলশান - বনানী লেকের কাছে পৌঁছে দেখি জব্বার চাচা আর শাজাহান ভাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমি আনোয়ার ভাইকে ওদের সঙ্গে লেক সাঁতরে ওপারে চলে যেতে বলি। স্টেন গান নিয়ে আমার পক্ষে সাঁতার দেওয়া হয় না। ...খুঁজতে খুঁজতে আমি একটি কোষা নৌকা পেয়ে যাই। সেটা নিয়ে আমি গুলশান ২ নম্বর ব্রিজের কাছাকাছি আসি।”
“এদিকে গোলাগুলির শব্দে একের পর এক পাক আর্মির ট্রাক মোনায়েম খানের বাসার দিকে রওনা হয়েছে। দূরে বড় রাস্তা দিয়ে ট্রাকের চলাচল দেখি। ওই ব্রিজটির ওপর আর্মির চেক পোস্ট ছিলো। আমি ধরা পড়ার ঝুঁকি নিয়েই ক্রলিং করে ব্রিজের নীচ দিয়ে একটু একটু করে ভাটারা পৌঁছাই।”
“ভাটারা বাজারে তখন একটি চায়ের দোকানে সহযোগি তিনজন আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। স্টেনগান কাঁেধ সেই প্রথম গ্রামের মানুষ আমাকে দেখে। এর আগে তারা কানাঘুষায় শুনেছিল, আমি ট্রেনিং নিয়েছি। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করেনি। তখন আমাকে দেখে ভয়ে সবাই দৌড়ে পালায়। আমি শীতে কাঁপতে কাঁপতে (তখন অক্টোবর মাস) কোন রকমে আনোয়ার ভাইকে স্টেনগান দিয়ে বলি, আমার খুব শরীর খারাপ লাগছে! এর পর আমি জ্ঞান হারাই।”
“জ্ঞান ফিরে আসে রাতে আমার বাড়িতে। দেখি, বাড়ির লোকজন ছাড়াও জব্বার চাচা, শাজাহান ভাই আর আনোয়ার ভাই আমাকে ঘিরে আছেন।
আনোয়ার ভাই বলেন, এখানে থাকা নিরাপদ নয়। আমরা নারায়নগঞ্জের রূপগঞ্জে যাচ্ছি। তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো। আমি তাদের বলি রওনা হয়ে যেতে। আমি রাতটুকু এখানেই বিশ্রাম নিয়ে পরদিন রূপগঞ্জে পৌঁছাবো।”
“পরদিন সকালে ঘুমিয়ে আছি, আমার এক চাচা এসে বললেন, রাতে আকাম করে এসে এখনও তুই বাড়িতে! রেডিও খবরে বলছে, মোনায়েম খান মারা গেছে। এখনই তুই পালা।...আমি রূপগঞ্জে পালিয়ে যাই। সেখানে আমাদের গ্র“পের অন্য সহযোদ্ধারা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।”
এবার আমি একটু অফ ট্র্যাকে যাই। জানতে চাই, “আচ্ছা মোজাম্মেল ভাই, স্বাধীনতার ৩৬ বছরেও তো স্বাধীনতা বিরোধী - যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হলো না। এর কারণ কী বলে মনে হয়?”
মোজাম্মেল হক বলেন, “অতীতে রাজনৈতিক দলগুলো কোনো না কোনো স্বার্থের কারণে জামায়াতসহ স্বাধীনতা বিরোধী -- যুদ্ধাপরাধীদের লালন - পালন করেছে। তারা ক্ষমতার লোভে ঘৃণ্য এই সব চরম অপরাধীদের সঙ্গে আপোষ করেছে।”
“আপনি কী মনে করেন, দল নিরপেক্ষ এই সেনা সমর্থিত তত্ত্ববধায়ক সরকার যে এখন স্বাধীনতা বিরোধী - যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলছে, এই দাযিত্ব তাদেরই নেওয়া উচিৎ?”
“অবশ্যই। সবদেশে সরকার পক্ষই স্বাধীনতা বিরোধী - যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দায়িত্ব নেয়। এই সরকার দুর্নীতি ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে এরই মধ্যে সুনাম কুড়িয়েছেন। এখন তাদের উচিত হবে বক্তৃতাবাজীর বাইরে চরম অপরাধী হিসেবে স্বাধীনতা বিরোধী - যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজটা অন্তত শুরু করা। নইলে আমরা ধরে নেবো, অতীতের সরকারগুলোর মতো দলনিরপেক্ষ এই তত্ত্বাধবায়ক সরকারেরও কোনো কেনো স্বার্থ রয়েছে; তারাও আপোষকামী। এ ক্ষেত্রে অতীতের সরকারগুলোর সাথে তাদের কোনো পার্থক্য থাকবে না।”
তার কাছে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সহযোদ্ধাদের কথা জানতে চাই। মোজাম্মেল ভাই বলেন, “১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলেও মিরপুরে বিহারীদের কাছে প্রচুর অস্ত্র ছিল। তারা তখনও অস্ত্র সমর্পন করেনি। বিহারীদের পরাজিত করতে সে সময় একাধিক যুদ্ধ হয়। আমি নিজেও এরকম কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেই। মুক্তিযোদ্ধা জহিরুদ্দীন ঢালি ও দিল মোহাম্মাদ ঢালি একটি প্রাইভেট কার নিয়ে মিরপুরে ঢোকার চেষ্টার করলে দুই দিক থেকে বিহারীরা গুলি করে তাদের খুন করে। সহযোদ্ধাদের এমন করুন মৃত্যূর খবরে আমি নিজেই তাদের লাশ নিয়ে আসার জন্য অপারেশন চালাই। দেখি, গুলিতে ঝাঁঝড়া হওয়া গাড়ির ভেতরে তাদের দুজন রক্তাক্ত অবস্থায় মরে পড়ে আছেন। তীব্র আক্রমনের মুখে তাদের লাশ আর নিয়ে আসতে পারিনি। কিন্তু সব সময়েই তাদের কথা মনে পড়ে।”...
“আর মুক্তিযোদ্ধাদের তো কেউ ঠিকভাবে মূল্যায়নই করেনি” বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি, “সারাদেশেই সব মুক্তিযোদ্ধারাই অবহেলিত। আর এখন সবখানেই রাজাকার, আলবদর, আল শামসের জয়জয়াকার। ...যখন পত্রিকায় পড়ি, মুক্তিযোদ্ধা রিকশা চালান, ভিক্ষে করেন, তখন মনে হয়, এই রকম বাংলাদেশ তো আমরা চাইনি। ...একদিকে টাকার পাহাড় গড়ে উঠছে, আরেকদিনে মানুষ অভাবে, অনাহারে, অপুষ্টি আর অশিক্ষায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে।...আমাদের দাবি, খুব সামান্য -- মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারগুলোকে যেনো রাষ্ট্র নূন্যতম সন্মান দেয়। কিন্তু গত ৩৬ বছরে কোনো সরকারই এই কাজ করেনি।”
“মুক্তিযোদ্ধাদের দুরাবস্থা দেখে, এখন মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করি, তাহলে কী একাত্তরে আমরা ভুল করেছি? গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জমি - জমা সংক্রান্ত ৫০ টি মিথ্যে মামলায় আমাকে হয়রানী করা হয়। এর মধ্যে ৮ টি মামলায় আমাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে দুমাস জেল খাটতে হয়। অথচ আমি একজন বীর প্রতীক, ইউপি চেয়ারম্যান। তাহলে সারাদেশে অন্য সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের কী অবস্থা, তা তো সহজেই অনুমেয়।”
*
মোজাম্মেল হক, বীর প্রতীকের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতা শেষে আমি যখন ফিরে আসছিলাম, তখন অন্য নানান কথা সঙ্গে তার সেই শেষ কথাটিই বার বার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে, “ তাহলে কী একাত্তরে আমরা ভুল করেছি?”...
__
http://mukto-mona.net/Articles/biplob_rahaman/monayem_killing.htm
 PT | 213.110.243.21 | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ১০:১৫582868
PT | 213.110.243.21 | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ১০:১৫582868- কেউ একটু সারসংক্ষেপ করে দেবেন? বুঝতে সুবিধে হত। নাকি এই আলোচনা শাহবাগ "বিস্ফোরণের" সময় মুজিব-বিদ্বেষ ফেনিয়ে তোলার চেষ্টা?
 বিপ্লব রহমান | 127.18.231.3 | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ১৬:৫৫582869
বিপ্লব রহমান | 127.18.231.3 | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ১৬:৫৫582869- # PT,
একদম ঠিক ধরেছেন! :পি
 বিপ্লব রহমান | 127.18.231.3 | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ১৭:১২582871
বিপ্লব রহমান | 127.18.231.3 | ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ১৭:১২582871- এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়…
লিখেছেন: বিপ্লব রহমান
_________________________________________
‘এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাওয়ার তার শ্রেষ্ঠ সময়’…। কবি হেলাল হাফিজের ‘নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়’ র অমর কবিতা। দ্বিতীয় প্রজেন্মের চলমান মুক্তিযুদ্ধে কবিতাটির অক্ষরগুলো যেনো প্রাণ ফিরে পেয়েছে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে, ১৯৯০ এর জে. এরশাদ সরকার বিরোধী ছাত্র-গণঅভ্যুত্থান থেকে শুরু করে অসংখ্য গণআন্দোলনে, মিছিলে, মিছিলে, গণসমাবেশে, দেওয়াল লিখনে, আন্দোলনের মঞ্চে অসংখ্যবার উদ্ধৃত হয়েছে এই অজয় কবিতা। শাহবাগের মোড় — প্রজন্ম চত্বরকে ঘিরে সারাদেশে চলমান গণজাগরনের মঞ্চগুলোতেও পাঠ হচ্ছে উদ্দীপনী এই কাব্যগাঁথা।
কিন্তু কি ছিলো এই কবিতা রচনার প্রেক্ষাপট? কেমন করে একজন কবির কলমের ডগায় গ্রন্থিত হয় এমন অবিনাশী অক্ষরসমূহ? কোন মন্ত্রবলে লেখা হয় এমন যুদ্ধের আহ্বান?
এইসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে ছাত্রত্ব ঘুচে যাওয়ার পর সাংবাদিকতার শুরুতে, একাধিক সাপ্তাহিকের প্রদায়ক হিসেবে কাজ করার কালে ১৯৯২ সালের দিকে এক পড়ন্ত বিকেলে আরো একজন সহকর্মীসহ মুখোমুখি বসা হয়েছিলো কবি হেলাল হাফিজের। তিনি তখন ‘দৈনিক দেশ’ নামক একটি সংবাদপত্রের সাহিত্য সম্পাদকের দায়িত্বে। সেগুন বাগিচায় ইংলিশ প্যাটার্নের পুরনো যে দোতলা বাড়িতে এখন গড়ে উঠেছে ‘মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর’, সেটিই তখন ছিলো পত্রিকারটি কার্যালয়। সাংবাদিকতায় যুক্ত হওয়ার সুবাদে কবি প্রেসক্লাবের সদস্যপদ পেয়েছিলেন। সেখানেরই গেস্ট ক্যান্টিনে ধূমায়িত চায়ের কাপ নিয়ে বসা গেছে।
এ কথা, সে কথা, কবিতার সঙ্গে কবির সংসার, অনিয়মিত পেশা, আয় ও অনাহার, সব কিছু অকপটে বলতে থাকেন কালো চাপ দাঁড়িতে সৌম্য দর্শনের হেলাল হাফিজ। তার কোনো প্রেম বা দ্রোহের কবিতাই শেষ পর্যন্ত ওই একটিমাত্র কবিতাটিকে ছাপিয়ে যায়নি কেনো? এমন প্রশ্নের জবাবে কবি বেশ খানিকটা থমকে যান। দু-এক মুহূর্ত কপালের দুপাশের রগ দুহাতে চেপে ধরে, চোখ বন্ধ করে ভাবেন। তারপর অনর্গল বলতে থাকেন একটি অক্ষয় কবিতা রচনার আদ্যপান্ত, বলাভালো, ইতিহাস।
সেদিন কবি হেলাল হাফিজ ক্ষুদে সাংবাদিককে যা বলেছিলেন, তা কবির বয়ানে অনেকটা এরকম:
দেখুন, একটি কবিতা একটানেই হয়তো লেখা হয়, কিন্তু এর নির্মাণ প্রক্রিয়া মাথার ভেতরে চলে দীর্ঘ সময় ধরে। বিখ্যাত লেখকেরা একে বলেন, প্রস্তুতিপর্ব। এটি নির্ভর করে শুধু কাব্যভাবনার ওপরে নয়, কবির চারপাশে যা ঘটছে, যা কবিকে ভাবাচ্ছে, অথবা কবি যা ভাবতে চান, সব কিছুর ওপর। বিষয়টি একটি ছোট্ট চারাগাছের জন্মের সঙ্গেই তুলনা করে চলে। এক সকালে আপনি দেখলেন, অনুর্বর জমিতে হয়তো উঁকি মেরেছে একটি ছোট্ট চারাগাছের দুটি কিশলয়। এটি আপনা-আপনি, নিজে নিজে প্রকৃতিতে ঘটে না। চারাগাছ জন্মের জন্য সুস্থ-সবল বীজ চাই। বীজটি সঠিক জমিতে, সঠিক আলো-হাওয়ায়, সঠিক সার-পানিতে বোনা চাই। তবেই এটি হয়তো একদিন মাটি ভেদ করে সূর্যের আলো দেখবে। কবিতাও ঠিক তেমননি। এটি কবিই কলমে দিয়ে কাগজে অক্ষর দিয়ে ফুঁটিয়ে তোলেন ঠিকই। কিন্তু এর নির্মাণকাল চারাগাছের জন্ম নেওয়ার মতোই একটি ঘটনা। গাছটি উপকারি হলে মানুষ যেমন একে যতœ করে যুগ যুগ বাঁচিয়ে রাখে, তেমনি কবিতাও মানুষের মনে আঁচড় কাটতে সক্ষম হলে এর পাঠকরাই একে যতœ করে বছরের পর বছর ধরে বাঁচিয়ে রাখে। …
সেটি ছিল ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাস। টগবগে লাভার ভেতরে ফুটতে থাকা উত্তাল পূর্ব বাংলা। ছাত্র-গণঅভূত্থানের সময়। ২১ জানুয়ারির বিকেলে শুনশান, নিস্তব্ধ এক অচেনা নগরীর পথ ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বন্ধুর রুমে রাতটুকু কাটানোর জন্য রিকশা ধরে যাচ্ছি। সন্ধ্যার পরেই আরো সংঘাত-সংঘর্ষের আশঙ্কায় দ্রুত আশ্রয়ে ফেরার জন্য সকলেরই খুব তাড়া। এর আগেরদিনই ২০ জানুয়ারি পাক-সামরিক জান্তার লেলিয়ে দেওয়া পুলিশ- ইপিআর বাহিনীর (ইপিআর, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, সীমান্তরক্ষী বাহিনী) গুলিতে নিহত হয়েছেন ছাত্র নেতা আসাদ। পুরো ঢাকা শহর ক্ষোভের জ্বলছে। সারাদেশেই ছড়িয়ে পড়েছে গণ-বিক্ষোভ। ঢাকার এখানে-সেখানে ছাত্র-জনতা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। মিছিলের পর মিছিল। শ্লোগানের পর শ্লোগান। বিশালাকায় মিছিল-সমাবেশের আয়তন। প্রায় প্রতিদিনই পুলিশের গুলিতে কোনো না কোনো ছাত্র মারা যাচ্ছেন। তবু জনতার সংগ্রাম চলছেই। …
রিকশায় বসে বন্ধুর ছাত্রবাসে ফিরতে ফিরতে এইসবই ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছিল মাথার ভেতর। এরপর করণীয় কী? কি হবে বাংলার ভবিষ্যত? যুদ্ধ কি সত্যিই আসন্ন? স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হচ্ছে কবে? রিকশা যখন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর পেরিয়ে যাচ্ছে, তখন অস্থিরতার ভেতরেই বুড়ো মতোন রিকশা ওয়ালাকেই জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা চাচা মিয়া, বলেন তো, এই যে ছাত্ররা প্রতিদিন মিছিলে গুলি খেয়ে মরছে, তবু আন্দোলন চলছেই, এর শেষ কোথায়? আর কতো গুলি চলবে? আর কতো রক্তক্ষয় হবে? এখন কি করণীয়? বুড়ো রিকশাওয়ালা ঘাড় ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে এক নজর দেখে সেদিন যা বলেছিলেন, তা এখনো স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন ওই বুড়ো আমাকে বলেছিলেন, বাবা, কিছু মনে করো না। আমার মনে হয়, অনেক ছাত্র খুন হইছে। এখন এর বিহিত করনের সময় হইছে। এখন ছাত্রদেরও উচিত হইবো কিছু পুলিশ-ইপিআর মাইরা ফেলা। কারণ, সব হত্যায় পাপ নাই!
এই কথা শুনে সেদিন আমার সর্ব শরীর কেঁপে উঠেছিল। কথাগুলো একদম কলজের ভেতরে গেঁথে যায়। বন্ধুর ছাত্রাবাসের রুমে গিয়ে আমি ভেতরে ভেতরে আরো অস্থির হয়ে উঠি। সেখানেও তখন ছাত্ররা মিছিল-মিটিং, আন্দোলন-সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে। হাতে লেখা পোস্টার তৈরি হচ্ছে। সর্বত্র যুদ্ধের আবহ। রাত হতে না হতে ক্যাম্পাসের শুনশান নিরবতা ভেদ করে দূর থেকে ভেসে আসতে থাকে শ্লোগানের ধ্বণী। সেদিন রাতে অনেক চেষ্টা করেও আর ঘুমাতে পারিনি। বার বার মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল বুড়ো রিকশাওয়ালার সেই কথাগুলো। কি যন্ত্রণায় মনে মনে ছটফট করতে করতে ভোর রাতে উঠে রুমের বাতি জ্বালাই। কাগজ-কলম টেনে নিয়ে একটানে লিখে ফেলি ওই কবিতাটি:
কোনো কোনো প্রেম আছে প্রেমিককে খুনী হতে হয় ।
যদি কেউ ভালোবেসে খুনী হতে চান
তাই হয়ে যান
উৎকৃষ্ট সময় কিন্তু আজ বয়ে যায় ।
এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়
এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময় ।…
[লিংক]
পরে সকাল হওয়ার জন্য অপেক্ষা করি। তখন আমাদের তরুণ কবিদের প্রেরণাদাতা ছিলেন আহমদ ছফা, ছফা ভাই। এখন যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ, এর উল্টোদিকের মাঠের এককোনো তখন ঝুপড়ি একটি রেঁস্তোরা ছিলো। আমরা কবি-সাহিত্যিকরা সেখানে বসেই আড্ডা দিতাম। ছফা ভাই প্রতি সকালে সেখানে আসতেন নাস্তা করতে। আমি দোকানটিতে গিয়ে ছফা ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। তিনি এলে পকেট থেকে কবিতা লেখা কাগজটি বের করে তাকে দেখাই। ছফা ভাই কবিতাটি একবার-দুবার পড়েন। এরপর আবারো পড়েন। তারপর হঠাৎ উল্লাস করে আমাকে জড়িয়ে ধরেন। বলেন, হেলাল, তুমি বোধহয় তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ লেখাটি লিখে ফেলেছো! এই কবিতাটিতেই তুমি আজীবন বেঁচে থাকবে।
সেদিন ছফা ভাই ওই কথা কেনো বলেছিলেন, বুঝতে পারিনি। পরে কবিতাটি ছফা ভাই উদ্যোগ নিয়ে লিফলেট আকরে প্রকাশ করেন। ছাত্র-জনতা কবিতাটিকে সারা বাংলায় ছড়িয়ে দেন। এটি অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরিস্থিতির কারণেই তখন কবিতাটি কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। …
তবে ছফা ভাই সেদিন বোধহয় ঠিকই বলেছিলেন। এরপর অনেক কবিতা লিখেছি। এখনো লেখার চেষ্টা করছি। প্রেমের কবিতা, প্রকৃতির কবিতা, সংগ্রামের কবিতা। কিছু কিছু কবিতা পাঠক প্রিয়তা পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু কোনো কবিতাই কখনোই ওই কবিতাটির জনপ্রিয়তাকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি। … একজন কবি জীবদ্দশায় তার নিজেরই লেখা একটি কবিতার এমন অবিশ্বাস্য জয়-জয়াকার দেখেছেন, এটি ওই কবিতার জনক হিসেবে আমার কাছে অনেক বড়ো পাওয়া। কবিতা বা জীবনের কাছে আমার আর কোনো প্রাপ্তি নেই। …
পরে কবির এই কথোপকথনটি সে সময় প্রয়াত সাংবাদিক মিনার মাহমুদ সম্পাদিত জনপ্রিয় সাপ্তাহিক ‘বিচিন্তা’য় ছাপা হয়। এর শিরোনাম ছিলো: ‘কোনো কোনো প্রেম আছে প্রেমিককে খুনী হতে হয়’… ।
—
http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=33669
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... অগ্নি, Sjs)
(লিখছেন... ইমানুল হক )
(লিখছেন... dc, :|:, রমিত চট্টোপাধ্যায়)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... দ, :|:, upal mukhopadhyay)
(লিখছেন... Eman Bhasha, সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... রঞ্জন )
(লিখছেন... অসিতবরণ বিশ্বাস )
(লিখছেন... )
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... পাঠক, রঞ্জন )
(লিখছেন... জায় রাম, হায় রাম, :|:)
(লিখছেন... kk, দীপ, dc)
(লিখছেন... )
(লিখছেন... দীপ, হে হে)
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : [email protected] ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত