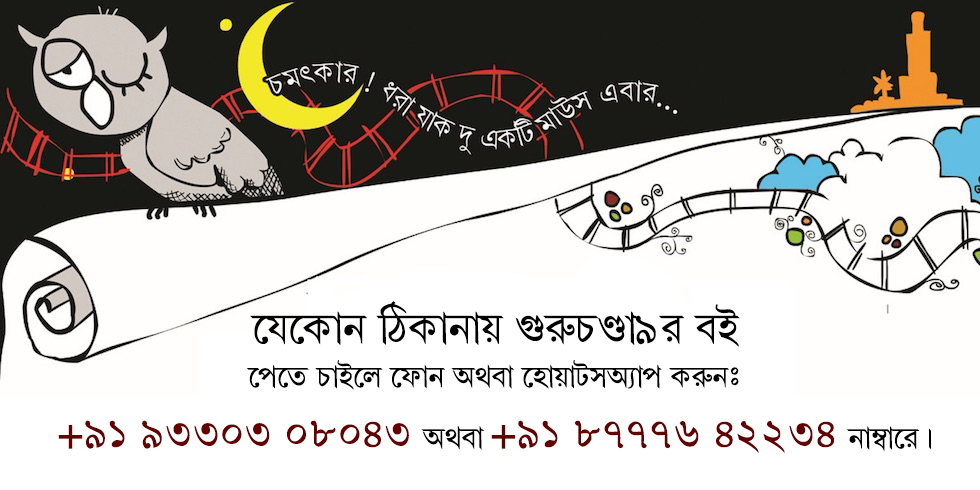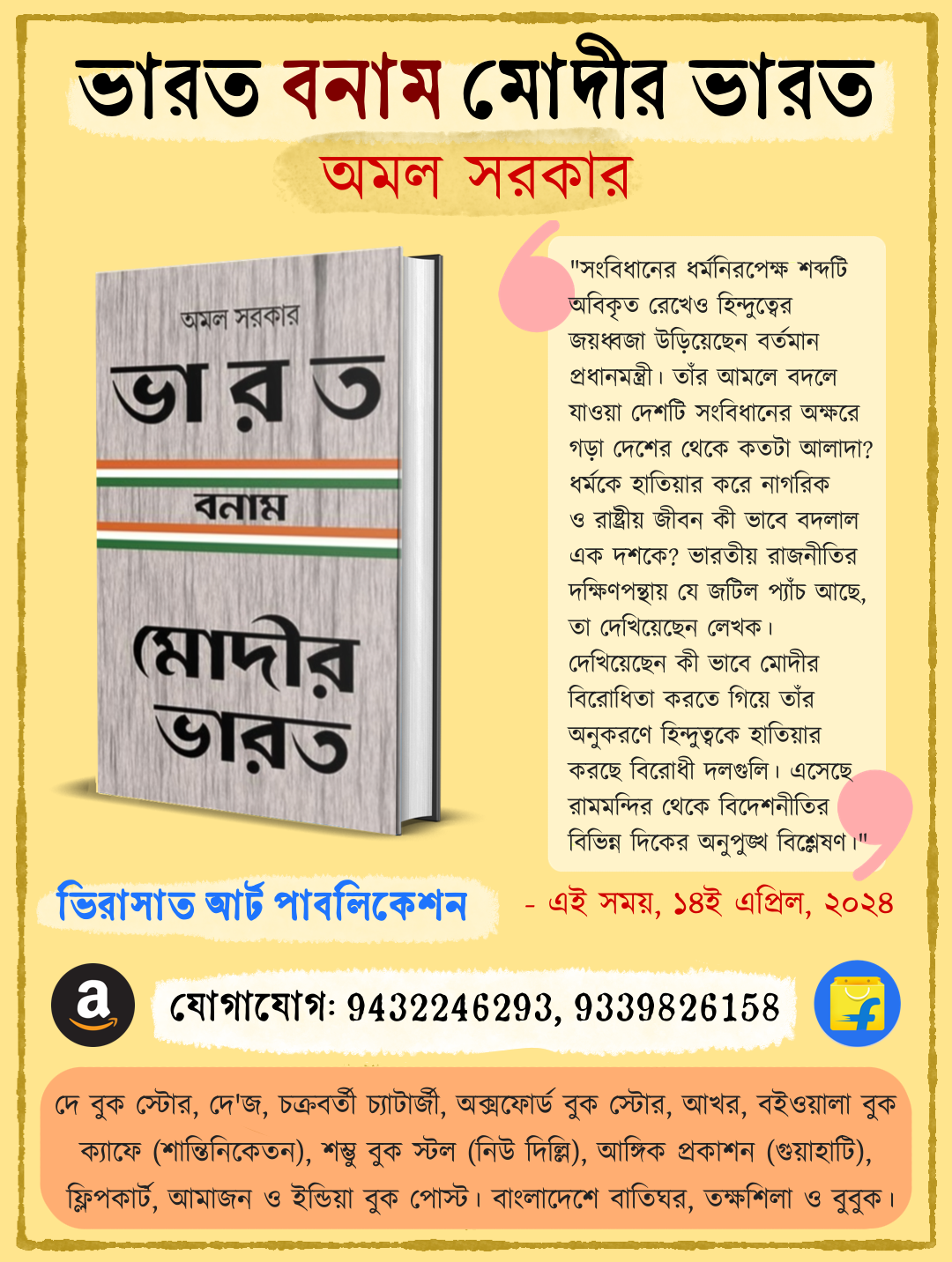- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
 arjo | 168.26.215.54 | ১১ জুলাই ২০০৮ ১৮:২৪399428
arjo | 168.26.215.54 | ১১ জুলাই ২০০৮ ১৮:২৪399428- এটাকে তুলি।
 c | 131.95.121.107 | ১২ জুলাই ২০০৮ ২০:৫৬399439
c | 131.95.121.107 | ১২ জুলাই ২০০৮ ২০:৫৬399439- এই থ্রেডে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। এটা চলুক।সকলেরই তো দরকার।
 I | 59.93.245.60 | ১২ জুলাই ২০০৮ ২২:৫৭399450
I | 59.93.245.60 | ১২ জুলাই ২০০৮ ২২:৫৭399450- ডাক্তারদের স্কিল নিয়ে কলকাতা শহরে খুব একটা সমস্যা নেই। দায়িত্ব নিয়ে বলছি। অনেক ডাক্তার আছেন, যাঁরা বিশ্বের যে কোনো সেরা সেন্টারে হেসেখেলে বড় ডাক্তার হতে পারেন। ইন ফ্যাক্ট, বিলেত ও আমেরিকায় এরকম বেশ কিছু বাঙালী ডাক্তার রয়েইছেন।
কিন্তু যেটা সমস্যা সেটা হল আমাদের কারিকুলাম ও পরীক্ষাব্যবস্থা। বেশ নির্বোধ। কাজে লাগেনা। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই, একটু পরিভাষা ব্যবহার করছি, সরি। মাইট্রাল স্টেনোসিস। হার্টের ভ্যালভের রোগ। শ্বাসকষ্ট হয়, স্ট্রোক-ও, কখনো কখনো। আমাদের কারিকুলামে মাইট্রাল স্টেনোসিসের গন্ডাদশেক aetiology পড়ানো হবে (কথার কথা, mitral stenosis-এর দশ গন্ডা aetiology নেই) ও ছাত্ররা পরীক্ষায় তা উগরে দিয়ে আসবে আশা করা হবে- তবেই পাশ, নইলে নয়। বিদেশে কিন্তু জোর দেওয়া হবে হার্টের কারণে শ্বাসকষ্ট হলে কিভাবে তার ডায়াগনোসিসে পৌঁছনো যাবে, তার উপরে। যার মধ্যে বলা বাহুল্য, মাইট্রাল স্টেনোসিসও থাকবে, থাকবে তার সম্পর্কিত তথ্যাদি। কিন্তু ঐ গাদাগাদা rarest of the rare aetiology মুখস্ত করার চাপ নেই।
অর্থাৎ কিনা সবকিছুই বেশ protocolised। যার ফলে ওখানকার সাধারণ ছাত্রদের গড় মান আমাদের তুলনায় ভালো। protocol-এর অবশ্য একটা সমস্যা এই যে সেটা বেশ যান্ত্রিক। মধ্যমেধাকে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু protocol-এর বিশাল সুবিধা হল, বড়সড় ভুল হবার সম্ভাবনা কম থাকে।
তাই বলে আবার শ্যামল যেভাবে বললেন সেরকমও না। আজ প্রতিটি মেডিক্যাল প্রটোকলই ভীষণ, ভীষণভাবে ইনভেস্টিগেশন-ডিপেন্ড্যান্ট, অতএব infrastructure-dependant। তাই পেটে বিদ্যা থাকলেও আপনি গ্রামের PHC-তে বসে কিছু রোগ diagnose করতে পারবেন না, যা নীলরতনে করা যাবে; বা নীলরতনে পারবেন না, অ্যাপোলোতে পারবেন। তবে Beth Israel কিংবা Cedars-Sinai তে যা করতে পারবেন, তার হয়তো ৯০-৯৫% অ্যাপোলো-AMRI ইত্যাদিতে পারবেন।
 I | 59.93.245.60 | ১২ জুলাই ২০০৮ ২৩:০১399461
I | 59.93.245.60 | ১২ জুলাই ২০০৮ ২৩:০১399461- একটুখানি ফালতু জ্ঞান দিয়ে নি। স্ট্রোকের কথায় মনে এল। অনেকেই স্ট্রোক আর হার্ট অ্যাটাককে গুলিয়ে ফেলেন। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। স্ট্রোক হয় মস্তিষ্কে , আর হার্ট অ্যাটাক...no prize for guessing।
 I | 59.93.245.60 | ১২ জুলাই ২০০৮ ২৩:১০399472
I | 59.93.245.60 | ১২ জুলাই ২০০৮ ২৩:১০399472- মনে হল, আগের আগের পোস্টে কিছু মন্তব্য পরস্পরবিরোধী শোনাচ্ছে। আমি বলতে চেয়েছিলাম, despite this system আমাদের শহরে ভালো ডাক্তার তৈরী হয়।
 nyara | 64.105.168.210 | ১৩ জুলাই ২০০৮ ০৪:১৮399483
nyara | 64.105.168.210 | ১৩ জুলাই ২০০৮ ০৪:১৮399483- ডাক্তারদের স্কিল প্রসঙ্গে, আমার ব্যক্তিগত ধারণা, দেশের (কলকাতার, কারণ ঐ একটা শহরের ডাক্তারদের সম্বন্ধেই আমার যা কিছু ধারণা আছে) ডাক্তারদের ডায়াগনস্টিক স্কিল অ্যামেরিকার ডাক্তারদের থেকে বেশি। ডায়াগনস্টিক স্কিল বলতে বলছি মুলত: সিম্পটমস দেখে আর সাধারণ কিছু পরীক্ষা করে যে ডায়াগনসিস করা হয়। হতে পারে নতুন ও উন্নত টেকনোলজির ওপর ভরসা করে ও ম্যালপ্র্যাকটিস ল'সুটের ভয়ে এখানকার ডাকতাররা ঐ স্কিল ব্যবহার না করতে করতে স্কিলটাই ভুলে গেছেন।
তবে দেশের ডাক্তারদের সম্বন্ধে আমার মনে হয় তাঁরা সবসময়ে ঘোড়ায় জিন দিয়ে আছেন। রুগীর সবকথা ভাল করে শোনার ইচ্ছে তো নেইই, সময়ও নেই। অন্যদিকে এদেশের ডাক্তার, সে তিনি যেমনই হোক, মন দিয়ে রুগীর বক্তব্য শোনেন - বুঝুন আর নাই বুঝুন।
 arjo | 24.214.28.245 | ১৩ জুলাই ২০০৮ ০৭:২৫399494
arjo | 24.214.28.245 | ১৩ জুলাই ২০০৮ ০৭:২৫399494- ভারতবর্ষে ডাক্তারদের স্কিল হয়ত আছে, কিন্তু আপনি সেই স্কিলফুল ডাক্তারের খোঁজ পাবেন এবং সেই ডাক্তার আপনার ক্ষেত্রে সঠিক ডায়াগনসিস ও চিকিৎসা করবেন, পুরোটাই খুব প্রোবাবিলিস্টিক। রিলায়াবিলিটি খুব কম। কারণ মনে হয় কোনো কিছুই প্রসেস ডিপেণ্ডেট নয়। হয়ত এর কারণও আছে। থেরাপিউটিক ডায়গনসিস তো ইনভেস্টিগেশনের ওপর ডিপেন্ড করে। অনেক ক্ষেত্রেই পেশেন্টের আর্থিক অবস্থা এমনই হয় যে সেটাও বোধহয় করা যায় না। আরও অনেক কারণ থাকতে পারে। এক্ষেত্রে মনে হয় ডাক্তারদের অবস্থাও খুব খারাপ। ডাক্তার হয়ত কি কি করা যাবে সেটা বোঝার জন্য জিগ্যেস করলেন 'কি করেন?" পেশেন্ট ভাবল এটা বোধহয় পয়সা খিঁচে নেবার জন্য। আরও কিছু কিছু কারণ তো ইন্দ্রণীল দাও আগের পোস্টে বলেছে।
আমার অর্থনৈতিক অবস্থা যদি পারমিট করে তাহলে আমি চাইব সমস্ত রকম টেস্ট হোক। একটু কঠিন অসুখের ক্ষেত্রে এলিমিনেশনের জন্য হলেও আমি চাইব সমস্ত ইনভেস্টিগেশন করতে। তাই আমার এদেশের ঐ সমস্ত কিছু দেখে নেওয়ার প্রবণতা ভালো লাগে। বেশ একটা নিশ্চিন্ত বোধ করি। দেশে সেই নিশ্চিন্ত বোধটাই হয় না। সব সময় একটা টেনশন, সব কিছু ঠিক হচ্ছে তো।
 Suvajit | 144.137.115.180 | ১৩ জুলাই ২০০৮ ১২:১৫399496
Suvajit | 144.137.115.180 | ১৩ জুলাই ২০০৮ ১২:১৫399496- আমেরিকার কথা বলতে পারব না, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার কথা বলতে পারি। এখানে কখনো ডাক্তার দেখাতে গেলে মেডিকাল সেন্টারে প্রথমে খোঁজ নি কোনো ভারতীয় বা শ্রীলংকান জিপি আছেন কিনা। নানা কারনে ও ঘটনায় সাহেব ডাক্তারদের ওপর আমার তিলমাত্র ভরসা নেই। ভুল ডায়গনসিসের ঝুড়ি ঝুড়ি উদাহরন আছে। আমার এক কলিগের হাতে মাইনর ফ্রাকচার হয়েছিলো। ২ টি মাস তাকে ব্যান্ডেজ বেঁধে, নানান রকম এক্স রে করে, গাদা গাদা ওষুধ খাইয়ে পরে বুঝলেন যে ওহ য়্যুভ গট আ ফ্রাকচার ইন হিয়ার। কলকাতা হলে খিস্তি বা হাল্কা ধোলাই বাঁধা থাকত কিন্তু এখানে গোরা ডাক্তারকে হাসিমুখে থ্যাঙ্কু বলে আসতে হয়েছিলো।
আর এখানে ডেন্টিস্টদের তো কথাই নেই। আমার এক বন্ধু যা পায়সা খরচ করে দাঁত ফিলিং করলো, সে পয়সায় ও ইন্ডিয়া এসে সব দাঁত ফিলিং, সিলিং করলেও বিলিং কম পড়তো।
আসলে সবার মেডিকেয়ার আছে বা ইন্সুরেন্স আছে তাই টাকাটা গায়ে লাগে না। আমাদের দেশের মতো গাঁটের কড়ি খরচ করে ভুল চিকিৎসা হলে সত্যি গায়ে লাগে।
আমার মেয়ের গতবছর নিউমোনিয়া হয়েছিলো। এখানে নিয়ম প্রথমে জিপি দেখে রেকমেন্ড করলে তবে হাসপাতালে নেওয়া যাবে। তো জিপি দেখে ইমেডিয়েট হসপিটালাইজ্ড করতে বললেন। সরকারী ওয়েস্টইড চিল্ডেন্স হসপিটালে এমার্জেন্সিতে নিয়ে গেলাম। এবার ওদের নিয়ম আছে ওখানকার রিসেপশনের জুনিয়র ডাক্তার বা নার্সেরা পেশেন্টকে দেখে একটা ক্যাটাগরিতে ফেলবেন, ১, ২ , ৩, ৪ এরকম। মরো মরো রোগী পড়বে ১ নম্বরে, তার থেকে ভালো ২ নম্বরে এরকম আর কি। আমার মেয়ে পড়ল ৩ নম্বরে। এবার অপেক্ষা করা। যেহেতু ৩ নম্বর তাই প্রায়োরিটি কম। বসে আছি তো আছিই। আমার মেয়ে এমনিতেই কাহিল ছিলো। প্রায় ঘন্টা পাঁচেক বসার পর একদম কেলিয়ে গেল। আর উদ্দাম জ্বর। আবার দেখা হল। ক্যাটাগরি বদলালো না। শেষে আরও ৩ ঘন্টা পরে রাত নটার সময় ডাক পড়ল। মেয়েকে দেখে, ব্লাড টেস্ট করে বলল অ্যাকুট নিউমোনিয়া। আমরা ভর্তি করে নিচ্ছি। কিন্তু রুম নেই। একটা বেড পাওয়া গেল সেটা করিডরে রেখে তাতে মেয়েকে শোয়ালাম। ওর মা তো টেনশনে কাঁপছে। তারপর গভীর রাত্রে কেবিন পাওয়া গেল। সেখানে শিফট করানো হল। তবে ভর্তি হবার পর থেকে, সংগে সংগে স্যালাইন লাগানো, নিয়মিত ভাবে ডাক্তাররা চেক করে যাচ্ছে, নার্সেরা ওষুধ খাইয়ে যাচ্ছে, কোনো সমস্যা নেই। আর কেবিন তো এলাহি ব্যাপার। আমাদের বাড়ির বেডরুমের দেড় গুন বড়ো, টিভি ফ্রিজ মাইক্রোয়েভ সব আছে। তিন দিন পরে মেয়েকে ছাড়া হলো।
আন্দুলের কাছে ওয়েস্টব্যাঙ্ক বলে একটা হাসপাতাল হয়েছে বেশ কয়েকবছর হলো। কিছু বাঙ্গালী এন আর আই ডাক্তার মিলে খুলেছেন। প্রাইভেট হাসপাতাল কিন্তু গরীবদের থেকে নামমাত্র ফিস নেওয়া হয়। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। অনেক ভালো ভালো ডাক্তার বসেন। পরিসেবা, ব্যাবহার অত্যন্ত ভালো। রোগীর খাবারদাবার উঁচুমানের। আর হাসপাতালের ক্যান্টিনটা টপক্লাস। ওখানে খাওয়া পাবদা মাছের ঝোলের স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে।
দিল্লিতেও আমি অত্যন্ত ভালো, ভদ্র যাক্তারদের পেয়েছি। সে প্রাইভেট চেম্বারেই হোক, রামমোহন লোহিয়া বা গঙ্গারামই হোক।
তাই ডাক্তারের কথা হলে আমি সর্বতোভাবে ভারতীয় ডাক্তারের গুনগান গাইবো।
 pi | 69.251.184.3 | ১৩ জুলাই ২০০৮ ১৩:১৫399497
pi | 69.251.184.3 | ১৩ জুলাই ২০০৮ ১৩:১৫399497- আচ্ছা, এই ইনভেস্টিগেশান বেসড থেরাপেউটিক ডায়গনসিস, যা করিয়ে নেওয়া ডাক্তার থেকে রোগী বা তার পরিবার নিশ্চিন্তি ও নিরাপত্তার জন্য ক্রমশ: অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক হয়ে উঠছে, সেই প্রচণ্ড প্রয়োজনীয় ও প্রচণ্ড রকম infrastructure dependent পরিষেবাটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মধ্যবিত্ত কি নিম্নবিত্ত মানুষের কতটা আয়ত্তের মধ্যে ?
ইনস্টিটিউশান কি কম্পানী র মেডিক্যাল বেনিফিট এ কভার করার কতিপয় কেস বাদ রেখে জানতে চাইছি। ব্যক্তিগত ভাবে ইনসিউরেন্স করানোর চল ও তো খুব বেশি নেই , যদ্দুর জানি।
সরকারী হাসপাতাল, গ্রাম মফস্বলের চিকিৎসায় এগুলো কতটা কি করা হয় বা করা সম্ভব , সে আলোচনাও একটু করলে ভালো হয়।
 I | 59.93.241.245 | ১৩ জুলাই ২০০৮ ১৩:২৫399499
I | 59.93.241.245 | ১৩ জুলাই ২০০৮ ১৩:২৫399499- ন্যাড়াদা, আর্য , শুভজিতকে ডিটো।
হ্যা, কলকাতা শহরে ডাক্তাররা আস্তে আস্তে ক্লিনিক্যাল স্কিল লুজ করছে। সাহেবরা মনে হয় আরো করেছেন। কিন্তু এ কথাটা বলতেই হবে যে, এই ল্যাব-ভরোসার দিনেও ক্লিনিক্যাল স্কিলের মার নেই। ভালো, আত্মবিশ্বাসী ক্লিনিশিয়ান অনেক কম ইনভেস্টিগেশনে রোগ ডায়াগনোজ করতে পারেন, যেটা করতে মাঝারি ক্লিনিশিয়ানকে অনেক বেশী ইনভেস্টিগেশন করাতে হয়। আর যেখানেই ল'সুট, মারধোর ও খিস্তি খাওয়ার ভয়, সেখানেই আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া,ফলে বাড়তি ইনভেস্টিগেশন। ফলে রোগীর মনে অবিশ্বাস, ডাক্তারকে গালাগাল, তাকে শত্রু/প্রতিপক্ষ ভাবা। ফলে ডাক্তারের আরো আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া, রোগী/তার আত্মীয়স্বজনকে প্রতিপক্ষ ভাবা....
এইরকম এক বিষচক্র, অলাতচক্র তৈরী হয়েছে, হচ্ছে।
টেবিলের দুপাশে বসে আছেন দুজন প্রতিপক্ষ। একের অন্যকে ছাড়া চলবে না।
 I | 59.93.208.15 | ১৩ জুলাই ২০০৮ ২০:২৩399500
I | 59.93.208.15 | ১৩ জুলাই ২০০৮ ২০:২৩399500- pi, নিম্ন-মধ্যবিত্তের আশা বেশ কম। মধ্যবিত্তেরই নেই, যদি না insurance করা থাকে।
সরকারী হাসপাতাল নিয়ে আলোচনায় পরে আসবো। সঙ্গে থাকো। ভুলে গেলে মনে করিয়ে দিও।
 I | 59.93.208.15 | ১৩ জুলাই ২০০৮ ২০:৪৩399501
I | 59.93.208.15 | ১৩ জুলাই ২০০৮ ২০:৪৩399501- আর্যর শেষ পোস্ট নিয়ে:
যে কথাটা পরিষ্কার করে বলতে পারিনি, তা হল-কলকাতা শহরে ভালো ডাক্তার বেশ কিছু আছেন; মাঝারী-খারাপ ডাক্তার অনেক। বিলেতে কিন্তু মোটামুটি একটা মান সবারই আছে। কারণটা আগেই বলা।
আমি জিপিদের (বিলেতের) এই লিস্টির বাইরে রাখছি। তাঁরা আমাদের দেশের জিপিদের মত, কি তার চেয়েও খারাপ। এঁরা বেসিক্যালি মেডিক্যাল ক্লার্কিং ও triage করে থাকেন, তা-ও বেশ বাজে triaging; ডাক্তারী-ফাক্তারী করেন না।
UK-র অবস্থাও বোধ হয় অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় খুব ভালো না। NHS আস্তে আস্তে কাহিল হয়ে আসছে। ট্রাস্টগুলি এক এক করে বেশ কিছু হাসপাতাল তুলে দিচ্ছে, কিছু হাসপাতাল merge করিয়ে দিচ্ছে। waiting time প্রচুর। সাইকায়াট্রিস্ট দেখাতে ছ-মাস , MRI -করাতে চার-পাঁচ মাস -এইরকম সব সময় লাগে। এদিকে তেমন ভালো parallel private system তৈরী হয়ে ওঠে নি। মোট কথা ,অবস্থাটা প্রথম বিশ্বের তুলনায় মোটেও ভালো বলা চলে না।
আমার মনে আছে, james paget-এ observership-এর সময় এক রোগীকে দেখেছিলাম, হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, জরুরী বাইপাস করানো দরকার। কনসালট্যান্ট (এঁর কলকাতা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা আছে) বললেন, এ কি তোমার অ্যাপোলো হাসপাতাল পেয়েছ? যে পেশেন্ট এল আর অমনি emergency CABG হয়ে গেল?
 I | 59.93.165.28 | ১৩ জুলাই ২০০৮ ২১:৪৬399502
I | 59.93.165.28 | ১৩ জুলাই ২০০৮ ২১:৪৬399502- মিডিয়া নিয়ে অন্য একটা থ্রেডে কথা উঠেছে। আমাদের দেশে জুডিসিয়ারি ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থা এরকম প্রশ্নাতীত ক্ষমতা ভোগ করেনা। মিডিয়া নিজেই একধরণের জুডিসিয়ারি। তারাই অভিযোগকারী, বিচারকও তারাই। শুধু হাতে ধরে শাস্তিটা দিতে পারেনা, এই যা। এরকম দায়িত্বহীন ক্ষমতা আর কারো হাতে আছে কি/কী?
সেনসেশন্যাল খবরের লোভ যে কি করতে পারে, তার একটা উদাহরণ শিল্পী বাঙাল। যাঁরা জানেন না, তাঁদের জন্য: এই মহিলা epilepsy -তে ভুগতেন। কলকাতার কোনো একটি সরকারী হাসপাতাল থেকে তাঁকে carbamazepine নামে মৃগী রোগের একটি ওষুধ দেওয়া হয়। ঐ ওষুধ খাওয়ার পর তাঁর শরীরে ওষুধের এক বিশেষ ধরণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যার নাম erythema multiforme অথবা Stevens-Johnson's syndrome। এতে শরীরের সর্বত্র বড় বড় ফোস্কা পড়ে, তেমন খারাপ হলে মুখের ভেতর, হাত-পায়ের তালুও বাদ পড়ে না। মৃত্যুহার খুব বেশী ,৩০-৪০%। শিল্পী বাঙালও মারা গেলেন।
আনন্দবাজারের ভাষায় "... হাড়-মাংস আলাদা হয়ে গেছিল।' আর একটি টিভি চ্যানেলে বলা হল -ভুল ওষুধ প্রয়োগে মৃত্যু।
এই মূর্খদের কে বোঝাবে , কার্বামাজেপিন এপিলেপ্সির একটি স্বীকৃত ওষুধ এবং এই ওষুধ প্রয়োগে কার এরকম মারাত্মক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, সেটা আগে থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই। এধরণের sensitive প্রতিবেদন লেখা /টেলিকাস্ট করার আগে কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মতামত নেওয়ার দরকার আছে , সেটা কেউ ভাবেনা। হয়তো প্রতিবেদক সায়েন্স গ্রাজুয়েটও নয়।
এটা জাস্ট একটা কেস। এরকম অজস্র রিপোর্টিং রোজ চোখে পড়ে। ভুল নাম, ভুল বানান, ভুল ইনফারেন্স। একবার রেফারেন্স ঘাঁটার প্রয়োজন আছে বলেও কেউ মনে করে না। বদারই করেনা। তাহলে আর রগরগে মসালাদার খবর কিকরে হবে ! কম্পিট করা যাবে কে- সিরিজ কিম্বা ষড়যন্ত্রমূলক বং সিরিয়ালের সঙ্গে!
মানুষের কাছে যে কি মেসেজ যায়, সহজেই অনুমেয়। ঘোলা জল আরো ঘোলা করে আ:, শুভ লাভ!
 arjo | 24.214.28.245 | ১৪ জুলাই ২০০৮ ০৫:৫৬399503
arjo | 24.214.28.245 | ১৪ জুলাই ২০০৮ ০৫:৫৬399503- আই (বড্ড বড় তোমার নাম, তাই ছোট করে নিলাম), একটা প্রশ্ন আছে, শুধুই কি ডাক্তারের মানের ওপর ডিপেন্ড করে? যেমন ধর এখানে ডাক্তার দেখাতে গেলে প্রথম কাজ যেটা করে তাহল, প্রেসার দেখে, ওজন মাপে, আর টেম্পারাচার কত দেখে। আর আমি নিয়মিত যে ডাক্তারের কাছে যাই সেখানে এই রেকর্ড রাখা থাকে আমার ফাইলে (কাগজে)। এটা একটা সিম্পল প্রসেস, খরচাও নেই, উন্নত প্রযুক্তিরও কোনো দরকার নেই। কিন্তু ওভার অল হেলথ সম্বন্ধে একটা ধারণা দেয়। এছাড়াও যেটা করে তাহল নিয়মিত ব্লাডটেস্ট। উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে আর যেহেতু ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড রাখা হয় আরও বেশ কিছু কাজ হেলথ ইন্সিরিওয়েন্স নিজের গরজেই করে থাকে, কিন্তু সে অনেক দূরের ব্যপার। এই বেসিক রেকর্ড কিপিং, বেসিক প্রসেস মেন্টেন করা তো অসাধ্য কিছু না, কিন্তু হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই আর্লি ডিটেকশনে সাহায্য করে। প্রশ্ন হল এই বেসিক প্রসেসের প্রয়োজনীয়তা কতটা? আর প্রয়োজনীয়তা থাকলে সেটা পাঠ্যক্রমে থাকা উচিত কি? বিলেতে কি এমন কোনো প্রসেস আছে?
বোস্টনে ছেলে হবার ১০-১২ দিন পরে বউয়ের জ্বর হয়। ডাক্তারকে ফোন করলে এমার্জেন্সি রুমে নিয়ে যেতে বলেন। তখন ছিল রাত, অনেকটা শুভজিত দার মতনই অভিজ্ঞতা। প্রথমে একটা বেডে মাটিতে শুয়ে থাকতে হয়। তারপর একটা ট্রলিতে, শেষে প্রায় ঘণ্টা তিনেক বাদে ঘর পাওয়া যায়। এসব সঙ্কেÄও ১০-১২ দিনের ছেলে নিয়ে, অসুস্থ বউকে নিয়ে আমি কিন্তু একটুও ইনসিকিওরড ফিল করি নি। ডাক্তাররা নিয়মিত আসছিলেন, পরীক্ষা করছিলেন, আমার সাথে হেসে দু মিনিট গল্প করছিলেন। এর আগেই বিশদে বুঝিয়েছিলেন কি কি হতে পারে আর চিকিৎসার স্টেপ কি। টেনশন ছিল কিন্তু সিকিওরড ফিলিং টাও ছিল।
 shyamal | 67.60.254.15 | ১৪ জুলাই ২০০৮ ১০:১৩399504
shyamal | 67.60.254.15 | ১৪ জুলাই ২০০৮ ১০:১৩399504- আর্যর কথা প্রসঙ্গে, আমার আমেরিকার পেডিয়াট্রিশিয়ানদের ওপর একেবারে ভরসা নেই। অন্ধের মতন চলে কমন সেন্স না ব্যবহার করে।
ছেলে হওয়ার পর বলল, একটুও জল দেবেনা। তাহলে নাকি ব্রেস্ট ফিড করতে চাইবেনা। ডাক্তার বলল, মায়ের দুধ খেলে জলের চাহিদাও মিটবে। এদিকে যে কোন কারণেই হোক, ছেলে ব্রেস্ট ফিড করতে পারছেনা। আমি বৌকে বললাম , জল দাও বোতলে। না, ডাক্তার বলেছে একবার বোতল অভ্যাস হয়ে গেলে বোতলই চাইবে। ঠিক আছে। তার পরে রাত দশটা নাগাদ দেখি ছেলের শরীর ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে। টেম্পারেচার নিয়ে দেখি ৯৯। ব্যাস , আমি বললাম এমারজেন্সীতে চলো। কারণ জন্মানো বাচ্চার সামান্য জ্বরও ব্রেনের পক্ষে ডেনজারাস। যাওয়ার আগে বললাম , ডাক্তার যাই বলুক ওকে বোতলে জল দাও। জল দিতেই সে চুক চুক করে খেল কিছুটা।
তার পরে এমারজেন্সীতে নার্স যখন টেম্পারেচার নিল, জ্বর চলে গেছে।
অনেকে অ্যাডভাইস দিয়েছিল, ডাক্তাররা বলে বাচ্চাকে উল্টো করে শোয়াতে। মানে পেট, বুক বিছানা টাচ করবে। আমরা ঠিক করলাম সোজা করেই শোয়াব। দেশে কেউ উল্টো শোয়ায় না। তাতে কোনই অসুবিধা হয়নি। তার কয়েক বছর পরে দেখি, সুবিখ্যাত New England Journal of Medicine -- যেটা মোটামুটি এদেশের বাইবেল, তাঁরা বলেছেন বাচ্চাকে উল্টো করে না শোয়াতে। কারণ এতে দেখা গেছে Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) এর চান্স অনেক বেশী।
কি আর বলব? আমার মনে হয় আমাদের দেশের মা, ঠাকুমা, দিদিমারা পাঁচ হাজার বছরের কালেক্টেড অভিজ্ঞতা নিয়ে কাজ করে। সেটা উড়িয়ে দেওয়ার নয়।
 nyara | 64.105.168.210 | ১৪ জুলাই ২০০৮ ১০:৪৪399505
nyara | 64.105.168.210 | ১৪ জুলাই ২০০৮ ১০:৪৪399505- আমারও - যতটুকুই হোক - অভিজ্ঞতা বলে যে আমাদের যা ট্রাইবাল নলেজ, মা-মাসি-ঠাকুমা-দিদিমাদের নিদান - সেগুলো অধিকাংশই অত্যন্ত ফলদায়ী। মাঝে মাঝে তাবড় তাবড় মেডিকাল রিসার্চ জার্নাল যখন এক এক করে সেগুলোকে কনফার্ম করে, খুব আমোদ পাই।
 Arijit | 61.95.144.123 | ১৪ জুলাই ২০০৮ ১০:৪৯399506
Arijit | 61.95.144.123 | ১৪ জুলাই ২০০৮ ১০:৪৯399506- এই জল খাওয়ানো এবং উল্টো করে শোয়ানো নিয়ে দ্বিমত আছে। আমেরিকান পেডিয়াট্রিক সোসাইটির বইটা বেশ নামকরা - সেখানে দেখেছি, এবং আমেরিকা ও ইংল্যান্ড দুই দেশেই এই দুটো নিয়ে ডাক্তার/মিডওয়াইফ একই কথা বলেছে। যে ছয় মাস বয়স অবধি জলের দরকার পড়ে না। ভারতে খাওয়ায় কারণ এখানে গরম অনেক বেশি। ডিহাইড্রেশন হয়। এবং উপুড় করে শোয়ালে (নাকি) ঘাড় এবং পিঠের মাসল শক্ত হয়। ঋক আর ঋতি - দুজনকেই আমরা তাই করেছি, এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দুজনেই বেশ ঘাড় সোজা করে বসতে শিখেছিলো। উল্টোতেও শিখেছিলো তাড়াতাড়ি।
 S | 202.140.54.29 | ১৪ জুলাই ২০০৮ ১১:৫৬399507
S | 202.140.54.29 | ১৪ জুলাই ২০০৮ ১১:৫৬399507- প্রথম ছ মাস বাচ্চাকে এক ফোঁটাও জল না খাওয়ানোর নির্দেশ আমরাও অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলাম। ছ মাসের আগে জল দিই নি।
আর কোনওদিন বোতল খাওয়াই নি। ঝিনুক-বাটি রেগুলার ফুটিয়ে তাতে করে জল খাওয়াতাম। ছ-মাস পরে অবশ্যই।
 shyamal | 64.47.121.98 | ১৪ জুলাই ২০০৮ ১৯:৩৭399508
shyamal | 64.47.121.98 | ১৪ জুলাই ২০০৮ ১৯:৩৭399508- আমেরিকায় সামারে প্রচন্ড গরম পড়ে। যদিও সে¾ট্রালি এ সি। সরি। আমি , কটা ডাক্তার দু পাতা পড়ে বলল জল খাওয়াবেননা, এটা মানতে পারিনি। আমার ছেলে ব্রেস্ট ফিড করেছে, প্রচুর জল খেয়েছে আর ফরমুলাও খেয়েছে। কোন ক্ষতি হয়নি। ডক্টর স্পক বলেছেন, মা বাবার হাঞ্চ হচ্ছে সব থেকে জরুরী।
বললাম তো, এখন New England Journal of Medicine বলছে সোজা করে শোয়াতে।
 I | 59.93.215.169 | ১৪ জুলাই ২০০৮ ২১:৩৪399510
I | 59.93.215.169 | ১৪ জুলাই ২০০৮ ২১:৩৪399510- আজ্জোর কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। ও কোন সিস্টেমের কথা বলছে? সরকারী না বেসরকারী?
সরকারী ব্যবস্থায় মানুষের বেসিক ক্লিনিক্যাল প্যারামিটারের রেকর্ড কিপিং? গুড়ায়ও হাসবো, দাদা!
আর বেসরকারী হাসপাতালগুলো রাখে , কিন্তু মেথডিক্যালি না। রাখলেই বা কি! আজ তুমি woodlands-এ দেখালে, কাল belle-vue-তে। আশা করো, তারা রেকর্ড বিনিময় করবে?
হ্যা, UK-তে রাখে তো। তাড়া তাড়া, ইয়া মোটকা মোটকা সব ফাইল। তোমার যাবতীয় সব তথ্য,ফ্যাক্টস ও ফিগারস: স-অব কম্পিউটারবন্দী।
না:, আমি ফুকোর ধারে যাব না।
প্রয়োজনীয়তার কথায় বলি,রেকর্ড কিপিং প্রয়োজনীয় তো বটেই। আমাদের স্ট্রাটার মানুষ অবশ্য নিজেরাই রাখেন; পুরনো প্রেশক্রিপশন ইত্যাদি। গরীব মানুষ রাখেনা,রাষ্ট্রও তাদের হয়ে রাখেনা। তবে, প্রায়োরিটির কথা বললে আমি বলবো, এর চেয়েও জরুরী হল বেসিক জনস্বাস্থ্য-ভ্যাক্সিনেশন, জীবাণুমুক্ত পানীয় জল etc।
এবার এই আলোচনা আর বেশীদূর গড়ালে শান্তনুদার কথামত.....
 rimi | 24.214.28.245 | ১৪ জুলাই ২০০৮ ২২:২০399511
rimi | 24.214.28.245 | ১৪ জুলাই ২০০৮ ২২:২০399511- মা দিদিমা বনাম ডাক্তার:
আমার ডাক্তার বলেছিল জল খাওয়ানোর দরকার নেই, কারণ যেটুকু ফ্লুইড দরকার তা মিল্ক থেকেই আসে। কিন্তু আমার ইচ্ছা হলে আমি জল খাওয়াতে পারি। একেবারে জল খাওয়াতে আদৌ বারণ করে নি।
আর উপুড় করে শোয়ালে মাসল শক্ত হয় তাড়াতাড়ি। আমেরিকান পেডিয়াট্রিক সোসাইটি রাত্রে বা ঘুমোনোর সময় বাচ্চাকে সোজা করে শোয়াতে বলে ঠিকই, কিন্তু এটাও বলে যে বাচ্চাকে ফ্রিকোয়েন্টলি tummy time দিতে, যখন বাচ্চা জেগে থাকে।
আমার ছেলে জন্মানোর পরে ডাক্তার দেখিয়ে দিয়েছিল কেমন করে বসিয়ে বার্প করাতে হয়। বাড়িতে সেটা শুনে সবাই বল্ল ঐটুকু বাচ্চাকে বসালে নাকি তার শিড়দাঁড়া বেঁকে যায়। আমি তো দিব্বি বসালাম, কিছুই শিরদাঁড়া বেঁকলো না। অন্যদিকে, বাড়ি থেকে বলা হয়েছিল বাচ্চাকে সর্ষের তেল মাখিয়ে রোদে ফেলে রাখতে খালি গায়ে। যাতে ভিটামিন ডি পায়। কিন্তু এখানকার ডাক্তাররা সেটা স্ট্রিকটলি বারণ করেন। আমি রোদে শোয়াই নি। বাচ্চার কিন্তু ভিটামিন ডির কোনো অভাব হয় নি।
আরো একটা ব্যপার, বাচ্চার মাথায় একটা নরম স্পট থাকে। মা দিদিমার উপদেশ হল, মাথায় খুব করে তেল মাখাতে হবে, নইলে ঐ জায়গাতা শক্ত হবে না। এখানকার ডাক্তার বলেছিলেন ওটা নিজে থেকেই শক্ত হয়ে যায়। আমি তেল মাখাই নি। নিজে থেকেই দিব্বি শক্ত হল।
এগুলো সব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। এই নিয়ে থিওরি দেওয়া একেবারে সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমি ডাক্তার নই। তবে উনিশ শতকের চিকিৎসা বিজ্ঞান নামে একটি বই আমি পড়েছি। তাতে আমাদের দেশের মা দিদিমার কালেক্টিভ নলেজ সম্পর্কে যা বিবরণ দেওয়া আছে, তাতে সেই নলেজের থেকে ডাক্তারের উপর নির্ভর করা আমার শ্রেয় মনে হয়েছে। ভারতবর্ষে শিশু মৃত্যুর হার এক সময়ে অসম্ভব বেশী ছিল, তার কারন মা দিদিমার ঐ কালেক্টিভ নলেজ। রিসার্চ করে ডাক্তাররা যদি সেইসব থিওরি কে ভ্যালিডেট করে, তবে অবশ্যই ভালো। কিন্তু সেটা না করলে অন্তত আমি ভরসা পাই না।
 santanu | 217.196.19.45 | ১৪ জুলাই ২০০৮ ২২:২২399512
santanu | 217.196.19.45 | ১৪ জুলাই ২০০৮ ২২:২২399512- ডাক্তার, UK, USA র কথা শুনে কি হবে? সারা UK তে ৬০ মিলিয়ান, গোটা ইলিনয়েস স্টেটে ১২ মিলিয়ন, সেখানে শুধু কলকাতা আর আশপাশের এলাকাতেই ১৫ মিলিয়ন লোক, তার ওপর গরীব দেশ - তাই এই তুলনা শুনে আর দু:খ বাড়িয়ে লাভ কি?
তার চেয়ে সময় পেলে একটু বলো, এই অবস্থাতেই আমরা মধ্যবিত্ত রুগীরা how to get best out of this system, বলো ঐ West Bank এর কথা, বলো দেবি শেঠি শান্তিনিকেতন এ গ্রামীণ ক্লিনিক খুলেছেন তার কথা। কাউকেই বদলানো যাবে না, নিজেদের বদলে যদি, বেশী সুস্থ ভাবে বাঁচা যায়।
 rimi | 168.26.191.117 | ১৫ জুলাই ২০০৮ ০০:১৭399513
rimi | 168.26.191.117 | ১৫ জুলাই ২০০৮ ০০:১৭399513- আমার বন্ধুদের অনেকেরি ভারতে বাচ্চা জন্মেছে। তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি যে ব্রেস্টফিডিং থেকে শুরু করে তেল মাখানো সম্বন্ধে এখানে পেডিয়ট্রিশিয়ানরা যা বলেন, ওখানেও এখনকার ভারতীয় পেডিয়াট্রিশিয়ানরা প্রায় সেই একই পরামর্শ দেন। অবশ্য আমার এই স্যাম্পেল সাইজ বেশ ছোটো, আর যাদের সঙ্গে কথা হয়েছে তারা নামী জায়গাতে (যেমন অ্যাপোলো কিম্বা পিয়ারলেস ) চিকিৎসা করায়।
 sarathi | 59.160.220.131 | ১৫ জুলাই ২০০৮ ০৮:৪৯399514
sarathi | 59.160.220.131 | ১৫ জুলাই ২০০৮ ০৮:৪৯399514- সদ্য অপারেশানের অভিজ্ঞতা হল কলকাতার এক তথাকথিত নামী নার্সিংহোমে
আজকে আপিস জয়েন করলুম, পরে ডিটেলে জানাচ্ছি
 Riju | 121.240.210.2 | ১৫ জুলাই ২০০৮ ০৯:৩২399515
Riju | 121.240.210.2 | ১৫ জুলাই ২০০৮ ০৯:৩২399515- আমার একটা প্রস্তাব আছে - এই চাপান উতোরের পাশে যদি কলকাতা তথা বাংলায় কোথায় কোন হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে বা কোন ডাক্তার স্পেসালিস্টের কাছে কোন রোগের ভালো চিকিৎসা হয় এটা যদি লিস্ট করা যায় , ভবিষ্যতে কারুর কাজেও লাগতে পারে
 m | 12.240.14.60 | ১৫ জুলাই ২০০৮ ১১:০৪399516
m | 12.240.14.60 | ১৫ জুলাই ২০০৮ ১১:০৪399516- ছেলের জন্যে ভারতীয় ডাক্তার সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা ভালো নয়।
দেশে গিয়ে আমার ছেলের সারা হাতে র্যাশ বেড়িয়েছিলো- এক বন্ধুর পরামমর্শে বিলেত ফেরত এক শিশু বিশেষজ্ঞ কে দেখালাম। নির্ধারিত সময়ে গিয়ে দেখি ভিড় নেই,সাড়ে ছটাতেই ডাক পড়লো-ভদ্রমহিলা কে দেখেই বেশ শ্রদ্ধাভক্তি হলো,যত্ন করে ছেলেকে দেখলেন,এমন কি ওজন -উচ্চতা ইত্যাদি মেপে আমাকে মোহিত করে ফেল্লেন। প্যাড বের করে খাবার-লাগানোর মোট ছ'রকমের ওষুধ লিখে দিলেন।সাড়ে চারশো টাকা ভিজিট দিয়ে যখন বেরিয়ে আসছি,বল্লেন সামনের ওষুধের দোকান থেকে যেন ওষুধ কিনে আজ সন্ধ্যে থেকেই দিতে শুরু করে দিই- এদিক সেদিক দু তিনটে দোকানে সব ওষুধ পেলাম না ,তারপর ওর বলা দোকান থেকে (সল্ট লেকে এ এক বাড়ির নীচে ঘুপচি গ্যারাজ ঘর) সাড়েতিনশো টাকার ওষুধ কিনে বাড়ি এলাম- হাতের র্যাশের জন্যে খাবার ওষুধ গুলো দেবার দরকার বোধ করি নি- সেগুলো জলে গেলো- লাগানোর ওষুধ পাঁচ দিন লাগিয়ে আবার ওর কাছে গেলাম- আমি ফেরত যাবার আগে একবার হাত টা ওকে দেখিয়ে নিতে বলেছিলেন- গেলাম,বল্লেন কিছু না,গরম থেকে হাতে ঐরকম র্যাশ বেরিয়েছে-কোলকাতা ছাড়লেই সেরে যাবে-আমি খাবার ওষুধ দিই নি শুনে বল্লেন ও ঠিকই আছে এদিন আবার সাড়ে চারশো টাকা নিলেন। দমদমেই দেখলাম হাতের অস্বস্তি কমে গেছে- ইনি আমাদের ছটা ওষুধ কেন দিয়েছিলেন আজো জানি না।পরের বার দেশে যাবার আগে এখানে ডাক্তার বলে দিলেন,র্যাশ হলে বরফ লাগাতে আর ক্যালামাইন লোশান সঙ্গে রাখতে- ওষুধের নাকি কোনো দরকার নেই।
এরপর এদেশে এক ভারতীয়(মারাঠি) ডাক্তারের সঙ্গে মোলাকাত হলো। ইনি আমার ছেলের ডাক্তারের বদলি হিসেবে সেদিন ছেলেকে দেখেছিলেন- চল্লিশ মিনিট এক চিলতে ঘরে বসে অপেক্ষা করে করে ছেলে তখন বেশ বিরক্ত- কিছুতেই স্ট্রোলারে বসতে রাজি নয়- ইনি দু সেকেন্ড ছেলেকে পর্যবেক্ষণ করে বল্লেন- এর হাইপার অ্যাকটিভিটির কোনো সমস্যা আছে কিনা- শুনে আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার জোগাড়।-ছেলের জন্যে এখানে ভারতীয় ডাক্তার সেই প্রথম আর এখনো পর্যন্ত শেষ।
 Kevin Keegan | 61.95.144.123 | ১৫ জুলাই ২০০৮ ১৭:৩৬399517
Kevin Keegan | 61.95.144.123 | ১৫ জুলাই ২০০৮ ১৭:৩৬399517- তুললাম
 arjo | 168.26.215.54 | ১৫ জুলাই ২০০৮ ১৯:১৫399518
arjo | 168.26.215.54 | ১৫ জুলাই ২০০৮ ১৯:১৫399518- আই,
সরকারী হাসপাতালের কথা আমি বলছি না। আমি বলছি বেসরকারী ছোট বড় নার্সিং হোম বা প্রাইভেট প্র্যাকটিসের কথা। মূল বক্তব্য ছিল ডাক্তার দেখাতে গেলে কিছু রুটিন চেক আপ করার মতন প্রসেস এস্ট্যাবলিস করা খুব কঠিন কি? একটা উদা দিই। আমার মায়ের শরীর খারাপ। মায়ের যে ট্রিটমেন্ট চলছে তাতে জেনারাল হেলথ কেমন সেটা নিয়মিত দেখা দরকার। এবারে জেনারাল হেলথের একটা ভালো ইন্ডেক্স হল ওজন। কিন্তু পুরো প্রসেসে কেউ একবারের জন্যও ওজন দেখে নি। আমার বক্তব্য ছিল এই রুটিন চেক করাটা কেন প্রসেসে ফেলা যায় না। অন্তত বেসরকারী সংস্থায়। রেকর্ড কিপিং এর প্র্যাকটিকাল অসুবিধা নয় বোঝা গেল। এবারে পাঠ্যক্রমের কথা বলেছিলাম অন্য একটা সাবজেক্টের সাথে তুলনা করে। যেমন ধর কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে গেলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নামে একটা আপাত দৃষ্টিতে ম্যানেজেরিয়াল সাবজেক্ট পড়তে হয়। সেটা আমাদের মতন সেল্ফ টট ইঞ্জিনিয়ারদের ও পড়তে হয়েছে। তার মানে কি আমি সাংঘাতিক প্রসেস ওরিয়েন্টেড হয়ে গেছি। কিন্তু একটু একটু হয়েছি যাতে আমার কাজের স্ট্যান্ডার্ড এরর অনেক কমেছে। দ, এদিক ওদিক মাঝে মাঝেই চেকলিস্টের কথা বলে আর খিল্লিত হয়। কিন্তু আমার নিজের মনে হয় রিপিটেটিভ ওয়ার্ক দিনের পর দিন একই রকম ভাবে করতে চেকলিস্টের প্রয়োজন আছে। নয়ত হিউম্যান এরর বাড়ে। এই ছোটখাটো প্রসেসের ইম্পলিমেন্টেশন কেমন ভাবে হতে পারে সেই কথা বলতে চেয়েছিলাম, ঠিক করে বলতে পারি নি :-)।
 arjo | 168.26.215.54 | ১৫ জুলাই ২০০৮ ১৯:৩৩399519
arjo | 168.26.215.54 | ১৫ জুলাই ২০০৮ ১৯:৩৩399519- আরও ভালো করে বল্লে, থিংকিং অ্যালাউড। পেশেণ্ট হিসেবে অসুবিধা কোথায় হয় বলতে পারি। আর নিজের মতন করে সলিউশন খোঁজার চেষ্টা করি। এই আর কি।
 shyamal | 64.47.121.98 | ১৫ জুলাই ২০০৮ ১৯:৪৪399521
shyamal | 64.47.121.98 | ১৫ জুলাই ২০০৮ ১৯:৪৪399521- এ ব্যাপারে আর্যর সঙ্গে এক মত। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রসেস বা মেথডোলজি হয়েছে অনেক। অন্য ফিল্ডের কথা জানিনা। তবে যদি কারো এম বি এ থাকে বলতে পারবেন যে ফর্মাল প্রসেস নিয়ে কোন সাবজেক্ট আছে কিনা। আমাদের দেশে শুধু চিকিৎসায় নয়, সর্ব ক্ষেত্রে প্রসেসের অভাব। যেখানে আছে , সেটাও একশো বছরের পুরোনো। প্রসেসের সঙ্গে আরেকটা জিনিষ আসে, কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট। প্রসেস কোন স্থাবর জিনিষ নয়। সব সময়েই তার উন্নতি করা যায়। কিন্তু প্রসেস হবে লিখিত।
আমাদের দেশে বহু ব্যাপারে অ্যাড হক পদ্ধতির কারণ হল কোন কর্মচারীকে প্রসেসে ট্রেন করা হয়না। প্রসেসে বিল্ট ইন চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সেস থাকে।
- মতামত দিন
-
বিষয়বস্তু*:
-
গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন
কোনোরকম কর্পোরেট ফান্ডিং ছাড়া সম্পূর্ণরূপে জনতার শ্রম ও অর্থে পরিচালিত এই নন-প্রফিট এবং স্বাধীন উদ্যোগটিকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুচণ্ডা৯-র গ্রাহক হোন। গুরুচণ্ডা৯তে প্রকাশিত লেখাগুলি পেতে চাইলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন, অথবা, আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলটির গ্রাহক হোন।
- ভাটিয়ালি | টইপত্তর | বুলবুলভাজা | হরিদাস পাল | খেরোর খাতা | বই
- বুলবুলভাজা : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... upal mukhopadhyay, যোষিতা, girija sankar kundu)
- হরিদাস পালেরা : যাঁরা সম্প্রতি লিখেছেন
(লিখছেন... dc, অরিন)
(লিখছেন... পাগল পাগল বোধ )
(লিখছেন... )
(লিখছেন... অরিন, সমরেশ মুখার্জী, অরিন)
(লিখছেন... পলিটিশিয়ান, হীরেন সিংহরায়, হীরেন সিংহরায়)
- টইপত্তর : সর্বশেষ লেখাগুলি
(লিখছেন... অরিন, অরিন, অমিতাভ চক্রবর্ত্তী)
(লিখছেন... সমরেশ মুখার্জী, ছোট মুখে , সমরেশ মুখার্জী)
(লিখছেন... dc, এক্সিট পোল ভোট শেয়ার, দেখা যাক)
(লিখছেন... kk, দীপ, dc)
(লিখছেন... )
- কি, কেন, ইত্যাদি
- বাজার অর্থনীতির ধরাবাঁধা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে এসে এমন এক আস্তানা বানাব আমরা, যেখানে ক্রমশ: মুছে যাবে লেখক ও পাঠকের বিস্তীর্ণ ব্যবধান। পাঠকই লেখক হবে, মিডিয়ার জগতে থাকবেনা কোন ব্যকরণশিক্ষক, ক্লাসরুমে থাকবেনা মিডিয়ার মাস্টারমশাইয়ের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম। এসব আদৌ হবে কিনা, গুরুচণ্ডালি টিকবে কিনা, সে পরের কথা, কিন্তু দু পা ফেলে দেখতে দোষ কী? ... আরও ...
- আমাদের কথা
- আপনি কি কম্পিউটার স্যাভি? সারাদিন মেশিনের সামনে বসে থেকে আপনার ঘাড়ে পিঠে কি স্পন্ডেলাইটিস আর চোখে পুরু অ্যান্টিগ্লেয়ার হাইপাওয়ার চশমা? এন্টার মেরে মেরে ডান হাতের কড়ি আঙুলে কি কড়া পড়ে গেছে? আপনি কি অন্তর্জালের গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়াছেন? সাইট থেকে সাইটান্তরে বাঁদরলাফ দিয়ে দিয়ে আপনি কি ক্লান্ত? বিরাট অঙ্কের টেলিফোন বিল কি জীবন থেকে সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে? আপনার দুশ্চিন্তার দিন শেষ হল। ... আরও ...
- বুলবুলভাজা
- এ হল ক্ষমতাহীনের মিডিয়া। গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল যখন নিজের ঢাক নিজে পেটায়, তখন তাকেই বলে হরিদাস পালের বুলবুলভাজা। পড়তে থাকুন রোজরোজ। দু-পয়সা দিতে পারেন আপনিও, কারণ ক্ষমতাহীন মানেই অক্ষম নয়। বুলবুলভাজায় বাছাই করা সম্পাদিত লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে লেখা দিতে হলে লেখাটি ইমেইল করুন, বা, গুরুচন্ডা৯ ব্লগ (হরিদাস পাল) বা অন্য কোথাও লেখা থাকলে সেই ওয়েব ঠিকানা পাঠান (ইমেইল ঠিকানা পাতার নীচে আছে), অনুমোদিত এবং সম্পাদিত হলে লেখা এখানে প্রকাশিত হবে। ... আরও ...
- হরিদাস পালেরা
- এটি একটি খোলা পাতা, যাকে আমরা ব্লগ বলে থাকি। গুরুচন্ডালির সম্পাদকমন্ডলীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই, স্বীকৃত ব্যবহারকারীরা এখানে নিজের লেখা লিখতে পারেন। সেটি গুরুচন্ডালি সাইটে দেখা যাবে। খুলে ফেলুন আপনার নিজের বাংলা ব্লগ, হয়ে উঠুন একমেবাদ্বিতীয়ম হরিদাস পাল, এ সুযোগ পাবেন না আর, দেখে যান নিজের চোখে...... আরও ...
- টইপত্তর
- নতুন কোনো বই পড়ছেন? সদ্য দেখা কোনো সিনেমা নিয়ে আলোচনার জায়গা খুঁজছেন? নতুন কোনো অ্যালবাম কানে লেগে আছে এখনও? সবাইকে জানান। এখনই। ভালো লাগলে হাত খুলে প্রশংসা করুন। খারাপ লাগলে চুটিয়ে গাল দিন। জ্ঞানের কথা বলার হলে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদুন। হাসুন কাঁদুন তক্কো করুন। স্রেফ এই কারণেই এই সাইটে আছে আমাদের বিভাগ টইপত্তর। ... আরও ...
- ভাটিয়া৯
- যে যা খুশি লিখবেন৷ লিখবেন এবং পোস্ট করবেন৷ তৎক্ষণাৎ তা উঠে যাবে এই পাতায়৷ এখানে এডিটিং এর রক্তচক্ষু নেই, সেন্সরশিপের ঝামেলা নেই৷ এখানে কোনো ভান নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা তৈরি করার কোনো ঝকমারি নেই৷ সাজানো বাগান নয়, আসুন তৈরি করি ফুল ফল ও বুনো আগাছায় ভরে থাকা এক নিজস্ব চারণভূমি৷ আসুন, গড়ে তুলি এক আড়ালহীন কমিউনিটি ... আরও ...
- টইপত্তর, ভাটিয়া৯, হরিদাস পাল(ব্লগ) এবং খেরোর খাতার লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, গুরুচণ্ডা৯র কোন দায়িত্ব নেই। | ♦ : পঠিত সংখ্যাটি ১৩ই জানুয়ারি ২০২০ থেকে, লেখাটি যদি তার আগে লেখা হয়ে থাকে তাহলে এই সংখ্যাটি সঠিক পরিমাপ নয়। এই বিভ্রান্তির জন্য আমরা দুঃখিত।
গুরুচণ্ডা৯-র সম্পাদিত বিভাগের যে কোনো লেখা অথবা লেখার অংশবিশেষ অন্যত্র প্রকাশ করার আগে গুরুচণ্ডা৯-র লিখিত অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।
অসম্পাদিত বিভাগের লেখা প্রকাশের সময় গুরুতে প্রকাশের উল্লেখ আমরা পারস্পরিক সৌজন্যের প্রকাশ হিসেবে অনুরোধ করি।
যোগাযোগ করুন, লেখা পাঠান এই ঠিকানায় : [email protected] ।
মে ১৩, ২০১৪ থেকে সাইটটি
বার পঠিত